ড. মইনুল ইসলাম
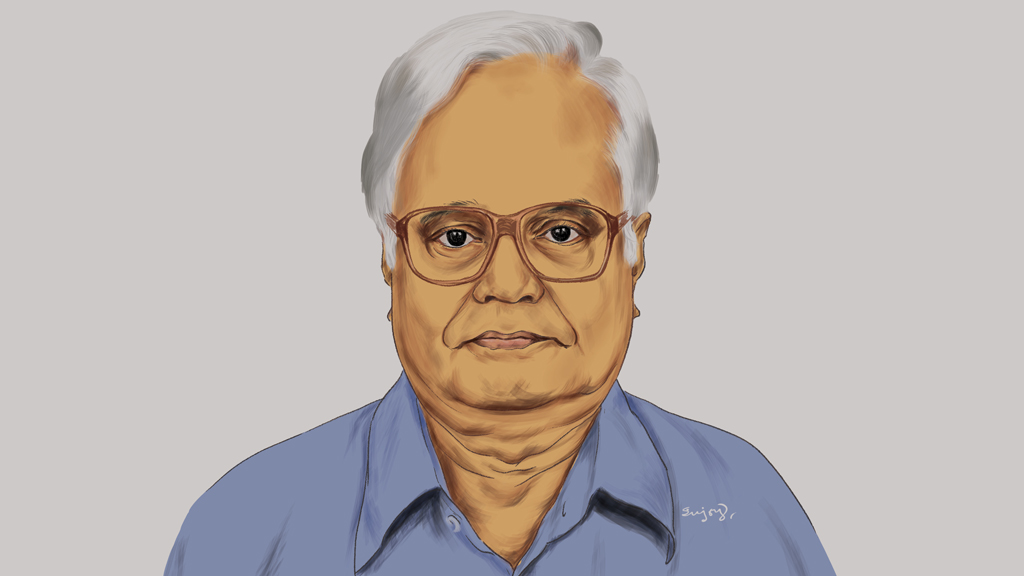
টাকার মানের এই ধস ঠেকানোর জন্য অবিলম্বে আমদানি নীতিতে কিছু কঠোর নিয়ন্ত্রণ চালু করা এখন সরকারের জন্য ফরজ হয়ে পড়েছে। কয়েক মাস ধরে দেশের রপ্তানি খাতের পুনরুদ্ধারের গতির চেয়ে আমদানি এলসি খোলার গতি অনেক বেশি বেড়ে চলেছে।
সম্প্রতি বাংলাদেশের মুদ্রা টাকার বিপরীতে ডলারের দাম হু হু করে বাড়তে শুরু করেছে। দুই মাস আগে এক ডলারের বিনিময়ে ব্যাংকে পাওয়া যেত ৮৪.৮০ থেকে ৮৫ টাকা, কার্ব মার্কেটে ডলারের দাম ছিল ৮৭ টাকা। এখন কার্ব মার্কেটে ১ ডলার কিনতে লাগছে ৯১ থেকে ৯২ টাকা, ব্যাংকে লাগছে ৮৯ টাকা। বাজারে ডলারের চাহিদা ও সরবরাহের মাঝে ক্রমবর্ধমান ঘাটতি সৃষ্টি হওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে টাকার মানে ধস নেমেছে, যা পুরো অর্থনীতির জন্য বড়সড় ‘অশনিসংকেত’ বলা চলে।
বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে টাকার মান কয়েক বছর ধরে ডলারে ৮৫ টাকার আশপাশে স্থিতিশীল ছিল, করোনাভাইরাস মহামারি আঘাত হানার পরও ওই মানে ধস নামেনি। রপ্তানি আয় ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ৪২ বিলিয়ন ডলার থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩৩ দশমিক ৬৭ বিলিয়ন ডলারে নেমে আসা সত্ত্বেও ফরমাল চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধির কারণে এবং আমদানি প্রবাহের নিম্নগতির ফলে টাকার মানে তেমন হেরফের ঘটেনি। মহামারির কারণে দেশে-বিদেশের হুন্ডিব্যবস্থাও প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পুঁজি পাচার ওই সময়ে অনেক কমে গিয়েছিল, যার ফলে ডলারের চাহিদায় উল্লেখযোগ্য কমতি দৃশ্যমান হয়েছিল। উপরন্তু, বাংলাদেশিদের বিদেশভ্রমণও ওই দেড় বছর প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ডলারের চাহিদা লক্ষণীয়ভাবে কমে গিয়েছিল। অথচ ওই সময়ে পাকিস্তান ও ভারতের রুপি ব্যাপক দরপতনের শিকার হয়েছে। কিন্তু গত কয়েক মাসে আবার আমদানির এলসি ব্যাপকভাবে বাড়তে থাকার পাশাপাশি জুলাই মাস থেকে চার মাস যাবৎ ফরমাল চ্যানেলের মাধ্যমে রেমিট্যান্স প্রেরণে বড়সড় নেতিবাচক প্রবণতা দেখা দেওয়ায় এই চার মাসে ডলারের চাহিদা ও সরবরাহের ক্রমবর্ধমান ফারাক সৃষ্টি হচ্ছে।
বোঝা যাচ্ছে, হুন্ডি-ডলারের বাজার আবারও চাঙা হয়ে উঠেছে। আমদানির নামে ওভার ইনভয়েসিং পদ্ধতিতে বিদেশে পুঁজি পাচারও আবার প্রবলাকার ধারণ করেছে। একই সঙ্গে বিদেশ থেকে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে আসা সম্প্রতি অনেকখানি কমে যাওয়ায় দেশে আসার সময় তাঁরা যে বিপুল পরিমাণ ডলার নিয়ে আসতেন, সেই প্রবাহেও বড়সড় ধস নেমেছে। কার্ব মার্কেটে ডলারের জোগানে বড়সড় ঘাটতির এটাই প্রধান কারণ।
বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকগুলোর কাছে বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রি ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে বৈদেশিক মুদ্রাবাজারকে স্থিতিশীল করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমদানি এলসি এত দ্রুত বাড়ছে যে তাদের প্রয়াস সংকট কাটিয়ে ওঠায় তেমন সফল হচ্ছে না। গত দুই মাসে বাংলাদেশ ব্যাংক ১৫০ কোটি ডলার বিক্রি করেছে, অথচ করোনাভাইরাস মহামারি আঘাত হানার পর তারা বৈদেশিক মুদ্রাবাজার থেকে ৭৭০ কোটি ডলার ক্রয় করে ডলারের তুলনায় টাকার মান বাড়তে দেয়নি। এই ক্রয়ের ফলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে ২০২১ সালের আগস্টে ৪৮ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে গিয়েছিল। ব্যবসায়ী মহল থেকে দাবি করা হচ্ছে যে করোনাভাইরাস মহামারির প্রকোপ কমে আসায় আমদানি প্রবাহের ক্রমবর্ধমান গতিশীলতা অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারের লক্ষণ। তাদের এই দাবি অর্ধসত্য, যা সমস্যার আসল রূপকে আড়াল করছে। ওভার ইনভয়েসিং পদ্ধতিতে পুঁজি পাচার বৃদ্ধি, হুন্ডিব্যবস্থা চাঙা হওয়া, ফরমাল চ্যানেলের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিদের রেমিট্যান্স প্রবাহে মহামারির সময়কালের স্ফীতির উল্টোযাত্রা, কার্ব মার্কেটে ডলারের জোগানে ধস—এগুলোর কোনোটাই দেশের জন্য হিতকর হবে না।
অতএব, আমার মতে, টাকার মানের এই ধস ঠেকানোর জন্য অবিলম্বে আমদানি নীতিতে কিছু কঠোর নিয়ন্ত্রণ চালু করা এখন সরকারের জন্য ফরজ হয়ে পড়েছে। কয়েক মাস ধরে দেশের রপ্তানি খাতের পুনরুদ্ধারের গতির চেয়ে আমদানি এলসি খোলার গতি অনেক বেশি বেড়ে চলেছে। এই আমদানি এলসিগুলো গভীরভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, এগুলোর উল্লেখযোগ্য অংশ আদতে অর্থনীতির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কারণে খোলা হচ্ছে না, প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি এলসি করা হচ্ছে বেশির ভাগ আইটেমের ক্ষেত্রে। অনেক কম প্রয়োজনীয় আইটেম আমদানির এলসি খোলারও হিড়িক পড়েছে। এখানেই রয়ে গেছে আসল ঘাপলা, প্রকৃতপক্ষে পুঁজি পাচার চাঙা হওয়ার কারণেই আমদানি এলসি করার হিড়িক পড়েছে। মহামারির কারণে উন্নত দেশগুলোর অর্থনীতি প্রায় দেড় বছর সংকটের গিরিখাতে পতিত হওয়ার ফলে বিদেশে অভিবাসন এবং বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পুঁজি পাচারে যে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছিল, এখন ওই অর্থনীতিগুলো আবার চাঙা হতে শুরু করায় বাধাগুলো ক্রমেই কেটে যাচ্ছে। ফলে ওই সব দেশের অভিবাসন-প্রক্রিয়াও আবার স্বাভাবিক গতি ফিরে পাচ্ছে। অতএব, বাংলাদেশের উচ্চ-মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং ধনাঢ্য পরিবারগুলোর দেশ থেকে বিদেশে অভিবাসন নিয়ে চলে যাওয়ার গতি এবং/অথবা বিদেশ ভ্রমণের হিড়িক আবার বেড়ে যাচ্ছে, একই সঙ্গে বাড়ছে হুন্ডি বাজারে এবং কার্ব মার্কেটে ডলার কেনার হিড়িক।
আমরা জানি, ডলারের তুলনায় টাকার মানে বর্তমানে যে ধস নেমেছে, সেটা দেশের রপ্তানিকারকদের আয়-উল্লম্ফন ঘটাবে। একই সঙ্গে প্রবাসী বাংলাদেশিদের রেমিট্যান্সের বিপরীতে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে প্রবাসীদের জন্যও এটা খুশির সংবাদ মনে হতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের মতো আমদানিনির্ভর অর্থনীতিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সিংহভাগই যেহেতু বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়, তাই টাকার মানের এই ধস বাজারে অবশ্যম্ভাবীভাবে মুদ্রাস্ফীতি ঘটাবেই। এমনিতেই বিশ্ববাজারে তেল, কয়লা ও এলএনজির দাম কয়েক গুণ বেড়ে গেছে গত এক বছরে, যার ফলে দেশে কেরোসিন, ডিজেল ও এলপিজির দাম ইতিমধ্যেই বাড়ানো হয়েছে।
গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। এর সঙ্গে যখন ডলারের দাম বাড়ার অভিঘাত যুক্ত হবে, তখন সব আমদানি করা আইটেমের দাম বাড়ানোর প্রয়োজন পড়বে। এই কয়েক মাসেই দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রায় আড়াই বিলিয়ন ডলার হ্রাস পেয়েছে, আগস্ট মাসের ৪৮ বিলিয়ন ডলার থেকে কমে তা ৪৬ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে গেছে।
গত কয়েক মাসে দেশের বাণিজ্য ভারসাম্যের ঘাটতি যেভাবে বেড়ে চলেছে, তাতে ২০২১-২২ অর্থবছরে সামগ্রিক লেনদেন ভারসাম্যের কারেন্ট অ্যাকাউন্টের ঘাটতি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাবে। এক দশক ধরে দেশের লেনদেন ভারসাম্যের কারেন্ট অ্যাকাউন্টে প্রায় প্রতিবছর উদ্বৃত্ত হতে থাকায় টাকার বৈদেশিক মান ডলারের তুলনায় বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা (মানে ১ ডলারের দাম ৮৫ টাকার নিচে নেমে আসার প্রবণতা) জোরদার হওয়া সত্ত্বেও রপ্তানিকারক এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্বার্থহানি ঘটার যুক্তিতে ১ ডলারে টাকার দাম ৮৫ টাকার নিচে নামতে দেওয়া হয়নি। আমাদের রপ্তানিপণ্যের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতাও এর ফলে বিঘ্নিত হতো বলে যুক্তি দেখানো হয়েছে। কিন্তু একটি দেশের মুদ্রার বৈদেশিক মান ক্রমেই উন্নীত (এপ্রেসিয়েশন) হতে থাকলে ওই দেশের অর্থনীতি সম্পর্কে বিশ্বে আস্থার সৃষ্টি হয়।
অতএব, আমার মতে, আইএমএফের পুরোনো দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে ডলারের তুলনায় টাকার মান বাড়তে না দেওয়ার অবস্থান গ্রহণ ঠিক হয়নি; বরং একটি দেশের মুদ্রার বৈদেশিক মানে ব্যাপক ধস নামলে কী সমস্যার সৃষ্টি হয়, তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছে পাকিস্তান। ২০০৭ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানি রুপির মান বাংলাদেশের টাকার চেয়ে বেশি ছিল, মানে এক রুপি দিয়ে এক টাকার বেশি পাওয়া যেত বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে। কিন্তু গত ১৪ বছরে রুপির মানের ক্রম-অবনমনের ধারাবাহিকতায় এখন ১ টাকায় প্রায় পাকিস্তানি ২ রুপি পাওয়া যায়, ১ ডলারের দাম পাকিস্তানে প্রায় ১৭০ রুপি। ভারতের রুপিও কয়েক বছর ধরে এই ক্রম-অবনমনের শিকার হয়েছে। ২০১৪ সালে ১ ডলারে ৬৩ ভারতীয় রুপি পাওয়া যেত, অথচ এখন ৭৫ ভারতীয় রুপি দিয়ে ১ ডলার কিনতে হয়।
দেশের মুদ্রার অবনমন হলেই ওই দেশের রপ্তানি বেড়ে যাবে বলে যে পুরোনো ধারণা ছিল, ভারতের ক্ষেত্রে তা-ও ভুল প্রমাণিত হয়েছে। ভারতের রপ্তানি আয় কয়েক বছর ধরে তেমন বাড়ছেই না। অতএব, বাংলাদেশি টাকার মানে ধস ঠেকানোর ব্যবস্থা গ্রহণ দেশের নীতি-প্রণেতাদের জন্য ফরজ হয়ে গেছে।
লেখক: অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
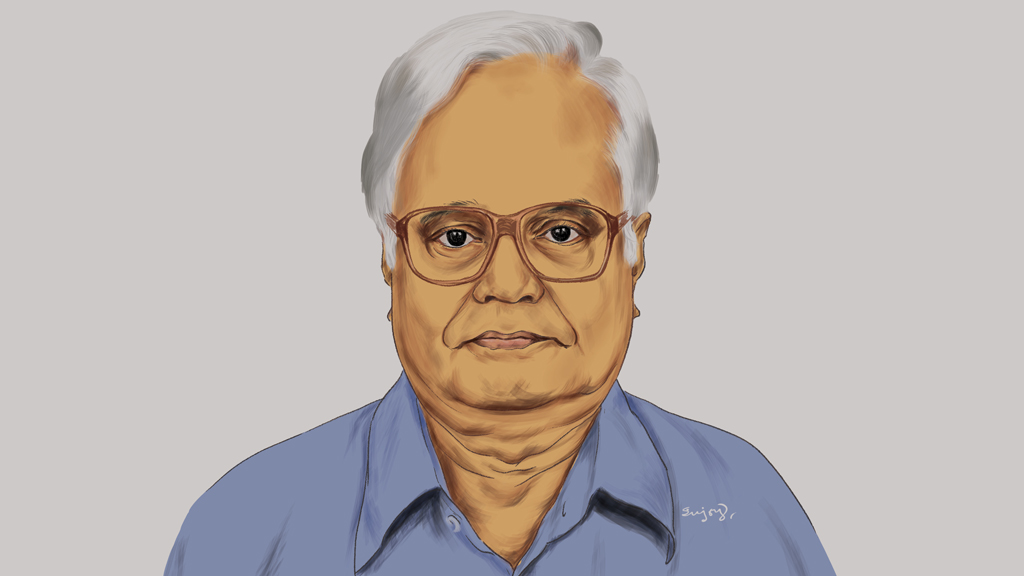
টাকার মানের এই ধস ঠেকানোর জন্য অবিলম্বে আমদানি নীতিতে কিছু কঠোর নিয়ন্ত্রণ চালু করা এখন সরকারের জন্য ফরজ হয়ে পড়েছে। কয়েক মাস ধরে দেশের রপ্তানি খাতের পুনরুদ্ধারের গতির চেয়ে আমদানি এলসি খোলার গতি অনেক বেশি বেড়ে চলেছে।
সম্প্রতি বাংলাদেশের মুদ্রা টাকার বিপরীতে ডলারের দাম হু হু করে বাড়তে শুরু করেছে। দুই মাস আগে এক ডলারের বিনিময়ে ব্যাংকে পাওয়া যেত ৮৪.৮০ থেকে ৮৫ টাকা, কার্ব মার্কেটে ডলারের দাম ছিল ৮৭ টাকা। এখন কার্ব মার্কেটে ১ ডলার কিনতে লাগছে ৯১ থেকে ৯২ টাকা, ব্যাংকে লাগছে ৮৯ টাকা। বাজারে ডলারের চাহিদা ও সরবরাহের মাঝে ক্রমবর্ধমান ঘাটতি সৃষ্টি হওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে টাকার মানে ধস নেমেছে, যা পুরো অর্থনীতির জন্য বড়সড় ‘অশনিসংকেত’ বলা চলে।
বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে টাকার মান কয়েক বছর ধরে ডলারে ৮৫ টাকার আশপাশে স্থিতিশীল ছিল, করোনাভাইরাস মহামারি আঘাত হানার পরও ওই মানে ধস নামেনি। রপ্তানি আয় ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ৪২ বিলিয়ন ডলার থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩৩ দশমিক ৬৭ বিলিয়ন ডলারে নেমে আসা সত্ত্বেও ফরমাল চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধির কারণে এবং আমদানি প্রবাহের নিম্নগতির ফলে টাকার মানে তেমন হেরফের ঘটেনি। মহামারির কারণে দেশে-বিদেশের হুন্ডিব্যবস্থাও প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পুঁজি পাচার ওই সময়ে অনেক কমে গিয়েছিল, যার ফলে ডলারের চাহিদায় উল্লেখযোগ্য কমতি দৃশ্যমান হয়েছিল। উপরন্তু, বাংলাদেশিদের বিদেশভ্রমণও ওই দেড় বছর প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ডলারের চাহিদা লক্ষণীয়ভাবে কমে গিয়েছিল। অথচ ওই সময়ে পাকিস্তান ও ভারতের রুপি ব্যাপক দরপতনের শিকার হয়েছে। কিন্তু গত কয়েক মাসে আবার আমদানির এলসি ব্যাপকভাবে বাড়তে থাকার পাশাপাশি জুলাই মাস থেকে চার মাস যাবৎ ফরমাল চ্যানেলের মাধ্যমে রেমিট্যান্স প্রেরণে বড়সড় নেতিবাচক প্রবণতা দেখা দেওয়ায় এই চার মাসে ডলারের চাহিদা ও সরবরাহের ক্রমবর্ধমান ফারাক সৃষ্টি হচ্ছে।
বোঝা যাচ্ছে, হুন্ডি-ডলারের বাজার আবারও চাঙা হয়ে উঠেছে। আমদানির নামে ওভার ইনভয়েসিং পদ্ধতিতে বিদেশে পুঁজি পাচারও আবার প্রবলাকার ধারণ করেছে। একই সঙ্গে বিদেশ থেকে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে আসা সম্প্রতি অনেকখানি কমে যাওয়ায় দেশে আসার সময় তাঁরা যে বিপুল পরিমাণ ডলার নিয়ে আসতেন, সেই প্রবাহেও বড়সড় ধস নেমেছে। কার্ব মার্কেটে ডলারের জোগানে বড়সড় ঘাটতির এটাই প্রধান কারণ।
বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকগুলোর কাছে বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রি ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে বৈদেশিক মুদ্রাবাজারকে স্থিতিশীল করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমদানি এলসি এত দ্রুত বাড়ছে যে তাদের প্রয়াস সংকট কাটিয়ে ওঠায় তেমন সফল হচ্ছে না। গত দুই মাসে বাংলাদেশ ব্যাংক ১৫০ কোটি ডলার বিক্রি করেছে, অথচ করোনাভাইরাস মহামারি আঘাত হানার পর তারা বৈদেশিক মুদ্রাবাজার থেকে ৭৭০ কোটি ডলার ক্রয় করে ডলারের তুলনায় টাকার মান বাড়তে দেয়নি। এই ক্রয়ের ফলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে ২০২১ সালের আগস্টে ৪৮ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে গিয়েছিল। ব্যবসায়ী মহল থেকে দাবি করা হচ্ছে যে করোনাভাইরাস মহামারির প্রকোপ কমে আসায় আমদানি প্রবাহের ক্রমবর্ধমান গতিশীলতা অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারের লক্ষণ। তাদের এই দাবি অর্ধসত্য, যা সমস্যার আসল রূপকে আড়াল করছে। ওভার ইনভয়েসিং পদ্ধতিতে পুঁজি পাচার বৃদ্ধি, হুন্ডিব্যবস্থা চাঙা হওয়া, ফরমাল চ্যানেলের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিদের রেমিট্যান্স প্রবাহে মহামারির সময়কালের স্ফীতির উল্টোযাত্রা, কার্ব মার্কেটে ডলারের জোগানে ধস—এগুলোর কোনোটাই দেশের জন্য হিতকর হবে না।
অতএব, আমার মতে, টাকার মানের এই ধস ঠেকানোর জন্য অবিলম্বে আমদানি নীতিতে কিছু কঠোর নিয়ন্ত্রণ চালু করা এখন সরকারের জন্য ফরজ হয়ে পড়েছে। কয়েক মাস ধরে দেশের রপ্তানি খাতের পুনরুদ্ধারের গতির চেয়ে আমদানি এলসি খোলার গতি অনেক বেশি বেড়ে চলেছে। এই আমদানি এলসিগুলো গভীরভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, এগুলোর উল্লেখযোগ্য অংশ আদতে অর্থনীতির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কারণে খোলা হচ্ছে না, প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি এলসি করা হচ্ছে বেশির ভাগ আইটেমের ক্ষেত্রে। অনেক কম প্রয়োজনীয় আইটেম আমদানির এলসি খোলারও হিড়িক পড়েছে। এখানেই রয়ে গেছে আসল ঘাপলা, প্রকৃতপক্ষে পুঁজি পাচার চাঙা হওয়ার কারণেই আমদানি এলসি করার হিড়িক পড়েছে। মহামারির কারণে উন্নত দেশগুলোর অর্থনীতি প্রায় দেড় বছর সংকটের গিরিখাতে পতিত হওয়ার ফলে বিদেশে অভিবাসন এবং বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পুঁজি পাচারে যে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছিল, এখন ওই অর্থনীতিগুলো আবার চাঙা হতে শুরু করায় বাধাগুলো ক্রমেই কেটে যাচ্ছে। ফলে ওই সব দেশের অভিবাসন-প্রক্রিয়াও আবার স্বাভাবিক গতি ফিরে পাচ্ছে। অতএব, বাংলাদেশের উচ্চ-মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং ধনাঢ্য পরিবারগুলোর দেশ থেকে বিদেশে অভিবাসন নিয়ে চলে যাওয়ার গতি এবং/অথবা বিদেশ ভ্রমণের হিড়িক আবার বেড়ে যাচ্ছে, একই সঙ্গে বাড়ছে হুন্ডি বাজারে এবং কার্ব মার্কেটে ডলার কেনার হিড়িক।
আমরা জানি, ডলারের তুলনায় টাকার মানে বর্তমানে যে ধস নেমেছে, সেটা দেশের রপ্তানিকারকদের আয়-উল্লম্ফন ঘটাবে। একই সঙ্গে প্রবাসী বাংলাদেশিদের রেমিট্যান্সের বিপরীতে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে প্রবাসীদের জন্যও এটা খুশির সংবাদ মনে হতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের মতো আমদানিনির্ভর অর্থনীতিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সিংহভাগই যেহেতু বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়, তাই টাকার মানের এই ধস বাজারে অবশ্যম্ভাবীভাবে মুদ্রাস্ফীতি ঘটাবেই। এমনিতেই বিশ্ববাজারে তেল, কয়লা ও এলএনজির দাম কয়েক গুণ বেড়ে গেছে গত এক বছরে, যার ফলে দেশে কেরোসিন, ডিজেল ও এলপিজির দাম ইতিমধ্যেই বাড়ানো হয়েছে।
গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। এর সঙ্গে যখন ডলারের দাম বাড়ার অভিঘাত যুক্ত হবে, তখন সব আমদানি করা আইটেমের দাম বাড়ানোর প্রয়োজন পড়বে। এই কয়েক মাসেই দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রায় আড়াই বিলিয়ন ডলার হ্রাস পেয়েছে, আগস্ট মাসের ৪৮ বিলিয়ন ডলার থেকে কমে তা ৪৬ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে গেছে।
গত কয়েক মাসে দেশের বাণিজ্য ভারসাম্যের ঘাটতি যেভাবে বেড়ে চলেছে, তাতে ২০২১-২২ অর্থবছরে সামগ্রিক লেনদেন ভারসাম্যের কারেন্ট অ্যাকাউন্টের ঘাটতি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাবে। এক দশক ধরে দেশের লেনদেন ভারসাম্যের কারেন্ট অ্যাকাউন্টে প্রায় প্রতিবছর উদ্বৃত্ত হতে থাকায় টাকার বৈদেশিক মান ডলারের তুলনায় বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা (মানে ১ ডলারের দাম ৮৫ টাকার নিচে নেমে আসার প্রবণতা) জোরদার হওয়া সত্ত্বেও রপ্তানিকারক এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্বার্থহানি ঘটার যুক্তিতে ১ ডলারে টাকার দাম ৮৫ টাকার নিচে নামতে দেওয়া হয়নি। আমাদের রপ্তানিপণ্যের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতাও এর ফলে বিঘ্নিত হতো বলে যুক্তি দেখানো হয়েছে। কিন্তু একটি দেশের মুদ্রার বৈদেশিক মান ক্রমেই উন্নীত (এপ্রেসিয়েশন) হতে থাকলে ওই দেশের অর্থনীতি সম্পর্কে বিশ্বে আস্থার সৃষ্টি হয়।
অতএব, আমার মতে, আইএমএফের পুরোনো দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে ডলারের তুলনায় টাকার মান বাড়তে না দেওয়ার অবস্থান গ্রহণ ঠিক হয়নি; বরং একটি দেশের মুদ্রার বৈদেশিক মানে ব্যাপক ধস নামলে কী সমস্যার সৃষ্টি হয়, তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছে পাকিস্তান। ২০০৭ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানি রুপির মান বাংলাদেশের টাকার চেয়ে বেশি ছিল, মানে এক রুপি দিয়ে এক টাকার বেশি পাওয়া যেত বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে। কিন্তু গত ১৪ বছরে রুপির মানের ক্রম-অবনমনের ধারাবাহিকতায় এখন ১ টাকায় প্রায় পাকিস্তানি ২ রুপি পাওয়া যায়, ১ ডলারের দাম পাকিস্তানে প্রায় ১৭০ রুপি। ভারতের রুপিও কয়েক বছর ধরে এই ক্রম-অবনমনের শিকার হয়েছে। ২০১৪ সালে ১ ডলারে ৬৩ ভারতীয় রুপি পাওয়া যেত, অথচ এখন ৭৫ ভারতীয় রুপি দিয়ে ১ ডলার কিনতে হয়।
দেশের মুদ্রার অবনমন হলেই ওই দেশের রপ্তানি বেড়ে যাবে বলে যে পুরোনো ধারণা ছিল, ভারতের ক্ষেত্রে তা-ও ভুল প্রমাণিত হয়েছে। ভারতের রপ্তানি আয় কয়েক বছর ধরে তেমন বাড়ছেই না। অতএব, বাংলাদেশি টাকার মানে ধস ঠেকানোর ব্যবস্থা গ্রহণ দেশের নীতি-প্রণেতাদের জন্য ফরজ হয়ে গেছে।
লেখক: অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

আজকের পত্রিকায় ১৩ আগস্ট একটি সংবাদ পড়ে এবং এ বিষয়ে টিভি চ্যানেলের সংবাদ দেখে মর্মাহত হয়েছিলাম। এভাবে কেউ কোনো দেশের একটি প্রাকৃতিক সম্পদের বিনাশ ঘটাতে পারে? আজকের পত্রিকায় ‘সাদাপাথরের সৌন্দর্য হারানোর কান্না’ শিরোনামের সে প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, গত বছরের ৫ আগস্ট সরকার পরিবর্তনের পর থেকেই শুরু হয় পাথর
৯ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা এখন শতাধিক। প্রতিবছর এখানে হাজারো গবেষণা হয়, যার বড় অংশের উদ্দেশ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশ। নিঃসন্দেহে বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষকের মর্যাদা এবং বৈশ্বিক পরিচিতি বৃদ্ধির অন্যতম মাধ্যম।
৯ ঘণ্টা আগে
খবরটি খুবই লজ্জার। বাংলাদেশ বিমানের একজন কেবিন ক্রু সোনা পাচারের দায়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন। ৪ আগস্ট বিকেলে সৌদি আরবের রিয়াদ থেকে বিজি-৩৪০ ফ্লাইটে ঢাকায় অবতরণ করার পর গ্রিন চ্যানেল অতিক্রমের সময় এই কেবিন ক্রুর গতিবিধিতে সন্দেহ জাগে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের। স্ক্যানিং মেশিনের নিচে তিনি পা দিয়ে কিছু লুকানোর
৯ ঘণ্টা আগে
সম্প্রতি ঢাকায় বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সম্মেলনে জাপানি বিনিয়োগ পরামর্শক তাকাও হিরোসে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও রাজনীতির জন্য অশনিসংকেত দিয়েছেন। তাঁর স্পষ্ট ভাষ্য, তাঁরা দ্রুত মুনাফার খোঁজে থাকা আগ্রাসী বিনিয়োগকারী, খামখেয়ালিও।
২০ ঘণ্টা আগে