সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

সাতচল্লিশের দেশভাগকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িকতা ক্রমাগত তীব্র হলো। রক্তপাত ঘটল। পরে যখন স্বাধীন হলো ভারতবর্ষ, তখন একটির জায়গায় দুটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটল। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার সমস্যার সমাধান হলো না; না পাকিস্তানে, না ভারতে। পাকিস্তানের সব ধর্মাবলম্বীকে বলা হলো রাজনৈতিকভাবে নিজ নিজ ধর্মমত ভুলে গিয়ে খাঁটি পাকিস্তানিতে পরিণত হতে। জিন্নাহ ধর্মীয় রাষ্ট্র চাননি, আধুনিক রাষ্ট্রই চেয়েছিলেন।
কিন্তু ধর্মের ভিত্তিটা তো রয়েই গেল রাষ্ট্রের মূলে। তা ছাড়া পাকিস্তান দ্রুত পরিণত হলো একটি আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে। সামরিক-বেসামরিক আমলারা রাষ্ট্র পরিচালনার কর্তৃত্ব দখল করে নিল। নিজেরা যদিও মোটেই ধার্মিক ছিল না, তথাপি তারা ধর্মকে ব্যবহার করতে চাইল, ঠিক সেই পুরোনো কারণেই। শ্রেণিবিভাজনকে অস্পষ্ট করে দেওয়ার জন্য। সেই সঙ্গে উগ্র ভারতবিদ্বেষ সৃষ্টি এবং সংখ্যাগুরু জনগণকে ধর্মচর্চার স্বাধীনতা (আসলে একমাত্র স্বাধীনতা) দিয়ে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর নিপীড়নমূলক চরিত্রকে আড়াল করে রাখার চেষ্টা করল।
তখনকার পূর্ব বাংলা এতে সন্তুষ্ট হয়নি। অভিজ্ঞতা সেখানকার মানুষকে দ্রুত বলে দিয়েছে যে ধর্মীয় বিভাজন যদিও মিথ্যা হয়, তবু তার চেয়ে অনেক বড় সত্য ভাষার বিভাজন। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের জায়গায় তাই নতুন চেতনা গড়ে উঠল, সেটি ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। ১৯৫২-এর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার প্রথম ব্যাপক রাষ্ট্রবিরোধী আন্দোলন। ভাষা পুরোপুরি ইহজাগতিক, ভাষা আন্দোলনও ছিল তাই। এখানে ধর্মের জন্য কোনো জায়গা ছিল না। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা। ওই আন্দোলন ক্রমাগত তীব্র হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তা স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। পাকিস্তানিরা ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের আওয়াজ থামায়নি। একাত্তরে যুদ্ধের সময় গণহত্যায় উদ্বুদ্ধকরণের প্রয়োজনে ব্যক্তিগতভাবে সর্বপ্রকার পাপাচারে লিপ্ত জেনারেলরা ইসলাম রক্ষার কথাই বলেছিল তাদের সৈন্যদের।
বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে। সেগুলো হলো জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র। কিন্তু এই মূলনীতিগুলো বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সেটি একটি মর্মান্তিক সত্য। রাষ্ট্রের হওয়ার কথা ছিল সম্পূর্ণরূপে ধর্মনিরপেক্ষ অর্থাৎ ইহজাগতিক। কিন্তু রাষ্ট্র তা হয়নি, কেন যে হয়নি তার কারণগুলো বেশ স্পষ্ট। প্রথম সত্য হলো এই যে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থটাই শাসকশ্রেণির কাছে পরিষ্কার ছিল না। এমনকি তাঁদের কাছেও নয়, যাঁরা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন এবং ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ধ্বজাধারীদের বিরুদ্ধে লড়েছেন। ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে তাঁরা ইহলৌকিকতা বোঝাননি, বোঝাননি এই প্রয়োজনটা যে ধর্ম ও রাষ্ট্রকে আলাদা করে ফেলতে হবে পরস্পর থেকে। বরং উল্টো বুঝিয়েছেন, সব ধর্মের সমান অধিকার এবং পারলে আরও বেশি ধর্মচর্চা করা। দ্বিতীয় সত্য এই যে শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর রাষ্ট্রক্ষমতায় যারা এসেছে, তারা অনেকেই ছিল পাকিস্তানপন্থী। পাকিস্তানের প্রতি দুর্বলতা ছাড়াও তাদের ভেতর আরেকটি প্রবণতা ছিল। সেটি হলো বাংলাদেশকে একটি আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করা। তাদের প্রভু ও সমমনারা একদা যেমন করেছিল পাকিস্তানকে। তবে প্রয়োজনটা বাইরে থেকে আসেনি, উৎপন্ন হয়েছে ভেতরের প্রয়োজন থেকেই। সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রই দেশ শাসন করবে, বিশেষ করে শেখ মুজিবের পর থেকে, তারা রাষ্ট্রকে তাদের মনের মতো করে তৈরি করে নেবে এটাই স্বাভাবিক। সেই ঘটনাই পুনরায় ঘটছে বাংলাদেশে। আর লেজ টানলে যেমন মাথা আসে, তেমনি আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহারের আবশ্যকতাটাও ফিরে এসেছে। যার ফলে দেখা গেল দেশের সংবিধান থেকে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান স্বয়ং ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র কেটে বাদ দিয়ে দিলেন। গণতন্ত্র তো ছিলই না। সামরিক আমলাদের শাসন চলছিল; বাঙালি জাতীয়তাবাদও গেল। সে জায়গায় আনা হলো বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ। এরশাদ ব্যাপারটাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন। তিনি সংবিধানকে আরও একবার রক্তাক্ত করে দিয়ে রাষ্ট্রধর্ম প্রবর্তন করলেন। সময় পেলে হয়তো রাষ্ট্রের নামই বদলে দেওয়ার পদক্ষেপ নিতেন। সময় পাননি। যার পাঁয়তারা এখন আমরা দেখতে পারছি।
জিয়ার সময় রুশ-ভারত বিরোধিতার একটা আওয়াজ উঠেছিল। জিয়াই তুলে দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের বামপন্থীদের একাংশ ওই আওয়াজে আকৃষ্ট হয়ে জিয়ার সঙ্গে সহযোগিতায় মেতে উঠেছিল। তাতে রুশ-ভারতের ক্ষতি-বৃদ্ধি যা-ই হোক না কেন, জিয়াউর রহমানের বেশ সুবিধা হয়েছিল। তাঁর শক্ত হাত আরও শক্ত হয়ে উঠেছিল। তারই ধারাবাহিকতা বর্তমানে দেখা যাচ্ছে।
জিয়ার পরে জেনারেল এরশাদ এলেন। মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে তাঁর ক্ষীণতম সম্পর্কও ছিল না। তিনি ছিলেন উল্টো দিকে। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন জনগণকে শান্তি এনে দেবেন। দিতে পারলেন না। প্রতিশ্রুতি ছিল দুর্নীতি দমনের, পারেননি তো বটেই, বরং তাঁর প্রশ্রয়ে দুর্নীতি বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষানীতি থেকে শুরু করে সাইকেলে চড়ে অফিসে যাওয়ার নীতি পর্যন্ত তাঁর সব নীতিই চরমভাবে ব্যর্থ হয়ে গেছে। ফলে আর কিছু না পেয়ে তিনি ধর্ম দিলেন। রাষ্ট্রীয় ধর্ম প্রবর্তন করলেন, সেই পাকিস্তানি শাসকদের কায়দায়।
২. সংস্কারের প্রয়োজনে অন্তর্বর্তী সরকার ১১টি কমিশন গঠন করেছে, কিন্তু তারা শিক্ষা সংস্কারের লক্ষ্যে যে কোনো কমিশন গঠন করেনি, এ জন্য অবশ্যই প্রশংসা দাবি করতে পারে। আমাদের মূল ধারার শিক্ষাব্যবস্থা এমনিতেই নড়বড়ে অবস্থায় রয়েছে, তার মধ্যে আবার সংস্কারের ধাক্কাধাক্কি সে বেচারাকে নতুন জ্বালাতনের মধ্যে ফেলুক, এটা মোটেই কাঙ্ক্ষিত নয়। অতীতে দেখা গেছে যে যখনই কোনো ‘বৈপ্লবিক’ সরকারের আগমন ঘটে, তখনই সঙ্গে সঙ্গেই, তারা শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি ঘটানোর জন্য ব্যস্তসমস্ত হয়ে পড়ে এবং মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থা একটা ধাক্কা খায়। পরবর্তী ‘বিপ্লবী’ সরকার আবার নতুন সংস্কারে হাত লাগিয়ে ব্যবস্থাটাকে আরেকটা ধাক্কা দেয়। মূল যে সংস্কার প্রয়োজন, সেটা হলো একটি অভিন্ন ব্যবস্থা চালু করা, রাষ্ট্রপরিচালকেরা সে ব্যাপারটাকে বিবেচনার মধ্যেই আনেন না। বৈষম্যনির্ভর পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটা আগের মতোই সহাস্যে টিকে থাকে।
বিগত আওয়ামী লীগ সরকার সংস্কারের নাম করে কয়েকটি অতিরিক্ত পাবলিক পরীক্ষার সংযোজন ঘটিয়ে মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সাধনে তৎপর হয়েছিল। তাতে দুর্বল ব্যবস্থাটা আরও একটা ঝুঁকির মুখে পড়েছিল। বিভিন্ন মহল থেকে প্রতিবাদ ওঠায় তারা অতিরিক্ত পরীক্ষা রদ করেছে। কিন্তু ২০১৭ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড যে তাদের নিজেদের প্রণীত বাংলা পাঠ্যপুস্তক থেকে আচমকা ১১টি কবিতা, ৫টি গল্প ও প্রবন্ধ বাদ দিয়ে দিল, সেই বৈপ্লবিক কাজটি কেন করা হলো তার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর তাদের অনেক নৃশংসতা, অপকর্ম ও দুর্নীতির তদন্ত করা হচ্ছে এবং হতে থাকবে, কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের ওপর নির্মম ও ক্ষতিকর হামলাটি কেন ঘটেছিল, সে বিষয়ে কোনো তদন্ত হয়নি। তদন্ত হওয়াটা কিন্তু আবশ্যক। জানা দরকার শিক্ষার ওপর অমন হস্তক্ষেপটি কারা এবং কীভাবে ঘটিয়েছিল। কাজটা বর্তমান সরকার শিক্ষাকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে সেটা জানার ব্যাপারেও সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।
ভালো কথা, বিগত সরকার দেশে যে ৫৬০টি মডেল মসজিদ নির্মাণ করেছিল, তার জন্য অর্থ ও অনুপ্রেরণা কোথা থেকে এসেছিল সে ব্যাপারে জনমনে বড় রকমের একটা জিজ্ঞাসা রয়ে গেছে। শোনা গিয়েছিল যে টাকাটা এসেছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে; এমনও ধারণা ছিল যে ওই তহবিল মধ্যপ্রাচ্যের মাধ্যমে এসেছে ঠিকই, কিন্তু প্রেরক হচ্ছে সিআইএ; এখন নাকি প্রকাশ পেয়েছে টাকা অন্য কেউ দেয়নি, দিয়েছে সরকার নিজেই। একসময়ে ঢাকা শহরকে বলা হতো মসজিদের শহর। সেই সুখ্যাতি এখন বিলক্ষণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে; শুধু ঢাকা শহর নয়, বাংলাদেশের কোথাও মসজিদের কোনো অভাব নেই। মসজিদ প্রতিষ্ঠার নামে সরকারি জায়গা দখল করা হয়েছে, এমন অভিযোগও বিস্তর শোনা গেছে। তার মধ্যে হঠাৎ করে আবার মডেল মসজিদ তৈরির আবশ্যকতা কেন দেখা দিল। বিগত সরকার দেশব্যাপী মডেল সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে এমন খবর কিন্তু আমাদের জানা নেই। তাহলে?
এসব হলো রাজনৈতিক ঘটনা। পাশাপাশি এ সত্যও তো রয়ে গেছে যে উপমহাদেশের যে সাংস্কৃতিক ভূমি ধর্মবাদিতা ও ধর্মভীরুতার বিকাশের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী, সে ভূমি বাংলাদেশেও বিদ্যমান। বাংলাদেশে তার উর্বরাশক্তি বরং বেশি। কেননা দেশটি অনেক বেশি দরিদ্র, অনেক বেশি পশ্চাৎপদ। দীর্ঘকাল এ ভূমি পরাধীন ছিল। আজও সে স্বাধীন নয়। আজও সে বিশ্ব পুঁজিবাদের অধীন। কাজেই মানুষ এখানে আত্মসমর্পণে অভ্যস্ত। সে আত্মসমর্পণ করেছে বিদেশি শাসকের কাছে, করেছে ভাগ্যের কাছে। তার আত্মবিশ্বাস নেই। তার জন্য খুবই প্রয়োজন পারলৌকিক আশ্রয়ের। যে জন্য ধর্মবাদিতা ও সাম্প্রদায়িকতা দুটোই টিকে আছে এবং সুযোগ পেয়ে এখন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, এ দেশে।

সাতচল্লিশের দেশভাগকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িকতা ক্রমাগত তীব্র হলো। রক্তপাত ঘটল। পরে যখন স্বাধীন হলো ভারতবর্ষ, তখন একটির জায়গায় দুটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটল। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার সমস্যার সমাধান হলো না; না পাকিস্তানে, না ভারতে। পাকিস্তানের সব ধর্মাবলম্বীকে বলা হলো রাজনৈতিকভাবে নিজ নিজ ধর্মমত ভুলে গিয়ে খাঁটি পাকিস্তানিতে পরিণত হতে। জিন্নাহ ধর্মীয় রাষ্ট্র চাননি, আধুনিক রাষ্ট্রই চেয়েছিলেন।
কিন্তু ধর্মের ভিত্তিটা তো রয়েই গেল রাষ্ট্রের মূলে। তা ছাড়া পাকিস্তান দ্রুত পরিণত হলো একটি আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে। সামরিক-বেসামরিক আমলারা রাষ্ট্র পরিচালনার কর্তৃত্ব দখল করে নিল। নিজেরা যদিও মোটেই ধার্মিক ছিল না, তথাপি তারা ধর্মকে ব্যবহার করতে চাইল, ঠিক সেই পুরোনো কারণেই। শ্রেণিবিভাজনকে অস্পষ্ট করে দেওয়ার জন্য। সেই সঙ্গে উগ্র ভারতবিদ্বেষ সৃষ্টি এবং সংখ্যাগুরু জনগণকে ধর্মচর্চার স্বাধীনতা (আসলে একমাত্র স্বাধীনতা) দিয়ে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর নিপীড়নমূলক চরিত্রকে আড়াল করে রাখার চেষ্টা করল।
তখনকার পূর্ব বাংলা এতে সন্তুষ্ট হয়নি। অভিজ্ঞতা সেখানকার মানুষকে দ্রুত বলে দিয়েছে যে ধর্মীয় বিভাজন যদিও মিথ্যা হয়, তবু তার চেয়ে অনেক বড় সত্য ভাষার বিভাজন। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের জায়গায় তাই নতুন চেতনা গড়ে উঠল, সেটি ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। ১৯৫২-এর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার প্রথম ব্যাপক রাষ্ট্রবিরোধী আন্দোলন। ভাষা পুরোপুরি ইহজাগতিক, ভাষা আন্দোলনও ছিল তাই। এখানে ধর্মের জন্য কোনো জায়গা ছিল না। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা। ওই আন্দোলন ক্রমাগত তীব্র হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তা স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। পাকিস্তানিরা ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের আওয়াজ থামায়নি। একাত্তরে যুদ্ধের সময় গণহত্যায় উদ্বুদ্ধকরণের প্রয়োজনে ব্যক্তিগতভাবে সর্বপ্রকার পাপাচারে লিপ্ত জেনারেলরা ইসলাম রক্ষার কথাই বলেছিল তাদের সৈন্যদের।
বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে। সেগুলো হলো জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র। কিন্তু এই মূলনীতিগুলো বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সেটি একটি মর্মান্তিক সত্য। রাষ্ট্রের হওয়ার কথা ছিল সম্পূর্ণরূপে ধর্মনিরপেক্ষ অর্থাৎ ইহজাগতিক। কিন্তু রাষ্ট্র তা হয়নি, কেন যে হয়নি তার কারণগুলো বেশ স্পষ্ট। প্রথম সত্য হলো এই যে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থটাই শাসকশ্রেণির কাছে পরিষ্কার ছিল না। এমনকি তাঁদের কাছেও নয়, যাঁরা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন এবং ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ধ্বজাধারীদের বিরুদ্ধে লড়েছেন। ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে তাঁরা ইহলৌকিকতা বোঝাননি, বোঝাননি এই প্রয়োজনটা যে ধর্ম ও রাষ্ট্রকে আলাদা করে ফেলতে হবে পরস্পর থেকে। বরং উল্টো বুঝিয়েছেন, সব ধর্মের সমান অধিকার এবং পারলে আরও বেশি ধর্মচর্চা করা। দ্বিতীয় সত্য এই যে শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর রাষ্ট্রক্ষমতায় যারা এসেছে, তারা অনেকেই ছিল পাকিস্তানপন্থী। পাকিস্তানের প্রতি দুর্বলতা ছাড়াও তাদের ভেতর আরেকটি প্রবণতা ছিল। সেটি হলো বাংলাদেশকে একটি আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করা। তাদের প্রভু ও সমমনারা একদা যেমন করেছিল পাকিস্তানকে। তবে প্রয়োজনটা বাইরে থেকে আসেনি, উৎপন্ন হয়েছে ভেতরের প্রয়োজন থেকেই। সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রই দেশ শাসন করবে, বিশেষ করে শেখ মুজিবের পর থেকে, তারা রাষ্ট্রকে তাদের মনের মতো করে তৈরি করে নেবে এটাই স্বাভাবিক। সেই ঘটনাই পুনরায় ঘটছে বাংলাদেশে। আর লেজ টানলে যেমন মাথা আসে, তেমনি আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহারের আবশ্যকতাটাও ফিরে এসেছে। যার ফলে দেখা গেল দেশের সংবিধান থেকে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান স্বয়ং ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র কেটে বাদ দিয়ে দিলেন। গণতন্ত্র তো ছিলই না। সামরিক আমলাদের শাসন চলছিল; বাঙালি জাতীয়তাবাদও গেল। সে জায়গায় আনা হলো বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ। এরশাদ ব্যাপারটাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন। তিনি সংবিধানকে আরও একবার রক্তাক্ত করে দিয়ে রাষ্ট্রধর্ম প্রবর্তন করলেন। সময় পেলে হয়তো রাষ্ট্রের নামই বদলে দেওয়ার পদক্ষেপ নিতেন। সময় পাননি। যার পাঁয়তারা এখন আমরা দেখতে পারছি।
জিয়ার সময় রুশ-ভারত বিরোধিতার একটা আওয়াজ উঠেছিল। জিয়াই তুলে দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের বামপন্থীদের একাংশ ওই আওয়াজে আকৃষ্ট হয়ে জিয়ার সঙ্গে সহযোগিতায় মেতে উঠেছিল। তাতে রুশ-ভারতের ক্ষতি-বৃদ্ধি যা-ই হোক না কেন, জিয়াউর রহমানের বেশ সুবিধা হয়েছিল। তাঁর শক্ত হাত আরও শক্ত হয়ে উঠেছিল। তারই ধারাবাহিকতা বর্তমানে দেখা যাচ্ছে।
জিয়ার পরে জেনারেল এরশাদ এলেন। মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে তাঁর ক্ষীণতম সম্পর্কও ছিল না। তিনি ছিলেন উল্টো দিকে। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন জনগণকে শান্তি এনে দেবেন। দিতে পারলেন না। প্রতিশ্রুতি ছিল দুর্নীতি দমনের, পারেননি তো বটেই, বরং তাঁর প্রশ্রয়ে দুর্নীতি বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষানীতি থেকে শুরু করে সাইকেলে চড়ে অফিসে যাওয়ার নীতি পর্যন্ত তাঁর সব নীতিই চরমভাবে ব্যর্থ হয়ে গেছে। ফলে আর কিছু না পেয়ে তিনি ধর্ম দিলেন। রাষ্ট্রীয় ধর্ম প্রবর্তন করলেন, সেই পাকিস্তানি শাসকদের কায়দায়।
২. সংস্কারের প্রয়োজনে অন্তর্বর্তী সরকার ১১টি কমিশন গঠন করেছে, কিন্তু তারা শিক্ষা সংস্কারের লক্ষ্যে যে কোনো কমিশন গঠন করেনি, এ জন্য অবশ্যই প্রশংসা দাবি করতে পারে। আমাদের মূল ধারার শিক্ষাব্যবস্থা এমনিতেই নড়বড়ে অবস্থায় রয়েছে, তার মধ্যে আবার সংস্কারের ধাক্কাধাক্কি সে বেচারাকে নতুন জ্বালাতনের মধ্যে ফেলুক, এটা মোটেই কাঙ্ক্ষিত নয়। অতীতে দেখা গেছে যে যখনই কোনো ‘বৈপ্লবিক’ সরকারের আগমন ঘটে, তখনই সঙ্গে সঙ্গেই, তারা শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি ঘটানোর জন্য ব্যস্তসমস্ত হয়ে পড়ে এবং মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থা একটা ধাক্কা খায়। পরবর্তী ‘বিপ্লবী’ সরকার আবার নতুন সংস্কারে হাত লাগিয়ে ব্যবস্থাটাকে আরেকটা ধাক্কা দেয়। মূল যে সংস্কার প্রয়োজন, সেটা হলো একটি অভিন্ন ব্যবস্থা চালু করা, রাষ্ট্রপরিচালকেরা সে ব্যাপারটাকে বিবেচনার মধ্যেই আনেন না। বৈষম্যনির্ভর পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটা আগের মতোই সহাস্যে টিকে থাকে।
বিগত আওয়ামী লীগ সরকার সংস্কারের নাম করে কয়েকটি অতিরিক্ত পাবলিক পরীক্ষার সংযোজন ঘটিয়ে মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সাধনে তৎপর হয়েছিল। তাতে দুর্বল ব্যবস্থাটা আরও একটা ঝুঁকির মুখে পড়েছিল। বিভিন্ন মহল থেকে প্রতিবাদ ওঠায় তারা অতিরিক্ত পরীক্ষা রদ করেছে। কিন্তু ২০১৭ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড যে তাদের নিজেদের প্রণীত বাংলা পাঠ্যপুস্তক থেকে আচমকা ১১টি কবিতা, ৫টি গল্প ও প্রবন্ধ বাদ দিয়ে দিল, সেই বৈপ্লবিক কাজটি কেন করা হলো তার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর তাদের অনেক নৃশংসতা, অপকর্ম ও দুর্নীতির তদন্ত করা হচ্ছে এবং হতে থাকবে, কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের ওপর নির্মম ও ক্ষতিকর হামলাটি কেন ঘটেছিল, সে বিষয়ে কোনো তদন্ত হয়নি। তদন্ত হওয়াটা কিন্তু আবশ্যক। জানা দরকার শিক্ষার ওপর অমন হস্তক্ষেপটি কারা এবং কীভাবে ঘটিয়েছিল। কাজটা বর্তমান সরকার শিক্ষাকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে সেটা জানার ব্যাপারেও সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।
ভালো কথা, বিগত সরকার দেশে যে ৫৬০টি মডেল মসজিদ নির্মাণ করেছিল, তার জন্য অর্থ ও অনুপ্রেরণা কোথা থেকে এসেছিল সে ব্যাপারে জনমনে বড় রকমের একটা জিজ্ঞাসা রয়ে গেছে। শোনা গিয়েছিল যে টাকাটা এসেছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে; এমনও ধারণা ছিল যে ওই তহবিল মধ্যপ্রাচ্যের মাধ্যমে এসেছে ঠিকই, কিন্তু প্রেরক হচ্ছে সিআইএ; এখন নাকি প্রকাশ পেয়েছে টাকা অন্য কেউ দেয়নি, দিয়েছে সরকার নিজেই। একসময়ে ঢাকা শহরকে বলা হতো মসজিদের শহর। সেই সুখ্যাতি এখন বিলক্ষণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে; শুধু ঢাকা শহর নয়, বাংলাদেশের কোথাও মসজিদের কোনো অভাব নেই। মসজিদ প্রতিষ্ঠার নামে সরকারি জায়গা দখল করা হয়েছে, এমন অভিযোগও বিস্তর শোনা গেছে। তার মধ্যে হঠাৎ করে আবার মডেল মসজিদ তৈরির আবশ্যকতা কেন দেখা দিল। বিগত সরকার দেশব্যাপী মডেল সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে এমন খবর কিন্তু আমাদের জানা নেই। তাহলে?
এসব হলো রাজনৈতিক ঘটনা। পাশাপাশি এ সত্যও তো রয়ে গেছে যে উপমহাদেশের যে সাংস্কৃতিক ভূমি ধর্মবাদিতা ও ধর্মভীরুতার বিকাশের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী, সে ভূমি বাংলাদেশেও বিদ্যমান। বাংলাদেশে তার উর্বরাশক্তি বরং বেশি। কেননা দেশটি অনেক বেশি দরিদ্র, অনেক বেশি পশ্চাৎপদ। দীর্ঘকাল এ ভূমি পরাধীন ছিল। আজও সে স্বাধীন নয়। আজও সে বিশ্ব পুঁজিবাদের অধীন। কাজেই মানুষ এখানে আত্মসমর্পণে অভ্যস্ত। সে আত্মসমর্পণ করেছে বিদেশি শাসকের কাছে, করেছে ভাগ্যের কাছে। তার আত্মবিশ্বাস নেই। তার জন্য খুবই প্রয়োজন পারলৌকিক আশ্রয়ের। যে জন্য ধর্মবাদিতা ও সাম্প্রদায়িকতা দুটোই টিকে আছে এবং সুযোগ পেয়ে এখন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, এ দেশে।
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

সাতচল্লিশের দেশভাগকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িকতা ক্রমাগত তীব্র হলো। রক্তপাত ঘটল। পরে যখন স্বাধীন হলো ভারতবর্ষ, তখন একটির জায়গায় দুটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটল। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার সমস্যার সমাধান হলো না; না পাকিস্তানে, না ভারতে। পাকিস্তানের সব ধর্মাবলম্বীকে বলা হলো রাজনৈতিকভাবে নিজ নিজ ধর্মমত ভুলে গিয়ে খাঁটি পাকিস্তানিতে পরিণত হতে। জিন্নাহ ধর্মীয় রাষ্ট্র চাননি, আধুনিক রাষ্ট্রই চেয়েছিলেন।
কিন্তু ধর্মের ভিত্তিটা তো রয়েই গেল রাষ্ট্রের মূলে। তা ছাড়া পাকিস্তান দ্রুত পরিণত হলো একটি আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে। সামরিক-বেসামরিক আমলারা রাষ্ট্র পরিচালনার কর্তৃত্ব দখল করে নিল। নিজেরা যদিও মোটেই ধার্মিক ছিল না, তথাপি তারা ধর্মকে ব্যবহার করতে চাইল, ঠিক সেই পুরোনো কারণেই। শ্রেণিবিভাজনকে অস্পষ্ট করে দেওয়ার জন্য। সেই সঙ্গে উগ্র ভারতবিদ্বেষ সৃষ্টি এবং সংখ্যাগুরু জনগণকে ধর্মচর্চার স্বাধীনতা (আসলে একমাত্র স্বাধীনতা) দিয়ে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর নিপীড়নমূলক চরিত্রকে আড়াল করে রাখার চেষ্টা করল।
তখনকার পূর্ব বাংলা এতে সন্তুষ্ট হয়নি। অভিজ্ঞতা সেখানকার মানুষকে দ্রুত বলে দিয়েছে যে ধর্মীয় বিভাজন যদিও মিথ্যা হয়, তবু তার চেয়ে অনেক বড় সত্য ভাষার বিভাজন। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের জায়গায় তাই নতুন চেতনা গড়ে উঠল, সেটি ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। ১৯৫২-এর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার প্রথম ব্যাপক রাষ্ট্রবিরোধী আন্দোলন। ভাষা পুরোপুরি ইহজাগতিক, ভাষা আন্দোলনও ছিল তাই। এখানে ধর্মের জন্য কোনো জায়গা ছিল না। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা। ওই আন্দোলন ক্রমাগত তীব্র হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তা স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। পাকিস্তানিরা ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের আওয়াজ থামায়নি। একাত্তরে যুদ্ধের সময় গণহত্যায় উদ্বুদ্ধকরণের প্রয়োজনে ব্যক্তিগতভাবে সর্বপ্রকার পাপাচারে লিপ্ত জেনারেলরা ইসলাম রক্ষার কথাই বলেছিল তাদের সৈন্যদের।
বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে। সেগুলো হলো জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র। কিন্তু এই মূলনীতিগুলো বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সেটি একটি মর্মান্তিক সত্য। রাষ্ট্রের হওয়ার কথা ছিল সম্পূর্ণরূপে ধর্মনিরপেক্ষ অর্থাৎ ইহজাগতিক। কিন্তু রাষ্ট্র তা হয়নি, কেন যে হয়নি তার কারণগুলো বেশ স্পষ্ট। প্রথম সত্য হলো এই যে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থটাই শাসকশ্রেণির কাছে পরিষ্কার ছিল না। এমনকি তাঁদের কাছেও নয়, যাঁরা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন এবং ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ধ্বজাধারীদের বিরুদ্ধে লড়েছেন। ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে তাঁরা ইহলৌকিকতা বোঝাননি, বোঝাননি এই প্রয়োজনটা যে ধর্ম ও রাষ্ট্রকে আলাদা করে ফেলতে হবে পরস্পর থেকে। বরং উল্টো বুঝিয়েছেন, সব ধর্মের সমান অধিকার এবং পারলে আরও বেশি ধর্মচর্চা করা। দ্বিতীয় সত্য এই যে শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর রাষ্ট্রক্ষমতায় যারা এসেছে, তারা অনেকেই ছিল পাকিস্তানপন্থী। পাকিস্তানের প্রতি দুর্বলতা ছাড়াও তাদের ভেতর আরেকটি প্রবণতা ছিল। সেটি হলো বাংলাদেশকে একটি আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করা। তাদের প্রভু ও সমমনারা একদা যেমন করেছিল পাকিস্তানকে। তবে প্রয়োজনটা বাইরে থেকে আসেনি, উৎপন্ন হয়েছে ভেতরের প্রয়োজন থেকেই। সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রই দেশ শাসন করবে, বিশেষ করে শেখ মুজিবের পর থেকে, তারা রাষ্ট্রকে তাদের মনের মতো করে তৈরি করে নেবে এটাই স্বাভাবিক। সেই ঘটনাই পুনরায় ঘটছে বাংলাদেশে। আর লেজ টানলে যেমন মাথা আসে, তেমনি আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহারের আবশ্যকতাটাও ফিরে এসেছে। যার ফলে দেখা গেল দেশের সংবিধান থেকে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান স্বয়ং ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র কেটে বাদ দিয়ে দিলেন। গণতন্ত্র তো ছিলই না। সামরিক আমলাদের শাসন চলছিল; বাঙালি জাতীয়তাবাদও গেল। সে জায়গায় আনা হলো বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ। এরশাদ ব্যাপারটাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন। তিনি সংবিধানকে আরও একবার রক্তাক্ত করে দিয়ে রাষ্ট্রধর্ম প্রবর্তন করলেন। সময় পেলে হয়তো রাষ্ট্রের নামই বদলে দেওয়ার পদক্ষেপ নিতেন। সময় পাননি। যার পাঁয়তারা এখন আমরা দেখতে পারছি।
জিয়ার সময় রুশ-ভারত বিরোধিতার একটা আওয়াজ উঠেছিল। জিয়াই তুলে দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের বামপন্থীদের একাংশ ওই আওয়াজে আকৃষ্ট হয়ে জিয়ার সঙ্গে সহযোগিতায় মেতে উঠেছিল। তাতে রুশ-ভারতের ক্ষতি-বৃদ্ধি যা-ই হোক না কেন, জিয়াউর রহমানের বেশ সুবিধা হয়েছিল। তাঁর শক্ত হাত আরও শক্ত হয়ে উঠেছিল। তারই ধারাবাহিকতা বর্তমানে দেখা যাচ্ছে।
জিয়ার পরে জেনারেল এরশাদ এলেন। মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে তাঁর ক্ষীণতম সম্পর্কও ছিল না। তিনি ছিলেন উল্টো দিকে। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন জনগণকে শান্তি এনে দেবেন। দিতে পারলেন না। প্রতিশ্রুতি ছিল দুর্নীতি দমনের, পারেননি তো বটেই, বরং তাঁর প্রশ্রয়ে দুর্নীতি বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষানীতি থেকে শুরু করে সাইকেলে চড়ে অফিসে যাওয়ার নীতি পর্যন্ত তাঁর সব নীতিই চরমভাবে ব্যর্থ হয়ে গেছে। ফলে আর কিছু না পেয়ে তিনি ধর্ম দিলেন। রাষ্ট্রীয় ধর্ম প্রবর্তন করলেন, সেই পাকিস্তানি শাসকদের কায়দায়।
২. সংস্কারের প্রয়োজনে অন্তর্বর্তী সরকার ১১টি কমিশন গঠন করেছে, কিন্তু তারা শিক্ষা সংস্কারের লক্ষ্যে যে কোনো কমিশন গঠন করেনি, এ জন্য অবশ্যই প্রশংসা দাবি করতে পারে। আমাদের মূল ধারার শিক্ষাব্যবস্থা এমনিতেই নড়বড়ে অবস্থায় রয়েছে, তার মধ্যে আবার সংস্কারের ধাক্কাধাক্কি সে বেচারাকে নতুন জ্বালাতনের মধ্যে ফেলুক, এটা মোটেই কাঙ্ক্ষিত নয়। অতীতে দেখা গেছে যে যখনই কোনো ‘বৈপ্লবিক’ সরকারের আগমন ঘটে, তখনই সঙ্গে সঙ্গেই, তারা শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি ঘটানোর জন্য ব্যস্তসমস্ত হয়ে পড়ে এবং মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থা একটা ধাক্কা খায়। পরবর্তী ‘বিপ্লবী’ সরকার আবার নতুন সংস্কারে হাত লাগিয়ে ব্যবস্থাটাকে আরেকটা ধাক্কা দেয়। মূল যে সংস্কার প্রয়োজন, সেটা হলো একটি অভিন্ন ব্যবস্থা চালু করা, রাষ্ট্রপরিচালকেরা সে ব্যাপারটাকে বিবেচনার মধ্যেই আনেন না। বৈষম্যনির্ভর পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটা আগের মতোই সহাস্যে টিকে থাকে।
বিগত আওয়ামী লীগ সরকার সংস্কারের নাম করে কয়েকটি অতিরিক্ত পাবলিক পরীক্ষার সংযোজন ঘটিয়ে মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সাধনে তৎপর হয়েছিল। তাতে দুর্বল ব্যবস্থাটা আরও একটা ঝুঁকির মুখে পড়েছিল। বিভিন্ন মহল থেকে প্রতিবাদ ওঠায় তারা অতিরিক্ত পরীক্ষা রদ করেছে। কিন্তু ২০১৭ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড যে তাদের নিজেদের প্রণীত বাংলা পাঠ্যপুস্তক থেকে আচমকা ১১টি কবিতা, ৫টি গল্প ও প্রবন্ধ বাদ দিয়ে দিল, সেই বৈপ্লবিক কাজটি কেন করা হলো তার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর তাদের অনেক নৃশংসতা, অপকর্ম ও দুর্নীতির তদন্ত করা হচ্ছে এবং হতে থাকবে, কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের ওপর নির্মম ও ক্ষতিকর হামলাটি কেন ঘটেছিল, সে বিষয়ে কোনো তদন্ত হয়নি। তদন্ত হওয়াটা কিন্তু আবশ্যক। জানা দরকার শিক্ষার ওপর অমন হস্তক্ষেপটি কারা এবং কীভাবে ঘটিয়েছিল। কাজটা বর্তমান সরকার শিক্ষাকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে সেটা জানার ব্যাপারেও সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।
ভালো কথা, বিগত সরকার দেশে যে ৫৬০টি মডেল মসজিদ নির্মাণ করেছিল, তার জন্য অর্থ ও অনুপ্রেরণা কোথা থেকে এসেছিল সে ব্যাপারে জনমনে বড় রকমের একটা জিজ্ঞাসা রয়ে গেছে। শোনা গিয়েছিল যে টাকাটা এসেছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে; এমনও ধারণা ছিল যে ওই তহবিল মধ্যপ্রাচ্যের মাধ্যমে এসেছে ঠিকই, কিন্তু প্রেরক হচ্ছে সিআইএ; এখন নাকি প্রকাশ পেয়েছে টাকা অন্য কেউ দেয়নি, দিয়েছে সরকার নিজেই। একসময়ে ঢাকা শহরকে বলা হতো মসজিদের শহর। সেই সুখ্যাতি এখন বিলক্ষণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে; শুধু ঢাকা শহর নয়, বাংলাদেশের কোথাও মসজিদের কোনো অভাব নেই। মসজিদ প্রতিষ্ঠার নামে সরকারি জায়গা দখল করা হয়েছে, এমন অভিযোগও বিস্তর শোনা গেছে। তার মধ্যে হঠাৎ করে আবার মডেল মসজিদ তৈরির আবশ্যকতা কেন দেখা দিল। বিগত সরকার দেশব্যাপী মডেল সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে এমন খবর কিন্তু আমাদের জানা নেই। তাহলে?
এসব হলো রাজনৈতিক ঘটনা। পাশাপাশি এ সত্যও তো রয়ে গেছে যে উপমহাদেশের যে সাংস্কৃতিক ভূমি ধর্মবাদিতা ও ধর্মভীরুতার বিকাশের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী, সে ভূমি বাংলাদেশেও বিদ্যমান। বাংলাদেশে তার উর্বরাশক্তি বরং বেশি। কেননা দেশটি অনেক বেশি দরিদ্র, অনেক বেশি পশ্চাৎপদ। দীর্ঘকাল এ ভূমি পরাধীন ছিল। আজও সে স্বাধীন নয়। আজও সে বিশ্ব পুঁজিবাদের অধীন। কাজেই মানুষ এখানে আত্মসমর্পণে অভ্যস্ত। সে আত্মসমর্পণ করেছে বিদেশি শাসকের কাছে, করেছে ভাগ্যের কাছে। তার আত্মবিশ্বাস নেই। তার জন্য খুবই প্রয়োজন পারলৌকিক আশ্রয়ের। যে জন্য ধর্মবাদিতা ও সাম্প্রদায়িকতা দুটোই টিকে আছে এবং সুযোগ পেয়ে এখন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, এ দেশে।

সাতচল্লিশের দেশভাগকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িকতা ক্রমাগত তীব্র হলো। রক্তপাত ঘটল। পরে যখন স্বাধীন হলো ভারতবর্ষ, তখন একটির জায়গায় দুটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটল। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার সমস্যার সমাধান হলো না; না পাকিস্তানে, না ভারতে। পাকিস্তানের সব ধর্মাবলম্বীকে বলা হলো রাজনৈতিকভাবে নিজ নিজ ধর্মমত ভুলে গিয়ে খাঁটি পাকিস্তানিতে পরিণত হতে। জিন্নাহ ধর্মীয় রাষ্ট্র চাননি, আধুনিক রাষ্ট্রই চেয়েছিলেন।
কিন্তু ধর্মের ভিত্তিটা তো রয়েই গেল রাষ্ট্রের মূলে। তা ছাড়া পাকিস্তান দ্রুত পরিণত হলো একটি আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে। সামরিক-বেসামরিক আমলারা রাষ্ট্র পরিচালনার কর্তৃত্ব দখল করে নিল। নিজেরা যদিও মোটেই ধার্মিক ছিল না, তথাপি তারা ধর্মকে ব্যবহার করতে চাইল, ঠিক সেই পুরোনো কারণেই। শ্রেণিবিভাজনকে অস্পষ্ট করে দেওয়ার জন্য। সেই সঙ্গে উগ্র ভারতবিদ্বেষ সৃষ্টি এবং সংখ্যাগুরু জনগণকে ধর্মচর্চার স্বাধীনতা (আসলে একমাত্র স্বাধীনতা) দিয়ে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর নিপীড়নমূলক চরিত্রকে আড়াল করে রাখার চেষ্টা করল।
তখনকার পূর্ব বাংলা এতে সন্তুষ্ট হয়নি। অভিজ্ঞতা সেখানকার মানুষকে দ্রুত বলে দিয়েছে যে ধর্মীয় বিভাজন যদিও মিথ্যা হয়, তবু তার চেয়ে অনেক বড় সত্য ভাষার বিভাজন। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের জায়গায় তাই নতুন চেতনা গড়ে উঠল, সেটি ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। ১৯৫২-এর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার প্রথম ব্যাপক রাষ্ট্রবিরোধী আন্দোলন। ভাষা পুরোপুরি ইহজাগতিক, ভাষা আন্দোলনও ছিল তাই। এখানে ধর্মের জন্য কোনো জায়গা ছিল না। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা। ওই আন্দোলন ক্রমাগত তীব্র হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তা স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। পাকিস্তানিরা ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের আওয়াজ থামায়নি। একাত্তরে যুদ্ধের সময় গণহত্যায় উদ্বুদ্ধকরণের প্রয়োজনে ব্যক্তিগতভাবে সর্বপ্রকার পাপাচারে লিপ্ত জেনারেলরা ইসলাম রক্ষার কথাই বলেছিল তাদের সৈন্যদের।
বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে। সেগুলো হলো জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র। কিন্তু এই মূলনীতিগুলো বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সেটি একটি মর্মান্তিক সত্য। রাষ্ট্রের হওয়ার কথা ছিল সম্পূর্ণরূপে ধর্মনিরপেক্ষ অর্থাৎ ইহজাগতিক। কিন্তু রাষ্ট্র তা হয়নি, কেন যে হয়নি তার কারণগুলো বেশ স্পষ্ট। প্রথম সত্য হলো এই যে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থটাই শাসকশ্রেণির কাছে পরিষ্কার ছিল না। এমনকি তাঁদের কাছেও নয়, যাঁরা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন এবং ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ধ্বজাধারীদের বিরুদ্ধে লড়েছেন। ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে তাঁরা ইহলৌকিকতা বোঝাননি, বোঝাননি এই প্রয়োজনটা যে ধর্ম ও রাষ্ট্রকে আলাদা করে ফেলতে হবে পরস্পর থেকে। বরং উল্টো বুঝিয়েছেন, সব ধর্মের সমান অধিকার এবং পারলে আরও বেশি ধর্মচর্চা করা। দ্বিতীয় সত্য এই যে শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর রাষ্ট্রক্ষমতায় যারা এসেছে, তারা অনেকেই ছিল পাকিস্তানপন্থী। পাকিস্তানের প্রতি দুর্বলতা ছাড়াও তাদের ভেতর আরেকটি প্রবণতা ছিল। সেটি হলো বাংলাদেশকে একটি আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করা। তাদের প্রভু ও সমমনারা একদা যেমন করেছিল পাকিস্তানকে। তবে প্রয়োজনটা বাইরে থেকে আসেনি, উৎপন্ন হয়েছে ভেতরের প্রয়োজন থেকেই। সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রই দেশ শাসন করবে, বিশেষ করে শেখ মুজিবের পর থেকে, তারা রাষ্ট্রকে তাদের মনের মতো করে তৈরি করে নেবে এটাই স্বাভাবিক। সেই ঘটনাই পুনরায় ঘটছে বাংলাদেশে। আর লেজ টানলে যেমন মাথা আসে, তেমনি আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহারের আবশ্যকতাটাও ফিরে এসেছে। যার ফলে দেখা গেল দেশের সংবিধান থেকে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান স্বয়ং ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র কেটে বাদ দিয়ে দিলেন। গণতন্ত্র তো ছিলই না। সামরিক আমলাদের শাসন চলছিল; বাঙালি জাতীয়তাবাদও গেল। সে জায়গায় আনা হলো বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ। এরশাদ ব্যাপারটাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন। তিনি সংবিধানকে আরও একবার রক্তাক্ত করে দিয়ে রাষ্ট্রধর্ম প্রবর্তন করলেন। সময় পেলে হয়তো রাষ্ট্রের নামই বদলে দেওয়ার পদক্ষেপ নিতেন। সময় পাননি। যার পাঁয়তারা এখন আমরা দেখতে পারছি।
জিয়ার সময় রুশ-ভারত বিরোধিতার একটা আওয়াজ উঠেছিল। জিয়াই তুলে দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের বামপন্থীদের একাংশ ওই আওয়াজে আকৃষ্ট হয়ে জিয়ার সঙ্গে সহযোগিতায় মেতে উঠেছিল। তাতে রুশ-ভারতের ক্ষতি-বৃদ্ধি যা-ই হোক না কেন, জিয়াউর রহমানের বেশ সুবিধা হয়েছিল। তাঁর শক্ত হাত আরও শক্ত হয়ে উঠেছিল। তারই ধারাবাহিকতা বর্তমানে দেখা যাচ্ছে।
জিয়ার পরে জেনারেল এরশাদ এলেন। মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে তাঁর ক্ষীণতম সম্পর্কও ছিল না। তিনি ছিলেন উল্টো দিকে। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন জনগণকে শান্তি এনে দেবেন। দিতে পারলেন না। প্রতিশ্রুতি ছিল দুর্নীতি দমনের, পারেননি তো বটেই, বরং তাঁর প্রশ্রয়ে দুর্নীতি বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষানীতি থেকে শুরু করে সাইকেলে চড়ে অফিসে যাওয়ার নীতি পর্যন্ত তাঁর সব নীতিই চরমভাবে ব্যর্থ হয়ে গেছে। ফলে আর কিছু না পেয়ে তিনি ধর্ম দিলেন। রাষ্ট্রীয় ধর্ম প্রবর্তন করলেন, সেই পাকিস্তানি শাসকদের কায়দায়।
২. সংস্কারের প্রয়োজনে অন্তর্বর্তী সরকার ১১টি কমিশন গঠন করেছে, কিন্তু তারা শিক্ষা সংস্কারের লক্ষ্যে যে কোনো কমিশন গঠন করেনি, এ জন্য অবশ্যই প্রশংসা দাবি করতে পারে। আমাদের মূল ধারার শিক্ষাব্যবস্থা এমনিতেই নড়বড়ে অবস্থায় রয়েছে, তার মধ্যে আবার সংস্কারের ধাক্কাধাক্কি সে বেচারাকে নতুন জ্বালাতনের মধ্যে ফেলুক, এটা মোটেই কাঙ্ক্ষিত নয়। অতীতে দেখা গেছে যে যখনই কোনো ‘বৈপ্লবিক’ সরকারের আগমন ঘটে, তখনই সঙ্গে সঙ্গেই, তারা শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি ঘটানোর জন্য ব্যস্তসমস্ত হয়ে পড়ে এবং মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থা একটা ধাক্কা খায়। পরবর্তী ‘বিপ্লবী’ সরকার আবার নতুন সংস্কারে হাত লাগিয়ে ব্যবস্থাটাকে আরেকটা ধাক্কা দেয়। মূল যে সংস্কার প্রয়োজন, সেটা হলো একটি অভিন্ন ব্যবস্থা চালু করা, রাষ্ট্রপরিচালকেরা সে ব্যাপারটাকে বিবেচনার মধ্যেই আনেন না। বৈষম্যনির্ভর পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটা আগের মতোই সহাস্যে টিকে থাকে।
বিগত আওয়ামী লীগ সরকার সংস্কারের নাম করে কয়েকটি অতিরিক্ত পাবলিক পরীক্ষার সংযোজন ঘটিয়ে মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সাধনে তৎপর হয়েছিল। তাতে দুর্বল ব্যবস্থাটা আরও একটা ঝুঁকির মুখে পড়েছিল। বিভিন্ন মহল থেকে প্রতিবাদ ওঠায় তারা অতিরিক্ত পরীক্ষা রদ করেছে। কিন্তু ২০১৭ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড যে তাদের নিজেদের প্রণীত বাংলা পাঠ্যপুস্তক থেকে আচমকা ১১টি কবিতা, ৫টি গল্প ও প্রবন্ধ বাদ দিয়ে দিল, সেই বৈপ্লবিক কাজটি কেন করা হলো তার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর তাদের অনেক নৃশংসতা, অপকর্ম ও দুর্নীতির তদন্ত করা হচ্ছে এবং হতে থাকবে, কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের ওপর নির্মম ও ক্ষতিকর হামলাটি কেন ঘটেছিল, সে বিষয়ে কোনো তদন্ত হয়নি। তদন্ত হওয়াটা কিন্তু আবশ্যক। জানা দরকার শিক্ষার ওপর অমন হস্তক্ষেপটি কারা এবং কীভাবে ঘটিয়েছিল। কাজটা বর্তমান সরকার শিক্ষাকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে সেটা জানার ব্যাপারেও সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।
ভালো কথা, বিগত সরকার দেশে যে ৫৬০টি মডেল মসজিদ নির্মাণ করেছিল, তার জন্য অর্থ ও অনুপ্রেরণা কোথা থেকে এসেছিল সে ব্যাপারে জনমনে বড় রকমের একটা জিজ্ঞাসা রয়ে গেছে। শোনা গিয়েছিল যে টাকাটা এসেছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে; এমনও ধারণা ছিল যে ওই তহবিল মধ্যপ্রাচ্যের মাধ্যমে এসেছে ঠিকই, কিন্তু প্রেরক হচ্ছে সিআইএ; এখন নাকি প্রকাশ পেয়েছে টাকা অন্য কেউ দেয়নি, দিয়েছে সরকার নিজেই। একসময়ে ঢাকা শহরকে বলা হতো মসজিদের শহর। সেই সুখ্যাতি এখন বিলক্ষণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে; শুধু ঢাকা শহর নয়, বাংলাদেশের কোথাও মসজিদের কোনো অভাব নেই। মসজিদ প্রতিষ্ঠার নামে সরকারি জায়গা দখল করা হয়েছে, এমন অভিযোগও বিস্তর শোনা গেছে। তার মধ্যে হঠাৎ করে আবার মডেল মসজিদ তৈরির আবশ্যকতা কেন দেখা দিল। বিগত সরকার দেশব্যাপী মডেল সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে এমন খবর কিন্তু আমাদের জানা নেই। তাহলে?
এসব হলো রাজনৈতিক ঘটনা। পাশাপাশি এ সত্যও তো রয়ে গেছে যে উপমহাদেশের যে সাংস্কৃতিক ভূমি ধর্মবাদিতা ও ধর্মভীরুতার বিকাশের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী, সে ভূমি বাংলাদেশেও বিদ্যমান। বাংলাদেশে তার উর্বরাশক্তি বরং বেশি। কেননা দেশটি অনেক বেশি দরিদ্র, অনেক বেশি পশ্চাৎপদ। দীর্ঘকাল এ ভূমি পরাধীন ছিল। আজও সে স্বাধীন নয়। আজও সে বিশ্ব পুঁজিবাদের অধীন। কাজেই মানুষ এখানে আত্মসমর্পণে অভ্যস্ত। সে আত্মসমর্পণ করেছে বিদেশি শাসকের কাছে, করেছে ভাগ্যের কাছে। তার আত্মবিশ্বাস নেই। তার জন্য খুবই প্রয়োজন পারলৌকিক আশ্রয়ের। যে জন্য ধর্মবাদিতা ও সাম্প্রদায়িকতা দুটোই টিকে আছে এবং সুযোগ পেয়ে এখন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, এ দেশে।

মিরপুরের শিয়ালবাড়ী এলাকায় একটি রাসায়নিক গুদামে আগুন লাগার পর যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল, সে কথা সবাই এখন জানেন। যাঁরা স্বজন হারিয়েছেন, তাঁরা জানেন এটা তাঁদের পরিবারের জন্য কত বড় ক্ষতি। নিহতদের পরিবার ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে কি না, তাদের জীবনে স্থিতি ফিরিয়ে আনতে কী করা দরকার...
১০ ঘণ্টা আগে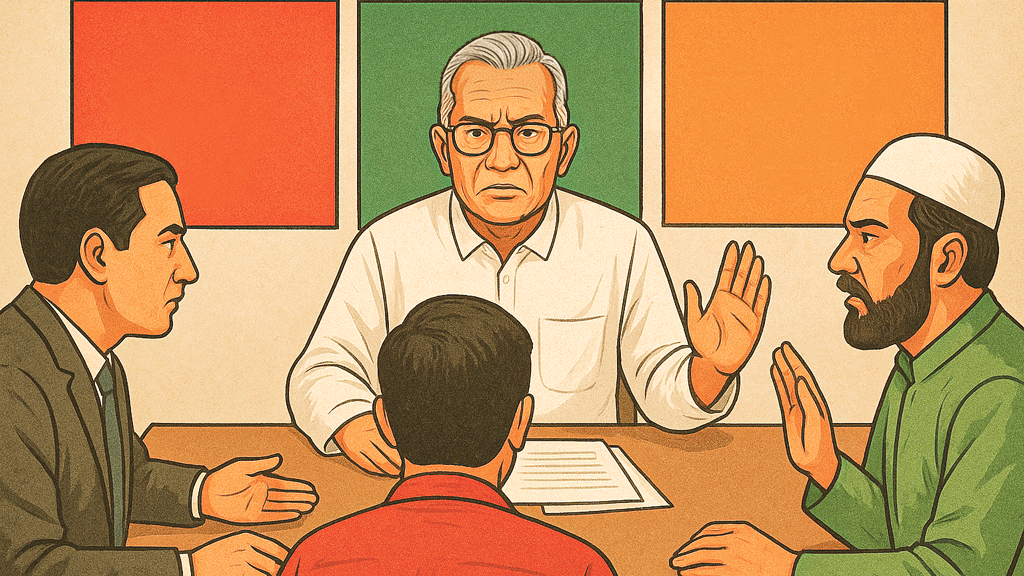
না, সব উপদেষ্টা প্রশ্নবিদ্ধ নন। তবে সংখ্যাটা যে নেহাত কম হবে না, তা অনুমান করা যায় যখন প্রধান তিনটি প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলই আলাদা আলাদাভাবে উপদেষ্টাদের দলঘনিষ্ঠতার অভিযোগ তোলে। অবশ্য এবারই প্রথম নয়, এর আগেও একই অভিযোগ তোলা হয়েছে, যখন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম কোনো কোনো উপদেষ্টার সেফ...
১১ ঘণ্টা আগে
সমাজ এগিয়ে চলেছে দ্রুতগতিতে, পৃথিবী প্রবেশ করেছে এক নতুন যুগে। এই গতিময় সভ্যতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে আমরা হয়তো অনেক কিছু পাচ্ছি, কিন্তু হারিয়ে ফেলছি আরও বেশি কিছু। আজ আমরা এক অদ্ভুত স্বার্থপর সময়ে বাস করছি, যেখানে প্রতিটি সম্পর্কের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতি।
১১ ঘণ্টা আগে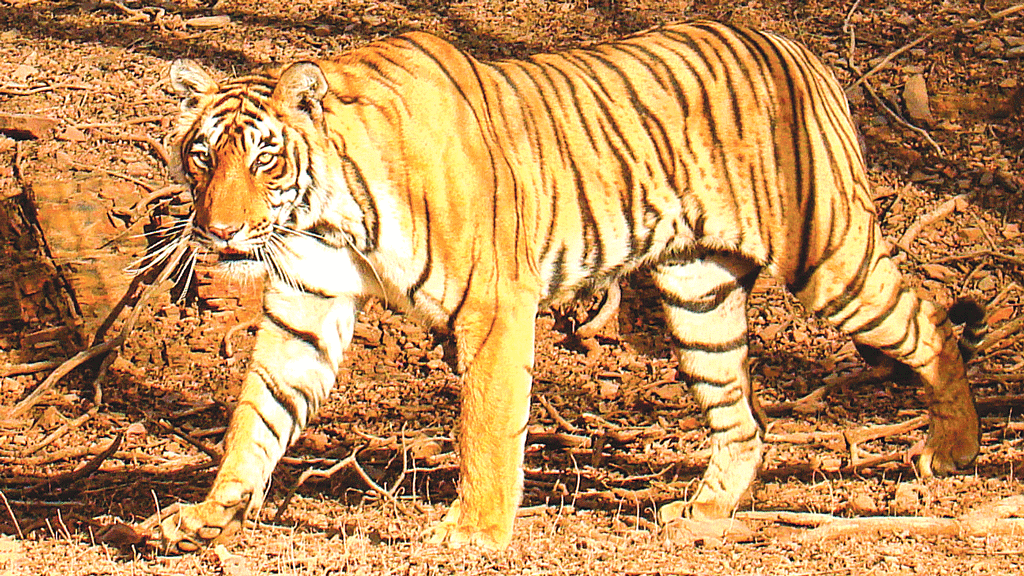
প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি সুন্দরবন এ দেশের দক্ষিণাঞ্চলকে মাতৃস্নেহে আগলে রেখেছে। ঝড়-ঝঞ্ঝা, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিক্ষয় রোধসহ সব প্রাকৃতিক দুর্যোগে সুন্দরবন আমাদের রক্ষা করে আসছে। এই সুন্দরবনের এক অনন্য প্রজাতির প্রাণী হলো রয়েল বেঙ্গল টাইগার।
১১ ঘণ্টা আগেসম্পাদকীয়

মিরপুরের শিয়ালবাড়ী এলাকায় একটি রাসায়নিক গুদামে আগুন লাগার পর যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল, সে কথা সবাই এখন জানেন। যাঁরা স্বজন হারিয়েছেন, তাঁরা জানেন এটা তাঁদের পরিবারের জন্য কত বড় ক্ষতি। নিহতদের পরিবার ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে কি না, তাদের জীবনে স্থিতি ফিরিয়ে আনতে কী করা দরকার—তা নিয়ে সংশ্লিষ্টরা নিশ্চয়ই ভাববেন। এ রকম একটা অবস্থায় দুর্ঘটনা-পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে খুব কম মানুষই মাথা ঘামায়। দুর্ঘটনা-পরবর্তী সময়টিতে স্থানীয় পরিবেশ ও পরিস্থিতি যে মোটেও অনুকূল থাকে না, সেটা বোঝা দরকার।
সম্প্রতি আমাদের প্রতিবেদক শিয়ালবাড়ীর ক্ষতিগ্রস্ত রাসায়নিক গুদামে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখেছেন, এতগুলো দিন পার হওয়ার পরও বিষাক্ত রাসায়নিকের কারণে এখনো অসুস্থ হচ্ছে মানুষ। রাসায়নিকের ড্রাম থেকে নির্গত বিষাক্ত গ্যাস ও ধোঁয়া মানুষকে অসুস্থ করে দিচ্ছে। অসুস্থদের মধ্যে শিশু ও বৃদ্ধরা রয়েছেন ঝুঁকির মধ্যে। প্রায়ই দেখা যায়, একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর দু-এক দিন সংবাদপত্রে রিপোর্ট হয়, তারপর একসময় সেটা ভুলে যায় মানুষ। কিন্তু যে মানুষেরা ভুক্তভোগী, তাদের প্রতিটি দিনই যে কাটছে ভয়ংকর রাসায়নিকের সঙ্গে লড়াই করে, সে খবর কয়জন রাখে?
চিকিৎসকেরা বলেছেন, অগ্নিকাণ্ডের কয়েক দিন পরও বিষাক্ত গ্যাস ও ধোঁয়ার ঘনত্ব বেশি থাকে। পরে ধীরে ধীরে তা কমে যায়। মাটিতে পড়ে থাকা রাসায়নিক দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ ভুক্তভোগীর শরীরে ঢোকে। ঘন ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ার কারণে বাতাসে ভাসমান ক্ষুদ্র ধূলিকণা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে যায়। এই কারণে ভবিষ্যতেও তা বিপদ সৃষ্টি করতে পারে।
বিষাক্ত কণিকা বা গ্যাস মানবদেহে ঢোকে শ্বাসের মাধ্যমে, ত্বকের মাধ্যমে এবং খাদ্যের মাধ্যমে। এই গ্যাস অ্যাজমা, কাশি, গলাজ্বলা বা শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। চোখ আর ত্বকও তাতে আক্রান্ত হতে পারে। তৈরি হতে পারে মাথাব্যথা, বমি ও ক্লান্তির মতো ঘটনা। ভারী ধাতু দীর্ঘ মেয়াদে স্নায়ুতন্ত্র দুর্বল করে দেয়। তাতে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে।
শিয়ালবাড়ীর দুর্ঘটনাস্থলের অন্তত এক হাজার গজ পর্যন্ত এলাকায় বাতাসে এখনো পোড়া জিনিস ও গ্যাসের মতো কটু গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। তাতে মনে হয়, এই এলাকার মানুষের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি এখনো রয়েছে সংকটের মুখে।
আমরা সবাই জানি, স্বাস্থ্য আমাদের মৌলিক অধিকারের একটি। কিন্তু দেশের মানুষ এ কথাও জানে, সেই মৌলিক অধিকার সব সময় সমুন্নত রাখা হয় না। রাসায়নিক গুদামে অগ্নিকাণ্ড ঘটলে কীভাবে তার মোকাবিলা করতে হবে, তার পূর্বপ্রস্তুতি কয়টি গুদামে আছে? এসব জায়গায় কি নিয়মিত ইন্সপেকশন হয়? শুধু গুদাম কেন, কারখানাগুলোয় কি সঠিক নিরাপত্তাব্যবস্থা রয়েছে? শ্রমিকেরা কি নিরাপদে তাঁদের কাজ করে যেতে পারেন?
এসব দুর্ঘটনায় মূলত সমাজের নিচুতলার মানুষেরা বিপদে পড়েন। তাঁদের পাশে যদি দাঁড়ানো না হয়, তাহলে বুঝতে হবে, শিল্প-ব্যবস্থাপনায় যে ঘাটতি আছে, তা নিরসনের কোনো চিন্তা কারও নেই।

মিরপুরের শিয়ালবাড়ী এলাকায় একটি রাসায়নিক গুদামে আগুন লাগার পর যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল, সে কথা সবাই এখন জানেন। যাঁরা স্বজন হারিয়েছেন, তাঁরা জানেন এটা তাঁদের পরিবারের জন্য কত বড় ক্ষতি। নিহতদের পরিবার ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে কি না, তাদের জীবনে স্থিতি ফিরিয়ে আনতে কী করা দরকার—তা নিয়ে সংশ্লিষ্টরা নিশ্চয়ই ভাববেন। এ রকম একটা অবস্থায় দুর্ঘটনা-পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে খুব কম মানুষই মাথা ঘামায়। দুর্ঘটনা-পরবর্তী সময়টিতে স্থানীয় পরিবেশ ও পরিস্থিতি যে মোটেও অনুকূল থাকে না, সেটা বোঝা দরকার।
সম্প্রতি আমাদের প্রতিবেদক শিয়ালবাড়ীর ক্ষতিগ্রস্ত রাসায়নিক গুদামে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখেছেন, এতগুলো দিন পার হওয়ার পরও বিষাক্ত রাসায়নিকের কারণে এখনো অসুস্থ হচ্ছে মানুষ। রাসায়নিকের ড্রাম থেকে নির্গত বিষাক্ত গ্যাস ও ধোঁয়া মানুষকে অসুস্থ করে দিচ্ছে। অসুস্থদের মধ্যে শিশু ও বৃদ্ধরা রয়েছেন ঝুঁকির মধ্যে। প্রায়ই দেখা যায়, একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর দু-এক দিন সংবাদপত্রে রিপোর্ট হয়, তারপর একসময় সেটা ভুলে যায় মানুষ। কিন্তু যে মানুষেরা ভুক্তভোগী, তাদের প্রতিটি দিনই যে কাটছে ভয়ংকর রাসায়নিকের সঙ্গে লড়াই করে, সে খবর কয়জন রাখে?
চিকিৎসকেরা বলেছেন, অগ্নিকাণ্ডের কয়েক দিন পরও বিষাক্ত গ্যাস ও ধোঁয়ার ঘনত্ব বেশি থাকে। পরে ধীরে ধীরে তা কমে যায়। মাটিতে পড়ে থাকা রাসায়নিক দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ ভুক্তভোগীর শরীরে ঢোকে। ঘন ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ার কারণে বাতাসে ভাসমান ক্ষুদ্র ধূলিকণা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে যায়। এই কারণে ভবিষ্যতেও তা বিপদ সৃষ্টি করতে পারে।
বিষাক্ত কণিকা বা গ্যাস মানবদেহে ঢোকে শ্বাসের মাধ্যমে, ত্বকের মাধ্যমে এবং খাদ্যের মাধ্যমে। এই গ্যাস অ্যাজমা, কাশি, গলাজ্বলা বা শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। চোখ আর ত্বকও তাতে আক্রান্ত হতে পারে। তৈরি হতে পারে মাথাব্যথা, বমি ও ক্লান্তির মতো ঘটনা। ভারী ধাতু দীর্ঘ মেয়াদে স্নায়ুতন্ত্র দুর্বল করে দেয়। তাতে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে।
শিয়ালবাড়ীর দুর্ঘটনাস্থলের অন্তত এক হাজার গজ পর্যন্ত এলাকায় বাতাসে এখনো পোড়া জিনিস ও গ্যাসের মতো কটু গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। তাতে মনে হয়, এই এলাকার মানুষের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি এখনো রয়েছে সংকটের মুখে।
আমরা সবাই জানি, স্বাস্থ্য আমাদের মৌলিক অধিকারের একটি। কিন্তু দেশের মানুষ এ কথাও জানে, সেই মৌলিক অধিকার সব সময় সমুন্নত রাখা হয় না। রাসায়নিক গুদামে অগ্নিকাণ্ড ঘটলে কীভাবে তার মোকাবিলা করতে হবে, তার পূর্বপ্রস্তুতি কয়টি গুদামে আছে? এসব জায়গায় কি নিয়মিত ইন্সপেকশন হয়? শুধু গুদাম কেন, কারখানাগুলোয় কি সঠিক নিরাপত্তাব্যবস্থা রয়েছে? শ্রমিকেরা কি নিরাপদে তাঁদের কাজ করে যেতে পারেন?
এসব দুর্ঘটনায় মূলত সমাজের নিচুতলার মানুষেরা বিপদে পড়েন। তাঁদের পাশে যদি দাঁড়ানো না হয়, তাহলে বুঝতে হবে, শিল্প-ব্যবস্থাপনায় যে ঘাটতি আছে, তা নিরসনের কোনো চিন্তা কারও নেই।

সাতচল্লিশের দেশভাগকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িকতা ক্রমাগত তীব্র হলো। রক্তপাত ঘটল। পরে যখন স্বাধীন হলো ভারতবর্ষ, তখন একটির জায়গায় দুটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটল। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার সমস্যার সমাধান হলো না; না পাকিস্তানে, না ভারতে। পাকিস্তানের সব ধর্মাবলম্বীকে বলা হলো রাজনৈতিকভাবে নিজ নিজ ধর্মমত ভুলে
১৬ জুলাই ২০২৫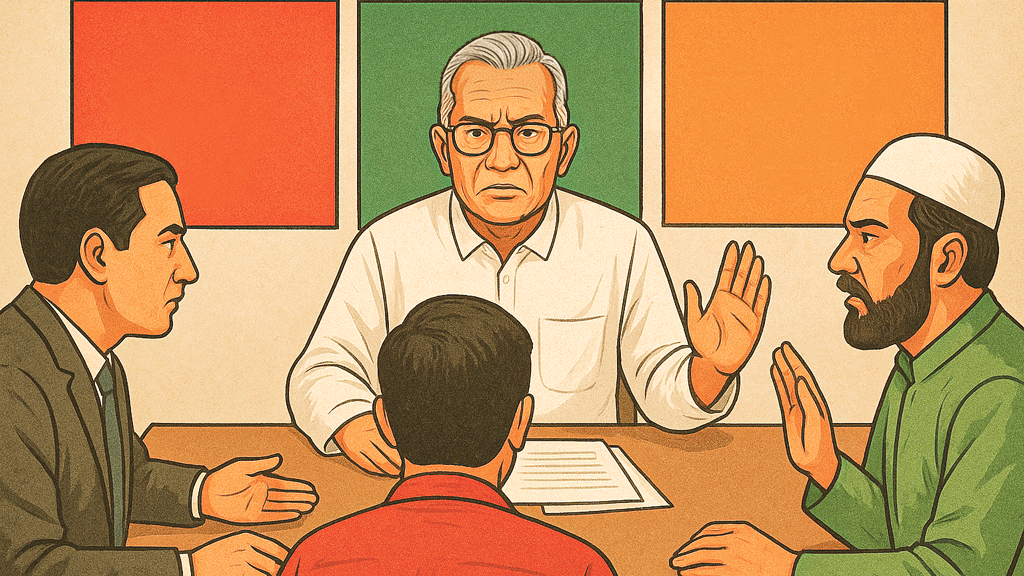
না, সব উপদেষ্টা প্রশ্নবিদ্ধ নন। তবে সংখ্যাটা যে নেহাত কম হবে না, তা অনুমান করা যায় যখন প্রধান তিনটি প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলই আলাদা আলাদাভাবে উপদেষ্টাদের দলঘনিষ্ঠতার অভিযোগ তোলে। অবশ্য এবারই প্রথম নয়, এর আগেও একই অভিযোগ তোলা হয়েছে, যখন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম কোনো কোনো উপদেষ্টার সেফ...
১১ ঘণ্টা আগে
সমাজ এগিয়ে চলেছে দ্রুতগতিতে, পৃথিবী প্রবেশ করেছে এক নতুন যুগে। এই গতিময় সভ্যতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে আমরা হয়তো অনেক কিছু পাচ্ছি, কিন্তু হারিয়ে ফেলছি আরও বেশি কিছু। আজ আমরা এক অদ্ভুত স্বার্থপর সময়ে বাস করছি, যেখানে প্রতিটি সম্পর্কের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতি।
১১ ঘণ্টা আগে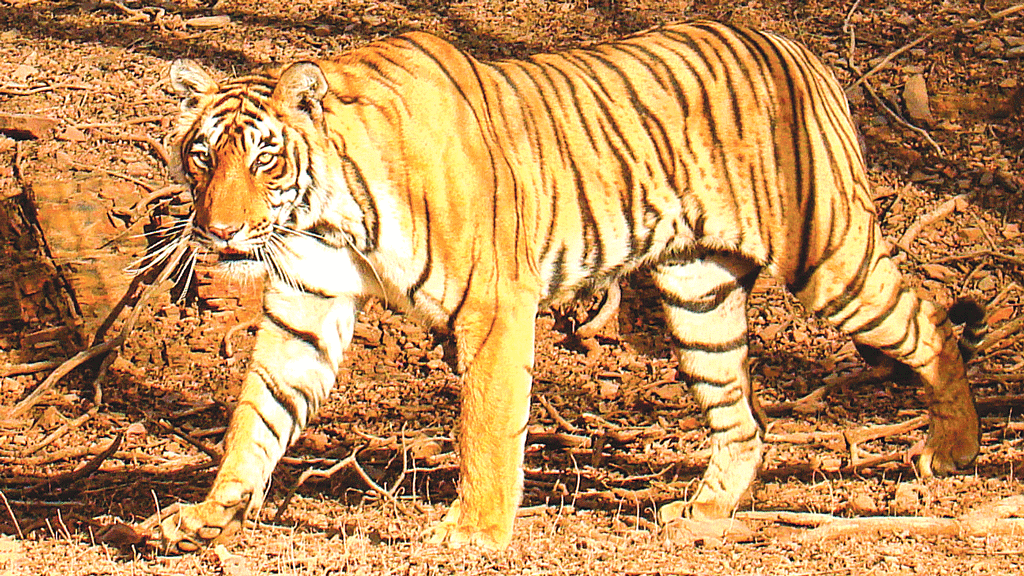
প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি সুন্দরবন এ দেশের দক্ষিণাঞ্চলকে মাতৃস্নেহে আগলে রেখেছে। ঝড়-ঝঞ্ঝা, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিক্ষয় রোধসহ সব প্রাকৃতিক দুর্যোগে সুন্দরবন আমাদের রক্ষা করে আসছে। এই সুন্দরবনের এক অনন্য প্রজাতির প্রাণী হলো রয়েল বেঙ্গল টাইগার।
১১ ঘণ্টা আগেঅরুণ কর্মকার
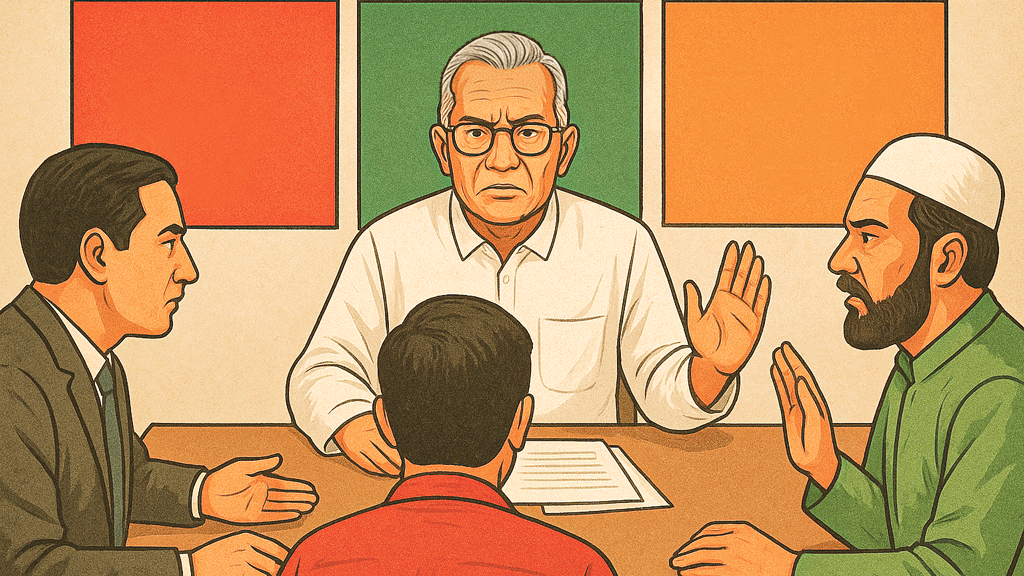
না, সব উপদেষ্টা প্রশ্নবিদ্ধ নন। তবে সংখ্যাটা যে নেহাত কম হবে না, তা অনুমান করা যায় যখন প্রধান তিনটি প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলই আলাদা আলাদাভাবে উপদেষ্টাদের দলঘনিষ্ঠতার অভিযোগ তোলে। অবশ্য এবারই প্রথম নয়, এর আগেও একই অভিযোগ তোলা হয়েছে, যখন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম কোনো কোনো উপদেষ্টার সেফ এক্সিটের প্রসঙ্গটি তুলেছিলেন। আর এবার তো জানা গেল প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে গত বুধবার অনুষ্ঠিত বৈঠকে জামায়াতে ইসলামী তাদের দৃষ্টিতে দলঘনিষ্ঠ উপদেষ্টাদের নামধামের তালিকাই নিয়ে গিয়েছিল। তবে ওই দিন সেই তালিকা তারা প্রধান উপদেষ্টাকে দেয়নি। প্রয়োজন হলে পরে দেবে। এবার শুধু বিষয়টি সম্পর্কে প্রধান উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং কয়েকজন উপদেষ্টা বিএনপির পক্ষে কাজ করছেন বলে অভিযোগ করেছে।
শুধু উপদেষ্টা নয়, জামায়াত সুনির্দিষ্ট নাম-ঠিকানা নিয়ে গিয়েছিল প্রায় ৪০ জন আমলারও, যাঁরা তাদের দৃষ্টিতে কোনো না কোনো দলের হয়ে, বিশেষত বিএনপির হয়ে কাজ করছেন। আর বৈঠক-পরবর্তী সংবাদ ব্রিফিংয়ে জামায়াতের নেতারা উল্লেখ করেছেন যে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রশাসন ও পুলিশের ৭০ থেকে ৮০ ভাগ লোকই বিএনপির। বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টাকে জামায়াত বলেছে, নির্বাচনের আগে সরকারকে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে। এ জন্য সচিবালয়, পুলিশ প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিবালয়ে রদবদল আনতে হবে। বিএনপির বিরুদ্ধে জামায়াতের আরও অভিযোগ, বিএনপি রাজনৈতিক চাপে পড়ে গণভোটে রাজি হলেও এখন জটিলতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে।
ওই দিনই জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) একটি প্রতিনিধিদলও পৃথকভাবে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এরপর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, তাঁরা প্রধান উপদেষ্টাকে বলেছেন, নির্বাচনের আগে বড় রাজনৈতিক দলগুলো প্রশাসন ও পুলিশে নিজেদের মতো ভাগ-বাঁটোয়ারা শুরু করেছে। ডিসি-এসপিদের তালিকা করে সরকারকে দিচ্ছে এবং সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের মধ্য থেকেও এ ব্যাপারে তারা সহযোগিতা পাচ্ছে।
এনসিপির আরও বড় অভিযোগ নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে। প্রধান উপদেষ্টাকে তারা বলেছে, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ আচরণ করছে না। কোনো কোনো দলের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ করছে। শাপলা প্রতীক পাওয়া প্রসঙ্গে নাহিদ ইসলামের স্পষ্ট বক্তব্য হলো, যে নির্বাচন কমিশন নিবন্ধন এবং প্রতীকের বিষয়ে এনসিপির সঙ্গে ন্যায়বিচার করে না, তার অধীনে নির্বাচনে গিয়ে ন্যায়বিচার এবং নিরপেক্ষতা বা সঠিক ফলাফল পাওয়ার ব্যাপারে ভরসা করা যায় না। তাই নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। তাঁদের যুক্তি হলো, নির্বাচন কমিশনের কারণে যদি সুষ্ঠু নির্বাচন না হয়, সেই দায়ও সরকারের ওপরই পড়বে।
উপদেষ্টাদের নিয়ে প্রশ্ন আছে বিএনপিরও। জামায়াত ও এনসিপির এক দিন আগে, গত মঙ্গলবার প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করেছে বিএনপি। সেই বৈঠকে তারাও কয়েকজন উপদেষ্টাকে নিয়ে আপত্তি তুলেছে। কারও নাম উল্লেখ না করেই বিতর্কিত উপদেষ্টাদের বাদ দেওয়ার জন্য প্রধান উপদেষ্টাকে আহ্বান জানিয়েছে দলটি। এর আগেও বিএনপির পক্ষ থেকে এমন আহ্বান জানানো হয়েছিল। তখন দুই ছাত্র উপদেষ্টাকে পদত্যাগ করতে বলা হয়েছিল বলেও খবর বেরিয়েছে। তবে তাঁরা তখনই তাতে রাজি হননি। উপদেষ্টাদের ছাড়াও প্রশাসন নিয়েও অন্য দুই দলের মতোই উদ্বেগ আছে বিএনপিরও। মঙ্গলবারের বৈঠকে তারা এই বলে প্রধান উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যে প্রশাসন, পুলিশ এবং বিচার বিভাগের প্রায় ৫০ ভাগ ফ্যাসিস্টের দোসর।
তিনটি দলের সঙ্গে বৈঠকেই প্রধান উপদেষ্টা সরকারের নিরপেক্ষ অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘আমাদের নিরপেক্ষতা নিয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে আমরা ইতিমধ্যে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি; সামনে আরও অনেক উদ্যোগ আপনারা দেখতে পাবেন।’
তা প্রধান উপদেষ্টা যতই নিশ্চয়তা দিন না কেন, যেখানে সব দলের কাছেই উপদেষ্টাদের (সবার নয়) এবং প্রশাসনের পক্ষপাতদুষ্টতা স্পষ্ট, যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ আছে উল্লেখ করে যখন প্রকাশ্যে বারবার অভিযোগ করা হচ্ছে, সেখানে রাজনৈতিক দলগুলো কীভাবে নিশ্চিন্তে নিশ্চিত থাকতে পারে! তা ছাড়া, মাঝেমধ্যেই তো দলগুলোর পরস্পরের প্রতি বৈরী বক্তব্য রাজনৈতিক অঙ্গনে উত্তাপ ছড়াচ্ছে। যেমন কিছুদিন আগে এনসিপির আহ্বায়ক তাঁর ফেসবুক পোস্টে বললেন, সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন (পিআর) নিয়ে জামায়াতের আন্দোলন রাজনৈতিক প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। কিংবা জামায়াত জুলাই অভ্যুত্থানের আগে-পরে কখনোই সংস্কার আলোচনায় যুক্ত হয়নি। তারা কোনো কার্যকর প্রস্তাব দেয়নি। কোনো সাংবিধানিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেনি এবং গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতি কোনো অঙ্গীকারও দেখায়নি।
এর পরিপ্রেক্ষিতে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বললেন আরও একটু শক্ত কথা—‘জন্মের পরই বাপের সাথে পাল্লা দিতে যেও না।’ সরকার ভাবতে পারে যে এগুলো তো রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেকার বাহাস। এটা নিয়ে তাদের অতটা না ভাবলেও চলবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এই বাহাসগুলো তো রাজনৈতিক বাস্তবতা। এগুলো তো রাজনৈতিক অঙ্গনকে অস্থিতিশীল করতে পারে, যা শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের পরিবেশেও প্রভাব ফেলতে পারে।
তারপর উল্লেখ করা যায় মঙ্গলবারের বৈঠকে বিএনপি যে অন্তর্বর্তী সরকারকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে, সে সম্পর্কে এনসিপির প্রতিক্রিয়ার কথা। এনসিপি বলল হঠাৎ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার পরামর্শটি দুরভিসন্ধিমূলক। কারণ, অন্তর্বর্তী সরকার গণ-অভ্যুত্থানের সরকার। সংস্কার, বিচার ও নির্বাচন—এই তিনটি তাদের ম্যান্ডেট। অথচ বিএনপির বক্তব্যটি ছিল—নিরপেক্ষতার নিরিখে এখন অন্তর্বর্তী সরকারকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা নিতে হবে।
এইসব রাজনৈতিক টানাপোড়েন ছাড়াও কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখনো অমীমাংসিত রয়েছে। যেমন জামায়াতের কাছে অমীমাংসিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি, সনদ বাস্তবায়নের পদ্ধতি, ওই সনদের ভিত্তিতে নির্বাচন, পিআর পদ্ধতির নির্বাচন এবং জাতীয় নির্বাচনের আগে আগামী নভেম্বরে গণভোট। এই দাবিতে জামায়াতসহ আটটি দল আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এনসিপির কাছে অমীমাংসিত বিষয় জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি, সনদ বাস্তবায়নের পদ্ধতি, নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠন এবং তাদের দাবিকৃত নির্বাচনী প্রতীক শাপলা বরাদ্দ দেওয়া। বিএনপির কাছে সবচেয়ে বড় ইস্যু সময়মতো সুষ্ঠু নির্বাচন। এ ছাড়া এই তিনটি দলের কাছেই (হয়তো আরও অনেক দলের কাছে) সাধারণ ইস্যু হচ্ছে সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য দলঘনিষ্ঠ উপদেষ্টাদের সরিয়ে দেওয়া। এর মধ্যে বেশ কিছু বিষয় প্রতিটি দল চায় না। এসব বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের নিরপেক্ষ ভূমিকা নিশ্চিত করা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে সেই ভূমিকা নিরপেক্ষ হিসেবেই প্রতীয়মান হওয়া এক বড় চ্যালেঞ্জই বটে।
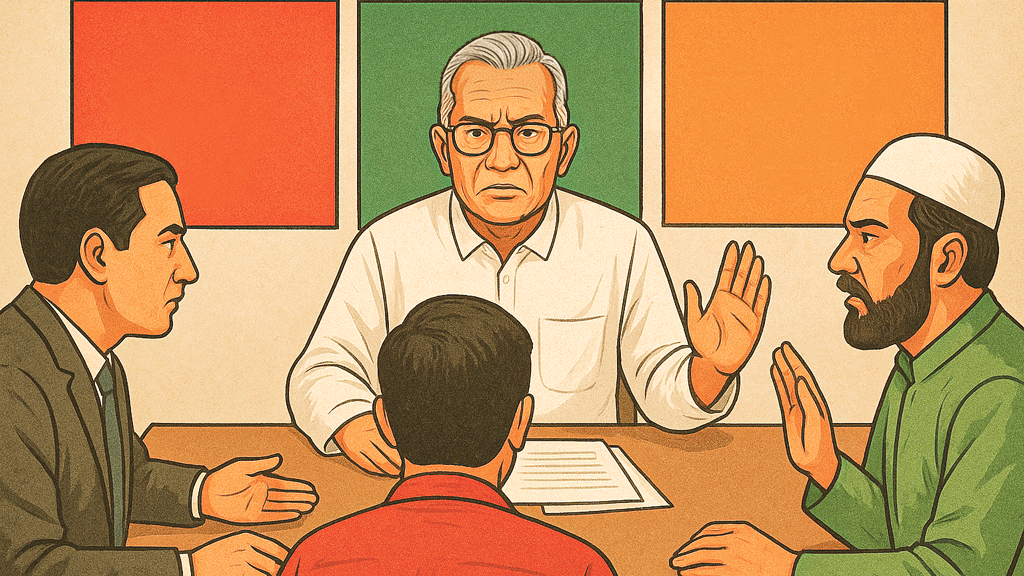
না, সব উপদেষ্টা প্রশ্নবিদ্ধ নন। তবে সংখ্যাটা যে নেহাত কম হবে না, তা অনুমান করা যায় যখন প্রধান তিনটি প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলই আলাদা আলাদাভাবে উপদেষ্টাদের দলঘনিষ্ঠতার অভিযোগ তোলে। অবশ্য এবারই প্রথম নয়, এর আগেও একই অভিযোগ তোলা হয়েছে, যখন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম কোনো কোনো উপদেষ্টার সেফ এক্সিটের প্রসঙ্গটি তুলেছিলেন। আর এবার তো জানা গেল প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে গত বুধবার অনুষ্ঠিত বৈঠকে জামায়াতে ইসলামী তাদের দৃষ্টিতে দলঘনিষ্ঠ উপদেষ্টাদের নামধামের তালিকাই নিয়ে গিয়েছিল। তবে ওই দিন সেই তালিকা তারা প্রধান উপদেষ্টাকে দেয়নি। প্রয়োজন হলে পরে দেবে। এবার শুধু বিষয়টি সম্পর্কে প্রধান উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং কয়েকজন উপদেষ্টা বিএনপির পক্ষে কাজ করছেন বলে অভিযোগ করেছে।
শুধু উপদেষ্টা নয়, জামায়াত সুনির্দিষ্ট নাম-ঠিকানা নিয়ে গিয়েছিল প্রায় ৪০ জন আমলারও, যাঁরা তাদের দৃষ্টিতে কোনো না কোনো দলের হয়ে, বিশেষত বিএনপির হয়ে কাজ করছেন। আর বৈঠক-পরবর্তী সংবাদ ব্রিফিংয়ে জামায়াতের নেতারা উল্লেখ করেছেন যে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রশাসন ও পুলিশের ৭০ থেকে ৮০ ভাগ লোকই বিএনপির। বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টাকে জামায়াত বলেছে, নির্বাচনের আগে সরকারকে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে। এ জন্য সচিবালয়, পুলিশ প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিবালয়ে রদবদল আনতে হবে। বিএনপির বিরুদ্ধে জামায়াতের আরও অভিযোগ, বিএনপি রাজনৈতিক চাপে পড়ে গণভোটে রাজি হলেও এখন জটিলতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে।
ওই দিনই জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) একটি প্রতিনিধিদলও পৃথকভাবে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এরপর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, তাঁরা প্রধান উপদেষ্টাকে বলেছেন, নির্বাচনের আগে বড় রাজনৈতিক দলগুলো প্রশাসন ও পুলিশে নিজেদের মতো ভাগ-বাঁটোয়ারা শুরু করেছে। ডিসি-এসপিদের তালিকা করে সরকারকে দিচ্ছে এবং সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের মধ্য থেকেও এ ব্যাপারে তারা সহযোগিতা পাচ্ছে।
এনসিপির আরও বড় অভিযোগ নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে। প্রধান উপদেষ্টাকে তারা বলেছে, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ আচরণ করছে না। কোনো কোনো দলের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ করছে। শাপলা প্রতীক পাওয়া প্রসঙ্গে নাহিদ ইসলামের স্পষ্ট বক্তব্য হলো, যে নির্বাচন কমিশন নিবন্ধন এবং প্রতীকের বিষয়ে এনসিপির সঙ্গে ন্যায়বিচার করে না, তার অধীনে নির্বাচনে গিয়ে ন্যায়বিচার এবং নিরপেক্ষতা বা সঠিক ফলাফল পাওয়ার ব্যাপারে ভরসা করা যায় না। তাই নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। তাঁদের যুক্তি হলো, নির্বাচন কমিশনের কারণে যদি সুষ্ঠু নির্বাচন না হয়, সেই দায়ও সরকারের ওপরই পড়বে।
উপদেষ্টাদের নিয়ে প্রশ্ন আছে বিএনপিরও। জামায়াত ও এনসিপির এক দিন আগে, গত মঙ্গলবার প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করেছে বিএনপি। সেই বৈঠকে তারাও কয়েকজন উপদেষ্টাকে নিয়ে আপত্তি তুলেছে। কারও নাম উল্লেখ না করেই বিতর্কিত উপদেষ্টাদের বাদ দেওয়ার জন্য প্রধান উপদেষ্টাকে আহ্বান জানিয়েছে দলটি। এর আগেও বিএনপির পক্ষ থেকে এমন আহ্বান জানানো হয়েছিল। তখন দুই ছাত্র উপদেষ্টাকে পদত্যাগ করতে বলা হয়েছিল বলেও খবর বেরিয়েছে। তবে তাঁরা তখনই তাতে রাজি হননি। উপদেষ্টাদের ছাড়াও প্রশাসন নিয়েও অন্য দুই দলের মতোই উদ্বেগ আছে বিএনপিরও। মঙ্গলবারের বৈঠকে তারা এই বলে প্রধান উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যে প্রশাসন, পুলিশ এবং বিচার বিভাগের প্রায় ৫০ ভাগ ফ্যাসিস্টের দোসর।
তিনটি দলের সঙ্গে বৈঠকেই প্রধান উপদেষ্টা সরকারের নিরপেক্ষ অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘আমাদের নিরপেক্ষতা নিয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে আমরা ইতিমধ্যে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি; সামনে আরও অনেক উদ্যোগ আপনারা দেখতে পাবেন।’
তা প্রধান উপদেষ্টা যতই নিশ্চয়তা দিন না কেন, যেখানে সব দলের কাছেই উপদেষ্টাদের (সবার নয়) এবং প্রশাসনের পক্ষপাতদুষ্টতা স্পষ্ট, যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ আছে উল্লেখ করে যখন প্রকাশ্যে বারবার অভিযোগ করা হচ্ছে, সেখানে রাজনৈতিক দলগুলো কীভাবে নিশ্চিন্তে নিশ্চিত থাকতে পারে! তা ছাড়া, মাঝেমধ্যেই তো দলগুলোর পরস্পরের প্রতি বৈরী বক্তব্য রাজনৈতিক অঙ্গনে উত্তাপ ছড়াচ্ছে। যেমন কিছুদিন আগে এনসিপির আহ্বায়ক তাঁর ফেসবুক পোস্টে বললেন, সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন (পিআর) নিয়ে জামায়াতের আন্দোলন রাজনৈতিক প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। কিংবা জামায়াত জুলাই অভ্যুত্থানের আগে-পরে কখনোই সংস্কার আলোচনায় যুক্ত হয়নি। তারা কোনো কার্যকর প্রস্তাব দেয়নি। কোনো সাংবিধানিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেনি এবং গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতি কোনো অঙ্গীকারও দেখায়নি।
এর পরিপ্রেক্ষিতে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বললেন আরও একটু শক্ত কথা—‘জন্মের পরই বাপের সাথে পাল্লা দিতে যেও না।’ সরকার ভাবতে পারে যে এগুলো তো রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেকার বাহাস। এটা নিয়ে তাদের অতটা না ভাবলেও চলবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এই বাহাসগুলো তো রাজনৈতিক বাস্তবতা। এগুলো তো রাজনৈতিক অঙ্গনকে অস্থিতিশীল করতে পারে, যা শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের পরিবেশেও প্রভাব ফেলতে পারে।
তারপর উল্লেখ করা যায় মঙ্গলবারের বৈঠকে বিএনপি যে অন্তর্বর্তী সরকারকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে, সে সম্পর্কে এনসিপির প্রতিক্রিয়ার কথা। এনসিপি বলল হঠাৎ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার পরামর্শটি দুরভিসন্ধিমূলক। কারণ, অন্তর্বর্তী সরকার গণ-অভ্যুত্থানের সরকার। সংস্কার, বিচার ও নির্বাচন—এই তিনটি তাদের ম্যান্ডেট। অথচ বিএনপির বক্তব্যটি ছিল—নিরপেক্ষতার নিরিখে এখন অন্তর্বর্তী সরকারকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা নিতে হবে।
এইসব রাজনৈতিক টানাপোড়েন ছাড়াও কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখনো অমীমাংসিত রয়েছে। যেমন জামায়াতের কাছে অমীমাংসিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি, সনদ বাস্তবায়নের পদ্ধতি, ওই সনদের ভিত্তিতে নির্বাচন, পিআর পদ্ধতির নির্বাচন এবং জাতীয় নির্বাচনের আগে আগামী নভেম্বরে গণভোট। এই দাবিতে জামায়াতসহ আটটি দল আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এনসিপির কাছে অমীমাংসিত বিষয় জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি, সনদ বাস্তবায়নের পদ্ধতি, নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠন এবং তাদের দাবিকৃত নির্বাচনী প্রতীক শাপলা বরাদ্দ দেওয়া। বিএনপির কাছে সবচেয়ে বড় ইস্যু সময়মতো সুষ্ঠু নির্বাচন। এ ছাড়া এই তিনটি দলের কাছেই (হয়তো আরও অনেক দলের কাছে) সাধারণ ইস্যু হচ্ছে সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য দলঘনিষ্ঠ উপদেষ্টাদের সরিয়ে দেওয়া। এর মধ্যে বেশ কিছু বিষয় প্রতিটি দল চায় না। এসব বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের নিরপেক্ষ ভূমিকা নিশ্চিত করা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে সেই ভূমিকা নিরপেক্ষ হিসেবেই প্রতীয়মান হওয়া এক বড় চ্যালেঞ্জই বটে।

সাতচল্লিশের দেশভাগকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িকতা ক্রমাগত তীব্র হলো। রক্তপাত ঘটল। পরে যখন স্বাধীন হলো ভারতবর্ষ, তখন একটির জায়গায় দুটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটল। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার সমস্যার সমাধান হলো না; না পাকিস্তানে, না ভারতে। পাকিস্তানের সব ধর্মাবলম্বীকে বলা হলো রাজনৈতিকভাবে নিজ নিজ ধর্মমত ভুলে
১৬ জুলাই ২০২৫
মিরপুরের শিয়ালবাড়ী এলাকায় একটি রাসায়নিক গুদামে আগুন লাগার পর যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল, সে কথা সবাই এখন জানেন। যাঁরা স্বজন হারিয়েছেন, তাঁরা জানেন এটা তাঁদের পরিবারের জন্য কত বড় ক্ষতি। নিহতদের পরিবার ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে কি না, তাদের জীবনে স্থিতি ফিরিয়ে আনতে কী করা দরকার...
১০ ঘণ্টা আগে
সমাজ এগিয়ে চলেছে দ্রুতগতিতে, পৃথিবী প্রবেশ করেছে এক নতুন যুগে। এই গতিময় সভ্যতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে আমরা হয়তো অনেক কিছু পাচ্ছি, কিন্তু হারিয়ে ফেলছি আরও বেশি কিছু। আজ আমরা এক অদ্ভুত স্বার্থপর সময়ে বাস করছি, যেখানে প্রতিটি সম্পর্কের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতি।
১১ ঘণ্টা আগে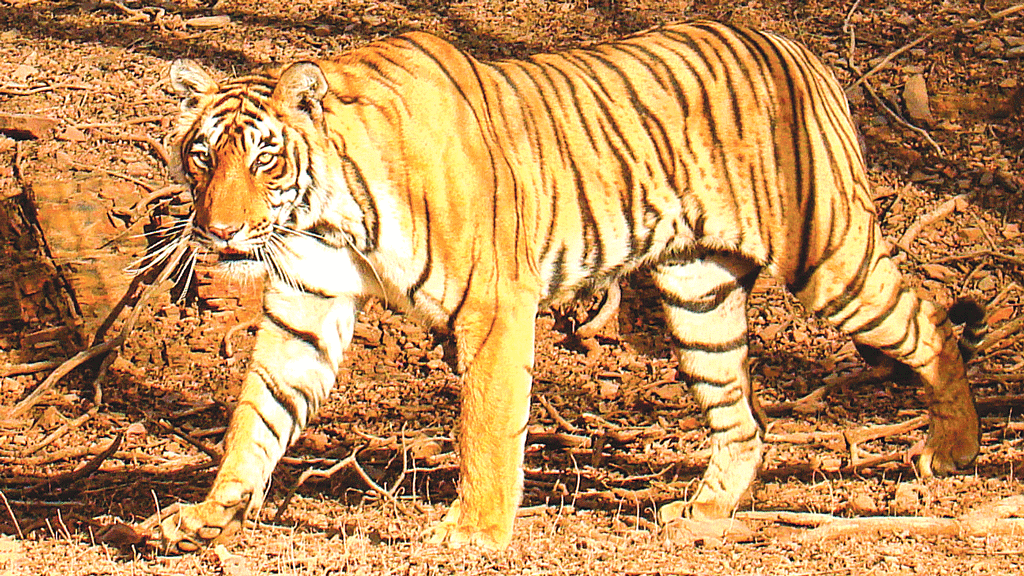
প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি সুন্দরবন এ দেশের দক্ষিণাঞ্চলকে মাতৃস্নেহে আগলে রেখেছে। ঝড়-ঝঞ্ঝা, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিক্ষয় রোধসহ সব প্রাকৃতিক দুর্যোগে সুন্দরবন আমাদের রক্ষা করে আসছে। এই সুন্দরবনের এক অনন্য প্রজাতির প্রাণী হলো রয়েল বেঙ্গল টাইগার।
১১ ঘণ্টা আগেহেনা শিকদার

সমাজ এগিয়ে চলেছে দ্রুতগতিতে, পৃথিবী প্রবেশ করেছে এক নতুন যুগে। এই গতিময় সভ্যতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে আমরা হয়তো অনেক কিছু পাচ্ছি, কিন্তু হারিয়ে ফেলছি আরও বেশি কিছু। আজ আমরা এক অদ্ভুত স্বার্থপর সময়ে বাস করছি, যেখানে প্রতিটি সম্পর্কের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতি। এমন এক পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বড় প্রশ্নের মুখে পড়েছে যে সম্পর্কটি, মানুষের আত্মার সঙ্গে মিশে থাকে—বন্ধুত্ব।
একসময় বন্ধুত্ব ছিল নিঃস্বার্থ ভালোবাসার এক দারুণ উদাহরণ। সেখানে লেনদেনের কোনো হিসাব ছিল না, ছিল শুধু একে অপরের প্রতি বিশ্বাস, আস্থা এবং নির্ভরতা। শৈশবের সেই দিনগুলোর কথা মনে করলে আজও অনেকের মন আর্দ্র হয়ে ওঠে। টিফিনের খাবার ভাগ করে খাওয়া, বন্ধুর দুঃখে নির্দ্বিধায় পাশে দাঁড়ানো, কিংবা সামান্য কারণে অহেতুক ঝগড়া করে আবার মুহূর্তেই সব ভুলে গিয়ে একে অপরের হাত ধরার মধ্যে যে পবিত্রতা ছিল, আজকের যান্ত্রিক সভ্যতায় তা যেন এক দুর্লভ বস্তু।
বর্তমান সমাজব্যবস্থা আমাদের শিখিয়েছে কীভাবে সবকিছুকে ব্যক্তিগত লাভের নিরিখে বিচার করতে হয়। আমরা এখন বন্ধু বানানোর আগেও অবচেতন মনে বিচার করে নিই—এই সম্পর্কটি আমার জীবনে কতটা মূল্য যোগ করবে? তার সামাজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা, কিংবা তার মাধ্যমে আমার কোনো উপকার হবে কি না—এইসব প্রশ্নই এখন বন্ধুত্বের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে, একধরনের ‘শর্তাধীন’ বন্ধুত্বের জন্ম হচ্ছে, যেখানে স্বার্থের লেনদেন শেষ হলেই সম্পর্কের সুতো ছিঁড়ে যায়। এই ধরনের বন্ধুত্ব অনেকটা ব্যবসায়িক চুক্তির মতো, যেখানে একে অপরকে ব্যবহার করে নিজের আখের গোছানোই মূল উদ্দেশ্য।
এই স্বার্থপরতার পেছনে অবশ্য বেশ কিছু সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক কারণও রয়েছে। প্রথমত, আধুনিক জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান চাপ এবং প্রতিযোগিতা মানুষকে এতটাই আত্মকেন্দ্রিক করে তুলেছে যে, সে নিজের জগৎ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছে না। দ্বিতীয়ত, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিস্তার এক মায়াবী জগতের সৃষ্টি করেছে। এখানে মানুষের বন্ধুর সংখ্যা হাজার হাজার, কিন্তু সত্যিকার অর্থে ভরসা করার মতো বন্ধুর সংখ্যা প্রায় শূন্য। লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ারের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই ভার্চুয়াল বন্ধুত্ব আসলে একধরনের লোকদেখানো সম্পর্ক, যার গভীরে কোনো প্রাণের ছোঁয়া নেই। এখানে সবাই যেন এক অদৃশ্য প্রতিযোগিতায় নেমেছে—কার কত বন্ধু, কে কতটা জনপ্রিয়। এই জাঁকজমকপূর্ণ সংস্কৃতি আমাদের সত্যিকারের আবেগ এবং অনুভূতি থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।
তবে এই হতাশাজনক চিত্রের মধ্যেও আশার আলো রয়েছে। স্বার্থের এই ঝোড়ো হাওয়ার বিপরীতে দাঁড়িয়েও কিছু মানুষ এখনো সত্যিকারের বন্ধুত্বের পতাকা উড়িয়ে চলেছেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন, বন্ধুত্ব মানে শুধু দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক নয়, বরং এটি একটি আত্মিক টান, যা কোনো স্বার্থের বিনিময়ে বিক্রি হয় না। একজন সত্যিকারের বন্ধু আয়নার মতো, যে কেবল আমাদের ভালো দিকগুলোই তুলে ধরে না, বরং আমাদের ভুলগুলোও দেখিয়ে দেয়। সে আমাদের বিপদের দিনে ঢাল হয়ে দাঁড়ায় এবং আনন্দের দিনে মন খুলে হাসে।
এই স্বার্থপর সময়ে সত্যিকারের বন্ধু খুঁজে পাওয়া হয়তো কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন নিজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। বন্ধুত্বের সম্পর্ককে যদি আমরা লাভ-ক্ষতির হিসাব থেকে মুক্ত করতে পারি, তবেই এর আসল সৌন্দর্য উপলব্ধি করা সম্ভব। বন্ধুত্ব কোনো পণ্য নয় যে তাকে ব্যবহার করে ফেলে দিতে হবে। এটি একটি চারা গাছের মতো, যাকে যত্ন, বিশ্বাস এবং সময় দিয়ে বড় করে তুলতে হয়। যখন একজন মানুষ সব ধরনের স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে আরেকজন মানুষের পাশে দাঁড়ায়, তখনই জন্ম নেয় এক নির্মল বন্ধুত্ব।
স্বার্থের এই সমাজে বন্ধুত্বের মানে হলো এক নিঃস্বার্থ আশ্রয়। এমন এক সম্পর্ক, যেখানে আপনি কোনো মুখোশ ছাড়াই নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন, যেখানে আপনার দুর্বলতাগুলো নিয়ে কেউ উপহাস করবে না, বরং আপনাকে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে সাহায্য করবে। এই বন্ধুত্ব আপনাকে শেখাবে যে পৃথিবীতে এখনো এমন কিছু সম্পর্ক আছে, যা অর্থ বা ক্ষমতার বিনিময়ে কেনা যায় না, যা কেবল হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায়। তাই এই যান্ত্রিক সভ্যতায় হারিয়ে যাওয়ার আগে আমাদের উচিত জীবনের সেই নিঃস্বার্থ বন্ধুত্বের সম্পর্কগুলোকে খুঁজে বের করা এবং পরম মমতায় সেগুলো আগলে রাখা। কারণ, দিন শেষে এই সম্পর্কগুলোই আমাদের বেঁচে থাকার আসল প্রেরণা জোগায়।
শিক্ষার্থী, দর্শন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

সমাজ এগিয়ে চলেছে দ্রুতগতিতে, পৃথিবী প্রবেশ করেছে এক নতুন যুগে। এই গতিময় সভ্যতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে আমরা হয়তো অনেক কিছু পাচ্ছি, কিন্তু হারিয়ে ফেলছি আরও বেশি কিছু। আজ আমরা এক অদ্ভুত স্বার্থপর সময়ে বাস করছি, যেখানে প্রতিটি সম্পর্কের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতি। এমন এক পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বড় প্রশ্নের মুখে পড়েছে যে সম্পর্কটি, মানুষের আত্মার সঙ্গে মিশে থাকে—বন্ধুত্ব।
একসময় বন্ধুত্ব ছিল নিঃস্বার্থ ভালোবাসার এক দারুণ উদাহরণ। সেখানে লেনদেনের কোনো হিসাব ছিল না, ছিল শুধু একে অপরের প্রতি বিশ্বাস, আস্থা এবং নির্ভরতা। শৈশবের সেই দিনগুলোর কথা মনে করলে আজও অনেকের মন আর্দ্র হয়ে ওঠে। টিফিনের খাবার ভাগ করে খাওয়া, বন্ধুর দুঃখে নির্দ্বিধায় পাশে দাঁড়ানো, কিংবা সামান্য কারণে অহেতুক ঝগড়া করে আবার মুহূর্তেই সব ভুলে গিয়ে একে অপরের হাত ধরার মধ্যে যে পবিত্রতা ছিল, আজকের যান্ত্রিক সভ্যতায় তা যেন এক দুর্লভ বস্তু।
বর্তমান সমাজব্যবস্থা আমাদের শিখিয়েছে কীভাবে সবকিছুকে ব্যক্তিগত লাভের নিরিখে বিচার করতে হয়। আমরা এখন বন্ধু বানানোর আগেও অবচেতন মনে বিচার করে নিই—এই সম্পর্কটি আমার জীবনে কতটা মূল্য যোগ করবে? তার সামাজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা, কিংবা তার মাধ্যমে আমার কোনো উপকার হবে কি না—এইসব প্রশ্নই এখন বন্ধুত্বের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে, একধরনের ‘শর্তাধীন’ বন্ধুত্বের জন্ম হচ্ছে, যেখানে স্বার্থের লেনদেন শেষ হলেই সম্পর্কের সুতো ছিঁড়ে যায়। এই ধরনের বন্ধুত্ব অনেকটা ব্যবসায়িক চুক্তির মতো, যেখানে একে অপরকে ব্যবহার করে নিজের আখের গোছানোই মূল উদ্দেশ্য।
এই স্বার্থপরতার পেছনে অবশ্য বেশ কিছু সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক কারণও রয়েছে। প্রথমত, আধুনিক জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান চাপ এবং প্রতিযোগিতা মানুষকে এতটাই আত্মকেন্দ্রিক করে তুলেছে যে, সে নিজের জগৎ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছে না। দ্বিতীয়ত, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিস্তার এক মায়াবী জগতের সৃষ্টি করেছে। এখানে মানুষের বন্ধুর সংখ্যা হাজার হাজার, কিন্তু সত্যিকার অর্থে ভরসা করার মতো বন্ধুর সংখ্যা প্রায় শূন্য। লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ারের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই ভার্চুয়াল বন্ধুত্ব আসলে একধরনের লোকদেখানো সম্পর্ক, যার গভীরে কোনো প্রাণের ছোঁয়া নেই। এখানে সবাই যেন এক অদৃশ্য প্রতিযোগিতায় নেমেছে—কার কত বন্ধু, কে কতটা জনপ্রিয়। এই জাঁকজমকপূর্ণ সংস্কৃতি আমাদের সত্যিকারের আবেগ এবং অনুভূতি থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।
তবে এই হতাশাজনক চিত্রের মধ্যেও আশার আলো রয়েছে। স্বার্থের এই ঝোড়ো হাওয়ার বিপরীতে দাঁড়িয়েও কিছু মানুষ এখনো সত্যিকারের বন্ধুত্বের পতাকা উড়িয়ে চলেছেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন, বন্ধুত্ব মানে শুধু দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক নয়, বরং এটি একটি আত্মিক টান, যা কোনো স্বার্থের বিনিময়ে বিক্রি হয় না। একজন সত্যিকারের বন্ধু আয়নার মতো, যে কেবল আমাদের ভালো দিকগুলোই তুলে ধরে না, বরং আমাদের ভুলগুলোও দেখিয়ে দেয়। সে আমাদের বিপদের দিনে ঢাল হয়ে দাঁড়ায় এবং আনন্দের দিনে মন খুলে হাসে।
এই স্বার্থপর সময়ে সত্যিকারের বন্ধু খুঁজে পাওয়া হয়তো কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন নিজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। বন্ধুত্বের সম্পর্ককে যদি আমরা লাভ-ক্ষতির হিসাব থেকে মুক্ত করতে পারি, তবেই এর আসল সৌন্দর্য উপলব্ধি করা সম্ভব। বন্ধুত্ব কোনো পণ্য নয় যে তাকে ব্যবহার করে ফেলে দিতে হবে। এটি একটি চারা গাছের মতো, যাকে যত্ন, বিশ্বাস এবং সময় দিয়ে বড় করে তুলতে হয়। যখন একজন মানুষ সব ধরনের স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে আরেকজন মানুষের পাশে দাঁড়ায়, তখনই জন্ম নেয় এক নির্মল বন্ধুত্ব।
স্বার্থের এই সমাজে বন্ধুত্বের মানে হলো এক নিঃস্বার্থ আশ্রয়। এমন এক সম্পর্ক, যেখানে আপনি কোনো মুখোশ ছাড়াই নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন, যেখানে আপনার দুর্বলতাগুলো নিয়ে কেউ উপহাস করবে না, বরং আপনাকে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে সাহায্য করবে। এই বন্ধুত্ব আপনাকে শেখাবে যে পৃথিবীতে এখনো এমন কিছু সম্পর্ক আছে, যা অর্থ বা ক্ষমতার বিনিময়ে কেনা যায় না, যা কেবল হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায়। তাই এই যান্ত্রিক সভ্যতায় হারিয়ে যাওয়ার আগে আমাদের উচিত জীবনের সেই নিঃস্বার্থ বন্ধুত্বের সম্পর্কগুলোকে খুঁজে বের করা এবং পরম মমতায় সেগুলো আগলে রাখা। কারণ, দিন শেষে এই সম্পর্কগুলোই আমাদের বেঁচে থাকার আসল প্রেরণা জোগায়।
শিক্ষার্থী, দর্শন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

সাতচল্লিশের দেশভাগকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িকতা ক্রমাগত তীব্র হলো। রক্তপাত ঘটল। পরে যখন স্বাধীন হলো ভারতবর্ষ, তখন একটির জায়গায় দুটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটল। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার সমস্যার সমাধান হলো না; না পাকিস্তানে, না ভারতে। পাকিস্তানের সব ধর্মাবলম্বীকে বলা হলো রাজনৈতিকভাবে নিজ নিজ ধর্মমত ভুলে
১৬ জুলাই ২০২৫
মিরপুরের শিয়ালবাড়ী এলাকায় একটি রাসায়নিক গুদামে আগুন লাগার পর যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল, সে কথা সবাই এখন জানেন। যাঁরা স্বজন হারিয়েছেন, তাঁরা জানেন এটা তাঁদের পরিবারের জন্য কত বড় ক্ষতি। নিহতদের পরিবার ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে কি না, তাদের জীবনে স্থিতি ফিরিয়ে আনতে কী করা দরকার...
১০ ঘণ্টা আগে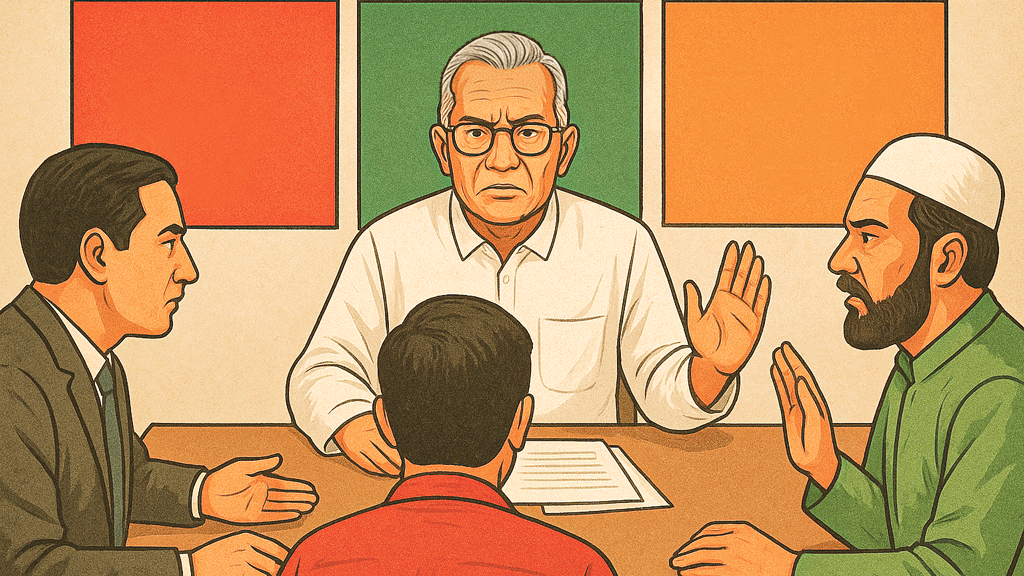
না, সব উপদেষ্টা প্রশ্নবিদ্ধ নন। তবে সংখ্যাটা যে নেহাত কম হবে না, তা অনুমান করা যায় যখন প্রধান তিনটি প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলই আলাদা আলাদাভাবে উপদেষ্টাদের দলঘনিষ্ঠতার অভিযোগ তোলে। অবশ্য এবারই প্রথম নয়, এর আগেও একই অভিযোগ তোলা হয়েছে, যখন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম কোনো কোনো উপদেষ্টার সেফ...
১১ ঘণ্টা আগে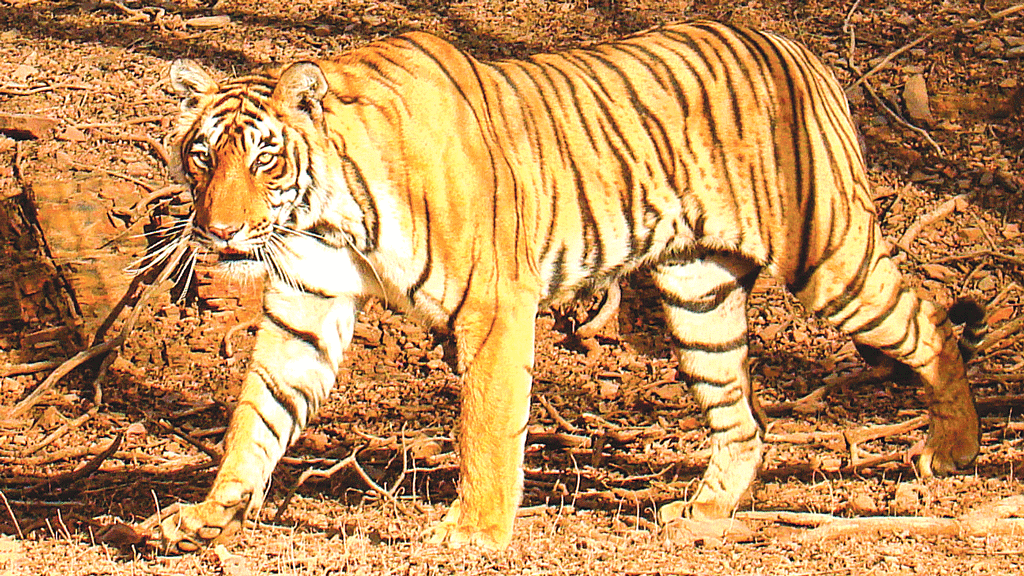
প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি সুন্দরবন এ দেশের দক্ষিণাঞ্চলকে মাতৃস্নেহে আগলে রেখেছে। ঝড়-ঝঞ্ঝা, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিক্ষয় রোধসহ সব প্রাকৃতিক দুর্যোগে সুন্দরবন আমাদের রক্ষা করে আসছে। এই সুন্দরবনের এক অনন্য প্রজাতির প্রাণী হলো রয়েল বেঙ্গল টাইগার।
১১ ঘণ্টা আগেরিয়াদ হোসেন
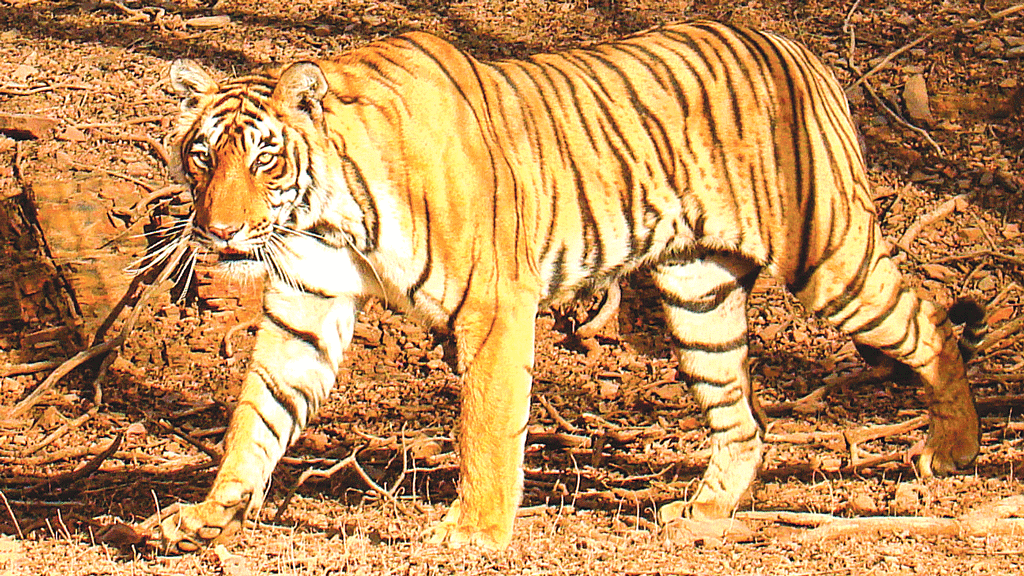
প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি সুন্দরবন এ দেশের দক্ষিণাঞ্চলকে মাতৃস্নেহে আগলে রেখেছে। ঝড়-ঝঞ্ঝা, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিক্ষয় রোধসহ সব প্রাকৃতিক দুর্যোগে সুন্দরবন আমাদের রক্ষা করে আসছে। এই সুন্দরবনের এক অনন্য প্রজাতির প্রাণী হলো রয়েল বেঙ্গল টাইগার।
সাধারণ মানুষের মতো বাঘেরও প্রধান দুটি মৌলিক চাহিদা হলো খাদ্য ও বাসস্থান। বিশেষ করে খাদ্যের জোগান এবং আবাসস্থল নিরাপদ করতে পারলে বাঘ বাঁচিয়ে রাখা কিংবা তাদের প্রজনন বৃদ্ধিতে অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। এ জন্য সুন্দরবনকে বন্য প্রাণীর অবাধ বিচরণের জায়গা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তাহলে বাঘসহ অন্য প্রজাতির প্রাণীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। পৃথিবীর মাত্র ১৩টি দেশে এখন বাঘের অস্তিত্ব আছে। বাঘ বাঁচাতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সেসব দেশের সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
সুন্দরবনের বাস্তুসংস্থান রক্ষায় অন্য প্রজাতির প্রাণী থেকে বাঘ সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে সুন্দরবনে চোরা শিকারি বাঘের প্রধান হুমকি। কিছু অতিলোভী চোরা শিকারি ও বনদস্যুদের জন্য দিন দিন বাঘের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। সবশেষ তথ্যমতে, সুন্দরবনে বাঘ রয়েছে ১১৪টি। কয়েক বছর আগে বড় বড় বনদস্যু দলের আত্মসমর্পণের ফলে বাঘনিধন কিছুটা কমে এসেছে। দুই বছর আগেও খাদ্যসংকটে বাঘ লোকালয়ে এলে হত্যা করা হতো। এখন সেটিও অনেকটা বন্ধ হয়েছে। বন সংরক্ষণে বন মন্ত্রণালয়ের নানামুখী পদক্ষেপের কারণে সুন্দরবনসংলগ্ন স্থানীয় মানুষ আগের থেকে অনেক সচেতন হয়ে উঠেছে। এ জন্য বনের ওপর নির্ভরশীল মানুষগুলোর জীবিকায় সরকারকে আরও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। তাদের জীবন-জীবিকার জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের বিষয়ে আরও বেশি কাজ করতে হবে।
সুন্দরবনকে বাঁচাতে এবং বনের জীববৈচিত্র্য রক্ষা করতে বাঘ সংরক্ষণের বিকল্প নেই। আর এ জন্য বন বিভাগ কিংবা সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকলে সুন্দরবন বা বাঘ কোনোটাই রক্ষা করা সম্ভব হবে না; যদি আমরা আমাদের নিজেদের জায়গা থেকে সচেতন না হই। পাশাপাশি বাঘনিধন ও হরিণ শিকার বন্ধের জন্য ২০১২ সালে বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। যে আইনের ৩৬ ধারায় বাঘশিকারি বা হত্যাকারী জামিন-অযোগ্য হবেন এবং সর্বোচ্চ সাত বছর সর্বনিম্ন দুই বছর কারাদণ্ড ও ১ লাখ থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। এ আইনটিও অপরাধীদের বিরুদ্ধে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। তাহলে সুন্দরবন বাঁচানোর পাশাপাশি বাঘ, হরিণসহ নানা প্রজাতির প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।
শিক্ষার্থী, সরকারি বিএল কলেজ, খুলনা
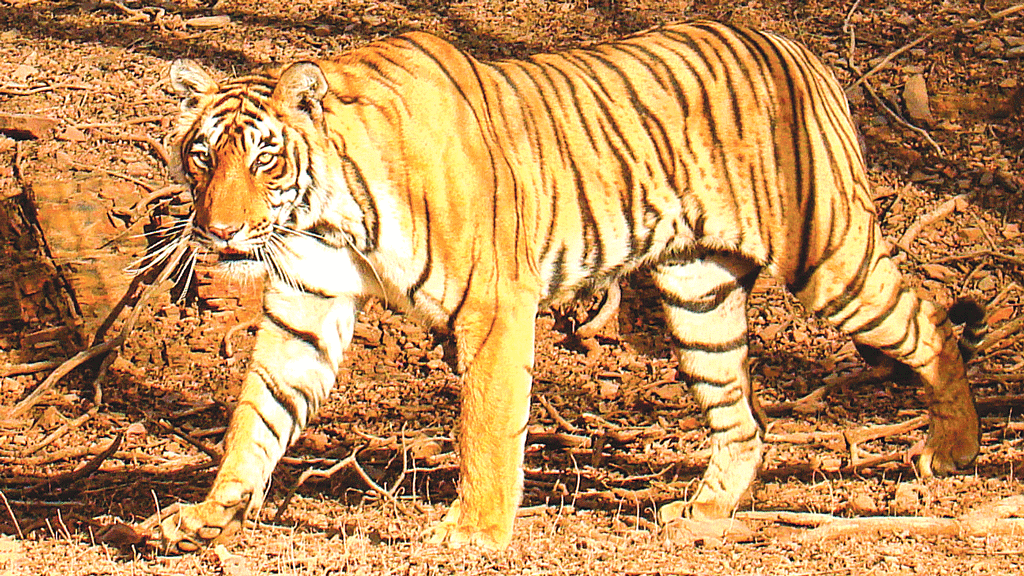
প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি সুন্দরবন এ দেশের দক্ষিণাঞ্চলকে মাতৃস্নেহে আগলে রেখেছে। ঝড়-ঝঞ্ঝা, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিক্ষয় রোধসহ সব প্রাকৃতিক দুর্যোগে সুন্দরবন আমাদের রক্ষা করে আসছে। এই সুন্দরবনের এক অনন্য প্রজাতির প্রাণী হলো রয়েল বেঙ্গল টাইগার।
সাধারণ মানুষের মতো বাঘেরও প্রধান দুটি মৌলিক চাহিদা হলো খাদ্য ও বাসস্থান। বিশেষ করে খাদ্যের জোগান এবং আবাসস্থল নিরাপদ করতে পারলে বাঘ বাঁচিয়ে রাখা কিংবা তাদের প্রজনন বৃদ্ধিতে অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। এ জন্য সুন্দরবনকে বন্য প্রাণীর অবাধ বিচরণের জায়গা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তাহলে বাঘসহ অন্য প্রজাতির প্রাণীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। পৃথিবীর মাত্র ১৩টি দেশে এখন বাঘের অস্তিত্ব আছে। বাঘ বাঁচাতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সেসব দেশের সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
সুন্দরবনের বাস্তুসংস্থান রক্ষায় অন্য প্রজাতির প্রাণী থেকে বাঘ সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে সুন্দরবনে চোরা শিকারি বাঘের প্রধান হুমকি। কিছু অতিলোভী চোরা শিকারি ও বনদস্যুদের জন্য দিন দিন বাঘের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। সবশেষ তথ্যমতে, সুন্দরবনে বাঘ রয়েছে ১১৪টি। কয়েক বছর আগে বড় বড় বনদস্যু দলের আত্মসমর্পণের ফলে বাঘনিধন কিছুটা কমে এসেছে। দুই বছর আগেও খাদ্যসংকটে বাঘ লোকালয়ে এলে হত্যা করা হতো। এখন সেটিও অনেকটা বন্ধ হয়েছে। বন সংরক্ষণে বন মন্ত্রণালয়ের নানামুখী পদক্ষেপের কারণে সুন্দরবনসংলগ্ন স্থানীয় মানুষ আগের থেকে অনেক সচেতন হয়ে উঠেছে। এ জন্য বনের ওপর নির্ভরশীল মানুষগুলোর জীবিকায় সরকারকে আরও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। তাদের জীবন-জীবিকার জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের বিষয়ে আরও বেশি কাজ করতে হবে।
সুন্দরবনকে বাঁচাতে এবং বনের জীববৈচিত্র্য রক্ষা করতে বাঘ সংরক্ষণের বিকল্প নেই। আর এ জন্য বন বিভাগ কিংবা সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকলে সুন্দরবন বা বাঘ কোনোটাই রক্ষা করা সম্ভব হবে না; যদি আমরা আমাদের নিজেদের জায়গা থেকে সচেতন না হই। পাশাপাশি বাঘনিধন ও হরিণ শিকার বন্ধের জন্য ২০১২ সালে বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। যে আইনের ৩৬ ধারায় বাঘশিকারি বা হত্যাকারী জামিন-অযোগ্য হবেন এবং সর্বোচ্চ সাত বছর সর্বনিম্ন দুই বছর কারাদণ্ড ও ১ লাখ থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। এ আইনটিও অপরাধীদের বিরুদ্ধে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। তাহলে সুন্দরবন বাঁচানোর পাশাপাশি বাঘ, হরিণসহ নানা প্রজাতির প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।
শিক্ষার্থী, সরকারি বিএল কলেজ, খুলনা

সাতচল্লিশের দেশভাগকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িকতা ক্রমাগত তীব্র হলো। রক্তপাত ঘটল। পরে যখন স্বাধীন হলো ভারতবর্ষ, তখন একটির জায়গায় দুটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটল। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার সমস্যার সমাধান হলো না; না পাকিস্তানে, না ভারতে। পাকিস্তানের সব ধর্মাবলম্বীকে বলা হলো রাজনৈতিকভাবে নিজ নিজ ধর্মমত ভুলে
১৬ জুলাই ২০২৫
মিরপুরের শিয়ালবাড়ী এলাকায় একটি রাসায়নিক গুদামে আগুন লাগার পর যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল, সে কথা সবাই এখন জানেন। যাঁরা স্বজন হারিয়েছেন, তাঁরা জানেন এটা তাঁদের পরিবারের জন্য কত বড় ক্ষতি। নিহতদের পরিবার ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে কি না, তাদের জীবনে স্থিতি ফিরিয়ে আনতে কী করা দরকার...
১০ ঘণ্টা আগে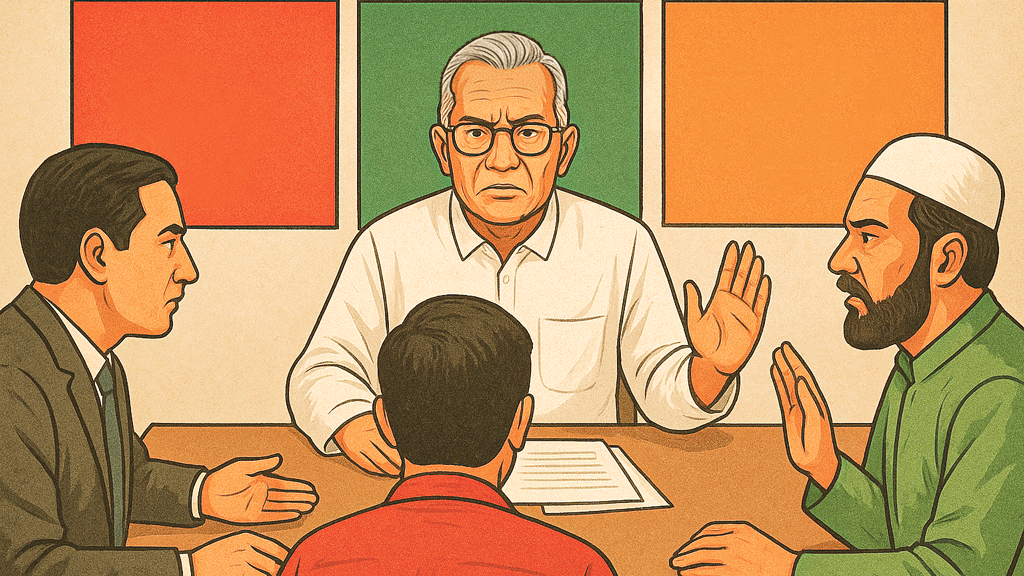
না, সব উপদেষ্টা প্রশ্নবিদ্ধ নন। তবে সংখ্যাটা যে নেহাত কম হবে না, তা অনুমান করা যায় যখন প্রধান তিনটি প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলই আলাদা আলাদাভাবে উপদেষ্টাদের দলঘনিষ্ঠতার অভিযোগ তোলে। অবশ্য এবারই প্রথম নয়, এর আগেও একই অভিযোগ তোলা হয়েছে, যখন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম কোনো কোনো উপদেষ্টার সেফ...
১১ ঘণ্টা আগে
সমাজ এগিয়ে চলেছে দ্রুতগতিতে, পৃথিবী প্রবেশ করেছে এক নতুন যুগে। এই গতিময় সভ্যতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে আমরা হয়তো অনেক কিছু পাচ্ছি, কিন্তু হারিয়ে ফেলছি আরও বেশি কিছু। আজ আমরা এক অদ্ভুত স্বার্থপর সময়ে বাস করছি, যেখানে প্রতিটি সম্পর্কের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতি।
১১ ঘণ্টা আগে