জাহীদ রেজা নূর
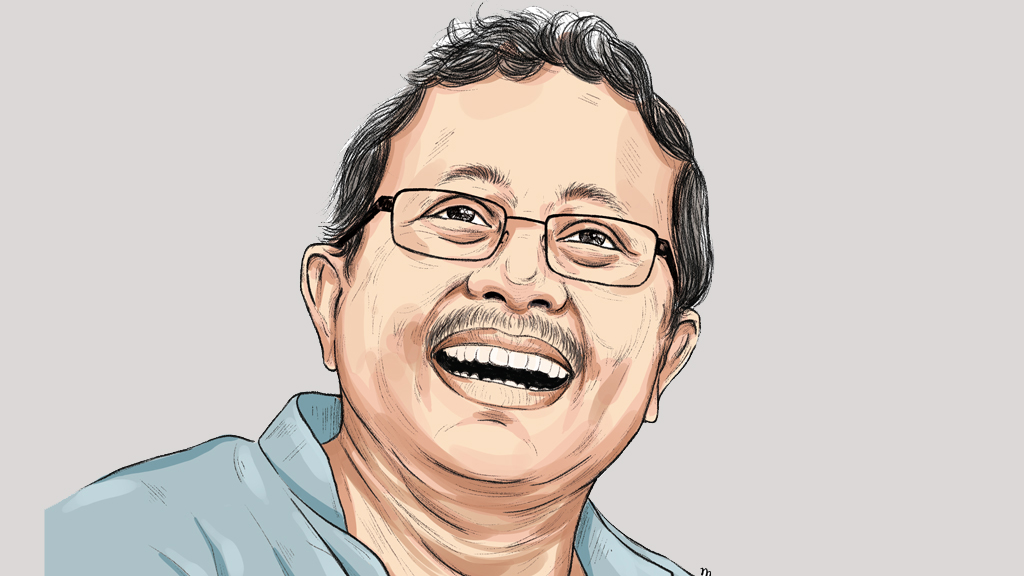
তারুণ্য চলে গতির ওপর নির্ভর করে। অদম্য গতিতে সে ছারখার করে দিতে চায় প্রচলিত সমাজব্যবস্থা। একটু বয়স হলে তার সে গতিতে আসে ভাটার টান।
কিছুদিন আগে অবকাশযাপনে গিয়েছিলাম ইনানী সৈকতে। কোভিড-সাম্রাজ্যকে সতর্কতার সঙ্গে মোকাবিলা করেই যেতে হয়েছিল ভ্রমণে এবং মাত্র আড়াই দিনের অভিজ্ঞতায় বোঝা গেল, একটু অবকাশ মনকে চাঙা করে তুলতে পারে।
গাছ কাটা, কংক্রিটের শহর নির্মাণের কথা আমলে নিয়েও এ কথা বলতে হয়, প্রকৃতি আমাদের উজাড় করে দিয়েছে। বঙ্গোপসাগর যেমন, তেমনি বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন অংশ, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকা, নেত্রকোনার বিরিশিরি, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পুরাকীর্তিসংলগ্ন প্রকৃতি—সবটা নিয়েই বলা যায়, এ দেশটি নয়নাভিরাম। শহরের কোলাহল ছাড়িয়ে দুই পাশে বৃক্ষশোভিত রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকলে ঠিকই মনে হবে, ‘এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি...’।
সমুদ্রসৈকতে গিয়ে কয়েকটি দৃশ্য ছবি হয়ে গেঁথে থাকল মনে। তার একটি হচ্ছে টি-শার্ট ও টাইট প্যান্ট পরনে তরুণীদের সাহসী পদচারণ, আপাদমস্তক বোরকায় আচ্ছাদিত তরুণীর সবার অলক্ষ্যে সঙ্গীকে চুম্বন, সৈকত এলাকার নিরাপত্তা। তিনটি বিষয়কে এক করলাম এ কারণে যে, আমার লেখাটি পরবর্তীকালে এ পথেই এগোবে।
দুই.
বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গত শতাব্দীর ষাটের দশকে যে স্বাধিকার আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তাতে আমাদের সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের একটা রূপরেখা ছিল। ‘ফিরে চল মাটির টানে’ শব্দগুলোকে মনে ধারণ করে সে সময় বাঙালি উৎসে ফেরার চেষ্টা করেছিল। তারপর সেই স্বাধিকারের পথ বেয়েই এল স্বাধীনতা এবং এর পর থেকে আমরা চারপাশে শুনতে পাচ্ছি, ‘স্বাধীনতার ফসল’ ঘরে তুলতে হবে। সংকটের শুরু এখানেই।
বলা হলো ‘স্বাধীনতার ফসল’। অথচ কবে জমি প্রস্তুত করা হলো, কবে বীজ বোনা হলো, কবে ফসল উঠল, তা রয়ে গেল অস্পষ্ট। বীজ বোনার পর্যায়েই তো জাতির জনককে হত্যা করা হলো। তারপর জিয়াউর রহমানের হাত ধরে দেশটা পিছিয়ে যেতে থাকল। যে অর্জনগুলো দৃশ্যমান হচ্ছিল, সেগুলো সরিয়ে দিয়ে আবার ধর্মীয় জোশের জন্ম দেওয়া হলো। অর্থাৎ যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ—ধর্মের নামে মানুষকে দমিয়ে রাখা, তারই ‘মিনি’ রূপ ফিরে এল দেশে। অসাম্প্রদায়িকতা যাই যাই করতে থাকল জীবন থেকে।
যতই কণ্ঠ জোরে ছাড়া হোক না কেন, বাঙালির কণ্ঠে অসাম্প্রদায়িকতার প্রত্যয় এখন আর মানায় না। তাই সুমনের ‘হাল ছেড়ো না, বন্ধু’ শব্দগুলোকে বড় দূরের কোনো দ্বীপ বলে মনে হয়। ভেতরে-ভেতরে বাঙালি সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠেছে। এমনকি যে রাজনৈতিক দলের হাত ধরে স্বাধীনতা এসেছিল, সেই আওয়ামী লীগের নেতাদের অনেকেরই চৈতন্যে অসাম্প্রদায়িকতা দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে। ফলে বাংলাদেশটা এগিয়ে যেতে থাকল দুদিকে—পশ্চিমাদের সর্বাঙ্গীণ অনুকরণের দিকে আর ধর্মীয় জোশের পুনরুজ্জীবনের দিকে, বাদ পড়ে গেল আত্মপরিচয়। সেটা খুইয়ে ফেলার প্রাণান্ত চেষ্টা বোধকরি সফল হতে চলেছে। আর তাই ভণ্ডামি হয়ে উঠেছে জাতির সবচেয়ে দৃশ্যমান পোস্টার।
তিন.
হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের আমল নিয়ে কত মুখরোচক কথাই না ঘুরে বেড়ায়। তিনি শুধু মূর্তিমান স্বৈরাচারই ছিলেন না, ছিলেন নারীলোভী, বকধার্মিক। এ কথা অনেকেরই মনে পড়ে যাবে, মসজিদে মসজিদে গিয়ে তিনি বলতেন, ‘কাল রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি, আপনাদের মসজিদে আমি নামাজ পড়ছি।’ ডাহা মিথ্যে! এরশাদ ওই মসজিদে পদার্পণ করার কয়েক দিন আগে থেকেই গোয়েন্দা-গুপ্তচরদের আনাগোনা শুরু হয়ে যেত। সবাই বুঝতে পারত, কিছু একটা ঘটতে চলেছে।
সেই এরশাদ, যিনি ধর্ম নিয়ে এই ভণ্ডামি করেছেন, যিনি নারীদের সঙ্গে অবমাননাকর ব্যবহার করেছেন, তিনিই কিনা রাষ্ট্রীয় ধর্মের পক্ষে ওকালতি করে সংবিধান পরিবর্তন করে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করে ফেললেন! এমন একজন রাষ্ট্রধর্ম বসিয়ে দিল সংবিধানে এবং তা নিয়ে বাহ্বা দেওয়া কি মানায়?
সংবিধানে লেখা আছে, ‘রাষ্ট্রধর্ম, ২(ক), প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সম-অধিকার নিশ্চিত করিবেন।’
তার মানে সমমর্যাদা ও সম-অধিকার আছে সবার। সে ক্ষেত্রে আলাদাভাবে রাষ্ট্রধর্মের কী মানে থাকতে পারে? বিষয়টি নিয়ে এখনকার তরুণেরা কী ভাবছে, তা জানার উপায় কি আছে?
চার.
বলা হয়, সবই অনিত্য। ইউরোপীয় পোশাক শরীরে জড়ালেই কেউ ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে যায় না। তেমনি আরবের পোশাকও মানুষকে আরবীয় সংস্কৃতির মুখপাত্র করে তোলে না। কারও পোশাক নিয়ে প্রশ্ন তোলা আমার উদ্দেশ্য নয়। পোশাক নিয়ে একটু পড়াশোনা করলেই বোঝা যাবে, আবহাওয়ার কারণেই পৃথিবীর একেক জায়গায় একেক রকম পোশাক পরা হয়। বছরের পর বছর ধরে মানুষের অভিজ্ঞতা তার সংস্কৃতির স্রোতোধারায় প্রবাহিত হয়। সেভাবেই সে বেছে নেয় পোশাক-আশাক, খাবার, আচরণের ধরন। এক সংস্কৃতির ধারায় এসে মিশে যায় আরেক সংস্কৃতি, কিছুকাল অস্বস্তির পর সেটাও একসময় হয়ে ওঠে সংস্কৃতির অঙ্গ। যা টেকার, তা টিকে থাকে; যা যাওয়ার, তা চলে যায়। এটাই নিয়ম। কিন্তু কোনো সংস্কৃতিকে জোর করে নিজের সংস্কৃতিতে টেনে আনা হলে প্রশ্ন ওঠে। বোঝা যায়, এই সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।
ইউরোপ-আমেরিকায় সমুদ্রস্নানের সময় স্বল্পপোশাক পরিধানের রয়েছে বৈজ্ঞানিক কারণ, তেমনি মধ্যপ্রাচ্যে পা থেকে মাথা পর্যন্ত পোশাক পরারও বৈজ্ঞানিক কারণ রয়েছে। আর এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম হয়েছে সাধারণ মানুষের হাজার বছরের অভিজ্ঞতা থেকে। সাধারণ মানুষই তা আবিষ্কার করেছে।
শুরুতে যে কথা বলেছিলাম, তাতে ফিরে যাই। আরবীয় পোশাকের যে তরুণীকে দেখলাম, বোরকা থেকে মুখ বের করে চুম্বন করছেন, তিনি আসলে বয়সের ধর্মকেই সবচেয়ে বড় ধর্ম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন ঠিক সে সময়টিতে। তখন তাঁর আশপাশের সবকিছু অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, তিনি বেঁচে ছিলেন তাঁর যৌবনের ওপর নির্ভর করে। ধর্মীয় অনুশাসনের তোয়াক্কা তিনি করেননি। তেমনি ইউরোপীয় পোশাক পরে যে মেয়েটি মুক্তভাবে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন চোখের সামনে, তিনিও কিন্তু বেছে নিয়েছিলেন যৌবনের শক্তিকে। এতগুলো পুরুষ-চক্ষুকে তিনি থোড়াই কেয়ার করেছেন।
কোন কাজটা ঠিক আর কোনটা নয়, সে বিচারের কথা ভাবছি না একটুও। বলতে চাইছি কেবল, চাপিয়ে দেওয়া কোনো কিছুই সমাজে টিকে থাকে না। কিছুটা সময় হয়তো তা শাসন করে বোধের জায়গাটা, তারপর আবার সবকিছু ঠিক জায়গায় ফিরে আসে। আবার কখনো নতুন করে ওঠে আলোড়ন, আবার তা স্তিমিত হয়, এভাবেই তো এগিয়ে চলে সময়।
সংস্কৃতির এই দেওয়া-নেওয়া কী চোখে দেখছে তরুণেরা তার ওপরও আমাদের এগিয়ে চলা অনেকটা নির্ভরশীল।
পাঁচ.
তারুণ্য চলে গতির ওপর নির্ভর করে। অদম্য গতিতে সে ছারখার করে দিতে চায় প্রচলিত সমাজব্যবস্থা। একটু বয়স হলে তার সে গতিতে আসে ভাটার টান। তখন সে ধীরে ধীরে নিজের চারপাশে একটা বলয় তৈরি করে নেয়। যেকোনো নতুনকে বরণ করে নেওয়ার মানসিকতা হারায়। তবে ভাবনার জগতে সে এগিয়ে চলে। বলা হয়ে থাকে, তরুণের গতি আর বর্ষীয়ানের জ্ঞানের সমন্বয়েই সমাজ এগিয়ে চলে স্বাস্থ্যকর পথে।
এ বিষয়েই আমি কয়েকটি প্রশ্ন রেখে যাব। আমাদের তারুণ্যে আশাবাদ কি দেখা যাচ্ছে? সামগ্রিকভাবে একটা ফাঁপা ‘জোর যার মুল্লুক তার’ সমাজ যে ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিচ্ছে আমাদের, সেটা কি বুঝতে পারছি আমরা? করপোরেটের ভূত যে অধস্তনদের একেবারে চামচায় পরিণত করছে, সেটা কি দেখতে পাচ্ছি আমরা? তেলবাজিই যে এখন সংস্কৃতির একটি অপরিত্যাজ্য মূল উপাদানে পরিণত হয়েছে, সে কথা স্বীকার করে নিতে দ্বিধা কেন আমাদের? ধর্ম নয়, ধর্ম প্রদর্শন ও ধর্মব্যবসা যখন গিলে ফেলছে আমাদের, তখন তারুণ্য নীরব কেন কিংবা নিজে থেকে এ বিষয়ে পড়াশোনা না করে ওই ধর্মব্যবসার প্রতি নিঃশর্ত সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে কেন? সংস্কৃতির নামে ঘটতে থাকা অনাচারগুলো কি নজরে পড়ছে আমাদের? লোকসংস্কৃতিকে বিদায় করার সব উপাদান জড়ো করা হয়েছে শহরে-গ্রামে-বন্দরে, সেটা কি বুঝতে পারছি?
আরও অনেক প্রশ্ন আছে, আগে এই প্রশ্নগুলোর জবাব নিজের কাছে খুঁজুন।
প্রাকৃতিক নয়নাভিরাম দেশটির মানুষের মনে আজ গভীর অসুখ। সেই অসুখ সারানো খুব সহজ কথা নয়। সে বাঙালি না মুসলমান না ইংরেজ, সে প্রশ্নেরই সমাধান সে করতে পারে না।
সে নারী-পুরুষ সমতায় বিশ্বাস করে কি না, সে প্রশ্নের উত্তরও তার জানা নেই। সে নিজের দেশকে ভালোবাসে কি না, তা নিয়ে মেকি উত্তর তার তৈরি আছে, কিন্তু আসলে তার মন ইউরোপে, আরব দেশে না কোথায় আটকে আছে, সেটা সে জানে না।
ভাবনার জগতে বৈপরীত্য এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, অভিন্নহৃদয় হয়ে, একই রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে সবাই গর্বভরে নিজের পরিচয় দেব, সে আশার সলতে অনেক কষ্ট করে জ্বালিয়ে রাখতে হচ্ছে।
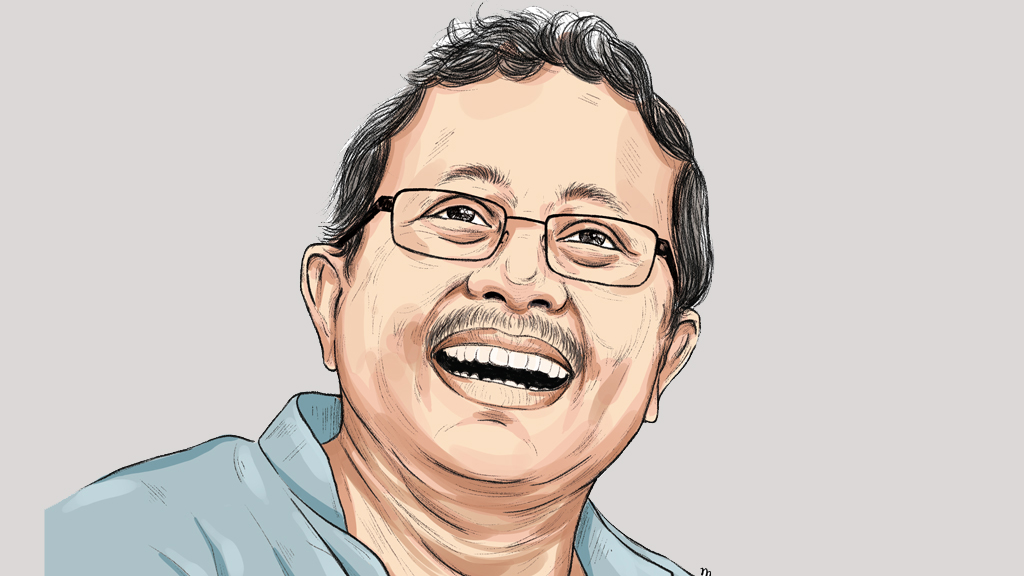
তারুণ্য চলে গতির ওপর নির্ভর করে। অদম্য গতিতে সে ছারখার করে দিতে চায় প্রচলিত সমাজব্যবস্থা। একটু বয়স হলে তার সে গতিতে আসে ভাটার টান।
কিছুদিন আগে অবকাশযাপনে গিয়েছিলাম ইনানী সৈকতে। কোভিড-সাম্রাজ্যকে সতর্কতার সঙ্গে মোকাবিলা করেই যেতে হয়েছিল ভ্রমণে এবং মাত্র আড়াই দিনের অভিজ্ঞতায় বোঝা গেল, একটু অবকাশ মনকে চাঙা করে তুলতে পারে।
গাছ কাটা, কংক্রিটের শহর নির্মাণের কথা আমলে নিয়েও এ কথা বলতে হয়, প্রকৃতি আমাদের উজাড় করে দিয়েছে। বঙ্গোপসাগর যেমন, তেমনি বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন অংশ, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকা, নেত্রকোনার বিরিশিরি, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পুরাকীর্তিসংলগ্ন প্রকৃতি—সবটা নিয়েই বলা যায়, এ দেশটি নয়নাভিরাম। শহরের কোলাহল ছাড়িয়ে দুই পাশে বৃক্ষশোভিত রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকলে ঠিকই মনে হবে, ‘এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি...’।
সমুদ্রসৈকতে গিয়ে কয়েকটি দৃশ্য ছবি হয়ে গেঁথে থাকল মনে। তার একটি হচ্ছে টি-শার্ট ও টাইট প্যান্ট পরনে তরুণীদের সাহসী পদচারণ, আপাদমস্তক বোরকায় আচ্ছাদিত তরুণীর সবার অলক্ষ্যে সঙ্গীকে চুম্বন, সৈকত এলাকার নিরাপত্তা। তিনটি বিষয়কে এক করলাম এ কারণে যে, আমার লেখাটি পরবর্তীকালে এ পথেই এগোবে।
দুই.
বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গত শতাব্দীর ষাটের দশকে যে স্বাধিকার আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তাতে আমাদের সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের একটা রূপরেখা ছিল। ‘ফিরে চল মাটির টানে’ শব্দগুলোকে মনে ধারণ করে সে সময় বাঙালি উৎসে ফেরার চেষ্টা করেছিল। তারপর সেই স্বাধিকারের পথ বেয়েই এল স্বাধীনতা এবং এর পর থেকে আমরা চারপাশে শুনতে পাচ্ছি, ‘স্বাধীনতার ফসল’ ঘরে তুলতে হবে। সংকটের শুরু এখানেই।
বলা হলো ‘স্বাধীনতার ফসল’। অথচ কবে জমি প্রস্তুত করা হলো, কবে বীজ বোনা হলো, কবে ফসল উঠল, তা রয়ে গেল অস্পষ্ট। বীজ বোনার পর্যায়েই তো জাতির জনককে হত্যা করা হলো। তারপর জিয়াউর রহমানের হাত ধরে দেশটা পিছিয়ে যেতে থাকল। যে অর্জনগুলো দৃশ্যমান হচ্ছিল, সেগুলো সরিয়ে দিয়ে আবার ধর্মীয় জোশের জন্ম দেওয়া হলো। অর্থাৎ যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ—ধর্মের নামে মানুষকে দমিয়ে রাখা, তারই ‘মিনি’ রূপ ফিরে এল দেশে। অসাম্প্রদায়িকতা যাই যাই করতে থাকল জীবন থেকে।
যতই কণ্ঠ জোরে ছাড়া হোক না কেন, বাঙালির কণ্ঠে অসাম্প্রদায়িকতার প্রত্যয় এখন আর মানায় না। তাই সুমনের ‘হাল ছেড়ো না, বন্ধু’ শব্দগুলোকে বড় দূরের কোনো দ্বীপ বলে মনে হয়। ভেতরে-ভেতরে বাঙালি সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠেছে। এমনকি যে রাজনৈতিক দলের হাত ধরে স্বাধীনতা এসেছিল, সেই আওয়ামী লীগের নেতাদের অনেকেরই চৈতন্যে অসাম্প্রদায়িকতা দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে। ফলে বাংলাদেশটা এগিয়ে যেতে থাকল দুদিকে—পশ্চিমাদের সর্বাঙ্গীণ অনুকরণের দিকে আর ধর্মীয় জোশের পুনরুজ্জীবনের দিকে, বাদ পড়ে গেল আত্মপরিচয়। সেটা খুইয়ে ফেলার প্রাণান্ত চেষ্টা বোধকরি সফল হতে চলেছে। আর তাই ভণ্ডামি হয়ে উঠেছে জাতির সবচেয়ে দৃশ্যমান পোস্টার।
তিন.
হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের আমল নিয়ে কত মুখরোচক কথাই না ঘুরে বেড়ায়। তিনি শুধু মূর্তিমান স্বৈরাচারই ছিলেন না, ছিলেন নারীলোভী, বকধার্মিক। এ কথা অনেকেরই মনে পড়ে যাবে, মসজিদে মসজিদে গিয়ে তিনি বলতেন, ‘কাল রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি, আপনাদের মসজিদে আমি নামাজ পড়ছি।’ ডাহা মিথ্যে! এরশাদ ওই মসজিদে পদার্পণ করার কয়েক দিন আগে থেকেই গোয়েন্দা-গুপ্তচরদের আনাগোনা শুরু হয়ে যেত। সবাই বুঝতে পারত, কিছু একটা ঘটতে চলেছে।
সেই এরশাদ, যিনি ধর্ম নিয়ে এই ভণ্ডামি করেছেন, যিনি নারীদের সঙ্গে অবমাননাকর ব্যবহার করেছেন, তিনিই কিনা রাষ্ট্রীয় ধর্মের পক্ষে ওকালতি করে সংবিধান পরিবর্তন করে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করে ফেললেন! এমন একজন রাষ্ট্রধর্ম বসিয়ে দিল সংবিধানে এবং তা নিয়ে বাহ্বা দেওয়া কি মানায়?
সংবিধানে লেখা আছে, ‘রাষ্ট্রধর্ম, ২(ক), প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সম-অধিকার নিশ্চিত করিবেন।’
তার মানে সমমর্যাদা ও সম-অধিকার আছে সবার। সে ক্ষেত্রে আলাদাভাবে রাষ্ট্রধর্মের কী মানে থাকতে পারে? বিষয়টি নিয়ে এখনকার তরুণেরা কী ভাবছে, তা জানার উপায় কি আছে?
চার.
বলা হয়, সবই অনিত্য। ইউরোপীয় পোশাক শরীরে জড়ালেই কেউ ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে যায় না। তেমনি আরবের পোশাকও মানুষকে আরবীয় সংস্কৃতির মুখপাত্র করে তোলে না। কারও পোশাক নিয়ে প্রশ্ন তোলা আমার উদ্দেশ্য নয়। পোশাক নিয়ে একটু পড়াশোনা করলেই বোঝা যাবে, আবহাওয়ার কারণেই পৃথিবীর একেক জায়গায় একেক রকম পোশাক পরা হয়। বছরের পর বছর ধরে মানুষের অভিজ্ঞতা তার সংস্কৃতির স্রোতোধারায় প্রবাহিত হয়। সেভাবেই সে বেছে নেয় পোশাক-আশাক, খাবার, আচরণের ধরন। এক সংস্কৃতির ধারায় এসে মিশে যায় আরেক সংস্কৃতি, কিছুকাল অস্বস্তির পর সেটাও একসময় হয়ে ওঠে সংস্কৃতির অঙ্গ। যা টেকার, তা টিকে থাকে; যা যাওয়ার, তা চলে যায়। এটাই নিয়ম। কিন্তু কোনো সংস্কৃতিকে জোর করে নিজের সংস্কৃতিতে টেনে আনা হলে প্রশ্ন ওঠে। বোঝা যায়, এই সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।
ইউরোপ-আমেরিকায় সমুদ্রস্নানের সময় স্বল্পপোশাক পরিধানের রয়েছে বৈজ্ঞানিক কারণ, তেমনি মধ্যপ্রাচ্যে পা থেকে মাথা পর্যন্ত পোশাক পরারও বৈজ্ঞানিক কারণ রয়েছে। আর এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম হয়েছে সাধারণ মানুষের হাজার বছরের অভিজ্ঞতা থেকে। সাধারণ মানুষই তা আবিষ্কার করেছে।
শুরুতে যে কথা বলেছিলাম, তাতে ফিরে যাই। আরবীয় পোশাকের যে তরুণীকে দেখলাম, বোরকা থেকে মুখ বের করে চুম্বন করছেন, তিনি আসলে বয়সের ধর্মকেই সবচেয়ে বড় ধর্ম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন ঠিক সে সময়টিতে। তখন তাঁর আশপাশের সবকিছু অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, তিনি বেঁচে ছিলেন তাঁর যৌবনের ওপর নির্ভর করে। ধর্মীয় অনুশাসনের তোয়াক্কা তিনি করেননি। তেমনি ইউরোপীয় পোশাক পরে যে মেয়েটি মুক্তভাবে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন চোখের সামনে, তিনিও কিন্তু বেছে নিয়েছিলেন যৌবনের শক্তিকে। এতগুলো পুরুষ-চক্ষুকে তিনি থোড়াই কেয়ার করেছেন।
কোন কাজটা ঠিক আর কোনটা নয়, সে বিচারের কথা ভাবছি না একটুও। বলতে চাইছি কেবল, চাপিয়ে দেওয়া কোনো কিছুই সমাজে টিকে থাকে না। কিছুটা সময় হয়তো তা শাসন করে বোধের জায়গাটা, তারপর আবার সবকিছু ঠিক জায়গায় ফিরে আসে। আবার কখনো নতুন করে ওঠে আলোড়ন, আবার তা স্তিমিত হয়, এভাবেই তো এগিয়ে চলে সময়।
সংস্কৃতির এই দেওয়া-নেওয়া কী চোখে দেখছে তরুণেরা তার ওপরও আমাদের এগিয়ে চলা অনেকটা নির্ভরশীল।
পাঁচ.
তারুণ্য চলে গতির ওপর নির্ভর করে। অদম্য গতিতে সে ছারখার করে দিতে চায় প্রচলিত সমাজব্যবস্থা। একটু বয়স হলে তার সে গতিতে আসে ভাটার টান। তখন সে ধীরে ধীরে নিজের চারপাশে একটা বলয় তৈরি করে নেয়। যেকোনো নতুনকে বরণ করে নেওয়ার মানসিকতা হারায়। তবে ভাবনার জগতে সে এগিয়ে চলে। বলা হয়ে থাকে, তরুণের গতি আর বর্ষীয়ানের জ্ঞানের সমন্বয়েই সমাজ এগিয়ে চলে স্বাস্থ্যকর পথে।
এ বিষয়েই আমি কয়েকটি প্রশ্ন রেখে যাব। আমাদের তারুণ্যে আশাবাদ কি দেখা যাচ্ছে? সামগ্রিকভাবে একটা ফাঁপা ‘জোর যার মুল্লুক তার’ সমাজ যে ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিচ্ছে আমাদের, সেটা কি বুঝতে পারছি আমরা? করপোরেটের ভূত যে অধস্তনদের একেবারে চামচায় পরিণত করছে, সেটা কি দেখতে পাচ্ছি আমরা? তেলবাজিই যে এখন সংস্কৃতির একটি অপরিত্যাজ্য মূল উপাদানে পরিণত হয়েছে, সে কথা স্বীকার করে নিতে দ্বিধা কেন আমাদের? ধর্ম নয়, ধর্ম প্রদর্শন ও ধর্মব্যবসা যখন গিলে ফেলছে আমাদের, তখন তারুণ্য নীরব কেন কিংবা নিজে থেকে এ বিষয়ে পড়াশোনা না করে ওই ধর্মব্যবসার প্রতি নিঃশর্ত সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে কেন? সংস্কৃতির নামে ঘটতে থাকা অনাচারগুলো কি নজরে পড়ছে আমাদের? লোকসংস্কৃতিকে বিদায় করার সব উপাদান জড়ো করা হয়েছে শহরে-গ্রামে-বন্দরে, সেটা কি বুঝতে পারছি?
আরও অনেক প্রশ্ন আছে, আগে এই প্রশ্নগুলোর জবাব নিজের কাছে খুঁজুন।
প্রাকৃতিক নয়নাভিরাম দেশটির মানুষের মনে আজ গভীর অসুখ। সেই অসুখ সারানো খুব সহজ কথা নয়। সে বাঙালি না মুসলমান না ইংরেজ, সে প্রশ্নেরই সমাধান সে করতে পারে না।
সে নারী-পুরুষ সমতায় বিশ্বাস করে কি না, সে প্রশ্নের উত্তরও তার জানা নেই। সে নিজের দেশকে ভালোবাসে কি না, তা নিয়ে মেকি উত্তর তার তৈরি আছে, কিন্তু আসলে তার মন ইউরোপে, আরব দেশে না কোথায় আটকে আছে, সেটা সে জানে না।
ভাবনার জগতে বৈপরীত্য এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, অভিন্নহৃদয় হয়ে, একই রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে সবাই গর্বভরে নিজের পরিচয় দেব, সে আশার সলতে অনেক কষ্ট করে জ্বালিয়ে রাখতে হচ্ছে।

আজকের পত্রিকায় ১৩ আগস্ট একটি সংবাদ পড়ে এবং এ বিষয়ে টিভি চ্যানেলের সংবাদ দেখে মর্মাহত হয়েছিলাম। এভাবে কেউ কোনো দেশের একটি প্রাকৃতিক সম্পদের বিনাশ ঘটাতে পারে? আজকের পত্রিকায় ‘সাদাপাথরের সৌন্দর্য হারানোর কান্না’ শিরোনামের সে প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, গত বছরের ৫ আগস্ট সরকার পরিবর্তনের পর থেকেই শুরু হয় পাথর
১১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা এখন শতাধিক। প্রতিবছর এখানে হাজারো গবেষণা হয়, যার বড় অংশের উদ্দেশ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশ। নিঃসন্দেহে বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষকের মর্যাদা এবং বৈশ্বিক পরিচিতি বৃদ্ধির অন্যতম মাধ্যম।
১১ ঘণ্টা আগে
খবরটি খুবই লজ্জার। বাংলাদেশ বিমানের একজন কেবিন ক্রু সোনা পাচারের দায়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন। ৪ আগস্ট বিকেলে সৌদি আরবের রিয়াদ থেকে বিজি-৩৪০ ফ্লাইটে ঢাকায় অবতরণ করার পর গ্রিন চ্যানেল অতিক্রমের সময় এই কেবিন ক্রুর গতিবিধিতে সন্দেহ জাগে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের। স্ক্যানিং মেশিনের নিচে তিনি পা দিয়ে কিছু লুকানোর
১১ ঘণ্টা আগে
সম্প্রতি ঢাকায় বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সম্মেলনে জাপানি বিনিয়োগ পরামর্শক তাকাও হিরোসে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও রাজনীতির জন্য অশনিসংকেত দিয়েছেন। তাঁর স্পষ্ট ভাষ্য, তাঁরা দ্রুত মুনাফার খোঁজে থাকা আগ্রাসী বিনিয়োগকারী, খামখেয়ালিও।
১ দিন আগে