ড. মইনুল ইসলাম
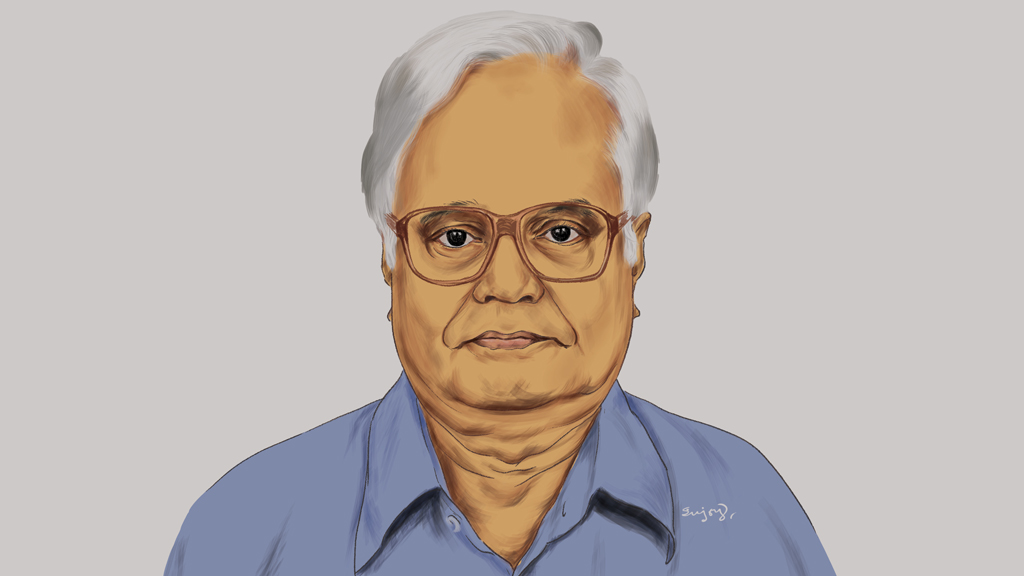
বাংলাদেশ সরকারকে আরেকটি ব্যাপারে সাবধান হতে হবে। চীনের ২১ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার সম্ভাব্য ঋণের লোভে যেন অপ্রয়োজনীয় কিংবা কম প্রয়োজনীয় প্রকল্পে আমরা বিনিয়োগ না করি।
দ্য বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই) গণচীনের সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে সাড়াজাগানো আঞ্চলিক সহযোগিতা গড়ে তোলার উদ্যোগ, যার মাধ্যমে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও ওশেনিয়ার ৬০টি দেশের যোগাযোগব্যবস্থা, ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং শিল্পায়নে গণচীনের প্রভূত বিনিয়োগ অর্থায়ন সহযোগিতায় বিপ্লবী পরিবর্তন আনবে। এটাকে ‘ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড’ (OBOR) বলা হয়, যার মধ্যে একটি ডাইমেনশন হলো স্থলবেষ্টিত দেশগুলোর মহাসড়ক, রেলযোগাযোগ ও বিমান যোগাযোগ উন্নয়নের মাধ্যমে ‘সিল্ক রোড ইকোনমিক বেল্ট’ গড়ে তোলা আর অপরটি হলো সমুদ্র-তীরবর্তী দেশগুলোয় গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের মাধ্যমে ‘একুশ শতকের মেরিটাইম সিল্ক রোড’ উন্নয়ন কৌশল। এর আগে গণচীন ২০১৪ সালে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকার যৌথ মালিকানায় এসব দেশের ইংরেজি নামের আদ্যাক্ষর নিয়ে গঠিত ব্রিক্স (BRICS) ব্যাংক স্থাপন করেছে, যেটাকে এখন ‘নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক’ নামে আখ্যায়িত করা হচ্ছে।
এরপর, গণচীন আরও বিস্তৃত পরিসরে ‘এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবি) স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে, যেখানে বিশ্বের অনেক উন্নত দেশও পার্টনার হিসেবে অংশগ্রহণ করছে।
এতদসত্ত্বেও যখন ২০১৬ সালে গণচীন অনেক বেশি উচ্চাভিলাষী বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই) গ্রহণের ঘোষণা দিল, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ভারত এই উদ্যোগকে বিশ্বব্যাপী চীনের আধিপত্য বিস্তারের প্রত্যক্ষ প্রয়াস হিসেবে চিহ্নিত করে এর বিরুদ্ধে সরাসরি অবস্থান গ্রহণ করেছে। অপরদিকে, রাশিয়া ও ইতালি বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বিআরআই এখন বৈশ্বিক ভূরাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের পাশা খেলায় পরিণত হয়েছে বলা যায়।
২০১৬ সালে বিআরআই ঘোষণার এক দশক আগেই বাংলাদেশ-চীন-ভারত-মিয়ানমার (বিসিআইএম) ইকোনমিক করিডর গঠনের কাজ শুরু হয়েছিল ‘কুনমিং ইনিশিয়েটিভ’-এর মাধ্যমে। ভারতের তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার বিসিআইএম ইকোনমিক করিডরের কার্যক্রমে প্রায় এক দশক ধরে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছে। কিন্তু ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার ভারতে ক্ষমতাসীন হয়েই এই চুক্তি বাস্তবায়ন বন্ধ করে দেয়। ফলে এখন ‘কুনমিং ইনিশিয়েটিভ’ জীবন্মৃত অবস্থায় ঝুলে গেছে। ২০১৪ সালে ভারতের সরাসরি চাপের কারণেই কক্সবাজারের সোনাদিয়ায় গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণে চীনকে অর্থায়ন করার আমন্ত্রণ জানিয়েও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চীন সফরের সময় বাংলাদেশ শেষ মুহূর্তে ‘মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং’ স্বাক্ষর বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিল। এর ফলে সোনাদিয়ায় গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ প্রকল্পটি পরিত্যক্ত হয়ে গেছে।
কিন্তু গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ এখন বাংলাদেশের জন্য ফরজ হয়ে পড়েছে। কারণ, চট্টগ্রাম বন্দর এখন প্রধানত ‘লাইটারেজ পোর্টে’ পরিণত হয়েছে। নয় মিটারের বেশি ড্রাফটের কোনো জাহাজ এখন চট্টগ্রাম বন্দরের জেটিতে ঢুকতে পারে না। বড় জাহাজগুলোকে হয় আউটার এনকারেজে নোঙর ফেলতে হয়, নয়তো কুতুবদিয়ার কাছাকাছি নোঙর ফেলে ছোট ছোট লাইটারেজ ভ্যাসেলে মালপত্র নামিয়ে দিতে হয়। রপ্তানির বেলায়ও লাইটারেজ ভ্যাসেলের সহায়তা লাগে। এমনকি, কিছু কিছু মাদারশিপ সিঙ্গাপুরে কিংবা কলম্বোয় কার্গো নামিয়ে দিয়ে চলে যায়, আমরা ছোট ছোট কনটেইনার ভ্যাসেলে ওই কার্গো চট্টগ্রাম বন্দরে নিয়ে আসি। রপ্তানির বেলায়ও অনেক সময় এভাবে সিঙ্গাপুর বা কলম্বোর সহায়তা নিতে হচ্ছে। এহেন লাইটারেজের কারণে এখন চট্টগ্রাম একটি ব্যয়বহুল বন্দরে পরিণত হয়েছে।
আরেকটি সীমাবদ্ধতা হলো, কর্ণফুলী নদীর প্রশস্ততা বেশি না হওয়ায় ১৯০ মিটারের বেশি দৈর্ঘ্যের জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরের জেটিগুলোতে ঢুকতে পারে না ঘোরানোর জন্য যথেষ্ট জায়গার অভাবে। অতএব, বিকল্প গভীর সমুদ্রবন্দর হিসেবে এখন সোনাদিয়া দ্বীপের কিছুটা দূরে মহেশখালীর মাতারবাড়ীতে জাপানের সহায়তায় একটি গভীর সমুদ্রবন্দর গড়ে তোলা হচ্ছে, যে কাজ ২০২৫ সালে সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। দুটো কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের কয়লা আমদানির জন্য মাতারবাড়ীর বন্দরটি অরিজিনালি গড়ে তোলার পরিকল্পনা গৃহীত হলেও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই বন্দরের ১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ চ্যানেলটির গভীরতা বাড়িয়ে ১৮ মিটারে উন্নীত করা এবং প্রশস্ততাও যথাযোগ্যভাবে বাড়ানোর মাধ্যমে এটিকে গভীর সমুদ্রবন্দর হিসেবে গড়ে তোলা হবে। হয়তো মাতারবাড়ীতে আমরা ভাগ্যক্রমে সোনাদিয়ার একটি ভালো বিকল্প পেয়ে যাব। অবশ্য, সোনাদিয়ায় সাগরের তলদেশে যে একটি ‘গভীর প্রাকৃতিক খাঁড়ি’ আছে আল্লাহর এই নেয়ামত থেকে ভারতের কারণে বাংলাদেশের জনগণ বঞ্চিত হয়ে গেল। ওই খাঁড়ি পেলে সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দরের চ্যানেলের গভীরতা ১৮ মিটার বা তারও বেশি প্রাকৃতিকভাবেই পাওয়া যেত, ব্যয়বহুল খননের মাধ্যমে নাব্যতা রক্ষার প্রয়োজন পড়ত না।
চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় বঙ্গোপসাগরের তীরে নির্মীয়মাণ বে টার্মিনালও চট্টগ্রাম বন্দরের সীমাবদ্ধতা দূর করতে যাচ্ছে, যেখানে প্রায় ১৩ মিটার ড্রাফটের জাহাজ ভিড়তে পারবে। বে টার্মিনাল নির্মাণ সম্পন্ন হলে বর্তমান চট্টগ্রাম বন্দরের জেটিতে কর্ণফুলী নদীর প্রশস্ততার সীমাবদ্ধতার কারণে যে ১৯০ মিটারের বেশি দৈর্ঘ্যের জাহাজ ভিড়তে পারে না, সেই প্রতিবন্ধকতাও আর থাকবে না। বলা হচ্ছে, বে টার্মিনালের শিপ হ্যান্ডলিং ক্যাপাসিটি বর্তমান চট্টগ্রাম বন্দরের চার গুণে গিয়ে দাঁড়াবে।
২০১৬ সালে বাংলাদেশ বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওই বছর চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের বাংলাদেশ সফরের সময় চীন বাংলাদেশকে ২১ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারের প্রকল্প ঋণ প্রদানের অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করেছে। ২০১৯ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চীন সফরের সময় কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে দুই দেশ। কিন্তু মোদি সরকারের আমলে বাংলাদেশ যদি ভারতকে চটিয়ে বিআরআইয়ের ব্যাপারে বেশি আগ্রহ দেখায়, তাহলে ভারত বাংলাদেশকে বিভিন্নভাবে বিপদে ফেলতে চাইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানও যেহেতু এই ভূরাজনৈতিক খেলায় ভারতের দোসর থাকবে, সে জন্য বাংলাদেশকে খুবই সাবধানে পা ফেলতে হবে চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর ব্যাপারে। মনে রাখতে হবে, বিংশ শতাব্দীজুড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই ছিল বিশ্বের একাধিপতি সুপারপাওয়ার। এখন গণচীন অর্থনৈতিক সুপারপাওয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যাতে কোনোভাবেই বিশ্বের দ্বিতীয় সামরিক সুপারপাওয়ার হয়ে উঠতে না পারে, সে জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বাত্মক প্রয়াস চালাচ্ছে। তাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে জোটবদ্ধ থাকবে জাপান ও ভারত। কারণ, ভারতের সঙ্গে চীনের শুধু সীমান্ত-বিরোধ নয়, আঞ্চলিক সুপারপাওয়ার হওয়ার প্রতিযোগিতাও চালু রয়েছে। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর চীন-ভারতের সম্পর্ক আবার চরম বৈরিতায় পর্যবসিত হয়েছে। জাপানও কোনোমতেই চাইবে না প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীন তাদের ওপর টেক্কা দেওয়ার অবস্থানে চলে যাক; বিশেষত চীনের সঙ্গে তাদের সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ দীর্ঘদিনের।
বাংলাদেশ সরকারকে আরেকটি ব্যাপারে সাবধান হতে হবে। চীনের ২১ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার সম্ভাব্য ঋণের লোভে যেন অপ্রয়োজনীয় কিংবা কম প্রয়োজনীয় প্রকল্পে আমরা বিনিয়োগ না করি। সাম্প্রতিক কালে ‘চীনা ঋণের ফাঁদ’-সম্পর্কীয় প্রচার-প্রোপাগান্ডা তুঙ্গে উঠেছে। পাকিস্তানের চীন-পাকিস্তান ইকোনমিক করিডর (সিপেক) ও গোয়াদার গভীর সমুদ্রবন্দর, শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটা গভীর সমুদ্রবন্দর ও কলম্বো চায়নিজ সিটি, মালদ্বীপের আন্তদ্বীপ যোগাযোগ সেতু, মিয়ানমারের কিয়াকফ্যু গভীর সমুদ্রবন্দর ও তেল-গ্যাস পাইপলাইন—এগুলো চীনা ঋণের ফাঁদের উদাহরণ হিসেবে ইদানীং প্রোপাগান্ডা-যুদ্ধে ব্যবহৃত হচ্ছে।
বিশেষত, বন্দর ব্যবহার বাড়াতে ব্যর্থ হয়ে শ্রীলঙ্কা হাম্বানটোটা বন্দরকে চীনের কাছে ৯৯ বছরের জন্য ইজারা দিতে বাধ্য হওয়ায় ব্যাপারটিকে ‘ফাঁদ’ হিসেবে সহজেই ব্যবহার করা যাচ্ছে। পাকিস্তানের গোয়াদার বন্দরের ব্যবহারও তেমন বাড়ানো যাচ্ছে না এবং সিপেকের সুবিধা নিয়ে চীন থেকে গোয়াদার বন্দর পর্যন্ত নির্মিত দীর্ঘ মহাসড়কের আশপাশে শিল্পায়নের মহাযজ্ঞ শুরু হয়ে যাবে বলে যে আশাবাদ পাকিস্তানে সৃষ্টি হয়েছিল, তারও কোনো হদিস মিলছে না।
লাওস, জিবুতি, মঙ্গোলিয়া, মন্টেনেগ্রো, কিরগিজস্তান এবং তাজিকিস্তানও তাদের নানা প্রকল্পের কারণে চীনা ঋণের ফাঁদে আটকে গেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আমার বিবেচনায়, বাংলাদেশের নিচে উল্লিখিত প্রকল্পগুলো খুব প্রয়োজনীয় নয়: দ্বিতীয় স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ, প্রস্তাবিত দ্বিতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং প্রস্তাবিত ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার বুলেট ট্রেন প্রকল্প।
লেখক: সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, একুশে পদকপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ ও অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
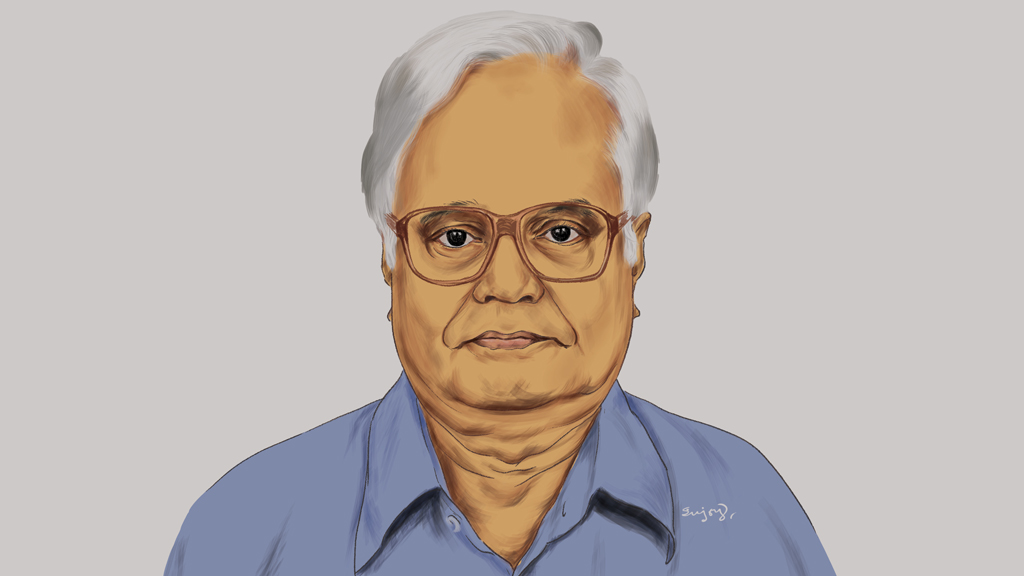
বাংলাদেশ সরকারকে আরেকটি ব্যাপারে সাবধান হতে হবে। চীনের ২১ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার সম্ভাব্য ঋণের লোভে যেন অপ্রয়োজনীয় কিংবা কম প্রয়োজনীয় প্রকল্পে আমরা বিনিয়োগ না করি।
দ্য বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই) গণচীনের সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে সাড়াজাগানো আঞ্চলিক সহযোগিতা গড়ে তোলার উদ্যোগ, যার মাধ্যমে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও ওশেনিয়ার ৬০টি দেশের যোগাযোগব্যবস্থা, ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং শিল্পায়নে গণচীনের প্রভূত বিনিয়োগ অর্থায়ন সহযোগিতায় বিপ্লবী পরিবর্তন আনবে। এটাকে ‘ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড’ (OBOR) বলা হয়, যার মধ্যে একটি ডাইমেনশন হলো স্থলবেষ্টিত দেশগুলোর মহাসড়ক, রেলযোগাযোগ ও বিমান যোগাযোগ উন্নয়নের মাধ্যমে ‘সিল্ক রোড ইকোনমিক বেল্ট’ গড়ে তোলা আর অপরটি হলো সমুদ্র-তীরবর্তী দেশগুলোয় গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের মাধ্যমে ‘একুশ শতকের মেরিটাইম সিল্ক রোড’ উন্নয়ন কৌশল। এর আগে গণচীন ২০১৪ সালে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকার যৌথ মালিকানায় এসব দেশের ইংরেজি নামের আদ্যাক্ষর নিয়ে গঠিত ব্রিক্স (BRICS) ব্যাংক স্থাপন করেছে, যেটাকে এখন ‘নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক’ নামে আখ্যায়িত করা হচ্ছে।
এরপর, গণচীন আরও বিস্তৃত পরিসরে ‘এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবি) স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে, যেখানে বিশ্বের অনেক উন্নত দেশও পার্টনার হিসেবে অংশগ্রহণ করছে।
এতদসত্ত্বেও যখন ২০১৬ সালে গণচীন অনেক বেশি উচ্চাভিলাষী বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই) গ্রহণের ঘোষণা দিল, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ভারত এই উদ্যোগকে বিশ্বব্যাপী চীনের আধিপত্য বিস্তারের প্রত্যক্ষ প্রয়াস হিসেবে চিহ্নিত করে এর বিরুদ্ধে সরাসরি অবস্থান গ্রহণ করেছে। অপরদিকে, রাশিয়া ও ইতালি বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বিআরআই এখন বৈশ্বিক ভূরাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের পাশা খেলায় পরিণত হয়েছে বলা যায়।
২০১৬ সালে বিআরআই ঘোষণার এক দশক আগেই বাংলাদেশ-চীন-ভারত-মিয়ানমার (বিসিআইএম) ইকোনমিক করিডর গঠনের কাজ শুরু হয়েছিল ‘কুনমিং ইনিশিয়েটিভ’-এর মাধ্যমে। ভারতের তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার বিসিআইএম ইকোনমিক করিডরের কার্যক্রমে প্রায় এক দশক ধরে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছে। কিন্তু ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার ভারতে ক্ষমতাসীন হয়েই এই চুক্তি বাস্তবায়ন বন্ধ করে দেয়। ফলে এখন ‘কুনমিং ইনিশিয়েটিভ’ জীবন্মৃত অবস্থায় ঝুলে গেছে। ২০১৪ সালে ভারতের সরাসরি চাপের কারণেই কক্সবাজারের সোনাদিয়ায় গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণে চীনকে অর্থায়ন করার আমন্ত্রণ জানিয়েও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চীন সফরের সময় বাংলাদেশ শেষ মুহূর্তে ‘মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং’ স্বাক্ষর বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিল। এর ফলে সোনাদিয়ায় গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ প্রকল্পটি পরিত্যক্ত হয়ে গেছে।
কিন্তু গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ এখন বাংলাদেশের জন্য ফরজ হয়ে পড়েছে। কারণ, চট্টগ্রাম বন্দর এখন প্রধানত ‘লাইটারেজ পোর্টে’ পরিণত হয়েছে। নয় মিটারের বেশি ড্রাফটের কোনো জাহাজ এখন চট্টগ্রাম বন্দরের জেটিতে ঢুকতে পারে না। বড় জাহাজগুলোকে হয় আউটার এনকারেজে নোঙর ফেলতে হয়, নয়তো কুতুবদিয়ার কাছাকাছি নোঙর ফেলে ছোট ছোট লাইটারেজ ভ্যাসেলে মালপত্র নামিয়ে দিতে হয়। রপ্তানির বেলায়ও লাইটারেজ ভ্যাসেলের সহায়তা লাগে। এমনকি, কিছু কিছু মাদারশিপ সিঙ্গাপুরে কিংবা কলম্বোয় কার্গো নামিয়ে দিয়ে চলে যায়, আমরা ছোট ছোট কনটেইনার ভ্যাসেলে ওই কার্গো চট্টগ্রাম বন্দরে নিয়ে আসি। রপ্তানির বেলায়ও অনেক সময় এভাবে সিঙ্গাপুর বা কলম্বোর সহায়তা নিতে হচ্ছে। এহেন লাইটারেজের কারণে এখন চট্টগ্রাম একটি ব্যয়বহুল বন্দরে পরিণত হয়েছে।
আরেকটি সীমাবদ্ধতা হলো, কর্ণফুলী নদীর প্রশস্ততা বেশি না হওয়ায় ১৯০ মিটারের বেশি দৈর্ঘ্যের জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরের জেটিগুলোতে ঢুকতে পারে না ঘোরানোর জন্য যথেষ্ট জায়গার অভাবে। অতএব, বিকল্প গভীর সমুদ্রবন্দর হিসেবে এখন সোনাদিয়া দ্বীপের কিছুটা দূরে মহেশখালীর মাতারবাড়ীতে জাপানের সহায়তায় একটি গভীর সমুদ্রবন্দর গড়ে তোলা হচ্ছে, যে কাজ ২০২৫ সালে সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। দুটো কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের কয়লা আমদানির জন্য মাতারবাড়ীর বন্দরটি অরিজিনালি গড়ে তোলার পরিকল্পনা গৃহীত হলেও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই বন্দরের ১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ চ্যানেলটির গভীরতা বাড়িয়ে ১৮ মিটারে উন্নীত করা এবং প্রশস্ততাও যথাযোগ্যভাবে বাড়ানোর মাধ্যমে এটিকে গভীর সমুদ্রবন্দর হিসেবে গড়ে তোলা হবে। হয়তো মাতারবাড়ীতে আমরা ভাগ্যক্রমে সোনাদিয়ার একটি ভালো বিকল্প পেয়ে যাব। অবশ্য, সোনাদিয়ায় সাগরের তলদেশে যে একটি ‘গভীর প্রাকৃতিক খাঁড়ি’ আছে আল্লাহর এই নেয়ামত থেকে ভারতের কারণে বাংলাদেশের জনগণ বঞ্চিত হয়ে গেল। ওই খাঁড়ি পেলে সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দরের চ্যানেলের গভীরতা ১৮ মিটার বা তারও বেশি প্রাকৃতিকভাবেই পাওয়া যেত, ব্যয়বহুল খননের মাধ্যমে নাব্যতা রক্ষার প্রয়োজন পড়ত না।
চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় বঙ্গোপসাগরের তীরে নির্মীয়মাণ বে টার্মিনালও চট্টগ্রাম বন্দরের সীমাবদ্ধতা দূর করতে যাচ্ছে, যেখানে প্রায় ১৩ মিটার ড্রাফটের জাহাজ ভিড়তে পারবে। বে টার্মিনাল নির্মাণ সম্পন্ন হলে বর্তমান চট্টগ্রাম বন্দরের জেটিতে কর্ণফুলী নদীর প্রশস্ততার সীমাবদ্ধতার কারণে যে ১৯০ মিটারের বেশি দৈর্ঘ্যের জাহাজ ভিড়তে পারে না, সেই প্রতিবন্ধকতাও আর থাকবে না। বলা হচ্ছে, বে টার্মিনালের শিপ হ্যান্ডলিং ক্যাপাসিটি বর্তমান চট্টগ্রাম বন্দরের চার গুণে গিয়ে দাঁড়াবে।
২০১৬ সালে বাংলাদেশ বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওই বছর চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের বাংলাদেশ সফরের সময় চীন বাংলাদেশকে ২১ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারের প্রকল্প ঋণ প্রদানের অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করেছে। ২০১৯ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চীন সফরের সময় কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে দুই দেশ। কিন্তু মোদি সরকারের আমলে বাংলাদেশ যদি ভারতকে চটিয়ে বিআরআইয়ের ব্যাপারে বেশি আগ্রহ দেখায়, তাহলে ভারত বাংলাদেশকে বিভিন্নভাবে বিপদে ফেলতে চাইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানও যেহেতু এই ভূরাজনৈতিক খেলায় ভারতের দোসর থাকবে, সে জন্য বাংলাদেশকে খুবই সাবধানে পা ফেলতে হবে চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর ব্যাপারে। মনে রাখতে হবে, বিংশ শতাব্দীজুড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই ছিল বিশ্বের একাধিপতি সুপারপাওয়ার। এখন গণচীন অর্থনৈতিক সুপারপাওয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যাতে কোনোভাবেই বিশ্বের দ্বিতীয় সামরিক সুপারপাওয়ার হয়ে উঠতে না পারে, সে জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বাত্মক প্রয়াস চালাচ্ছে। তাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে জোটবদ্ধ থাকবে জাপান ও ভারত। কারণ, ভারতের সঙ্গে চীনের শুধু সীমান্ত-বিরোধ নয়, আঞ্চলিক সুপারপাওয়ার হওয়ার প্রতিযোগিতাও চালু রয়েছে। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর চীন-ভারতের সম্পর্ক আবার চরম বৈরিতায় পর্যবসিত হয়েছে। জাপানও কোনোমতেই চাইবে না প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীন তাদের ওপর টেক্কা দেওয়ার অবস্থানে চলে যাক; বিশেষত চীনের সঙ্গে তাদের সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ দীর্ঘদিনের।
বাংলাদেশ সরকারকে আরেকটি ব্যাপারে সাবধান হতে হবে। চীনের ২১ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার সম্ভাব্য ঋণের লোভে যেন অপ্রয়োজনীয় কিংবা কম প্রয়োজনীয় প্রকল্পে আমরা বিনিয়োগ না করি। সাম্প্রতিক কালে ‘চীনা ঋণের ফাঁদ’-সম্পর্কীয় প্রচার-প্রোপাগান্ডা তুঙ্গে উঠেছে। পাকিস্তানের চীন-পাকিস্তান ইকোনমিক করিডর (সিপেক) ও গোয়াদার গভীর সমুদ্রবন্দর, শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটা গভীর সমুদ্রবন্দর ও কলম্বো চায়নিজ সিটি, মালদ্বীপের আন্তদ্বীপ যোগাযোগ সেতু, মিয়ানমারের কিয়াকফ্যু গভীর সমুদ্রবন্দর ও তেল-গ্যাস পাইপলাইন—এগুলো চীনা ঋণের ফাঁদের উদাহরণ হিসেবে ইদানীং প্রোপাগান্ডা-যুদ্ধে ব্যবহৃত হচ্ছে।
বিশেষত, বন্দর ব্যবহার বাড়াতে ব্যর্থ হয়ে শ্রীলঙ্কা হাম্বানটোটা বন্দরকে চীনের কাছে ৯৯ বছরের জন্য ইজারা দিতে বাধ্য হওয়ায় ব্যাপারটিকে ‘ফাঁদ’ হিসেবে সহজেই ব্যবহার করা যাচ্ছে। পাকিস্তানের গোয়াদার বন্দরের ব্যবহারও তেমন বাড়ানো যাচ্ছে না এবং সিপেকের সুবিধা নিয়ে চীন থেকে গোয়াদার বন্দর পর্যন্ত নির্মিত দীর্ঘ মহাসড়কের আশপাশে শিল্পায়নের মহাযজ্ঞ শুরু হয়ে যাবে বলে যে আশাবাদ পাকিস্তানে সৃষ্টি হয়েছিল, তারও কোনো হদিস মিলছে না।
লাওস, জিবুতি, মঙ্গোলিয়া, মন্টেনেগ্রো, কিরগিজস্তান এবং তাজিকিস্তানও তাদের নানা প্রকল্পের কারণে চীনা ঋণের ফাঁদে আটকে গেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আমার বিবেচনায়, বাংলাদেশের নিচে উল্লিখিত প্রকল্পগুলো খুব প্রয়োজনীয় নয়: দ্বিতীয় স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ, প্রস্তাবিত দ্বিতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং প্রস্তাবিত ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার বুলেট ট্রেন প্রকল্প।
লেখক: সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, একুশে পদকপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ ও অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

আজকের পত্রিকায় ১৩ আগস্ট একটি সংবাদ পড়ে এবং এ বিষয়ে টিভি চ্যানেলের সংবাদ দেখে মর্মাহত হয়েছিলাম। এভাবে কেউ কোনো দেশের একটি প্রাকৃতিক সম্পদের বিনাশ ঘটাতে পারে? আজকের পত্রিকায় ‘সাদাপাথরের সৌন্দর্য হারানোর কান্না’ শিরোনামের সে প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, গত বছরের ৫ আগস্ট সরকার পরিবর্তনের পর থেকেই শুরু হয় পাথর
১৫ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা এখন শতাধিক। প্রতিবছর এখানে হাজারো গবেষণা হয়, যার বড় অংশের উদ্দেশ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশ। নিঃসন্দেহে বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষকের মর্যাদা এবং বৈশ্বিক পরিচিতি বৃদ্ধির অন্যতম মাধ্যম।
১৫ ঘণ্টা আগে
খবরটি খুবই লজ্জার। বাংলাদেশ বিমানের একজন কেবিন ক্রু সোনা পাচারের দায়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন। ৪ আগস্ট বিকেলে সৌদি আরবের রিয়াদ থেকে বিজি-৩৪০ ফ্লাইটে ঢাকায় অবতরণ করার পর গ্রিন চ্যানেল অতিক্রমের সময় এই কেবিন ক্রুর গতিবিধিতে সন্দেহ জাগে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের। স্ক্যানিং মেশিনের নিচে তিনি পা দিয়ে কিছু লুকানোর
১৫ ঘণ্টা আগে
সম্প্রতি ঢাকায় বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সম্মেলনে জাপানি বিনিয়োগ পরামর্শক তাকাও হিরোসে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও রাজনীতির জন্য অশনিসংকেত দিয়েছেন। তাঁর স্পষ্ট ভাষ্য, তাঁরা দ্রুত মুনাফার খোঁজে থাকা আগ্রাসী বিনিয়োগকারী, খামখেয়ালিও।
১ দিন আগে