মো. আকিক তানজিল জিহান
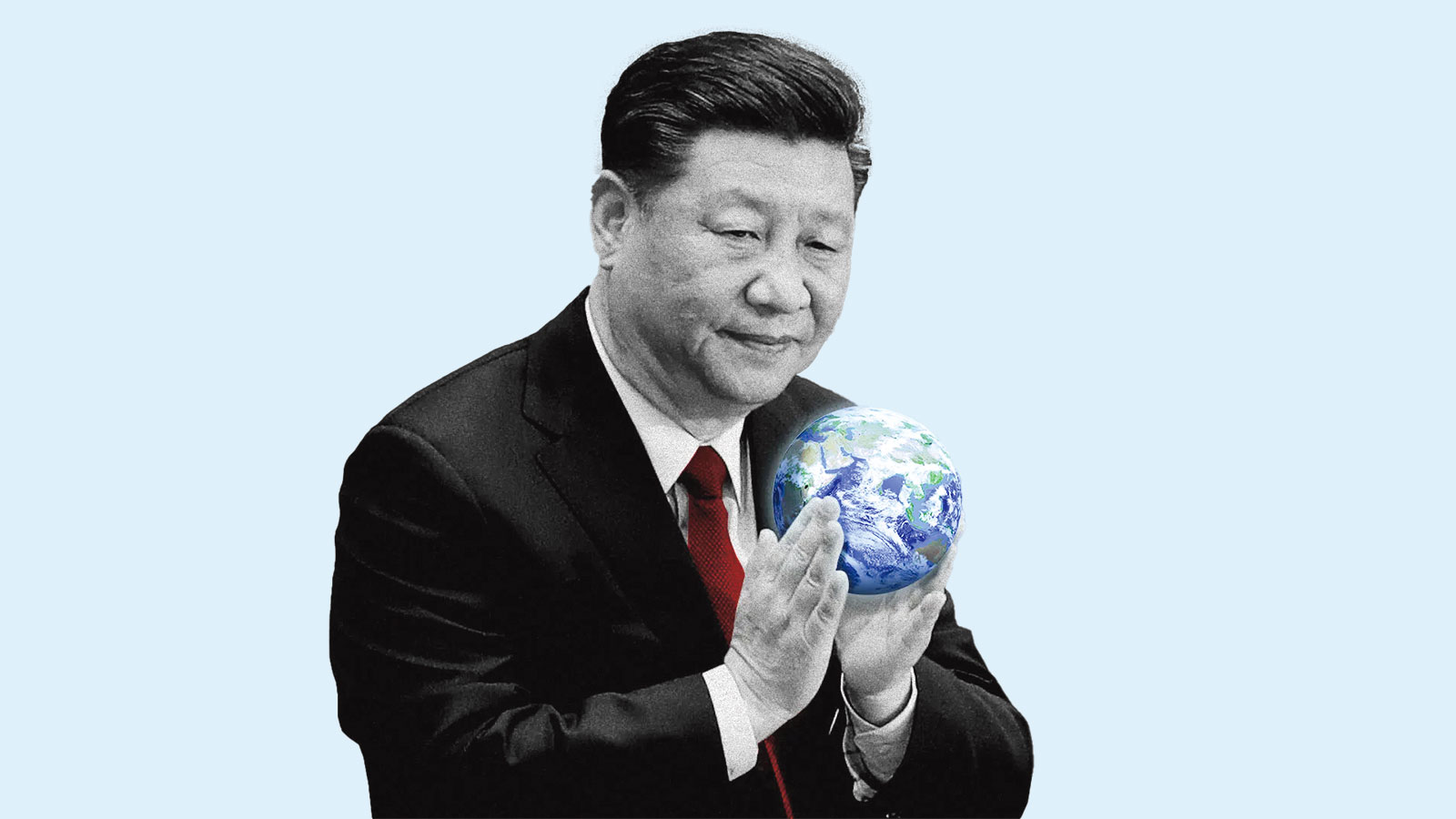
২০০০ সালে যুক্তরাষ্ট্র ছিল উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ দেশ, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের কিছু বড় অর্থনীতির দেশ এবং আফ্রিকার কিছু দেশের প্রধান বাণিজ্য অংশীদার। আর ইউরোপীয় ইউনিয়ন আধিপত্য বিস্তার করেছিল ইউরোপের প্রায় পুরো অঞ্চল, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিস্তৃত অংশ এবং দক্ষিণ আমেরিকার কিছু দেশের সঙ্গে। তখন চীন ছিল মাত্র কয়েকটি অপেক্ষাকৃত ছোট অর্থনীতির (যেমন মিয়ানমার, মঙ্গোলিয়া, উত্তর কোরিয়া, ওমান, সুদান ও ইয়েমেন) প্রধান বাণিজ্য অংশীদার। কিন্তু ২০২৪ সালের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। চীনের বাণিজ্যিক প্রভাব ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছে। চীন এখন পুরো এশিয়া, আফ্রিকার অধিকাংশ অংশ এবং দক্ষিণ আমেরিকার বেশির ভাগ দেশের প্রধান বাণিজ্য অংশীদারে পরিণত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র তাদের আধিপত্য ধরে রেখেছে মূলত উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার কিছু নির্দিষ্ট দেশে। তবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এখনো ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকার অনেক দেশের প্রধান বাণিজ্য অংশীদার হলেও বৈশ্বিক প্রভাবের দিক থেকে চীনের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে।
চীনের মোট বাণিজ্য ২০০০ সালে যেখানে ছিল মাত্র ৪৭৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০২৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬ দশমিক ২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নকে ছাড়িয়ে বিশ্বের প্রধান বাণিজ্যিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে চীন।
চীনের বাণিজ্যিক উত্থান শুধু অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি বৈশ্বিক ভূরাজনীতির গতিপথ আমূল বদলে দিচ্ছে। চীনের বিশাল রপ্তানি ও আমদানি ক্ষমতা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে চীনা বাজার ও বিনিয়োগের ওপর ক্রমবর্ধমানভাবে নির্ভরশীল করে তুলেছে। আফ্রিকার বহু দেশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো চীনের ঋণের ওপর নির্ভর করে নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ খুঁজছে। ফলে এই অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ নীতিনির্ধারণেও বেইজিংয়ের প্রভাব বাড়ছে।
এদিকে চীনের আধিপত্য শুধু বাণিজ্যে নয়, বরং বৈশ্বিক কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উৎপাদন, কাঁচামাল সরবরাহ এবং উচ্চ প্রযুক্তি খাতে চীনের অংশগ্রহণ ছাড়া অনেক দেশের শিল্প খাত টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে। এই নির্ভরশীলতা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্য বড় কৌশলগত উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেমিকন্ডাক্টর, সবুজ প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো ক্ষেত্রগুলোতে চীনের বাজার ও উৎপাদনক্ষমতা বিশ্ব নেতৃত্বের নতুন মেরু তৈরি করছে।
অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউ ইতিমধ্যে বিভিন্ন বাণিজ্য চুক্তি, কৌশলগত অংশীদারত্ব এবং সরবরাহ শৃঙ্খল পুনর্গঠনের মাধ্যমে চীনের প্রভাবকে ভারসাম্যপূর্ণ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু চীনের বাণিজ্যনীতির কাছে তা পেরে উঠছে না।
যেসব দেশ অর্থনৈতিকভাবে চীনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত, সেসব দেশ আন্তর্জাতিক সংস্থায় (যেমন জাতিসংঘ) চীনের পক্ষে ভোট দেওয়ার প্রবণতা বাড়াচ্ছে। আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বহু দেশ তাদের পররাষ্ট্রনীতিকে বেইজিংমুখী করছে। এভাবে অর্থনীতি ও রাজনীতির সমন্বয়ে চীনের ‘সফট পাওয়ার’ ও ‘হার্ড পাওয়ার’ দুটোই বাড়ছে।
যদিও চীনের উত্থান স্পষ্টত বৈশ্বিক মন্দা, ভূরাজনৈতিক সংঘাত (যেমন ইউক্রেন যুদ্ধ বা তাইওয়ান সংকট) এবং দেশটির অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জও এই আধিপত্যের স্থায়িত্বে প্রভাব ফেলতে পারে। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ নতুন বাণিজ্য জোট, প্রযুক্তি নিষেধাজ্ঞা ও বিনিয়োগ সীমাবদ্ধতার মাধ্যমে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ নিচ্ছে। ফলে বাণিজ্য আধিপত্যের এই দ্বন্দ্ব ভবিষ্যতে আরও তীব্র হতে পারে।
চীনের বাণিজ্যিক উত্থান দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতিতেও বড় ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্ম দিয়েছে। ভারত ঐতিহাসিকভাবে এই অঞ্চলের প্রভাবশালী শক্তি হলেও চীনের বাণিজ্য ও অবকাঠামো বিনিয়োগ ভারতের আশপাশের দেশগুলোতে এক নতুন বিকল্প প্রভাব পড়ছে। চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে বিশেষ করে নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান, যা নয়াদিল্লির জন্য কৌশলগত উদ্বেগ তৈরি করছে। এই অবস্থায় ভারতও চীনের প্রভাব মোকাবিলার জন্য যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে জোট গড়ে তুলছে।
বাংলাদেশ এই প্রতিযোগিতার মাঝখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূ-অবস্থান দখল করে আছে। একদিকে, বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় চীনা অর্থ ও প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অন্যদিকে, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
এ ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার সমুদ্র-বাণিজ্য ও সংযুক্তির ক্ষেত্রে চীনের প্রভাব বৃদ্ধি নতুন ‘স্ট্রিং অব পার্লস’ তত্ত্বকেও জোরালো করেছে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী চীন বঙ্গোপসাগর থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বন্দর ও সরবরাহ কেন্দ্রের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে রাজনৈতিক ও সামরিক প্রভাব বিস্তার করতে পারে। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও পায়রা বন্দর, শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটা বন্দর এবং পাকিস্তানের গওদার বন্দর এই কৌশলের অংশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশকে বাণিজ্যিক সম্পর্ক পরিচালনার পাশাপাশি এই কৌশলগত বাস্তবতাও সামলাতে হচ্ছে।
সব মিলিয়ে, দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে চীনের বাণিজ্য আধিপত্য এক নতুন বাস্তবতা তৈরি করেছে—যেখানে অর্থনৈতিক সম্ভাবনা, ঋণনির্ভরতা, নিরাপত্তার ঝুঁকি এবং কৌশলগত ভারসাম্য সবই মিলেমিশে জটিল এক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে। ভবিষ্যতে এই অঞ্চলের স্থিতিশীলতা, উন্নয়ন ও কূটনৈতিক সম্পর্ক চীনের প্রভাব ব্যবস্থাপনার ওপর অনেকাংশে নির্ভর করবে।
চীনের বাণিজ্যিক প্রভাব কেবল বড় প্রকল্প ও পণ্য বাণিজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল সংযোগেও দ্রুত বিস্তৃত হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাংলাদেশের মোবাইল নেটওয়ার্কে হুয়াওয়ের সরঞ্জামের ব্যবহার, সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে ক্লাউড সেবা ও নজরদারি প্রযুক্তি, এমনকি স্মার্ট সিটি প্রকল্পের ক্ষেত্রেও চীনের প্রযুক্তিনির্ভরতার বিষয়টি দৃশ্যমান। এর ফলে ডিজিটাল নিরাপত্তা, সাইবার ঝুঁকি এবং তথ্যনির্ভরতা সম্পর্কেও নতুন প্রশ্ন উঠে আসছে।
চীনের বাণিজ্যিক প্রভাব বৃদ্ধির ঢেউ দক্ষিণ এশিয়ায়ও গভীরভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। ২০০০ সালে এই অঞ্চলের দেশগুলোর প্রধান বাণিজ্য অংশীদার ছিল যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন। ভারত তুলনামূলকভাবে স্বনির্ভর বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করছিল। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা প্রধানত পশ্চিমা বাজারের ওপর নির্ভর করত, বিশেষ করে তৈরি পোশাক ও হালকা শিল্প রপ্তানিতে। কিন্তু ২০২৪ সালে
চীনের উত্থান দক্ষিণ এশিয়ার বাণিজ্য মানচিত্র আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছে। পাকিস্তান এখন চীনা বিনিয়োগের অন্যতম
বড় উপভোক্তা, যেখানে চায়না-পাকিস্তান ইকোনমিক করিডর
বহু অবকাঠামো ও বিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি করেছে। শ্রীলঙ্কায় হাম্বানটোটা বন্দরসহ বিশাল চীনা ঋণ ও বিনিয়োগ এসেছে। নেপাল ও মালদ্বীপও ক্রমে বেইজিংয়ের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক অংশীদারে পরিণত হচ্ছে।
চীনের উত্থান বাংলাদেশের জন্য কিছু সম্ভাবনা ও ঝুঁকি দুই-ই তৈরি করেছে। একদিকে চীনের বিনিয়োগ, প্রযুক্তি ও বাজার ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার সুযোগ রয়েছে। অন্যদিকে অতিরিক্ত ঋণ ও বাণিজ্যনির্ভরতা ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক ও কৌশলগত ঝুঁকির কারণ হতে পারে। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষার চ্যালেঞ্জও ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে।
লেখক: মো. আকিক তানজিল জিহান, শিক্ষার্থী, গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
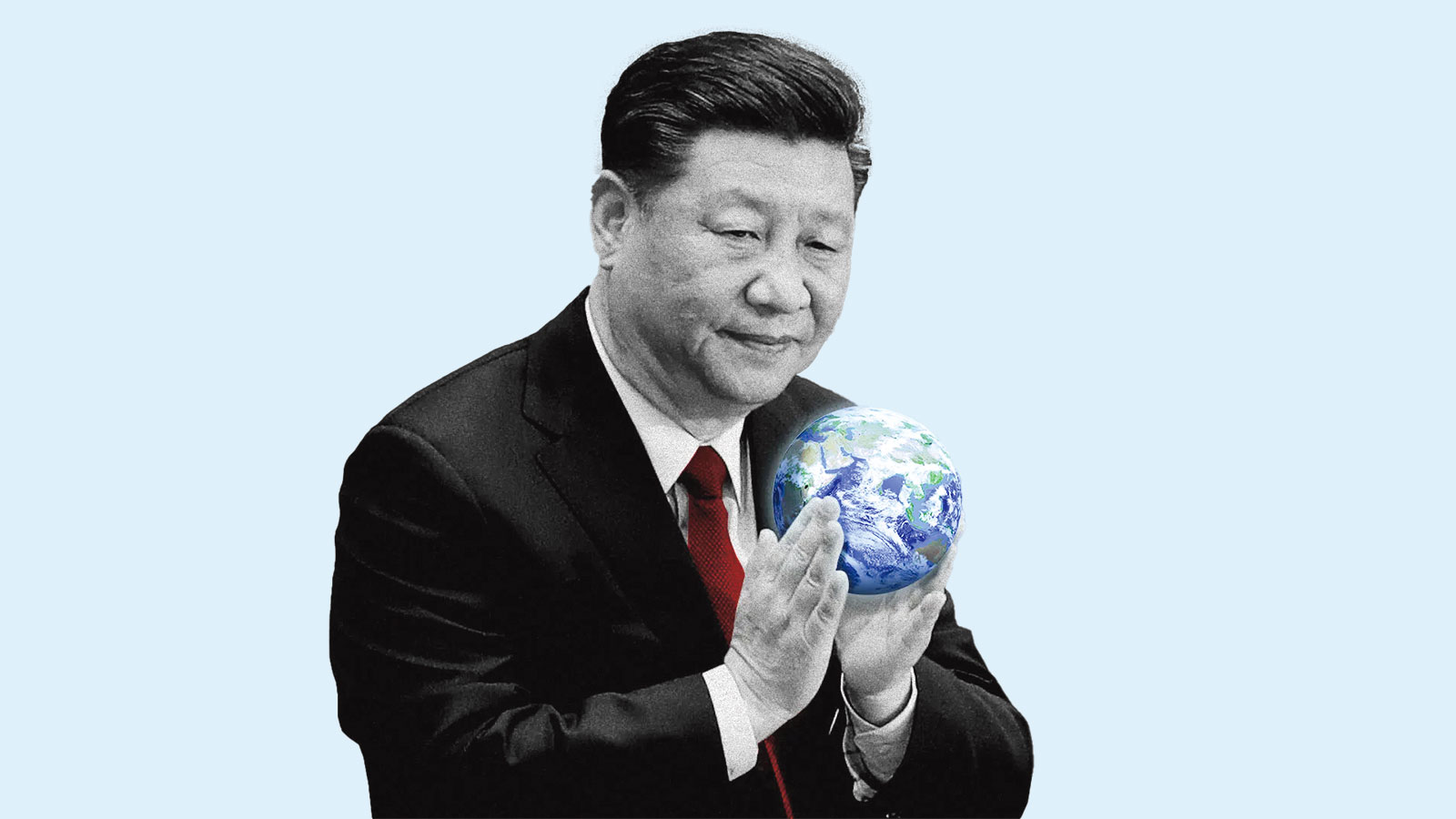
২০০০ সালে যুক্তরাষ্ট্র ছিল উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ দেশ, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের কিছু বড় অর্থনীতির দেশ এবং আফ্রিকার কিছু দেশের প্রধান বাণিজ্য অংশীদার। আর ইউরোপীয় ইউনিয়ন আধিপত্য বিস্তার করেছিল ইউরোপের প্রায় পুরো অঞ্চল, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিস্তৃত অংশ এবং দক্ষিণ আমেরিকার কিছু দেশের সঙ্গে। তখন চীন ছিল মাত্র কয়েকটি অপেক্ষাকৃত ছোট অর্থনীতির (যেমন মিয়ানমার, মঙ্গোলিয়া, উত্তর কোরিয়া, ওমান, সুদান ও ইয়েমেন) প্রধান বাণিজ্য অংশীদার। কিন্তু ২০২৪ সালের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। চীনের বাণিজ্যিক প্রভাব ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছে। চীন এখন পুরো এশিয়া, আফ্রিকার অধিকাংশ অংশ এবং দক্ষিণ আমেরিকার বেশির ভাগ দেশের প্রধান বাণিজ্য অংশীদারে পরিণত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র তাদের আধিপত্য ধরে রেখেছে মূলত উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার কিছু নির্দিষ্ট দেশে। তবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এখনো ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকার অনেক দেশের প্রধান বাণিজ্য অংশীদার হলেও বৈশ্বিক প্রভাবের দিক থেকে চীনের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে।
চীনের মোট বাণিজ্য ২০০০ সালে যেখানে ছিল মাত্র ৪৭৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০২৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬ দশমিক ২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নকে ছাড়িয়ে বিশ্বের প্রধান বাণিজ্যিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে চীন।
চীনের বাণিজ্যিক উত্থান শুধু অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি বৈশ্বিক ভূরাজনীতির গতিপথ আমূল বদলে দিচ্ছে। চীনের বিশাল রপ্তানি ও আমদানি ক্ষমতা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে চীনা বাজার ও বিনিয়োগের ওপর ক্রমবর্ধমানভাবে নির্ভরশীল করে তুলেছে। আফ্রিকার বহু দেশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো চীনের ঋণের ওপর নির্ভর করে নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ খুঁজছে। ফলে এই অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ নীতিনির্ধারণেও বেইজিংয়ের প্রভাব বাড়ছে।
এদিকে চীনের আধিপত্য শুধু বাণিজ্যে নয়, বরং বৈশ্বিক কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উৎপাদন, কাঁচামাল সরবরাহ এবং উচ্চ প্রযুক্তি খাতে চীনের অংশগ্রহণ ছাড়া অনেক দেশের শিল্প খাত টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে। এই নির্ভরশীলতা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্য বড় কৌশলগত উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেমিকন্ডাক্টর, সবুজ প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো ক্ষেত্রগুলোতে চীনের বাজার ও উৎপাদনক্ষমতা বিশ্ব নেতৃত্বের নতুন মেরু তৈরি করছে।
অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউ ইতিমধ্যে বিভিন্ন বাণিজ্য চুক্তি, কৌশলগত অংশীদারত্ব এবং সরবরাহ শৃঙ্খল পুনর্গঠনের মাধ্যমে চীনের প্রভাবকে ভারসাম্যপূর্ণ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু চীনের বাণিজ্যনীতির কাছে তা পেরে উঠছে না।
যেসব দেশ অর্থনৈতিকভাবে চীনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত, সেসব দেশ আন্তর্জাতিক সংস্থায় (যেমন জাতিসংঘ) চীনের পক্ষে ভোট দেওয়ার প্রবণতা বাড়াচ্ছে। আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বহু দেশ তাদের পররাষ্ট্রনীতিকে বেইজিংমুখী করছে। এভাবে অর্থনীতি ও রাজনীতির সমন্বয়ে চীনের ‘সফট পাওয়ার’ ও ‘হার্ড পাওয়ার’ দুটোই বাড়ছে।
যদিও চীনের উত্থান স্পষ্টত বৈশ্বিক মন্দা, ভূরাজনৈতিক সংঘাত (যেমন ইউক্রেন যুদ্ধ বা তাইওয়ান সংকট) এবং দেশটির অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জও এই আধিপত্যের স্থায়িত্বে প্রভাব ফেলতে পারে। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ নতুন বাণিজ্য জোট, প্রযুক্তি নিষেধাজ্ঞা ও বিনিয়োগ সীমাবদ্ধতার মাধ্যমে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ নিচ্ছে। ফলে বাণিজ্য আধিপত্যের এই দ্বন্দ্ব ভবিষ্যতে আরও তীব্র হতে পারে।
চীনের বাণিজ্যিক উত্থান দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতিতেও বড় ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্ম দিয়েছে। ভারত ঐতিহাসিকভাবে এই অঞ্চলের প্রভাবশালী শক্তি হলেও চীনের বাণিজ্য ও অবকাঠামো বিনিয়োগ ভারতের আশপাশের দেশগুলোতে এক নতুন বিকল্প প্রভাব পড়ছে। চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে বিশেষ করে নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান, যা নয়াদিল্লির জন্য কৌশলগত উদ্বেগ তৈরি করছে। এই অবস্থায় ভারতও চীনের প্রভাব মোকাবিলার জন্য যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে জোট গড়ে তুলছে।
বাংলাদেশ এই প্রতিযোগিতার মাঝখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূ-অবস্থান দখল করে আছে। একদিকে, বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় চীনা অর্থ ও প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অন্যদিকে, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
এ ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার সমুদ্র-বাণিজ্য ও সংযুক্তির ক্ষেত্রে চীনের প্রভাব বৃদ্ধি নতুন ‘স্ট্রিং অব পার্লস’ তত্ত্বকেও জোরালো করেছে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী চীন বঙ্গোপসাগর থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বন্দর ও সরবরাহ কেন্দ্রের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে রাজনৈতিক ও সামরিক প্রভাব বিস্তার করতে পারে। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও পায়রা বন্দর, শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটা বন্দর এবং পাকিস্তানের গওদার বন্দর এই কৌশলের অংশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশকে বাণিজ্যিক সম্পর্ক পরিচালনার পাশাপাশি এই কৌশলগত বাস্তবতাও সামলাতে হচ্ছে।
সব মিলিয়ে, দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে চীনের বাণিজ্য আধিপত্য এক নতুন বাস্তবতা তৈরি করেছে—যেখানে অর্থনৈতিক সম্ভাবনা, ঋণনির্ভরতা, নিরাপত্তার ঝুঁকি এবং কৌশলগত ভারসাম্য সবই মিলেমিশে জটিল এক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে। ভবিষ্যতে এই অঞ্চলের স্থিতিশীলতা, উন্নয়ন ও কূটনৈতিক সম্পর্ক চীনের প্রভাব ব্যবস্থাপনার ওপর অনেকাংশে নির্ভর করবে।
চীনের বাণিজ্যিক প্রভাব কেবল বড় প্রকল্প ও পণ্য বাণিজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল সংযোগেও দ্রুত বিস্তৃত হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাংলাদেশের মোবাইল নেটওয়ার্কে হুয়াওয়ের সরঞ্জামের ব্যবহার, সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে ক্লাউড সেবা ও নজরদারি প্রযুক্তি, এমনকি স্মার্ট সিটি প্রকল্পের ক্ষেত্রেও চীনের প্রযুক্তিনির্ভরতার বিষয়টি দৃশ্যমান। এর ফলে ডিজিটাল নিরাপত্তা, সাইবার ঝুঁকি এবং তথ্যনির্ভরতা সম্পর্কেও নতুন প্রশ্ন উঠে আসছে।
চীনের বাণিজ্যিক প্রভাব বৃদ্ধির ঢেউ দক্ষিণ এশিয়ায়ও গভীরভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। ২০০০ সালে এই অঞ্চলের দেশগুলোর প্রধান বাণিজ্য অংশীদার ছিল যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন। ভারত তুলনামূলকভাবে স্বনির্ভর বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করছিল। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা প্রধানত পশ্চিমা বাজারের ওপর নির্ভর করত, বিশেষ করে তৈরি পোশাক ও হালকা শিল্প রপ্তানিতে। কিন্তু ২০২৪ সালে
চীনের উত্থান দক্ষিণ এশিয়ার বাণিজ্য মানচিত্র আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছে। পাকিস্তান এখন চীনা বিনিয়োগের অন্যতম
বড় উপভোক্তা, যেখানে চায়না-পাকিস্তান ইকোনমিক করিডর
বহু অবকাঠামো ও বিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি করেছে। শ্রীলঙ্কায় হাম্বানটোটা বন্দরসহ বিশাল চীনা ঋণ ও বিনিয়োগ এসেছে। নেপাল ও মালদ্বীপও ক্রমে বেইজিংয়ের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক অংশীদারে পরিণত হচ্ছে।
চীনের উত্থান বাংলাদেশের জন্য কিছু সম্ভাবনা ও ঝুঁকি দুই-ই তৈরি করেছে। একদিকে চীনের বিনিয়োগ, প্রযুক্তি ও বাজার ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার সুযোগ রয়েছে। অন্যদিকে অতিরিক্ত ঋণ ও বাণিজ্যনির্ভরতা ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক ও কৌশলগত ঝুঁকির কারণ হতে পারে। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষার চ্যালেঞ্জও ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে।
লেখক: মো. আকিক তানজিল জিহান, শিক্ষার্থী, গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন আয়োজিত অনুষ্ঠানে জুলাই জাতীয় সনদ সই করা হয়েছে। ১৭ অক্টোবর শুক্রবার বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ২৫টি রাজনৈতিক দলের নেতারা অংশ নেন।
৭ ঘণ্টা আগে
এ বছর পৃথিবীতে বসবাসযোগ্য শহরের তালিকায় ষষ্ঠ স্থান পেয়েছে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহর। আর মেলবোর্ন আছে চতুর্থ স্থানে। ২৯ বছর আগে এক ভোরবেলায় এ দেশের মাটিতে পা রেখেছিলাম। ট্যাক্সিতে চড়ে যাওয়ার সময় ছবির মতো বাড়িঘর, সামনে বাগান, সারি সারি বৃক্ষ ও সাজানো রাস্তাঘাট দেখে মনে হচ্ছিল আমি কোনো সিনেমার শুটিং...
৭ ঘণ্টা আগে
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজের আমদানি পণ্য কমপ্লেক্সে ১৮ অক্টোবর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এক সপ্তাহের ব্যবধানে দেশে তিনটি বড় দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটল।
৮ ঘণ্টা আগে
জুলাই সনদ ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রশ্নে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতা, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের ভূমিকা, জোট রাজনীতি, নারীনীতি, নির্বাচনী প্রতীক ইস্যু থেকে শুরু করে ফান্ডিং ও ‘মেধা বনাম কোটার’ বিতর্ক—এসব বিষয়ে দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা..
১ দিন আগে