সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
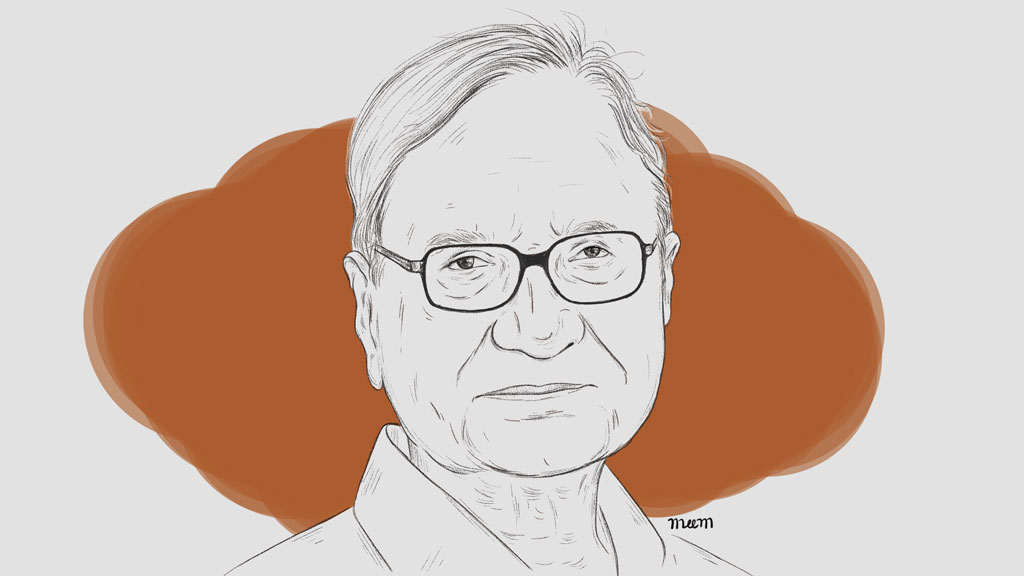
স্বাধীন হওয়ার পরপরই টের পাওয়া গেল যে পূর্ব বাংলা পাঞ্জাব-শাসিত পাকিস্তানের একটি অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ হতে চলেছে। সে জন্যই দাবি উঠেছে স্বায়ত্তশাসনের এবং ওই দাবিকে যৌক্তিক দিক দিয়ে জোরদার করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে আদি লাহোর প্রস্তাবের। বলা হয়ে থাকে, মুসলিম লীগের নেতাদের স্বার্থান্বেষী ও স্বেচ্ছাচারী আচরণে বিক্ষুব্ধ হয়ে সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিমপন্থীরাই উদ্যোগ নিয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তৎপরতাটা সোহরাওয়ার্দীপন্থীদের তুলনায় হাশিমপন্থীদের দিক থেকেই ছিল অধিক উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, সোহরাওয়ার্দী নিজে পূর্ববঙ্গকে নয়, পশ্চিম পাকিস্তানকেই তাঁর কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন; দ্বিতীয়ত, তিনি সেখানে গিয়ে জিন্নাহ-আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে একটি দল গঠন করেছিলেন এবং আশা করছিলেন পূর্ববঙ্গে তার একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হবে। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনে যে তরুণেরা উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন শামসুল হক, যাঁকে দলের সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করা হয়; এবং মতাদর্শিকভাবে শামসুল হক ছিলেন আবুল হাশিমের রব্বানিয়াত দর্শনের অনুসারী। নতুন দলের ঘোষণাপত্রটি শামসুল হকই লিখে থাকবেন। কারণ তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে পাকিস্তান খেলাফত বা আল্লাহর প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র হবে এবং আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতা ও প্রভুত্বের অধিকারী হবে। এটি রব্বানিয়াত দর্শনেরই কথা। তবে ‘মূল দাবি’ হিসেবে শামসুল হক যে লাহোর প্রস্তাবের কথা বলেছেন, সেটা আরও অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর মতে, লাহোর প্রস্তাব ‘সর্বকালের সর্ব যুগের সর্ব দেশের যুগপ্রবর্তক ঘটনাবলির ন্যায় একটি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে।’ মনে হচ্ছে উদ্যোগীদের দৃষ্টিতে লাহোর প্রস্তাব ছিল একটি মহাবৈপ্লবিক ঘটনা। তবে, তাঁদের মতে, মুসলিম লীগ নেতৃত্বের অপারগতার দরুন ওই বিপ্লবের লক্ষ্যগুলো অর্জন করা যেহেতু সম্ভব হয়নি, তাই মুসলিম লীগকে ‘স্বার্থান্বেষী মুষ্টিমেয় লোকদের পকেট হইতে বাহির করিয়া সত্যিকারের জনগণের মুসলিম লীগ হিসেবে গড়ে তোলা আবশ্যক।’ অর্থাৎ কিনা লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়ন চাই। নতুন সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হন মওলানা ভাসানী, এর আগে যিনি আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন এবং মনেপ্রাণে যিনি লাহোর প্রস্তাবের ‘দুই পাকিস্তান’ নীতিতে বিশ্বাস করতেন। যে মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়, সেটির আহ্বান করা হয়েছিল ভাসানীর নামেই; যার প্রতিক্রিয়ায় পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) ও অন্য কয়েকজন কর্মকর্তা মিলে এক বিবৃতিতে জানান যে, ‘মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সাহেবের দ্বারা আগামী ২৩শে ও ২৪শে জুন তারিখে মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলন নামে যে সভা আহূত হইয়াছে, তাহার সহিত মুসলিম লীগের কোন সম্পর্ক নাই। বস্তুত ইহা দলগত স্বার্থ ও ক্ষমতা লাভের জন্য মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির দ্বারা মুসলমান সংহতি নষ্ট করিয়া পাকিস্তানের স্থায়িত্ব ও অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আহূত হইয়াছে।’
নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রাদেশিক মুসলিম লীগের মতো ‘প্রাদেশিক’ ছিল না; ছিল লাহোর প্রস্তাবে যে ধারণা ব্যক্ত হয়েছিল, কল্পনার সেই স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের একটি সংগঠন। মওলানা ভাসানী অবশ্য সোহরাওয়ার্দীকে এর সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। সেটা এই লক্ষ্যে যে পাকিস্তানজুড়ে সংগঠনের বিস্তার ঘটলে মুসলিম লীগের বিরোধী শক্তি হিসেবে এর শক্তি বৃদ্ধি পাবে। সোহরাওয়ার্দী তখন থাকতেন লাহোরে, ভাসানী শেখ মুজিবকে লাহোরে পাঠিয়েছিলেন সোহরাওয়ার্দী ও সম্ভব হলে মিয়া ইফতেখার উদ্দিনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। সেটা ১৯৪৯-এরই ঘটনা। এর পরে ১৯৫২-তে মুজিব আবার পশ্চিম পাকিস্তানে যান; একই উদ্দেশ্যে; সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে দেখা করতে। সোহরাওয়ার্দী তখন তাঁকে জানান যে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পক্ষে পশ্চিমে-গঠিত জিন্নাহ-আওয়ামী মুসলিম লীগের অ্যাফিলিয়েশন নেওয়া দরকার। অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে শেখ মুজিব লিখেছেন, ‘তিনি বললেন, একটা কনফারেন্স ডাকবো, তার আগে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের এ্যাফিলিয়েশন নেওয়া দরকার।’ জবাবে শেখ মুজিব তখন তাঁকে যা বলেছিলেন সেটা এ রকমের:
আমি তাঁকে জানালাম, ‘আপনি জিন্নাহ আওয়ামী লীগ করেছেন, আমরা নাম পরিবর্তন করতে পারব না। কোনো ব্যক্তির নাম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগ করতে চাই না। দ্বিতীয়ত, আমাদের ম্যানিফেস্টো আছে, গঠনতন্ত্র আছে, তার পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। মওলানা সাহেব আমাকে ১৯৪৯ সালে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলেন। তখনও তিনি নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ গঠনের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তাঁরও কোনো আপত্তি থাকবে না যদি আপনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো ও গঠনতন্ত্র মেনে নেন। অনেক আপত্তির পর তিনি মানতে রাজি হলেন এবং নিজ হাতে তাঁর সম্মতির কথা লিখে দিলেন।’
মুজিব লিখেছেন, ‘আমি আর এটাও অনুরোধ করলাম তাঁকে লিখে দিতে যে, উর্দু ও বাংলা দুটোকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে তিনি সমর্থন করেন। কারণ অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে। মুসলিম লীগ ও তথাকথিত প্রগতিশীলরা প্রোপাগান্ডা করছে তাঁর বিরুদ্ধে। [...] তিনি লিখে দিলেন।’
অন্যরা তেমনভাবে খেয়াল না করলেও শেখ মুজিব ঠিকই লক্ষ করছিলেন যে, ‘পূর্ব বাংলার সম্পদকে কেড়ে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানকে কত তাড়াতাড়ি গড়া যায়, একদল পশ্চিমা তথাকথিত নেতা ও বড় বড় সরকারি কর্মচারী গোপনে সে কাজ করে চলছিল। তাদের একটা ধারণা ছিল, পূর্ব বাংলা শেষ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে থাকবে না। তাই যত তাড়াতাড়ি পারা যায় পশ্চিম পাকিস্তানকে গড়ে তুলতে হবে।’
অর্থাৎ লাহোর প্রস্তাবের যে অঙ্গীকার–দুটি স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম পাকিস্তানের, সেটা সব দিক থেকেই অকার্যকর করে তোলা হচ্ছিল। এই উপলব্ধি থেকেই মওলানা ভাসানী ১৯৫৭ সালের কাগমারী সম্মেলনে প্রয়োজনে পশ্চিম পাকিস্তানকে আসসালামু আলাইকুম জানানো হবে বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। শেখ মুজিব সে সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু ১৯৬৬-তে এসেই তাঁর মনে কোনো সংশয় থাকেনি যে পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতিদের সঙ্গে থাকা যাবে না, যে কথা তিনি তখনকার কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের বলেছিলেন এক গোপন বৈঠকে; ১৯৬১ সালের ডিসেম্বরের দিকে।
লাহোর প্রস্তাবের রাজনৈতিক মর্মবস্তুতে অবশ্য আরেকটি জিনিস ছিল, সেটি হলো দ্বিজাতি তত্ত্ব। ভারতবর্ষের মুসলমানরা একটি অভিন্ন ও স্বতন্ত্র জাতি, এই ধারণার ওপর দাঁড়িয়েই লাহোর প্রস্তাব তৈরি করা হয়েছিল। ধরে নেওয়া হয়েছিল যে জাতীয় সত্তার প্রধান ভিত্তি হচ্ছে ধর্ম। সেটা যে সত্য নয়, প্রধান ভিত্তি যে ভাষা, সেটা তো অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বের হয়ে এসেছিল বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়েই। সোহরাওয়ার্দী কিন্তু লাহোর প্রস্তাবের ওই মর্মবস্তুটিকে কখনোই খারিজ করে দেননি; জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দ্বিজাতি তত্ত্বকে তিনি সত্য বলে জেনেছেন, যে জন্য পাকিস্তানকে ভাঙা নয়, তাকে রক্ষা করার কাজেই তিনি সচেষ্ট ছিলেন। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান যখন তাঁকে কারারুদ্ধ করেন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান যে অভিযোগ আনা হয়েছিল সেটি হলো, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই, ‘বিশেষ করে গত তিন বছর ধরে, তিনি ভেতরের ও বাইরের পাকিস্তানবিরোধীদের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছেন।’ অভিযোগনামার জবাবে জেলখানা থেকেই সোহরাওয়ার্দী যে জোরালো চিঠিটি লিখেছিলেন তাতে তিনি বলেছেন, এই অভিযোগ পড়ে তিনি যারপরনাই মর্মাহত হয়েছেন। কারণ তিনি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, ‘মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান হচ্ছে এক ও অবিভাজ্য;’ এবং এই বিশ্বাসের দ্বারা তাড়িত হয়েই তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের জীবনকে বিপন্ন করেছেন এবং এখন বার্ধক্যে এসে পৌঁছেছেন। পূর্ব ও পশ্চিমকে একসঙ্গে থাকতে হবে–এই বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হয়েই তিনি কাজ করে গেছেন।
এরপরও তাঁকে যে পাকিস্তানের ঐক্য-বিনষ্টকারী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং সেই অভিযোগে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছে, সেটা কেবল যে দুঃখজনক তা-ই নয়, এর দ্বারা তাঁর যে রাজনৈতিক ‘উপযোগিতা’ (utility) ছিল তা ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। তিনি বলছেন যে, তিনি কখনো পদের জন্য লালায়িত ছিলেন না; কিন্তু তিনি পাকিস্তানের অখণ্ডতা (অবশ্যই এককেন্দ্রিক) রক্ষার জন্য কাজ করতে পারতেন। দুঃখের বিষয় আইয়ুব খান তাঁর সেই উপযোগিতাকে ধ্বংস করে ছেড়েছেন। পাকিস্তানকে তিনি এক জাতির দেশ বলেই মনে করতেন। এখানে আইয়ুব খানের সঙ্গে তাঁর কোনো বিরোধ ছিল না, উভয়েই পাকিস্তানকে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে একত্র রাখতে চেয়েছেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহও এমন একটি অবিচ্ছেদ্য পাকিস্তানি জাতিই তৈরি করবেন বলেই ভেবেছিলেন। স্পষ্টতই আইয়ুব খানের সঙ্গে সোহরাওয়ার্দীর দ্বন্দ্বটা ছিল ক্ষমতা নিয়ে; আইয়ুব সোহরাওয়ার্দীকে মুক্ত রেখে স্বস্তি পাচ্ছিলেন না, কারণ তখন সোহরাওয়ার্দীই ছিলেন তাঁর ক্ষমতায় থাকার প্রতি প্রধান চ্যালেঞ্জ; বিশেষ করে এই জন্য যে, সোহরাওয়ার্দীর প্রতি আমেরিকানদের পক্ষপাতিত্ব আইয়ুবের তুলনায় কিছুটা বেশি ছিল বলেই সন্দেহ হচ্ছিল। আইয়ুব অবশ্য সোহরাওয়ার্দীকে বেশি দিন বন্দী করে রাখতে পারেননি, প্রবল জনপ্রতিবাদের মুখে ১৯৬২ সালের জানুয়ারির শেষ দিনে আটক করে আট মাস যেতে না যেতেই ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তার আগে অবশ্য আইয়ুব তাঁর নিজের রচিত সংবিধানটি ঘোষণা করার কাজটি সম্পন্ন করে নিয়েছিলেন; সে সংবিধানে সংখ্যাসাম্য ও এক ইউনিট, দুটোই ছিল।
লেখক: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
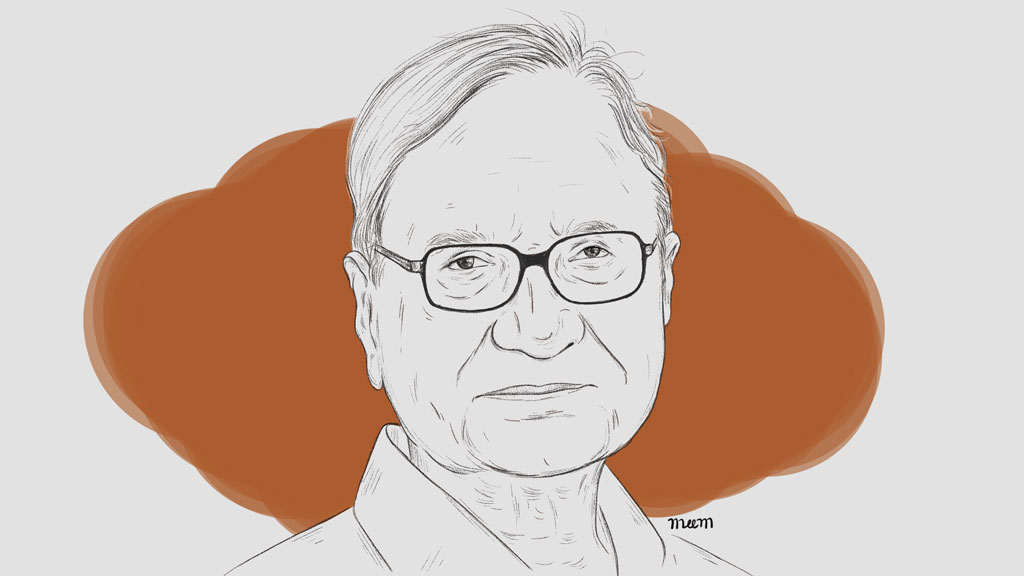
স্বাধীন হওয়ার পরপরই টের পাওয়া গেল যে পূর্ব বাংলা পাঞ্জাব-শাসিত পাকিস্তানের একটি অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ হতে চলেছে। সে জন্যই দাবি উঠেছে স্বায়ত্তশাসনের এবং ওই দাবিকে যৌক্তিক দিক দিয়ে জোরদার করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে আদি লাহোর প্রস্তাবের। বলা হয়ে থাকে, মুসলিম লীগের নেতাদের স্বার্থান্বেষী ও স্বেচ্ছাচারী আচরণে বিক্ষুব্ধ হয়ে সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিমপন্থীরাই উদ্যোগ নিয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তৎপরতাটা সোহরাওয়ার্দীপন্থীদের তুলনায় হাশিমপন্থীদের দিক থেকেই ছিল অধিক উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, সোহরাওয়ার্দী নিজে পূর্ববঙ্গকে নয়, পশ্চিম পাকিস্তানকেই তাঁর কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন; দ্বিতীয়ত, তিনি সেখানে গিয়ে জিন্নাহ-আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে একটি দল গঠন করেছিলেন এবং আশা করছিলেন পূর্ববঙ্গে তার একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হবে। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনে যে তরুণেরা উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন শামসুল হক, যাঁকে দলের সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করা হয়; এবং মতাদর্শিকভাবে শামসুল হক ছিলেন আবুল হাশিমের রব্বানিয়াত দর্শনের অনুসারী। নতুন দলের ঘোষণাপত্রটি শামসুল হকই লিখে থাকবেন। কারণ তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে পাকিস্তান খেলাফত বা আল্লাহর প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র হবে এবং আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতা ও প্রভুত্বের অধিকারী হবে। এটি রব্বানিয়াত দর্শনেরই কথা। তবে ‘মূল দাবি’ হিসেবে শামসুল হক যে লাহোর প্রস্তাবের কথা বলেছেন, সেটা আরও অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর মতে, লাহোর প্রস্তাব ‘সর্বকালের সর্ব যুগের সর্ব দেশের যুগপ্রবর্তক ঘটনাবলির ন্যায় একটি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে।’ মনে হচ্ছে উদ্যোগীদের দৃষ্টিতে লাহোর প্রস্তাব ছিল একটি মহাবৈপ্লবিক ঘটনা। তবে, তাঁদের মতে, মুসলিম লীগ নেতৃত্বের অপারগতার দরুন ওই বিপ্লবের লক্ষ্যগুলো অর্জন করা যেহেতু সম্ভব হয়নি, তাই মুসলিম লীগকে ‘স্বার্থান্বেষী মুষ্টিমেয় লোকদের পকেট হইতে বাহির করিয়া সত্যিকারের জনগণের মুসলিম লীগ হিসেবে গড়ে তোলা আবশ্যক।’ অর্থাৎ কিনা লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়ন চাই। নতুন সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হন মওলানা ভাসানী, এর আগে যিনি আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন এবং মনেপ্রাণে যিনি লাহোর প্রস্তাবের ‘দুই পাকিস্তান’ নীতিতে বিশ্বাস করতেন। যে মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়, সেটির আহ্বান করা হয়েছিল ভাসানীর নামেই; যার প্রতিক্রিয়ায় পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) ও অন্য কয়েকজন কর্মকর্তা মিলে এক বিবৃতিতে জানান যে, ‘মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সাহেবের দ্বারা আগামী ২৩শে ও ২৪শে জুন তারিখে মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলন নামে যে সভা আহূত হইয়াছে, তাহার সহিত মুসলিম লীগের কোন সম্পর্ক নাই। বস্তুত ইহা দলগত স্বার্থ ও ক্ষমতা লাভের জন্য মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির দ্বারা মুসলমান সংহতি নষ্ট করিয়া পাকিস্তানের স্থায়িত্ব ও অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আহূত হইয়াছে।’
নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রাদেশিক মুসলিম লীগের মতো ‘প্রাদেশিক’ ছিল না; ছিল লাহোর প্রস্তাবে যে ধারণা ব্যক্ত হয়েছিল, কল্পনার সেই স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের একটি সংগঠন। মওলানা ভাসানী অবশ্য সোহরাওয়ার্দীকে এর সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। সেটা এই লক্ষ্যে যে পাকিস্তানজুড়ে সংগঠনের বিস্তার ঘটলে মুসলিম লীগের বিরোধী শক্তি হিসেবে এর শক্তি বৃদ্ধি পাবে। সোহরাওয়ার্দী তখন থাকতেন লাহোরে, ভাসানী শেখ মুজিবকে লাহোরে পাঠিয়েছিলেন সোহরাওয়ার্দী ও সম্ভব হলে মিয়া ইফতেখার উদ্দিনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। সেটা ১৯৪৯-এরই ঘটনা। এর পরে ১৯৫২-তে মুজিব আবার পশ্চিম পাকিস্তানে যান; একই উদ্দেশ্যে; সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে দেখা করতে। সোহরাওয়ার্দী তখন তাঁকে জানান যে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পক্ষে পশ্চিমে-গঠিত জিন্নাহ-আওয়ামী মুসলিম লীগের অ্যাফিলিয়েশন নেওয়া দরকার। অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে শেখ মুজিব লিখেছেন, ‘তিনি বললেন, একটা কনফারেন্স ডাকবো, তার আগে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের এ্যাফিলিয়েশন নেওয়া দরকার।’ জবাবে শেখ মুজিব তখন তাঁকে যা বলেছিলেন সেটা এ রকমের:
আমি তাঁকে জানালাম, ‘আপনি জিন্নাহ আওয়ামী লীগ করেছেন, আমরা নাম পরিবর্তন করতে পারব না। কোনো ব্যক্তির নাম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগ করতে চাই না। দ্বিতীয়ত, আমাদের ম্যানিফেস্টো আছে, গঠনতন্ত্র আছে, তার পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। মওলানা সাহেব আমাকে ১৯৪৯ সালে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলেন। তখনও তিনি নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ গঠনের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তাঁরও কোনো আপত্তি থাকবে না যদি আপনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো ও গঠনতন্ত্র মেনে নেন। অনেক আপত্তির পর তিনি মানতে রাজি হলেন এবং নিজ হাতে তাঁর সম্মতির কথা লিখে দিলেন।’
মুজিব লিখেছেন, ‘আমি আর এটাও অনুরোধ করলাম তাঁকে লিখে দিতে যে, উর্দু ও বাংলা দুটোকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে তিনি সমর্থন করেন। কারণ অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে। মুসলিম লীগ ও তথাকথিত প্রগতিশীলরা প্রোপাগান্ডা করছে তাঁর বিরুদ্ধে। [...] তিনি লিখে দিলেন।’
অন্যরা তেমনভাবে খেয়াল না করলেও শেখ মুজিব ঠিকই লক্ষ করছিলেন যে, ‘পূর্ব বাংলার সম্পদকে কেড়ে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানকে কত তাড়াতাড়ি গড়া যায়, একদল পশ্চিমা তথাকথিত নেতা ও বড় বড় সরকারি কর্মচারী গোপনে সে কাজ করে চলছিল। তাদের একটা ধারণা ছিল, পূর্ব বাংলা শেষ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে থাকবে না। তাই যত তাড়াতাড়ি পারা যায় পশ্চিম পাকিস্তানকে গড়ে তুলতে হবে।’
অর্থাৎ লাহোর প্রস্তাবের যে অঙ্গীকার–দুটি স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম পাকিস্তানের, সেটা সব দিক থেকেই অকার্যকর করে তোলা হচ্ছিল। এই উপলব্ধি থেকেই মওলানা ভাসানী ১৯৫৭ সালের কাগমারী সম্মেলনে প্রয়োজনে পশ্চিম পাকিস্তানকে আসসালামু আলাইকুম জানানো হবে বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। শেখ মুজিব সে সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু ১৯৬৬-তে এসেই তাঁর মনে কোনো সংশয় থাকেনি যে পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতিদের সঙ্গে থাকা যাবে না, যে কথা তিনি তখনকার কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের বলেছিলেন এক গোপন বৈঠকে; ১৯৬১ সালের ডিসেম্বরের দিকে।
লাহোর প্রস্তাবের রাজনৈতিক মর্মবস্তুতে অবশ্য আরেকটি জিনিস ছিল, সেটি হলো দ্বিজাতি তত্ত্ব। ভারতবর্ষের মুসলমানরা একটি অভিন্ন ও স্বতন্ত্র জাতি, এই ধারণার ওপর দাঁড়িয়েই লাহোর প্রস্তাব তৈরি করা হয়েছিল। ধরে নেওয়া হয়েছিল যে জাতীয় সত্তার প্রধান ভিত্তি হচ্ছে ধর্ম। সেটা যে সত্য নয়, প্রধান ভিত্তি যে ভাষা, সেটা তো অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বের হয়ে এসেছিল বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়েই। সোহরাওয়ার্দী কিন্তু লাহোর প্রস্তাবের ওই মর্মবস্তুটিকে কখনোই খারিজ করে দেননি; জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দ্বিজাতি তত্ত্বকে তিনি সত্য বলে জেনেছেন, যে জন্য পাকিস্তানকে ভাঙা নয়, তাকে রক্ষা করার কাজেই তিনি সচেষ্ট ছিলেন। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান যখন তাঁকে কারারুদ্ধ করেন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান যে অভিযোগ আনা হয়েছিল সেটি হলো, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই, ‘বিশেষ করে গত তিন বছর ধরে, তিনি ভেতরের ও বাইরের পাকিস্তানবিরোধীদের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছেন।’ অভিযোগনামার জবাবে জেলখানা থেকেই সোহরাওয়ার্দী যে জোরালো চিঠিটি লিখেছিলেন তাতে তিনি বলেছেন, এই অভিযোগ পড়ে তিনি যারপরনাই মর্মাহত হয়েছেন। কারণ তিনি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, ‘মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান হচ্ছে এক ও অবিভাজ্য;’ এবং এই বিশ্বাসের দ্বারা তাড়িত হয়েই তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের জীবনকে বিপন্ন করেছেন এবং এখন বার্ধক্যে এসে পৌঁছেছেন। পূর্ব ও পশ্চিমকে একসঙ্গে থাকতে হবে–এই বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হয়েই তিনি কাজ করে গেছেন।
এরপরও তাঁকে যে পাকিস্তানের ঐক্য-বিনষ্টকারী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং সেই অভিযোগে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছে, সেটা কেবল যে দুঃখজনক তা-ই নয়, এর দ্বারা তাঁর যে রাজনৈতিক ‘উপযোগিতা’ (utility) ছিল তা ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। তিনি বলছেন যে, তিনি কখনো পদের জন্য লালায়িত ছিলেন না; কিন্তু তিনি পাকিস্তানের অখণ্ডতা (অবশ্যই এককেন্দ্রিক) রক্ষার জন্য কাজ করতে পারতেন। দুঃখের বিষয় আইয়ুব খান তাঁর সেই উপযোগিতাকে ধ্বংস করে ছেড়েছেন। পাকিস্তানকে তিনি এক জাতির দেশ বলেই মনে করতেন। এখানে আইয়ুব খানের সঙ্গে তাঁর কোনো বিরোধ ছিল না, উভয়েই পাকিস্তানকে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে একত্র রাখতে চেয়েছেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহও এমন একটি অবিচ্ছেদ্য পাকিস্তানি জাতিই তৈরি করবেন বলেই ভেবেছিলেন। স্পষ্টতই আইয়ুব খানের সঙ্গে সোহরাওয়ার্দীর দ্বন্দ্বটা ছিল ক্ষমতা নিয়ে; আইয়ুব সোহরাওয়ার্দীকে মুক্ত রেখে স্বস্তি পাচ্ছিলেন না, কারণ তখন সোহরাওয়ার্দীই ছিলেন তাঁর ক্ষমতায় থাকার প্রতি প্রধান চ্যালেঞ্জ; বিশেষ করে এই জন্য যে, সোহরাওয়ার্দীর প্রতি আমেরিকানদের পক্ষপাতিত্ব আইয়ুবের তুলনায় কিছুটা বেশি ছিল বলেই সন্দেহ হচ্ছিল। আইয়ুব অবশ্য সোহরাওয়ার্দীকে বেশি দিন বন্দী করে রাখতে পারেননি, প্রবল জনপ্রতিবাদের মুখে ১৯৬২ সালের জানুয়ারির শেষ দিনে আটক করে আট মাস যেতে না যেতেই ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তার আগে অবশ্য আইয়ুব তাঁর নিজের রচিত সংবিধানটি ঘোষণা করার কাজটি সম্পন্ন করে নিয়েছিলেন; সে সংবিধানে সংখ্যাসাম্য ও এক ইউনিট, দুটোই ছিল।
লেখক: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
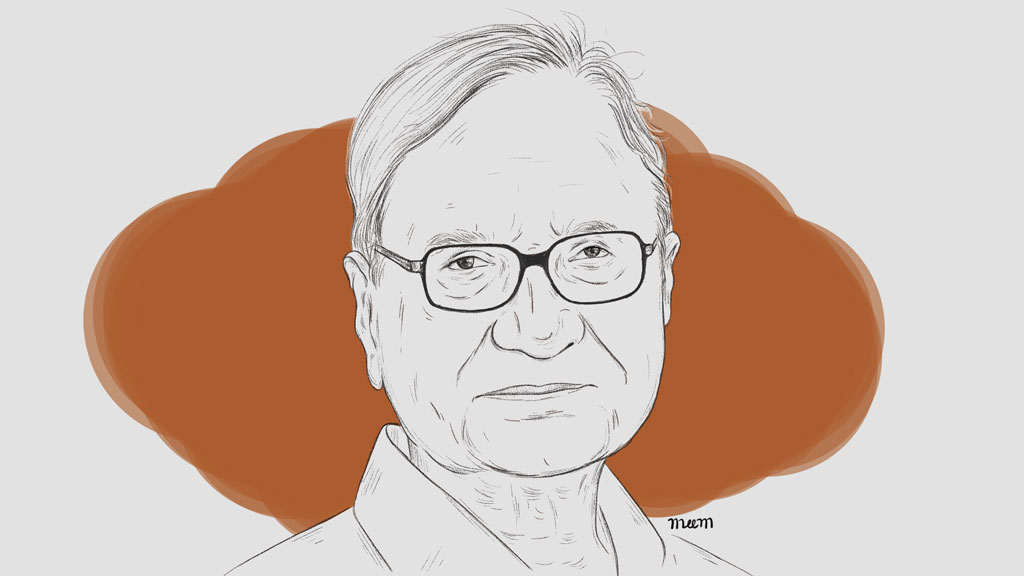
স্বাধীন হওয়ার পরপরই টের পাওয়া গেল যে পূর্ব বাংলা পাঞ্জাব-শাসিত পাকিস্তানের একটি অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ হতে চলেছে। সে জন্যই দাবি উঠেছে স্বায়ত্তশাসনের এবং ওই দাবিকে যৌক্তিক দিক দিয়ে জোরদার করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে আদি লাহোর প্রস্তাবের। বলা হয়ে থাকে, মুসলিম লীগের নেতাদের স্বার্থান্বেষী ও স্বেচ্ছাচারী আচরণে বিক্ষুব্ধ হয়ে সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিমপন্থীরাই উদ্যোগ নিয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তৎপরতাটা সোহরাওয়ার্দীপন্থীদের তুলনায় হাশিমপন্থীদের দিক থেকেই ছিল অধিক উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, সোহরাওয়ার্দী নিজে পূর্ববঙ্গকে নয়, পশ্চিম পাকিস্তানকেই তাঁর কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন; দ্বিতীয়ত, তিনি সেখানে গিয়ে জিন্নাহ-আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে একটি দল গঠন করেছিলেন এবং আশা করছিলেন পূর্ববঙ্গে তার একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হবে। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনে যে তরুণেরা উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন শামসুল হক, যাঁকে দলের সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করা হয়; এবং মতাদর্শিকভাবে শামসুল হক ছিলেন আবুল হাশিমের রব্বানিয়াত দর্শনের অনুসারী। নতুন দলের ঘোষণাপত্রটি শামসুল হকই লিখে থাকবেন। কারণ তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে পাকিস্তান খেলাফত বা আল্লাহর প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র হবে এবং আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতা ও প্রভুত্বের অধিকারী হবে। এটি রব্বানিয়াত দর্শনেরই কথা। তবে ‘মূল দাবি’ হিসেবে শামসুল হক যে লাহোর প্রস্তাবের কথা বলেছেন, সেটা আরও অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর মতে, লাহোর প্রস্তাব ‘সর্বকালের সর্ব যুগের সর্ব দেশের যুগপ্রবর্তক ঘটনাবলির ন্যায় একটি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে।’ মনে হচ্ছে উদ্যোগীদের দৃষ্টিতে লাহোর প্রস্তাব ছিল একটি মহাবৈপ্লবিক ঘটনা। তবে, তাঁদের মতে, মুসলিম লীগ নেতৃত্বের অপারগতার দরুন ওই বিপ্লবের লক্ষ্যগুলো অর্জন করা যেহেতু সম্ভব হয়নি, তাই মুসলিম লীগকে ‘স্বার্থান্বেষী মুষ্টিমেয় লোকদের পকেট হইতে বাহির করিয়া সত্যিকারের জনগণের মুসলিম লীগ হিসেবে গড়ে তোলা আবশ্যক।’ অর্থাৎ কিনা লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়ন চাই। নতুন সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হন মওলানা ভাসানী, এর আগে যিনি আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন এবং মনেপ্রাণে যিনি লাহোর প্রস্তাবের ‘দুই পাকিস্তান’ নীতিতে বিশ্বাস করতেন। যে মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়, সেটির আহ্বান করা হয়েছিল ভাসানীর নামেই; যার প্রতিক্রিয়ায় পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) ও অন্য কয়েকজন কর্মকর্তা মিলে এক বিবৃতিতে জানান যে, ‘মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সাহেবের দ্বারা আগামী ২৩শে ও ২৪শে জুন তারিখে মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলন নামে যে সভা আহূত হইয়াছে, তাহার সহিত মুসলিম লীগের কোন সম্পর্ক নাই। বস্তুত ইহা দলগত স্বার্থ ও ক্ষমতা লাভের জন্য মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির দ্বারা মুসলমান সংহতি নষ্ট করিয়া পাকিস্তানের স্থায়িত্ব ও অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আহূত হইয়াছে।’
নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রাদেশিক মুসলিম লীগের মতো ‘প্রাদেশিক’ ছিল না; ছিল লাহোর প্রস্তাবে যে ধারণা ব্যক্ত হয়েছিল, কল্পনার সেই স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের একটি সংগঠন। মওলানা ভাসানী অবশ্য সোহরাওয়ার্দীকে এর সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। সেটা এই লক্ষ্যে যে পাকিস্তানজুড়ে সংগঠনের বিস্তার ঘটলে মুসলিম লীগের বিরোধী শক্তি হিসেবে এর শক্তি বৃদ্ধি পাবে। সোহরাওয়ার্দী তখন থাকতেন লাহোরে, ভাসানী শেখ মুজিবকে লাহোরে পাঠিয়েছিলেন সোহরাওয়ার্দী ও সম্ভব হলে মিয়া ইফতেখার উদ্দিনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। সেটা ১৯৪৯-এরই ঘটনা। এর পরে ১৯৫২-তে মুজিব আবার পশ্চিম পাকিস্তানে যান; একই উদ্দেশ্যে; সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে দেখা করতে। সোহরাওয়ার্দী তখন তাঁকে জানান যে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পক্ষে পশ্চিমে-গঠিত জিন্নাহ-আওয়ামী মুসলিম লীগের অ্যাফিলিয়েশন নেওয়া দরকার। অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে শেখ মুজিব লিখেছেন, ‘তিনি বললেন, একটা কনফারেন্স ডাকবো, তার আগে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের এ্যাফিলিয়েশন নেওয়া দরকার।’ জবাবে শেখ মুজিব তখন তাঁকে যা বলেছিলেন সেটা এ রকমের:
আমি তাঁকে জানালাম, ‘আপনি জিন্নাহ আওয়ামী লীগ করেছেন, আমরা নাম পরিবর্তন করতে পারব না। কোনো ব্যক্তির নাম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগ করতে চাই না। দ্বিতীয়ত, আমাদের ম্যানিফেস্টো আছে, গঠনতন্ত্র আছে, তার পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। মওলানা সাহেব আমাকে ১৯৪৯ সালে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলেন। তখনও তিনি নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ গঠনের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তাঁরও কোনো আপত্তি থাকবে না যদি আপনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো ও গঠনতন্ত্র মেনে নেন। অনেক আপত্তির পর তিনি মানতে রাজি হলেন এবং নিজ হাতে তাঁর সম্মতির কথা লিখে দিলেন।’
মুজিব লিখেছেন, ‘আমি আর এটাও অনুরোধ করলাম তাঁকে লিখে দিতে যে, উর্দু ও বাংলা দুটোকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে তিনি সমর্থন করেন। কারণ অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে। মুসলিম লীগ ও তথাকথিত প্রগতিশীলরা প্রোপাগান্ডা করছে তাঁর বিরুদ্ধে। [...] তিনি লিখে দিলেন।’
অন্যরা তেমনভাবে খেয়াল না করলেও শেখ মুজিব ঠিকই লক্ষ করছিলেন যে, ‘পূর্ব বাংলার সম্পদকে কেড়ে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানকে কত তাড়াতাড়ি গড়া যায়, একদল পশ্চিমা তথাকথিত নেতা ও বড় বড় সরকারি কর্মচারী গোপনে সে কাজ করে চলছিল। তাদের একটা ধারণা ছিল, পূর্ব বাংলা শেষ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে থাকবে না। তাই যত তাড়াতাড়ি পারা যায় পশ্চিম পাকিস্তানকে গড়ে তুলতে হবে।’
অর্থাৎ লাহোর প্রস্তাবের যে অঙ্গীকার–দুটি স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম পাকিস্তানের, সেটা সব দিক থেকেই অকার্যকর করে তোলা হচ্ছিল। এই উপলব্ধি থেকেই মওলানা ভাসানী ১৯৫৭ সালের কাগমারী সম্মেলনে প্রয়োজনে পশ্চিম পাকিস্তানকে আসসালামু আলাইকুম জানানো হবে বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। শেখ মুজিব সে সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু ১৯৬৬-তে এসেই তাঁর মনে কোনো সংশয় থাকেনি যে পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতিদের সঙ্গে থাকা যাবে না, যে কথা তিনি তখনকার কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের বলেছিলেন এক গোপন বৈঠকে; ১৯৬১ সালের ডিসেম্বরের দিকে।
লাহোর প্রস্তাবের রাজনৈতিক মর্মবস্তুতে অবশ্য আরেকটি জিনিস ছিল, সেটি হলো দ্বিজাতি তত্ত্ব। ভারতবর্ষের মুসলমানরা একটি অভিন্ন ও স্বতন্ত্র জাতি, এই ধারণার ওপর দাঁড়িয়েই লাহোর প্রস্তাব তৈরি করা হয়েছিল। ধরে নেওয়া হয়েছিল যে জাতীয় সত্তার প্রধান ভিত্তি হচ্ছে ধর্ম। সেটা যে সত্য নয়, প্রধান ভিত্তি যে ভাষা, সেটা তো অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বের হয়ে এসেছিল বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়েই। সোহরাওয়ার্দী কিন্তু লাহোর প্রস্তাবের ওই মর্মবস্তুটিকে কখনোই খারিজ করে দেননি; জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দ্বিজাতি তত্ত্বকে তিনি সত্য বলে জেনেছেন, যে জন্য পাকিস্তানকে ভাঙা নয়, তাকে রক্ষা করার কাজেই তিনি সচেষ্ট ছিলেন। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান যখন তাঁকে কারারুদ্ধ করেন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান যে অভিযোগ আনা হয়েছিল সেটি হলো, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই, ‘বিশেষ করে গত তিন বছর ধরে, তিনি ভেতরের ও বাইরের পাকিস্তানবিরোধীদের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছেন।’ অভিযোগনামার জবাবে জেলখানা থেকেই সোহরাওয়ার্দী যে জোরালো চিঠিটি লিখেছিলেন তাতে তিনি বলেছেন, এই অভিযোগ পড়ে তিনি যারপরনাই মর্মাহত হয়েছেন। কারণ তিনি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, ‘মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান হচ্ছে এক ও অবিভাজ্য;’ এবং এই বিশ্বাসের দ্বারা তাড়িত হয়েই তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের জীবনকে বিপন্ন করেছেন এবং এখন বার্ধক্যে এসে পৌঁছেছেন। পূর্ব ও পশ্চিমকে একসঙ্গে থাকতে হবে–এই বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হয়েই তিনি কাজ করে গেছেন।
এরপরও তাঁকে যে পাকিস্তানের ঐক্য-বিনষ্টকারী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং সেই অভিযোগে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছে, সেটা কেবল যে দুঃখজনক তা-ই নয়, এর দ্বারা তাঁর যে রাজনৈতিক ‘উপযোগিতা’ (utility) ছিল তা ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। তিনি বলছেন যে, তিনি কখনো পদের জন্য লালায়িত ছিলেন না; কিন্তু তিনি পাকিস্তানের অখণ্ডতা (অবশ্যই এককেন্দ্রিক) রক্ষার জন্য কাজ করতে পারতেন। দুঃখের বিষয় আইয়ুব খান তাঁর সেই উপযোগিতাকে ধ্বংস করে ছেড়েছেন। পাকিস্তানকে তিনি এক জাতির দেশ বলেই মনে করতেন। এখানে আইয়ুব খানের সঙ্গে তাঁর কোনো বিরোধ ছিল না, উভয়েই পাকিস্তানকে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে একত্র রাখতে চেয়েছেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহও এমন একটি অবিচ্ছেদ্য পাকিস্তানি জাতিই তৈরি করবেন বলেই ভেবেছিলেন। স্পষ্টতই আইয়ুব খানের সঙ্গে সোহরাওয়ার্দীর দ্বন্দ্বটা ছিল ক্ষমতা নিয়ে; আইয়ুব সোহরাওয়ার্দীকে মুক্ত রেখে স্বস্তি পাচ্ছিলেন না, কারণ তখন সোহরাওয়ার্দীই ছিলেন তাঁর ক্ষমতায় থাকার প্রতি প্রধান চ্যালেঞ্জ; বিশেষ করে এই জন্য যে, সোহরাওয়ার্দীর প্রতি আমেরিকানদের পক্ষপাতিত্ব আইয়ুবের তুলনায় কিছুটা বেশি ছিল বলেই সন্দেহ হচ্ছিল। আইয়ুব অবশ্য সোহরাওয়ার্দীকে বেশি দিন বন্দী করে রাখতে পারেননি, প্রবল জনপ্রতিবাদের মুখে ১৯৬২ সালের জানুয়ারির শেষ দিনে আটক করে আট মাস যেতে না যেতেই ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তার আগে অবশ্য আইয়ুব তাঁর নিজের রচিত সংবিধানটি ঘোষণা করার কাজটি সম্পন্ন করে নিয়েছিলেন; সে সংবিধানে সংখ্যাসাম্য ও এক ইউনিট, দুটোই ছিল।
লেখক: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
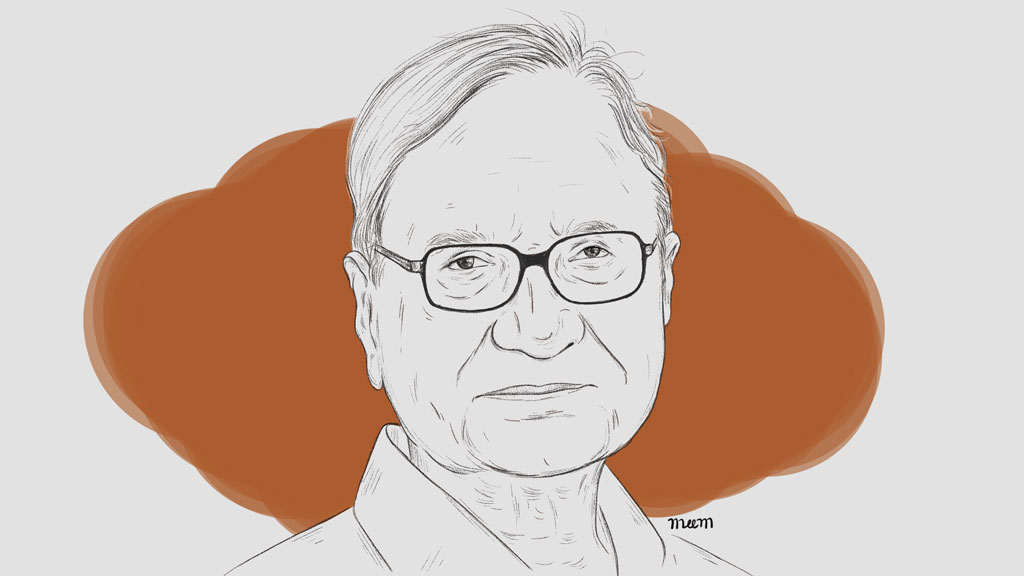
স্বাধীন হওয়ার পরপরই টের পাওয়া গেল যে পূর্ব বাংলা পাঞ্জাব-শাসিত পাকিস্তানের একটি অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ হতে চলেছে। সে জন্যই দাবি উঠেছে স্বায়ত্তশাসনের এবং ওই দাবিকে যৌক্তিক দিক দিয়ে জোরদার করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে আদি লাহোর প্রস্তাবের। বলা হয়ে থাকে, মুসলিম লীগের নেতাদের স্বার্থান্বেষী ও স্বেচ্ছাচারী আচরণে বিক্ষুব্ধ হয়ে সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিমপন্থীরাই উদ্যোগ নিয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তৎপরতাটা সোহরাওয়ার্দীপন্থীদের তুলনায় হাশিমপন্থীদের দিক থেকেই ছিল অধিক উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, সোহরাওয়ার্দী নিজে পূর্ববঙ্গকে নয়, পশ্চিম পাকিস্তানকেই তাঁর কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন; দ্বিতীয়ত, তিনি সেখানে গিয়ে জিন্নাহ-আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে একটি দল গঠন করেছিলেন এবং আশা করছিলেন পূর্ববঙ্গে তার একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হবে। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনে যে তরুণেরা উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন শামসুল হক, যাঁকে দলের সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করা হয়; এবং মতাদর্শিকভাবে শামসুল হক ছিলেন আবুল হাশিমের রব্বানিয়াত দর্শনের অনুসারী। নতুন দলের ঘোষণাপত্রটি শামসুল হকই লিখে থাকবেন। কারণ তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে পাকিস্তান খেলাফত বা আল্লাহর প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র হবে এবং আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতা ও প্রভুত্বের অধিকারী হবে। এটি রব্বানিয়াত দর্শনেরই কথা। তবে ‘মূল দাবি’ হিসেবে শামসুল হক যে লাহোর প্রস্তাবের কথা বলেছেন, সেটা আরও অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর মতে, লাহোর প্রস্তাব ‘সর্বকালের সর্ব যুগের সর্ব দেশের যুগপ্রবর্তক ঘটনাবলির ন্যায় একটি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে।’ মনে হচ্ছে উদ্যোগীদের দৃষ্টিতে লাহোর প্রস্তাব ছিল একটি মহাবৈপ্লবিক ঘটনা। তবে, তাঁদের মতে, মুসলিম লীগ নেতৃত্বের অপারগতার দরুন ওই বিপ্লবের লক্ষ্যগুলো অর্জন করা যেহেতু সম্ভব হয়নি, তাই মুসলিম লীগকে ‘স্বার্থান্বেষী মুষ্টিমেয় লোকদের পকেট হইতে বাহির করিয়া সত্যিকারের জনগণের মুসলিম লীগ হিসেবে গড়ে তোলা আবশ্যক।’ অর্থাৎ কিনা লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়ন চাই। নতুন সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হন মওলানা ভাসানী, এর আগে যিনি আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন এবং মনেপ্রাণে যিনি লাহোর প্রস্তাবের ‘দুই পাকিস্তান’ নীতিতে বিশ্বাস করতেন। যে মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়, সেটির আহ্বান করা হয়েছিল ভাসানীর নামেই; যার প্রতিক্রিয়ায় পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) ও অন্য কয়েকজন কর্মকর্তা মিলে এক বিবৃতিতে জানান যে, ‘মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সাহেবের দ্বারা আগামী ২৩শে ও ২৪শে জুন তারিখে মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলন নামে যে সভা আহূত হইয়াছে, তাহার সহিত মুসলিম লীগের কোন সম্পর্ক নাই। বস্তুত ইহা দলগত স্বার্থ ও ক্ষমতা লাভের জন্য মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির দ্বারা মুসলমান সংহতি নষ্ট করিয়া পাকিস্তানের স্থায়িত্ব ও অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আহূত হইয়াছে।’
নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রাদেশিক মুসলিম লীগের মতো ‘প্রাদেশিক’ ছিল না; ছিল লাহোর প্রস্তাবে যে ধারণা ব্যক্ত হয়েছিল, কল্পনার সেই স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের একটি সংগঠন। মওলানা ভাসানী অবশ্য সোহরাওয়ার্দীকে এর সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। সেটা এই লক্ষ্যে যে পাকিস্তানজুড়ে সংগঠনের বিস্তার ঘটলে মুসলিম লীগের বিরোধী শক্তি হিসেবে এর শক্তি বৃদ্ধি পাবে। সোহরাওয়ার্দী তখন থাকতেন লাহোরে, ভাসানী শেখ মুজিবকে লাহোরে পাঠিয়েছিলেন সোহরাওয়ার্দী ও সম্ভব হলে মিয়া ইফতেখার উদ্দিনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। সেটা ১৯৪৯-এরই ঘটনা। এর পরে ১৯৫২-তে মুজিব আবার পশ্চিম পাকিস্তানে যান; একই উদ্দেশ্যে; সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে দেখা করতে। সোহরাওয়ার্দী তখন তাঁকে জানান যে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পক্ষে পশ্চিমে-গঠিত জিন্নাহ-আওয়ামী মুসলিম লীগের অ্যাফিলিয়েশন নেওয়া দরকার। অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে শেখ মুজিব লিখেছেন, ‘তিনি বললেন, একটা কনফারেন্স ডাকবো, তার আগে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের এ্যাফিলিয়েশন নেওয়া দরকার।’ জবাবে শেখ মুজিব তখন তাঁকে যা বলেছিলেন সেটা এ রকমের:
আমি তাঁকে জানালাম, ‘আপনি জিন্নাহ আওয়ামী লীগ করেছেন, আমরা নাম পরিবর্তন করতে পারব না। কোনো ব্যক্তির নাম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগ করতে চাই না। দ্বিতীয়ত, আমাদের ম্যানিফেস্টো আছে, গঠনতন্ত্র আছে, তার পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। মওলানা সাহেব আমাকে ১৯৪৯ সালে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলেন। তখনও তিনি নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ গঠনের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তাঁরও কোনো আপত্তি থাকবে না যদি আপনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো ও গঠনতন্ত্র মেনে নেন। অনেক আপত্তির পর তিনি মানতে রাজি হলেন এবং নিজ হাতে তাঁর সম্মতির কথা লিখে দিলেন।’
মুজিব লিখেছেন, ‘আমি আর এটাও অনুরোধ করলাম তাঁকে লিখে দিতে যে, উর্দু ও বাংলা দুটোকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে তিনি সমর্থন করেন। কারণ অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে। মুসলিম লীগ ও তথাকথিত প্রগতিশীলরা প্রোপাগান্ডা করছে তাঁর বিরুদ্ধে। [...] তিনি লিখে দিলেন।’
অন্যরা তেমনভাবে খেয়াল না করলেও শেখ মুজিব ঠিকই লক্ষ করছিলেন যে, ‘পূর্ব বাংলার সম্পদকে কেড়ে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানকে কত তাড়াতাড়ি গড়া যায়, একদল পশ্চিমা তথাকথিত নেতা ও বড় বড় সরকারি কর্মচারী গোপনে সে কাজ করে চলছিল। তাদের একটা ধারণা ছিল, পূর্ব বাংলা শেষ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে থাকবে না। তাই যত তাড়াতাড়ি পারা যায় পশ্চিম পাকিস্তানকে গড়ে তুলতে হবে।’
অর্থাৎ লাহোর প্রস্তাবের যে অঙ্গীকার–দুটি স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম পাকিস্তানের, সেটা সব দিক থেকেই অকার্যকর করে তোলা হচ্ছিল। এই উপলব্ধি থেকেই মওলানা ভাসানী ১৯৫৭ সালের কাগমারী সম্মেলনে প্রয়োজনে পশ্চিম পাকিস্তানকে আসসালামু আলাইকুম জানানো হবে বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। শেখ মুজিব সে সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু ১৯৬৬-তে এসেই তাঁর মনে কোনো সংশয় থাকেনি যে পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতিদের সঙ্গে থাকা যাবে না, যে কথা তিনি তখনকার কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের বলেছিলেন এক গোপন বৈঠকে; ১৯৬১ সালের ডিসেম্বরের দিকে।
লাহোর প্রস্তাবের রাজনৈতিক মর্মবস্তুতে অবশ্য আরেকটি জিনিস ছিল, সেটি হলো দ্বিজাতি তত্ত্ব। ভারতবর্ষের মুসলমানরা একটি অভিন্ন ও স্বতন্ত্র জাতি, এই ধারণার ওপর দাঁড়িয়েই লাহোর প্রস্তাব তৈরি করা হয়েছিল। ধরে নেওয়া হয়েছিল যে জাতীয় সত্তার প্রধান ভিত্তি হচ্ছে ধর্ম। সেটা যে সত্য নয়, প্রধান ভিত্তি যে ভাষা, সেটা তো অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বের হয়ে এসেছিল বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়েই। সোহরাওয়ার্দী কিন্তু লাহোর প্রস্তাবের ওই মর্মবস্তুটিকে কখনোই খারিজ করে দেননি; জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দ্বিজাতি তত্ত্বকে তিনি সত্য বলে জেনেছেন, যে জন্য পাকিস্তানকে ভাঙা নয়, তাকে রক্ষা করার কাজেই তিনি সচেষ্ট ছিলেন। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান যখন তাঁকে কারারুদ্ধ করেন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান যে অভিযোগ আনা হয়েছিল সেটি হলো, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই, ‘বিশেষ করে গত তিন বছর ধরে, তিনি ভেতরের ও বাইরের পাকিস্তানবিরোধীদের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছেন।’ অভিযোগনামার জবাবে জেলখানা থেকেই সোহরাওয়ার্দী যে জোরালো চিঠিটি লিখেছিলেন তাতে তিনি বলেছেন, এই অভিযোগ পড়ে তিনি যারপরনাই মর্মাহত হয়েছেন। কারণ তিনি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, ‘মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান হচ্ছে এক ও অবিভাজ্য;’ এবং এই বিশ্বাসের দ্বারা তাড়িত হয়েই তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের জীবনকে বিপন্ন করেছেন এবং এখন বার্ধক্যে এসে পৌঁছেছেন। পূর্ব ও পশ্চিমকে একসঙ্গে থাকতে হবে–এই বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হয়েই তিনি কাজ করে গেছেন।
এরপরও তাঁকে যে পাকিস্তানের ঐক্য-বিনষ্টকারী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং সেই অভিযোগে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছে, সেটা কেবল যে দুঃখজনক তা-ই নয়, এর দ্বারা তাঁর যে রাজনৈতিক ‘উপযোগিতা’ (utility) ছিল তা ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। তিনি বলছেন যে, তিনি কখনো পদের জন্য লালায়িত ছিলেন না; কিন্তু তিনি পাকিস্তানের অখণ্ডতা (অবশ্যই এককেন্দ্রিক) রক্ষার জন্য কাজ করতে পারতেন। দুঃখের বিষয় আইয়ুব খান তাঁর সেই উপযোগিতাকে ধ্বংস করে ছেড়েছেন। পাকিস্তানকে তিনি এক জাতির দেশ বলেই মনে করতেন। এখানে আইয়ুব খানের সঙ্গে তাঁর কোনো বিরোধ ছিল না, উভয়েই পাকিস্তানকে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে একত্র রাখতে চেয়েছেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহও এমন একটি অবিচ্ছেদ্য পাকিস্তানি জাতিই তৈরি করবেন বলেই ভেবেছিলেন। স্পষ্টতই আইয়ুব খানের সঙ্গে সোহরাওয়ার্দীর দ্বন্দ্বটা ছিল ক্ষমতা নিয়ে; আইয়ুব সোহরাওয়ার্দীকে মুক্ত রেখে স্বস্তি পাচ্ছিলেন না, কারণ তখন সোহরাওয়ার্দীই ছিলেন তাঁর ক্ষমতায় থাকার প্রতি প্রধান চ্যালেঞ্জ; বিশেষ করে এই জন্য যে, সোহরাওয়ার্দীর প্রতি আমেরিকানদের পক্ষপাতিত্ব আইয়ুবের তুলনায় কিছুটা বেশি ছিল বলেই সন্দেহ হচ্ছিল। আইয়ুব অবশ্য সোহরাওয়ার্দীকে বেশি দিন বন্দী করে রাখতে পারেননি, প্রবল জনপ্রতিবাদের মুখে ১৯৬২ সালের জানুয়ারির শেষ দিনে আটক করে আট মাস যেতে না যেতেই ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তার আগে অবশ্য আইয়ুব তাঁর নিজের রচিত সংবিধানটি ঘোষণা করার কাজটি সম্পন্ন করে নিয়েছিলেন; সে সংবিধানে সংখ্যাসাম্য ও এক ইউনিট, দুটোই ছিল।
লেখক: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিমের বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তাদের উপনিবেশ দেশগুলোর অধিকাংশকেই স্বাধীনতা দিয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। তবে তারা উপনিবেশ পরিত্যাগ করলেও নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাকে একমুহূর্তের জন্যও বিসর্জন দেয়নি।
২১ ঘণ্টা আগে
আজকের পৃথিবী সত্যিই হাতের মুঠোয়। সকালবেলা ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে আমরা হাতে নিই মোবাইল ফোন। এরপর নোটিফিকেশন, মেসেজ, স্টোরি, ভিডিও—সবকিছু এক স্পর্শেই পাওয়া যায়। কিন্তু এই অগণিত সংযোগের মাঝেই মানুষ যেন ক্রমেই আরও নিঃসঙ্গ হয়ে উঠছে।
২১ ঘণ্টা আগে
কৃষিপ্রযুক্তির প্রসার সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি ধারণা পেয়েছি নেদারল্যান্ডসে গিয়ে। ইউরোপের এই ছোট দেশটি কৃষিতে যতটা সমৃদ্ধ, ততটাই উদ্ভাবনী। যেখানে কৃষি গবেষণা, প্রযুক্তির প্রয়োগ, উৎপাদন ও বিপণন এক সুসমন্বিত চক্রে ঘুরছে নিরবচ্ছিন্নভাবে।
২১ ঘণ্টা আগে
সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ নির্মল সেন লিখেছিলেন, ‘স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই’। কথাটি স্বাধীনতার পরপরই দেশে হইচই ফেলে দেয়। নির্মল সেনের কথাটি সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে ভিন্ন থাকলেও, এরপর নানা ঘটনায় কথাটির প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করার সুযোগ নেই।
২১ ঘণ্টা আগেআবু তাহের খান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিমের বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তাদের উপনিবেশ দেশগুলোর অধিকাংশকেই স্বাধীনতা দিয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। তবে তারা উপনিবেশ পরিত্যাগ করলেও নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাকে একমুহূর্তের জন্যও বিসর্জন দেয়নি। বরং নতুন কৌশলে তাদের আধিপত্যবাদী চিন্তাকে অধিক শক্তিমত্তার সঙ্গে ব্যবহার করছে উপনিবেশিত দেশগুলোয়। নিজেদের প্রযুক্তিগত দক্ষতাকে সম্প্রসারিত করে এর নাম দেয় চতুর্থ শিল্পবিপ্লব। এই চতুর বিশেষণের মাধ্যমে অনগ্রসর দেশগুলোর নানা খাতের বিপুল পরিমাণ সম্পদ নিজেদের দেশে পাচার করা এবং একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করাই হলো এর মূল্য উদ্দেশ্য।
কিন্তু তাদের দ্বারা নীরব শোষণের শিকার দেশের জনগণ বুঝতেই পারে না নতুন ধারার এসব প্রযুক্তি কীভাবে তাদের কষ্টার্জিত সম্পদ নিজেদের অজান্তে অন্য দেশে পাচার করে নিয়ে যাচ্ছে! যেমন ফেসবুক, লিংকডইন, এক্স বা টুইটার ইত্যাদির মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো জনগণকে নেশায় বুঁদ বানিয়ে রেখে তাদের অর্থ কৌশলে হাতিয়ে নিচ্ছে। একইভাবে তারা মুনাফার বিস্তার ও একচেটিয়াত্ব প্রতিষ্ঠা করছে কৃষি খাতে। অনুন্নত দেশগুলোর ভবিষ্যতের কৃষিকে বহুজাতিক কোম্পানির ব্যবসায়িক চক্রের হাতে বৃত্তাবদ্ধ করে ফেলছে। এটা তারা করছে কৃষির প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করে নানা ক্ষতিকর রাসায়নিকের ব্যবহারের চক্রে ফেলে, যা কৃষির প্রাকৃতিক উৎসকে চিরদিনের জন্য ধ্বংস করে দেয়।
১৯৭০-এর দশক থেকেই বিশ্বব্যাপী কৃষি গবেষণার ক্ষেত্রে বড় ধরনের অগ্রগতি সাধিত হয়। ফলে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বহু দেশই কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বড় পরিসরের সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়। কিন্তু ১৯৯০-এর দশকের প্রথমার্ধ থেকে পশ্চিমের দেশগুলোতে বীজ ও অন্যান্য কৃষিসংশ্লিষ্ট জীবের জিন পরিবর্তনের মাধ্যমে জিএমও (জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম) নামের এমন সব নতুন প্রজাতি উদ্ভাবিত হতে থাকে, যেগুলোর সঙ্গে ক্রমান্বয়ে একধরনের পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবসা যুক্ত হয়ে পড়ে। আর এ-জাতীয় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে বাজারজাত করা জিএমওভিত্তিক কৃষি উপকরণ কৃষকের সৃজনশীল চিন্তাভাবনা, জমির উর্বরতা ও কৃষিসংশ্লিষ্ট জীববৈচিত্র্যকে শুধু ধ্বংসের পথেই নিয়ে যায়নি—সংশ্লিষ্ট কৃষককে আর্থিকভাবে সর্বস্বান্ত করে। এর বড় প্রমাণ হলো যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বহুজাতিক কোম্পানি মনসান্টো কর্তৃক ভারতের পাঞ্জাবের তুলাচাষিদের মধ্যে ১৯৯৮ সালে বিটি বীজ সরবরাহ করে তাঁদের সম্পূর্ণভাবে পঙ্গু করে দেওয়া হয়।
একসময়ে পাঞ্জাবের প্রধান অর্থকরী ফসল ছিল তুলা। তুলা চাষের সঙ্গে জড়িত সেখানকার হাজার হাজার চাষি সে সময় মনসান্টোর প্রলোভনের খপ্পরে পড়ে বেশি ফলনের আশায় বিটি বীজ কিনে তাঁদের অধিকাংশ জমিতে বপন করেন। এতে করে প্রথম এক-দুই বছর তাঁরা ভালো ফলনও পান। কিন্তু দুই বছর পরেই তুলার মাঠে সর্বনাশের লক্ষণগুলো একটু একটু করে প্রকাশ পেতে শুরু করে। একসময় দেখা যায়—বিটি প্রজাতির ফসলের বীজ নতুন বীজ হিসেবে ব্যবহার করা যাচ্ছে না। ফলে নতুনভাবে চাষের জন্য তাঁদের উচ্চ দামের মনসান্টোর জিএমও বীজের ওপর নির্ভরশীল হতে হচ্ছে। এ বীজ বপনের পর প্রচলিত ধাঁচের সার, কীটনাশক, বালাইনাশক ইত্যাদি কোনো কাজে আসছে না। তাই সেই কোম্পানির কীটনাশকের ওপর নির্ভরশীল হতে হচ্ছে। এবং এ ক্ষেত্রেও তাঁদের এসব জিএমও উপকরণ মনসান্টো বা তার মনোনীত ডিলারদের কাছ থেকে কিনতে হচ্ছে।
যে জমিতে একবার সেই বীজ ব্যবহার করা হয়েছে, সে জমিতে আর দেশীয় প্রজাতির বীজ ও উপকরণ দ্বারা ফসল ফলানো সম্ভব হচ্ছে না। শেষে দেখা গেছে, এসব বিটি বীজ, সার, কীটনাশক ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা শক্তি ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে।
এরপর পাঞ্জাবের তুলাচাষিদের কয়েক বছরের মধ্যেই তুলা চাষ নিয়ে তাঁদের অতীতের সব গর্ব ও অহংকারকে বিসর্জন দিয়ে অনেকটাই মাথায় হাত দিয়ে পথে বসতে হয়। তুলা আর এখন গম উৎপাদনের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া পাঞ্জাবের এক নম্বর অর্থকরী ফসল নয়।
মনসান্টো ও তাদের সমগোত্রীয় বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এখন বাংলাদেশেও লোভের থাবা বিস্তার করতে শুরু করেছে। বিটি বেগুনসহ বিভিন্ন ফসলের জিএমও প্রজাতি বাংলাদেশের কৃষকদের কাছে গছাবার জন্য এক যুগের বেশি সময় ধরে তারা নাছোড়বান্দার মতো লেগে আছে এবং কৃষকের অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে ইতিমধ্যে তারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে সফলও হয়েছে। আর এটি সম্ভব হয়েছে বস্তুত কতিপয় অতিমুনাফালোভী ব্যবসায়ী ও ন্যূনতম দেশাত্মবোধহীন অসৎ আমলাদের হীন তৎপরতা ও যোগসাজশের কারণে। রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা কি আসলেই জানেন জিএমও বীজ কীভাবে কৃষির অন্তর্গত শক্তিকে তিলে তিলে ধ্বংস করে দিচ্ছে?
বাংলাদেশে বিটি বেগুন চাষের অনুমতি দেওয়া হয় ২০১৩ সালে। পরবর্তী সময়ে সোনালি ধান বা গোল্ডেন রাইস নামের অন্য একটি জিএমও বীজ প্রবর্তনের অনুমতি লাভের জন্য সংশ্লিষ্ট বহুজাতিক কোম্পানির পাশাপাশি খোদ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিআরআরআই) শীর্ষ পর্যায়ের কর্তারাও তদবিরে নামেন। যদিও এ বিষয়ে চূড়ান্ত অনুমোদন এখনো মেলেনি। বস্তুত পরিবেশবাদী সংগঠনগুলোর বাধা ও আপত্তির কারণেই এখন পর্যন্ত তা ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে।
কিন্তু অত্যন্ত হতাশা ও পরিতাপের বিষয় এই যে কোনো প্রকার আলাপ-আলোচনা ও নীতিগত সিদ্ধান্ত ছাড়াই ২০১৬-২০ মেয়াদি দেশের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জিএমওভিত্তিক কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে দৃঢ় অঙ্গীকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, উল্লিখিত সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলটি যাঁরা জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠকে বসে অনুমোদন করেছিলেন, তাঁরা কি সত্যি সত্যি ওই দলিলে জিএমও প্রযুক্তির পক্ষে অঙ্গীকার থাকার বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন? আসলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক নীতিনির্ধারকেরা কত সর্বনাশা সিদ্ধান্ত যে এভাবে নিজেদের অজান্তেই গ্রহণ করছেন, তা বোধকরি তাঁরা নিজেরাও জানেন না।
উল্লেখ্য, পশ্চিমের উন্নত দেশগুলোতে তো বটেই—এমনকি এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অনেক অনুন্নত বা মাঝারি পর্যায়ের দেশের কৃষিতেও জিএমও উপকরণ পুরোপুরি নিষিদ্ধ। পাঞ্জাবের তুলা চাষের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত ইতিমধ্যে তাদের দেশে জিএমওর ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেছে। ফিলিপাইন একেবারে গোড়া থেকেই মার্কিন প্রভাববলয়ের দেশ হওয়ার কারণে মনসান্টোর মতো মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানিকে ঠেকানোর জন্য তাদেরকে আদালত পর্যন্ত যেতে হয়েছে। তারপরও আদালতের সহায়তায় তারা কৃষিতে জিএমওকে ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে চরম দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে জিএমও ঠেকাতে উল্টো এখানে সাধারণ মানুষকেই সরকারের বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে। অথচ হওয়ার কথা ছিল এর বিপরীতটি।
প্রধান উপদেষ্টা প্রায় তাঁর তিন শূন্য তত্ত্বের কথা বলে থাকেন। এ তত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে, দারিদ্র্য দূরীকরণের পাশাপাশি পৃথিবীর পরিবেশকে রক্ষা করা। কিন্তু কৃষিতে জিএমওর প্রবর্তন বন্ধ রাখত সেই তিন শূন্য তত্ত্বেরই সম্পূরক কার্যক্রম। তিনি কেন জিএমওর প্রবর্তন বন্ধ করছেন না? অথচ এ কাজটি করলে কৃষি ও কৃষকের জন্য একটি সুরক্ষামূলক সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য ইতিহাসে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারতেন।
অন্যদিকে জিএমওর ব্যাপারে কৃষকদের মধ্যকার সচেতনতার স্তরও অত্যন্ত নিম্নবর্তী। কৃষকদের মধ্যে উল্লিখিত সচেতনতার স্তর উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বাস্তবে তেমন কিছুই করছে না। এ অবস্থায় কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি খাতসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি অনুরোধ, জিএমওর ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে কৃষকদের এ ব্যাপারে সচেতন করে তুলুন। তাতে আপনাদের দৈনন্দিন কাজের বোঝা অনেকখানি হালকা হয়ে আসবে।
দেশের কৃষি ও কৃষকদের জিএমওর হাত থেকে বাঁচান। নইলে বাংলাদেশের কৃষি খাত অচিরেই মনসান্টোর মতো জিএমও বাজারজাতকারী বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর কাছে জিম্মি হয়ে পড়তে পারে। বিষয়টি দেশের নীতিনির্ধারকেরা যত দ্রুত বুঝবেন, ততই মঙ্গল।
লেখক: সাবেক পরিচালক, বিসিক

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিমের বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তাদের উপনিবেশ দেশগুলোর অধিকাংশকেই স্বাধীনতা দিয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। তবে তারা উপনিবেশ পরিত্যাগ করলেও নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাকে একমুহূর্তের জন্যও বিসর্জন দেয়নি। বরং নতুন কৌশলে তাদের আধিপত্যবাদী চিন্তাকে অধিক শক্তিমত্তার সঙ্গে ব্যবহার করছে উপনিবেশিত দেশগুলোয়। নিজেদের প্রযুক্তিগত দক্ষতাকে সম্প্রসারিত করে এর নাম দেয় চতুর্থ শিল্পবিপ্লব। এই চতুর বিশেষণের মাধ্যমে অনগ্রসর দেশগুলোর নানা খাতের বিপুল পরিমাণ সম্পদ নিজেদের দেশে পাচার করা এবং একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করাই হলো এর মূল্য উদ্দেশ্য।
কিন্তু তাদের দ্বারা নীরব শোষণের শিকার দেশের জনগণ বুঝতেই পারে না নতুন ধারার এসব প্রযুক্তি কীভাবে তাদের কষ্টার্জিত সম্পদ নিজেদের অজান্তে অন্য দেশে পাচার করে নিয়ে যাচ্ছে! যেমন ফেসবুক, লিংকডইন, এক্স বা টুইটার ইত্যাদির মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো জনগণকে নেশায় বুঁদ বানিয়ে রেখে তাদের অর্থ কৌশলে হাতিয়ে নিচ্ছে। একইভাবে তারা মুনাফার বিস্তার ও একচেটিয়াত্ব প্রতিষ্ঠা করছে কৃষি খাতে। অনুন্নত দেশগুলোর ভবিষ্যতের কৃষিকে বহুজাতিক কোম্পানির ব্যবসায়িক চক্রের হাতে বৃত্তাবদ্ধ করে ফেলছে। এটা তারা করছে কৃষির প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করে নানা ক্ষতিকর রাসায়নিকের ব্যবহারের চক্রে ফেলে, যা কৃষির প্রাকৃতিক উৎসকে চিরদিনের জন্য ধ্বংস করে দেয়।
১৯৭০-এর দশক থেকেই বিশ্বব্যাপী কৃষি গবেষণার ক্ষেত্রে বড় ধরনের অগ্রগতি সাধিত হয়। ফলে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বহু দেশই কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বড় পরিসরের সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়। কিন্তু ১৯৯০-এর দশকের প্রথমার্ধ থেকে পশ্চিমের দেশগুলোতে বীজ ও অন্যান্য কৃষিসংশ্লিষ্ট জীবের জিন পরিবর্তনের মাধ্যমে জিএমও (জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম) নামের এমন সব নতুন প্রজাতি উদ্ভাবিত হতে থাকে, যেগুলোর সঙ্গে ক্রমান্বয়ে একধরনের পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবসা যুক্ত হয়ে পড়ে। আর এ-জাতীয় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে বাজারজাত করা জিএমওভিত্তিক কৃষি উপকরণ কৃষকের সৃজনশীল চিন্তাভাবনা, জমির উর্বরতা ও কৃষিসংশ্লিষ্ট জীববৈচিত্র্যকে শুধু ধ্বংসের পথেই নিয়ে যায়নি—সংশ্লিষ্ট কৃষককে আর্থিকভাবে সর্বস্বান্ত করে। এর বড় প্রমাণ হলো যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বহুজাতিক কোম্পানি মনসান্টো কর্তৃক ভারতের পাঞ্জাবের তুলাচাষিদের মধ্যে ১৯৯৮ সালে বিটি বীজ সরবরাহ করে তাঁদের সম্পূর্ণভাবে পঙ্গু করে দেওয়া হয়।
একসময়ে পাঞ্জাবের প্রধান অর্থকরী ফসল ছিল তুলা। তুলা চাষের সঙ্গে জড়িত সেখানকার হাজার হাজার চাষি সে সময় মনসান্টোর প্রলোভনের খপ্পরে পড়ে বেশি ফলনের আশায় বিটি বীজ কিনে তাঁদের অধিকাংশ জমিতে বপন করেন। এতে করে প্রথম এক-দুই বছর তাঁরা ভালো ফলনও পান। কিন্তু দুই বছর পরেই তুলার মাঠে সর্বনাশের লক্ষণগুলো একটু একটু করে প্রকাশ পেতে শুরু করে। একসময় দেখা যায়—বিটি প্রজাতির ফসলের বীজ নতুন বীজ হিসেবে ব্যবহার করা যাচ্ছে না। ফলে নতুনভাবে চাষের জন্য তাঁদের উচ্চ দামের মনসান্টোর জিএমও বীজের ওপর নির্ভরশীল হতে হচ্ছে। এ বীজ বপনের পর প্রচলিত ধাঁচের সার, কীটনাশক, বালাইনাশক ইত্যাদি কোনো কাজে আসছে না। তাই সেই কোম্পানির কীটনাশকের ওপর নির্ভরশীল হতে হচ্ছে। এবং এ ক্ষেত্রেও তাঁদের এসব জিএমও উপকরণ মনসান্টো বা তার মনোনীত ডিলারদের কাছ থেকে কিনতে হচ্ছে।
যে জমিতে একবার সেই বীজ ব্যবহার করা হয়েছে, সে জমিতে আর দেশীয় প্রজাতির বীজ ও উপকরণ দ্বারা ফসল ফলানো সম্ভব হচ্ছে না। শেষে দেখা গেছে, এসব বিটি বীজ, সার, কীটনাশক ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা শক্তি ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে।
এরপর পাঞ্জাবের তুলাচাষিদের কয়েক বছরের মধ্যেই তুলা চাষ নিয়ে তাঁদের অতীতের সব গর্ব ও অহংকারকে বিসর্জন দিয়ে অনেকটাই মাথায় হাত দিয়ে পথে বসতে হয়। তুলা আর এখন গম উৎপাদনের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া পাঞ্জাবের এক নম্বর অর্থকরী ফসল নয়।
মনসান্টো ও তাদের সমগোত্রীয় বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এখন বাংলাদেশেও লোভের থাবা বিস্তার করতে শুরু করেছে। বিটি বেগুনসহ বিভিন্ন ফসলের জিএমও প্রজাতি বাংলাদেশের কৃষকদের কাছে গছাবার জন্য এক যুগের বেশি সময় ধরে তারা নাছোড়বান্দার মতো লেগে আছে এবং কৃষকের অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে ইতিমধ্যে তারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে সফলও হয়েছে। আর এটি সম্ভব হয়েছে বস্তুত কতিপয় অতিমুনাফালোভী ব্যবসায়ী ও ন্যূনতম দেশাত্মবোধহীন অসৎ আমলাদের হীন তৎপরতা ও যোগসাজশের কারণে। রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা কি আসলেই জানেন জিএমও বীজ কীভাবে কৃষির অন্তর্গত শক্তিকে তিলে তিলে ধ্বংস করে দিচ্ছে?
বাংলাদেশে বিটি বেগুন চাষের অনুমতি দেওয়া হয় ২০১৩ সালে। পরবর্তী সময়ে সোনালি ধান বা গোল্ডেন রাইস নামের অন্য একটি জিএমও বীজ প্রবর্তনের অনুমতি লাভের জন্য সংশ্লিষ্ট বহুজাতিক কোম্পানির পাশাপাশি খোদ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিআরআরআই) শীর্ষ পর্যায়ের কর্তারাও তদবিরে নামেন। যদিও এ বিষয়ে চূড়ান্ত অনুমোদন এখনো মেলেনি। বস্তুত পরিবেশবাদী সংগঠনগুলোর বাধা ও আপত্তির কারণেই এখন পর্যন্ত তা ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে।
কিন্তু অত্যন্ত হতাশা ও পরিতাপের বিষয় এই যে কোনো প্রকার আলাপ-আলোচনা ও নীতিগত সিদ্ধান্ত ছাড়াই ২০১৬-২০ মেয়াদি দেশের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জিএমওভিত্তিক কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে দৃঢ় অঙ্গীকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, উল্লিখিত সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলটি যাঁরা জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠকে বসে অনুমোদন করেছিলেন, তাঁরা কি সত্যি সত্যি ওই দলিলে জিএমও প্রযুক্তির পক্ষে অঙ্গীকার থাকার বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন? আসলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক নীতিনির্ধারকেরা কত সর্বনাশা সিদ্ধান্ত যে এভাবে নিজেদের অজান্তেই গ্রহণ করছেন, তা বোধকরি তাঁরা নিজেরাও জানেন না।
উল্লেখ্য, পশ্চিমের উন্নত দেশগুলোতে তো বটেই—এমনকি এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অনেক অনুন্নত বা মাঝারি পর্যায়ের দেশের কৃষিতেও জিএমও উপকরণ পুরোপুরি নিষিদ্ধ। পাঞ্জাবের তুলা চাষের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত ইতিমধ্যে তাদের দেশে জিএমওর ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেছে। ফিলিপাইন একেবারে গোড়া থেকেই মার্কিন প্রভাববলয়ের দেশ হওয়ার কারণে মনসান্টোর মতো মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানিকে ঠেকানোর জন্য তাদেরকে আদালত পর্যন্ত যেতে হয়েছে। তারপরও আদালতের সহায়তায় তারা কৃষিতে জিএমওকে ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে চরম দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে জিএমও ঠেকাতে উল্টো এখানে সাধারণ মানুষকেই সরকারের বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে। অথচ হওয়ার কথা ছিল এর বিপরীতটি।
প্রধান উপদেষ্টা প্রায় তাঁর তিন শূন্য তত্ত্বের কথা বলে থাকেন। এ তত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে, দারিদ্র্য দূরীকরণের পাশাপাশি পৃথিবীর পরিবেশকে রক্ষা করা। কিন্তু কৃষিতে জিএমওর প্রবর্তন বন্ধ রাখত সেই তিন শূন্য তত্ত্বেরই সম্পূরক কার্যক্রম। তিনি কেন জিএমওর প্রবর্তন বন্ধ করছেন না? অথচ এ কাজটি করলে কৃষি ও কৃষকের জন্য একটি সুরক্ষামূলক সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য ইতিহাসে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারতেন।
অন্যদিকে জিএমওর ব্যাপারে কৃষকদের মধ্যকার সচেতনতার স্তরও অত্যন্ত নিম্নবর্তী। কৃষকদের মধ্যে উল্লিখিত সচেতনতার স্তর উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বাস্তবে তেমন কিছুই করছে না। এ অবস্থায় কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি খাতসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি অনুরোধ, জিএমওর ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে কৃষকদের এ ব্যাপারে সচেতন করে তুলুন। তাতে আপনাদের দৈনন্দিন কাজের বোঝা অনেকখানি হালকা হয়ে আসবে।
দেশের কৃষি ও কৃষকদের জিএমওর হাত থেকে বাঁচান। নইলে বাংলাদেশের কৃষি খাত অচিরেই মনসান্টোর মতো জিএমও বাজারজাতকারী বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর কাছে জিম্মি হয়ে পড়তে পারে। বিষয়টি দেশের নীতিনির্ধারকেরা যত দ্রুত বুঝবেন, ততই মঙ্গল।
লেখক: সাবেক পরিচালক, বিসিক
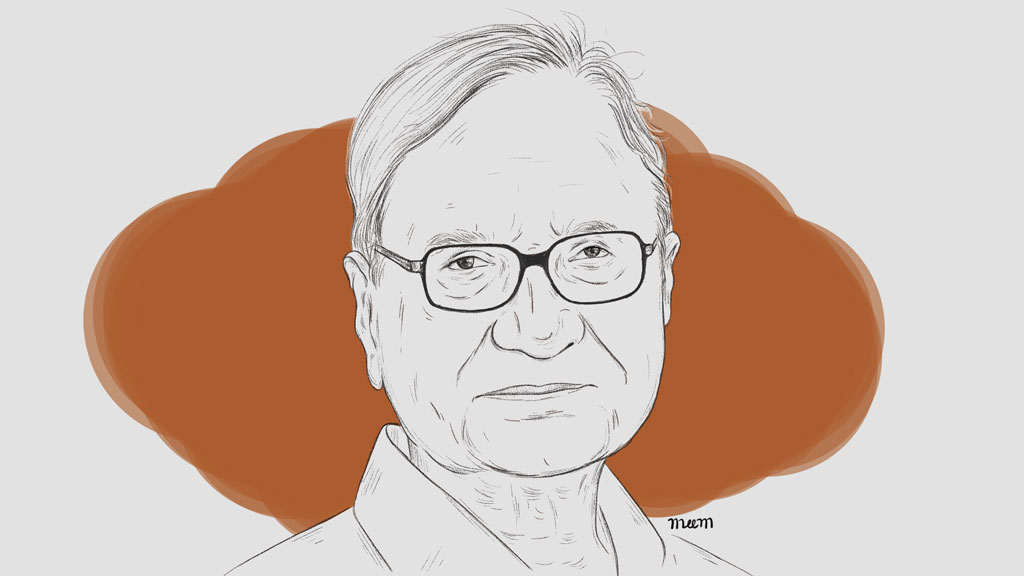
স্বাধীন হওয়ার পরপরই টের পাওয়া গেল যে পূর্ব বাংলা পাঞ্জাব-শাসিত পাকিস্তানের একটি অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ হতে চলেছে। সে জন্যই দাবি উঠেছে স্বায়ত্তশাসনের এবং ওই দাবিকে যৌক্তিক দিক দিয়ে জোরদার করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে আদি লাহোর প্রস্তাবের।
১৮ আগস্ট ২০২১
আজকের পৃথিবী সত্যিই হাতের মুঠোয়। সকালবেলা ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে আমরা হাতে নিই মোবাইল ফোন। এরপর নোটিফিকেশন, মেসেজ, স্টোরি, ভিডিও—সবকিছু এক স্পর্শেই পাওয়া যায়। কিন্তু এই অগণিত সংযোগের মাঝেই মানুষ যেন ক্রমেই আরও নিঃসঙ্গ হয়ে উঠছে।
২১ ঘণ্টা আগে
কৃষিপ্রযুক্তির প্রসার সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি ধারণা পেয়েছি নেদারল্যান্ডসে গিয়ে। ইউরোপের এই ছোট দেশটি কৃষিতে যতটা সমৃদ্ধ, ততটাই উদ্ভাবনী। যেখানে কৃষি গবেষণা, প্রযুক্তির প্রয়োগ, উৎপাদন ও বিপণন এক সুসমন্বিত চক্রে ঘুরছে নিরবচ্ছিন্নভাবে।
২১ ঘণ্টা আগে
সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ নির্মল সেন লিখেছিলেন, ‘স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই’। কথাটি স্বাধীনতার পরপরই দেশে হইচই ফেলে দেয়। নির্মল সেনের কথাটি সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে ভিন্ন থাকলেও, এরপর নানা ঘটনায় কথাটির প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করার সুযোগ নেই।
২১ ঘণ্টা আগেমাহফুজা খাতুন

আজকের পৃথিবী সত্যিই হাতের মুঠোয়। সকালবেলা ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে আমরা হাতে নিই মোবাইল ফোন। এরপর নোটিফিকেশন, মেসেজ, স্টোরি, ভিডিও—সবকিছু এক স্পর্শেই পাওয়া যায়। কিন্তু এই অগণিত সংযোগের মাঝেই মানুষ যেন ক্রমেই আরও নিঃসঙ্গ হয়ে উঠছে। প্রযুক্তি আমাদের কাছাকাছি এনেছে, কিন্তু হৃদয়ের দূরত্ব যেন দিন দিন বেড়েই চলেছে। ফলে একাকিত্ব ডিজিটাল যুগের এক বাস্তবতা হিসেবে হাজির হয়েছে।
একসময় বন্ধুর মানে ছিল একসঙ্গে আড্ডা দেওয়া, গল্প করা এবং মাঠে দল বেঁধে খেলা করা। এখন বন্ধুত্ব মানে জুম কলে দেখা, মেসেঞ্জারে ‘রিঅ্যাক্ট’ দেওয়া কিংবা ফেসবুক-ইনস্টাগ্রামে একে অপরের পোস্টে মন্তব্য করা। এই ভার্চুয়াল যোগাযোগ অনেক সময় আমাদের বাস্তব সম্পর্কের বিকল্প হয়ে উঠেছে। কিন্তু এতে কি সত্যিকারের বন্ধন তৈরি হয়?
গবেষণায় দেখা গেছে, যাঁরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশি সময় ব্যয় করেন, তাঁদের মধ্যে মানসিক চাপ, আত্মসম্মানবোধের ঘাটতি ও একাকিত্বের প্রবণতা তুলনামূলকভাবে বেশি। কারণ, অনলাইন জগৎ এমন এক স্থান যেখানে সবাই নিজেদের সেরা হিসেবে দেখতে এবং উপস্থাপন করতে চায়। এই নিখুঁত জীবনের প্রদর্শনীতে অন্যের জীবনের সঙ্গে নিজের তুলনা করতে করতে অনেকেই হারিয়ে ফেলেন আত্মবিশ্বাস।
যেকোনো ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সবার আগে দেখে নেয় কতজন তার স্টোরিতে ‘ভিউ’ দিয়েছে। সারা দিনের কাজের মধ্যেও বারবার ফোন চেক করে, নতুন মেসেজের অপেক্ষায় থাকে। বাইরে থেকে সে খুবই সক্রিয় ও সংযুক্ত মনে হলেও, দিন শেষে নিজের ঘরে বসে অনুভব করে ভয়ংকর এক নিঃসঙ্গতা। এই চিত্র শুধু তার নয়, এ আমাদের প্রজন্মের গল্প। ডিজিটাল মাধ্যমে যে যত বেশি সক্রিয়, বাস্তবজীবনে সে তত বেশি নিঃসঙ্গ বোধ করে।
মানুষ সামাজিক প্রাণী। যোগাযোগ, সহানুভূতি ও সম্পর্কই তাকে মানসিকভাবে সুস্থ রাখে। কিন্তু ডিজিটাল যুগে এই মৌলিক চাহিদাগুলো ভার্চুয়াল পরিসরে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন, একাকিত্ব মানে কেবল শারীরিকভাবে একা থাকা নয়; বরং মানসিকভাবে বিচ্ছিন্নতা অনুভব করা।
ফেসবুকে হাজার ফ্রেন্ড বা ইনস্টাগ্রামে হাজার ফলোয়ার থাকলেও, কেউ যদি মনের কথা বলার মতো একজনকেও না পায়, তবে সে নিঃসন্দেহে একা। এ একাকিত্ব ধীরে ধীরে তৈরি করে অবসাদ, উদ্বেগ, এমনকি আত্মসম্মানহীনতা।
তবে একে একেবারে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা ঠিক নয়। ডিজিটাল মাধ্যম অনেকের জন্য আশীর্বাদও বটে। দূর দেশে থাকা পরিবার বা প্রবাসী প্রিয়জনদের সঙ্গে যোগাযোগ, অনলাইন সাপোর্ট গ্রুপ, মানসিক স্বাস্থ্য কাউন্সেলিং—এসবই প্রযুক্তির দান। কিন্তু সমস্যা শুরু হয় তখন, যখন বাস্তব সম্পর্কগুলো ভার্চুয়াল সম্পর্কের চাপে ম্লান হয়ে যায়। যখন ফোনের পর্দার মানুষগুলো আমাদের কাছে বাস্তবজীবনের মানুষদের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।
ডিজিটাল যুগে একাকিত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া মানে প্রযুক্তিকে বর্জন নয়; বরং তার সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করা। সপ্তাহে অন্তত এক দিন ডিজিটাল ডিটক্স করুন মানে ফোন, সোশ্যাল মিডিয়া থেকে কিছু সময় দূরে থাকা অভ্যাস গড়ে তুলুন। বন্ধুর সঙ্গে দেখা করা, পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো, মনের কথা মুখে বলা। সর্বোপরি, নিজেকে সময় দেওয়া, বই পড়া, হাঁটাহাঁটি, গান শোনা ও সিনেমা দেখার মাধ্যমে নিজের ভেতরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করুন। কেবল নিজের পোস্টে ‘লাইক’ নয়, অন্যের গল্প মনোযোগ দিয়ে শোনাও একধরনের সংযোগ।
প্রযুক্তি আমাদের জীবনের অপরিহার্য অংশ। কিন্তু যদি আমরা মানবিক সম্পর্কের সেতু হারিয়ে ফেলি। তবে এই অগ্রগতি অর্থহীন। ডিজিটাল যুগের প্রকৃত চ্যালেঞ্জ হলো—সংযোগের ভেতর মানবিকতা ধরে রাখা।
আমরা সবাই অনলাইনে অ্যাক্টিভ বা সক্রিয়, কিন্তু মন থেকে যদি সংযুক্ত না থাকি, তবে একে অপরের জীবনে আমরা কেবল নোটিফিকেশন মাত্র।
লেখক: শিক্ষার্থী, সমাজকর্ম বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

আজকের পৃথিবী সত্যিই হাতের মুঠোয়। সকালবেলা ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে আমরা হাতে নিই মোবাইল ফোন। এরপর নোটিফিকেশন, মেসেজ, স্টোরি, ভিডিও—সবকিছু এক স্পর্শেই পাওয়া যায়। কিন্তু এই অগণিত সংযোগের মাঝেই মানুষ যেন ক্রমেই আরও নিঃসঙ্গ হয়ে উঠছে। প্রযুক্তি আমাদের কাছাকাছি এনেছে, কিন্তু হৃদয়ের দূরত্ব যেন দিন দিন বেড়েই চলেছে। ফলে একাকিত্ব ডিজিটাল যুগের এক বাস্তবতা হিসেবে হাজির হয়েছে।
একসময় বন্ধুর মানে ছিল একসঙ্গে আড্ডা দেওয়া, গল্প করা এবং মাঠে দল বেঁধে খেলা করা। এখন বন্ধুত্ব মানে জুম কলে দেখা, মেসেঞ্জারে ‘রিঅ্যাক্ট’ দেওয়া কিংবা ফেসবুক-ইনস্টাগ্রামে একে অপরের পোস্টে মন্তব্য করা। এই ভার্চুয়াল যোগাযোগ অনেক সময় আমাদের বাস্তব সম্পর্কের বিকল্প হয়ে উঠেছে। কিন্তু এতে কি সত্যিকারের বন্ধন তৈরি হয়?
গবেষণায় দেখা গেছে, যাঁরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশি সময় ব্যয় করেন, তাঁদের মধ্যে মানসিক চাপ, আত্মসম্মানবোধের ঘাটতি ও একাকিত্বের প্রবণতা তুলনামূলকভাবে বেশি। কারণ, অনলাইন জগৎ এমন এক স্থান যেখানে সবাই নিজেদের সেরা হিসেবে দেখতে এবং উপস্থাপন করতে চায়। এই নিখুঁত জীবনের প্রদর্শনীতে অন্যের জীবনের সঙ্গে নিজের তুলনা করতে করতে অনেকেই হারিয়ে ফেলেন আত্মবিশ্বাস।
যেকোনো ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সবার আগে দেখে নেয় কতজন তার স্টোরিতে ‘ভিউ’ দিয়েছে। সারা দিনের কাজের মধ্যেও বারবার ফোন চেক করে, নতুন মেসেজের অপেক্ষায় থাকে। বাইরে থেকে সে খুবই সক্রিয় ও সংযুক্ত মনে হলেও, দিন শেষে নিজের ঘরে বসে অনুভব করে ভয়ংকর এক নিঃসঙ্গতা। এই চিত্র শুধু তার নয়, এ আমাদের প্রজন্মের গল্প। ডিজিটাল মাধ্যমে যে যত বেশি সক্রিয়, বাস্তবজীবনে সে তত বেশি নিঃসঙ্গ বোধ করে।
মানুষ সামাজিক প্রাণী। যোগাযোগ, সহানুভূতি ও সম্পর্কই তাকে মানসিকভাবে সুস্থ রাখে। কিন্তু ডিজিটাল যুগে এই মৌলিক চাহিদাগুলো ভার্চুয়াল পরিসরে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন, একাকিত্ব মানে কেবল শারীরিকভাবে একা থাকা নয়; বরং মানসিকভাবে বিচ্ছিন্নতা অনুভব করা।
ফেসবুকে হাজার ফ্রেন্ড বা ইনস্টাগ্রামে হাজার ফলোয়ার থাকলেও, কেউ যদি মনের কথা বলার মতো একজনকেও না পায়, তবে সে নিঃসন্দেহে একা। এ একাকিত্ব ধীরে ধীরে তৈরি করে অবসাদ, উদ্বেগ, এমনকি আত্মসম্মানহীনতা।
তবে একে একেবারে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা ঠিক নয়। ডিজিটাল মাধ্যম অনেকের জন্য আশীর্বাদও বটে। দূর দেশে থাকা পরিবার বা প্রবাসী প্রিয়জনদের সঙ্গে যোগাযোগ, অনলাইন সাপোর্ট গ্রুপ, মানসিক স্বাস্থ্য কাউন্সেলিং—এসবই প্রযুক্তির দান। কিন্তু সমস্যা শুরু হয় তখন, যখন বাস্তব সম্পর্কগুলো ভার্চুয়াল সম্পর্কের চাপে ম্লান হয়ে যায়। যখন ফোনের পর্দার মানুষগুলো আমাদের কাছে বাস্তবজীবনের মানুষদের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।
ডিজিটাল যুগে একাকিত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া মানে প্রযুক্তিকে বর্জন নয়; বরং তার সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করা। সপ্তাহে অন্তত এক দিন ডিজিটাল ডিটক্স করুন মানে ফোন, সোশ্যাল মিডিয়া থেকে কিছু সময় দূরে থাকা অভ্যাস গড়ে তুলুন। বন্ধুর সঙ্গে দেখা করা, পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো, মনের কথা মুখে বলা। সর্বোপরি, নিজেকে সময় দেওয়া, বই পড়া, হাঁটাহাঁটি, গান শোনা ও সিনেমা দেখার মাধ্যমে নিজের ভেতরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করুন। কেবল নিজের পোস্টে ‘লাইক’ নয়, অন্যের গল্প মনোযোগ দিয়ে শোনাও একধরনের সংযোগ।
প্রযুক্তি আমাদের জীবনের অপরিহার্য অংশ। কিন্তু যদি আমরা মানবিক সম্পর্কের সেতু হারিয়ে ফেলি। তবে এই অগ্রগতি অর্থহীন। ডিজিটাল যুগের প্রকৃত চ্যালেঞ্জ হলো—সংযোগের ভেতর মানবিকতা ধরে রাখা।
আমরা সবাই অনলাইনে অ্যাক্টিভ বা সক্রিয়, কিন্তু মন থেকে যদি সংযুক্ত না থাকি, তবে একে অপরের জীবনে আমরা কেবল নোটিফিকেশন মাত্র।
লেখক: শিক্ষার্থী, সমাজকর্ম বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
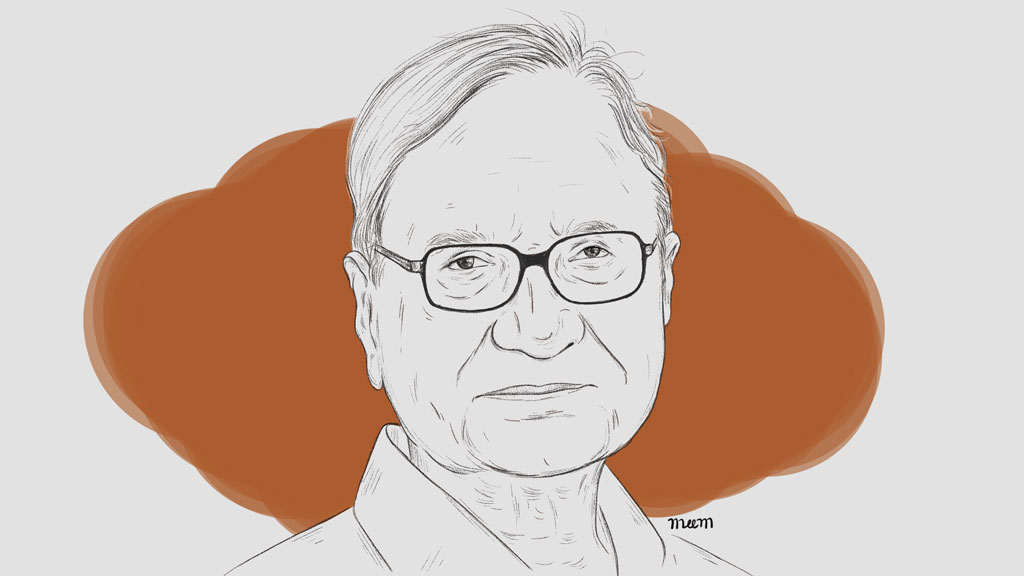
স্বাধীন হওয়ার পরপরই টের পাওয়া গেল যে পূর্ব বাংলা পাঞ্জাব-শাসিত পাকিস্তানের একটি অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ হতে চলেছে। সে জন্যই দাবি উঠেছে স্বায়ত্তশাসনের এবং ওই দাবিকে যৌক্তিক দিক দিয়ে জোরদার করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে আদি লাহোর প্রস্তাবের।
১৮ আগস্ট ২০২১
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিমের বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তাদের উপনিবেশ দেশগুলোর অধিকাংশকেই স্বাধীনতা দিয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। তবে তারা উপনিবেশ পরিত্যাগ করলেও নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাকে একমুহূর্তের জন্যও বিসর্জন দেয়নি।
২১ ঘণ্টা আগে
কৃষিপ্রযুক্তির প্রসার সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি ধারণা পেয়েছি নেদারল্যান্ডসে গিয়ে। ইউরোপের এই ছোট দেশটি কৃষিতে যতটা সমৃদ্ধ, ততটাই উদ্ভাবনী। যেখানে কৃষি গবেষণা, প্রযুক্তির প্রয়োগ, উৎপাদন ও বিপণন এক সুসমন্বিত চক্রে ঘুরছে নিরবচ্ছিন্নভাবে।
২১ ঘণ্টা আগে
সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ নির্মল সেন লিখেছিলেন, ‘স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই’। কথাটি স্বাধীনতার পরপরই দেশে হইচই ফেলে দেয়। নির্মল সেনের কথাটি সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে ভিন্ন থাকলেও, এরপর নানা ঘটনায় কথাটির প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করার সুযোগ নেই।
২১ ঘণ্টা আগেশাইখ সিরাজ

কৃষিপ্রযুক্তির প্রসার সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি ধারণা পেয়েছি নেদারল্যান্ডসে গিয়ে। ইউরোপের এই ছোট দেশটি কৃষিতে যতটা সমৃদ্ধ, ততটাই উদ্ভাবনী। যেখানে কৃষি গবেষণা, প্রযুক্তির প্রয়োগ, উৎপাদন ও বিপণন এক সুসমন্বিত চক্রে ঘুরছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। ২০১৫ সালে যখন প্রথম সেখানে যাই, তখনো বিস্ময়ে ভরে গিয়েছিল মন। সাত বছর পর ২০২২ সালে গিয়ে দেখলাম—তাদের অগ্রগতির গতি আরও বহুগুণ বেড়ে গেছে।
এক উজ্জ্বল রোদের দিন, নীল আকাশের নিচে আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম আমাদের নির্ধারিত গাড়িতে। গন্তব্য—অ্যাগ্রোপার্ক লিংগেজেন। পথে যেতে যেতে ভাবছিলাম, কৃষিতে এমন প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিকায়ন কীভাবে সম্ভব হলো নেদারল্যান্ডসে? কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম এডে সেন্ট্রাল স্টেশনে, যেখানে আমাদের স্বাগত জানালেন ড. পিটার স্মিটস, সেদিনের গাইড ও হোস্ট। ষাটোর্ধ্ব এই ভদ্রলোকের চেহারায় বয়সের রেখা থাকলেও তাঁর চলন-বলনে ছিল এক অনন্য তারুণ্য।
পিটার আমাদের জানালেন, খাদ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণে জৈব নিরাপত্তার কারণে নেদারল্যান্ডসে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাইরের লোকজনকে উৎপাদনকেন্দ্রের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় না। ফলে বেশির ভাগ জায়গাই আমাদের দেখতে হবে গাড়ি থেকে। শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কারণ, একজন টেলিভিশন সাংবাদিক হিসেবে আমি চেয়েছিলাম দর্শকদের ক্যামেরার চোখে দেখাতে, কীভাবে কাজ করছে আধুনিক ইউরোপের কৃষি।
প্রথম গন্তব্য ছিল ভেনলো এলাকার ‘ফ্রেশ পার্ক’। এলাকাটা আমাদের দেশের শিল্পনগরীর মতোই, এটি একধরনের কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ পার্ক। গ্রিনহাউস বা খামার থেকে আসা কৃষিপণ্য এখানে সর্টিং, প্যাকেজিং ও ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য আসে। বড় বড় লরি পণ্য নিয়ে ছুটে চলে বিভিন্ন দেশে। গাড়ির ভেতর বসে পিটার আমাদের জানালেন, এখান থেকেই তাজা সবজি ও ফল বিদেশে যায়। নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রা ও আর্দ্রতায় রাখা হয় প্রতিটি পণ্যকে সতেজ রাখার জন্য।
একপর্যায়ে দূরের এক ভবন দেখিয়ে পিটার বললেন, ওটা রয়্যাল জন, একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান। ষাটের দশকে কিছু কৃষক মিলে শুরু করেছিলেন। এখন তাঁদের সঙ্গে যুক্ত চার শতাধিক কৃষক। প্রতিদিন সকালে অনলাইনে অকশন হয়, সারা দিন ধরে সেই পণ্য দেশের বাজারে ও বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।
বাইরে থেকে দেখা যতটুকু সম্ভব দেখলাম। ভেতরে খুব কম মানুষ, সবকিছু করছে রোবট। পুরো প্রক্রিয়া অটোমেটেড। প্রযুক্তির শৃঙ্খলা ও কার্যকারিতা দেখে সত্যিই মুগ্ধ হতে হয়।
তারপর আমাদের গাড়ি চলল বারেনড্রেখ্টের দিকে। সেখানে বিশাল বিশাল সব গ্রিনহাউস। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় বড় বড় সব কারখানা। কারখানাই বটে, তবে ফসল উৎপাদনের কারখানা। পিটার বলছিলেন, এখানে কোনো গ্রিনহাউসই ৫ হেক্টরের কম নয়। সকালের রোদ পড়ে চিকচিক করে উঠছে একেকটা গ্রিনহাউস। সারি সারি অসংখ্য গ্রিনহাউস। ২০১৪-১৫ সালের দিকে নেদারল্যান্ডসে এত বেশি গ্রিনহাউস নির্মাণের হিড়িক পড়ে যে নেদারল্যান্ডস পরিচিত হয়ে উঠছিল গ্লাস হাউসের দেশ হিসেবে। পরবর্তী সময়ে গ্রিনহাউস নির্মাণে নিয়ন্ত্রণ আনা হয়। পিটার আমাদের পুনরায় হতাশ করলেন। বললেন, এখানেও কোনো গ্রিনহাউসে আপনারা প্রবেশ করতে পারবেন না। বাইরে থেকে দেখতে পাচ্ছি গ্রিনহাউসের কোনোটিতে শসা, কোনোটিতে টমেটো, কোনোটিতে ক্যাপসিকাম চাষ হচ্ছে। কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করে তাঁদের চাষপদ্ধতি আমার দেশের কৃষককে দেখাতে পারব না। কোনো মানে হয়! পিটারকে বুঝিয়ে বললাম, আমি যদি ক্যামেরায় কোনো কিছু ধারণ করতে না পারি, আমার দর্শককে না দেখাতে পারলে শুধু বাইরে থেকে আমি দেখে গেলে লাভ কী?
পিটার ব্যাপারটা বুঝলেন। কারও সঙ্গে ফোনে কথা বললেন। আমাদের জানালেন, ‘ঠিক আছে, আপনাদের একটা ক্যাপসিকামের গ্রিনহাউসে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছি। তবে কোনো কিছুতেই হাত দেওয়া যাবে না। নির্দিষ্ট লাইন অতিক্রম করা যাবে না।’ আমরা রাজি হলাম। কোনো কিছুতেই হাত দেব না। কোনো সীমাই আমরা অতিক্রম করব না। কেবল ক্যামেরায় দর্শকদের জন্য ভিডিও ফুটেজ ধারণ করব।
অবশেষে আমরা পৌঁছালাম বেমোলে, ফির্মা ফান ডার হার্ঘ নামের একটি গ্রিনহাউসে। ওখানে প্রবেশের অনুমতি পেলাম। ভেতরে ঢোকার আগে পিটার দেখালেন কার্বন ডাই-অক্সাইডের বড় ট্যাংক। বললেন, ‘ফসল বৃদ্ধিতে অতিরিক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইডের প্রয়োজন হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস পুড়িয়ে আমরা বিদ্যুৎ, তাপ ও কার্বন ডাই-অক্সাইড পাই। বিদ্যুৎ যায় জাতীয় গ্রিডে, তাপ ব্যবহৃত হয় গ্রিনহাউসে, আর কার্বন ডাই-অক্সাইড সংরক্ষিত থাকে এমন ট্যাংকে।’
ভেতরে ঢুকে দেখা হলো ইয়ন ফান ডের অলেখ-এর সঙ্গে। তিনিই গ্রিনহাউসের তরুণ মালিক। অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও উদ্যমী মানুষ। তাঁর সঙ্গে কথোপকথন থেকে জানতে পারলাম, গ্রিনহাউসটির জমির আয়তন ৮.৬ হেক্টর, গাছের সংখ্যা প্রায় দুই লাখ, বার্ষিক উৎপাদন ২৫০০ টন লাল ক্যাপসিকাম, ফসলের সময়কাল ডিসেম্বর থেকে অক্টোবর পর্যন্ত।
ইয়ন জানালেন, ‘সবকিছুই কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত। সেচ, সার, পুষ্টি—সব নির্ধারিত হয় সফটওয়্যারের নির্দেশে। আমরা মূলত ‘ড্রিপ ওয়াটার ইরিগেশন’ ব্যবহার করি। পানির সঙ্গে মিশে থাকে সার ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট। একফোঁটাও অপচয় হয় না।’
তিনি আরও বললেন, ‘আমরা বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করি, সেটিই সেচে ব্যবহার হয়। এমনকি তাপ নিয়ন্ত্রণ ও আলোর ব্যবস্থাও রোবট দ্বারা সম্পন্ন হয়।’ সত্যিই, এই গ্রিনহাউস যেন প্রযুক্তির এক নিখুঁত সাম্রাজ্য, যেখানে মানুষ কেবল নিয়ন্ত্রক, শ্রমিক নয়।
সবচেয়ে অবাক লাগল তাঁদের বায়োপেস্ট কন্ট্রোল পদ্ধতি দেখে। ইয়ন বললেন, ‘আমরা কোনো রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করি না। উপকারী পোকাই ক্ষতিকর পোকা খেয়ে ফেলে। লুপারস, হোয়াইট ফ্লাই বা স্পাইডার মাইট দমন করা হয় এমন পদ্ধতিতে।’ আমি অবাক হয়ে বললাম, অর্থাৎ পোকা খায় পোকাকে? তিনি হেসে উত্তর দিলেন, ঠিক তাই!
এই দৃশ্যগুলো দেখে আমি বুঝেছিলাম, উন্নত জাতি মানেই শুধু অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নয়, বরং নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তাও। নেদারল্যান্ডস প্রমাণ করেছে—প্রযুক্তি, দক্ষতা আর সততার সমন্বয় ঘটালে কৃষি হতে পারে এক সমৃদ্ধ শিল্প।
আজ যখন বিশ্বের নানা দেশে খাদ্যনিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিচ্ছে, তখন নেদারল্যান্ডসের মতো দেশগুলো দেখিয়ে দিচ্ছে পথ—কীভাবে পরিবেশ রক্ষা করেও উৎপাদন বাড়ানো যায়। তাদের কৃষি মডেল শুধু প্রযুক্তিনির্ভর নয়, এটি টেকসই উন্নয়নেরও প্রতিচ্ছবি।
বাংলাদেশেও আমরা যদি কৃষিতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনকে আরও শক্তভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি, তবে কৃষি যেমন জীবিকার উৎস, তেমনি এটি হতে পারে শক্তিশালী অর্থনীতির ভিত্তিও।
লেখক: পরিচালক ও বার্তাপ্রধান, চ্যানেল আই

কৃষিপ্রযুক্তির প্রসার সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি ধারণা পেয়েছি নেদারল্যান্ডসে গিয়ে। ইউরোপের এই ছোট দেশটি কৃষিতে যতটা সমৃদ্ধ, ততটাই উদ্ভাবনী। যেখানে কৃষি গবেষণা, প্রযুক্তির প্রয়োগ, উৎপাদন ও বিপণন এক সুসমন্বিত চক্রে ঘুরছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। ২০১৫ সালে যখন প্রথম সেখানে যাই, তখনো বিস্ময়ে ভরে গিয়েছিল মন। সাত বছর পর ২০২২ সালে গিয়ে দেখলাম—তাদের অগ্রগতির গতি আরও বহুগুণ বেড়ে গেছে।
এক উজ্জ্বল রোদের দিন, নীল আকাশের নিচে আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম আমাদের নির্ধারিত গাড়িতে। গন্তব্য—অ্যাগ্রোপার্ক লিংগেজেন। পথে যেতে যেতে ভাবছিলাম, কৃষিতে এমন প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিকায়ন কীভাবে সম্ভব হলো নেদারল্যান্ডসে? কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম এডে সেন্ট্রাল স্টেশনে, যেখানে আমাদের স্বাগত জানালেন ড. পিটার স্মিটস, সেদিনের গাইড ও হোস্ট। ষাটোর্ধ্ব এই ভদ্রলোকের চেহারায় বয়সের রেখা থাকলেও তাঁর চলন-বলনে ছিল এক অনন্য তারুণ্য।
পিটার আমাদের জানালেন, খাদ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণে জৈব নিরাপত্তার কারণে নেদারল্যান্ডসে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাইরের লোকজনকে উৎপাদনকেন্দ্রের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় না। ফলে বেশির ভাগ জায়গাই আমাদের দেখতে হবে গাড়ি থেকে। শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কারণ, একজন টেলিভিশন সাংবাদিক হিসেবে আমি চেয়েছিলাম দর্শকদের ক্যামেরার চোখে দেখাতে, কীভাবে কাজ করছে আধুনিক ইউরোপের কৃষি।
প্রথম গন্তব্য ছিল ভেনলো এলাকার ‘ফ্রেশ পার্ক’। এলাকাটা আমাদের দেশের শিল্পনগরীর মতোই, এটি একধরনের কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ পার্ক। গ্রিনহাউস বা খামার থেকে আসা কৃষিপণ্য এখানে সর্টিং, প্যাকেজিং ও ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য আসে। বড় বড় লরি পণ্য নিয়ে ছুটে চলে বিভিন্ন দেশে। গাড়ির ভেতর বসে পিটার আমাদের জানালেন, এখান থেকেই তাজা সবজি ও ফল বিদেশে যায়। নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রা ও আর্দ্রতায় রাখা হয় প্রতিটি পণ্যকে সতেজ রাখার জন্য।
একপর্যায়ে দূরের এক ভবন দেখিয়ে পিটার বললেন, ওটা রয়্যাল জন, একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান। ষাটের দশকে কিছু কৃষক মিলে শুরু করেছিলেন। এখন তাঁদের সঙ্গে যুক্ত চার শতাধিক কৃষক। প্রতিদিন সকালে অনলাইনে অকশন হয়, সারা দিন ধরে সেই পণ্য দেশের বাজারে ও বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।
বাইরে থেকে দেখা যতটুকু সম্ভব দেখলাম। ভেতরে খুব কম মানুষ, সবকিছু করছে রোবট। পুরো প্রক্রিয়া অটোমেটেড। প্রযুক্তির শৃঙ্খলা ও কার্যকারিতা দেখে সত্যিই মুগ্ধ হতে হয়।
তারপর আমাদের গাড়ি চলল বারেনড্রেখ্টের দিকে। সেখানে বিশাল বিশাল সব গ্রিনহাউস। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় বড় বড় সব কারখানা। কারখানাই বটে, তবে ফসল উৎপাদনের কারখানা। পিটার বলছিলেন, এখানে কোনো গ্রিনহাউসই ৫ হেক্টরের কম নয়। সকালের রোদ পড়ে চিকচিক করে উঠছে একেকটা গ্রিনহাউস। সারি সারি অসংখ্য গ্রিনহাউস। ২০১৪-১৫ সালের দিকে নেদারল্যান্ডসে এত বেশি গ্রিনহাউস নির্মাণের হিড়িক পড়ে যে নেদারল্যান্ডস পরিচিত হয়ে উঠছিল গ্লাস হাউসের দেশ হিসেবে। পরবর্তী সময়ে গ্রিনহাউস নির্মাণে নিয়ন্ত্রণ আনা হয়। পিটার আমাদের পুনরায় হতাশ করলেন। বললেন, এখানেও কোনো গ্রিনহাউসে আপনারা প্রবেশ করতে পারবেন না। বাইরে থেকে দেখতে পাচ্ছি গ্রিনহাউসের কোনোটিতে শসা, কোনোটিতে টমেটো, কোনোটিতে ক্যাপসিকাম চাষ হচ্ছে। কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করে তাঁদের চাষপদ্ধতি আমার দেশের কৃষককে দেখাতে পারব না। কোনো মানে হয়! পিটারকে বুঝিয়ে বললাম, আমি যদি ক্যামেরায় কোনো কিছু ধারণ করতে না পারি, আমার দর্শককে না দেখাতে পারলে শুধু বাইরে থেকে আমি দেখে গেলে লাভ কী?
পিটার ব্যাপারটা বুঝলেন। কারও সঙ্গে ফোনে কথা বললেন। আমাদের জানালেন, ‘ঠিক আছে, আপনাদের একটা ক্যাপসিকামের গ্রিনহাউসে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছি। তবে কোনো কিছুতেই হাত দেওয়া যাবে না। নির্দিষ্ট লাইন অতিক্রম করা যাবে না।’ আমরা রাজি হলাম। কোনো কিছুতেই হাত দেব না। কোনো সীমাই আমরা অতিক্রম করব না। কেবল ক্যামেরায় দর্শকদের জন্য ভিডিও ফুটেজ ধারণ করব।
অবশেষে আমরা পৌঁছালাম বেমোলে, ফির্মা ফান ডার হার্ঘ নামের একটি গ্রিনহাউসে। ওখানে প্রবেশের অনুমতি পেলাম। ভেতরে ঢোকার আগে পিটার দেখালেন কার্বন ডাই-অক্সাইডের বড় ট্যাংক। বললেন, ‘ফসল বৃদ্ধিতে অতিরিক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইডের প্রয়োজন হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস পুড়িয়ে আমরা বিদ্যুৎ, তাপ ও কার্বন ডাই-অক্সাইড পাই। বিদ্যুৎ যায় জাতীয় গ্রিডে, তাপ ব্যবহৃত হয় গ্রিনহাউসে, আর কার্বন ডাই-অক্সাইড সংরক্ষিত থাকে এমন ট্যাংকে।’
ভেতরে ঢুকে দেখা হলো ইয়ন ফান ডের অলেখ-এর সঙ্গে। তিনিই গ্রিনহাউসের তরুণ মালিক। অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও উদ্যমী মানুষ। তাঁর সঙ্গে কথোপকথন থেকে জানতে পারলাম, গ্রিনহাউসটির জমির আয়তন ৮.৬ হেক্টর, গাছের সংখ্যা প্রায় দুই লাখ, বার্ষিক উৎপাদন ২৫০০ টন লাল ক্যাপসিকাম, ফসলের সময়কাল ডিসেম্বর থেকে অক্টোবর পর্যন্ত।
ইয়ন জানালেন, ‘সবকিছুই কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত। সেচ, সার, পুষ্টি—সব নির্ধারিত হয় সফটওয়্যারের নির্দেশে। আমরা মূলত ‘ড্রিপ ওয়াটার ইরিগেশন’ ব্যবহার করি। পানির সঙ্গে মিশে থাকে সার ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট। একফোঁটাও অপচয় হয় না।’
তিনি আরও বললেন, ‘আমরা বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করি, সেটিই সেচে ব্যবহার হয়। এমনকি তাপ নিয়ন্ত্রণ ও আলোর ব্যবস্থাও রোবট দ্বারা সম্পন্ন হয়।’ সত্যিই, এই গ্রিনহাউস যেন প্রযুক্তির এক নিখুঁত সাম্রাজ্য, যেখানে মানুষ কেবল নিয়ন্ত্রক, শ্রমিক নয়।
সবচেয়ে অবাক লাগল তাঁদের বায়োপেস্ট কন্ট্রোল পদ্ধতি দেখে। ইয়ন বললেন, ‘আমরা কোনো রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করি না। উপকারী পোকাই ক্ষতিকর পোকা খেয়ে ফেলে। লুপারস, হোয়াইট ফ্লাই বা স্পাইডার মাইট দমন করা হয় এমন পদ্ধতিতে।’ আমি অবাক হয়ে বললাম, অর্থাৎ পোকা খায় পোকাকে? তিনি হেসে উত্তর দিলেন, ঠিক তাই!
এই দৃশ্যগুলো দেখে আমি বুঝেছিলাম, উন্নত জাতি মানেই শুধু অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নয়, বরং নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তাও। নেদারল্যান্ডস প্রমাণ করেছে—প্রযুক্তি, দক্ষতা আর সততার সমন্বয় ঘটালে কৃষি হতে পারে এক সমৃদ্ধ শিল্প।
আজ যখন বিশ্বের নানা দেশে খাদ্যনিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিচ্ছে, তখন নেদারল্যান্ডসের মতো দেশগুলো দেখিয়ে দিচ্ছে পথ—কীভাবে পরিবেশ রক্ষা করেও উৎপাদন বাড়ানো যায়। তাদের কৃষি মডেল শুধু প্রযুক্তিনির্ভর নয়, এটি টেকসই উন্নয়নেরও প্রতিচ্ছবি।
বাংলাদেশেও আমরা যদি কৃষিতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনকে আরও শক্তভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি, তবে কৃষি যেমন জীবিকার উৎস, তেমনি এটি হতে পারে শক্তিশালী অর্থনীতির ভিত্তিও।
লেখক: পরিচালক ও বার্তাপ্রধান, চ্যানেল আই
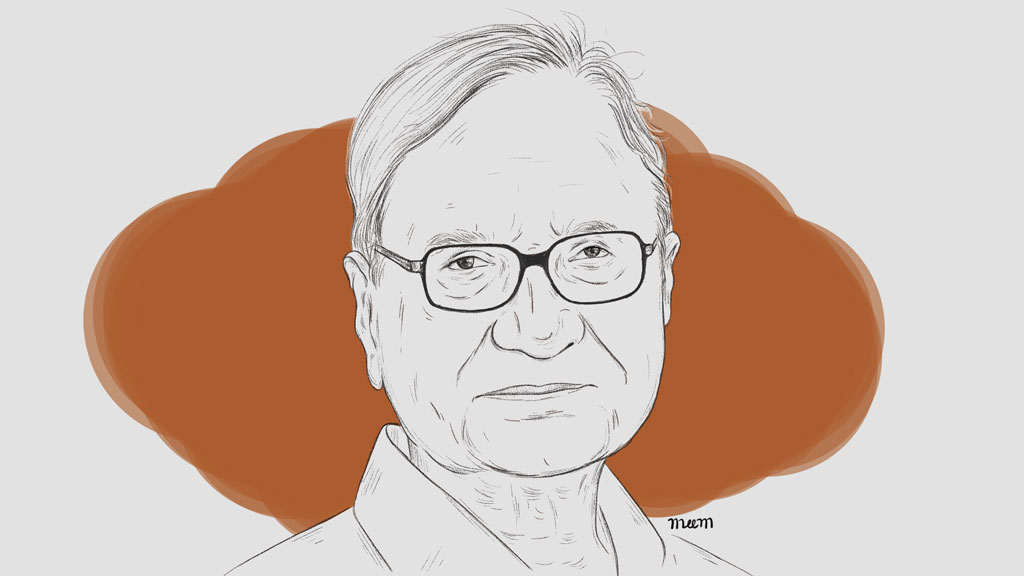
স্বাধীন হওয়ার পরপরই টের পাওয়া গেল যে পূর্ব বাংলা পাঞ্জাব-শাসিত পাকিস্তানের একটি অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ হতে চলেছে। সে জন্যই দাবি উঠেছে স্বায়ত্তশাসনের এবং ওই দাবিকে যৌক্তিক দিক দিয়ে জোরদার করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে আদি লাহোর প্রস্তাবের।
১৮ আগস্ট ২০২১
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিমের বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তাদের উপনিবেশ দেশগুলোর অধিকাংশকেই স্বাধীনতা দিয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। তবে তারা উপনিবেশ পরিত্যাগ করলেও নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাকে একমুহূর্তের জন্যও বিসর্জন দেয়নি।
২১ ঘণ্টা আগে
আজকের পৃথিবী সত্যিই হাতের মুঠোয়। সকালবেলা ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে আমরা হাতে নিই মোবাইল ফোন। এরপর নোটিফিকেশন, মেসেজ, স্টোরি, ভিডিও—সবকিছু এক স্পর্শেই পাওয়া যায়। কিন্তু এই অগণিত সংযোগের মাঝেই মানুষ যেন ক্রমেই আরও নিঃসঙ্গ হয়ে উঠছে।
২১ ঘণ্টা আগে
সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ নির্মল সেন লিখেছিলেন, ‘স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই’। কথাটি স্বাধীনতার পরপরই দেশে হইচই ফেলে দেয়। নির্মল সেনের কথাটি সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে ভিন্ন থাকলেও, এরপর নানা ঘটনায় কথাটির প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করার সুযোগ নেই।
২১ ঘণ্টা আগেসম্পাদকীয়

সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ নির্মল সেন লিখেছিলেন, ‘স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই’। কথাটি স্বাধীনতার পরপরই দেশে হইচই ফেলে দেয়। নির্মল সেনের কথাটি সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে ভিন্ন থাকলেও, এরপর নানা ঘটনায় কথাটির প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। যতই দিন যাচ্ছে বাংলাদেশে অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা বেড়েই চলছে। রোববার ফার্মগেটের কাছে মেট্রোরেলের ৪৩৩ নম্বর পিলার থেকে বিয়ারিং প্যাড খুলে নিচে পড়ে গিয়ে একজন পথচারীর মর্মান্তিক মৃত্যু এবং দুজন ব্যক্তি আহত হয়েছেন। ঘটনাটি এবারে নতুন নয়। গত বছর সেপ্টেম্বরে একই ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু সেবার কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
গত বছর যখন ৪৩০ নম্বর পিলারের কাছাকাছি এলাকা থেকে বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়েছিল, তখনই বিশেষজ্ঞরা নকশাগত ত্রুটির কথা বলেছিলেন। বুয়েটের দুর্ঘটনা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক ড. হাদিউজ্জামান সে সময় গণমাধ্যমে বলেছিলেন, মেট্রোরেলের যেখান থেকে বিয়ারিং প্যাড খুলে গেছে, সেই জায়গাটিতে বাঁক আছে। ট্রেন যখন সেই জায়গাটি অতিক্রম করে তখন লাইনের এক পাশে বাড়তি চাপ তৈরি হয়। তখন বিয়ারিং প্যাডের একদিকে বাড়তি চাপ পড়লে অন্য রাবারের বিয়ারিং প্যাড ছিটকে বেরিয়ে আসে।
কিন্তু মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ সেই সাবধানতার কোনো গুরুত্ব দেয়নি। ফলে রোববারের ঘটনাটি ঘটেছে। প্রশ্ন হলো, এক বছর সময়ের মধ্যে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ এবং নকশা তৈরি ও নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত কোম্পানিগুলো ঠিক কী পদক্ষেপ নিয়েছিল? তারা যে সেটা করেনি, এই ঘটনাই তার বড় প্রমাণ। এ জন্য প্রাণহানির দায় তারা এড়াতে পারে না।
কারণ, বাংলাদেশের মেট্রোরেলের নির্মাণব্যয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি ছিল। এই মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়ের ন্যায্যতা হিসেবে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান জাইকা উচ্চ গুণগত মান রক্ষার কথা বলেছিল। তাদের যুক্তি ছিল, প্রাথমিক ব্যয় বেশি হলেও রক্ষণাবেক্ষণে খরচ কম হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, উচ্চ গুণগত মান রক্ষা করেনি তারা। মেট্রোরেলের নিরাপত্তা নিয়ে যখন এমন উদ্বেগজনক ঘটনা ঘটছে, তখন এই অতিরিক্ত ব্যয়ের হিসাব এবং উচ্চমানের প্রতিশ্রুতি অর্থহীন নয় কি?
ছিটকে পড়া বিয়ারিং প্যাডের ছবিতে আয়তাকার প্যাডের এক কোণে ভর বেশি থাকার যে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে, তা পিলারের সংযোগস্থলে সমান ভরের ত্রুটিকেই তুলে ধরে। এটি সুস্পষ্টভাবে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা এবং যথাযথ তদারকির অভাবকেই দায়ী করে।
মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ বা সরকার নিহত ব্যক্তির পরিবারের কাছে শুধু ক্ষতিপূরণ দিয়েই তাদের দায় শেষ করতে পারে না। মানুষের জীবনের মূল্য কোনো আর্থিক সাহায্য দিয়ে পূরণ করা সম্ভব নয়।
এখন খুব জরুরি করণীয় হলো, জাইকার ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর না করে আন্তর্জাতিক মানের কোনো বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পুরো মেট্রোরেলের লাইনের নকশা ও নিরাপত্তাব্যবস্থা পরীক্ষা করা। এটা না করে যদি আবার ওই কোম্পানির ওপর ত্রুটি সংশোধনের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহলে সেটা কোনো বিবেচনাপ্রসূত কাজ হবে না। কারণ মেট্রোরেল কেবল একটি পরিবহনব্যবস্থা নয়, এটি আমাদের জাতীয় সম্পদ।

সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ নির্মল সেন লিখেছিলেন, ‘স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই’। কথাটি স্বাধীনতার পরপরই দেশে হইচই ফেলে দেয়। নির্মল সেনের কথাটি সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে ভিন্ন থাকলেও, এরপর নানা ঘটনায় কথাটির প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। যতই দিন যাচ্ছে বাংলাদেশে অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা বেড়েই চলছে। রোববার ফার্মগেটের কাছে মেট্রোরেলের ৪৩৩ নম্বর পিলার থেকে বিয়ারিং প্যাড খুলে নিচে পড়ে গিয়ে একজন পথচারীর মর্মান্তিক মৃত্যু এবং দুজন ব্যক্তি আহত হয়েছেন। ঘটনাটি এবারে নতুন নয়। গত বছর সেপ্টেম্বরে একই ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু সেবার কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
গত বছর যখন ৪৩০ নম্বর পিলারের কাছাকাছি এলাকা থেকে বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়েছিল, তখনই বিশেষজ্ঞরা নকশাগত ত্রুটির কথা বলেছিলেন। বুয়েটের দুর্ঘটনা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক ড. হাদিউজ্জামান সে সময় গণমাধ্যমে বলেছিলেন, মেট্রোরেলের যেখান থেকে বিয়ারিং প্যাড খুলে গেছে, সেই জায়গাটিতে বাঁক আছে। ট্রেন যখন সেই জায়গাটি অতিক্রম করে তখন লাইনের এক পাশে বাড়তি চাপ তৈরি হয়। তখন বিয়ারিং প্যাডের একদিকে বাড়তি চাপ পড়লে অন্য রাবারের বিয়ারিং প্যাড ছিটকে বেরিয়ে আসে।
কিন্তু মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ সেই সাবধানতার কোনো গুরুত্ব দেয়নি। ফলে রোববারের ঘটনাটি ঘটেছে। প্রশ্ন হলো, এক বছর সময়ের মধ্যে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ এবং নকশা তৈরি ও নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত কোম্পানিগুলো ঠিক কী পদক্ষেপ নিয়েছিল? তারা যে সেটা করেনি, এই ঘটনাই তার বড় প্রমাণ। এ জন্য প্রাণহানির দায় তারা এড়াতে পারে না।
কারণ, বাংলাদেশের মেট্রোরেলের নির্মাণব্যয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি ছিল। এই মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়ের ন্যায্যতা হিসেবে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান জাইকা উচ্চ গুণগত মান রক্ষার কথা বলেছিল। তাদের যুক্তি ছিল, প্রাথমিক ব্যয় বেশি হলেও রক্ষণাবেক্ষণে খরচ কম হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, উচ্চ গুণগত মান রক্ষা করেনি তারা। মেট্রোরেলের নিরাপত্তা নিয়ে যখন এমন উদ্বেগজনক ঘটনা ঘটছে, তখন এই অতিরিক্ত ব্যয়ের হিসাব এবং উচ্চমানের প্রতিশ্রুতি অর্থহীন নয় কি?
ছিটকে পড়া বিয়ারিং প্যাডের ছবিতে আয়তাকার প্যাডের এক কোণে ভর বেশি থাকার যে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে, তা পিলারের সংযোগস্থলে সমান ভরের ত্রুটিকেই তুলে ধরে। এটি সুস্পষ্টভাবে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা এবং যথাযথ তদারকির অভাবকেই দায়ী করে।
মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ বা সরকার নিহত ব্যক্তির পরিবারের কাছে শুধু ক্ষতিপূরণ দিয়েই তাদের দায় শেষ করতে পারে না। মানুষের জীবনের মূল্য কোনো আর্থিক সাহায্য দিয়ে পূরণ করা সম্ভব নয়।
এখন খুব জরুরি করণীয় হলো, জাইকার ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর না করে আন্তর্জাতিক মানের কোনো বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পুরো মেট্রোরেলের লাইনের নকশা ও নিরাপত্তাব্যবস্থা পরীক্ষা করা। এটা না করে যদি আবার ওই কোম্পানির ওপর ত্রুটি সংশোধনের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহলে সেটা কোনো বিবেচনাপ্রসূত কাজ হবে না। কারণ মেট্রোরেল কেবল একটি পরিবহনব্যবস্থা নয়, এটি আমাদের জাতীয় সম্পদ।
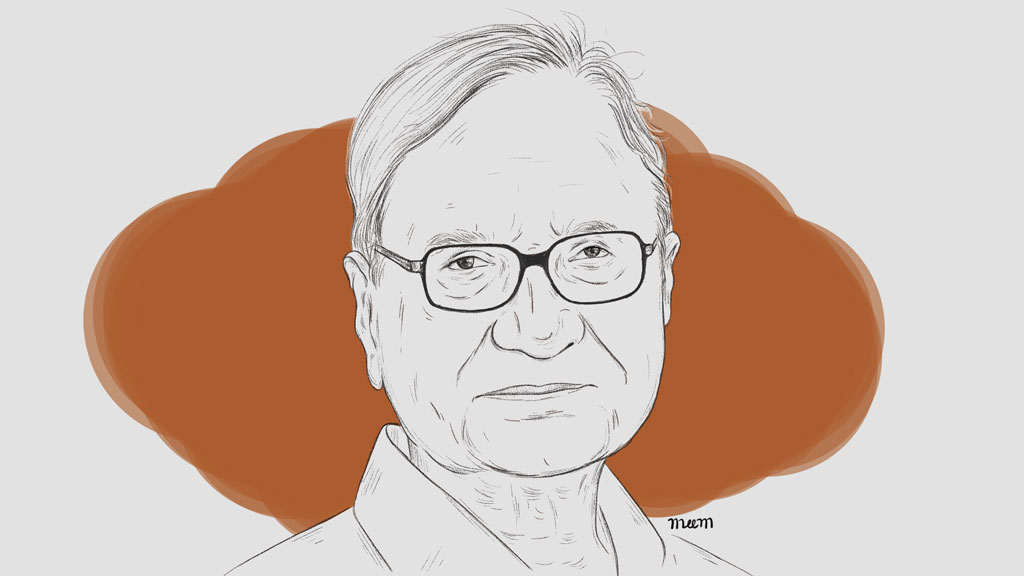
স্বাধীন হওয়ার পরপরই টের পাওয়া গেল যে পূর্ব বাংলা পাঞ্জাব-শাসিত পাকিস্তানের একটি অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ হতে চলেছে। সে জন্যই দাবি উঠেছে স্বায়ত্তশাসনের এবং ওই দাবিকে যৌক্তিক দিক দিয়ে জোরদার করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে আদি লাহোর প্রস্তাবের।
১৮ আগস্ট ২০২১
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিমের বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তাদের উপনিবেশ দেশগুলোর অধিকাংশকেই স্বাধীনতা দিয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। তবে তারা উপনিবেশ পরিত্যাগ করলেও নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাকে একমুহূর্তের জন্যও বিসর্জন দেয়নি।
২১ ঘণ্টা আগে
আজকের পৃথিবী সত্যিই হাতের মুঠোয়। সকালবেলা ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে আমরা হাতে নিই মোবাইল ফোন। এরপর নোটিফিকেশন, মেসেজ, স্টোরি, ভিডিও—সবকিছু এক স্পর্শেই পাওয়া যায়। কিন্তু এই অগণিত সংযোগের মাঝেই মানুষ যেন ক্রমেই আরও নিঃসঙ্গ হয়ে উঠছে।
২১ ঘণ্টা আগে
কৃষিপ্রযুক্তির প্রসার সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি ধারণা পেয়েছি নেদারল্যান্ডসে গিয়ে। ইউরোপের এই ছোট দেশটি কৃষিতে যতটা সমৃদ্ধ, ততটাই উদ্ভাবনী। যেখানে কৃষি গবেষণা, প্রযুক্তির প্রয়োগ, উৎপাদন ও বিপণন এক সুসমন্বিত চক্রে ঘুরছে নিরবচ্ছিন্নভাবে।
২১ ঘণ্টা আগে