সেলিম জাহান
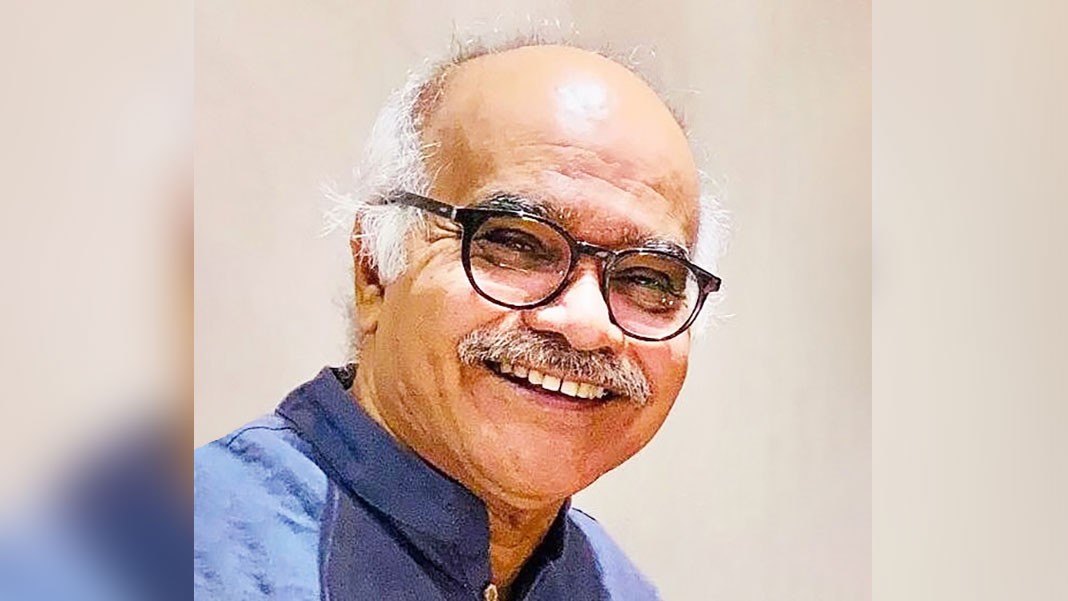
প্রতিবছরের শুরুতে সারা দেশে বসে বইমেলা। রাজধানী ঢাকা শহরে ফেব্রুয়ারি মাসে হয় মাসব্যাপী বইমেলা। এ ছাড়া জেলা-উপজেলা শহরগুলোতেও এ সময়ে বইমেলার হিড়িক পড়ে। মেলা উপলক্ষে নির্ধারিত এলাকা অপূর্ব সাজে সেজে ওঠে। প্রকাশকেরা তাঁদের স্টল সাজান নিজস্ব পছন্দমতো। এর বাইরে বইমেলাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটে। এই যেমন খাবারের দোকান, নানা শিল্পসামগ্রীর বিপণি। দলে দলে মানুষ বন্ধুবান্ধব, পরিবার-পরিজন নিয়ে মেলায় আসেন। সাংবাদিক-কবি-সাহিত্যিক-লেখকেরা আসেন। পত্রিকা, রেডিও-টেলিভিশনের সংবাদ প্রতিনিধিরা আসেন সংবাদ সংগ্রহ ও সম্প্রচারের জন্য। বই দেখা হয় নেড়েচেড়ে, ওলটানো হয় বইয়ের পাতা, বই কেনাবেচার ধুম পড়ে যায়। চারদিকে উৎসবের সমাবেশ, একটা আনন্দের আবহ।
বইমেলাকে আমার মনে হয় এটা বহুমাত্রিক কর্মপ্রবাহ। প্রথমত, এটি একটি মিলনমেলা; বই মাত্র উপলক্ষ। আসলে এ মেলা একটা সুযোগ তৈরি করে দেয়, একটা আধার হয়ে দাঁড়ায় মিলিত হওয়ার, দেখা-সাক্ষাতের, আড্ডা আর আলাপচারিতার। ব্যস্ততার এই শহরে, যাপিত নাগরিক জীবনের নানান টানাপোড়েনে আমাদের সময়ই হয় না প্রিয়জনদের সঙ্গে দেখা করার, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা
দেওয়ার। বইমেলা দুদণ্ড সময় বের করে দেয়, একটা ক্ষেত্র তৈরি করে দেয় সেই সব প্রশ্ন শুধানোর—‘এত দিন কোথায় ছিলেন?’, কিংবা ‘বন্ধু, আছো তো ভালো?’; দ্বিতীয়ত, বইমেলা একটা সংযোগ তৈরি করে দেয় লেখকে-পাঠকে, লেখকে-লেখকে, পাঠকে-পাঠকে, প্রকাশক-লেখকে, প্রকাশক-প্রকাশকে। সেই প্রক্রিয়ায় ঋদ্ধ হন পাঠক, উদ্বুদ্ধ হন লেখক, নতুন ধ্যান-ধারণা পেয়ে যান প্রকাশক। ফলে বুদ্ধি ও মননের নানান দিগন্ত খুলে যায়।
কিন্তু এসব ব্যক্তিগত ও সামাজিক বলয় ছাড়িয়ে বইমেলাগুলোর একটা অর্থনৈতিক মাত্রিকতাও তো আছে। ঢাকায় গত বইমেলায় ৬০ কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছিল। আগের বছর, অর্থাৎ ২০২৩ সালে বিক্রি হয়েছিল ৪৭ কোটি টাকার বই। কিন্তু বইমেলার অর্থনীতি শুধু বই বিক্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, সে অর্থনীতির নানান দিক আছে। বইমেলা শুরু হওয়ার আগে নানান ধাপ আছে এবং সেসব ধাপের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে নানান অর্থনৈতিক কারবার।
বই প্রকাশ দিয়েই শুরু করা যাক। লেখক বই লিখে প্রকাশককে দিলেই প্রাথমিক একটা লেনদেন হয়। তারপর অবশ্য বইমেলা শেষে কিংবা বছরের শেষে লেখকের সম্মানী আসে ‘রয়্যালটি’ হিসেবে। পাণ্ডুলিপিপ্রাপ্তির পর শুরু হয় সম্পাদনার কাজ, প্রচ্ছদের কাজ, কম্পিউটারের কাজ—তিনটি কাজেই সম্মানীর ব্যাপার আছে। তারপর শুরু হয়ে যায় প্রকাশনার দক্ষযজ্ঞ। ব্যস্ত হয়ে পড়ে ছাপাখানাগুলো, দিনরাত সেখানে কাজ চলে। সে প্রক্রিয়ায় খরচ আছে কাগজের, ছাপাখানাকর্মীদের মজুরির। চাপের মুখে যখন প্রকাশনা-অঙ্গীকার রাখতে হয়, তখন ছাপাখানাকর্মীদের বাড়তি মজুরি দিতে হয়। সারা বছরে সেটাই হয়তো তাঁদের অতিরিক্ত একটি আয়। গত কয়েক বছরে কাগজের মূল্যবৃদ্ধি পুস্তক প্রকাশনায় অর্থনীতির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে পুস্তক বাঁধাইয়ের খরচও নিতান্ত ফেলনা নয়। বই যত সুশোভন হবে, ততই বাঁধাই খরচও বাড়বে। মেলার শুরুতে এবং তার পরেও মেলা প্রাঙ্গণে পুস্তক পরিবহনের একটি ব্যয় আছে। আবার মেলা উপলক্ষে পরিবহনকর্মীদের জন্য সেটা সারা বছরের একটা বিশেষ আয়।
মেলা প্রাঙ্গণ সাজানো এবং বইয়ের স্টল তৈরি নিয়ে একটা বড় অর্থনীতি কাজ করে। স্টল বানানো এবং সেটাকে সাজানোর ক্ষেত্রে শিল্পী, স্থপতি ও মিস্ত্রিদের একটা ভূমিকা আছে। খরচ আছে নকশার, সাজসরঞ্জাম, মালমসলার এবং সম্মানী ও মজুরির। বহু ক্ষেত্রেই শিল্পী ও স্থপতিদের সম্মানী নির্ভর করে কাকে কাজে লাগানো হচ্ছে তার ওপর। বড় প্রকাশনা সংস্থাগুলো যেমন খ্যাতিমান শিল্পী ও স্থপতিদের নিযুক্ত করতে পারে, তেমনি ছোট ছোট সংস্থাগুলো সেটা করতে পারে না। মেলা প্রাঙ্গণে নানান অবকাঠামো সুবিধা এবং সেবার জন্যও মেলা উদ্যোক্তাদের অর্থ ব্যয় করতে হয়। এসব সুবিধার মধ্যে আছে মানুষের চলাচলের জন্য অস্থায়ী রাস্তা নির্মাণ, পানীয় জলের সুবিধা, মেলার নানান জায়গায় বসার ব্যবস্থা এবং বর্জ্য ফেলার কাঠামো গড়ে তোলা।
প্রকাশনা সংস্থাগুলোর স্টলে নিযুক্ত কর্মীদের মজুরি ব্যয় এ মেলার অর্থনীতির অংশ। প্রতিটি স্টলে পর্যাপ্তসংখ্যক কর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়। বহু ক্ষেত্রেই প্রকাশনা সংস্থার স্থায়ী কর্মীদের পাশাপাশি অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ দেওয়া হয় অতিরিক্ত কাজের কারণে। তাঁদের প্রশিক্ষণ এবং মজুরির জন্য অর্থ ব্যয় করতে হয়। বইমেলা উপলক্ষে বইয়ের স্টলগুলোকে আলোকসজ্জিত করা হয়, দীর্ঘক্ষণ সেসব বাতিকে জ্বালিয়ে রাখতে হয়। ফলে বিদ্যুতের খরচও হয় অনেক।
এরপর আসছে বইমেলার অর্থনীতির সেই উল্লেখযোগ্য বিষয়—বই বিক্রি। নতুন প্রকাশিত বই যেমন বিক্রি হয়, তেমনি বিক্রি হয় পূর্বপ্রকাশিত বইও। গত বইমেলায় মোট ৩ হাজার ৫২১টি নতুন প্রকাশিত বই এসেছিল, মেলায় দর্শনার্থী এসেছিলেন ৬০ লাখ। যেহেতু মেলায় মোট ৬০ কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছিল; সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে প্রত্যেক দর্শনার্থী গড়ে ১০০ টাকার বই কিনেছেন। মেলায় বই বিক্রি যদি আরও ব্যাপ্ত হয়, সে ক্ষেত্রে বই বিক্রি আরও বাড়তে পারে, যা মেলার অর্থনীতিকে আরও সংহত করবে।
মেলায় প্রকাশিত বইগুলোকে সংশ্লিষ্ট প্রকাশকেরা জেলা কিংবা উপজেলা শহরে চালান করেন, নানান পাঠাগারে পাঠান। কখনো কখনো ডাকযোগেও প্রকাশিত সেসব
বই পাঠকদের কাছে পাঠাতে হয়, ক্ষেত্রবিশেষে দেশের বাইরেও যায় প্রকাশিত বই। একধরনের অর্থনীতি সেখানেও জন্মলাভ করে।
সব মিলিয়ে বইমেলার চাকাকে সচল রাখতে একটি বহুমাত্রিক অর্থনীতি আছে। কিছু তার দৃশ্যমান, কিছু ঘটে দৃষ্টির আড়ালে। কিছু তার সরব, কিছু নীরব। তবে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, আমাদের দেশের বহু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং নানান মানুষের জীবন ও জীবিকা বইমেলার ওপর নির্ভর করে।
লেখক: অর্থনীতিবিদ
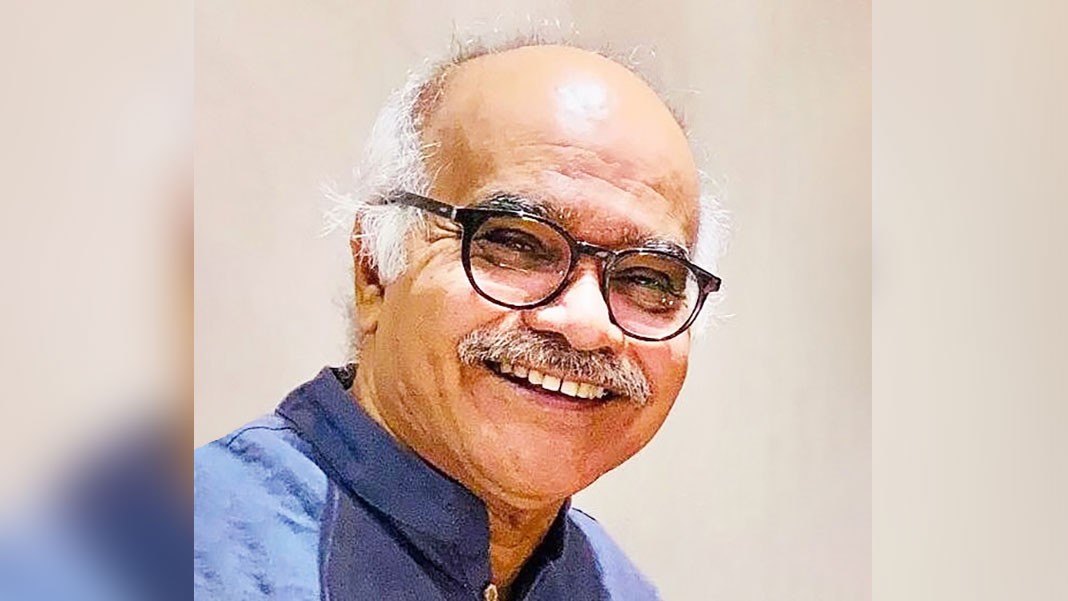
প্রতিবছরের শুরুতে সারা দেশে বসে বইমেলা। রাজধানী ঢাকা শহরে ফেব্রুয়ারি মাসে হয় মাসব্যাপী বইমেলা। এ ছাড়া জেলা-উপজেলা শহরগুলোতেও এ সময়ে বইমেলার হিড়িক পড়ে। মেলা উপলক্ষে নির্ধারিত এলাকা অপূর্ব সাজে সেজে ওঠে। প্রকাশকেরা তাঁদের স্টল সাজান নিজস্ব পছন্দমতো। এর বাইরে বইমেলাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটে। এই যেমন খাবারের দোকান, নানা শিল্পসামগ্রীর বিপণি। দলে দলে মানুষ বন্ধুবান্ধব, পরিবার-পরিজন নিয়ে মেলায় আসেন। সাংবাদিক-কবি-সাহিত্যিক-লেখকেরা আসেন। পত্রিকা, রেডিও-টেলিভিশনের সংবাদ প্রতিনিধিরা আসেন সংবাদ সংগ্রহ ও সম্প্রচারের জন্য। বই দেখা হয় নেড়েচেড়ে, ওলটানো হয় বইয়ের পাতা, বই কেনাবেচার ধুম পড়ে যায়। চারদিকে উৎসবের সমাবেশ, একটা আনন্দের আবহ।
বইমেলাকে আমার মনে হয় এটা বহুমাত্রিক কর্মপ্রবাহ। প্রথমত, এটি একটি মিলনমেলা; বই মাত্র উপলক্ষ। আসলে এ মেলা একটা সুযোগ তৈরি করে দেয়, একটা আধার হয়ে দাঁড়ায় মিলিত হওয়ার, দেখা-সাক্ষাতের, আড্ডা আর আলাপচারিতার। ব্যস্ততার এই শহরে, যাপিত নাগরিক জীবনের নানান টানাপোড়েনে আমাদের সময়ই হয় না প্রিয়জনদের সঙ্গে দেখা করার, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা
দেওয়ার। বইমেলা দুদণ্ড সময় বের করে দেয়, একটা ক্ষেত্র তৈরি করে দেয় সেই সব প্রশ্ন শুধানোর—‘এত দিন কোথায় ছিলেন?’, কিংবা ‘বন্ধু, আছো তো ভালো?’; দ্বিতীয়ত, বইমেলা একটা সংযোগ তৈরি করে দেয় লেখকে-পাঠকে, লেখকে-লেখকে, পাঠকে-পাঠকে, প্রকাশক-লেখকে, প্রকাশক-প্রকাশকে। সেই প্রক্রিয়ায় ঋদ্ধ হন পাঠক, উদ্বুদ্ধ হন লেখক, নতুন ধ্যান-ধারণা পেয়ে যান প্রকাশক। ফলে বুদ্ধি ও মননের নানান দিগন্ত খুলে যায়।
কিন্তু এসব ব্যক্তিগত ও সামাজিক বলয় ছাড়িয়ে বইমেলাগুলোর একটা অর্থনৈতিক মাত্রিকতাও তো আছে। ঢাকায় গত বইমেলায় ৬০ কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছিল। আগের বছর, অর্থাৎ ২০২৩ সালে বিক্রি হয়েছিল ৪৭ কোটি টাকার বই। কিন্তু বইমেলার অর্থনীতি শুধু বই বিক্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, সে অর্থনীতির নানান দিক আছে। বইমেলা শুরু হওয়ার আগে নানান ধাপ আছে এবং সেসব ধাপের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে নানান অর্থনৈতিক কারবার।
বই প্রকাশ দিয়েই শুরু করা যাক। লেখক বই লিখে প্রকাশককে দিলেই প্রাথমিক একটা লেনদেন হয়। তারপর অবশ্য বইমেলা শেষে কিংবা বছরের শেষে লেখকের সম্মানী আসে ‘রয়্যালটি’ হিসেবে। পাণ্ডুলিপিপ্রাপ্তির পর শুরু হয় সম্পাদনার কাজ, প্রচ্ছদের কাজ, কম্পিউটারের কাজ—তিনটি কাজেই সম্মানীর ব্যাপার আছে। তারপর শুরু হয়ে যায় প্রকাশনার দক্ষযজ্ঞ। ব্যস্ত হয়ে পড়ে ছাপাখানাগুলো, দিনরাত সেখানে কাজ চলে। সে প্রক্রিয়ায় খরচ আছে কাগজের, ছাপাখানাকর্মীদের মজুরির। চাপের মুখে যখন প্রকাশনা-অঙ্গীকার রাখতে হয়, তখন ছাপাখানাকর্মীদের বাড়তি মজুরি দিতে হয়। সারা বছরে সেটাই হয়তো তাঁদের অতিরিক্ত একটি আয়। গত কয়েক বছরে কাগজের মূল্যবৃদ্ধি পুস্তক প্রকাশনায় অর্থনীতির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে পুস্তক বাঁধাইয়ের খরচও নিতান্ত ফেলনা নয়। বই যত সুশোভন হবে, ততই বাঁধাই খরচও বাড়বে। মেলার শুরুতে এবং তার পরেও মেলা প্রাঙ্গণে পুস্তক পরিবহনের একটি ব্যয় আছে। আবার মেলা উপলক্ষে পরিবহনকর্মীদের জন্য সেটা সারা বছরের একটা বিশেষ আয়।
মেলা প্রাঙ্গণ সাজানো এবং বইয়ের স্টল তৈরি নিয়ে একটা বড় অর্থনীতি কাজ করে। স্টল বানানো এবং সেটাকে সাজানোর ক্ষেত্রে শিল্পী, স্থপতি ও মিস্ত্রিদের একটা ভূমিকা আছে। খরচ আছে নকশার, সাজসরঞ্জাম, মালমসলার এবং সম্মানী ও মজুরির। বহু ক্ষেত্রেই শিল্পী ও স্থপতিদের সম্মানী নির্ভর করে কাকে কাজে লাগানো হচ্ছে তার ওপর। বড় প্রকাশনা সংস্থাগুলো যেমন খ্যাতিমান শিল্পী ও স্থপতিদের নিযুক্ত করতে পারে, তেমনি ছোট ছোট সংস্থাগুলো সেটা করতে পারে না। মেলা প্রাঙ্গণে নানান অবকাঠামো সুবিধা এবং সেবার জন্যও মেলা উদ্যোক্তাদের অর্থ ব্যয় করতে হয়। এসব সুবিধার মধ্যে আছে মানুষের চলাচলের জন্য অস্থায়ী রাস্তা নির্মাণ, পানীয় জলের সুবিধা, মেলার নানান জায়গায় বসার ব্যবস্থা এবং বর্জ্য ফেলার কাঠামো গড়ে তোলা।
প্রকাশনা সংস্থাগুলোর স্টলে নিযুক্ত কর্মীদের মজুরি ব্যয় এ মেলার অর্থনীতির অংশ। প্রতিটি স্টলে পর্যাপ্তসংখ্যক কর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়। বহু ক্ষেত্রেই প্রকাশনা সংস্থার স্থায়ী কর্মীদের পাশাপাশি অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ দেওয়া হয় অতিরিক্ত কাজের কারণে। তাঁদের প্রশিক্ষণ এবং মজুরির জন্য অর্থ ব্যয় করতে হয়। বইমেলা উপলক্ষে বইয়ের স্টলগুলোকে আলোকসজ্জিত করা হয়, দীর্ঘক্ষণ সেসব বাতিকে জ্বালিয়ে রাখতে হয়। ফলে বিদ্যুতের খরচও হয় অনেক।
এরপর আসছে বইমেলার অর্থনীতির সেই উল্লেখযোগ্য বিষয়—বই বিক্রি। নতুন প্রকাশিত বই যেমন বিক্রি হয়, তেমনি বিক্রি হয় পূর্বপ্রকাশিত বইও। গত বইমেলায় মোট ৩ হাজার ৫২১টি নতুন প্রকাশিত বই এসেছিল, মেলায় দর্শনার্থী এসেছিলেন ৬০ লাখ। যেহেতু মেলায় মোট ৬০ কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছিল; সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে প্রত্যেক দর্শনার্থী গড়ে ১০০ টাকার বই কিনেছেন। মেলায় বই বিক্রি যদি আরও ব্যাপ্ত হয়, সে ক্ষেত্রে বই বিক্রি আরও বাড়তে পারে, যা মেলার অর্থনীতিকে আরও সংহত করবে।
মেলায় প্রকাশিত বইগুলোকে সংশ্লিষ্ট প্রকাশকেরা জেলা কিংবা উপজেলা শহরে চালান করেন, নানান পাঠাগারে পাঠান। কখনো কখনো ডাকযোগেও প্রকাশিত সেসব
বই পাঠকদের কাছে পাঠাতে হয়, ক্ষেত্রবিশেষে দেশের বাইরেও যায় প্রকাশিত বই। একধরনের অর্থনীতি সেখানেও জন্মলাভ করে।
সব মিলিয়ে বইমেলার চাকাকে সচল রাখতে একটি বহুমাত্রিক অর্থনীতি আছে। কিছু তার দৃশ্যমান, কিছু ঘটে দৃষ্টির আড়ালে। কিছু তার সরব, কিছু নীরব। তবে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, আমাদের দেশের বহু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং নানান মানুষের জীবন ও জীবিকা বইমেলার ওপর নির্ভর করে।
লেখক: অর্থনীতিবিদ

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার কর্তৃত্ববাদী সরকার অবসানের পর অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের এক বছর পূর্ণ হয়েছে। এ উপলক্ষে কয়েক দিন ধরে পত্রপত্রিকা ও টেলিভিশনের টক শোতে চলছে এক বছরের মূল্যায়ন।
১৫ ঘণ্টা আগে
দেশে নারী জাগরণ অভূতপূর্ব। এটা বলে বোঝানোর দরকার পড়ে না। বীরকন্যা প্রীতিলতা, বেগম রোকেয়া থেকে জাহানারা ইমামে এর উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে রয়েছে। বাংলাদেশ শাসিত হয়েছে নারীর অধীনে। এরশাদের পতনের পর সরাসরি সামরিক শাসনের অবসান হলে খালেদা জিয়া দেশ শাসনে আসেন।
১৫ ঘণ্টা আগে
আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছুদিন পরেই বৃষ্টিতে নাজেহাল হয়ে ওঠা মানুষদের এমনটাই মনে হবে। বাইরে হয়তো রোদ তখন তেমন কড়া নয়, আবার কড়াও হতে পারে, শেফালির শাখে বিহগ-বিহগী কে জানে কী গেয়ে যাবে!
১৫ ঘণ্টা আগে
চাঁদপুরের মতলব উত্তরের ছোট্ট গ্রাম সাড়ে পাঁচআনি। এখানেই বড় হচ্ছে সোহান—মাত্র সাড়ে পাঁচ বছরের এক বিস্ময়বালক, যার পায়ের জাদু দেখে বিস্মিত হচ্ছে দেশজুড়ে মানুষ।
১৫ ঘণ্টা আগে