সেলিম জাহান

‘এ কোথায় এলাম?’ গাড়ি থেকে নেমে নিজেকেই প্রশ্ন করি, এদিক-ওদিক তাকাই অবাক দৃষ্টিতে। আমার সঙ্গে নেমেছে পশ্চিম কেপ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন ছাত্র, কৃষ্ণাঙ্গ। সঙ্গের চালকটিও তা-ই। মনে মনে বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো যে, মিনিট দশেক আগেও ইউরোপীয় ধাঁচে গড়া কেপটাউন শহর কেন্দ্রের মাঝখানে কফি খাচ্ছিলাম এবং মিনিট পাঁচেক আগে ইংল্যান্ডের সুনন্দ পল্লি অঞ্চলের আদলে শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত আবাসিক এলাকা পেরিয়ে এসেছি। এই পরিবর্তন অবিশ্বাস্য। আমার বিহ্বল দৃষ্টিকে অনুসরণ করে একটি ছাত্র বলে ওঠে: ‘বলেছিলাম না, লাঙ্গায় নিয়ে আসব? এটা, এটাই লাঙ্গা।’
দুদিন আগে কেপটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘একবিংশ শতাব্দীর দক্ষিণ আফ্রিকা’ শীর্ষক নাদিন গর্ডিমার স্মারক বক্তৃতা শেষে পশ্চিম কেপ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্ররাই বলেছিল যে, কেপটাউন ছাড়ার আগে বিমানবন্দরে যাওয়ার পথে তারা আমাকে লাঙ্গা দেখিয়ে নেবে। দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে পুরোনো কৃষ্ণাঙ্গ বস্তি—বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের সূতিকাগার এবং যেখানে আশির দশকের শেষের দিকে সংগ্রামরত প্রতিবাদী মিছিলের ওপর শ্বেতাঙ্গ পুলিশ গুলি চালিয়ে দুই ঘণ্টায় ১৩০০ মানুষকে মেরে ফেলেছিল।
এই সেই লাঙ্গা—চারদিকে দারিদ্র্য, বঞ্চনা, শোষণের বীভৎস চিত্র। এ কোন মানবেতর জীবনপ্রবাহ দেখছি আমি? চারপাশের ছাপরা, নোংরা, ভাঙা পথঘাট। পৃথিবীর সবচেয়ে দরিদ্র দেশগুলোর বস্তিগুলোকেও যে হার মানায়। মানুষের ভাগাড় বলে যদি কিছু থাকে, তাহলে এটাই হচ্ছে মানুষের ভাগাড়। নরকও যে এর কাছে হার মানবে।
কিন্তু সবচেয়ে ভয়ংকর হচ্ছে মানুষগুলোর চোখ। ওখানে ক্রোধ, আক্রোশ আর চরম হতাশা ভিন্ন কিছুই নেই। মনে হচ্ছে, সে আক্রোশ অন্য যেকোনো মানুষের প্রতি, সে ক্রোধ সমগ্র পৃথিবীর ওপর, সে হতাশা সারা জীবনের প্রতি। কোনো সংঘর্ষ ভিন্ন মানুষের চোখে অমন হিংস্রতা আর কোথাও দেখিনি। সে হিংস্রতা উড়িয়ে দিতে পারে আশপাশ, পুড়িয়ে দিতে পারে সবকিছু।
‘কোনো দিকে তাকাবেন না, কারও চোখে চোখ রাখবেন না। কোনো কথা বলবেন না, কথা বলতে হলে আমরা বলব। কোনো অবস্থায়ই মুঠোফোন বের করবেন না। ছবি তোলার চেষ্টা করবেন না। বিশেষ বিশেষ জায়গায় আমরা ছবি তুলে দেব। কোনো হিংস্র কাণ্ড দেখে ভয় পেলেও স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করবেন। আমরা লাঙ্গারই লোক। আশা করছি কিছু হবে না। মনে রাখবেন, কৃষ্ণাঙ্গ ছাড়া এখানে কেউ ঢুকলে তাঁদের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। আপনার গায়ের রং এখানে নিষিদ্ধ।’
বলতে বলতে আমাদের গাড়িটি হুস করে দ্রুত বেরিয়ে যায়। এবার একটা শীতল ভয় আমার মেরুদণ্ড বেয়ে ওঠে। টের পাই ঘামে ভিজে যাচ্ছে আমার পোশাক এবং একটা শিরশিরানি কাঁপুনি আমার সারা শরীরে। ‘গাড়িটা একটা নিরাপদ জায়গায় আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে,’ আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে একটি ছাত্র। তারপর তারা তিনজন আমাকে অনেকটা বেষ্টনীর মতো ঘিরে সামনে এগোতে থাকে।
নানান জায়গায় ছোট ছোট জটলা, বাচ্চারা দাঁড়িয়ে আছে এখানে-ওখানে, কর্মরত মহিলাদের দেখা যায় ইতস্তত। কিন্তু টের পাই, আমাদের চারজনের দলটাকে দেখলেই কথা থেমে গিয়ে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা নেমে আসছে—পরিমাপ করা হচ্ছে আমাদের আনখশির। যেন একদল নেকড়ে দাঁত বের করে ঘিরে দাঁড়িয়েছে আমাদের চারদিকে। একটু বেচাল হয়েই ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের ওপরে, ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে আমাদের।
মদের গন্ধে ঘন হয়ে আছে বাতাস আর আশপাশ। ‘এদের প্রধান খাদ্য কি জানেন?’ একটি ছেলে ফিসফিসিয়ে আমাকে জানায়: ‘সকালের নাশতায় মদ, দুপুরের খাবারে মদ, নৈশভোজে সবচেয়ে কড়া মদ নিট। বিশ্বাস করবেন যে, এরা শিশুদেরও মদ গিলিয়ে দেয়, যাতে ওরা ঘুমিয়ে থাকে। তাই লাঙ্গায় কেউই কখনো প্রকৃতিস্থ অবস্থায় থাকে না। সুতরাং যখন যা কিছু ঘটতে পারে। পুলিশও এখানে ঢুকতে ভয় পায়, ঢোকে না। ওই দেখুন বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।’
এক জায়গায় দেখি, একটি ঝুপড়ির সামনে একটি তরুণী মেয়েকে এক যুবক বেধড়ক মারছে। কেন, কে জানে? ছেলেটির হুংকারে, মেয়েটির চিৎকারে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত। চড়-চাপ্পড়, লাঠির বাড়ি, অকথ্য গালিগালাজের তুবড়ি চারদিকে। আড়চোখে তাকিয়েও বুঝতে পারলাম, মেয়েটির চোখ-মুখ রক্তাক্ত। চারপাশ দিয়ে কতজন চলে যাচ্ছে, আশপাশে কতজন কথা বলছে, এদিকে-ওদিকে শিশুরা দাঁড়িয়ে আছে; কিন্তু কেউই ছেলেটিকে থামাতে আসছে না, কিংবা মেয়েটিকে রক্ষা করতে এগোচ্ছে না। যেন কিছুই হয়নি, যেন সবকিছুই স্বাভাবিক। এ কোন নির্বিকারত্ব, এ কোন নির্লিপ্ততা!
বিশ্বাস করুন কী দেখেছিলাম, আমার সবটা ভালো করে মনে নেই। যা মনে আছে, তা-ও বর্ণনা করার উপযুক্ত ভাষা আমার নেই। কেমন একটা ভীতির বুদ্বুদের মধ্যে, একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। যেন দেখতে পারছি না কিছু, যেন সবকিছু বোধের অগম্য। ছাত্রদের তোলা ছবিগুলো লাঙ্গার সবচেয়ে বড় প্রতিচ্ছবি। ওর চেয়ে ভালো সাক্ষ্য আর নেই।
জানতাম চারটি জাতিশ্রেণি আছে দক্ষিণ আফ্রিকায়—শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, বর্ণিল (মিশ্রিত) ও ভারতীয়। যেটা জানতাম না, সেটা হচ্ছে বিভাজনটা তীব্রতম, অবিশ্বাসটা চরমতম এবং হিংসাটি ব্যাপকতম। আমি ভারতীয়ের মধ্যে পড়ব। এবং লাঙ্গায় ভারতীয়রাও গ্রহণযোগ্য নয়। লাঙ্গা কৃষ্ণাঙ্গদের। শুধুই কৃষ্ণাঙ্গদের।
দেখতে দেখতে বড় রাস্তায় পৌঁছলে দেখা গেল রাস্তার ওপারে আমাদের গাড়ি অপেক্ষা করছে। গাড়ির কাছে যেতেই কৃষ্ণাঙ্গ চালক নেমে গেল এবং সে জায়গায় উঠল এক বর্ণিল চালক। মনে হচ্ছে যেন একটা গোয়েন্দা চলচ্চিত্র। রাস্তার ওপারে বর্ণিল জনপদ বন্তেহিউয়েলে ঢুকব। সেখানে কৃষ্ণাঙ্গদের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সুতরাং কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্র তিনজনও সেখানে ঢুকতে পারবে না। তবে আমার গাত্রবর্ণের কারণে আমার অসুবিধে নেই। আর এ জনপদে ভারতীয়রা প্রবেশ করতে পারে। আসলে এ জনপদে একটি বড় ভারতীয় জনগোষ্ঠীও বসবাস করে।
আর এ জনপদ অত ভীতিকরও নয়। এ জনপদের অবস্থাও উন্নততর—একটি নিম্ন মধ্যবিত্তের জনপদ। তবে এখানেও নামব না এবং গাড়ি থেকেই ছবি তুলতে হবে। ৩০ মিনিটের মতো বর্ণিল চালক আর আমি ওই জনপদ ঘুরে এলাম। দেখলাম, বাচ্চাদের হাত ধরে মা-বাবা চলছেন, বাজারের থলে হাতে ফিরছেন এক মহিলা, লাঠি ঠুকে ঠুকে চলছেন এক বৃদ্ধ। শিশুরা খেলছে বাড়ির সামনে, রান্নার গন্ধ ভেসে আসছে কোনো বাড়ি থেকে, একদল কিশোর-কিশোরীর হাস্যরোল শুনতে পাচ্ছি এক পথের বাঁকে। এক স্বাভাবিক জীবনের চালচিত্র।
এবার সবাই মিলে বিমানবন্দরের দিকে যাত্রা। গাড়ির কারও মুখে কোনো কথা নেই। শুধু কিন্তু আমি জানি, প্রত্যেকের মনের মধ্যে প্রত্যেকে কথা বলছে। অন্যদের কথা তো বলতে পারব না। তবে আমার মনের মধ্যে শুধু তোলপাড় করতে লাগল একটিই প্রশ্ন: ‘এ কোন দক্ষিণ আফ্রিকা?’ বারবার মনে হতে লাগল জয় গোস্বামীর কয়েক লাইন:
‘এ কোন দেশে আমরা এলাম?
যতবার গেছি ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেছে তার নাম।
কোথায় সে দেশ—অতীতে না ভবিষ্যতে?’
লেখক: সেলিম জাহান ভূতপূর্ব পরিচালক, মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন দপ্তর এবং দারিদ্র্য বিমোচন বিভাগ, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি
নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

‘এ কোথায় এলাম?’ গাড়ি থেকে নেমে নিজেকেই প্রশ্ন করি, এদিক-ওদিক তাকাই অবাক দৃষ্টিতে। আমার সঙ্গে নেমেছে পশ্চিম কেপ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন ছাত্র, কৃষ্ণাঙ্গ। সঙ্গের চালকটিও তা-ই। মনে মনে বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো যে, মিনিট দশেক আগেও ইউরোপীয় ধাঁচে গড়া কেপটাউন শহর কেন্দ্রের মাঝখানে কফি খাচ্ছিলাম এবং মিনিট পাঁচেক আগে ইংল্যান্ডের সুনন্দ পল্লি অঞ্চলের আদলে শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত আবাসিক এলাকা পেরিয়ে এসেছি। এই পরিবর্তন অবিশ্বাস্য। আমার বিহ্বল দৃষ্টিকে অনুসরণ করে একটি ছাত্র বলে ওঠে: ‘বলেছিলাম না, লাঙ্গায় নিয়ে আসব? এটা, এটাই লাঙ্গা।’
দুদিন আগে কেপটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘একবিংশ শতাব্দীর দক্ষিণ আফ্রিকা’ শীর্ষক নাদিন গর্ডিমার স্মারক বক্তৃতা শেষে পশ্চিম কেপ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্ররাই বলেছিল যে, কেপটাউন ছাড়ার আগে বিমানবন্দরে যাওয়ার পথে তারা আমাকে লাঙ্গা দেখিয়ে নেবে। দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে পুরোনো কৃষ্ণাঙ্গ বস্তি—বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের সূতিকাগার এবং যেখানে আশির দশকের শেষের দিকে সংগ্রামরত প্রতিবাদী মিছিলের ওপর শ্বেতাঙ্গ পুলিশ গুলি চালিয়ে দুই ঘণ্টায় ১৩০০ মানুষকে মেরে ফেলেছিল।
এই সেই লাঙ্গা—চারদিকে দারিদ্র্য, বঞ্চনা, শোষণের বীভৎস চিত্র। এ কোন মানবেতর জীবনপ্রবাহ দেখছি আমি? চারপাশের ছাপরা, নোংরা, ভাঙা পথঘাট। পৃথিবীর সবচেয়ে দরিদ্র দেশগুলোর বস্তিগুলোকেও যে হার মানায়। মানুষের ভাগাড় বলে যদি কিছু থাকে, তাহলে এটাই হচ্ছে মানুষের ভাগাড়। নরকও যে এর কাছে হার মানবে।
কিন্তু সবচেয়ে ভয়ংকর হচ্ছে মানুষগুলোর চোখ। ওখানে ক্রোধ, আক্রোশ আর চরম হতাশা ভিন্ন কিছুই নেই। মনে হচ্ছে, সে আক্রোশ অন্য যেকোনো মানুষের প্রতি, সে ক্রোধ সমগ্র পৃথিবীর ওপর, সে হতাশা সারা জীবনের প্রতি। কোনো সংঘর্ষ ভিন্ন মানুষের চোখে অমন হিংস্রতা আর কোথাও দেখিনি। সে হিংস্রতা উড়িয়ে দিতে পারে আশপাশ, পুড়িয়ে দিতে পারে সবকিছু।
‘কোনো দিকে তাকাবেন না, কারও চোখে চোখ রাখবেন না। কোনো কথা বলবেন না, কথা বলতে হলে আমরা বলব। কোনো অবস্থায়ই মুঠোফোন বের করবেন না। ছবি তোলার চেষ্টা করবেন না। বিশেষ বিশেষ জায়গায় আমরা ছবি তুলে দেব। কোনো হিংস্র কাণ্ড দেখে ভয় পেলেও স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করবেন। আমরা লাঙ্গারই লোক। আশা করছি কিছু হবে না। মনে রাখবেন, কৃষ্ণাঙ্গ ছাড়া এখানে কেউ ঢুকলে তাঁদের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। আপনার গায়ের রং এখানে নিষিদ্ধ।’
বলতে বলতে আমাদের গাড়িটি হুস করে দ্রুত বেরিয়ে যায়। এবার একটা শীতল ভয় আমার মেরুদণ্ড বেয়ে ওঠে। টের পাই ঘামে ভিজে যাচ্ছে আমার পোশাক এবং একটা শিরশিরানি কাঁপুনি আমার সারা শরীরে। ‘গাড়িটা একটা নিরাপদ জায়গায় আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে,’ আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে একটি ছাত্র। তারপর তারা তিনজন আমাকে অনেকটা বেষ্টনীর মতো ঘিরে সামনে এগোতে থাকে।
নানান জায়গায় ছোট ছোট জটলা, বাচ্চারা দাঁড়িয়ে আছে এখানে-ওখানে, কর্মরত মহিলাদের দেখা যায় ইতস্তত। কিন্তু টের পাই, আমাদের চারজনের দলটাকে দেখলেই কথা থেমে গিয়ে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা নেমে আসছে—পরিমাপ করা হচ্ছে আমাদের আনখশির। যেন একদল নেকড়ে দাঁত বের করে ঘিরে দাঁড়িয়েছে আমাদের চারদিকে। একটু বেচাল হয়েই ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের ওপরে, ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে আমাদের।
মদের গন্ধে ঘন হয়ে আছে বাতাস আর আশপাশ। ‘এদের প্রধান খাদ্য কি জানেন?’ একটি ছেলে ফিসফিসিয়ে আমাকে জানায়: ‘সকালের নাশতায় মদ, দুপুরের খাবারে মদ, নৈশভোজে সবচেয়ে কড়া মদ নিট। বিশ্বাস করবেন যে, এরা শিশুদেরও মদ গিলিয়ে দেয়, যাতে ওরা ঘুমিয়ে থাকে। তাই লাঙ্গায় কেউই কখনো প্রকৃতিস্থ অবস্থায় থাকে না। সুতরাং যখন যা কিছু ঘটতে পারে। পুলিশও এখানে ঢুকতে ভয় পায়, ঢোকে না। ওই দেখুন বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।’
এক জায়গায় দেখি, একটি ঝুপড়ির সামনে একটি তরুণী মেয়েকে এক যুবক বেধড়ক মারছে। কেন, কে জানে? ছেলেটির হুংকারে, মেয়েটির চিৎকারে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত। চড়-চাপ্পড়, লাঠির বাড়ি, অকথ্য গালিগালাজের তুবড়ি চারদিকে। আড়চোখে তাকিয়েও বুঝতে পারলাম, মেয়েটির চোখ-মুখ রক্তাক্ত। চারপাশ দিয়ে কতজন চলে যাচ্ছে, আশপাশে কতজন কথা বলছে, এদিকে-ওদিকে শিশুরা দাঁড়িয়ে আছে; কিন্তু কেউই ছেলেটিকে থামাতে আসছে না, কিংবা মেয়েটিকে রক্ষা করতে এগোচ্ছে না। যেন কিছুই হয়নি, যেন সবকিছুই স্বাভাবিক। এ কোন নির্বিকারত্ব, এ কোন নির্লিপ্ততা!
বিশ্বাস করুন কী দেখেছিলাম, আমার সবটা ভালো করে মনে নেই। যা মনে আছে, তা-ও বর্ণনা করার উপযুক্ত ভাষা আমার নেই। কেমন একটা ভীতির বুদ্বুদের মধ্যে, একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। যেন দেখতে পারছি না কিছু, যেন সবকিছু বোধের অগম্য। ছাত্রদের তোলা ছবিগুলো লাঙ্গার সবচেয়ে বড় প্রতিচ্ছবি। ওর চেয়ে ভালো সাক্ষ্য আর নেই।
জানতাম চারটি জাতিশ্রেণি আছে দক্ষিণ আফ্রিকায়—শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, বর্ণিল (মিশ্রিত) ও ভারতীয়। যেটা জানতাম না, সেটা হচ্ছে বিভাজনটা তীব্রতম, অবিশ্বাসটা চরমতম এবং হিংসাটি ব্যাপকতম। আমি ভারতীয়ের মধ্যে পড়ব। এবং লাঙ্গায় ভারতীয়রাও গ্রহণযোগ্য নয়। লাঙ্গা কৃষ্ণাঙ্গদের। শুধুই কৃষ্ণাঙ্গদের।
দেখতে দেখতে বড় রাস্তায় পৌঁছলে দেখা গেল রাস্তার ওপারে আমাদের গাড়ি অপেক্ষা করছে। গাড়ির কাছে যেতেই কৃষ্ণাঙ্গ চালক নেমে গেল এবং সে জায়গায় উঠল এক বর্ণিল চালক। মনে হচ্ছে যেন একটা গোয়েন্দা চলচ্চিত্র। রাস্তার ওপারে বর্ণিল জনপদ বন্তেহিউয়েলে ঢুকব। সেখানে কৃষ্ণাঙ্গদের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সুতরাং কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্র তিনজনও সেখানে ঢুকতে পারবে না। তবে আমার গাত্রবর্ণের কারণে আমার অসুবিধে নেই। আর এ জনপদে ভারতীয়রা প্রবেশ করতে পারে। আসলে এ জনপদে একটি বড় ভারতীয় জনগোষ্ঠীও বসবাস করে।
আর এ জনপদ অত ভীতিকরও নয়। এ জনপদের অবস্থাও উন্নততর—একটি নিম্ন মধ্যবিত্তের জনপদ। তবে এখানেও নামব না এবং গাড়ি থেকেই ছবি তুলতে হবে। ৩০ মিনিটের মতো বর্ণিল চালক আর আমি ওই জনপদ ঘুরে এলাম। দেখলাম, বাচ্চাদের হাত ধরে মা-বাবা চলছেন, বাজারের থলে হাতে ফিরছেন এক মহিলা, লাঠি ঠুকে ঠুকে চলছেন এক বৃদ্ধ। শিশুরা খেলছে বাড়ির সামনে, রান্নার গন্ধ ভেসে আসছে কোনো বাড়ি থেকে, একদল কিশোর-কিশোরীর হাস্যরোল শুনতে পাচ্ছি এক পথের বাঁকে। এক স্বাভাবিক জীবনের চালচিত্র।
এবার সবাই মিলে বিমানবন্দরের দিকে যাত্রা। গাড়ির কারও মুখে কোনো কথা নেই। শুধু কিন্তু আমি জানি, প্রত্যেকের মনের মধ্যে প্রত্যেকে কথা বলছে। অন্যদের কথা তো বলতে পারব না। তবে আমার মনের মধ্যে শুধু তোলপাড় করতে লাগল একটিই প্রশ্ন: ‘এ কোন দক্ষিণ আফ্রিকা?’ বারবার মনে হতে লাগল জয় গোস্বামীর কয়েক লাইন:
‘এ কোন দেশে আমরা এলাম?
যতবার গেছি ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেছে তার নাম।
কোথায় সে দেশ—অতীতে না ভবিষ্যতে?’
লেখক: সেলিম জাহান ভূতপূর্ব পরিচালক, মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন দপ্তর এবং দারিদ্র্য বিমোচন বিভাগ, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি
নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
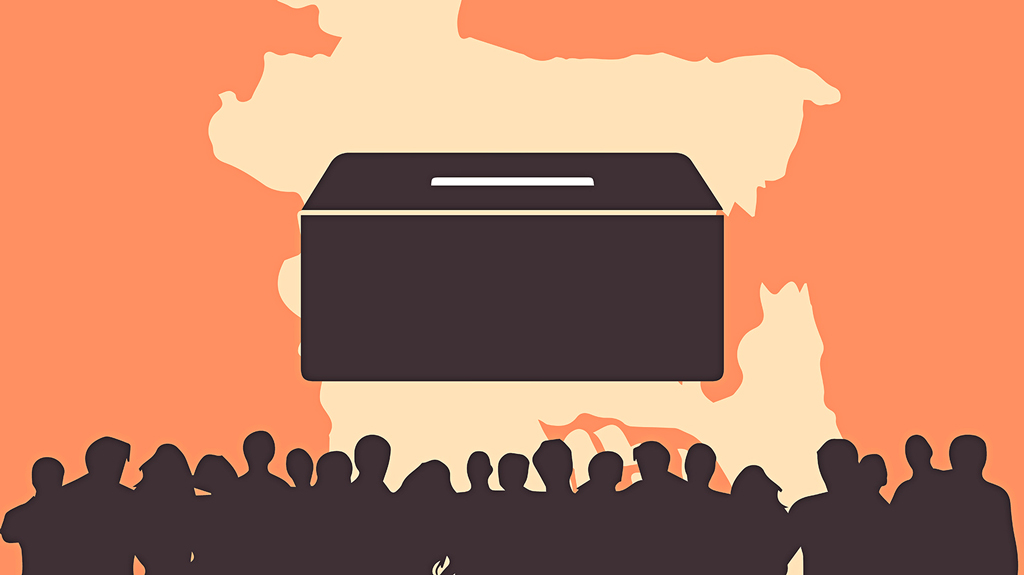
অনেকেরই সংশয় ছিল। কারও কিছুটা হালকা, কারও আবার গভীর। কেউ কেউ শঙ্কিতও ছিলেন। দেশের পরিস্থিতি কোন দিকে যায় তা নিয়ে। এদের সবার সেই সব সংশয় ও শঙ্কা এখন ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। ফলে দেশের শাসনব্যবস্থার গণতান্ত্রিক রূপান্তরকামী সাধারণ মানুষের জন্য তা হয়ে উঠেছে অশনিসংকেত। হ্যাঁ, এই কথাগুলো হচ্ছে ত্রয়োদশ জাতীয়
১৭ ঘণ্টা আগে
ন্যায়বিচার, সংস্কার ও বৈষম্য বিলোপের দাবি থেকে চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান সফল হয়েছিল। দুঃখজনক ব্যাপার হলো, গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে এই আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের অনেকেই অপরাধ চক্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। সম্প্রতি বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস) নেতার উন্মুক্ত চাঁদাবাজির ঘটনা এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।
১৭ ঘণ্টা আগে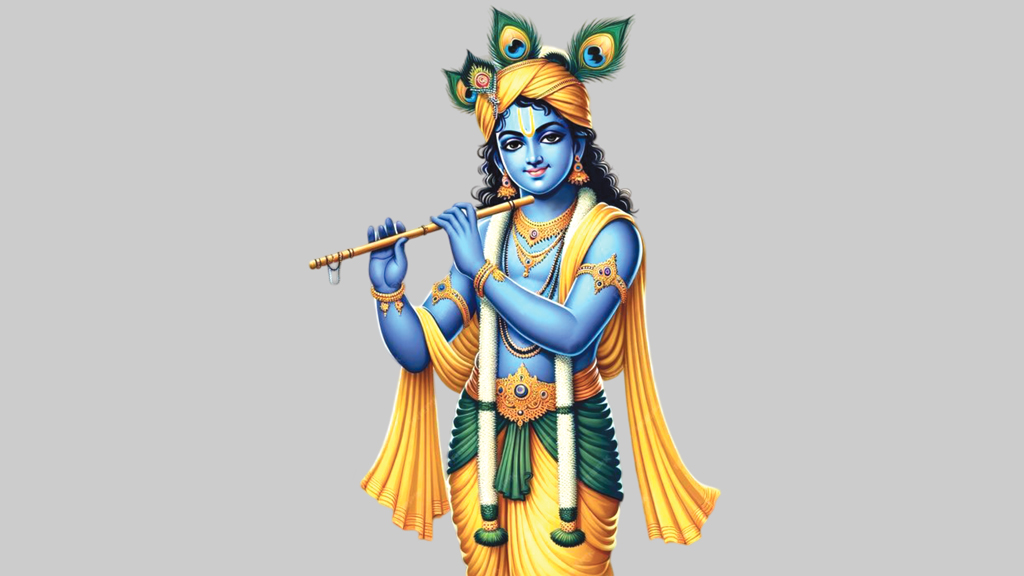
আমাদের সর্বসাধারণের মনে একটা প্রশ্ন সব সময়ই ঘুরপাক খায়—ভগবান যেহেতু অজ, তাহলে তাঁর আবার জন্ম কিসের? এই প্রশ্নের উত্তর ভগবান নিজেই গীতায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন। গীতায় ভগবান বলেছেন, তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি অজ অর্থাৎ জন্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও এই জড়জগতে জন্মগ্রহণ করেন। কেন তিনি জন্মগ্রহণ
১৭ ঘণ্টা আগে
একসময় ভরা মৌসুমে এ দেশের সাধারণ মানুষও ইলিশ কিনতে পারত। কিন্তু অনেক বছর থেকে ইলিশ শুধু উচ্চবিত্ত মানুষেরাই কিনতে পারছে। বাজারে ইলিশের সরবরাহ কম থাকায় এর আকাশছোঁয়া দামের কারণে এখন নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষের নাগালের মধ্যে নেই ইলিশ। এখন ভরা মৌসুমে ইলিশের দাম বাড়া নিয়ে ১৫ আগস্ট আজকের পত্রিকায় একটি সংবাদ
১৭ ঘণ্টা আগে