ফজলুল কবির

এ এক মনোরম শাঁখের করাত। আসতেও কাটছে, যেতেও কাটছে। কোনো নিদানের খোঁজ মিলছে না। যে কাটা পড়ছে, তার নাম ‘গণতন্ত্র’, আর যে কাটছে তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। একবার বলা হচ্ছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম বিশেষত ফেসবুক গণতন্ত্রের জন্য বিরাট হুমকি সৃষ্টি করেছে। আবার কোনো দেশ বা অঞ্চলের গণতান্ত্রিক অবস্থা কেমন, তা বিচারের অন্যতম মানদণ্ড হিসেবে দেখা হচ্ছে সামাজিক মাধ্যমের প্ল্যাটফর্মগুলোতে প্রবেশ এবং সেখানে নিজের মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়টিকে। সেখানে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে দেখা হচ্ছে গণতন্ত্রের জন্য হুমকি হিসেবে।
এই দুইয়ের টানাটানিতে সবচেয়ে করুণ অবস্থা হয়েছে বেচারা গণতন্ত্রের। কোথায় দাঁড়ালে যে এই মহার্ঘ বস্তুটি হুমকির ঊর্ধ্বে থাকবে, তা এখন বোঝা মুশকিল। সব মিলিয়ে ‘গণতন্ত্র’ শব্দটিই এক বিমূর্ত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কীসে যে সে থাকে, এবং কীসে যে থাকে না, তা বোঝা এক কথায় অসম্ভব। বাংলাদেশের মতো দেশে তো এই বস্তু বহু আগেই এক অবোধ্য ধারণায় পরিণত হয়েছে। ক্ষমতাসীন দলের কাছে গণতন্ত্র আছে। আর ক্ষমতার বাইরে থাকা দলের কাছে এ বস্তু তো কবেই গত হয়েছে। ফলে যে ‘গণ’ উপলক্ষ করে এত এত বাণী ও বিতর্ক, সেই গণ রীতিমতো ধন্ধে পড়ে যায় ‘গণতন্ত্র’ নিয়ে।
গত শুক্রবার শান্তিতে নোবেল পুরস্কার ঘোষণা হয়েছে। এই পুরস্কার এবার যৌথভাবে দুই সাংবাদিক পেয়েছেন। এর একজন রাশিয়ার দিমিত্রি মুরাতভ, অন্যজন ফিলিপাইনের মারিয়া রেসা। একজন ভ্লাদিমির পুতিনের দেশের লোক, অন্যজন রদ্রিগো দুতার্তের দেশের, যে দুই দেশ গোটা বিশ্বে একচেটিয়া শাসনের কারণে বেশ আলোচিত। এই দুই দেশ থেকে দুই সাংবাদিকের শান্তিতে নোবেল বিজয় তাই সবাইকে আগ্রহী করে তুলেছে। একই সঙ্গে এই দুই সাংবাদিক এমন দুই কট্টর শাসকের দেশে বসে কী করে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে লড়ে গেলেন, তা নিয়েও সবাই আগ্রহী।
এ অবস্থার মধ্যেই মারিয়া রেসা সাক্ষাৎকার দিলেন বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে। সেখানে তিনি বললেন, ‘ঘৃণা ও ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ। এর মধ্য দিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমটি গণতন্ত্রের জন্য হুমকি তৈরি করছে।’ এমন এক সময় মারিয়া রেসা এ মন্তব্য করলেন, যখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমটির ওপর ‘ভীতিকর ও মুসলিমবিদ্বেষী’ কনটেন্ট ছড়ানো ঠেকাতে ব্যর্থতার অভিযোগ এনেছেন প্রতিষ্ঠানটির সাবেক কর্মী ফ্রান্সেস হাউগেন।
বহুদিন থেকেই আলোচনার কেন্দ্রে ফেসবুক। সেই মার্কিন নির্বাচনে রুশ হস্তক্ষেপ থেকে শুরু করে ক্যাপিটল হিলে হামলা—সব ক্ষেত্রেই ফেসবুকের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ বারবার এসেছে। মূল অভিযোগ—‘ব্যবহারকারীরা ভীতিকর ও মুসলিমবিদ্বেষী কনটেন্ট ছড়াচ্ছেন জেনেও ফেসবুক ব্যবস্থা নিতে পারেনি। বিশ্বে ভুয়া তথ্য ও জাতিগত সহিংসতা ছড়ানোর এটি অন্যতম কারণ।’
কথা হলো এই যে অভিযোগ, এর বিপরীতে কিন্তু ফেসবুকের জোরালো কোনো বক্তব্য নেই। এর আগেও মার্কিন কংগ্রেসে শুনানির জন্য মার্ক জাকারবার্গকে ডাকা হয়েছে। নিজের প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তিনি যেমন সাফাই গেয়েছেন, তেমনি কিছু ভুল শুধরে নেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। তা তিনি রেখেছেন কি-না, বা এই যে নতুন করে নিজেদের সাবেক কর্মী ফ্রান্সিস হাউগেনের সঙ্গে ফেসবুকের মডারেটররা বসার আগ্রহ দেখিয়েছেন, তা কোনো পরিবর্তন আনবে কি-না, তা নিয়ে বলাটা এই লেখার উদ্দেশ্য নয়।
এই গোটা আলোচনায় কেন্দ্রটিই আসলে এখনো প্রচ্ছন্ন রয়ে গেছে। আর তা হলো—প্রচলিত তথ্য মাধ্যমগুলো প্রভাব হারাচ্ছে। মানুষের কাছে সংবাদের অন্যতম উৎস হয়ে উঠেছে ফেসবুকের মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো। অর্থাৎ, প্রচলিত সংবাদমাধ্যমের তুলনায় প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে এই প্ল্যাটফর্মগুলো। এগুলো আবার ওপেন প্ল্যাটফর্ম হওয়ায় যে যেমন পারছে, তেমন করে তথ্য দিচ্ছে। এর একেকটির একেক রকম উদ্দেশ্য থাকছে। ফেসবুকের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ হচ্ছে এই উদ্দেশ্যগুলোর মধ্য থেকে গুটিকয় উদ্দেশ্যকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহার করা।
এ তো গেল অভিযোগের বিষয়টি। এবার আসা যাক ফ্রিডম হাউসের কাছে। কোন দেশে গণতন্ত্রের অবস্থা কী, তা নিরূপণে যে কয়টি মানদণ্ড এই সংস্থার রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। অনলাইনে মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি মানদণ্ড হিসেবে দেখে সংস্থাটি। তাদের সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বজুড়েই ইন্টারনেটে স্বাধীনতা কমেছে। তাও এক-দু বছর ধরে নয়, এগারো বছর ধরে। সবচেয়ে বাজে অবস্থা মিয়ানমার, বেলারুশ ও উগান্ডার। বাংলাদেশের অবস্থানও খুব খারাপ। এ ক্ষেত্রে অনলাইনে প্রবেশযোগ্যতা, সবার জন্য এই সেবার প্রাপ্যতা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের মত প্রকাশের স্বাধীনতা ইত্যাদিকে গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে দেখা হয়েছে। এই সব ক্ষেত্রেই অবনমন হয়েছে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বহু দেশের। ফ্রিডম হাউস এই পরিস্থিতিকে গণতন্ত্রের জন্য হুমকি বলে মনে করছে।
ফলে গণতন্ত্রের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যেন এক দু-ধারি তলোয়ারে পরিণত হয়েছে। এটি বন্ধ বা নিয়ন্ত্রিত থাকলেও গণতন্ত্র ঝুঁকিতে পড়ছে, আবার ব্যাপক সরব থাকলেও পড়ছে। এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে একেকজন একেক ধরনের দাওয়াই দিচ্ছে। কেউ বলছে নিয়ন্ত্রণ করা হোক। খোদ ফেসবুকের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা সম্প্রতি বলেছেন, কিছু ক্ষেত্রে ফেসবুকের অ্যালগরিদমে রাষ্ট্রীয় তদারককারী প্রতিষ্ঠানের প্রবেশাধিকার থাকা দরকার বলে তিনি মনে করেন।
কিন্তু ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্ল্যাটফর্মগুলো জনমত প্রভাবিত করছে, বা সরকারি সংস্থাগুলো নানা নজরদারি প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষের নিত্যদিনের আচরণও নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে—এই আলোচনার কী হবে। এই কিছুদিন আগেই তো নজরদারি নিয়ে বেশ একটা হইচই হয়ে গেল। বলা হলো গণতন্ত্র একেবারে রসাতলে গেল। কিন্তু এখন আবার ফেসবুকে গুজব, ভুয়া তথ্য ইত্যাদি ছড়ানোর বিষয়কে সামনে এনে এই তদারকির নামে যা বলা হচ্ছে, তা কি ঘুরপথে নজরদারিই নয়? তাহলে বিষয়টি কি এমন দাঁড়াল যে, সোজাসুজি নজরদারিতে গণতন্ত্র আহত হলেও ঘুরপথের নজরদারিতে হয় না?
মোদ্দা কথা হলো, নতুন সময়ের এই প্রযুক্তির সঙ্গে দেশে দেশে বিদ্যমান আইনগুলো ঠিক পেরে উঠছে না। মানুষের অধিকারের প্রশ্নের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই আইনের যেমন নবায়ন হয়নি, তেমনি নতুন বাস্তবতার জন্য সামাজিক ও রাজনৈতিক চুক্তিটি ঠিক কী হবে, তাও নিশ্চিত নয়। এই অনিশ্চয়তাই এখন সবচেয়ে প্রভাবশালী। তাই রাজনীতি প্রযুক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করছে, নাকি প্রযুক্তি রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে, করলে মাত্রাটি ঠিক কী, এ দুইয়ের সম্পর্কই-বা কেমন হবে বা হওয়া উচিত, তা এখনো নির্ধারণে হিমশিম খেতে হচ্ছে নীতিনির্ধারকদের।
এ তো গেল একটি দিক। হালের এই আলোচনাগুলো কিন্তু একটি সত্যের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে—আর তা হলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম আদতে ‘নিমিত্ত মাত্র’। ওই যে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত সংলাপ—‘যা করে দাদার খড়ম, আমি তো নিমিত্তমাত্র।’ ঠিক সেই দশা চলছে এখন। যে শাসক জনগণের অধিকার হরণ করতে চায়, সে করছে। যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে মূল্য দিতে চায়, সে দিচ্ছে। তফাৎ হলো, আগের মতো অধিকার প্রশ্নে পথে-ঘাটে আর আন্দোলন হচ্ছে না। ফলে অধিকার হরণ করতে চাওয়া শাসকের সংখ্যা বা শাসকের মধ্যে অধিকার খর্বের প্রবণতা বাড়ছে। আন্দোলন হচ্ছে না বললে অবশ্য এখনকার নেটাগরিকেরা একটু চটে যেতে পারেন। কিন্তু ভেবে দেখুন, অনলাইনে হ্যাশট্যাগ আন্দোলন, বা প্রোফাইল ছবি কালো করে ক্ষোভ জানানো, একের পর এক মিম তৈরি করে শাসকের সমালোচনা করা—এতে আসলে কার কতটুকু আসে-যায়? বিপরীতে জনা বিশেক লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে অবরোধ করল, রাস্তায় যানজট ইত্যাদি সৃষ্টি হলো, আরও হাজারজন দাবিটি মন দিয়ে বা বিরক্তি নিয়ে শুনল, অর্থনীতির চাকায় একটা মৃদু ধাক্কা লাগল, সাধারণের নিত্যকার জীবনযাপনে একটা অস্বস্তি তৈরি হলো—এতে কজনের কী এল-গেল? নিশ্চিতভাবে দ্বিতীয় দশাটিই এড়াতে চাইবেন যেকোনো শাসক। আর তাই অনলাইনে ক্ষোভ-বিক্ষোভ প্রকাশে শাসকদের একটা পর্যায় পর্যন্ত বেশ সহনশীল হতে দেখা যায়। এর শতভাগের একভাগও দেখা যায় না রাস্তায় সশরীরে আন্দোলনের ক্ষেত্রে।
সবচেয়ে বড় কথা হলো—রাজনীতির ময়দান এখনো রাজাদেরই দখলে। এত এত বুলি ও প্রতিশ্রুতি, সূচক ইত্যাদি সত্ত্বেও এই ‘নীতি’ কিন্তু রাজার বাড়ি ছেড়ে জনতার বাড়িতে আসতে পারেনি। ‘রাজনীতি’ থেকে ‘জননীতি’ হয়ে উঠতে না পারা এই নীতিই কিন্তু ‘গণতন্ত্রের’ ‘গণ-বিচ্ছিন্ন’ থেকে যাওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ। এই কারণ এখনো শনাক্ত হয়নি কেন, বা হলেও কেন এতটা অনালোচিত, তা অবশ্য বোধগম্য নয়। এও একটি ‘রাজনীতিই’ নয়?
ফজলুল কবির: লেখক ও সাংবাদিক

এ এক মনোরম শাঁখের করাত। আসতেও কাটছে, যেতেও কাটছে। কোনো নিদানের খোঁজ মিলছে না। যে কাটা পড়ছে, তার নাম ‘গণতন্ত্র’, আর যে কাটছে তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। একবার বলা হচ্ছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম বিশেষত ফেসবুক গণতন্ত্রের জন্য বিরাট হুমকি সৃষ্টি করেছে। আবার কোনো দেশ বা অঞ্চলের গণতান্ত্রিক অবস্থা কেমন, তা বিচারের অন্যতম মানদণ্ড হিসেবে দেখা হচ্ছে সামাজিক মাধ্যমের প্ল্যাটফর্মগুলোতে প্রবেশ এবং সেখানে নিজের মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়টিকে। সেখানে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে দেখা হচ্ছে গণতন্ত্রের জন্য হুমকি হিসেবে।
এই দুইয়ের টানাটানিতে সবচেয়ে করুণ অবস্থা হয়েছে বেচারা গণতন্ত্রের। কোথায় দাঁড়ালে যে এই মহার্ঘ বস্তুটি হুমকির ঊর্ধ্বে থাকবে, তা এখন বোঝা মুশকিল। সব মিলিয়ে ‘গণতন্ত্র’ শব্দটিই এক বিমূর্ত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কীসে যে সে থাকে, এবং কীসে যে থাকে না, তা বোঝা এক কথায় অসম্ভব। বাংলাদেশের মতো দেশে তো এই বস্তু বহু আগেই এক অবোধ্য ধারণায় পরিণত হয়েছে। ক্ষমতাসীন দলের কাছে গণতন্ত্র আছে। আর ক্ষমতার বাইরে থাকা দলের কাছে এ বস্তু তো কবেই গত হয়েছে। ফলে যে ‘গণ’ উপলক্ষ করে এত এত বাণী ও বিতর্ক, সেই গণ রীতিমতো ধন্ধে পড়ে যায় ‘গণতন্ত্র’ নিয়ে।
গত শুক্রবার শান্তিতে নোবেল পুরস্কার ঘোষণা হয়েছে। এই পুরস্কার এবার যৌথভাবে দুই সাংবাদিক পেয়েছেন। এর একজন রাশিয়ার দিমিত্রি মুরাতভ, অন্যজন ফিলিপাইনের মারিয়া রেসা। একজন ভ্লাদিমির পুতিনের দেশের লোক, অন্যজন রদ্রিগো দুতার্তের দেশের, যে দুই দেশ গোটা বিশ্বে একচেটিয়া শাসনের কারণে বেশ আলোচিত। এই দুই দেশ থেকে দুই সাংবাদিকের শান্তিতে নোবেল বিজয় তাই সবাইকে আগ্রহী করে তুলেছে। একই সঙ্গে এই দুই সাংবাদিক এমন দুই কট্টর শাসকের দেশে বসে কী করে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে লড়ে গেলেন, তা নিয়েও সবাই আগ্রহী।
এ অবস্থার মধ্যেই মারিয়া রেসা সাক্ষাৎকার দিলেন বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে। সেখানে তিনি বললেন, ‘ঘৃণা ও ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ। এর মধ্য দিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমটি গণতন্ত্রের জন্য হুমকি তৈরি করছে।’ এমন এক সময় মারিয়া রেসা এ মন্তব্য করলেন, যখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমটির ওপর ‘ভীতিকর ও মুসলিমবিদ্বেষী’ কনটেন্ট ছড়ানো ঠেকাতে ব্যর্থতার অভিযোগ এনেছেন প্রতিষ্ঠানটির সাবেক কর্মী ফ্রান্সেস হাউগেন।
বহুদিন থেকেই আলোচনার কেন্দ্রে ফেসবুক। সেই মার্কিন নির্বাচনে রুশ হস্তক্ষেপ থেকে শুরু করে ক্যাপিটল হিলে হামলা—সব ক্ষেত্রেই ফেসবুকের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ বারবার এসেছে। মূল অভিযোগ—‘ব্যবহারকারীরা ভীতিকর ও মুসলিমবিদ্বেষী কনটেন্ট ছড়াচ্ছেন জেনেও ফেসবুক ব্যবস্থা নিতে পারেনি। বিশ্বে ভুয়া তথ্য ও জাতিগত সহিংসতা ছড়ানোর এটি অন্যতম কারণ।’
কথা হলো এই যে অভিযোগ, এর বিপরীতে কিন্তু ফেসবুকের জোরালো কোনো বক্তব্য নেই। এর আগেও মার্কিন কংগ্রেসে শুনানির জন্য মার্ক জাকারবার্গকে ডাকা হয়েছে। নিজের প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তিনি যেমন সাফাই গেয়েছেন, তেমনি কিছু ভুল শুধরে নেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। তা তিনি রেখেছেন কি-না, বা এই যে নতুন করে নিজেদের সাবেক কর্মী ফ্রান্সিস হাউগেনের সঙ্গে ফেসবুকের মডারেটররা বসার আগ্রহ দেখিয়েছেন, তা কোনো পরিবর্তন আনবে কি-না, তা নিয়ে বলাটা এই লেখার উদ্দেশ্য নয়।
এই গোটা আলোচনায় কেন্দ্রটিই আসলে এখনো প্রচ্ছন্ন রয়ে গেছে। আর তা হলো—প্রচলিত তথ্য মাধ্যমগুলো প্রভাব হারাচ্ছে। মানুষের কাছে সংবাদের অন্যতম উৎস হয়ে উঠেছে ফেসবুকের মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো। অর্থাৎ, প্রচলিত সংবাদমাধ্যমের তুলনায় প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে এই প্ল্যাটফর্মগুলো। এগুলো আবার ওপেন প্ল্যাটফর্ম হওয়ায় যে যেমন পারছে, তেমন করে তথ্য দিচ্ছে। এর একেকটির একেক রকম উদ্দেশ্য থাকছে। ফেসবুকের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ হচ্ছে এই উদ্দেশ্যগুলোর মধ্য থেকে গুটিকয় উদ্দেশ্যকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহার করা।
এ তো গেল অভিযোগের বিষয়টি। এবার আসা যাক ফ্রিডম হাউসের কাছে। কোন দেশে গণতন্ত্রের অবস্থা কী, তা নিরূপণে যে কয়টি মানদণ্ড এই সংস্থার রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। অনলাইনে মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি মানদণ্ড হিসেবে দেখে সংস্থাটি। তাদের সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বজুড়েই ইন্টারনেটে স্বাধীনতা কমেছে। তাও এক-দু বছর ধরে নয়, এগারো বছর ধরে। সবচেয়ে বাজে অবস্থা মিয়ানমার, বেলারুশ ও উগান্ডার। বাংলাদেশের অবস্থানও খুব খারাপ। এ ক্ষেত্রে অনলাইনে প্রবেশযোগ্যতা, সবার জন্য এই সেবার প্রাপ্যতা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের মত প্রকাশের স্বাধীনতা ইত্যাদিকে গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে দেখা হয়েছে। এই সব ক্ষেত্রেই অবনমন হয়েছে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বহু দেশের। ফ্রিডম হাউস এই পরিস্থিতিকে গণতন্ত্রের জন্য হুমকি বলে মনে করছে।
ফলে গণতন্ত্রের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যেন এক দু-ধারি তলোয়ারে পরিণত হয়েছে। এটি বন্ধ বা নিয়ন্ত্রিত থাকলেও গণতন্ত্র ঝুঁকিতে পড়ছে, আবার ব্যাপক সরব থাকলেও পড়ছে। এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে একেকজন একেক ধরনের দাওয়াই দিচ্ছে। কেউ বলছে নিয়ন্ত্রণ করা হোক। খোদ ফেসবুকের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা সম্প্রতি বলেছেন, কিছু ক্ষেত্রে ফেসবুকের অ্যালগরিদমে রাষ্ট্রীয় তদারককারী প্রতিষ্ঠানের প্রবেশাধিকার থাকা দরকার বলে তিনি মনে করেন।
কিন্তু ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্ল্যাটফর্মগুলো জনমত প্রভাবিত করছে, বা সরকারি সংস্থাগুলো নানা নজরদারি প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষের নিত্যদিনের আচরণও নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে—এই আলোচনার কী হবে। এই কিছুদিন আগেই তো নজরদারি নিয়ে বেশ একটা হইচই হয়ে গেল। বলা হলো গণতন্ত্র একেবারে রসাতলে গেল। কিন্তু এখন আবার ফেসবুকে গুজব, ভুয়া তথ্য ইত্যাদি ছড়ানোর বিষয়কে সামনে এনে এই তদারকির নামে যা বলা হচ্ছে, তা কি ঘুরপথে নজরদারিই নয়? তাহলে বিষয়টি কি এমন দাঁড়াল যে, সোজাসুজি নজরদারিতে গণতন্ত্র আহত হলেও ঘুরপথের নজরদারিতে হয় না?
মোদ্দা কথা হলো, নতুন সময়ের এই প্রযুক্তির সঙ্গে দেশে দেশে বিদ্যমান আইনগুলো ঠিক পেরে উঠছে না। মানুষের অধিকারের প্রশ্নের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই আইনের যেমন নবায়ন হয়নি, তেমনি নতুন বাস্তবতার জন্য সামাজিক ও রাজনৈতিক চুক্তিটি ঠিক কী হবে, তাও নিশ্চিত নয়। এই অনিশ্চয়তাই এখন সবচেয়ে প্রভাবশালী। তাই রাজনীতি প্রযুক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করছে, নাকি প্রযুক্তি রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে, করলে মাত্রাটি ঠিক কী, এ দুইয়ের সম্পর্কই-বা কেমন হবে বা হওয়া উচিত, তা এখনো নির্ধারণে হিমশিম খেতে হচ্ছে নীতিনির্ধারকদের।
এ তো গেল একটি দিক। হালের এই আলোচনাগুলো কিন্তু একটি সত্যের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে—আর তা হলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম আদতে ‘নিমিত্ত মাত্র’। ওই যে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত সংলাপ—‘যা করে দাদার খড়ম, আমি তো নিমিত্তমাত্র।’ ঠিক সেই দশা চলছে এখন। যে শাসক জনগণের অধিকার হরণ করতে চায়, সে করছে। যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে মূল্য দিতে চায়, সে দিচ্ছে। তফাৎ হলো, আগের মতো অধিকার প্রশ্নে পথে-ঘাটে আর আন্দোলন হচ্ছে না। ফলে অধিকার হরণ করতে চাওয়া শাসকের সংখ্যা বা শাসকের মধ্যে অধিকার খর্বের প্রবণতা বাড়ছে। আন্দোলন হচ্ছে না বললে অবশ্য এখনকার নেটাগরিকেরা একটু চটে যেতে পারেন। কিন্তু ভেবে দেখুন, অনলাইনে হ্যাশট্যাগ আন্দোলন, বা প্রোফাইল ছবি কালো করে ক্ষোভ জানানো, একের পর এক মিম তৈরি করে শাসকের সমালোচনা করা—এতে আসলে কার কতটুকু আসে-যায়? বিপরীতে জনা বিশেক লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে অবরোধ করল, রাস্তায় যানজট ইত্যাদি সৃষ্টি হলো, আরও হাজারজন দাবিটি মন দিয়ে বা বিরক্তি নিয়ে শুনল, অর্থনীতির চাকায় একটা মৃদু ধাক্কা লাগল, সাধারণের নিত্যকার জীবনযাপনে একটা অস্বস্তি তৈরি হলো—এতে কজনের কী এল-গেল? নিশ্চিতভাবে দ্বিতীয় দশাটিই এড়াতে চাইবেন যেকোনো শাসক। আর তাই অনলাইনে ক্ষোভ-বিক্ষোভ প্রকাশে শাসকদের একটা পর্যায় পর্যন্ত বেশ সহনশীল হতে দেখা যায়। এর শতভাগের একভাগও দেখা যায় না রাস্তায় সশরীরে আন্দোলনের ক্ষেত্রে।
সবচেয়ে বড় কথা হলো—রাজনীতির ময়দান এখনো রাজাদেরই দখলে। এত এত বুলি ও প্রতিশ্রুতি, সূচক ইত্যাদি সত্ত্বেও এই ‘নীতি’ কিন্তু রাজার বাড়ি ছেড়ে জনতার বাড়িতে আসতে পারেনি। ‘রাজনীতি’ থেকে ‘জননীতি’ হয়ে উঠতে না পারা এই নীতিই কিন্তু ‘গণতন্ত্রের’ ‘গণ-বিচ্ছিন্ন’ থেকে যাওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ। এই কারণ এখনো শনাক্ত হয়নি কেন, বা হলেও কেন এতটা অনালোচিত, তা অবশ্য বোধগম্য নয়। এও একটি ‘রাজনীতিই’ নয়?
ফজলুল কবির: লেখক ও সাংবাদিক

আসন্ন নির্বাচন সম্পর্কে প্রায়ই নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হই—প্রাক্-নির্বাচন আইনগত এবং সাংবিধানিক বিষয়ে এবং নির্বাচন-পরবর্তী বিষয়েও। প্রথম বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে একধরনের স্বস্তি বোধ করি—প্রশ্নকারীকে সরাসরি বলি যে আমি আইনের লোক নই কিংবা সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞও নই।
১৩ ঘণ্টা আগে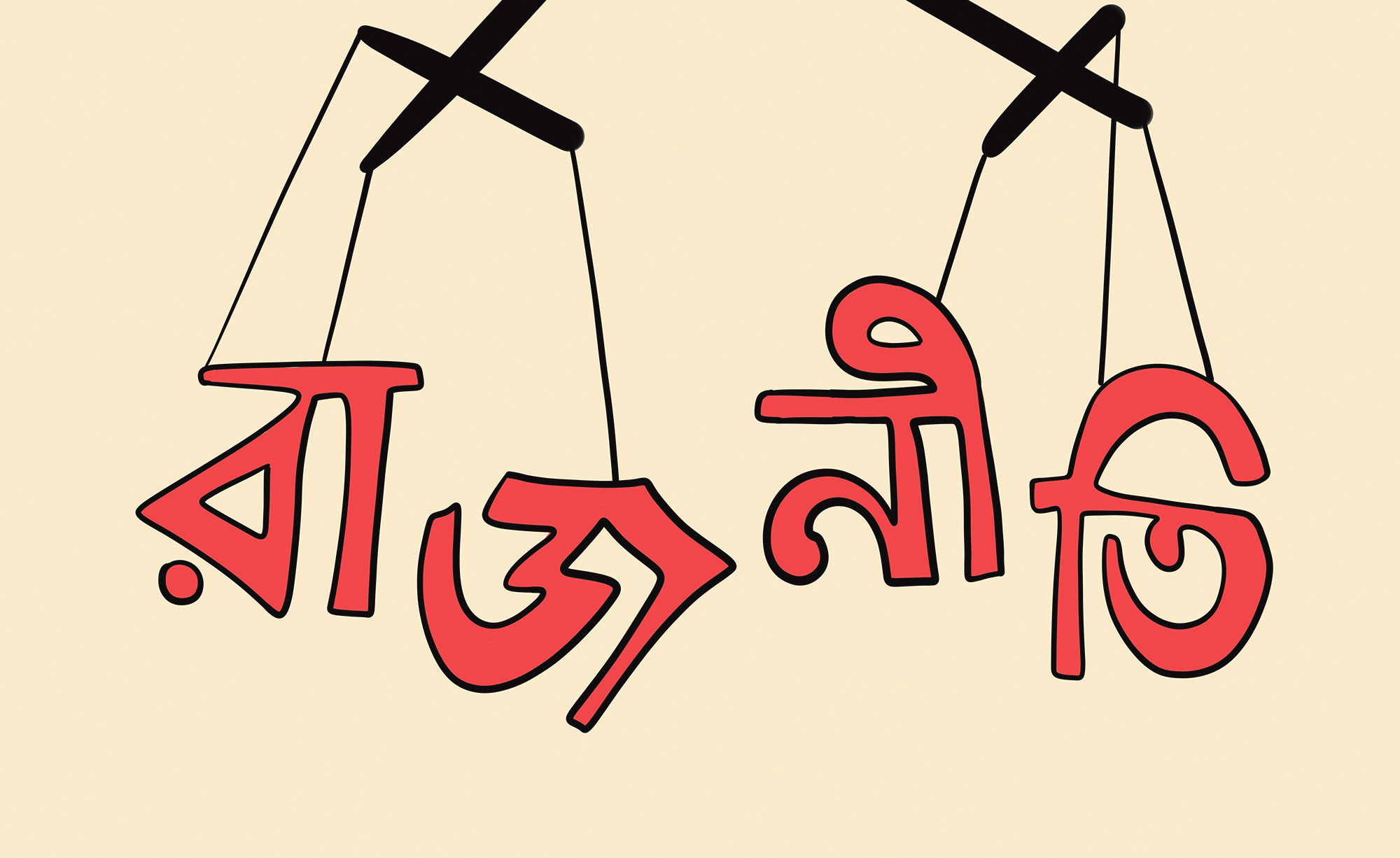
বাংলাদেশের রাজনীতিতে জুলাই সনদ ২০২৫ এবং গণভোট ইস্যু একধরনের বহুমাত্রিক সংকটের সূচনা করেছে, যা সাংবিধানিক বাস্তবতা, রাজনৈতিক মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া, জনগণের অংশগ্রহণ এবং সামাজিক আস্থার সঙ্গে জড়িত। এই সংকট শুধু রাজনৈতিক দলের কৌশলগত দ্বন্দ্ব নয়...
১৩ ঘণ্টা আগে
উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছে। শুধু রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেই নয়, সাধারণ মানুষের মনেও জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ককটেল, বাসে আগুন, জুলাই সনদ বিষয়ে রাজনৈতিক বিভিন্ন দলের বিতর্ক ইত্যাদি কারণে অস্থিরতা বাড়ছে।
১৩ ঘণ্টা আগে
গত এপ্রিলে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের ‘বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আউটলুক’-এর পূর্বাভাস জানিয়েছিল, এ বছর বাংলাদেশে নতুন করে আরও ৩০ লাখ মানুষ অতিদরিদ্র শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে এবং দারিদ্র্যের হার ২০ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ২১ দশমিক ২ শতাংশে।
২ দিন আগেপ্রায়ই প্রশ্ন শুনি, কোনটা আগে—গণতন্ত্র, না মানব উন্নয়ন? আসলে দুটিই একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, যেহেতু দুটিই পারস্পরিকভাবে সম্পৃক্ত। মানব উন্নয়নের দুটি মৌলিক মাত্রিকতা হচ্ছে মানুষের সক্ষমতা ও সুযোগের বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে তার কণ্ঠস্বরের অধিকার—মতপ্রকাশে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে।
সেলিম জাহান

আসন্ন নির্বাচন সম্পর্কে প্রায়ই নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হই—প্রাক্-নির্বাচন আইনগত এবং সাংবিধানিক বিষয়ে এবং নির্বাচন-পরবর্তী বিষয়েও। প্রথম বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে একধরনের স্বস্তি বোধ করি—প্রশ্নকারীকে সরাসরি বলি যে আমি আইনের লোক নই কিংবা সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞও নই। সুতরাং প্রাক্-নির্বাচন আইনগত এবং সাংবিধানিক বিষয়ে বলার মতো জ্ঞান আমার নেই। কিন্তু যখন আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে কী অবস্থা হবে, তখন বিব্রত বোধ করি। আমার কাছে তো কোনো ভবিষ্যৎ-লিখন স্ফটিক গোলক নেই যে ভবিষ্যৎ বলার স্পর্ধা রাখি।
তবে এটা জানি, দেশের জনগণ নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে আছে একবুক প্রত্যাশা নিয়ে। তারা আশা করে আছে যে নির্বাচনের পরে তাদের জীবনে স্বস্তি আসবে, বর্তমান সময়ের অনিশ্চিত আর অস্থির সময়ের অবসান হবে, উত্তরণ ঘটবে একটি গণতান্ত্রিক কাঠামো আর সংস্কৃতিতে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, একটি স্বচ্ছ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে একটি জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করা হলেই কি জনগণের প্রত্যাশা পূরণ হবে? একটি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে উঠবে, দারিদ্র্য ও বৈষম্য কমে যাবে এবং মানুষের জীবনের উন্নতি হবে?
গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রতিস্থাপন একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের দৌড় নয়, এটি একটি দীর্ঘ সময়ের পথযাত্রা। একটি সুষ্ঠু নির্বাচন এই পথযাত্রার একটি ধাপ, একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত, কিন্তু পর্যাপ্ত শর্ত নয়। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হলে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে হবে সর্বস্তরে—ব্যক্তিজীবনে, পারিবারিক অঙ্গনে, সামাজিক বলয়ে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে। সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের নিরন্তর চর্চা ভিন্ন কোনো জনগোষ্ঠীতে একটি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা যায় না। একই সঙ্গে প্রয়োজন হবে দৃশ্যমানতা এবং দায়বদ্ধতার একটি শক্ত কাঠামো। গণতন্ত্রের জন্য অবিরাম সংগ্রামের নামই গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি।
সাধারণভাবে, গণতন্ত্র বলতে আমরা রাজনৈতিক গণতন্ত্রকেই বুঝি। কিন্তু গণতন্ত্রের একটি অর্থনৈতিক মাত্রিকতাও আছে, যাকে আমরা অর্থনৈতিক গণতন্ত্র বলতে পারি। অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের তিনটি মৌলিক মাত্রিকতা থাকে—সক্ষমতা গঠন এবং সুযোগ ব্যবহারে সমান অধিকার; সমতামূলক অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব এবং ফলাফলে সাম্যমূলক বণ্টন। একটি সাম্যসম্পন্ন, বৈষম্যহীন এবং ন্যায্য অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে হলে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র অপরিহার্য। অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য হচ্ছে একটি অর্থনৈতিক সমতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। আর সেই জন্য প্রয়োজন হয় সব ক্ষেত্রে সমান সুযোগের। সেই সুযোগ গ্রহণ করার জন্য প্রত্যেক মানুষের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন হবে শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো মৌলিক সামাজিক সেবাগুলোতে সবার সমান প্রবেশাধিকার। কিন্তু সামাজিক সেবাগুলোতে অধিকারকে শুধু পরিমাণগত দিক থেকে দেখলে চলবে না, তাকে নিশ্চিত করতে হবে গুণগত দিক দিয়ে। মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং সুস্থ ব্যবস্থামূলক স্বাস্থ্য সবার কাছে লভ্য করে দিতে হবে।
প্রায়ই প্রশ্ন শুনি, কোনটা আগে—গণতন্ত্র, না মানব উন্নয়ন? আসলে দুটিই একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, যেহেতু দুটিই পারস্পরিকভাবে সম্পৃক্ত। মানব উন্নয়নের দুটি মৌলিক মাত্রিকতা হচ্ছে মানুষের সক্ষমতা এবং সুযোগের বৃদ্ধি; সেই সঙ্গে তার কণ্ঠস্বরের অধিকার—মতপ্রকাশে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে। মানব উন্নয়নের প্রথম মাত্রিকতা অর্জনে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র অপরিহার্য এবং তার দ্বিতীয় মাত্রিকতা অর্জনে রাজনৈতিক গণতন্ত্র লাগবেই।
গণতন্ত্র মানব উন্নয়নের মূল ভিত্তি নয়, তবে একটি অত্যাবশ্যকীয় স্তম্ভ। গণতন্ত্র এবং মানব উন্নয়ন—উভয়ের ভিত্তিভূমি হচ্ছে মানবাধিকার, সাম্য এবং মানবিক নিরাপত্তা। গণতন্ত্র ও মানব উন্নয়ন—উভয়েই উভয়কে শাণিত করে। রাজনৈতিক গণতন্ত্র না থাকলে মানুষের রাজনৈতিক অধিকার, তার নিরাপত্তা এবং তার কণ্ঠস্বরের স্বাধীনতা খর্ব হয়। অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের অনুপস্থিতিতে মানুষের সক্ষমতা এবং সুযোগ বিঘ্নিত হয়। অন্যদিকে মানব উন্নয়ন খর্বিত হলে মানুষ তার অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যায়; তার কণ্ঠস্বরের স্বাধীনতা সে প্রয়োগ করতে পারে না এবং সমাজের আলাপ-আলোচনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিতে পারে না।
অর্থনৈতিক গণতান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে পড়লে মানব উন্নয়নের তিনটি বিষয় বিঘ্নিত হয়। এক. অর্থনৈতিক সম্পদ এবং সামাজিক সেবায় সম-অধিকার বিনষ্ট হয়, ফলে সুযোগ ও সম্পদ একটি শ্রেণির হাতে কুক্ষিগত হয়ে যায়। দুই. অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা এবং দৃশ্যমানতা ও দায়বদ্ধতার কাঠামোটি ভেঙে পড়ে এবং তিন. দুর্নীতি ও লুণ্ঠনের একটি সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। এ প্রক্রিয়ার মাঝেই জনগণের অর্থের অপচয় এবং লোপাট ঘটে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায়। বিগত দিনগুলোতে বাংলাদেশে এই চিত্র আমরা বারবার দেখেছি।
আমরা সব সময় ‘অগ্রগতির’ ওপর জোর দিয়েছি, ‘উন্নয়নের’ ওপর নয়। তাই আমাদের চিন্তাচেতনায় ‘আয়ের প্রবৃদ্ধি’ যতখানি মনোযোগ পেয়েছে, তার বণ্টন ততটা পায়নি। আমরা ভৌত অবকাঠামোকে গুরুত্ব দিয়েছি, কিন্তু মানুষকে গুণসম্পন্ন সেবা প্রদানকে ততটা নয়। আমরা পরিমাণগত অগ্রগতির জন্য জান-প্রাণ খেটেছি, কিন্তু উপেক্ষা করেছি নানান সামাজিক সেবার গুণগত মান। তাই শিক্ষার হার বেড়েছে, কিন্তু শিক্ষার মান বাড়েনি। উন্নত মানের স্বাস্থ্যসেবা সংরক্ষিত রয়ে গেছে ধনিক শ্রেণির জন্য। নিম্নমানের সেবা কিংবা কোনো সেবাই পায়নি দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। ফলে অসমতা আর বৈষম্য আরও বেড়েছে। এমন একটি অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে কাঙ্ক্ষিত মানবসম্পদ আমরা গড়ে তুলতে পারিনি। ফলে একদিকে যেমন আমাদের প্রবৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তেমনি বেড়েছে কর্মহীনতা এবং জাতীয় আয়ে শ্রমের ভাগ ৪২ শতাংশের বেশি ওঠেনি, যুক্তরাষ্ট্রে যেটা ৬২ শতাংশ।
বিশ্বকে দেখানোর জন্য বিরাট অঙ্কের ঋণ নিয়ে বিশাল বিশাল মর্যাদামূলক প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, জনকুশলে যার অবদান তাৎপর্যহীন। সেসব ক্ষেত্রে সম্পদ প্রবাহিত হওয়ায় শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতে সম্পদের লভ্যতা কমেছে, মানব উন্নয়ন ব্যাহত হয়েছে, কিন্তু দেশের ঋণভার বেড়েছে। তার সুদ পরিশোধ করতে গিয়ে সম্পদের পরিমাণ আরও কমেছে।
গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিনির্মাণের ক্ষেত্রে নির্বাচন প্রসঙ্গে যে প্রশ্ন আগে উত্থাপিত হয়েছে, অর্থনৈতিক গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক নানান কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে সেই প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক। একটি স্বচ্ছ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে একটি জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেই কি অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, দারিদ্র্য ও বৈষম্য কমে যাবে এবং মানুষের জীবনের উন্নতি হবে?
না, সেই প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় নয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। মনে রাখা দরকার, রাজনৈতিক গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক গণতন্ত্র—দুটিই আমাদের অর্থনৈতিক অন্তরায়গুলো মোকাবিলা করার জন্য অত্যাবশ্যকীয়। নির্বাচিত সরকারকে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের কিছু কিছু মৌলিক বিষয়ে নজর দিতে হবে। প্রথমত, তাকে ‘উন্নয়নের’ দিকে নজর দিতে হবে; নিছক ‘অগ্রগতি’র দিকে নয়। সুতরাং শুধু পরিমাণগত বৃদ্ধি নয়, সেই বৃদ্ধির গুণগত মানের দিকেও সরকারের অগ্রাধিকার থাকবে। অর্থনৈতিক গণতন্ত্র নিশ্চিত করতে যথোপযুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে, দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং একটি দৃশ্যমানতা ও দায়বদ্ধতার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে।
এর জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন মেয়াদের বাস্তবায়নযোগ্য সংস্কার। অর্থনৈতিক নীতিমালাগুলোকে ঢেলে সাজাতে হবে, যাতে সব ধরনের সম্পদ, উৎপাদন উপকরণ ও সামাজিক সেবায় সমতাসম্পন্ন সাম্যমূলক অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকে।
দ্বিতীয়ত, যেসব বিষয় অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, স্থিতিশীলতা এবং অগ্রগতির পরিপন্থী হিসেবে কাজ করেছে, সেগুলো প্রতিহত করতে হবে। সমাজে ত্রাস, আশঙ্কা ও আতঙ্কের যে একটি পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তা দূর করা দরকার। নির্বাচিত সরকারের অর্থনৈতিক নীতিমালার প্রতি আস্থার কোনো বিকল্প নেই। এই আস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে পরে বিনিয়োগ বাড়বে, কর্মনিয়োজন বিস্তৃত হবে এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি কাঙ্ক্ষিত গতিময়তা সৃষ্টি হবে।
তৃতীয়ত, নির্বাচিত সরকারের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন রূপরেখায় একটি উন্নয়ন দর্শন থাকতে হবে। সেই দর্শনের মূলকথা হবে মানুষের উন্নয়ন, মানুষের জন্য উন্নয়ন এবং মানুষের দ্বারা উন্নয়ন। মানুষের সক্ষমতার প্রসার ঘটতে হবে—পরিমাণগত এবং গুণগত উভয় দিক থেকে এবং সেই সক্ষমতার প্রসার শুধু তার কুশলেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, তাতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে মানুষের কণ্ঠস্বরের স্বাধীনতা, তার অংশগ্রহণ। উন্নয়নের সুফল সুষমভাবে বণ্টিত হতে হবে—শুধু ফলাফলের সুষম বণ্টন নয়, সুযোগের সমবণ্টনও।
চতুর্থত, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পথযাত্রার একটি নৈতিক ভিত্তি থাকবে। উন্নয়নের লক্ষ্য শুধু প্রবৃদ্ধি নয়, শুধু বস্তুগত বিষয়ের সমাহার নয়, উন্নয়নের লক্ষ্য মানবাধিকারের প্রতিষ্ঠা, মানুষের মানবিক মর্যাদা সুনিশ্চিত করা, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, মানুষের মধ্যে সহনশীলতা, পরধর্ম এবং পরমতসহিষ্ণুতার একটি পরিবেশ গড়ে তোলা। উন্নয়নের নৈতিক ভিত্তির ভেতরে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অধিষ্ঠান ও নিরন্তর চর্চা একান্ত দরকার। সেই চর্চা হতে হবে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে, কর্মক্ষেত্রে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, রাজনৈতিক দল ও প্রক্রিয়ার মাঝে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে। এর পথ ধরেই পরিহার করতে হবে সন্ত্রাস এবং সহিংসতা।
পঞ্চমত, উন্নয়ন প্রসঙ্গে বাংলাদেশকে একটি বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হবে। বাংলাদেশ অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদি পথযাত্রার অন্যতম নির্ণায়ক হতে হবে বিশ্বের অর্থনীতি প্রবণতা, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কাঠামো এবং ভূ-রাজনৈতিক অবস্থা। সে প্রসঙ্গে আগামী বছরে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে বাংলাদেশের প্রস্তুতিপর্ব এবং উত্তরণ-উত্তর কার্যক্রম প্রণয়নের জন্য একটি বাস্তবসম্মত রূপরেখা তৈরি করতে হবে।
চূড়ান্ত বিচারে, একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন একটি নির্বাচিত সরকার বাংলাদেশের আগামী পথযাত্রার একটি আবশ্যকীয় শর্ত, কিন্তু একটি পর্যাপ্ত শর্ত নয়। সেই পথযাত্রার রূপরেখা তৈরির জন্য নির্বাচিত সরকারের যেমন অঙ্গীকার এবং অগ্রাধিকার লাগবে, তেমনি দরকার হবে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ। এই দুয়ের সমন্বয়ে হোক বাংলাদেশের দীপ্ত সম্মিলিত পথপরিক্রমা।
লেখক: অর্থনীতিবিদ

আসন্ন নির্বাচন সম্পর্কে প্রায়ই নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হই—প্রাক্-নির্বাচন আইনগত এবং সাংবিধানিক বিষয়ে এবং নির্বাচন-পরবর্তী বিষয়েও। প্রথম বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে একধরনের স্বস্তি বোধ করি—প্রশ্নকারীকে সরাসরি বলি যে আমি আইনের লোক নই কিংবা সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞও নই। সুতরাং প্রাক্-নির্বাচন আইনগত এবং সাংবিধানিক বিষয়ে বলার মতো জ্ঞান আমার নেই। কিন্তু যখন আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে কী অবস্থা হবে, তখন বিব্রত বোধ করি। আমার কাছে তো কোনো ভবিষ্যৎ-লিখন স্ফটিক গোলক নেই যে ভবিষ্যৎ বলার স্পর্ধা রাখি।
তবে এটা জানি, দেশের জনগণ নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে আছে একবুক প্রত্যাশা নিয়ে। তারা আশা করে আছে যে নির্বাচনের পরে তাদের জীবনে স্বস্তি আসবে, বর্তমান সময়ের অনিশ্চিত আর অস্থির সময়ের অবসান হবে, উত্তরণ ঘটবে একটি গণতান্ত্রিক কাঠামো আর সংস্কৃতিতে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, একটি স্বচ্ছ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে একটি জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করা হলেই কি জনগণের প্রত্যাশা পূরণ হবে? একটি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে উঠবে, দারিদ্র্য ও বৈষম্য কমে যাবে এবং মানুষের জীবনের উন্নতি হবে?
গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রতিস্থাপন একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের দৌড় নয়, এটি একটি দীর্ঘ সময়ের পথযাত্রা। একটি সুষ্ঠু নির্বাচন এই পথযাত্রার একটি ধাপ, একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত, কিন্তু পর্যাপ্ত শর্ত নয়। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হলে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে হবে সর্বস্তরে—ব্যক্তিজীবনে, পারিবারিক অঙ্গনে, সামাজিক বলয়ে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে। সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের নিরন্তর চর্চা ভিন্ন কোনো জনগোষ্ঠীতে একটি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা যায় না। একই সঙ্গে প্রয়োজন হবে দৃশ্যমানতা এবং দায়বদ্ধতার একটি শক্ত কাঠামো। গণতন্ত্রের জন্য অবিরাম সংগ্রামের নামই গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি।
সাধারণভাবে, গণতন্ত্র বলতে আমরা রাজনৈতিক গণতন্ত্রকেই বুঝি। কিন্তু গণতন্ত্রের একটি অর্থনৈতিক মাত্রিকতাও আছে, যাকে আমরা অর্থনৈতিক গণতন্ত্র বলতে পারি। অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের তিনটি মৌলিক মাত্রিকতা থাকে—সক্ষমতা গঠন এবং সুযোগ ব্যবহারে সমান অধিকার; সমতামূলক অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব এবং ফলাফলে সাম্যমূলক বণ্টন। একটি সাম্যসম্পন্ন, বৈষম্যহীন এবং ন্যায্য অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে হলে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র অপরিহার্য। অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য হচ্ছে একটি অর্থনৈতিক সমতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। আর সেই জন্য প্রয়োজন হয় সব ক্ষেত্রে সমান সুযোগের। সেই সুযোগ গ্রহণ করার জন্য প্রত্যেক মানুষের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন হবে শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো মৌলিক সামাজিক সেবাগুলোতে সবার সমান প্রবেশাধিকার। কিন্তু সামাজিক সেবাগুলোতে অধিকারকে শুধু পরিমাণগত দিক থেকে দেখলে চলবে না, তাকে নিশ্চিত করতে হবে গুণগত দিক দিয়ে। মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং সুস্থ ব্যবস্থামূলক স্বাস্থ্য সবার কাছে লভ্য করে দিতে হবে।
প্রায়ই প্রশ্ন শুনি, কোনটা আগে—গণতন্ত্র, না মানব উন্নয়ন? আসলে দুটিই একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, যেহেতু দুটিই পারস্পরিকভাবে সম্পৃক্ত। মানব উন্নয়নের দুটি মৌলিক মাত্রিকতা হচ্ছে মানুষের সক্ষমতা এবং সুযোগের বৃদ্ধি; সেই সঙ্গে তার কণ্ঠস্বরের অধিকার—মতপ্রকাশে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে। মানব উন্নয়নের প্রথম মাত্রিকতা অর্জনে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র অপরিহার্য এবং তার দ্বিতীয় মাত্রিকতা অর্জনে রাজনৈতিক গণতন্ত্র লাগবেই।
গণতন্ত্র মানব উন্নয়নের মূল ভিত্তি নয়, তবে একটি অত্যাবশ্যকীয় স্তম্ভ। গণতন্ত্র এবং মানব উন্নয়ন—উভয়ের ভিত্তিভূমি হচ্ছে মানবাধিকার, সাম্য এবং মানবিক নিরাপত্তা। গণতন্ত্র ও মানব উন্নয়ন—উভয়েই উভয়কে শাণিত করে। রাজনৈতিক গণতন্ত্র না থাকলে মানুষের রাজনৈতিক অধিকার, তার নিরাপত্তা এবং তার কণ্ঠস্বরের স্বাধীনতা খর্ব হয়। অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের অনুপস্থিতিতে মানুষের সক্ষমতা এবং সুযোগ বিঘ্নিত হয়। অন্যদিকে মানব উন্নয়ন খর্বিত হলে মানুষ তার অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যায়; তার কণ্ঠস্বরের স্বাধীনতা সে প্রয়োগ করতে পারে না এবং সমাজের আলাপ-আলোচনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিতে পারে না।
অর্থনৈতিক গণতান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে পড়লে মানব উন্নয়নের তিনটি বিষয় বিঘ্নিত হয়। এক. অর্থনৈতিক সম্পদ এবং সামাজিক সেবায় সম-অধিকার বিনষ্ট হয়, ফলে সুযোগ ও সম্পদ একটি শ্রেণির হাতে কুক্ষিগত হয়ে যায়। দুই. অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা এবং দৃশ্যমানতা ও দায়বদ্ধতার কাঠামোটি ভেঙে পড়ে এবং তিন. দুর্নীতি ও লুণ্ঠনের একটি সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। এ প্রক্রিয়ার মাঝেই জনগণের অর্থের অপচয় এবং লোপাট ঘটে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায়। বিগত দিনগুলোতে বাংলাদেশে এই চিত্র আমরা বারবার দেখেছি।
আমরা সব সময় ‘অগ্রগতির’ ওপর জোর দিয়েছি, ‘উন্নয়নের’ ওপর নয়। তাই আমাদের চিন্তাচেতনায় ‘আয়ের প্রবৃদ্ধি’ যতখানি মনোযোগ পেয়েছে, তার বণ্টন ততটা পায়নি। আমরা ভৌত অবকাঠামোকে গুরুত্ব দিয়েছি, কিন্তু মানুষকে গুণসম্পন্ন সেবা প্রদানকে ততটা নয়। আমরা পরিমাণগত অগ্রগতির জন্য জান-প্রাণ খেটেছি, কিন্তু উপেক্ষা করেছি নানান সামাজিক সেবার গুণগত মান। তাই শিক্ষার হার বেড়েছে, কিন্তু শিক্ষার মান বাড়েনি। উন্নত মানের স্বাস্থ্যসেবা সংরক্ষিত রয়ে গেছে ধনিক শ্রেণির জন্য। নিম্নমানের সেবা কিংবা কোনো সেবাই পায়নি দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। ফলে অসমতা আর বৈষম্য আরও বেড়েছে। এমন একটি অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে কাঙ্ক্ষিত মানবসম্পদ আমরা গড়ে তুলতে পারিনি। ফলে একদিকে যেমন আমাদের প্রবৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তেমনি বেড়েছে কর্মহীনতা এবং জাতীয় আয়ে শ্রমের ভাগ ৪২ শতাংশের বেশি ওঠেনি, যুক্তরাষ্ট্রে যেটা ৬২ শতাংশ।
বিশ্বকে দেখানোর জন্য বিরাট অঙ্কের ঋণ নিয়ে বিশাল বিশাল মর্যাদামূলক প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, জনকুশলে যার অবদান তাৎপর্যহীন। সেসব ক্ষেত্রে সম্পদ প্রবাহিত হওয়ায় শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতে সম্পদের লভ্যতা কমেছে, মানব উন্নয়ন ব্যাহত হয়েছে, কিন্তু দেশের ঋণভার বেড়েছে। তার সুদ পরিশোধ করতে গিয়ে সম্পদের পরিমাণ আরও কমেছে।
গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিনির্মাণের ক্ষেত্রে নির্বাচন প্রসঙ্গে যে প্রশ্ন আগে উত্থাপিত হয়েছে, অর্থনৈতিক গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক নানান কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে সেই প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক। একটি স্বচ্ছ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে একটি জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেই কি অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, দারিদ্র্য ও বৈষম্য কমে যাবে এবং মানুষের জীবনের উন্নতি হবে?
না, সেই প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় নয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। মনে রাখা দরকার, রাজনৈতিক গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক গণতন্ত্র—দুটিই আমাদের অর্থনৈতিক অন্তরায়গুলো মোকাবিলা করার জন্য অত্যাবশ্যকীয়। নির্বাচিত সরকারকে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের কিছু কিছু মৌলিক বিষয়ে নজর দিতে হবে। প্রথমত, তাকে ‘উন্নয়নের’ দিকে নজর দিতে হবে; নিছক ‘অগ্রগতি’র দিকে নয়। সুতরাং শুধু পরিমাণগত বৃদ্ধি নয়, সেই বৃদ্ধির গুণগত মানের দিকেও সরকারের অগ্রাধিকার থাকবে। অর্থনৈতিক গণতন্ত্র নিশ্চিত করতে যথোপযুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে, দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং একটি দৃশ্যমানতা ও দায়বদ্ধতার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে।
এর জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন মেয়াদের বাস্তবায়নযোগ্য সংস্কার। অর্থনৈতিক নীতিমালাগুলোকে ঢেলে সাজাতে হবে, যাতে সব ধরনের সম্পদ, উৎপাদন উপকরণ ও সামাজিক সেবায় সমতাসম্পন্ন সাম্যমূলক অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকে।
দ্বিতীয়ত, যেসব বিষয় অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, স্থিতিশীলতা এবং অগ্রগতির পরিপন্থী হিসেবে কাজ করেছে, সেগুলো প্রতিহত করতে হবে। সমাজে ত্রাস, আশঙ্কা ও আতঙ্কের যে একটি পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তা দূর করা দরকার। নির্বাচিত সরকারের অর্থনৈতিক নীতিমালার প্রতি আস্থার কোনো বিকল্প নেই। এই আস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে পরে বিনিয়োগ বাড়বে, কর্মনিয়োজন বিস্তৃত হবে এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি কাঙ্ক্ষিত গতিময়তা সৃষ্টি হবে।
তৃতীয়ত, নির্বাচিত সরকারের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন রূপরেখায় একটি উন্নয়ন দর্শন থাকতে হবে। সেই দর্শনের মূলকথা হবে মানুষের উন্নয়ন, মানুষের জন্য উন্নয়ন এবং মানুষের দ্বারা উন্নয়ন। মানুষের সক্ষমতার প্রসার ঘটতে হবে—পরিমাণগত এবং গুণগত উভয় দিক থেকে এবং সেই সক্ষমতার প্রসার শুধু তার কুশলেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, তাতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে মানুষের কণ্ঠস্বরের স্বাধীনতা, তার অংশগ্রহণ। উন্নয়নের সুফল সুষমভাবে বণ্টিত হতে হবে—শুধু ফলাফলের সুষম বণ্টন নয়, সুযোগের সমবণ্টনও।
চতুর্থত, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পথযাত্রার একটি নৈতিক ভিত্তি থাকবে। উন্নয়নের লক্ষ্য শুধু প্রবৃদ্ধি নয়, শুধু বস্তুগত বিষয়ের সমাহার নয়, উন্নয়নের লক্ষ্য মানবাধিকারের প্রতিষ্ঠা, মানুষের মানবিক মর্যাদা সুনিশ্চিত করা, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, মানুষের মধ্যে সহনশীলতা, পরধর্ম এবং পরমতসহিষ্ণুতার একটি পরিবেশ গড়ে তোলা। উন্নয়নের নৈতিক ভিত্তির ভেতরে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অধিষ্ঠান ও নিরন্তর চর্চা একান্ত দরকার। সেই চর্চা হতে হবে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে, কর্মক্ষেত্রে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, রাজনৈতিক দল ও প্রক্রিয়ার মাঝে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে। এর পথ ধরেই পরিহার করতে হবে সন্ত্রাস এবং সহিংসতা।
পঞ্চমত, উন্নয়ন প্রসঙ্গে বাংলাদেশকে একটি বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হবে। বাংলাদেশ অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদি পথযাত্রার অন্যতম নির্ণায়ক হতে হবে বিশ্বের অর্থনীতি প্রবণতা, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কাঠামো এবং ভূ-রাজনৈতিক অবস্থা। সে প্রসঙ্গে আগামী বছরে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে বাংলাদেশের প্রস্তুতিপর্ব এবং উত্তরণ-উত্তর কার্যক্রম প্রণয়নের জন্য একটি বাস্তবসম্মত রূপরেখা তৈরি করতে হবে।
চূড়ান্ত বিচারে, একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন একটি নির্বাচিত সরকার বাংলাদেশের আগামী পথযাত্রার একটি আবশ্যকীয় শর্ত, কিন্তু একটি পর্যাপ্ত শর্ত নয়। সেই পথযাত্রার রূপরেখা তৈরির জন্য নির্বাচিত সরকারের যেমন অঙ্গীকার এবং অগ্রাধিকার লাগবে, তেমনি দরকার হবে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ। এই দুয়ের সমন্বয়ে হোক বাংলাদেশের দীপ্ত সম্মিলিত পথপরিক্রমা।
লেখক: অর্থনীতিবিদ

সবচেয়ে করুণ অবস্থা হয়েছে বেচারা গণতন্ত্রের। কোথায় দাঁড়ালে যে এই মহার্ঘ বস্তুটি হুমকির ঊর্ধ্বে থাকবে, তা এখন বোঝা মুশকিল। সব মিলিয়ে ‘গণতন্ত্র’ শব্দটিই এক বিমূর্ত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কীসে যে সে থাকে, এবং কীসে যে থাকে না, তা বোঝা এক কথায় অসম্ভব।
১২ অক্টোবর ২০২১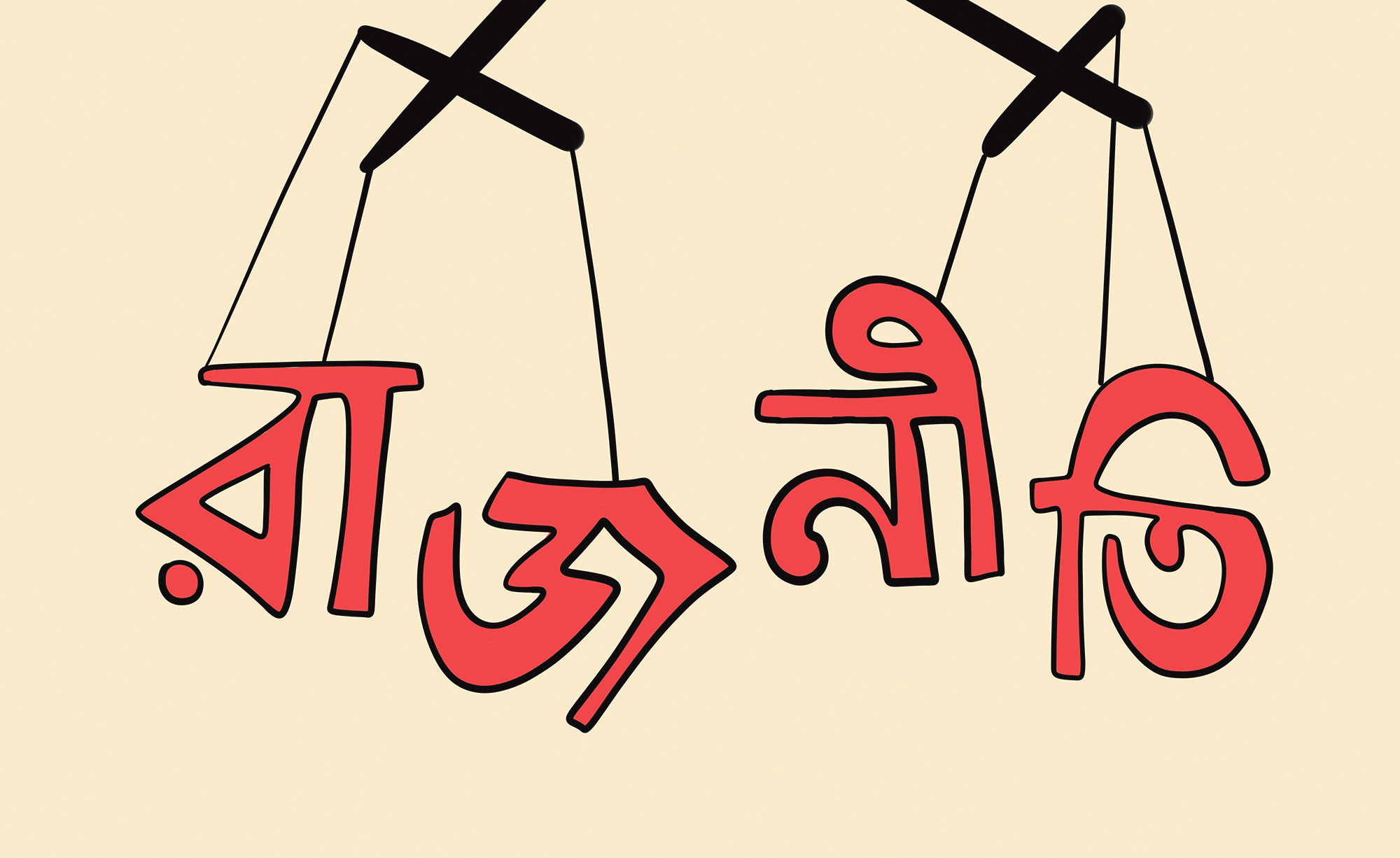
বাংলাদেশের রাজনীতিতে জুলাই সনদ ২০২৫ এবং গণভোট ইস্যু একধরনের বহুমাত্রিক সংকটের সূচনা করেছে, যা সাংবিধানিক বাস্তবতা, রাজনৈতিক মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া, জনগণের অংশগ্রহণ এবং সামাজিক আস্থার সঙ্গে জড়িত। এই সংকট শুধু রাজনৈতিক দলের কৌশলগত দ্বন্দ্ব নয়...
১৩ ঘণ্টা আগে
উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছে। শুধু রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেই নয়, সাধারণ মানুষের মনেও জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ককটেল, বাসে আগুন, জুলাই সনদ বিষয়ে রাজনৈতিক বিভিন্ন দলের বিতর্ক ইত্যাদি কারণে অস্থিরতা বাড়ছে।
১৩ ঘণ্টা আগে
গত এপ্রিলে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের ‘বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আউটলুক’-এর পূর্বাভাস জানিয়েছিল, এ বছর বাংলাদেশে নতুন করে আরও ৩০ লাখ মানুষ অতিদরিদ্র শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে এবং দারিদ্র্যের হার ২০ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ২১ দশমিক ২ শতাংশে।
২ দিন আগেরাফায়েল আহমেদ শামীম
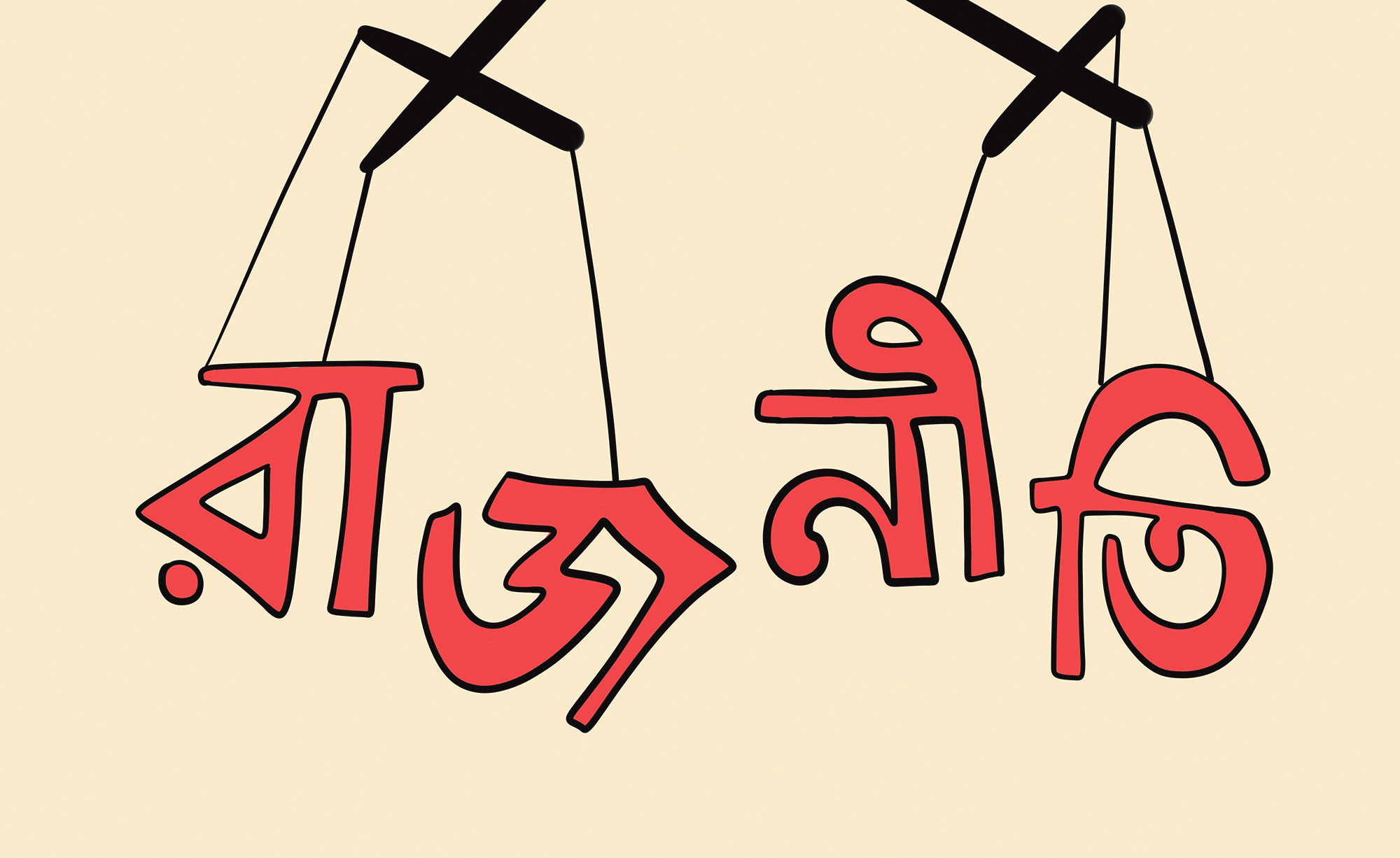
বাংলাদেশের রাজনীতিতে জুলাই সনদ ২০২৫ এবং গণভোট ইস্যু একধরনের বহুমাত্রিক সংকটের সূচনা করেছে, যা সাংবিধানিক বাস্তবতা, রাজনৈতিক মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া, জনগণের অংশগ্রহণ এবং সামাজিক আস্থার সঙ্গে জড়িত। এই সংকট শুধু রাজনৈতিক দলের কৌশলগত দ্বন্দ্ব নয়; বরং এটি দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি, অর্থনীতি, ভোটার মনস্তত্ত্ব এবং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।
বিএনপি ও জামায়াতের মুখোমুখি অবস্থান, সংলাপের ব্যর্থতা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মনস্তাত্ত্বিক কৌশল এই সংকটকে তীব্র করেছে। বিএনপি গণভোটের তারিখকে জাতীয় নির্বাচনের সঙ্গে মিলিয়ে আয়োজনের পক্ষে। তাদের যুক্তি হলো, বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনের আগে আলাদা গণভোট সম্ভব নয় এবং এটি ব্যয়বহুল ও রাজনৈতিকভাবে অপ্রয়োজনীয়। অন্যদিকে জামায়াত এবং এনসিপি নির্বাচনের আগে গণভোটের পক্ষে অনড়। তাদের যুক্তি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার নৈতিকতার সঙ্গে সম্পর্কিত। তারা মনে করে, নির্বাচনের আগে গণভোট অনুষ্ঠিত হলে জনগণ সাংবিধানিক সংস্কার, রাজনৈতিক পুনর্গঠন এবং অংশগ্রহণমূলক সুশাসনের লক্ষ্য গভীরভাবে উপলব্ধি করবে। এই অবস্থান রাজনৈতিক মনস্তত্ত্বের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, এটি ভোটারদের সচেতন অংশগ্রহণসহ রাজনৈতিক আস্থা বৃদ্ধির ওপর জোর দেয়।
রাজনৈতিক মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নির্দেশ করে যে বিএনপি এবং জামায়াতের অবস্থান শুধু স্বার্থসংশ্লিষ্ট নয়, বরং এটি জনগণের রাজনৈতিক আচরণ, সামাজিক আস্থা এবং ভোটার মনস্তত্ত্বের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। নির্বাচনের দিন এবং গণভোটের আলাদা দিন এই দুই বিষয় শুধু কৌশলগত নয়, বরং এটি রাজনৈতিক মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিন্যাস। বিএনপি মনে করে, এক দিনে নির্বাচন ও গণভোট আয়োজন করলে ভোটারদের মনস্তাত্ত্বিক বিভ্রান্তি কমবে। জামায়াতের মতে, আলাদা দিনে গণভোটের মাধ্যমে জনগণ বিষয়টি গভীরভাবে বুঝতে পারবে এবং সংস্কারের প্রতি আস্থা বাড়বে। সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, বর্তমান সংবিধানে গণভোটের কোনো প্রাসঙ্গিক বিধান নেই। বিএনপি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে, জাতীয় সংসদে পাস হওয়ার আগে গণভোটের কোনো সাংবিধানিক ভিত্তি নেই। জামায়াত এই শূন্যতাকে উপেক্ষা করে জনগণকে সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে চায়। এই সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক অমিল শুধু রাজনৈতিক উত্তেজনাই সৃষ্টি করছে না, বরং সামাজিক আস্থা ও জনগণের রাজনৈতিক বিশ্বাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে।
অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটও গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনের আগে আলাদা গণভোট আয়োজন ব্যয়বহুল এবং দেশের সীমিত আর্থিক সম্পদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। সরকার এবং নির্বাচন কমিশনকে অতিরিক্ত বাজেট ব্যবস্থাপনা করতে হবে, যা দেশের উন্নয়ন, সামাজিক বিনিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে, সংবিধান সংস্কার এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্যে গণভোট বা জনগণকে সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের প্রয়াস বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়।
নেপালে সংবিধান সংস্কারের ক্ষেত্রে ৯ বছরের দীর্ঘ প্রক্রিয়া চালানো হয়েছিল, যেখানে প্রতিটি ধাপেই রাজনৈতিক দলগুলোর মনস্তাত্ত্বিক অবস্থান, জনগণের মনোভাব এবং সামাজিক অংশগ্রহণ বিবেচনা করা হয়েছিল। বাংলাদেশেও রাজনৈতিক দলগুলোর মনস্তাত্ত্বিক কৌশল এবং জনগণের অংশগ্রহণের গুরুত্ব অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ভোটার মনস্তত্ত্বের দিক থেকে দেখা যায়, জনগণ দুটি সংকটকে মোকাবিলা করছে—একদিকে রাজনৈতিক অচলাবস্থা ও সংলাপহীনতা, অন্যদিকে সাংবিধানিক বাস্তবতা এবং সরকারের প্রক্রিয়ার প্রতি আস্থা। যদি নির্বাচনের আগে গণভোট অনুষ্ঠিত না হয়, জনগণের মধ্যে হতাশা এবং অবিশ্বাস বাড়তে পারে। কিন্তু নির্বাচনের সঙ্গে মিলিয়ে গণভোট আয়োজন করলে ভোটার মনস্তাত্ত্বিকভাবে সমন্বিত এবং কার্যকর অংশগ্রহণ করতে পারবে।
বিএনপি, জামায়াত এবং এনসিপির মধ্যে রাজনৈতিক মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব মূলত তিনটি স্তরে পর্যবসিত। প্রথম স্তর হলো সাংবিধানিক বাস্তবতা এবং সংলাপের সীমাবদ্ধতা। দ্বিতীয় স্তর হলো রাজনৈতিক স্বার্থ ও কৌশলগত অবস্থান এবং তৃতীয় স্তর হলো জনগণের মনস্তত্ত্ব এবং সামাজিক আস্থা। এই তিন স্তরের মধ্যে ভারসাম্য না থাকলে রাজনৈতিক অচলাবস্থা দীর্ঘমেয়াদি এবং গভীর হতে পারে। সংলাপ ও ঐকমত্যের অপ্রতুলতা এই সংকটকে আরও তীব্র করেছে। সরকার বিএনপি, জামায়াত এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দলের জন্য আলোচনার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল, কিন্তু দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা এবং আলোচনার অভাব রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। বিএনপি দলীয় বৈঠকে উল্লেখ করেছে, সরকার উদ্যোগ নিলে আলোচনা সম্ভব, অন্যথায় সমাধান অসম্ভব। এই মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতি প্রদর্শন করছে যে দলগুলো সরকারের প্রতি আস্থা রাখতে পারছে না, বরং তাদের নিজস্ব কৌশল এবং রাজনৈতিক স্বার্থে আবদ্ধ রয়েছে।
আন্তর্জাতিক তুলনায় দেখা যায়, সংবিধান সংস্কার ও গণভোটের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া প্রয়োজন। নেপাল, দক্ষিণ কোরিয়া ও ফিলিপাইনের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে সংলাপ, রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয় এবং জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা না হলে গণতান্ত্রিক সংস্কার ব্যর্থ হতে পারে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ব এবং ভোটার অংশগ্রহণ সমন্বয় করার প্রয়োজন রয়েছে।
বিএনপি ও জামায়াতের এই মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব শুধু রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকেই প্রভাবিত করছে না; বরং জনগণের রাজনৈতিক চেতনা, সামাজিক বিশ্বাস এবং নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতাও প্রভাবিত করছে। সংক্ষেপে বলা যায়, জুলাই সনদ ও গণভোটের সংকট শুধু নির্বাচন কিংবা সংবিধানবিষয়ক নয়। এটি রাজনৈতিক মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে একটি বহুমাত্রিক সংকট। সরকারের জন্য প্রয়োজন—দ্রুত, কার্যকর এবং ন্যায্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা, তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক—সংলাপ, সাংবিধানিক বাস্তবায়ন এবং রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করা। এই কার্যক্রম ব্যর্থ হলে রাজনৈতিক অচলাবস্থা, সামাজিক বিভাজন এবং গণতান্ত্রিক ক্ষয়—এগুলো বাংলাদেশের রাজনীতির জন্য দীর্ঘমেয়াদি হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।
এ ছাড়া দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি, সাংবিধানিক বাস্তবতা এবং জনগণের আস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই সরকারের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোরও দায়িত্ব—সংলাপ, মনস্তাত্ত্বিক কৌশল এবং সমঝোতার মাধ্যমে সংকটের সমাধান করা। বর্তমান এই পরিস্থিতিতে বিএনপি, জামায়াত এবং এনসিপি একদিকে সাংবিধানিক বাস্তবতা; অন্যদিকে রাজনৈতিক স্বার্থের মধ্যে বিভক্ত। বিএনপি গণভোটকে নির্বাচনের দিনই আয়োজন করার পক্ষে, জামায়াত নির্বাচনের আগে গণভোটের অধিকার নিশ্চিত করতে চাইছে। এই অবস্থান কার্যত একধরনের রাজনৈতিক সংকট তৈরি করেছে, যা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিরল। দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, সংবিধান সংস্কার এবং রাজনৈতিক সংস্কারের বাস্তবায়ন—এগুলো বর্তমানে রাজনৈতিক উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে।
রাফায়েল আহমেদ শামীম, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কলাম লেখক
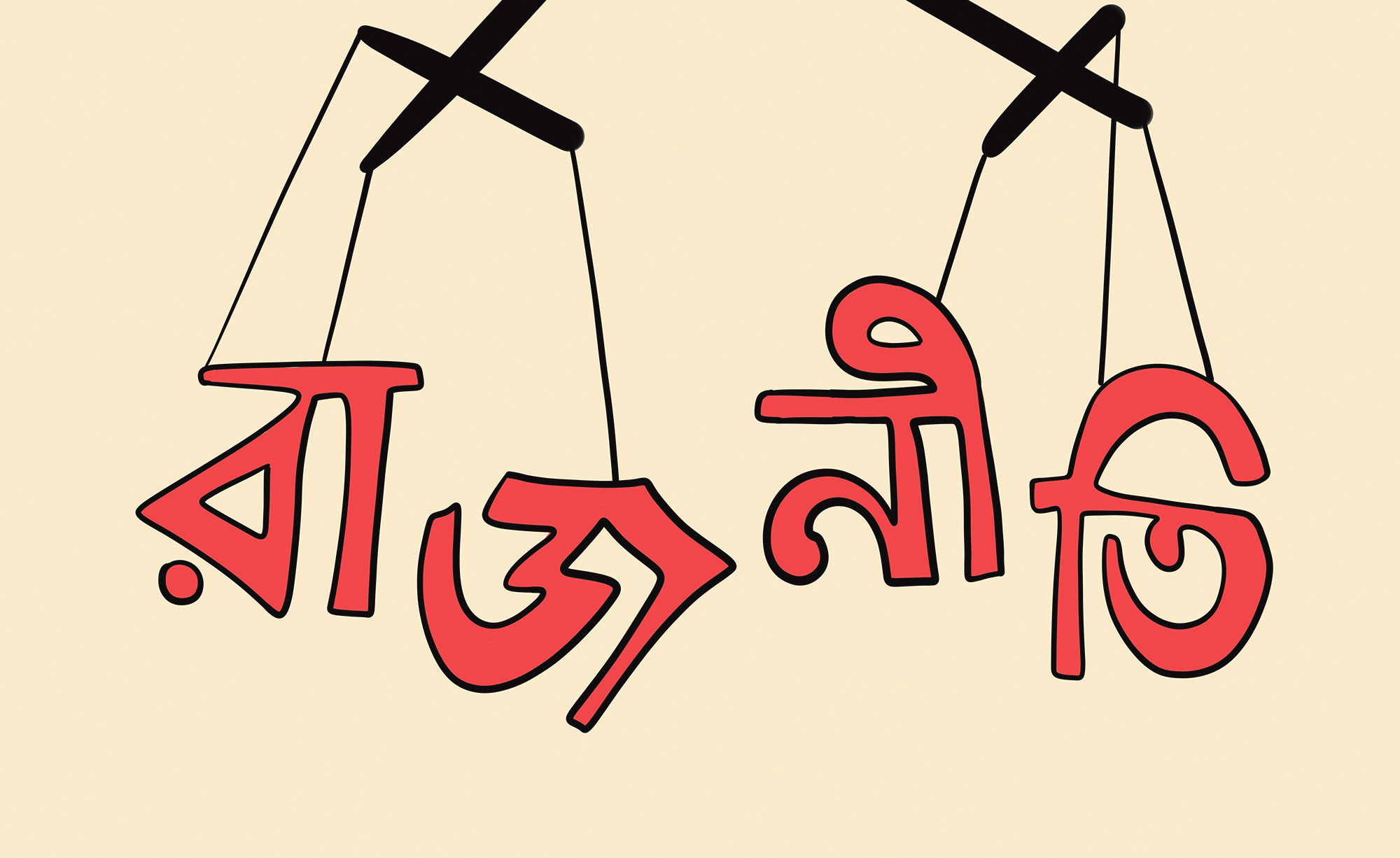
বাংলাদেশের রাজনীতিতে জুলাই সনদ ২০২৫ এবং গণভোট ইস্যু একধরনের বহুমাত্রিক সংকটের সূচনা করেছে, যা সাংবিধানিক বাস্তবতা, রাজনৈতিক মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া, জনগণের অংশগ্রহণ এবং সামাজিক আস্থার সঙ্গে জড়িত। এই সংকট শুধু রাজনৈতিক দলের কৌশলগত দ্বন্দ্ব নয়; বরং এটি দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি, অর্থনীতি, ভোটার মনস্তত্ত্ব এবং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।
বিএনপি ও জামায়াতের মুখোমুখি অবস্থান, সংলাপের ব্যর্থতা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মনস্তাত্ত্বিক কৌশল এই সংকটকে তীব্র করেছে। বিএনপি গণভোটের তারিখকে জাতীয় নির্বাচনের সঙ্গে মিলিয়ে আয়োজনের পক্ষে। তাদের যুক্তি হলো, বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনের আগে আলাদা গণভোট সম্ভব নয় এবং এটি ব্যয়বহুল ও রাজনৈতিকভাবে অপ্রয়োজনীয়। অন্যদিকে জামায়াত এবং এনসিপি নির্বাচনের আগে গণভোটের পক্ষে অনড়। তাদের যুক্তি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার নৈতিকতার সঙ্গে সম্পর্কিত। তারা মনে করে, নির্বাচনের আগে গণভোট অনুষ্ঠিত হলে জনগণ সাংবিধানিক সংস্কার, রাজনৈতিক পুনর্গঠন এবং অংশগ্রহণমূলক সুশাসনের লক্ষ্য গভীরভাবে উপলব্ধি করবে। এই অবস্থান রাজনৈতিক মনস্তত্ত্বের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, এটি ভোটারদের সচেতন অংশগ্রহণসহ রাজনৈতিক আস্থা বৃদ্ধির ওপর জোর দেয়।
রাজনৈতিক মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নির্দেশ করে যে বিএনপি এবং জামায়াতের অবস্থান শুধু স্বার্থসংশ্লিষ্ট নয়, বরং এটি জনগণের রাজনৈতিক আচরণ, সামাজিক আস্থা এবং ভোটার মনস্তত্ত্বের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। নির্বাচনের দিন এবং গণভোটের আলাদা দিন এই দুই বিষয় শুধু কৌশলগত নয়, বরং এটি রাজনৈতিক মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিন্যাস। বিএনপি মনে করে, এক দিনে নির্বাচন ও গণভোট আয়োজন করলে ভোটারদের মনস্তাত্ত্বিক বিভ্রান্তি কমবে। জামায়াতের মতে, আলাদা দিনে গণভোটের মাধ্যমে জনগণ বিষয়টি গভীরভাবে বুঝতে পারবে এবং সংস্কারের প্রতি আস্থা বাড়বে। সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, বর্তমান সংবিধানে গণভোটের কোনো প্রাসঙ্গিক বিধান নেই। বিএনপি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে, জাতীয় সংসদে পাস হওয়ার আগে গণভোটের কোনো সাংবিধানিক ভিত্তি নেই। জামায়াত এই শূন্যতাকে উপেক্ষা করে জনগণকে সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে চায়। এই সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক অমিল শুধু রাজনৈতিক উত্তেজনাই সৃষ্টি করছে না, বরং সামাজিক আস্থা ও জনগণের রাজনৈতিক বিশ্বাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে।
অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটও গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনের আগে আলাদা গণভোট আয়োজন ব্যয়বহুল এবং দেশের সীমিত আর্থিক সম্পদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। সরকার এবং নির্বাচন কমিশনকে অতিরিক্ত বাজেট ব্যবস্থাপনা করতে হবে, যা দেশের উন্নয়ন, সামাজিক বিনিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে, সংবিধান সংস্কার এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্যে গণভোট বা জনগণকে সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের প্রয়াস বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়।
নেপালে সংবিধান সংস্কারের ক্ষেত্রে ৯ বছরের দীর্ঘ প্রক্রিয়া চালানো হয়েছিল, যেখানে প্রতিটি ধাপেই রাজনৈতিক দলগুলোর মনস্তাত্ত্বিক অবস্থান, জনগণের মনোভাব এবং সামাজিক অংশগ্রহণ বিবেচনা করা হয়েছিল। বাংলাদেশেও রাজনৈতিক দলগুলোর মনস্তাত্ত্বিক কৌশল এবং জনগণের অংশগ্রহণের গুরুত্ব অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ভোটার মনস্তত্ত্বের দিক থেকে দেখা যায়, জনগণ দুটি সংকটকে মোকাবিলা করছে—একদিকে রাজনৈতিক অচলাবস্থা ও সংলাপহীনতা, অন্যদিকে সাংবিধানিক বাস্তবতা এবং সরকারের প্রক্রিয়ার প্রতি আস্থা। যদি নির্বাচনের আগে গণভোট অনুষ্ঠিত না হয়, জনগণের মধ্যে হতাশা এবং অবিশ্বাস বাড়তে পারে। কিন্তু নির্বাচনের সঙ্গে মিলিয়ে গণভোট আয়োজন করলে ভোটার মনস্তাত্ত্বিকভাবে সমন্বিত এবং কার্যকর অংশগ্রহণ করতে পারবে।
বিএনপি, জামায়াত এবং এনসিপির মধ্যে রাজনৈতিক মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব মূলত তিনটি স্তরে পর্যবসিত। প্রথম স্তর হলো সাংবিধানিক বাস্তবতা এবং সংলাপের সীমাবদ্ধতা। দ্বিতীয় স্তর হলো রাজনৈতিক স্বার্থ ও কৌশলগত অবস্থান এবং তৃতীয় স্তর হলো জনগণের মনস্তত্ত্ব এবং সামাজিক আস্থা। এই তিন স্তরের মধ্যে ভারসাম্য না থাকলে রাজনৈতিক অচলাবস্থা দীর্ঘমেয়াদি এবং গভীর হতে পারে। সংলাপ ও ঐকমত্যের অপ্রতুলতা এই সংকটকে আরও তীব্র করেছে। সরকার বিএনপি, জামায়াত এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দলের জন্য আলোচনার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল, কিন্তু দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা এবং আলোচনার অভাব রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। বিএনপি দলীয় বৈঠকে উল্লেখ করেছে, সরকার উদ্যোগ নিলে আলোচনা সম্ভব, অন্যথায় সমাধান অসম্ভব। এই মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতি প্রদর্শন করছে যে দলগুলো সরকারের প্রতি আস্থা রাখতে পারছে না, বরং তাদের নিজস্ব কৌশল এবং রাজনৈতিক স্বার্থে আবদ্ধ রয়েছে।
আন্তর্জাতিক তুলনায় দেখা যায়, সংবিধান সংস্কার ও গণভোটের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া প্রয়োজন। নেপাল, দক্ষিণ কোরিয়া ও ফিলিপাইনের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে সংলাপ, রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয় এবং জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা না হলে গণতান্ত্রিক সংস্কার ব্যর্থ হতে পারে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ব এবং ভোটার অংশগ্রহণ সমন্বয় করার প্রয়োজন রয়েছে।
বিএনপি ও জামায়াতের এই মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব শুধু রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকেই প্রভাবিত করছে না; বরং জনগণের রাজনৈতিক চেতনা, সামাজিক বিশ্বাস এবং নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতাও প্রভাবিত করছে। সংক্ষেপে বলা যায়, জুলাই সনদ ও গণভোটের সংকট শুধু নির্বাচন কিংবা সংবিধানবিষয়ক নয়। এটি রাজনৈতিক মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে একটি বহুমাত্রিক সংকট। সরকারের জন্য প্রয়োজন—দ্রুত, কার্যকর এবং ন্যায্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা, তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক—সংলাপ, সাংবিধানিক বাস্তবায়ন এবং রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করা। এই কার্যক্রম ব্যর্থ হলে রাজনৈতিক অচলাবস্থা, সামাজিক বিভাজন এবং গণতান্ত্রিক ক্ষয়—এগুলো বাংলাদেশের রাজনীতির জন্য দীর্ঘমেয়াদি হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।
এ ছাড়া দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি, সাংবিধানিক বাস্তবতা এবং জনগণের আস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই সরকারের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোরও দায়িত্ব—সংলাপ, মনস্তাত্ত্বিক কৌশল এবং সমঝোতার মাধ্যমে সংকটের সমাধান করা। বর্তমান এই পরিস্থিতিতে বিএনপি, জামায়াত এবং এনসিপি একদিকে সাংবিধানিক বাস্তবতা; অন্যদিকে রাজনৈতিক স্বার্থের মধ্যে বিভক্ত। বিএনপি গণভোটকে নির্বাচনের দিনই আয়োজন করার পক্ষে, জামায়াত নির্বাচনের আগে গণভোটের অধিকার নিশ্চিত করতে চাইছে। এই অবস্থান কার্যত একধরনের রাজনৈতিক সংকট তৈরি করেছে, যা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিরল। দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, সংবিধান সংস্কার এবং রাজনৈতিক সংস্কারের বাস্তবায়ন—এগুলো বর্তমানে রাজনৈতিক উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে।
রাফায়েল আহমেদ শামীম, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কলাম লেখক

সবচেয়ে করুণ অবস্থা হয়েছে বেচারা গণতন্ত্রের। কোথায় দাঁড়ালে যে এই মহার্ঘ বস্তুটি হুমকির ঊর্ধ্বে থাকবে, তা এখন বোঝা মুশকিল। সব মিলিয়ে ‘গণতন্ত্র’ শব্দটিই এক বিমূর্ত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কীসে যে সে থাকে, এবং কীসে যে থাকে না, তা বোঝা এক কথায় অসম্ভব।
১২ অক্টোবর ২০২১
আসন্ন নির্বাচন সম্পর্কে প্রায়ই নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হই—প্রাক্-নির্বাচন আইনগত এবং সাংবিধানিক বিষয়ে এবং নির্বাচন-পরবর্তী বিষয়েও। প্রথম বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে একধরনের স্বস্তি বোধ করি—প্রশ্নকারীকে সরাসরি বলি যে আমি আইনের লোক নই কিংবা সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞও নই।
১৩ ঘণ্টা আগে
উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছে। শুধু রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেই নয়, সাধারণ মানুষের মনেও জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ককটেল, বাসে আগুন, জুলাই সনদ বিষয়ে রাজনৈতিক বিভিন্ন দলের বিতর্ক ইত্যাদি কারণে অস্থিরতা বাড়ছে।
১৩ ঘণ্টা আগে
গত এপ্রিলে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের ‘বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আউটলুক’-এর পূর্বাভাস জানিয়েছিল, এ বছর বাংলাদেশে নতুন করে আরও ৩০ লাখ মানুষ অতিদরিদ্র শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে এবং দারিদ্র্যের হার ২০ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ২১ দশমিক ২ শতাংশে।
২ দিন আগেসম্পাদকীয়

উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছে। শুধু রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেই নয়, সাধারণ মানুষের মনেও জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ককটেল, বাসে আগুন, জুলাই সনদ বিষয়ে রাজনৈতিক বিভিন্ন দলের বিতর্ক ইত্যাদি কারণে অস্থিরতা বাড়ছে।
জুলাই সনদ নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আলোচনার যে সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, তা পার হয়ে গেছে। কোনো আলোচনা হয়নি। বিএনপি বলছে, নির্বাচন পেছানো মানেই দেশের সর্বনাশ। জামায়াতে ইসলামী নির্বাচনের আগে গণভোট, জুলাই আদেশ বাস্তবায়নের আদেশ জারিসহ পাঁচ দাবিতে আন্দোলন করছে। এসব বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে আগামীকাল বৃহস্পতিবার কোনো সিদ্ধান্ত আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
সহিংসতার আশঙ্কায় সারা দেশে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের নিরসন না করে শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা দিয়ে এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। ঠান্ডা মাথায় সব পক্ষ একসঙ্গে বসে কোনো ফলপ্রসূ সিদ্ধান্তে আসতে পারলেই কেবল এই সংকট থেকে মুক্তি সম্ভব।
সব রাজনৈতিক দলই জনতা কী চায়, সে ব্যাপারে নিজেদের ভাবনাকেই তুলে ধরার চেষ্টা করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে বিভক্ত মানুষের ভাবনা বিভক্তই হবে। কিন্তু সাধারণ জনগণ কয়েকটি ব্যাপারে একমত, সেই বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হলেই শুধু দেশবাসীর আকাঙ্ক্ষাগুলো মিলে যাওয়ার একটা দিশা পাওয়া যাবে।
গণতন্ত্র শক্তিশালী করতে হলে যেসব বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া দরকার, সেগুলো নিয়ে কিছুটা আলোচনা হতে পারে। যেসব বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলো নিয়ে সব রাজনৈতিক দলই নিশ্চয় ভাববে এবং একটা সিদ্ধান্তে আসবে।
সব গণতান্ত্রিক দেশেই স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পক্ষে থাকে সাধারণ জনগণ। সে পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে কি না, সেদিকে দেশের জনগণের দৃষ্টি থাকবে। নির্বাচন কমিশন স্বশাসিত, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ পদ্ধতি অনুসরণ করলে এই সংকটের একটা সুরাহা হবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, জনগণের এই আকাঙ্ক্ষাও নতুন নয়। ঘুষ-দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতির সমাধি রচিত হবে, এই অঙ্গীকার দেখতে চায় জনগণ। ক্ষমতাবানেরাও যেন আইনের আওতার বাইরে না থাকে, তা নিশ্চিত করার ওপর নির্ভর করে দেশটা সত্যিই গণতান্ত্রিক পথে চলবে কি না। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং মুক্ত গণমাধ্যম জরুরি। জনগণ চায়, তথ্যপ্রবাহে কোনো বাধা থাকবে না। অংশগ্রহণমূলক রাজনীতি না হলে রাজনীতি একদেশদর্শী হয়ে যায়, স্বৈরাচারী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধরনের প্রবণতা যেন নির্বাচনের পর না আসে, সেটা নিশ্চিত হতে পারে ঐকমত্যের ভিত্তিতে। শুধু নির্বাচনের সময়ই নয়, নিয়মিতভাবে জনগণের মতামত নেওয়ার মতো পরিবেশ বা ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে হবে। জনবান্ধব প্রশাসন হচ্ছে কি না, অর্থনৈতিক ন্যায্যতা পাওয়া যাচ্ছে কি না, সেগুলোও রাখতে হবে বিবেচনায়। আর নাগরিকের স্বাধীনতা, তার নিরাপত্তার নিশ্চয়তাও সাধারণ জনগণ চায়।
এসব চাওয়া-পাওয়ার জন্য বিরোধ ভুলে একটি জনগণের রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্য সব দলের প্রতি আহ্বান জানাই।

উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছে। শুধু রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেই নয়, সাধারণ মানুষের মনেও জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ককটেল, বাসে আগুন, জুলাই সনদ বিষয়ে রাজনৈতিক বিভিন্ন দলের বিতর্ক ইত্যাদি কারণে অস্থিরতা বাড়ছে।
জুলাই সনদ নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আলোচনার যে সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, তা পার হয়ে গেছে। কোনো আলোচনা হয়নি। বিএনপি বলছে, নির্বাচন পেছানো মানেই দেশের সর্বনাশ। জামায়াতে ইসলামী নির্বাচনের আগে গণভোট, জুলাই আদেশ বাস্তবায়নের আদেশ জারিসহ পাঁচ দাবিতে আন্দোলন করছে। এসব বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে আগামীকাল বৃহস্পতিবার কোনো সিদ্ধান্ত আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
সহিংসতার আশঙ্কায় সারা দেশে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের নিরসন না করে শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা দিয়ে এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। ঠান্ডা মাথায় সব পক্ষ একসঙ্গে বসে কোনো ফলপ্রসূ সিদ্ধান্তে আসতে পারলেই কেবল এই সংকট থেকে মুক্তি সম্ভব।
সব রাজনৈতিক দলই জনতা কী চায়, সে ব্যাপারে নিজেদের ভাবনাকেই তুলে ধরার চেষ্টা করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে বিভক্ত মানুষের ভাবনা বিভক্তই হবে। কিন্তু সাধারণ জনগণ কয়েকটি ব্যাপারে একমত, সেই বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হলেই শুধু দেশবাসীর আকাঙ্ক্ষাগুলো মিলে যাওয়ার একটা দিশা পাওয়া যাবে।
গণতন্ত্র শক্তিশালী করতে হলে যেসব বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া দরকার, সেগুলো নিয়ে কিছুটা আলোচনা হতে পারে। যেসব বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলো নিয়ে সব রাজনৈতিক দলই নিশ্চয় ভাববে এবং একটা সিদ্ধান্তে আসবে।
সব গণতান্ত্রিক দেশেই স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পক্ষে থাকে সাধারণ জনগণ। সে পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে কি না, সেদিকে দেশের জনগণের দৃষ্টি থাকবে। নির্বাচন কমিশন স্বশাসিত, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ পদ্ধতি অনুসরণ করলে এই সংকটের একটা সুরাহা হবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, জনগণের এই আকাঙ্ক্ষাও নতুন নয়। ঘুষ-দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতির সমাধি রচিত হবে, এই অঙ্গীকার দেখতে চায় জনগণ। ক্ষমতাবানেরাও যেন আইনের আওতার বাইরে না থাকে, তা নিশ্চিত করার ওপর নির্ভর করে দেশটা সত্যিই গণতান্ত্রিক পথে চলবে কি না। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং মুক্ত গণমাধ্যম জরুরি। জনগণ চায়, তথ্যপ্রবাহে কোনো বাধা থাকবে না। অংশগ্রহণমূলক রাজনীতি না হলে রাজনীতি একদেশদর্শী হয়ে যায়, স্বৈরাচারী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধরনের প্রবণতা যেন নির্বাচনের পর না আসে, সেটা নিশ্চিত হতে পারে ঐকমত্যের ভিত্তিতে। শুধু নির্বাচনের সময়ই নয়, নিয়মিতভাবে জনগণের মতামত নেওয়ার মতো পরিবেশ বা ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে হবে। জনবান্ধব প্রশাসন হচ্ছে কি না, অর্থনৈতিক ন্যায্যতা পাওয়া যাচ্ছে কি না, সেগুলোও রাখতে হবে বিবেচনায়। আর নাগরিকের স্বাধীনতা, তার নিরাপত্তার নিশ্চয়তাও সাধারণ জনগণ চায়।
এসব চাওয়া-পাওয়ার জন্য বিরোধ ভুলে একটি জনগণের রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্য সব দলের প্রতি আহ্বান জানাই।

সবচেয়ে করুণ অবস্থা হয়েছে বেচারা গণতন্ত্রের। কোথায় দাঁড়ালে যে এই মহার্ঘ বস্তুটি হুমকির ঊর্ধ্বে থাকবে, তা এখন বোঝা মুশকিল। সব মিলিয়ে ‘গণতন্ত্র’ শব্দটিই এক বিমূর্ত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কীসে যে সে থাকে, এবং কীসে যে থাকে না, তা বোঝা এক কথায় অসম্ভব।
১২ অক্টোবর ২০২১
আসন্ন নির্বাচন সম্পর্কে প্রায়ই নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হই—প্রাক্-নির্বাচন আইনগত এবং সাংবিধানিক বিষয়ে এবং নির্বাচন-পরবর্তী বিষয়েও। প্রথম বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে একধরনের স্বস্তি বোধ করি—প্রশ্নকারীকে সরাসরি বলি যে আমি আইনের লোক নই কিংবা সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞও নই।
১৩ ঘণ্টা আগে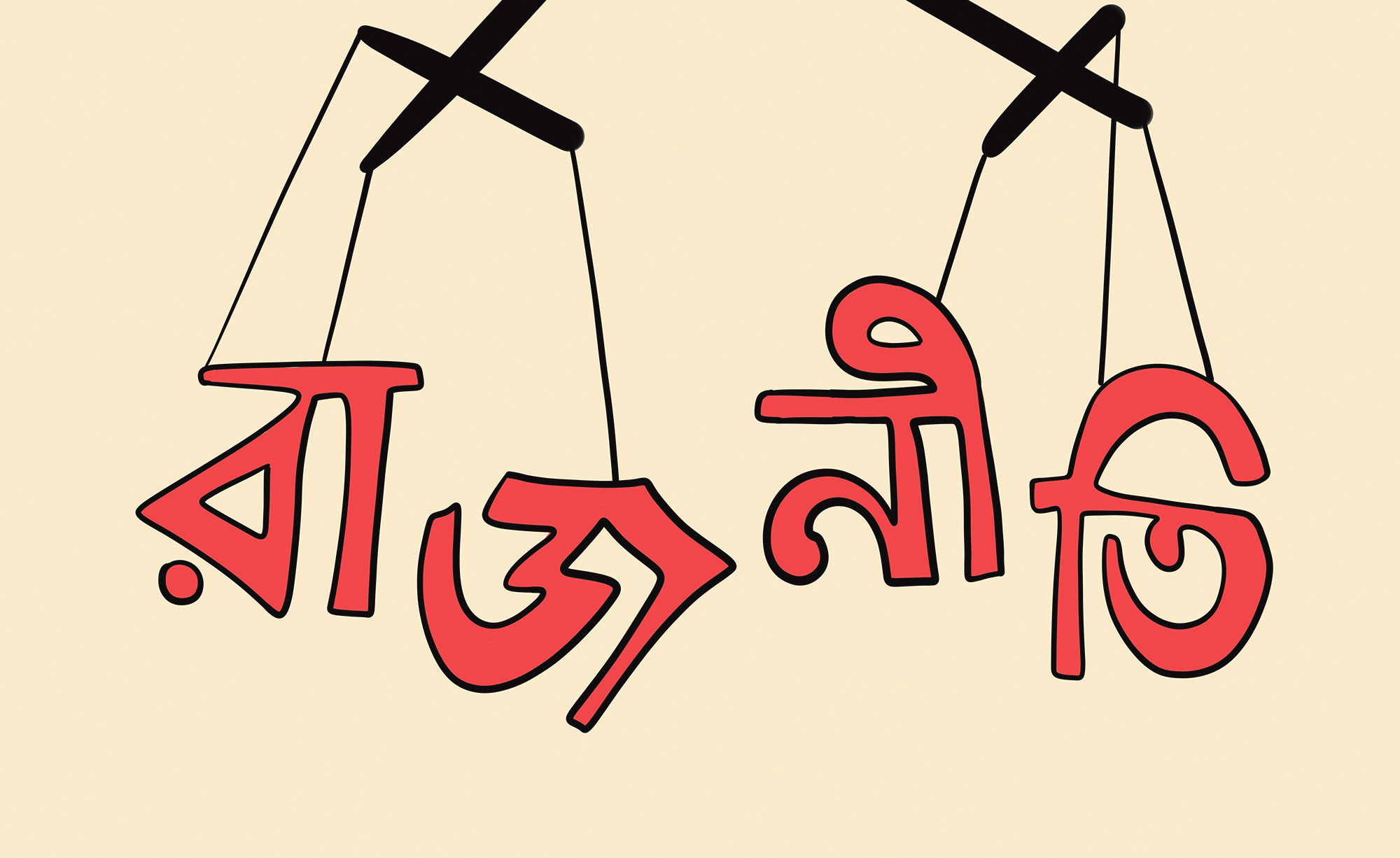
বাংলাদেশের রাজনীতিতে জুলাই সনদ ২০২৫ এবং গণভোট ইস্যু একধরনের বহুমাত্রিক সংকটের সূচনা করেছে, যা সাংবিধানিক বাস্তবতা, রাজনৈতিক মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া, জনগণের অংশগ্রহণ এবং সামাজিক আস্থার সঙ্গে জড়িত। এই সংকট শুধু রাজনৈতিক দলের কৌশলগত দ্বন্দ্ব নয়...
১৩ ঘণ্টা আগে
গত এপ্রিলে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের ‘বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আউটলুক’-এর পূর্বাভাস জানিয়েছিল, এ বছর বাংলাদেশে নতুন করে আরও ৩০ লাখ মানুষ অতিদরিদ্র শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে এবং দারিদ্র্যের হার ২০ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ২১ দশমিক ২ শতাংশে।
২ দিন আগেএকটি ন্যূনতম সভ্য রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তাদের মনের মধ্যে এ আকাঙ্ক্ষা থাকতেই পারে যে, এ রাষ্ট্র তথা এর পরিচালক ও রাজনীতিকেরা জনগণের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে বিরাজমান সংকট নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন এবং তা দূরীকরণের উপায় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করবেন। যেহেতু অন্তর্বর্তী সরকারের সব চিন্তাই সংসদ নির্বাচন নিয়ে, তাই তারা এ বিষয়টির প্রতি তেমন নজর দিতে পারছে না।
আবু তাহের খান

গত এপ্রিলে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের ‘বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আউটলুক’-এর পূর্বাভাস জানিয়েছিল, এ বছর বাংলাদেশে নতুন করে আরও ৩০ লাখ মানুষ অতিদরিদ্র শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে এবং দারিদ্র্যের হার ২০ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ২১ দশমিক ২ শতাংশে। বিশ্বব্যাংকের অধিকাংশ পরামর্শ ও সহায়তা বাংলাদেশের জন্য পরিত্যাজ্য হলেও তাদের এ পূর্বাভাসকে আমলে নেওয়ার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, এটি বাংলাদেশের বিত্তসহায়ক ও জনবিমুখ অর্থনৈতিক নীতিমালাজনিত এমন এক ফলাফলকে তুলে ধরেছে, যে বিষয়ে বাংলাদেশ জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হলে দেশে দারিদ্র্যের হার সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরও বাড়তেই থাকবে এবং এর ফলে দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষ, বিশেষত দরিদ্র ও নিম্নবিত্তের আওতাধীন জনগোষ্ঠী ক্ষুধা, অপুষ্টি ও অনাহারের মতো বড় ধরনের বিপর্যয়ের মুখে পড়তে পারে।
বিশ্বব্যাংকের দেওয়া ওই পূর্বাভাসের পর ইতিমধ্যে ছয় মাস পেরিয়ে গেছে। কিন্তু উল্লিখিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় অদ্যাবধি রাষ্ট্রের নীতিকাঠামোতে এমন কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি বা আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি, যা পরবর্তী বছরগুলোতে গিয়ে উল্লিখিত দারিদ্র্য বৃদ্ধির হারকে রুখে দিতে পারবে। তবে এ সরকার যেহেতু একটি অন্তর্বর্তী সরকার, সেহেতু এ বিষয়ে তাদের নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সীমাবদ্ধতা থাকতেই পারে। কিন্তু কথা হচ্ছে, ফেব্রুয়ারির আসন্ন নির্বাচনে (যদি হয়) জিতে যারা ক্ষমতায় যেতে চায়, তাদের কি এ বিষয়ে কোনো অঙ্গীকার, প্রস্তুতি বা চিন্তাভাবনা আছে? তাদের কথাবার্তা ও আচরণ দেখে তো তেমনটি মনে হচ্ছে না। বিষয়টি তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে অন্তর্বর্তী সরকারের অবস্থানগত দুর্বলতা এবং এ বিষয়ে ক্ষমতায় যেতে ইচ্ছুক রাজনৈতিক দলগুলোর সীমাহীন নির্লিপ্ততা—এ দুয়ে মিলে দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি মোকাবিলা-প্রচেষ্টা এখন একেবারেই শূন্যের কোঠায়। ফলে দেশের দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির পরিবারগুলো এখন চরম খাদ্যাভাব ও অপুষ্টিতে ভুগছে। তাদের সন্তানেরা গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষায় প্রবেশাধিকার না পেয়ে নিম্নব্যয়ের মানহীন মাদ্রাসাশিক্ষার দিকে ঝুঁকছে। চিকিৎসার জন্য শহরের সরকারি হাসপাতালই তাদের মূল ভরসা, যেখানে চাহিদার তুলনায় সেবা সরবরাহের পরিমাণ খুবই অপ্রতুল। আর ভোগ্যপণ্যের অতি উচ্চমূল্যের কারণে তাদের মধ্যকার একটি বড় অংশই দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম উপকরণটুকু সংগ্রহ করতে না পেরে প্রায়ই অর্ধাহার বা আপসমূলক নিম্ন-আহারের মধ্য দিয়ে জীবন কাটাচ্ছে। মোট কথা, বিত্তবান, সুবিধাভোগী ও রাষ্ট্রীয় প্রশ্রয়ে রাতারাতি অবৈধ বিত্তের মালিক হয়ে ওঠা নব্য বিত্তবানেরা ছাড়া দেশের সিংহভাগ মানুষকেই এখন চরম অর্থকষ্টের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে।
কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, দেশের সাধারণ মানুষের এইসব দুর্ভোগ ও মানবেতর জীবনযাপনের কষ্ট রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের বোধ, চিন্তা ও উপলব্ধিকে একেবারেই স্পর্শ করতে পারছে না অথবা বলা যেতে পারে, এসব কষ্ট উপলব্ধি করার মতো বোধই তাঁদের নেই। অন্যদিকে নিকট ভবিষ্যতে যাঁরা রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত প্রণয়নের দায়িত্বে যাবেন বলে আশা করছেন, তাঁরাও ঘুণাক্ষরে ভাবছেন না সাধারণ মানুষের জীবন কীভাবে ক্রমেই বিপন্ন থেকে বিপন্নতর হয়ে পড়ছে। আর উন্নয়ন অর্থনীতি সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন, ক্রমহ্রাসমান দারিদ্র্য যদি মাঝপথে এসে আবার পশ্চাৎমুখী হতে শুরু করে অর্থাৎ বাড়তে থাকে, তাহলে সেটিকে আর শিগগির কমিয়ে আনতে পারাটা অনেকটাই সাধ্যের বাইরে চলে যাবে। এবং দারিদ্র্যবিমোচন-প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সম্ভবত এই মুহূর্তে সে রকম একটি অন্তর্বর্তী সংকটকালই পার করছে। আর বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার সংস্কার ও বৈদেশিক চুক্তি সম্পাদনের পেছনে তাদের অধিকাংশ সময় ও মনোযোগ নিবদ্ধ করার কারণে জনস্বার্থের প্রতি তারা যে উপেক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে, বস্তুত তা থেকেই এ সংকটের সৃষ্টি।
জনস্বার্থের প্রতি অন্তর্বর্তী সরকারের উপেক্ষা ও নির্লিপ্ততার সবচেয়ে বড় শিকার এখন কৃষক ও কৃষি খাত এবং আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শ্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত শ্রমজীবী মানুষ। আর তাদের অধিকাংশই যেহেতু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া মানুষ এবং তারা যেহেতু সংগঠিত নয় বলে প্রতিবাদ করার কোনো সামর্থ্যও তাদের নেই। অন্যদিকে ক্ষমতারোহণের লড়াইয়ে উন্মত্ত রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতামগ্নতা এতটাই প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে যে তাদের পক্ষেও আর কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের দিকে তাকানোর ফুরসত নেই। অতএব দরিদ্র ও নিম্নবিত্তের মানুষের আপাতত এটাই নিয়তি যে, তাদের আরও কিছুকাল ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অনাহার, পুষ্টিহীনতা, অশিক্ষা, চিকিৎসাহীনতা, বাসস্থান-সংকট, মব-অত্যাচার ইত্যাদি বিষয়গুলোকে মোকাবিলা করেই টিকে থাকতে হবে।
তো এই যখন দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবনযাপনের স্তর ও বৈশিষ্ট্য, তখন একটি ন্যূনতম সভ্য রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তাদের মনের মধ্যে এ আকাঙ্ক্ষা থাকতেই পারে যে, এ রাষ্ট্র তথা এর পরিচালক ও রাজনীতিকেরা জনগণের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে বিরাজমান সংকট নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন এবং তা দূরীকরণের উপায় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করবেন। যেহেতু অন্তর্বর্তী সরকারের সব চিন্তাই সংসদ নির্বাচন নিয়ে, তাই তারা এ বিষয়টির প্রতি তেমন নজর দিতে পারছে না। অন্যদিকে, ক্ষমতায় যেতে ইচ্ছুক রাজনীতিকেরা জনগণের জীবনযাপনের সে কষ্ট ও দুর্ভোগ নিয়ে উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন তো দূরের কথা, তাঁদের কাছে জনগণ নিছকই ভোটের সময়কার বক্তৃতা-মাঠের মাথাগুনতির অলংকার ও উপকরণ মাত্র। আর সে কারণেই বিশ্বব্যাংক যখন তথ্য দেয় যে দারিদ্র্য আবার ফিরে আসছে, তখন মাঠের জীবনে অভ্যস্ত মানুষ হিসেবে ভয় হয়—বাংলাদেশ আবার দক্ষিণ সুদান, কঙ্গো বা মোজাম্বিকের দিকে যাত্রা করছে না তো?
দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে মানব উন্নয়ন সূচকে (এইচডিআই) বাংলাদেশ এই সেদিনও শ্রীলঙ্কা ও ভারত ব্যতীত অন্য পাঁচটি দেশের তুলনায় প্রায় সব কটি সূচকেই সুস্পষ্টভাবে এগিয়ে ছিল। এমনকি বেশ কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল শ্রীলঙ্কা ও ভারতের চেয়েও এগিয়ে। কিন্তু দারিদ্র্যহার বৃদ্ধির পূর্ব-প্রবণতা আবার ফিরে আসার পরিপ্রেক্ষিতে আশঙ্কা হয়, এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হয়তো পুনরায় পাকিস্তান বা আফগানিস্তানের পর্যায়ে নেমে যেতে পারে। এই সেদিনও বাংলাদেশের তুলনায় বহু ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা ভিয়েতনাম এখন বাংলাদেশকে প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই আর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে গণ্য করে না। এমনকি বাংলাদেশের নাগরিকদের তারা ভিসাও দিতে চায় না। ২০২২ সালের জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কায় প্রচণ্ড জনবিক্ষোভের মুখে সরকার পতনের মাত্র এক বছরের মধ্যে দেশটি শুধু ঘুরেই দাঁড়ায়নি, তাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার এখন ৫ দশমিক ২ শতাংশ, যা বাংলাদেশের তুলনায় দশমিক ৪ শতাংশ বেশি এবং সার্কভুক্ত দেশ হয়েও বাংলাদেশকে ভিসা দিতে তারা কড়াকড়ি করছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হারে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ এখন শুধু পাকিস্তানের (৩.২ শতাংশ) ও আফগানিস্তানের (২.৭ শতাংশ) চেয়ে এগিয়ে আছে।
এসব বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করার অবকাশ কি মনে হয় অন্তর্বর্তী সরকার বা ‘ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে’ অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণকারী দলসমূহের আছে? নেই। উপরিউক্ত পূর্বাভাস অনুযায়ী, এ বছর দেশে দারিদ্র্যের হার যেখানে ১ দশমিক ২ শতাংশ বাড়ছে, সেখানে পরবর্তী বছরগুলোতেও যদি এ ধারা অব্যাহত থাকে, তাহলে ২০৩০ সাল নাগাদ দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি ও সাধারণ জনগণের বিপর্যস্ত জীবনমানের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা ভাবতেই গা শিউরে ওঠে বৈকি! রাষ্ট্রের পরিচালকদের এ ব্যাপারে নির্বিকার থাকা চলে না। দেশ ও দেশের সাধারণ মানুষের এই মুহূর্তের কষ্টময় জীবনযাপনের প্রতি ন্যূনতম মমতা জানিয়ে বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া উচিত।
লেখক: সাবেক পরিচালক, বিসিক

গত এপ্রিলে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের ‘বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আউটলুক’-এর পূর্বাভাস জানিয়েছিল, এ বছর বাংলাদেশে নতুন করে আরও ৩০ লাখ মানুষ অতিদরিদ্র শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে এবং দারিদ্র্যের হার ২০ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ২১ দশমিক ২ শতাংশে। বিশ্বব্যাংকের অধিকাংশ পরামর্শ ও সহায়তা বাংলাদেশের জন্য পরিত্যাজ্য হলেও তাদের এ পূর্বাভাসকে আমলে নেওয়ার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, এটি বাংলাদেশের বিত্তসহায়ক ও জনবিমুখ অর্থনৈতিক নীতিমালাজনিত এমন এক ফলাফলকে তুলে ধরেছে, যে বিষয়ে বাংলাদেশ জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হলে দেশে দারিদ্র্যের হার সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরও বাড়তেই থাকবে এবং এর ফলে দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষ, বিশেষত দরিদ্র ও নিম্নবিত্তের আওতাধীন জনগোষ্ঠী ক্ষুধা, অপুষ্টি ও অনাহারের মতো বড় ধরনের বিপর্যয়ের মুখে পড়তে পারে।
বিশ্বব্যাংকের দেওয়া ওই পূর্বাভাসের পর ইতিমধ্যে ছয় মাস পেরিয়ে গেছে। কিন্তু উল্লিখিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় অদ্যাবধি রাষ্ট্রের নীতিকাঠামোতে এমন কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি বা আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি, যা পরবর্তী বছরগুলোতে গিয়ে উল্লিখিত দারিদ্র্য বৃদ্ধির হারকে রুখে দিতে পারবে। তবে এ সরকার যেহেতু একটি অন্তর্বর্তী সরকার, সেহেতু এ বিষয়ে তাদের নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সীমাবদ্ধতা থাকতেই পারে। কিন্তু কথা হচ্ছে, ফেব্রুয়ারির আসন্ন নির্বাচনে (যদি হয়) জিতে যারা ক্ষমতায় যেতে চায়, তাদের কি এ বিষয়ে কোনো অঙ্গীকার, প্রস্তুতি বা চিন্তাভাবনা আছে? তাদের কথাবার্তা ও আচরণ দেখে তো তেমনটি মনে হচ্ছে না। বিষয়টি তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে অন্তর্বর্তী সরকারের অবস্থানগত দুর্বলতা এবং এ বিষয়ে ক্ষমতায় যেতে ইচ্ছুক রাজনৈতিক দলগুলোর সীমাহীন নির্লিপ্ততা—এ দুয়ে মিলে দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি মোকাবিলা-প্রচেষ্টা এখন একেবারেই শূন্যের কোঠায়। ফলে দেশের দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির পরিবারগুলো এখন চরম খাদ্যাভাব ও অপুষ্টিতে ভুগছে। তাদের সন্তানেরা গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষায় প্রবেশাধিকার না পেয়ে নিম্নব্যয়ের মানহীন মাদ্রাসাশিক্ষার দিকে ঝুঁকছে। চিকিৎসার জন্য শহরের সরকারি হাসপাতালই তাদের মূল ভরসা, যেখানে চাহিদার তুলনায় সেবা সরবরাহের পরিমাণ খুবই অপ্রতুল। আর ভোগ্যপণ্যের অতি উচ্চমূল্যের কারণে তাদের মধ্যকার একটি বড় অংশই দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম উপকরণটুকু সংগ্রহ করতে না পেরে প্রায়ই অর্ধাহার বা আপসমূলক নিম্ন-আহারের মধ্য দিয়ে জীবন কাটাচ্ছে। মোট কথা, বিত্তবান, সুবিধাভোগী ও রাষ্ট্রীয় প্রশ্রয়ে রাতারাতি অবৈধ বিত্তের মালিক হয়ে ওঠা নব্য বিত্তবানেরা ছাড়া দেশের সিংহভাগ মানুষকেই এখন চরম অর্থকষ্টের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে।
কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, দেশের সাধারণ মানুষের এইসব দুর্ভোগ ও মানবেতর জীবনযাপনের কষ্ট রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের বোধ, চিন্তা ও উপলব্ধিকে একেবারেই স্পর্শ করতে পারছে না অথবা বলা যেতে পারে, এসব কষ্ট উপলব্ধি করার মতো বোধই তাঁদের নেই। অন্যদিকে নিকট ভবিষ্যতে যাঁরা রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত প্রণয়নের দায়িত্বে যাবেন বলে আশা করছেন, তাঁরাও ঘুণাক্ষরে ভাবছেন না সাধারণ মানুষের জীবন কীভাবে ক্রমেই বিপন্ন থেকে বিপন্নতর হয়ে পড়ছে। আর উন্নয়ন অর্থনীতি সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন, ক্রমহ্রাসমান দারিদ্র্য যদি মাঝপথে এসে আবার পশ্চাৎমুখী হতে শুরু করে অর্থাৎ বাড়তে থাকে, তাহলে সেটিকে আর শিগগির কমিয়ে আনতে পারাটা অনেকটাই সাধ্যের বাইরে চলে যাবে। এবং দারিদ্র্যবিমোচন-প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সম্ভবত এই মুহূর্তে সে রকম একটি অন্তর্বর্তী সংকটকালই পার করছে। আর বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার সংস্কার ও বৈদেশিক চুক্তি সম্পাদনের পেছনে তাদের অধিকাংশ সময় ও মনোযোগ নিবদ্ধ করার কারণে জনস্বার্থের প্রতি তারা যে উপেক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে, বস্তুত তা থেকেই এ সংকটের সৃষ্টি।
জনস্বার্থের প্রতি অন্তর্বর্তী সরকারের উপেক্ষা ও নির্লিপ্ততার সবচেয়ে বড় শিকার এখন কৃষক ও কৃষি খাত এবং আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শ্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত শ্রমজীবী মানুষ। আর তাদের অধিকাংশই যেহেতু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া মানুষ এবং তারা যেহেতু সংগঠিত নয় বলে প্রতিবাদ করার কোনো সামর্থ্যও তাদের নেই। অন্যদিকে ক্ষমতারোহণের লড়াইয়ে উন্মত্ত রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতামগ্নতা এতটাই প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে যে তাদের পক্ষেও আর কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের দিকে তাকানোর ফুরসত নেই। অতএব দরিদ্র ও নিম্নবিত্তের মানুষের আপাতত এটাই নিয়তি যে, তাদের আরও কিছুকাল ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অনাহার, পুষ্টিহীনতা, অশিক্ষা, চিকিৎসাহীনতা, বাসস্থান-সংকট, মব-অত্যাচার ইত্যাদি বিষয়গুলোকে মোকাবিলা করেই টিকে থাকতে হবে।
তো এই যখন দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবনযাপনের স্তর ও বৈশিষ্ট্য, তখন একটি ন্যূনতম সভ্য রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তাদের মনের মধ্যে এ আকাঙ্ক্ষা থাকতেই পারে যে, এ রাষ্ট্র তথা এর পরিচালক ও রাজনীতিকেরা জনগণের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে বিরাজমান সংকট নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন এবং তা দূরীকরণের উপায় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করবেন। যেহেতু অন্তর্বর্তী সরকারের সব চিন্তাই সংসদ নির্বাচন নিয়ে, তাই তারা এ বিষয়টির প্রতি তেমন নজর দিতে পারছে না। অন্যদিকে, ক্ষমতায় যেতে ইচ্ছুক রাজনীতিকেরা জনগণের জীবনযাপনের সে কষ্ট ও দুর্ভোগ নিয়ে উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন তো দূরের কথা, তাঁদের কাছে জনগণ নিছকই ভোটের সময়কার বক্তৃতা-মাঠের মাথাগুনতির অলংকার ও উপকরণ মাত্র। আর সে কারণেই বিশ্বব্যাংক যখন তথ্য দেয় যে দারিদ্র্য আবার ফিরে আসছে, তখন মাঠের জীবনে অভ্যস্ত মানুষ হিসেবে ভয় হয়—বাংলাদেশ আবার দক্ষিণ সুদান, কঙ্গো বা মোজাম্বিকের দিকে যাত্রা করছে না তো?
দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে মানব উন্নয়ন সূচকে (এইচডিআই) বাংলাদেশ এই সেদিনও শ্রীলঙ্কা ও ভারত ব্যতীত অন্য পাঁচটি দেশের তুলনায় প্রায় সব কটি সূচকেই সুস্পষ্টভাবে এগিয়ে ছিল। এমনকি বেশ কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল শ্রীলঙ্কা ও ভারতের চেয়েও এগিয়ে। কিন্তু দারিদ্র্যহার বৃদ্ধির পূর্ব-প্রবণতা আবার ফিরে আসার পরিপ্রেক্ষিতে আশঙ্কা হয়, এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হয়তো পুনরায় পাকিস্তান বা আফগানিস্তানের পর্যায়ে নেমে যেতে পারে। এই সেদিনও বাংলাদেশের তুলনায় বহু ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা ভিয়েতনাম এখন বাংলাদেশকে প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই আর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে গণ্য করে না। এমনকি বাংলাদেশের নাগরিকদের তারা ভিসাও দিতে চায় না। ২০২২ সালের জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কায় প্রচণ্ড জনবিক্ষোভের মুখে সরকার পতনের মাত্র এক বছরের মধ্যে দেশটি শুধু ঘুরেই দাঁড়ায়নি, তাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার এখন ৫ দশমিক ২ শতাংশ, যা বাংলাদেশের তুলনায় দশমিক ৪ শতাংশ বেশি এবং সার্কভুক্ত দেশ হয়েও বাংলাদেশকে ভিসা দিতে তারা কড়াকড়ি করছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হারে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ এখন শুধু পাকিস্তানের (৩.২ শতাংশ) ও আফগানিস্তানের (২.৭ শতাংশ) চেয়ে এগিয়ে আছে।
এসব বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করার অবকাশ কি মনে হয় অন্তর্বর্তী সরকার বা ‘ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে’ অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণকারী দলসমূহের আছে? নেই। উপরিউক্ত পূর্বাভাস অনুযায়ী, এ বছর দেশে দারিদ্র্যের হার যেখানে ১ দশমিক ২ শতাংশ বাড়ছে, সেখানে পরবর্তী বছরগুলোতেও যদি এ ধারা অব্যাহত থাকে, তাহলে ২০৩০ সাল নাগাদ দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি ও সাধারণ জনগণের বিপর্যস্ত জীবনমানের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা ভাবতেই গা শিউরে ওঠে বৈকি! রাষ্ট্রের পরিচালকদের এ ব্যাপারে নির্বিকার থাকা চলে না। দেশ ও দেশের সাধারণ মানুষের এই মুহূর্তের কষ্টময় জীবনযাপনের প্রতি ন্যূনতম মমতা জানিয়ে বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া উচিত।
লেখক: সাবেক পরিচালক, বিসিক

সবচেয়ে করুণ অবস্থা হয়েছে বেচারা গণতন্ত্রের। কোথায় দাঁড়ালে যে এই মহার্ঘ বস্তুটি হুমকির ঊর্ধ্বে থাকবে, তা এখন বোঝা মুশকিল। সব মিলিয়ে ‘গণতন্ত্র’ শব্দটিই এক বিমূর্ত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কীসে যে সে থাকে, এবং কীসে যে থাকে না, তা বোঝা এক কথায় অসম্ভব।
১২ অক্টোবর ২০২১
আসন্ন নির্বাচন সম্পর্কে প্রায়ই নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হই—প্রাক্-নির্বাচন আইনগত এবং সাংবিধানিক বিষয়ে এবং নির্বাচন-পরবর্তী বিষয়েও। প্রথম বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে একধরনের স্বস্তি বোধ করি—প্রশ্নকারীকে সরাসরি বলি যে আমি আইনের লোক নই কিংবা সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞও নই।
১৩ ঘণ্টা আগে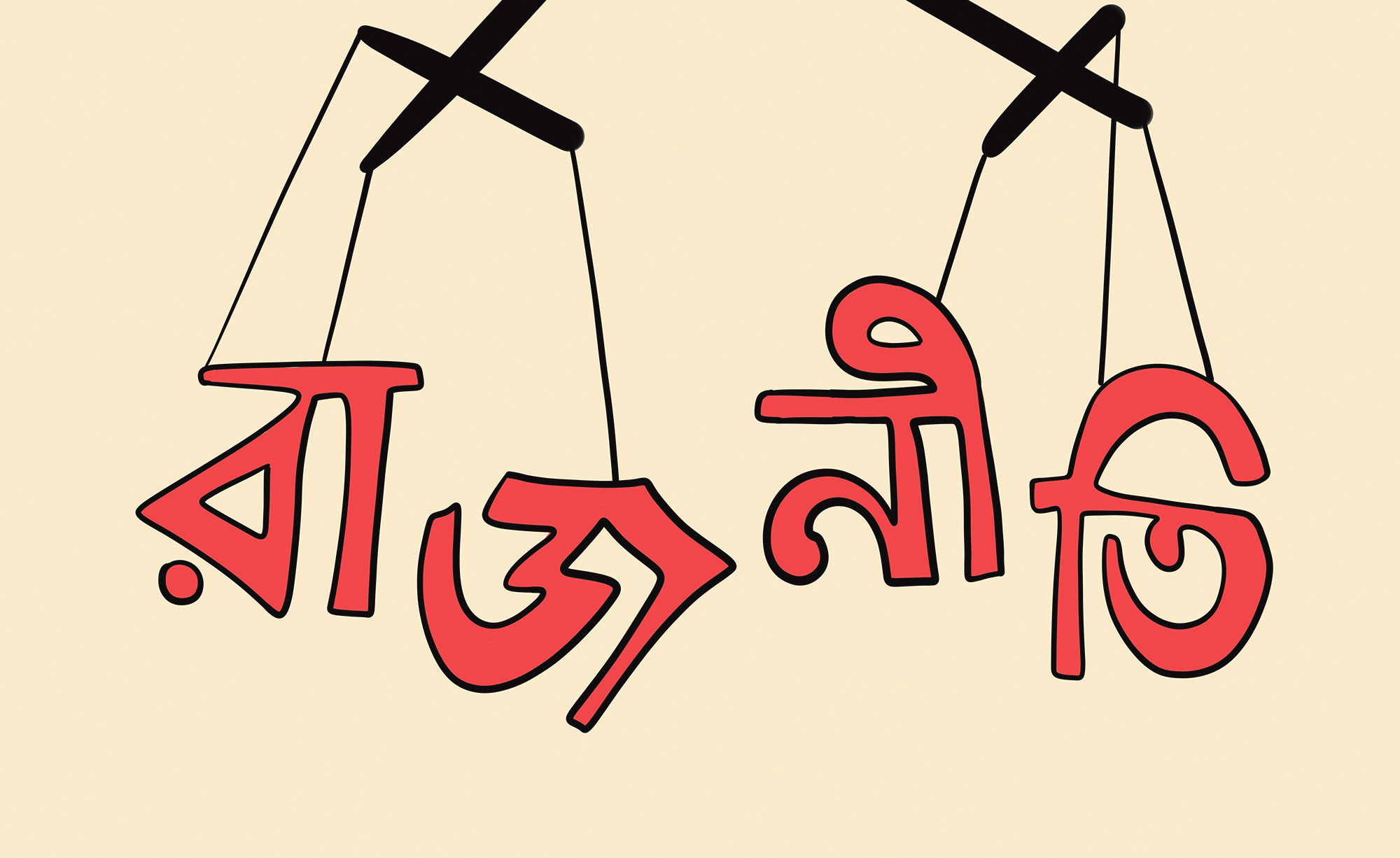
বাংলাদেশের রাজনীতিতে জুলাই সনদ ২০২৫ এবং গণভোট ইস্যু একধরনের বহুমাত্রিক সংকটের সূচনা করেছে, যা সাংবিধানিক বাস্তবতা, রাজনৈতিক মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া, জনগণের অংশগ্রহণ এবং সামাজিক আস্থার সঙ্গে জড়িত। এই সংকট শুধু রাজনৈতিক দলের কৌশলগত দ্বন্দ্ব নয়...
১৩ ঘণ্টা আগে
উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছে। শুধু রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেই নয়, সাধারণ মানুষের মনেও জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ককটেল, বাসে আগুন, জুলাই সনদ বিষয়ে রাজনৈতিক বিভিন্ন দলের বিতর্ক ইত্যাদি কারণে অস্থিরতা বাড়ছে।
১৩ ঘণ্টা আগে