কামরুল হাসান
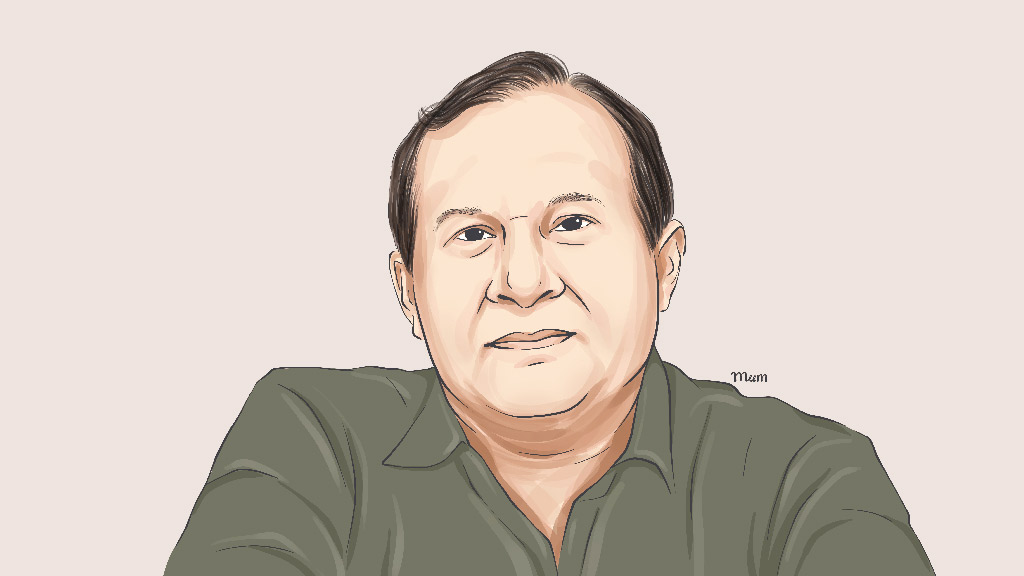
ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিডিআর-বিএসএফের মধ্যে আগে প্রায়ই গোলাগুলি হতো। ওপারে একটি গুলি ফুটলেই পাল্টা গুলি চলত এপারে। সীমান্ত এলাকার বাসিন্দা হওয়ার সুবাদে ছোট থেকেই গোলাগুলির সঙ্গে আরেকটি শব্দ আমাদের কান সওয়া হয়েছিল, তা হলো ‘লাইন অব কন্ট্রোল’। বাংলায় যার মানে ‘নিয়ন্ত্রণরেখা’। আধা সেনাদের এই সামরিক শব্দের একেবারে সার্থক প্রয়োগ ছিল আমাদের খাবারের টেবিলে, অন্তত ডিম ভাগাভাগিতে।
সচ্ছল গেরস্ত বলতে যা বোঝায়, আমরা ছিলাম সেই রকমের। কোনো জিনিসের অভাব ছিল না কখনো, কিন্তু গ্রামের মানুষ বলে চাহিদার সঙ্গে জোগানের একটি ঘাটতি থেকেই যেত। এর একটি হলো আমিষের ঘাটতি। একসময় গ্রামে চটজলদি আমিষ বলতে ছিল পুকুরের মাছ, ঘরের মোরগ-মুরগি আর মুরগির ডিম। সবার তো আর পুকুর নেই, ঘরে মোরগ-মুরগিও নেই। আমিষের জন্য তারা তাকিয়ে থাকত হাটবারের দিকে। হঠাৎ বাড়িতে মেহমান এলে ভরসা ছিল হাঁস-মুরগির ডিম। লেয়ার-ব্রয়লারের মতো ‘বাজারি’ মুরগি তখনো দেশে আসেনি আর দেশি মুরগিরা বরাবরই ছিল রক্ষণশীল। পুরোনো জমিদারবাড়ির মতো তারা রীতিমতো ‘হেরিটেজ’। ডিমও দিত গুনে গুনে। এক হালি ডিম পেতে তিন বাড়ি ঘুরতে হতো।
আমাদের বাড়িতে ঘন ঘন মেহমান আসত। আর মেহমান এলেই ডিমের খোঁজে মিনি ম্যারাথন শুরু হয়ে যেত। পাড়া চষে পাওয়া যেত বড়জোর চার বা পাঁচটি ডিম। মেহমানের খাওয়া শেষ হলে অবশিষ্ট ডিম ভাইবোনদের মধ্যে ভাগ করে খেতে হতো। আর সেখানেই ছিল ‘লাইন অব কন্ট্রোল’। আমার আগের বোনটিকে ‘যুধিষ্ঠির’ ভেবে ডিম ভাগাভাগির দায়িত্ব দেওয়া হতো। মা-খালারা যেভাবে সুতা ধরে চাঁদকে দুই ফালি করার গল্প বলতেন, তিনিও সেভাবে ‘লাইন অব কন্ট্রোল’ ঠিক রেখে ডিম ভাগ করতেন। লাইন একটু এদিক-ওদিক হলে আর রক্ষে নেই।
ডিম হোক বা ডিমের কুসুম—তা ভাগাভাগি নিয়ে পরিবারে ছোটদের মধ্যে মন-কষাকষি হয়নি এমন পরিবার মনে হয় এই বাংলাদেশে কমই আছে। তার পরও এসব ছিল পূর্ণিমার চাঁদ ভাগাভাগির মতো। যার দুই ভাগেই ছিল অবিরল জ্যোৎস্না। সেই জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলোয় ‘বিষাদ-সিন্ধু’র দুলদুল ঘোড়া হয়ে ঘুরে বেড়াত আমাদের অর্ধেক জীবন।
 এই যে অর্ধেক জীবন, তার বাকি অর্ধেকের ইতিহাস বদলে যাওয়ার, এগিয়ে যাওয়ারও। আজকের দিনে ডিম ভাগাভাগির তুচ্ছ গল্প কিশোরদের কাছে বড়ই বেমানান, কিছুটা সেকেলেও। ডিম এখন বাজারের সহজলভ্য ও সস্তা পণ্য। ফুটপাত থেকে ডিপার্টমেন্ট স্টোর—সর্বত্র ডিমের ছড়াছড়ি। এত পণ্যের ভিড়ে ডিমও পেয়েছে শিল্পপণ্যের মর্যাদা। নানা রঙের মোড়কে, ভিন্ন ভিন্ন দামে ডিম বিক্রি হচ্ছে বাজারে। ডিম নিয়ে এখন আর কোনো পরিবারের হাপিত্যেশ নেই। আজকের যুগের মায়েরা বাচ্চাদের ডিম গেলাতে ইউটিউব বা কার্টুনের মতো ডিজিটাল উৎকোচও দিচ্ছেন হরহামেশা। ডিমের সঙ্গে গেরস্তের ঘরের মুরগিও পেয়েছে বাজারের সুদৃশ্য খাঁচার আসন। বাস-ট্রাকের ছাদে ঝুলে জীবন পার করে দেওয়া সেই মোরগ-মুরগি এখন হাওয়ায় দোল খায় নিজস্ব পরিবহনে। মোরগ-মুরগি পরিবহনের জন্য যে আলাদা গাড়ি হবে—কেউ কি কোনো দিন ভেবেছে?
এই যে অর্ধেক জীবন, তার বাকি অর্ধেকের ইতিহাস বদলে যাওয়ার, এগিয়ে যাওয়ারও। আজকের দিনে ডিম ভাগাভাগির তুচ্ছ গল্প কিশোরদের কাছে বড়ই বেমানান, কিছুটা সেকেলেও। ডিম এখন বাজারের সহজলভ্য ও সস্তা পণ্য। ফুটপাত থেকে ডিপার্টমেন্ট স্টোর—সর্বত্র ডিমের ছড়াছড়ি। এত পণ্যের ভিড়ে ডিমও পেয়েছে শিল্পপণ্যের মর্যাদা। নানা রঙের মোড়কে, ভিন্ন ভিন্ন দামে ডিম বিক্রি হচ্ছে বাজারে। ডিম নিয়ে এখন আর কোনো পরিবারের হাপিত্যেশ নেই। আজকের যুগের মায়েরা বাচ্চাদের ডিম গেলাতে ইউটিউব বা কার্টুনের মতো ডিজিটাল উৎকোচও দিচ্ছেন হরহামেশা। ডিমের সঙ্গে গেরস্তের ঘরের মুরগিও পেয়েছে বাজারের সুদৃশ্য খাঁচার আসন। বাস-ট্রাকের ছাদে ঝুলে জীবন পার করে দেওয়া সেই মোরগ-মুরগি এখন হাওয়ায় দোল খায় নিজস্ব পরিবহনে। মোরগ-মুরগি পরিবহনের জন্য যে আলাদা গাড়ি হবে—কেউ কি কোনো দিন ভেবেছে?
এই অগ্রযাত্রায় অনেকের মতো নীলফামারীর ডিমলার তরুণ উদ্যোক্তা মেহেদীর ভূমিকাও কম নয়। গত রোববার তাঁকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন করেছে আজকের পত্রিকা। তাতে দেখলাম, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার পাট চোকানোর পর অন্য সব বঙ্গসন্তানের মতো একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিয়েছিলেন মেহেদী হাসান রুবেল। কিন্তু সেই কাজে তাঁর মন বসেনি। এরপর সিদ্ধান্ত নেন মুরগির খামার করবেন। মেহেদীর বাড়ি নীলফামারীর ডিমলা উপজেলার সদর ইউনিয়নের রামডাঙ্গা গ্রামে। সেখানেই ‘বায়োটেক ফার্মল্যান্ড’ নামে একটি মুরগির খামার গড়ে তোলেন। সেই খামার থেকে দিনে ২ হাজার মুরগির ডিম মেলে। এই আয় তাঁর জীবন বদলে দিয়েছে।
এই গল্প শুধু মেহেদীর একার নয়, তাঁর মতো আরও অনেক মেহেদী আছেন দেশজুড়ে। তাঁরাই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন আজকের বাংলাদেশকে। তার ফলও হাতে হাতে মিলছে। সংবাদপত্রে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (ডিএলএস) যে হিসাব দিয়েছে, তাতে দেখলাম—দেশে ডিম ও মাংসের উৎপাদনে বড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে। ডিএলএস ২০২০-২১ অর্থবছরের ‘লাইভ স্টক ইকোনমি’ বলে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, সেখানে বলা হয়েছে, দেশে ফি বছর ২০৫৭ দশমিক ৬৪ কোটি পিস ডিম উৎপাদন হয়। প্রতি সপ্তাহে মুরগির বাচ্চা উৎপাদন হয় দেড় থেকে তিন কোটি পর্যন্ত। দিনে ১ হাজার ৫৩০ টন মুরগির মাংস পাওয়া যায়। এই হিসাব থেকে সহজেই বোঝা যায় কোথায় চলেছি আমরা।
মনে আছে, পোলট্রি খামার মালিকদের নেতারা একবার জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে বলেছিলেন, তাঁরা সাদা ডিমের উৎপাদন যে পর্যায়ে নিয়ে গেছেন, সেটা একটি ‘বিপ্লব’।
আমি জানি না, তাঁদের এই কর্মকাণ্ডকে কেউ কোনো দিন বিপ্লব বলবেন কি না। তবে ডিম নিয়ে দেশে যা হয়েছে, তা সত্যিই একটি বিপ্লব। আর যদি কখনো সেই বিপ্লবের ইতিহাস লেখা হয়, তাহলে সেই ইতিহাসে মেহেদীরাও থাকবেন। তাঁদের নামও লেখা হবে সোনার আখরে।
লেখক: ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, আজকের পত্রিকা
আরও পড়ুন:
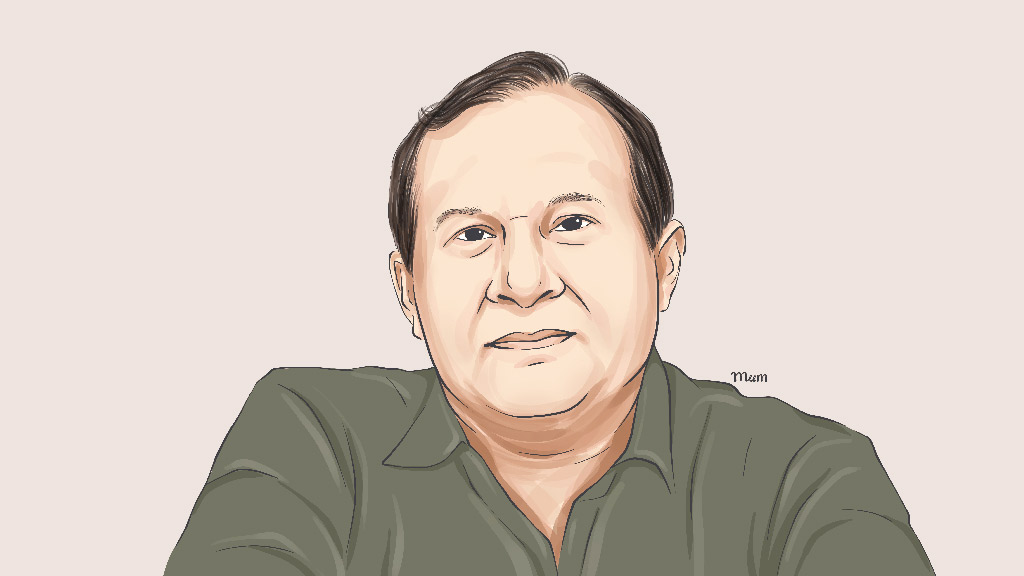
ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিডিআর-বিএসএফের মধ্যে আগে প্রায়ই গোলাগুলি হতো। ওপারে একটি গুলি ফুটলেই পাল্টা গুলি চলত এপারে। সীমান্ত এলাকার বাসিন্দা হওয়ার সুবাদে ছোট থেকেই গোলাগুলির সঙ্গে আরেকটি শব্দ আমাদের কান সওয়া হয়েছিল, তা হলো ‘লাইন অব কন্ট্রোল’। বাংলায় যার মানে ‘নিয়ন্ত্রণরেখা’। আধা সেনাদের এই সামরিক শব্দের একেবারে সার্থক প্রয়োগ ছিল আমাদের খাবারের টেবিলে, অন্তত ডিম ভাগাভাগিতে।
সচ্ছল গেরস্ত বলতে যা বোঝায়, আমরা ছিলাম সেই রকমের। কোনো জিনিসের অভাব ছিল না কখনো, কিন্তু গ্রামের মানুষ বলে চাহিদার সঙ্গে জোগানের একটি ঘাটতি থেকেই যেত। এর একটি হলো আমিষের ঘাটতি। একসময় গ্রামে চটজলদি আমিষ বলতে ছিল পুকুরের মাছ, ঘরের মোরগ-মুরগি আর মুরগির ডিম। সবার তো আর পুকুর নেই, ঘরে মোরগ-মুরগিও নেই। আমিষের জন্য তারা তাকিয়ে থাকত হাটবারের দিকে। হঠাৎ বাড়িতে মেহমান এলে ভরসা ছিল হাঁস-মুরগির ডিম। লেয়ার-ব্রয়লারের মতো ‘বাজারি’ মুরগি তখনো দেশে আসেনি আর দেশি মুরগিরা বরাবরই ছিল রক্ষণশীল। পুরোনো জমিদারবাড়ির মতো তারা রীতিমতো ‘হেরিটেজ’। ডিমও দিত গুনে গুনে। এক হালি ডিম পেতে তিন বাড়ি ঘুরতে হতো।
আমাদের বাড়িতে ঘন ঘন মেহমান আসত। আর মেহমান এলেই ডিমের খোঁজে মিনি ম্যারাথন শুরু হয়ে যেত। পাড়া চষে পাওয়া যেত বড়জোর চার বা পাঁচটি ডিম। মেহমানের খাওয়া শেষ হলে অবশিষ্ট ডিম ভাইবোনদের মধ্যে ভাগ করে খেতে হতো। আর সেখানেই ছিল ‘লাইন অব কন্ট্রোল’। আমার আগের বোনটিকে ‘যুধিষ্ঠির’ ভেবে ডিম ভাগাভাগির দায়িত্ব দেওয়া হতো। মা-খালারা যেভাবে সুতা ধরে চাঁদকে দুই ফালি করার গল্প বলতেন, তিনিও সেভাবে ‘লাইন অব কন্ট্রোল’ ঠিক রেখে ডিম ভাগ করতেন। লাইন একটু এদিক-ওদিক হলে আর রক্ষে নেই।
ডিম হোক বা ডিমের কুসুম—তা ভাগাভাগি নিয়ে পরিবারে ছোটদের মধ্যে মন-কষাকষি হয়নি এমন পরিবার মনে হয় এই বাংলাদেশে কমই আছে। তার পরও এসব ছিল পূর্ণিমার চাঁদ ভাগাভাগির মতো। যার দুই ভাগেই ছিল অবিরল জ্যোৎস্না। সেই জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলোয় ‘বিষাদ-সিন্ধু’র দুলদুল ঘোড়া হয়ে ঘুরে বেড়াত আমাদের অর্ধেক জীবন।
 এই যে অর্ধেক জীবন, তার বাকি অর্ধেকের ইতিহাস বদলে যাওয়ার, এগিয়ে যাওয়ারও। আজকের দিনে ডিম ভাগাভাগির তুচ্ছ গল্প কিশোরদের কাছে বড়ই বেমানান, কিছুটা সেকেলেও। ডিম এখন বাজারের সহজলভ্য ও সস্তা পণ্য। ফুটপাত থেকে ডিপার্টমেন্ট স্টোর—সর্বত্র ডিমের ছড়াছড়ি। এত পণ্যের ভিড়ে ডিমও পেয়েছে শিল্পপণ্যের মর্যাদা। নানা রঙের মোড়কে, ভিন্ন ভিন্ন দামে ডিম বিক্রি হচ্ছে বাজারে। ডিম নিয়ে এখন আর কোনো পরিবারের হাপিত্যেশ নেই। আজকের যুগের মায়েরা বাচ্চাদের ডিম গেলাতে ইউটিউব বা কার্টুনের মতো ডিজিটাল উৎকোচও দিচ্ছেন হরহামেশা। ডিমের সঙ্গে গেরস্তের ঘরের মুরগিও পেয়েছে বাজারের সুদৃশ্য খাঁচার আসন। বাস-ট্রাকের ছাদে ঝুলে জীবন পার করে দেওয়া সেই মোরগ-মুরগি এখন হাওয়ায় দোল খায় নিজস্ব পরিবহনে। মোরগ-মুরগি পরিবহনের জন্য যে আলাদা গাড়ি হবে—কেউ কি কোনো দিন ভেবেছে?
এই যে অর্ধেক জীবন, তার বাকি অর্ধেকের ইতিহাস বদলে যাওয়ার, এগিয়ে যাওয়ারও। আজকের দিনে ডিম ভাগাভাগির তুচ্ছ গল্প কিশোরদের কাছে বড়ই বেমানান, কিছুটা সেকেলেও। ডিম এখন বাজারের সহজলভ্য ও সস্তা পণ্য। ফুটপাত থেকে ডিপার্টমেন্ট স্টোর—সর্বত্র ডিমের ছড়াছড়ি। এত পণ্যের ভিড়ে ডিমও পেয়েছে শিল্পপণ্যের মর্যাদা। নানা রঙের মোড়কে, ভিন্ন ভিন্ন দামে ডিম বিক্রি হচ্ছে বাজারে। ডিম নিয়ে এখন আর কোনো পরিবারের হাপিত্যেশ নেই। আজকের যুগের মায়েরা বাচ্চাদের ডিম গেলাতে ইউটিউব বা কার্টুনের মতো ডিজিটাল উৎকোচও দিচ্ছেন হরহামেশা। ডিমের সঙ্গে গেরস্তের ঘরের মুরগিও পেয়েছে বাজারের সুদৃশ্য খাঁচার আসন। বাস-ট্রাকের ছাদে ঝুলে জীবন পার করে দেওয়া সেই মোরগ-মুরগি এখন হাওয়ায় দোল খায় নিজস্ব পরিবহনে। মোরগ-মুরগি পরিবহনের জন্য যে আলাদা গাড়ি হবে—কেউ কি কোনো দিন ভেবেছে?
এই অগ্রযাত্রায় অনেকের মতো নীলফামারীর ডিমলার তরুণ উদ্যোক্তা মেহেদীর ভূমিকাও কম নয়। গত রোববার তাঁকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন করেছে আজকের পত্রিকা। তাতে দেখলাম, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার পাট চোকানোর পর অন্য সব বঙ্গসন্তানের মতো একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিয়েছিলেন মেহেদী হাসান রুবেল। কিন্তু সেই কাজে তাঁর মন বসেনি। এরপর সিদ্ধান্ত নেন মুরগির খামার করবেন। মেহেদীর বাড়ি নীলফামারীর ডিমলা উপজেলার সদর ইউনিয়নের রামডাঙ্গা গ্রামে। সেখানেই ‘বায়োটেক ফার্মল্যান্ড’ নামে একটি মুরগির খামার গড়ে তোলেন। সেই খামার থেকে দিনে ২ হাজার মুরগির ডিম মেলে। এই আয় তাঁর জীবন বদলে দিয়েছে।
এই গল্প শুধু মেহেদীর একার নয়, তাঁর মতো আরও অনেক মেহেদী আছেন দেশজুড়ে। তাঁরাই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন আজকের বাংলাদেশকে। তার ফলও হাতে হাতে মিলছে। সংবাদপত্রে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (ডিএলএস) যে হিসাব দিয়েছে, তাতে দেখলাম—দেশে ডিম ও মাংসের উৎপাদনে বড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে। ডিএলএস ২০২০-২১ অর্থবছরের ‘লাইভ স্টক ইকোনমি’ বলে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, সেখানে বলা হয়েছে, দেশে ফি বছর ২০৫৭ দশমিক ৬৪ কোটি পিস ডিম উৎপাদন হয়। প্রতি সপ্তাহে মুরগির বাচ্চা উৎপাদন হয় দেড় থেকে তিন কোটি পর্যন্ত। দিনে ১ হাজার ৫৩০ টন মুরগির মাংস পাওয়া যায়। এই হিসাব থেকে সহজেই বোঝা যায় কোথায় চলেছি আমরা।
মনে আছে, পোলট্রি খামার মালিকদের নেতারা একবার জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে বলেছিলেন, তাঁরা সাদা ডিমের উৎপাদন যে পর্যায়ে নিয়ে গেছেন, সেটা একটি ‘বিপ্লব’।
আমি জানি না, তাঁদের এই কর্মকাণ্ডকে কেউ কোনো দিন বিপ্লব বলবেন কি না। তবে ডিম নিয়ে দেশে যা হয়েছে, তা সত্যিই একটি বিপ্লব। আর যদি কখনো সেই বিপ্লবের ইতিহাস লেখা হয়, তাহলে সেই ইতিহাসে মেহেদীরাও থাকবেন। তাঁদের নামও লেখা হবে সোনার আখরে।
লেখক: ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, আজকের পত্রিকা
আরও পড়ুন:

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন আয়োজিত অনুষ্ঠানে জুলাই জাতীয় সনদ সই করা হয়েছে। ১৭ অক্টোবর শুক্রবার বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ২৫টি রাজনৈতিক দলের নেতারা অংশ নেন।
১২ ঘণ্টা আগে
এ বছর পৃথিবীতে বসবাসযোগ্য শহরের তালিকায় ষষ্ঠ স্থান পেয়েছে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহর। আর মেলবোর্ন আছে চতুর্থ স্থানে। ২৯ বছর আগে এক ভোরবেলায় এ দেশের মাটিতে পা রেখেছিলাম। ট্যাক্সিতে চড়ে যাওয়ার সময় ছবির মতো বাড়িঘর, সামনে বাগান, সারি সারি বৃক্ষ ও সাজানো রাস্তাঘাট দেখে মনে হচ্ছিল আমি কোনো সিনেমার শুটিং...
১২ ঘণ্টা আগে
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজের আমদানি পণ্য কমপ্লেক্সে ১৮ অক্টোবর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এক সপ্তাহের ব্যবধানে দেশে তিনটি বড় দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটল।
১২ ঘণ্টা আগে
জুলাই সনদ ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রশ্নে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতা, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের ভূমিকা, জোট রাজনীতি, নারীনীতি, নির্বাচনী প্রতীক ইস্যু থেকে শুরু করে ফান্ডিং ও ‘মেধা বনাম কোটার’ বিতর্ক—এসব বিষয়ে দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা..
১ দিন আগে