
অনেকে বলছেন, এবারের লোকসভা নির্বাচনে ভারতের হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল বিজেপির প্রতি মানুষের প্রত্যাশা বেড়েছে। কিন্তু কেন? সোজা কথায় বলতে গেলে, এই দলটি প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় অনেক বেশি সুসংগঠিত। দলটির নেতা নরেন্দ্র মোদি ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসে যেকোনো রাজনৈতিক নেতার তুলনায় অনেক বেশি ‘ক্যারিশমাটিক’!
তবে কেবল এই দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে নয়, বিজেপির প্রতি জনপ্রত্যাশা, জনসমর্থন ইত্যাদির পেছনে আরও জটিল কারণ রয়েছে। ভারতের চলতি লোকসভা নির্বাচনে ভোট দিচ্ছেন ৯৬ কোটি ৮০ লাখ। ভোটার বিবেচনায় ভারতকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ বলা হয়। আর সেই দেশের রাজনৈতিক দল, মোদির বিজেপি বিশ্বেরও সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল। ধারণা করা হচ্ছে, বিজেপি টানা তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসতে যাচ্ছে।
ভারতের নির্বাচনী রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বিজেপির আধিপত্যের বেশ কয়েকটি কারণ আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো—সুসংহত সাংগঠনিক কাঠামো, নেতৃত্বে জনপ্রিয়দের স্থান দেওয়া, ভোটব্যাংক বাড়ানোর বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে কাজ করা। এর বাইরে, দক্ষতার সঙ্গে গরিব জনগোষ্ঠীকে সরকারি প্রকল্পের উপকারভোগী হিসেবে হাজির করা। গত কয়েক বছরে হিন্দুত্ববাদী এবং গরিবদের জন্য সরকারি সহায়তা প্রকল্পগুলোতে সরাসরি মোদির ব্র্যান্ডিং করা হয়েছে।
সামাজিকভাবে বিজেপি রক্ষণশীল হিন্দু ঘরানার এবং অর্থনৈতিক মতাদর্শে মধ্যপন্থী। আনুষ্ঠিকভাবে দলটি ১৯৮০ সালে যাত্রা শুরু করলেও এর শিকড় নিহিত ভারতীয় জনসংঘের মধ্যে। ভারতীয় জনসংঘ ১৯৫০—এর দশকের একটি রাজনৈতিক দল। যার মূল মতাদর্শই ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদ। সে সময় ভারতজুড়ে চলমান সমাজবাদী রাজনৈতিক মতাদর্শের বিপরীতে গড়ে উঠেছিল দলটি।
ভারতীয় জনসংঘ থেকে হিসাব করলে, দলটি প্রতিষ্ঠার ৭৭ বছরে বিজেপি মাত্র ১৯ বছর ক্ষমতায় ছিল (এখনো আছে)। প্রথমবার দলটি ক্ষমতায় আসে ১৯৭৭ সালে। সে সময় ক্ষমতায় ছিল ৩ বছর। এরপর মাত্র ১৩ দিন ক্ষমতায় ছিল ১৯৯৬ সালে, ১৯৯৮ সালে ক্ষমতায় ছিল ১ বছর। ১৯৯৯ সাল থেকে ক্ষমতায় ছিল পাঁচ বছর এবং এর পর ২০১৪ সাল থেকে টানা ১০ বছর ধরে ক্ষমতায় দলটি।
বিজেপি প্রতিষ্ঠার পর থেকে ক্রমেই ভারতীয়দের মনে জায়গা করে নিয়েছে। পার্লামেন্টে দলটির আসনসংখ্যা ক্রমে বেড়েছে। ২০১৯ সালে দলটি এককভাবে ৩০০ আসন জিতলেও এবারে আরও বেশি আসন পাওয়ার প্রত্যাশা করছে। দলটির মধ্যে, এক ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোভাব দেখা যায়। বিপরীতে ২০১৯ সালের নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস (এক সময় ভারতের সবচেয়ে বড় দল) মাত্র ৫১টি আসন পেয়েছিল।
বিজেপি ভারতের পার্লামেন্টে বিরোধীদের প্রথমবার চমকে দেয় ১৯৬০—এর দশকে। পরের দশক অর্থাৎ ১৯৭০—এ তারা সরকার গঠন করে, ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থা জারির পর। তবে ১৯৮০—এর দশক থেকে হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিজেপি সামাজিকভাবে পায়ের তলার মাটি শক্ত করতে শুরু করে। কংগ্রেসের অস্থির রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে বিজেপির জন্য বিষয়টি আরও সহজ হয়ে যায়। যার ধারাবাহিকতায় বিজেপি জাতীয়তাবাদী বার্তা পাঠানোর মাধ্যমে হিন্দু সমাজকে তাদের পেছনে ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হয় এবং সরকার গঠন করে। সেই প্রথম ভারতের কংগ্রেসের বাইরে কোনো দল ক্ষমতায় আসে।
বিগত এক দশকে ভারতের রাজনীতি ঠিক যেন ১৯৮০—এর দশকের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি দেখছে। ২০১৪ সালে কংগ্রেসের অতি আত্মতুষ্টি এবং আত্মবিশ্বাস এবং বিজেপি বিরোধী আঞ্চলিক দলগুলোর মধ্যে নেতৃত্বে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধ বিজেপির জয়ের পথ প্রশস্ত করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৪ সালের পর প্রথম দল হিসেবে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসে বিজেপি। এরপর থেকে বিজেপি ক্রমেই ভারতীয় সমাজের সর্বক্ষেত্রে এর মতাদর্শিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছে।
উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া রাজনৈতিক দণ্ড তথা পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতির দেশে বিজেপি প্রথম ‘যোগ্যতা ভিত্তিক’ দলীয় রাজনীতির সূচনা করে। যার সর্বশেষ নমুনা হলো—দলটি এবারের নির্বাচনে গত লোকসভার অন্তত এক–চতুর্থাংশ এমপির জায়গায় নতুন মুখ এনেছে। এর মাধ্যমে বিজেপি দুটি বিষয় পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে পেরেছে—প্রথমটি হলো, দলটি নির্বাচনের রাজনীতি খুব ভালোভাবে বোঝে এবং দলটি কঠিন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে ভয় পায় না। দ্বিতীয়ত, কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে দলের রাজনীতি কেন্দ্রীভূত নয়। শীর্ষ নেতৃত্বের এই কৌশল দলটির নেতাদের সব সময়ই নিজেদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সতর্ক রাখে এবং একই সঙ্গে কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে দলটির সর্বময় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়া থেকে বিরত রাখে।
আজ থেকে ৩০ বছর আগেও বিজেপির মূল সমর্থকেরা ছিল ভারতের উচ্চবর্ণের শহুরে হিন্দু জনগোষ্ঠী। কিন্তু এই ৩০ বছরে বিজেপি ক্রমেই সাধারণ মানুষের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। ২০১৯ সালের নির্বাচনে বিজেপি গ্রামাঞ্চলের মোট ভোটের ৩৭ দশমিক ৬ শতাংশ পেয়েছে, মফস্বল এলাকার মোট ভোটের ৩২ দশমিক ৯ শতাংশ, নিম্ন আয়ের মানুষদের ভোটের ৩৬ শতাংশ এবং অন্যান্য বর্ণ ও তফসিলি হিন্দু গোষ্ঠীর মোট ভোটের ৩৩–৪৮ শতাংশ পেয়েছে। এই ফলাফল মূলত দলটির আদর্শিক মূল সংগঠন—১৯২৫ সালে ভারতে হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত—রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) মৌলিক আদর্শের গ্রহণযোগ্যতাকেই প্রতিফলিত করে।
এরপরও খোলাখুলিভাবে হিন্দু জাতীয়তাবাদী মনোভাব পোষণ এবং মুসলিমদের লক্ষ্যবস্তু করা বিজেপি ভারতের অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটেও ভাগ বসিয়েছে। খোদ মুসলিম সম্প্রদায়েই বিজেপির ভোট বেড়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ। পরিসংখ্যান বলছে, ২০০৯ সালে বিজেপি ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মাত্র ৪ শতাংশ ভোট পেয়েছিল, ২০০৯ সালে সেই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৯ শতাংশে। ২০১৯ সালের নির্বাচনে বিজেপি মুসলিম সম্প্রদায়ের ভোট পায় ১৯ শতাংশ। অবশ্য ৩০ শতাংশ মুসলিম ভোটার ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছিল। ভোটের বাকি অংশ অন্য আঞ্চলিক দলগুলো পেয়েছে।
সাধারণ জনগণের মধ্যে বিজেপির আবেদন বাড়ার পেছনে অন্যতম একটি কারণ হলো—দলটির নেতৃত্বে সরকারের চালু করা বিভিন্ন প্রকল্প, যা সরাসরি জনসাধারণকে সুবিধা দেয়। ২০১৩ সালে বিজেপি সরকার ৯০ কোটি মানুষের মধ্যে ৩১৫টি সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে ৬ হাজার কোটি ডলার নগদ অর্থ বিতরণ করেছে। আজ থেকে ৪০ বছর আগে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বলেছিলেন, জনকল্যাণে ভারত সরকারের নেওয়া বিভিন্ন প্রকল্পের মাত্র ১৫ শতাংশ সুবিধা সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছায়। বিজেপি সরকার সেই চিত্র পাল্টে দিয়েছে।
অনেক বিশ্লেষক, বিজেপি নেতাদের গৃহীত তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর প্রশংসা করেন। তাঁদের মতে, এসব প্রকল্প সরাসরি সাধারণ মানুষের কাছেও গৃহীত হয়েছে দারুণভাবে। ২০১৪ সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর দলীয়ভাবে ‘সহযোগ নীতি’ গ্রহণ করে। যার ফলে, বিজেপির মন্ত্রীরা পালাক্রমে বাধ্যতামূলকভাবে দলীয় কার্যালয়ে উপস্থিত হতেন। এমনটা করা হয়েছিল, যেন দলীয় কর্মীরা মন্ত্রীদের সরাসরি সংস্পর্শে আসতে পারেন। প্রতিদিন প্রায় ২০০ জন করে ব্যক্তি মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। এসব কর্মী মূলত তৃণমূল পর্যায়ে সরকারি নীতি ও দলীয় নীতির মধ্যকার ফারাক এবং অন্যান্য সমস্যা তুলে ধরতেন। যা সরাসরি বিজেপির সাংগঠনিক এবং প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে, এখনো রাখছে।
এ ছাড়া, বিজেপি সরকার নরেন্দ্র মোদিকে কেন্দ্র করে একটি শক্তিশালী উন্নয়নের বয়ানও তৈরি করেছে। গত এক দশকে ৭৫টি নতুন বিমানবন্দর নির্মাণ, গত বছর ভারতে আয়োজিত জি–২০ শীর্ষ সম্মেলন এবং ৫ লাখ কোটি ডলারের জিডিপি লক্ষ্য, ভারত এখন বিশ্ব মঞ্চে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ—এই জাতীয় অনেক বিষয়কে ধরে বিজেপি এই বয়ান তৈরি করেছে যে, এমনটা কেবল সম্ভব হয়েছে মোদির নেতৃত্বে বিজেপি সরকারের কল্যাণে।
এরপরও বিজেপি লোকসভা নির্বাচনে প্রচারণায় কোনো একটি দিকও বাদ দেয়নি। একেবারে প্রত্যেক ভোটারকে কেন্দ্র করে দলটির নির্দিষ্ট নেতা–কর্মীদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যাতে তাঁরা সেই ভোটারকে বিজেপির পক্ষে আনতে পারেন। প্রতিটি জেলায় ১৮ থেকে ২০টি করে মিডিয়া ভ্যান পাঠানো হয়েছে, বিজেপির নির্বাচনী ইশতেহারসহ নানা উন্নয়ন বার্তা প্রচার করার জন্য। এমনকি, গ্রামও বাদ যায়নি। তাদের কাছে, প্রত্যেক ভোটার একেকজন ক্রেতা। কে কী কেনে তার ওপর ভিত্তি করে দলটি প্রচারণা চালায়। বিজেপির এই ‘আপনার গ্রাহক সম্পর্কে জানুন’ ডেটাবেইস এত সমৃদ্ধ যে, অনেক বহুজাতিক কোম্পানিকেও তা লজ্জায় ফেলে দিতে পারে।
এত কিছুর বাইরেও নরেন্দ্র মোদির ব্যক্তি ভাবমূর্তি বিজেপিকে বাড়তি শক্তি দিয়েছে। ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসে তাঁর মতো ক্যারিশমাটিক নেতা আর দ্বিতীয়টি নেই। সবচেয়ে বড় কথা হলো, যেকোনো ইস্যুতে তাঁর নিয়ন্ত্রণ অসাধারণ এবং তিনি যেকোনো ইস্যুকে নিজের অনুকূলে ব্যবহারের ক্ষমতা রাখেন। এসব গুণাবলি তাঁকে বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় নেতায় পরিণত করেছে। এক জরিপ বলছে, অন্তত ৭৮ (জরিপে অংশ নেওয়াদের মধ্যে) মানুষের মোদির প্রতি সমর্থন আছে বা তাঁকে পছন্দ করেন। বিজেপির অনেক প্রার্থীই মোদির নাম ব্যবহার করে নির্বাচনী বৈতরণি পার হওয়াকে সহজ মনে করেন। একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। ২০১৯ সালের নির্বাচনের সময় যেসব বিরোধী নেতা বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা গড়ে ৫৬ দশমিক ৫২ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন। কিন্তু অন্যান্য দলে যোগ দেওয়া নেতারা মাত্র ১৪ দশমিক ৯ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন।
বিজেপির শক্তির জায়গাগুলোর সমালোচনাও আছে। যেমন, দলটির যে হিন্দু জাতীয়তাবাদী মনোভাব সেটির চূড়ান্ত ফলাফল কী তা নিয়ে ধোঁয়াশা আছে, দলটির যে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোভাব সেটা অনেকটা দোধারী তলোয়ারের মতো, মোদির ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা দলটিকে মিথ্যা আত্মবিশ্বাস বা ফলস কনফিডেন্স জোগাতে পারে। এ ছাড়া, সবচেয়ে বড় যে সমস্যা, সেটি হলো—দলটির যে বিশাল কর্মীবাহিনী তা এক সময় দলটির বোঝায় পরিণত হতে পারে।
এই অবস্থায় ধারাবাহিকভাবে সরকারে থাকার ফলে দলে যে সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক ঝামেলাগুলো তৈরি হয়, বিজেপিকে সেই বিষয়গুলো মোকাবিলার বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। অন্তত কংগ্রেসের দিকে তাকিয়ে দলটি এই বিষয়ে শিক্ষা নিতে পারে। কারণ, এক সময়ের প্রতাপশালী দলটির প্রয়োজনীয়তা–গুরুত্ব নিয়েই এখন অনেকে প্রশ্ন তুলছেন। তাই বিজেপি যখন নিজে দলের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের কথা বলে, তখন তাদেরও ভারতীয় সেই পুরোনো প্রবাদ মনে রাখা উচিত, ‘কিলে আন্দার সে হি সাড় যাতে হ্যায়’, বা ‘দুর্গের ক্ষয় শুরু হয় ভেতর থেকেই, বাইরে থেকে নয়’।

অনেকে বলছেন, এবারের লোকসভা নির্বাচনে ভারতের হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল বিজেপির প্রতি মানুষের প্রত্যাশা বেড়েছে। কিন্তু কেন? সোজা কথায় বলতে গেলে, এই দলটি প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় অনেক বেশি সুসংগঠিত। দলটির নেতা নরেন্দ্র মোদি ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসে যেকোনো রাজনৈতিক নেতার তুলনায় অনেক বেশি ‘ক্যারিশমাটিক’!
তবে কেবল এই দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে নয়, বিজেপির প্রতি জনপ্রত্যাশা, জনসমর্থন ইত্যাদির পেছনে আরও জটিল কারণ রয়েছে। ভারতের চলতি লোকসভা নির্বাচনে ভোট দিচ্ছেন ৯৬ কোটি ৮০ লাখ। ভোটার বিবেচনায় ভারতকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ বলা হয়। আর সেই দেশের রাজনৈতিক দল, মোদির বিজেপি বিশ্বেরও সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল। ধারণা করা হচ্ছে, বিজেপি টানা তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসতে যাচ্ছে।
ভারতের নির্বাচনী রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বিজেপির আধিপত্যের বেশ কয়েকটি কারণ আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো—সুসংহত সাংগঠনিক কাঠামো, নেতৃত্বে জনপ্রিয়দের স্থান দেওয়া, ভোটব্যাংক বাড়ানোর বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে কাজ করা। এর বাইরে, দক্ষতার সঙ্গে গরিব জনগোষ্ঠীকে সরকারি প্রকল্পের উপকারভোগী হিসেবে হাজির করা। গত কয়েক বছরে হিন্দুত্ববাদী এবং গরিবদের জন্য সরকারি সহায়তা প্রকল্পগুলোতে সরাসরি মোদির ব্র্যান্ডিং করা হয়েছে।
সামাজিকভাবে বিজেপি রক্ষণশীল হিন্দু ঘরানার এবং অর্থনৈতিক মতাদর্শে মধ্যপন্থী। আনুষ্ঠিকভাবে দলটি ১৯৮০ সালে যাত্রা শুরু করলেও এর শিকড় নিহিত ভারতীয় জনসংঘের মধ্যে। ভারতীয় জনসংঘ ১৯৫০—এর দশকের একটি রাজনৈতিক দল। যার মূল মতাদর্শই ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদ। সে সময় ভারতজুড়ে চলমান সমাজবাদী রাজনৈতিক মতাদর্শের বিপরীতে গড়ে উঠেছিল দলটি।
ভারতীয় জনসংঘ থেকে হিসাব করলে, দলটি প্রতিষ্ঠার ৭৭ বছরে বিজেপি মাত্র ১৯ বছর ক্ষমতায় ছিল (এখনো আছে)। প্রথমবার দলটি ক্ষমতায় আসে ১৯৭৭ সালে। সে সময় ক্ষমতায় ছিল ৩ বছর। এরপর মাত্র ১৩ দিন ক্ষমতায় ছিল ১৯৯৬ সালে, ১৯৯৮ সালে ক্ষমতায় ছিল ১ বছর। ১৯৯৯ সাল থেকে ক্ষমতায় ছিল পাঁচ বছর এবং এর পর ২০১৪ সাল থেকে টানা ১০ বছর ধরে ক্ষমতায় দলটি।
বিজেপি প্রতিষ্ঠার পর থেকে ক্রমেই ভারতীয়দের মনে জায়গা করে নিয়েছে। পার্লামেন্টে দলটির আসনসংখ্যা ক্রমে বেড়েছে। ২০১৯ সালে দলটি এককভাবে ৩০০ আসন জিতলেও এবারে আরও বেশি আসন পাওয়ার প্রত্যাশা করছে। দলটির মধ্যে, এক ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোভাব দেখা যায়। বিপরীতে ২০১৯ সালের নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস (এক সময় ভারতের সবচেয়ে বড় দল) মাত্র ৫১টি আসন পেয়েছিল।
বিজেপি ভারতের পার্লামেন্টে বিরোধীদের প্রথমবার চমকে দেয় ১৯৬০—এর দশকে। পরের দশক অর্থাৎ ১৯৭০—এ তারা সরকার গঠন করে, ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থা জারির পর। তবে ১৯৮০—এর দশক থেকে হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিজেপি সামাজিকভাবে পায়ের তলার মাটি শক্ত করতে শুরু করে। কংগ্রেসের অস্থির রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে বিজেপির জন্য বিষয়টি আরও সহজ হয়ে যায়। যার ধারাবাহিকতায় বিজেপি জাতীয়তাবাদী বার্তা পাঠানোর মাধ্যমে হিন্দু সমাজকে তাদের পেছনে ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হয় এবং সরকার গঠন করে। সেই প্রথম ভারতের কংগ্রেসের বাইরে কোনো দল ক্ষমতায় আসে।
বিগত এক দশকে ভারতের রাজনীতি ঠিক যেন ১৯৮০—এর দশকের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি দেখছে। ২০১৪ সালে কংগ্রেসের অতি আত্মতুষ্টি এবং আত্মবিশ্বাস এবং বিজেপি বিরোধী আঞ্চলিক দলগুলোর মধ্যে নেতৃত্বে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধ বিজেপির জয়ের পথ প্রশস্ত করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৪ সালের পর প্রথম দল হিসেবে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসে বিজেপি। এরপর থেকে বিজেপি ক্রমেই ভারতীয় সমাজের সর্বক্ষেত্রে এর মতাদর্শিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছে।
উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া রাজনৈতিক দণ্ড তথা পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতির দেশে বিজেপি প্রথম ‘যোগ্যতা ভিত্তিক’ দলীয় রাজনীতির সূচনা করে। যার সর্বশেষ নমুনা হলো—দলটি এবারের নির্বাচনে গত লোকসভার অন্তত এক–চতুর্থাংশ এমপির জায়গায় নতুন মুখ এনেছে। এর মাধ্যমে বিজেপি দুটি বিষয় পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে পেরেছে—প্রথমটি হলো, দলটি নির্বাচনের রাজনীতি খুব ভালোভাবে বোঝে এবং দলটি কঠিন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে ভয় পায় না। দ্বিতীয়ত, কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে দলের রাজনীতি কেন্দ্রীভূত নয়। শীর্ষ নেতৃত্বের এই কৌশল দলটির নেতাদের সব সময়ই নিজেদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সতর্ক রাখে এবং একই সঙ্গে কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে দলটির সর্বময় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়া থেকে বিরত রাখে।
আজ থেকে ৩০ বছর আগেও বিজেপির মূল সমর্থকেরা ছিল ভারতের উচ্চবর্ণের শহুরে হিন্দু জনগোষ্ঠী। কিন্তু এই ৩০ বছরে বিজেপি ক্রমেই সাধারণ মানুষের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। ২০১৯ সালের নির্বাচনে বিজেপি গ্রামাঞ্চলের মোট ভোটের ৩৭ দশমিক ৬ শতাংশ পেয়েছে, মফস্বল এলাকার মোট ভোটের ৩২ দশমিক ৯ শতাংশ, নিম্ন আয়ের মানুষদের ভোটের ৩৬ শতাংশ এবং অন্যান্য বর্ণ ও তফসিলি হিন্দু গোষ্ঠীর মোট ভোটের ৩৩–৪৮ শতাংশ পেয়েছে। এই ফলাফল মূলত দলটির আদর্শিক মূল সংগঠন—১৯২৫ সালে ভারতে হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত—রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) মৌলিক আদর্শের গ্রহণযোগ্যতাকেই প্রতিফলিত করে।
এরপরও খোলাখুলিভাবে হিন্দু জাতীয়তাবাদী মনোভাব পোষণ এবং মুসলিমদের লক্ষ্যবস্তু করা বিজেপি ভারতের অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটেও ভাগ বসিয়েছে। খোদ মুসলিম সম্প্রদায়েই বিজেপির ভোট বেড়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ। পরিসংখ্যান বলছে, ২০০৯ সালে বিজেপি ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মাত্র ৪ শতাংশ ভোট পেয়েছিল, ২০০৯ সালে সেই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৯ শতাংশে। ২০১৯ সালের নির্বাচনে বিজেপি মুসলিম সম্প্রদায়ের ভোট পায় ১৯ শতাংশ। অবশ্য ৩০ শতাংশ মুসলিম ভোটার ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছিল। ভোটের বাকি অংশ অন্য আঞ্চলিক দলগুলো পেয়েছে।
সাধারণ জনগণের মধ্যে বিজেপির আবেদন বাড়ার পেছনে অন্যতম একটি কারণ হলো—দলটির নেতৃত্বে সরকারের চালু করা বিভিন্ন প্রকল্প, যা সরাসরি জনসাধারণকে সুবিধা দেয়। ২০১৩ সালে বিজেপি সরকার ৯০ কোটি মানুষের মধ্যে ৩১৫টি সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে ৬ হাজার কোটি ডলার নগদ অর্থ বিতরণ করেছে। আজ থেকে ৪০ বছর আগে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বলেছিলেন, জনকল্যাণে ভারত সরকারের নেওয়া বিভিন্ন প্রকল্পের মাত্র ১৫ শতাংশ সুবিধা সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছায়। বিজেপি সরকার সেই চিত্র পাল্টে দিয়েছে।
অনেক বিশ্লেষক, বিজেপি নেতাদের গৃহীত তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর প্রশংসা করেন। তাঁদের মতে, এসব প্রকল্প সরাসরি সাধারণ মানুষের কাছেও গৃহীত হয়েছে দারুণভাবে। ২০১৪ সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর দলীয়ভাবে ‘সহযোগ নীতি’ গ্রহণ করে। যার ফলে, বিজেপির মন্ত্রীরা পালাক্রমে বাধ্যতামূলকভাবে দলীয় কার্যালয়ে উপস্থিত হতেন। এমনটা করা হয়েছিল, যেন দলীয় কর্মীরা মন্ত্রীদের সরাসরি সংস্পর্শে আসতে পারেন। প্রতিদিন প্রায় ২০০ জন করে ব্যক্তি মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। এসব কর্মী মূলত তৃণমূল পর্যায়ে সরকারি নীতি ও দলীয় নীতির মধ্যকার ফারাক এবং অন্যান্য সমস্যা তুলে ধরতেন। যা সরাসরি বিজেপির সাংগঠনিক এবং প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে, এখনো রাখছে।
এ ছাড়া, বিজেপি সরকার নরেন্দ্র মোদিকে কেন্দ্র করে একটি শক্তিশালী উন্নয়নের বয়ানও তৈরি করেছে। গত এক দশকে ৭৫টি নতুন বিমানবন্দর নির্মাণ, গত বছর ভারতে আয়োজিত জি–২০ শীর্ষ সম্মেলন এবং ৫ লাখ কোটি ডলারের জিডিপি লক্ষ্য, ভারত এখন বিশ্ব মঞ্চে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ—এই জাতীয় অনেক বিষয়কে ধরে বিজেপি এই বয়ান তৈরি করেছে যে, এমনটা কেবল সম্ভব হয়েছে মোদির নেতৃত্বে বিজেপি সরকারের কল্যাণে।
এরপরও বিজেপি লোকসভা নির্বাচনে প্রচারণায় কোনো একটি দিকও বাদ দেয়নি। একেবারে প্রত্যেক ভোটারকে কেন্দ্র করে দলটির নির্দিষ্ট নেতা–কর্মীদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যাতে তাঁরা সেই ভোটারকে বিজেপির পক্ষে আনতে পারেন। প্রতিটি জেলায় ১৮ থেকে ২০টি করে মিডিয়া ভ্যান পাঠানো হয়েছে, বিজেপির নির্বাচনী ইশতেহারসহ নানা উন্নয়ন বার্তা প্রচার করার জন্য। এমনকি, গ্রামও বাদ যায়নি। তাদের কাছে, প্রত্যেক ভোটার একেকজন ক্রেতা। কে কী কেনে তার ওপর ভিত্তি করে দলটি প্রচারণা চালায়। বিজেপির এই ‘আপনার গ্রাহক সম্পর্কে জানুন’ ডেটাবেইস এত সমৃদ্ধ যে, অনেক বহুজাতিক কোম্পানিকেও তা লজ্জায় ফেলে দিতে পারে।
এত কিছুর বাইরেও নরেন্দ্র মোদির ব্যক্তি ভাবমূর্তি বিজেপিকে বাড়তি শক্তি দিয়েছে। ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসে তাঁর মতো ক্যারিশমাটিক নেতা আর দ্বিতীয়টি নেই। সবচেয়ে বড় কথা হলো, যেকোনো ইস্যুতে তাঁর নিয়ন্ত্রণ অসাধারণ এবং তিনি যেকোনো ইস্যুকে নিজের অনুকূলে ব্যবহারের ক্ষমতা রাখেন। এসব গুণাবলি তাঁকে বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় নেতায় পরিণত করেছে। এক জরিপ বলছে, অন্তত ৭৮ (জরিপে অংশ নেওয়াদের মধ্যে) মানুষের মোদির প্রতি সমর্থন আছে বা তাঁকে পছন্দ করেন। বিজেপির অনেক প্রার্থীই মোদির নাম ব্যবহার করে নির্বাচনী বৈতরণি পার হওয়াকে সহজ মনে করেন। একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। ২০১৯ সালের নির্বাচনের সময় যেসব বিরোধী নেতা বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা গড়ে ৫৬ দশমিক ৫২ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন। কিন্তু অন্যান্য দলে যোগ দেওয়া নেতারা মাত্র ১৪ দশমিক ৯ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন।
বিজেপির শক্তির জায়গাগুলোর সমালোচনাও আছে। যেমন, দলটির যে হিন্দু জাতীয়তাবাদী মনোভাব সেটির চূড়ান্ত ফলাফল কী তা নিয়ে ধোঁয়াশা আছে, দলটির যে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোভাব সেটা অনেকটা দোধারী তলোয়ারের মতো, মোদির ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা দলটিকে মিথ্যা আত্মবিশ্বাস বা ফলস কনফিডেন্স জোগাতে পারে। এ ছাড়া, সবচেয়ে বড় যে সমস্যা, সেটি হলো—দলটির যে বিশাল কর্মীবাহিনী তা এক সময় দলটির বোঝায় পরিণত হতে পারে।
এই অবস্থায় ধারাবাহিকভাবে সরকারে থাকার ফলে দলে যে সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক ঝামেলাগুলো তৈরি হয়, বিজেপিকে সেই বিষয়গুলো মোকাবিলার বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। অন্তত কংগ্রেসের দিকে তাকিয়ে দলটি এই বিষয়ে শিক্ষা নিতে পারে। কারণ, এক সময়ের প্রতাপশালী দলটির প্রয়োজনীয়তা–গুরুত্ব নিয়েই এখন অনেকে প্রশ্ন তুলছেন। তাই বিজেপি যখন নিজে দলের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের কথা বলে, তখন তাদেরও ভারতীয় সেই পুরোনো প্রবাদ মনে রাখা উচিত, ‘কিলে আন্দার সে হি সাড় যাতে হ্যায়’, বা ‘দুর্গের ক্ষয় শুরু হয় ভেতর থেকেই, বাইরে থেকে নয়’।

ডিজিটাল যুগে আমরা কেবল প্রযুক্তি ব্যবহার করছি না—আমরা প্রযুক্তির কাছে নিজেদের মনোযোগ, অনুভূতি, এমনকি চিন্তার স্বাধীনতাও তুলে দিচ্ছি। অ্যালগরিদম এখন আমাদের সিদ্ধান্ত, সম্পর্ক ও চেতনার গভীর স্তরে হস্তক্ষেপ করছে। শোষণ আজ আর কেবল শ্রমের ওপর নির্ভরশীল নয়—এখন তা মন ও মনোযোগের বাণিজ্যে রূপ নিয়েছে।
৪ দিন আগে
পুতিন যখন যুদ্ধে জয় নিয়ে খুব আত্মবিশ্বাসী মনোভাব দেখাচ্ছেন, ঠিক তখনই রাশিয়ার ভেতরে ড্রোন হামলা চালিয়ে অন্তত ৪০টি বোমারু বিমান ধ্বংস করে দিয়েছে ইউক্রেন। এগুলোর মধ্যে কিছু পারমাণবিক অস্ত্রবাহী যুদ্ধবিমানও ছিল।
৫ দিন আগে
বিশ্বের ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা ও ‘রুশ আগ্রাসনের নতুন যুগে’ প্রতিরক্ষা খাতে বড় পরিসরে বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাজ্য। গত সোমবার (২ জুন) প্রকাশিত যুক্তরাজ্যের কৌশলগত প্রতিরক্ষা পর্যালোচনায় (এসডিআর) উঠে এসেছে পারমাণবিক অস্ত্র, সাবমেরিন ও গোলাবারুদ তৈরির নতুন কারখানায় বিনিয়োগের পরিকল্পনা।
৫ দিন আগে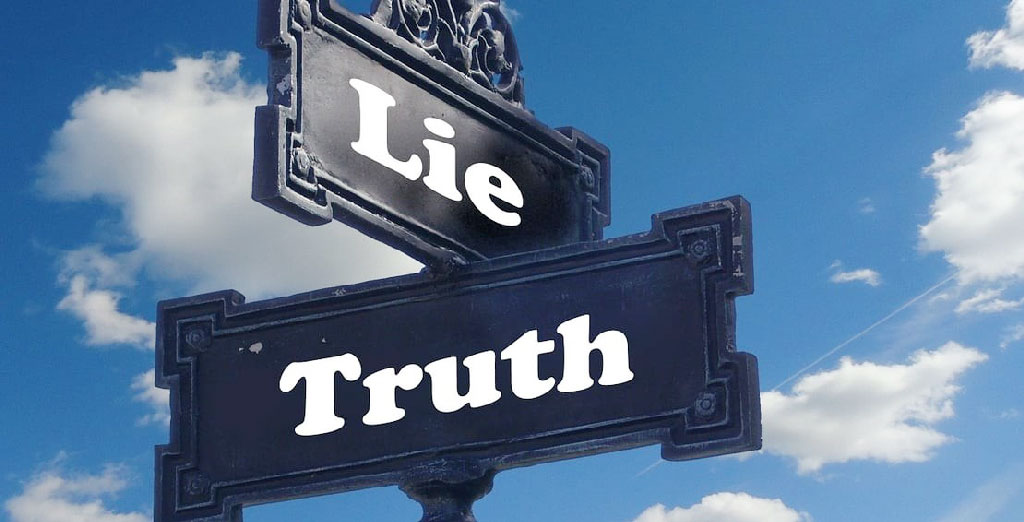
সত্য কী? অধিকাংশ মানুষের কাছে সত্য মানে হলো, যা বাস্তব তথ্যের সঙ্গে মিলে। অবশ্য আজকাল ‘বিকল্প সত্য’ নামে নতুন এক ধারণা অনেকে হাজির করছেন। সে যাই হোক, অভিজ্ঞতা বলে, সত্য শুধু বস্তুনিষ্ঠ হওয়াটাই যথেষ্ট নয়, সত্য প্রকাশের উপযুক্ত লগ্ন, সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য খুবই জরুরি।
৫ দিন আগে