জয়তী ঘোষ

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতি বিশ্ববাজারে যে অর্থনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করেছে, তার প্রভাবে বিশ্বজুড়ে সুরক্ষাবাদী (প্রটেকশনিস্ট) প্রবণতা বেড়েছে। এ বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কিছু সিদ্ধান্ত হয়তো স্বল্পস্থায়ী হবে, কিন্তু শুল্ককে ভূরাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার প্রবণতা আগামী কয়েক দশক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ধারা বদলে দিতে পারে।
তবে ট্রাম্পের শুল্কনীতি নিয়ে আলোচনার আড়ালে লুকিয়ে আছে আরও বড় একটি বিষয়, যুক্তরাষ্ট্র তার অর্থনৈতিক ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে বাজার উন্মুক্ত করা এবং মার্কিন কোম্পানিগুলোর জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা আদায় করছে, যা নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশের উন্নয়ন সম্ভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এই নীতির প্রধান হাতিয়ার হলো মেধাস্বত্ব (ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি বা আইপি) আইন, যার মাধ্যমে জ্ঞানকে বেসরকারি পণ্যে পরিণত করা হচ্ছে পেটেন্ট, কপিরাইট ও শিল্পনকশার মাধ্যমে।
সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র-ইন্দোনেশিয়া বাণিজ্য চুক্তিতে দেখা গেছে, ইন্দোনেশিয়া প্রযুক্তি ও শিল্প খাতের উন্নয়নকে সীমিত করে মার্কিন স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী, ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের ৯৯ শতাংশ শিল্প, খাদ্য ও কৃষিপণ্যে শুল্ক তুলে দেবে, অথচ মার্কিন বাজারে ইন্দোনেশিয়ার পণ্যের গড় শুল্ক থাকবে ১৯ শতাংশ। এর ফলে বিশেষত ইন্দোনেশিয়ার কৃষকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ, তাদের মার্কিন ভর্তুকিপ্রাপ্ত কৃষিপণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হবে। আরও উদ্বেগজনক হলো, অশুল্ক প্রতিবন্ধকতা দূর করার মাধ্যমে দেশটির প্রযুক্তি প্রাপ্তির সুযোগও সীমিত হবে।
এই প্রেক্ষাপটে সম্প্রতি ভারতের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের স্বাক্ষরিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) কিছু প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। দীর্ঘ বছরের আলোচনার পর এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও এর বাণিজ্যিক গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে কম। কারণ, দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য দুই দেশের মোট রপ্তানির ২ দশমিক ৫ শতাংশের কম। তা সত্ত্বেও দুই সরকার একে ‘ঐতিহাসিক’ বলে প্রচার করছে।
চুক্তির প্রচারে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে শুল্ক কমানোর দিকটি। এতে বলা হয়েছে, যুক্তরাজ্যের ৯২ শতাংশ রপ্তানি পণ্যে ভারত সম্পূর্ণ বা আংশিক শুল্ক ছাড় দেবে, আর ভারতের ৯৯ শতাংশ রপ্তানি পণ্য যুক্তরাজ্যে শুল্কমুক্ত হবে। ফলে ভারতীয় টেক্সটাইল, পোশাক ও গয়না এবং ব্রিটিশ মদ্যপ পানীয় ও গাড়ি রপ্তানিতে দ্বিগুণ প্রবৃদ্ধি আসতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হচ্ছে।
এই চুক্তির সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অংশ হলো মেধাস্বত্ব-সংক্রান্ত ধারা, যা পশ্চিমা পেটেন্টধারী কোম্পানিগুলোর স্বার্থ রক্ষায় ঝুঁকে আছে। এতে ভারতের ওষুধশিল্প ও জনস্বাস্থ্য খাতে বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।
চুক্তিতে বাধ্যতামূলক লাইসেন্সের পরিবর্তে স্বেচ্ছা লাইসেন্স ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বাধ্যতামূলক লাইসেন্স হলো এমন একটি ব্যবস্থা, যা সরকারি প্রয়োজনে পেটেন্টধারীর অনুমতি ছাড়াই ওষুধ উৎপাদনের সুযোগ দেয়, যাতে দাম কমে এবং প্রাপ্যতা বাড়ে। কিন্তু স্বেচ্ছা লাইসেন্স ব্যবহারে জোর দিলে ভবিষ্যতে দাম কমানোর সুযোগ সীমিত হয়ে যাবে।
আরেকটি ধারা পেটেন্টের মেয়াদ ‘এভারগ্রিনিং’ প্রক্রিয়ায় বাড়ানোর সুযোগ তৈরি করবে। এর মাধ্যমে ওষুধে সামান্য পরিবর্তন এনে পুরোনো পেটেন্ট নতুন করে নিবন্ধন করা সম্ভব হবে, যা প্রতিযোগিতা কমিয়ে দেবে এবং সস্তা বিকল্প ওষুধ বাজারে আনতে বিলম্ব ঘটাবে।
সবচেয়ে বিতর্কিত অংশ হলো ভারতে কোনো পেটেন্ট পণ্য কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেই তথ্য প্রকাশের সময়সীমা এক বছর থেকে বাড়িয়ে তিন বছর করা। এর ফলে বাজারে চাহিদা পূরণ না হওয়ার প্রমাণ পাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে, যা বাধ্যতামূলক লাইসেন্স কার্যকর করার পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে।
এই ধারা শুধু ভারতের ওষুধশিল্প নয়, বৈশ্বিকভাবে সাশ্রয়ী ওষুধ সরবরাহকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে। ভারত বিশ্বের অন্যতম প্রধান জেনেরিক ওষুধ উৎপাদনকারী দেশ, যা উন্নয়নশীল দেশের মানুষের জন্য জীবন রক্ষাকারী ওষুধ সুলভ করেছে। চুক্তির এসব বিধান কার্যকর হলে সেই সরবরাহব্যবস্থায় ধাক্কা লাগতে পারে। এ ছাড়া সবুজ প্রযুক্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও ভারতের সুযোগ সীমিত হতে পারে, যা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় দেশের অগ্রগতিকে ব্যাহত করবে।
তুলনামূলকভাবে দুর্বল ও সাবেক ঔপনিবেশিক শক্তির কাছে ভারত কেন এত বড় ছাড় দিল—যে দেশ বর্তমানে ভারতের শীর্ষ বাণিজ্য অংশীদারও নয়, এ মুহূর্তে এমন প্রশ্ন তোলা অস্বাভাবিক নয়। তবে এই চুক্তির সার্বিক দিক বিবেচনা করে বোঝা যাচ্ছে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চলমান বাণিজ্য আলোচনায় ভারত আরও বড় চাপের মুখে পড়তে পারে। এমন পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উচিত, ভারতের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ রক্ষায় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের অবস্থান শক্ত করা।
লেখক: জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক।
(প্রজেক্ট সিন্ডিকেট থেকে সংক্ষেপে অনূদিত)

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতি বিশ্ববাজারে যে অর্থনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করেছে, তার প্রভাবে বিশ্বজুড়ে সুরক্ষাবাদী (প্রটেকশনিস্ট) প্রবণতা বেড়েছে। এ বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কিছু সিদ্ধান্ত হয়তো স্বল্পস্থায়ী হবে, কিন্তু শুল্ককে ভূরাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার প্রবণতা আগামী কয়েক দশক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ধারা বদলে দিতে পারে।
তবে ট্রাম্পের শুল্কনীতি নিয়ে আলোচনার আড়ালে লুকিয়ে আছে আরও বড় একটি বিষয়, যুক্তরাষ্ট্র তার অর্থনৈতিক ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে বাজার উন্মুক্ত করা এবং মার্কিন কোম্পানিগুলোর জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা আদায় করছে, যা নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশের উন্নয়ন সম্ভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এই নীতির প্রধান হাতিয়ার হলো মেধাস্বত্ব (ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি বা আইপি) আইন, যার মাধ্যমে জ্ঞানকে বেসরকারি পণ্যে পরিণত করা হচ্ছে পেটেন্ট, কপিরাইট ও শিল্পনকশার মাধ্যমে।
সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র-ইন্দোনেশিয়া বাণিজ্য চুক্তিতে দেখা গেছে, ইন্দোনেশিয়া প্রযুক্তি ও শিল্প খাতের উন্নয়নকে সীমিত করে মার্কিন স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী, ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের ৯৯ শতাংশ শিল্প, খাদ্য ও কৃষিপণ্যে শুল্ক তুলে দেবে, অথচ মার্কিন বাজারে ইন্দোনেশিয়ার পণ্যের গড় শুল্ক থাকবে ১৯ শতাংশ। এর ফলে বিশেষত ইন্দোনেশিয়ার কৃষকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ, তাদের মার্কিন ভর্তুকিপ্রাপ্ত কৃষিপণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হবে। আরও উদ্বেগজনক হলো, অশুল্ক প্রতিবন্ধকতা দূর করার মাধ্যমে দেশটির প্রযুক্তি প্রাপ্তির সুযোগও সীমিত হবে।
এই প্রেক্ষাপটে সম্প্রতি ভারতের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের স্বাক্ষরিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) কিছু প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। দীর্ঘ বছরের আলোচনার পর এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও এর বাণিজ্যিক গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে কম। কারণ, দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য দুই দেশের মোট রপ্তানির ২ দশমিক ৫ শতাংশের কম। তা সত্ত্বেও দুই সরকার একে ‘ঐতিহাসিক’ বলে প্রচার করছে।
চুক্তির প্রচারে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে শুল্ক কমানোর দিকটি। এতে বলা হয়েছে, যুক্তরাজ্যের ৯২ শতাংশ রপ্তানি পণ্যে ভারত সম্পূর্ণ বা আংশিক শুল্ক ছাড় দেবে, আর ভারতের ৯৯ শতাংশ রপ্তানি পণ্য যুক্তরাজ্যে শুল্কমুক্ত হবে। ফলে ভারতীয় টেক্সটাইল, পোশাক ও গয়না এবং ব্রিটিশ মদ্যপ পানীয় ও গাড়ি রপ্তানিতে দ্বিগুণ প্রবৃদ্ধি আসতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হচ্ছে।
এই চুক্তির সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অংশ হলো মেধাস্বত্ব-সংক্রান্ত ধারা, যা পশ্চিমা পেটেন্টধারী কোম্পানিগুলোর স্বার্থ রক্ষায় ঝুঁকে আছে। এতে ভারতের ওষুধশিল্প ও জনস্বাস্থ্য খাতে বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।
চুক্তিতে বাধ্যতামূলক লাইসেন্সের পরিবর্তে স্বেচ্ছা লাইসেন্স ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বাধ্যতামূলক লাইসেন্স হলো এমন একটি ব্যবস্থা, যা সরকারি প্রয়োজনে পেটেন্টধারীর অনুমতি ছাড়াই ওষুধ উৎপাদনের সুযোগ দেয়, যাতে দাম কমে এবং প্রাপ্যতা বাড়ে। কিন্তু স্বেচ্ছা লাইসেন্স ব্যবহারে জোর দিলে ভবিষ্যতে দাম কমানোর সুযোগ সীমিত হয়ে যাবে।
আরেকটি ধারা পেটেন্টের মেয়াদ ‘এভারগ্রিনিং’ প্রক্রিয়ায় বাড়ানোর সুযোগ তৈরি করবে। এর মাধ্যমে ওষুধে সামান্য পরিবর্তন এনে পুরোনো পেটেন্ট নতুন করে নিবন্ধন করা সম্ভব হবে, যা প্রতিযোগিতা কমিয়ে দেবে এবং সস্তা বিকল্প ওষুধ বাজারে আনতে বিলম্ব ঘটাবে।
সবচেয়ে বিতর্কিত অংশ হলো ভারতে কোনো পেটেন্ট পণ্য কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেই তথ্য প্রকাশের সময়সীমা এক বছর থেকে বাড়িয়ে তিন বছর করা। এর ফলে বাজারে চাহিদা পূরণ না হওয়ার প্রমাণ পাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে, যা বাধ্যতামূলক লাইসেন্স কার্যকর করার পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে।
এই ধারা শুধু ভারতের ওষুধশিল্প নয়, বৈশ্বিকভাবে সাশ্রয়ী ওষুধ সরবরাহকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে। ভারত বিশ্বের অন্যতম প্রধান জেনেরিক ওষুধ উৎপাদনকারী দেশ, যা উন্নয়নশীল দেশের মানুষের জন্য জীবন রক্ষাকারী ওষুধ সুলভ করেছে। চুক্তির এসব বিধান কার্যকর হলে সেই সরবরাহব্যবস্থায় ধাক্কা লাগতে পারে। এ ছাড়া সবুজ প্রযুক্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও ভারতের সুযোগ সীমিত হতে পারে, যা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় দেশের অগ্রগতিকে ব্যাহত করবে।
তুলনামূলকভাবে দুর্বল ও সাবেক ঔপনিবেশিক শক্তির কাছে ভারত কেন এত বড় ছাড় দিল—যে দেশ বর্তমানে ভারতের শীর্ষ বাণিজ্য অংশীদারও নয়, এ মুহূর্তে এমন প্রশ্ন তোলা অস্বাভাবিক নয়। তবে এই চুক্তির সার্বিক দিক বিবেচনা করে বোঝা যাচ্ছে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চলমান বাণিজ্য আলোচনায় ভারত আরও বড় চাপের মুখে পড়তে পারে। এমন পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উচিত, ভারতের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ রক্ষায় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের অবস্থান শক্ত করা।
লেখক: জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক।
(প্রজেক্ট সিন্ডিকেট থেকে সংক্ষেপে অনূদিত)
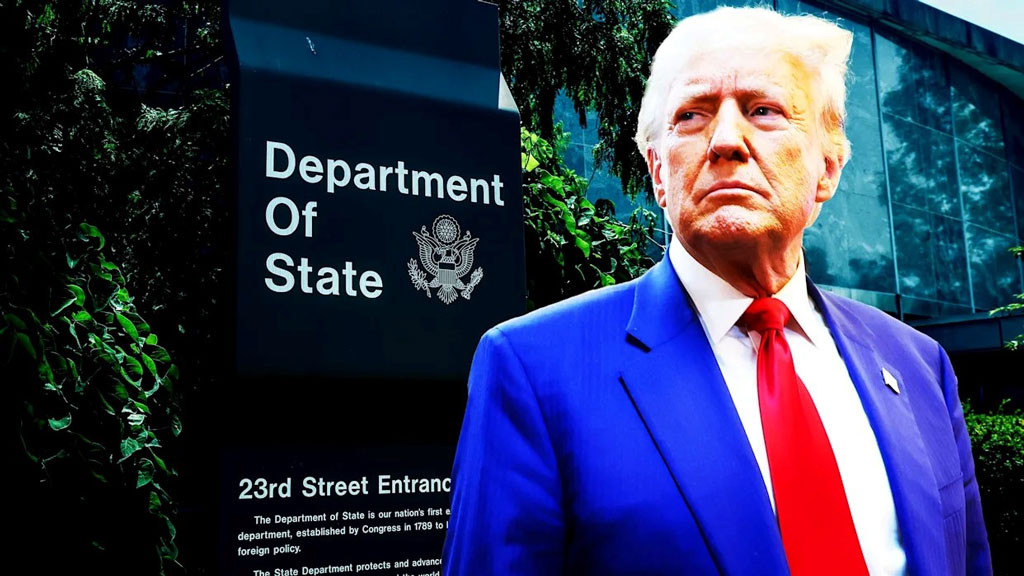
এবার ট্রাম্প প্রশাসন শুধু পূর্বের রিপাবলিকান ধারা অব্যাহতই রাখেনি, বরং নারীর অধিকার নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের দ্বিদলীয় নীতিকাঠামোই ভেঙে দিয়েছে। এর ফলে ছয় দশকেরও বেশি সময়ের নীতিনির্দেশনা উল্টে গেছে।
১৯ ঘণ্টা আগে
বিশ্লেষক ও কূটনীতিকদের মতে, এই সাফল্য টেকসই শান্তির পথে কত দূর এগোবে, তা নির্ভর করবে ট্রাম্প কতটা চাপ বজায় রাখতে পারেন তার ওপর। বিশেষ করে সেই নেতার ওপর, যাঁর সমর্থন তাঁর পরবর্তী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দরকার হবে। তিনি আর কেউ নন—ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু।
২ দিন আগে
গাজায় ইসরায়েলি যুদ্ধ বন্ধ, জিম্মি–বন্দিবিনিময় এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলটি পুনর্গঠনের লক্ষ্যে এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পসহ বিশ্বনেতারা। এর আগে হামাস এবং ইসরায়েল আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। কাতার, তুরস্ক, মিসর, পাকিস্তান, জর্ডানের নেতারাও এই চুক্তিতে...
২ দিন আগে
মাঝখানে কয়েক দিনের বিরতি দিয়ে টানা দুই বছরের ভয়াবহ যুদ্ধের পর এখন এক বিশাল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে গাজা। জাতিসংঘের সাম্প্রতিক স্যাটেলাইট চিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে—গাজা সিটির ৮৩ শতাংশ ভবনই ক্ষতিগ্রস্ত। সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে অন্তত ১৭ হাজার ৭০০টি ভবন।
৩ দিন আগে