আজকের পত্রিকা ডেস্ক

আরব দেশগুলোর ফিলিস্তিন ইস্যু নিয়ে আপাত-নীরবতা একটি জটিল এবং বহুমাত্রিক বিষয়। এর মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কৌশলগত এবং ঐতিহাসিক কারণ। স্বাধীন ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের দাবি এবং বাসিন্দাদের ওপর এই দীর্ঘ নিপীড়ন নিয়ে যে আরব দেশগুলো কিছুই করছে না, বা নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকছে—এই ধারণা পুরোপুরি সঠিক নয়। অনেক আরব দেশই ফিলিস্তিনকে প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়েছে অথবা কিছু পদক্ষেপও নিয়েছে।
তবে ফিলিস্তিন ইস্যুতে আরব দেশগুলোর সম্পৃক্ততার মাত্রা খুবই ভিন্ন। তাদের সম্পৃক্ততা বা পদক্ষেপগুলো, ফিলিস্তিনকেই আরবের কেন্দ্র বা শুধুই মুসলিম-ইহুদি ইস্যু হিসেবে যাঁরা দেখেন, তাঁদের প্রত্যাশার তুলনায় অনেক কমই। এর কারণগুলোর একটি ধারণাচিত্র দেওয়া হলো:
জাতীয় স্বার্থ এবং ভূরাজনৈতিক অগ্রাধিকার
অনেক আরব সরকার ফিলিস্তিন নিয়ে সাহসী অবস্থান নেওয়ার চেয়ে নিজেদের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। উদাহরণস্বরূপ, মিসর ও জর্ডানের মতো দেশ, যারা ইসরায়েলের সঙ্গে সীমান্ত রয়েছে এবং ১৯৭৯ ও ১৯৯৪ সালে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরকারী, তারা প্রায়ই এমন বক্তব্য বা পদক্ষেপ এড়িয়ে চলে, যা চুক্তিগুলোকে বিপন্ন করতে পারে। এই চুক্তিগুলো তাদের অর্থনৈতিক ও সামরিক সুবিধা দেয়। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হলো মার্কিন সাহায্য। দেশগুলো এই মার্কিন সহায়তার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। ইসরায়েলের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে জড়ালে এসব দেশের শাসকগোষ্ঠী অভ্যন্তরীণ অস্থিতিশীলতার মধ্যে পড়তে পারে, বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ; যেমন অর্থনৈতিক সংকট বা রাজনৈতিক অস্থিরতা এর মধ্যে অন্যতম।
ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ
সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, মরক্কো ও সুদানের মতো বেশ কয়েকটি আরব রাষ্ট্র ২০২০ সাল থেকে আব্রাহাম অ্যাকর্ডের মাধ্যমে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করেছে। এমনকি সৌদি আরবও এমন পদক্ষেপের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে। এই পরিবর্তন একটি কৌশলগত পুনর্বিন্যাসকেই প্রতিফলিত করে। যেখানে তারা ইরানের আঞ্চলিক প্রভাব নিয়ে উদ্বিগ্ন। এ ছাড়া অর্থনৈতিক সুযোগ (যেমন বাণিজ্য ও প্রযুক্তি) এবং মার্কিন কূটনৈতিক সমর্থনের ওপর তাদের নির্ভর করতে হয়। ফলে এই দেশগুলোর জন্য, ফিলিস্তিন নিয়ে কম কথা বলার কারণে যে রাজনৈতিক মূল্য দিতে হয়, তার চেয়ে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা বা গড়ে তোলার লাভ বেশি গুরুত্বপূর্ণ; বিশেষ করে যখন তারা মনে করে, ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান শিগগির সম্ভব নয়।
অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ
অনেক আরব দেশ গুরুতর অভ্যন্তরীণ সমস্যার সম্মুখীন। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, রাজনৈতিক অস্থিরতা বা গৃহযুদ্ধ তাদের কাছে অগ্রাধিকার পায়। উদাহরণস্বরূপ, ইয়েমেন, সিরিয়া ও লেবাননের মতো দেশগুলো চলমান যুদ্ধ বা অর্থনৈতিক সংকটের সঙ্গে লড়াই করছে। ফলে বাইরের ইস্যু, এমনকি ফিলিস্তিনের মতো আঞ্চলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার সামর্থ্য তাদের কম। এসব দেশের নেতারা ফিলিস্তিন নিয়ে জনগণের ক্ষোভ উসকে দেওয়া এড়িয়ে চলে; কারণ, তা দেশের ভেতরে শেষ পর্যন্ত সরকারবিরোধী মনোভাবকে আরও প্রবল করতে পারে।
বাস্তববাদিতা এবং ক্লান্তি
দশকের পর দশক যুদ্ধ (যেমন ১৯৪৮, ১৯৬৭, ১৯৭৩) এবং ব্যর্থ শান্তি উদ্যোগের পর কিছু আরব নেতা এবং জনগণ ফিলিস্তিনের সংগ্রাম নিয়ে ক্লান্ত। অথবা এই আন্দোলনকে হয়তো নিরর্থক বলেও বোধ হচ্ছে অনেকের। দীর্ঘ সংগ্রাম ও রক্তক্ষয়ের পর কোনো অগ্রগতি নেই—এই পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের অভ্যন্তরীণ বিভেদ এবং গাজায় হামাসের বিতর্কিত ভূমিকা। এসব কিছু মিলে আরব দেশগুলো সক্রিয় সম্পৃক্ততায় সম্ভবত তেমন আগ্রহ পাচ্ছে না। এর মানে এই নয় যে তারা উদাসীন, বরং তারা শুধু গলা চড়িয়ে সমর্থন দেওয়ার কোনো ব্যবহারিক ফলাফল দেখতে পাচ্ছে না।
পশ্চিমা শক্তির ওপর নির্ভরশীলতা
অনেক আরব রাষ্ট্র সামরিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সমর্থনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য পশ্চিমা দেশের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। যেহেতু মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের প্রধান মিত্র, তাই এই দেশগুলো দুই মিত্রের সমালোচনা থেকে সংযত থাকে, যাতে লাভজনক সম্পর্কগুলো বিপন্ন না হয়।
জনসমক্ষে নিন্দামন্দ করা হয়। যেমন আরব লিগের সম্মেলনে অনেক নেতাই কড়া কথা বলেন। কিন্তু এমন গলাবাজি পশ্চিমা প্রতিক্রিয়া ডেকে আনতে পারে, এমন সম্পর্ক ছিন্ন করা বা নিষেধাজ্ঞার মতো পদক্ষেপ পর্যন্ত গড়ায় না।
ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং আঞ্চলিক ভূরাজনীতি
ঐতিহাসিকভাবে, আরব দেশগুলো ফিলিস্তিন নিয়ে সব সময় ঐক্যবদ্ধ ছিল না। যদিও বিশ শতকের মাঝামাঝি ফিলিস্তিন নিয়ে তারা একটি সম্মেলনের ডাক দিয়েছিল। জর্ডানে ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর সংঘর্ষ (১৯৭০), যেখানে ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীগুলো জর্ডানের রাজতন্ত্রের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে, বা লেবাননের গৃহযুদ্ধ (১৯৭৫-৯০), যা আংশিকভাবে ফিলিস্তিনি মিলিশিয়াদের সম্পৃক্ততা ছিল। এসব অভিজ্ঞতা কিছু রাষ্ট্রকে ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীগুলোর ব্যাপারে সতর্ক করে তুলেছে। এসব ঘটনা একটি সতর্কতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছে, যেখানে দেশগুলো ইস্যুটিকে সরাসরি ডিল করার চেয়ে ‘নিয়ন্ত্রণে’ রাখতে পছন্দ করে।
জনগণ বনাম সরকারের বিভেদ
ফিলিস্তিন ইস্যুতে অনেক ক্ষেত্রে, নীরবতা সরকারি পর্যায়ে বেশি, জনগণের মধ্যে নয়। আরব নাগরিকেরা প্রায়ই বিক্ষোভ, সোশ্যাল মিডিয়া বা দাতব্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের প্রতি দৃঢ় সংহতি প্রকাশ করে। কিন্তু আরব বিশ্বের স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা এই কণ্ঠগুলোকে দমন করে বা সীমিত করে, যাতে উত্তেজনা না বাড়ে। উদাহরণস্বরূপ, এক্স পোস্টগুলোতে আরব জনগণ তাদের নেতাদের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করে। তারা শাসকদের ইসরায়েল বা যুক্তরাষ্ট্রকে সহযোগিতা বা তাদের ভীরুতার জন্য অভিযুক্ত করে। জনগণের এই মনোভাবগুলো সরকারি নীতিতে তেমন কোনো প্রভাব ফেলে না।
তবে ব্যতিক্রমও আছে। উদাহরণস্বরূপ, কাতার ও আলজেরিয়া ধারাবাহিকভাবে ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আসছে। কাতার গাজার পুনর্গঠনে অর্থায়ন করেছে এবং হামাস নেতাদের আশ্রয় দিয়েছে। ইয়েমেনের হুতিরা ইসরায়েল-সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে প্রতীকী সামরিক পদক্ষেপ নিয়েছে। এমনকি ইসরায়েলের সঙ্গে শান্তিচুক্তি সত্ত্বেও মিসর যুদ্ধবিরতি আলোচনায় মধ্যস্থতা করেছে এবং ২০২৫ সালের মার্চে আরব লিগ-সমর্থিত ৫৩ বিলিয়ন ডলারের পুনর্গঠন পরিকল্পনা প্রস্তাব করেছে।
ফিলিস্তিন ইস্যুতে আরব বিশ্বের ভূমিকা নিয়ে সংক্ষেপে বলা যায়, তারা সম্পূর্ণ ‘নীরব’ নয় বরং তাদের আপাত-নীরবতা অনেক আরব নেতার একটি হিসেবি অবস্থানকেই প্রতিফলিত করে। তারা মৌখিকভাবে ইসরায়েলের নিন্দা করতে পারে বা মানবিক সহায়তা পাঠাতে পারে, কিন্তু সম্পর্ক ছিন্ন করা বা সামরিক সমর্থনের মতো কঠোর পদক্ষেপ তাদের নিজস্ব কৌশলগত বাস্তবতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে বিবেচনা করে।
তাদের এই অবস্থান বিশ্বাসঘাতকতা, বাস্তববাদিতা, নাকি উভয়ের মিশ্রণ; তা নির্ভর করে ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। তবে এটা স্পষ্ট যে ফিলিস্তিন নিয়ে আরব দুনিয়ার একসময়ের ঐক্য সময়ের সঙ্গে দুর্বল হয়েছে বা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে।
লিখেছেন: জাহাঙ্গীর আলম, জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক, আজকের পত্রিকা

আরব দেশগুলোর ফিলিস্তিন ইস্যু নিয়ে আপাত-নীরবতা একটি জটিল এবং বহুমাত্রিক বিষয়। এর মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কৌশলগত এবং ঐতিহাসিক কারণ। স্বাধীন ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের দাবি এবং বাসিন্দাদের ওপর এই দীর্ঘ নিপীড়ন নিয়ে যে আরব দেশগুলো কিছুই করছে না, বা নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকছে—এই ধারণা পুরোপুরি সঠিক নয়। অনেক আরব দেশই ফিলিস্তিনকে প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়েছে অথবা কিছু পদক্ষেপও নিয়েছে।
তবে ফিলিস্তিন ইস্যুতে আরব দেশগুলোর সম্পৃক্ততার মাত্রা খুবই ভিন্ন। তাদের সম্পৃক্ততা বা পদক্ষেপগুলো, ফিলিস্তিনকেই আরবের কেন্দ্র বা শুধুই মুসলিম-ইহুদি ইস্যু হিসেবে যাঁরা দেখেন, তাঁদের প্রত্যাশার তুলনায় অনেক কমই। এর কারণগুলোর একটি ধারণাচিত্র দেওয়া হলো:
জাতীয় স্বার্থ এবং ভূরাজনৈতিক অগ্রাধিকার
অনেক আরব সরকার ফিলিস্তিন নিয়ে সাহসী অবস্থান নেওয়ার চেয়ে নিজেদের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। উদাহরণস্বরূপ, মিসর ও জর্ডানের মতো দেশ, যারা ইসরায়েলের সঙ্গে সীমান্ত রয়েছে এবং ১৯৭৯ ও ১৯৯৪ সালে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরকারী, তারা প্রায়ই এমন বক্তব্য বা পদক্ষেপ এড়িয়ে চলে, যা চুক্তিগুলোকে বিপন্ন করতে পারে। এই চুক্তিগুলো তাদের অর্থনৈতিক ও সামরিক সুবিধা দেয়। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হলো মার্কিন সাহায্য। দেশগুলো এই মার্কিন সহায়তার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। ইসরায়েলের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে জড়ালে এসব দেশের শাসকগোষ্ঠী অভ্যন্তরীণ অস্থিতিশীলতার মধ্যে পড়তে পারে, বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ; যেমন অর্থনৈতিক সংকট বা রাজনৈতিক অস্থিরতা এর মধ্যে অন্যতম।
ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ
সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, মরক্কো ও সুদানের মতো বেশ কয়েকটি আরব রাষ্ট্র ২০২০ সাল থেকে আব্রাহাম অ্যাকর্ডের মাধ্যমে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করেছে। এমনকি সৌদি আরবও এমন পদক্ষেপের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে। এই পরিবর্তন একটি কৌশলগত পুনর্বিন্যাসকেই প্রতিফলিত করে। যেখানে তারা ইরানের আঞ্চলিক প্রভাব নিয়ে উদ্বিগ্ন। এ ছাড়া অর্থনৈতিক সুযোগ (যেমন বাণিজ্য ও প্রযুক্তি) এবং মার্কিন কূটনৈতিক সমর্থনের ওপর তাদের নির্ভর করতে হয়। ফলে এই দেশগুলোর জন্য, ফিলিস্তিন নিয়ে কম কথা বলার কারণে যে রাজনৈতিক মূল্য দিতে হয়, তার চেয়ে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা বা গড়ে তোলার লাভ বেশি গুরুত্বপূর্ণ; বিশেষ করে যখন তারা মনে করে, ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান শিগগির সম্ভব নয়।
অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ
অনেক আরব দেশ গুরুতর অভ্যন্তরীণ সমস্যার সম্মুখীন। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, রাজনৈতিক অস্থিরতা বা গৃহযুদ্ধ তাদের কাছে অগ্রাধিকার পায়। উদাহরণস্বরূপ, ইয়েমেন, সিরিয়া ও লেবাননের মতো দেশগুলো চলমান যুদ্ধ বা অর্থনৈতিক সংকটের সঙ্গে লড়াই করছে। ফলে বাইরের ইস্যু, এমনকি ফিলিস্তিনের মতো আঞ্চলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার সামর্থ্য তাদের কম। এসব দেশের নেতারা ফিলিস্তিন নিয়ে জনগণের ক্ষোভ উসকে দেওয়া এড়িয়ে চলে; কারণ, তা দেশের ভেতরে শেষ পর্যন্ত সরকারবিরোধী মনোভাবকে আরও প্রবল করতে পারে।
বাস্তববাদিতা এবং ক্লান্তি
দশকের পর দশক যুদ্ধ (যেমন ১৯৪৮, ১৯৬৭, ১৯৭৩) এবং ব্যর্থ শান্তি উদ্যোগের পর কিছু আরব নেতা এবং জনগণ ফিলিস্তিনের সংগ্রাম নিয়ে ক্লান্ত। অথবা এই আন্দোলনকে হয়তো নিরর্থক বলেও বোধ হচ্ছে অনেকের। দীর্ঘ সংগ্রাম ও রক্তক্ষয়ের পর কোনো অগ্রগতি নেই—এই পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের অভ্যন্তরীণ বিভেদ এবং গাজায় হামাসের বিতর্কিত ভূমিকা। এসব কিছু মিলে আরব দেশগুলো সক্রিয় সম্পৃক্ততায় সম্ভবত তেমন আগ্রহ পাচ্ছে না। এর মানে এই নয় যে তারা উদাসীন, বরং তারা শুধু গলা চড়িয়ে সমর্থন দেওয়ার কোনো ব্যবহারিক ফলাফল দেখতে পাচ্ছে না।
পশ্চিমা শক্তির ওপর নির্ভরশীলতা
অনেক আরব রাষ্ট্র সামরিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সমর্থনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য পশ্চিমা দেশের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। যেহেতু মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের প্রধান মিত্র, তাই এই দেশগুলো দুই মিত্রের সমালোচনা থেকে সংযত থাকে, যাতে লাভজনক সম্পর্কগুলো বিপন্ন না হয়।
জনসমক্ষে নিন্দামন্দ করা হয়। যেমন আরব লিগের সম্মেলনে অনেক নেতাই কড়া কথা বলেন। কিন্তু এমন গলাবাজি পশ্চিমা প্রতিক্রিয়া ডেকে আনতে পারে, এমন সম্পর্ক ছিন্ন করা বা নিষেধাজ্ঞার মতো পদক্ষেপ পর্যন্ত গড়ায় না।
ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং আঞ্চলিক ভূরাজনীতি
ঐতিহাসিকভাবে, আরব দেশগুলো ফিলিস্তিন নিয়ে সব সময় ঐক্যবদ্ধ ছিল না। যদিও বিশ শতকের মাঝামাঝি ফিলিস্তিন নিয়ে তারা একটি সম্মেলনের ডাক দিয়েছিল। জর্ডানে ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর সংঘর্ষ (১৯৭০), যেখানে ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীগুলো জর্ডানের রাজতন্ত্রের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে, বা লেবাননের গৃহযুদ্ধ (১৯৭৫-৯০), যা আংশিকভাবে ফিলিস্তিনি মিলিশিয়াদের সম্পৃক্ততা ছিল। এসব অভিজ্ঞতা কিছু রাষ্ট্রকে ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীগুলোর ব্যাপারে সতর্ক করে তুলেছে। এসব ঘটনা একটি সতর্কতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছে, যেখানে দেশগুলো ইস্যুটিকে সরাসরি ডিল করার চেয়ে ‘নিয়ন্ত্রণে’ রাখতে পছন্দ করে।
জনগণ বনাম সরকারের বিভেদ
ফিলিস্তিন ইস্যুতে অনেক ক্ষেত্রে, নীরবতা সরকারি পর্যায়ে বেশি, জনগণের মধ্যে নয়। আরব নাগরিকেরা প্রায়ই বিক্ষোভ, সোশ্যাল মিডিয়া বা দাতব্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের প্রতি দৃঢ় সংহতি প্রকাশ করে। কিন্তু আরব বিশ্বের স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা এই কণ্ঠগুলোকে দমন করে বা সীমিত করে, যাতে উত্তেজনা না বাড়ে। উদাহরণস্বরূপ, এক্স পোস্টগুলোতে আরব জনগণ তাদের নেতাদের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করে। তারা শাসকদের ইসরায়েল বা যুক্তরাষ্ট্রকে সহযোগিতা বা তাদের ভীরুতার জন্য অভিযুক্ত করে। জনগণের এই মনোভাবগুলো সরকারি নীতিতে তেমন কোনো প্রভাব ফেলে না।
তবে ব্যতিক্রমও আছে। উদাহরণস্বরূপ, কাতার ও আলজেরিয়া ধারাবাহিকভাবে ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আসছে। কাতার গাজার পুনর্গঠনে অর্থায়ন করেছে এবং হামাস নেতাদের আশ্রয় দিয়েছে। ইয়েমেনের হুতিরা ইসরায়েল-সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে প্রতীকী সামরিক পদক্ষেপ নিয়েছে। এমনকি ইসরায়েলের সঙ্গে শান্তিচুক্তি সত্ত্বেও মিসর যুদ্ধবিরতি আলোচনায় মধ্যস্থতা করেছে এবং ২০২৫ সালের মার্চে আরব লিগ-সমর্থিত ৫৩ বিলিয়ন ডলারের পুনর্গঠন পরিকল্পনা প্রস্তাব করেছে।
ফিলিস্তিন ইস্যুতে আরব বিশ্বের ভূমিকা নিয়ে সংক্ষেপে বলা যায়, তারা সম্পূর্ণ ‘নীরব’ নয় বরং তাদের আপাত-নীরবতা অনেক আরব নেতার একটি হিসেবি অবস্থানকেই প্রতিফলিত করে। তারা মৌখিকভাবে ইসরায়েলের নিন্দা করতে পারে বা মানবিক সহায়তা পাঠাতে পারে, কিন্তু সম্পর্ক ছিন্ন করা বা সামরিক সমর্থনের মতো কঠোর পদক্ষেপ তাদের নিজস্ব কৌশলগত বাস্তবতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে বিবেচনা করে।
তাদের এই অবস্থান বিশ্বাসঘাতকতা, বাস্তববাদিতা, নাকি উভয়ের মিশ্রণ; তা নির্ভর করে ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। তবে এটা স্পষ্ট যে ফিলিস্তিন নিয়ে আরব দুনিয়ার একসময়ের ঐক্য সময়ের সঙ্গে দুর্বল হয়েছে বা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে।
লিখেছেন: জাহাঙ্গীর আলম, জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক, আজকের পত্রিকা

ভারতে আজকাল দিন শুরু হয় দুই ধরনের সংবাদ দিয়ে: একদিকে টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যায়—পাকিস্তানবিরোধী বিতর্ক, হিন্দুদের গৌরবগাথা আর নতুন ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা; অন্যদিকে অন্ধকার এক বাস্তবতা—প্রতিদিন কোথাও না কোথাও কোনো মুসলমান নিগৃহীত হচ্ছে, পিটিয়ে মারা হচ্ছে, মিথ্যা মামলায় বন্দী করা হচ্ছে, অথবা দেশদ্রোহী..
৪ ঘণ্টা আগে
ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি যেন উল্টোপাল্টা এক দাবার ছক, যেখানে পুরোনো মিত্ররা দূরে সরে যাচ্ছে, আর আগে যাদের ‘শত্রু’ ভাবা হতো, তারাই এখন হোয়াইট হাউসে জায়গা পাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে পাকিস্তান একেবারে আদর্শ উদাহরণ তৈরি করেছে।
১৮ ঘণ্টা আগে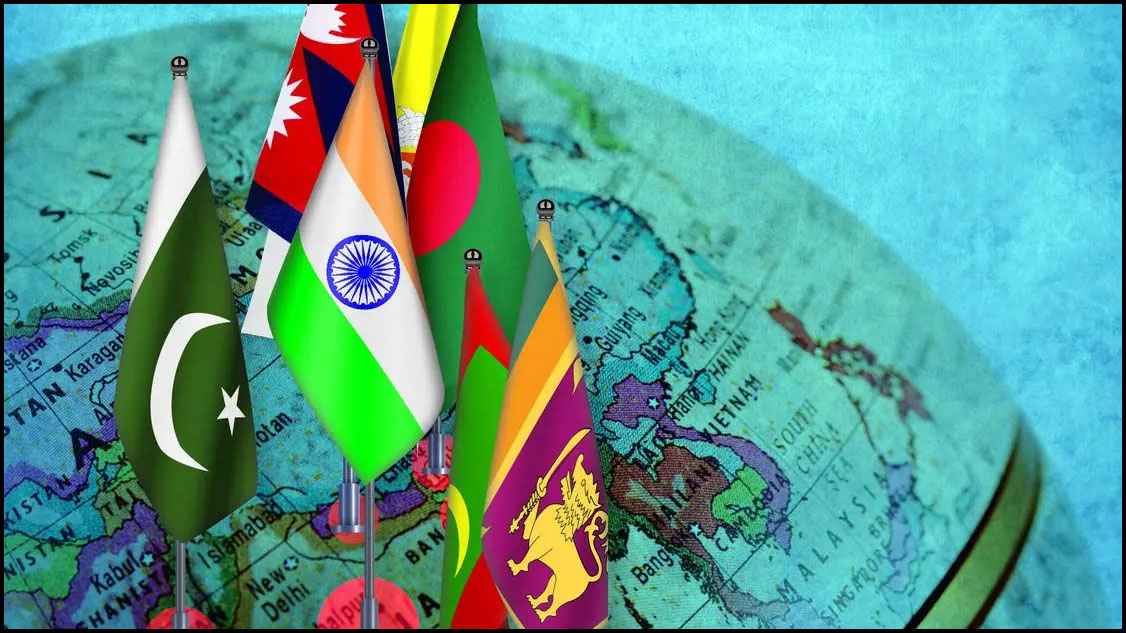
দক্ষিণ এশিয়া এখন সার্বভৌম ঋণ তথা সরকারের ঋণ ও রাজস্ব ঘাটতির ভারসাম্য রক্ষায় হিমশিম খাচ্ছে। স্থায়ী বাজেট ঘাটতির কারণে এ অঞ্চলের ঋণ বিশ্বের অন্যান্য উদীয়মান অর্থনীতির তুলনায় দ্রুত বেড়ে গেছে। ২০২৩ সালে সরকারগুলোর গড় ঋণের পরিমাণ পৌঁছেছে মোট জিডিপির ৭৭ শতাংশে।
১ দিন আগে
গাজায় বিধ্বংসী যুদ্ধের দুই বছর পর অবশেষে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে। কিন্তু শান্তির এই মুহূর্ত ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর জন্য আশীর্বাদ নয়, বরং নতুন ছয়টি বড় রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জের সূচনা বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।
৩ দিন আগে