সৈয়দা সাদিয়া শাহরীন

গটফ্রিড আইজনার ছিলেন স্কুলশিক্ষক। তাঁর স্ত্রী জোসেফিন ভিতাল ছিলেন সেই সময়ের উচ্চশিক্ষিত একজন নারী। জার্মানির একটি মধ্যবিত্ত পরিবার তাঁদের। নিজেদের সন্তানদের সুশিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলাই হয়তো ছিল তাঁদের লক্ষ্য। তাঁদের বড় সন্তান ক্লারা জন্মেছিলেন ১৮৫৭ সালে। তখন হয়তো ক্লারার বাবা-মা বুঝতেই পারেননি তিন সন্তানের মধ্যে মেয়ে ক্লারা ইতিহাসে নাম লেখাতে যাচ্ছে! কীভাবে? সে গল্পই তো বলছি।
ক্লারা জোসেফিন আইজনার জার্মানির লাইপ্ৎসিশ টিচারস কলেজ ফর উইমেন থেকে পড়াশোনা করেন। স্বাধীনচেতা বাবা-মা চেষ্টা করেছিলেন সন্তানদের সেরা পাঠদান করতে। ক্লারা তাঁদের চেষ্টা বৃথা যেতে দেননি। প্রশিক্ষণ নিয়ে শুরু করেছিলেন শিক্ষকজীবন। স্কুলজীবন থেকেই নারী শিক্ষা নিয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন। নারী ও পুরুষের সমান অধিকারে বিশ্বাস করতেন। বিশ্বাস করতেন নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে। ১৮৭৮ সালে যোগদান করে কাজ করছিলেন সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির হয়ে।
বিসমার্কের সমাজতন্ত্র বিরোধী আইনের খপ্পরে পড়ে ১৮৮২ সালে তাঁকে চলে যেতে হয় ফ্রান্সের প্যারিসে। কারণ, জার্মানিতে তখন কোনো সামাজিক কর্মকাণ্ড করা বারণ। প্যারিসে গিয়ে তাঁর পরিচয় হয় রুশ বিপ্লবী ওসিপ জেটকিনের সঙ্গে। প্রেমে পড়ে যান একে অপরের। ক্লারার আরেক নাম হয়ে যায় ক্লারা জেটকিন। বিয়ে করেছিলেন তাঁরা। তাঁদের ছিল দুই ছেলে, ম্যাক্সিম, আর কস্তিয়া। ক্লারা দিনের বেলায় ছেলেদের দেখাশোনা করতেন, আর রাতের বেলা করতেন লেখালেখির কাজ। কাজ করেছেন অনুবাদক হিসেবেও।
১৮৮৯ সালে ওসিপ খুব অসুস্থ হয়ে মারা যান। ১৮৯০ সালে ছেলেদের নিয়ে ক্লারা আবার চলে যান জার্মানিতে। বিয়ে করেন চিত্রশিল্পী গিয়োর্গ ফ্রিডরিচ জুন্ডেলকে। সেখানে ক্লারা সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক প্রেসে কাজও পান।
ওসিপ জেটকিনের সঙ্গে থাকার সময়েই তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। মূলত ওসিপের প্রেরণাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ, মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেছিলেন। তখন থেকেই নারী স্বাধীনতা ও অধিকার নিয়ে দাবি তুলতে থাকেন মার্কসবাদী ক্লারা। টানা ২৫ বছর তিনি ছিলেন জার্মানির সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির নারীদের জন্য প্রকাশিত পত্রিকা ডি গ্লাইচাইটের সম্পাদক।
শুধু নারী মুক্তি আন্দোলন নয়, শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি। ১৮৯৮ সালের দিকে রোজা লুক্সেমবার্গের সঙ্গে খুব ভালো বন্ধুত্ব হয় ক্লারার। নারী আন্দোলনে ক্লারার সঙ্গে রোজার অবদানও অনস্বীকার্য। বিপ্লবী ক্লারা ছিলেন কট্টর মার্কসবাদী, আন্তর্জাতিকতাবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। তিনি বিশ্বাস করতেন সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমজীবী শ্রেণির মুক্তি মিললেই মিলবে নারী মুক্তি। তাঁর চোখে লৈঙ্গিক বৈষম্য ছিল অর্থনৈতিক শোষণের পরিণতি। তিনি তাঁর সাংবাদিকতার মাধ্যমে নারীবাদকে বিকশিত করেছিলেন। নিয়মানুবর্তিতা এবং নেতৃত্বদানে তিনি রুশ বিপ্লবী নেতা লেলিনকে তাঁর গুরু মানতেন। তাঁদের মধ্যে ছিল বেশ ভালো বন্ধুত্ব।
যা হোক, ক্লারা ইতিহাসে নাম লেখানো শুরু করছিলেন এভাবেই। তবে তাঁকে বিশেষভাবে মনে রাখতে হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস প্রচলনের প্রস্তাবক হিসেবে। ১৯০৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি নিউইয়র্কের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট নারী সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজিত নারী সমাবেশে জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন হয়।
এর পর ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন। ১৭টি দেশ থেকে ১০০ জন নারী প্রতিনিধি এতে যোগ দিয়েছিলেন সম-অধিকার আদায়ের লক্ষ্য নিয়ে। সেখানেই ক্লারা আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের প্রস্তাব দেন। পরের বছর ১৯১১ সালের ১৯ মার্চ অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, জার্মানি এবং সুইজারল্যান্ডে নারী দিবস পালন করা হয় প্রথমবারের মতো। ইউরোপজুড়ে নারীরা সম-অধিকার, লৈঙ্গিক সমতা ও ভোটাধিকারের পক্ষে দাবি জানায়।
শুরুর দিকে কোনো নির্দিষ্ট তারিখ ছিল না। অনেক দেশ ফেব্রুয়ারির শেষে কিংবা মার্চের শুরুতে পালন করত নারী দিবস। যেমন, আমেরিকায় জাতীয় নারী দিবস পালন করা হতো ফেব্রুয়ারির শেষ রোববারে। আবার রাশিয়া প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করে ১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ শনিবারে। তারিখটি অবশ্য জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ছিল। গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে তা ৮ মার্চ।
১৯১৪ সাল থেকে বেশ কয়েকটি দেশে ৮ মার্চ পালিত হতে লাগল নারী দিবস। পরে ১৯৭৫ সালে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদান করে দিবসটি পালনের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রকে আহ্বান জানায় জাতিসংঘ। তার পর থেকে সারা পৃথিবীতেই পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস। একেক বছর একেক রকম প্রতিপাদ্য থাকলেও দিনটি বারবার নারীর সম-অধিকার আদায় ও লৈঙ্গিক সমতার কথাই বলে যায়। আর সে কথা বলার জন্য যে ক্লারা জেটকিনই প্রশ্রয় দিয়েছেন, তা বোধ হয় অনস্বীকার্য। আর তাঁকে হয়তো প্রশ্রয় দিয়েছিল তাঁর বাবা-মা, ওসিপ কিংবা রোজার সঙ্গ।
১৯৩৩ সালে ক্লারার মৃত্যুর পর তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান লিখেছিল, ‘গ্র্যান্ডমাদার অব জার্মান কমিউনিজম’, অর্থাৎ ‘জার্মান সাম্যবাদের মাতামহী’! তাঁকে নারী দিবসের জননী বললে কি খুব ভুল হবে?
সূত্র: ইন্টারন্যাশনাল এনসাইক্লোপিডিয়া অব দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার, ব্রিটানিকা, এনসাইক্লোপিডিয়া
লেখক: সহসম্পাদক, আজকের পত্রিকা

গটফ্রিড আইজনার ছিলেন স্কুলশিক্ষক। তাঁর স্ত্রী জোসেফিন ভিতাল ছিলেন সেই সময়ের উচ্চশিক্ষিত একজন নারী। জার্মানির একটি মধ্যবিত্ত পরিবার তাঁদের। নিজেদের সন্তানদের সুশিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলাই হয়তো ছিল তাঁদের লক্ষ্য। তাঁদের বড় সন্তান ক্লারা জন্মেছিলেন ১৮৫৭ সালে। তখন হয়তো ক্লারার বাবা-মা বুঝতেই পারেননি তিন সন্তানের মধ্যে মেয়ে ক্লারা ইতিহাসে নাম লেখাতে যাচ্ছে! কীভাবে? সে গল্পই তো বলছি।
ক্লারা জোসেফিন আইজনার জার্মানির লাইপ্ৎসিশ টিচারস কলেজ ফর উইমেন থেকে পড়াশোনা করেন। স্বাধীনচেতা বাবা-মা চেষ্টা করেছিলেন সন্তানদের সেরা পাঠদান করতে। ক্লারা তাঁদের চেষ্টা বৃথা যেতে দেননি। প্রশিক্ষণ নিয়ে শুরু করেছিলেন শিক্ষকজীবন। স্কুলজীবন থেকেই নারী শিক্ষা নিয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন। নারী ও পুরুষের সমান অধিকারে বিশ্বাস করতেন। বিশ্বাস করতেন নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে। ১৮৭৮ সালে যোগদান করে কাজ করছিলেন সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির হয়ে।
বিসমার্কের সমাজতন্ত্র বিরোধী আইনের খপ্পরে পড়ে ১৮৮২ সালে তাঁকে চলে যেতে হয় ফ্রান্সের প্যারিসে। কারণ, জার্মানিতে তখন কোনো সামাজিক কর্মকাণ্ড করা বারণ। প্যারিসে গিয়ে তাঁর পরিচয় হয় রুশ বিপ্লবী ওসিপ জেটকিনের সঙ্গে। প্রেমে পড়ে যান একে অপরের। ক্লারার আরেক নাম হয়ে যায় ক্লারা জেটকিন। বিয়ে করেছিলেন তাঁরা। তাঁদের ছিল দুই ছেলে, ম্যাক্সিম, আর কস্তিয়া। ক্লারা দিনের বেলায় ছেলেদের দেখাশোনা করতেন, আর রাতের বেলা করতেন লেখালেখির কাজ। কাজ করেছেন অনুবাদক হিসেবেও।
১৮৮৯ সালে ওসিপ খুব অসুস্থ হয়ে মারা যান। ১৮৯০ সালে ছেলেদের নিয়ে ক্লারা আবার চলে যান জার্মানিতে। বিয়ে করেন চিত্রশিল্পী গিয়োর্গ ফ্রিডরিচ জুন্ডেলকে। সেখানে ক্লারা সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক প্রেসে কাজও পান।
ওসিপ জেটকিনের সঙ্গে থাকার সময়েই তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। মূলত ওসিপের প্রেরণাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ, মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেছিলেন। তখন থেকেই নারী স্বাধীনতা ও অধিকার নিয়ে দাবি তুলতে থাকেন মার্কসবাদী ক্লারা। টানা ২৫ বছর তিনি ছিলেন জার্মানির সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির নারীদের জন্য প্রকাশিত পত্রিকা ডি গ্লাইচাইটের সম্পাদক।
শুধু নারী মুক্তি আন্দোলন নয়, শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি। ১৮৯৮ সালের দিকে রোজা লুক্সেমবার্গের সঙ্গে খুব ভালো বন্ধুত্ব হয় ক্লারার। নারী আন্দোলনে ক্লারার সঙ্গে রোজার অবদানও অনস্বীকার্য। বিপ্লবী ক্লারা ছিলেন কট্টর মার্কসবাদী, আন্তর্জাতিকতাবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। তিনি বিশ্বাস করতেন সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমজীবী শ্রেণির মুক্তি মিললেই মিলবে নারী মুক্তি। তাঁর চোখে লৈঙ্গিক বৈষম্য ছিল অর্থনৈতিক শোষণের পরিণতি। তিনি তাঁর সাংবাদিকতার মাধ্যমে নারীবাদকে বিকশিত করেছিলেন। নিয়মানুবর্তিতা এবং নেতৃত্বদানে তিনি রুশ বিপ্লবী নেতা লেলিনকে তাঁর গুরু মানতেন। তাঁদের মধ্যে ছিল বেশ ভালো বন্ধুত্ব।
যা হোক, ক্লারা ইতিহাসে নাম লেখানো শুরু করছিলেন এভাবেই। তবে তাঁকে বিশেষভাবে মনে রাখতে হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস প্রচলনের প্রস্তাবক হিসেবে। ১৯০৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি নিউইয়র্কের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট নারী সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজিত নারী সমাবেশে জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন হয়।
এর পর ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন। ১৭টি দেশ থেকে ১০০ জন নারী প্রতিনিধি এতে যোগ দিয়েছিলেন সম-অধিকার আদায়ের লক্ষ্য নিয়ে। সেখানেই ক্লারা আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের প্রস্তাব দেন। পরের বছর ১৯১১ সালের ১৯ মার্চ অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, জার্মানি এবং সুইজারল্যান্ডে নারী দিবস পালন করা হয় প্রথমবারের মতো। ইউরোপজুড়ে নারীরা সম-অধিকার, লৈঙ্গিক সমতা ও ভোটাধিকারের পক্ষে দাবি জানায়।
শুরুর দিকে কোনো নির্দিষ্ট তারিখ ছিল না। অনেক দেশ ফেব্রুয়ারির শেষে কিংবা মার্চের শুরুতে পালন করত নারী দিবস। যেমন, আমেরিকায় জাতীয় নারী দিবস পালন করা হতো ফেব্রুয়ারির শেষ রোববারে। আবার রাশিয়া প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করে ১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ শনিবারে। তারিখটি অবশ্য জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ছিল। গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে তা ৮ মার্চ।
১৯১৪ সাল থেকে বেশ কয়েকটি দেশে ৮ মার্চ পালিত হতে লাগল নারী দিবস। পরে ১৯৭৫ সালে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদান করে দিবসটি পালনের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রকে আহ্বান জানায় জাতিসংঘ। তার পর থেকে সারা পৃথিবীতেই পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস। একেক বছর একেক রকম প্রতিপাদ্য থাকলেও দিনটি বারবার নারীর সম-অধিকার আদায় ও লৈঙ্গিক সমতার কথাই বলে যায়। আর সে কথা বলার জন্য যে ক্লারা জেটকিনই প্রশ্রয় দিয়েছেন, তা বোধ হয় অনস্বীকার্য। আর তাঁকে হয়তো প্রশ্রয় দিয়েছিল তাঁর বাবা-মা, ওসিপ কিংবা রোজার সঙ্গ।
১৯৩৩ সালে ক্লারার মৃত্যুর পর তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান লিখেছিল, ‘গ্র্যান্ডমাদার অব জার্মান কমিউনিজম’, অর্থাৎ ‘জার্মান সাম্যবাদের মাতামহী’! তাঁকে নারী দিবসের জননী বললে কি খুব ভুল হবে?
সূত্র: ইন্টারন্যাশনাল এনসাইক্লোপিডিয়া অব দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার, ব্রিটানিকা, এনসাইক্লোপিডিয়া
লেখক: সহসম্পাদক, আজকের পত্রিকা

এখন নাকি বানর আর শূকরের পালকেই দেখা যায় লাউয়াছড়ায়। বিরল প্রজাতির অনেক পাখি ও প্রাণী বাস করত এই সংরক্ষিত বনে। কিন্তু সেসব লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বনটিকে নিজেদের অভয়ারণ্য বলে হয়তো ভাবতে পারছে না তারা।
৬ ঘণ্টা আগে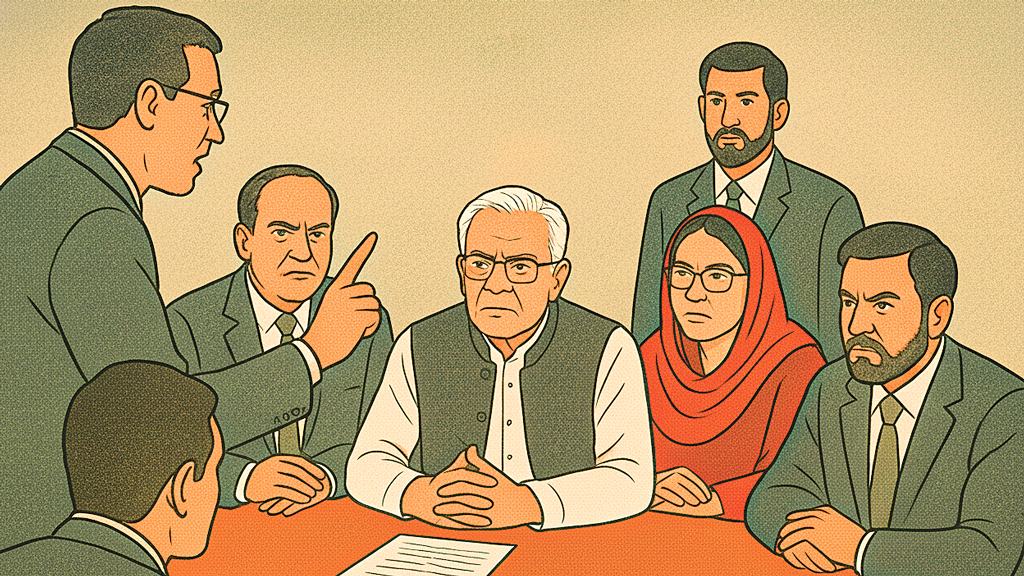
বিভাজন যেখানে ঘরে ঘরে, জনে জনে, সেখানে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া যথেষ্ট সাহসের কাজই বটে। অন্তর্বর্তী সরকার সেই সাহস দেখিয়েছিল। দেশি-প্রবাসী-বিদেশি একদল প্রাজ্ঞজনের সমন্বয়ে গঠন করেছিল জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। যদিও কমিশনের সভাপতি হিসেবে এর স্টিয়ারিং হুইল ছিল প্রধান উপদেষ্টা...
৬ ঘণ্টা আগে
মানুষের জীবনের শেষ অধ্যায় হলো অদৃশ্য বার্ধক্যের যাত্রা। কিন্তু সবাই বার্ধক্যের জীবনে সমান মর্যাদা পায় না। সমাজের প্রান্তিক এক শ্রেণি হলো যৌনকর্মীরা। যখন তাঁরা শেষ বয়সে পৌঁছান, তখন তাঁরা এক অনিশ্চিত জীবনের মধ্যে পড়ে যায়। যৌবনে যাঁদের দেহই ছিল আয়ের একমাত্র মূলধন, বার্ধক্যে এসে সেই দেহই যেন হয়ে...
৬ ঘণ্টা আগে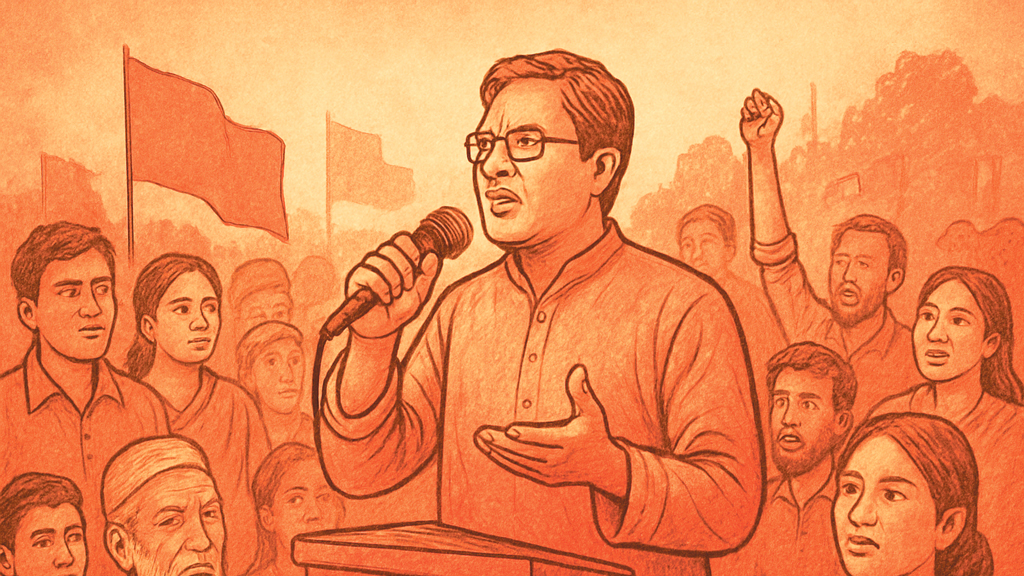
১৯৪৭-এর দেশভাগ থেকে শুরু করে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ—এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় জনগণই ছিল রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। তৎকালীন নেতারা কথা বলতেন জনগণের ভাষায় এবং তাঁদের দুঃখ, ক্ষোভ ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতেন রাজনীতিতে। কিন্তু স্বাধীনতার পরপরই অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে সামরিক শাসন...
৬ ঘণ্টা আগেসম্পাদকীয়

এখন নাকি বানর আর শূকরের পালকেই দেখা যায় লাউয়াছড়ায়। বিরল প্রজাতির অনেক পাখি ও প্রাণী বাস করত এই সংরক্ষিত বনে। কিন্তু সেসব লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বনটিকে নিজেদের অভয়ারণ্য বলে হয়তো ভাবতে পারছে না তারা।
পর্যটন এই জীববৈচিত্র্যকে ম্লান করে দেওয়ার একটি কারণ বলে মনে করছেন অনেকে। লাউয়াছড়া বনের অভ্যন্তরের অনেকটা পথে গাড়ি ঢুকতে পারে। বনের মধ্যে গাড়ি চলছে—এটা কোনো সুসংবাদ হতে পারে না। গাড়ি প্রবেশে নিশ্চয়ই কর্তৃপক্ষের অনুমতি লাগে। কীভাবে এই গাড়িওয়ালারা অনুমতি নিয়ে লাউয়াছড়ায় প্রবেশ করেন, তা জানা প্রয়োজন।
মৌলভীবাজারে অবস্থিত লাউয়াছড়াকে জাতীয় উদ্যান বলা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু জাতীয় উদ্যান হিসেবে বেঁচে থাকার কোনো ব্যবস্থাই রাখা হয়নি। আজকের পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, ২০১৪ সালের একটি জরিপে লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে ৪৬০ প্রজাতির দুর্লভ উদ্ভিদ ও প্রাণী থাকার কথা। এর মধ্যে ১৬৭ প্রজাতির উদ্ভিদ, ৪ প্রজাতির উভচর, ৬ প্রজাতির সরীসৃপ, ২৪৬ প্রজাতির পাখি ও ২০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী ছিল। কিন্তু এখন এত ধরনের উদ্ভিদ, পাখি ও প্রাণী কেন দেখা যায় না, সে প্রশ্ন তো তুলতেই হবে। যাঁদের ওপর এদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার, তাঁরা আদতে কী করছেন, তা জানতে হবে না?
তবে এ ব্যাপারে বন বিভাগ একটি খাঁটি কথা বলেছে। তাদের মতে, অতিরিক্ত পর্যটকের হট্টগোল, গাড়ি ও ট্রেনের আওয়াজ এবং জনসংখ্যা বাড়ার কারণে প্রাণীরা লোকালয় থেকে একটু দূরে চলে যায়। এসব কারণে প্রাণী কম দেখা যায় বনে। এ ছাড়া পর্যটন আর বনের প্রাকৃতিক পরিবেশ একসঙ্গে রক্ষা করা কঠিন।
শেষ কথাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ‘পর্যটন আর বনের প্রাকৃতিক পরিবেশ একসঙ্গে রক্ষা করা কঠিন।’ এ তো খুবই সত্যভাষণ। যদি সেটাই সত্য হয়ে থাকে, তাহলে এই বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে তারা ব্যবস্থা নেয় না কেন? এই বনের ঘনত্বের কারণে একসময় বনের ভেতর সূর্যের আলো সরাসরি পড়ত না। সেই ঘনত্ব কমে গেল কেন? কেন বনের সর্বত্র মানুষ অবাধে ঢুকে পড়ছে? বন বিভাগ কি জানে না, পশুর চারণক্ষেত্রে মানুষের অবাধ আনাগোনা পশু-পাখির জন্য স্বস্তিদায়ক নয়? আরও ভয়ংকর ব্যাপার হলো, এই বনে প্রাণীদের খাদ্যসংকট। পর্যাপ্ত খাদ্য না থাকলে এই বনে পশু-পাখি কেন থাকবে? পশুদের জীবনের বারোটা বাজিয়ে দেওয়ার জন্য চা-বাগানের কীটনাশক মেশানো পানিও অনেকটা দায়ী, যার কারণে ছড়ায় পানি খেতে আসা প্রাণীরা মারা পড়ে।
লাউয়াছড়ার জীববৈচিত্র্য ফিরিয়ে আনার জন্য কোনো বাড়তি পদক্ষেপের প্রয়োজন নেই। যে কারণে বনের এই দুর্দশা, তার প্রতিটির সমাধান করার উপায় বন বিভাগের জানা আছে। সেগুলো মেনে চললে লাউয়াছড়ায় বসবাসকারী পশু-পাখি ও উদ্ভিদ বেঁচে থাকতে পারবে। একই সঙ্গে প্রকৃতিকে বাঁচানো এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা সম্ভব যদি আন্তরিকতা থাকে। সরকারি কাজে সে রকম আন্তরিকতা কি একেবারেই দুর্লভ হয়ে গেছে? না হয়ে থাকলে তার প্রমাণ দেওয়া হোক।

এখন নাকি বানর আর শূকরের পালকেই দেখা যায় লাউয়াছড়ায়। বিরল প্রজাতির অনেক পাখি ও প্রাণী বাস করত এই সংরক্ষিত বনে। কিন্তু সেসব লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বনটিকে নিজেদের অভয়ারণ্য বলে হয়তো ভাবতে পারছে না তারা।
পর্যটন এই জীববৈচিত্র্যকে ম্লান করে দেওয়ার একটি কারণ বলে মনে করছেন অনেকে। লাউয়াছড়া বনের অভ্যন্তরের অনেকটা পথে গাড়ি ঢুকতে পারে। বনের মধ্যে গাড়ি চলছে—এটা কোনো সুসংবাদ হতে পারে না। গাড়ি প্রবেশে নিশ্চয়ই কর্তৃপক্ষের অনুমতি লাগে। কীভাবে এই গাড়িওয়ালারা অনুমতি নিয়ে লাউয়াছড়ায় প্রবেশ করেন, তা জানা প্রয়োজন।
মৌলভীবাজারে অবস্থিত লাউয়াছড়াকে জাতীয় উদ্যান বলা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু জাতীয় উদ্যান হিসেবে বেঁচে থাকার কোনো ব্যবস্থাই রাখা হয়নি। আজকের পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, ২০১৪ সালের একটি জরিপে লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে ৪৬০ প্রজাতির দুর্লভ উদ্ভিদ ও প্রাণী থাকার কথা। এর মধ্যে ১৬৭ প্রজাতির উদ্ভিদ, ৪ প্রজাতির উভচর, ৬ প্রজাতির সরীসৃপ, ২৪৬ প্রজাতির পাখি ও ২০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী ছিল। কিন্তু এখন এত ধরনের উদ্ভিদ, পাখি ও প্রাণী কেন দেখা যায় না, সে প্রশ্ন তো তুলতেই হবে। যাঁদের ওপর এদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার, তাঁরা আদতে কী করছেন, তা জানতে হবে না?
তবে এ ব্যাপারে বন বিভাগ একটি খাঁটি কথা বলেছে। তাদের মতে, অতিরিক্ত পর্যটকের হট্টগোল, গাড়ি ও ট্রেনের আওয়াজ এবং জনসংখ্যা বাড়ার কারণে প্রাণীরা লোকালয় থেকে একটু দূরে চলে যায়। এসব কারণে প্রাণী কম দেখা যায় বনে। এ ছাড়া পর্যটন আর বনের প্রাকৃতিক পরিবেশ একসঙ্গে রক্ষা করা কঠিন।
শেষ কথাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ‘পর্যটন আর বনের প্রাকৃতিক পরিবেশ একসঙ্গে রক্ষা করা কঠিন।’ এ তো খুবই সত্যভাষণ। যদি সেটাই সত্য হয়ে থাকে, তাহলে এই বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে তারা ব্যবস্থা নেয় না কেন? এই বনের ঘনত্বের কারণে একসময় বনের ভেতর সূর্যের আলো সরাসরি পড়ত না। সেই ঘনত্ব কমে গেল কেন? কেন বনের সর্বত্র মানুষ অবাধে ঢুকে পড়ছে? বন বিভাগ কি জানে না, পশুর চারণক্ষেত্রে মানুষের অবাধ আনাগোনা পশু-পাখির জন্য স্বস্তিদায়ক নয়? আরও ভয়ংকর ব্যাপার হলো, এই বনে প্রাণীদের খাদ্যসংকট। পর্যাপ্ত খাদ্য না থাকলে এই বনে পশু-পাখি কেন থাকবে? পশুদের জীবনের বারোটা বাজিয়ে দেওয়ার জন্য চা-বাগানের কীটনাশক মেশানো পানিও অনেকটা দায়ী, যার কারণে ছড়ায় পানি খেতে আসা প্রাণীরা মারা পড়ে।
লাউয়াছড়ার জীববৈচিত্র্য ফিরিয়ে আনার জন্য কোনো বাড়তি পদক্ষেপের প্রয়োজন নেই। যে কারণে বনের এই দুর্দশা, তার প্রতিটির সমাধান করার উপায় বন বিভাগের জানা আছে। সেগুলো মেনে চললে লাউয়াছড়ায় বসবাসকারী পশু-পাখি ও উদ্ভিদ বেঁচে থাকতে পারবে। একই সঙ্গে প্রকৃতিকে বাঁচানো এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা সম্ভব যদি আন্তরিকতা থাকে। সরকারি কাজে সে রকম আন্তরিকতা কি একেবারেই দুর্লভ হয়ে গেছে? না হয়ে থাকলে তার প্রমাণ দেওয়া হোক।

১৯৩৩ সালে ক্লারা জেটকিনের মৃত্যুর পর তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান লিখেছিল, ‘গ্র্যান্ডমাদার অব জার্মান কমিউনিজম’, অর্থাৎ ‘জার্মান সাম্যবাদের মাতামহ’! তাঁকে নারী দিবসের জননী বললে কি খুব ভুল হবে?
০৮ মার্চ ২০২২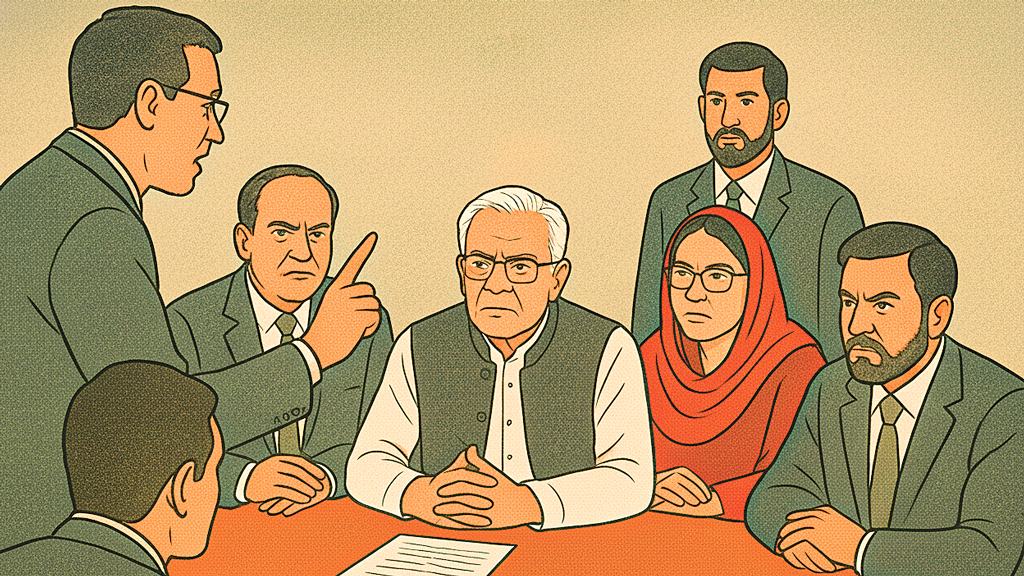
বিভাজন যেখানে ঘরে ঘরে, জনে জনে, সেখানে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া যথেষ্ট সাহসের কাজই বটে। অন্তর্বর্তী সরকার সেই সাহস দেখিয়েছিল। দেশি-প্রবাসী-বিদেশি একদল প্রাজ্ঞজনের সমন্বয়ে গঠন করেছিল জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। যদিও কমিশনের সভাপতি হিসেবে এর স্টিয়ারিং হুইল ছিল প্রধান উপদেষ্টা...
৬ ঘণ্টা আগে
মানুষের জীবনের শেষ অধ্যায় হলো অদৃশ্য বার্ধক্যের যাত্রা। কিন্তু সবাই বার্ধক্যের জীবনে সমান মর্যাদা পায় না। সমাজের প্রান্তিক এক শ্রেণি হলো যৌনকর্মীরা। যখন তাঁরা শেষ বয়সে পৌঁছান, তখন তাঁরা এক অনিশ্চিত জীবনের মধ্যে পড়ে যায়। যৌবনে যাঁদের দেহই ছিল আয়ের একমাত্র মূলধন, বার্ধক্যে এসে সেই দেহই যেন হয়ে...
৬ ঘণ্টা আগে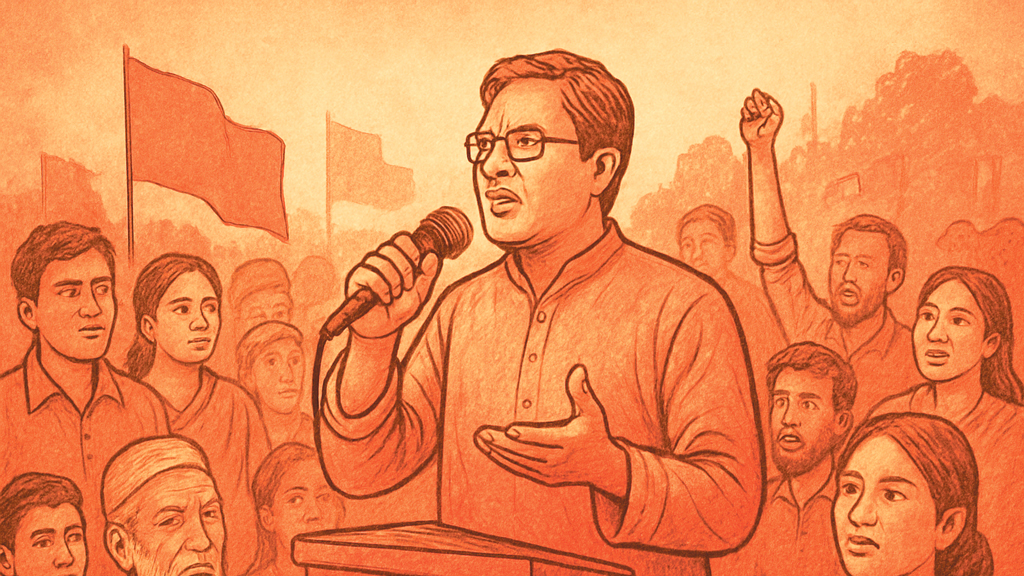
১৯৪৭-এর দেশভাগ থেকে শুরু করে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ—এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় জনগণই ছিল রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। তৎকালীন নেতারা কথা বলতেন জনগণের ভাষায় এবং তাঁদের দুঃখ, ক্ষোভ ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতেন রাজনীতিতে। কিন্তু স্বাধীনতার পরপরই অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে সামরিক শাসন...
৬ ঘণ্টা আগেঅরুণ কর্মকার
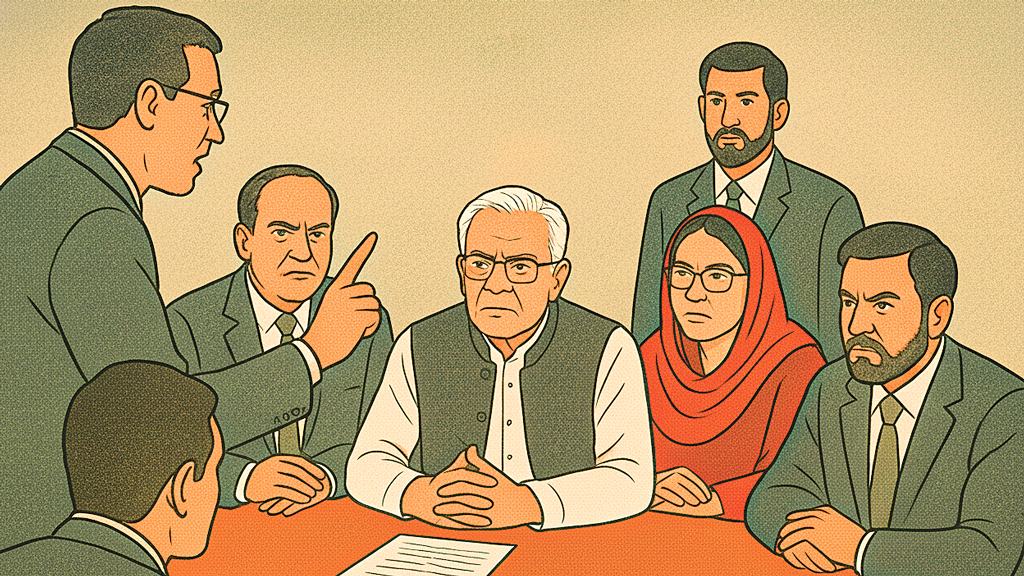
বিভাজন যেখানে ঘরে ঘরে, জনে জনে, সেখানে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া যথেষ্ট সাহসের কাজই বটে। অন্তর্বর্তী সরকার সেই সাহস দেখিয়েছিল। দেশি-প্রবাসী-বিদেশি একদল প্রাজ্ঞজনের সমন্বয়ে গঠন করেছিল জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। যদিও কমিশনের সভাপতি হিসেবে এর স্টিয়ারিং হুইল ছিল প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের হাতেই। কিন্তু বাস্তব কর্মক্ষেত্রে দীর্ঘ ২৭০ দিন ধরে ৩০টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সমন্বয় করেছেন সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের নেতৃত্বে কমিশনের অন্য সদস্যরা। জাতীয় ঐক্য গড়ার জন্য যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা প্রয়োজন, তার সবই হয়তো এই সদস্যদের ছিল বা আছে। কিন্তু তাঁদের অধ্যবসায়ে কিছু একটার যে অভাব ছিল, তা এখন স্পষ্ট। না হলে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের সুপারিশসহ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করে প্রধান উপদেষ্টার কাছে উপস্থাপন করার সঙ্গে সঙ্গে বিভেদ-বিভাজন ও অনৈক্যের আগুনে একেবারে ঘি পড়ার মতো অবস্থা হলো কেন? এ কথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে কমিশনের সভাপতি তথা প্রধান উপদেষ্টার অজ্ঞাতসারে কিংবা অনুমোদন ছাড়া এই প্রতিবেদন চূড়ান্ত হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে তিনি যেমন প্রতিবেদন গ্রহণ করেছেন, তেমনি কমিশনের সভাপতি হিসেবে ওই প্রতিবেদনে স্বাক্ষরও করেছেন।
তাহলে সবাই তো ছিলেন। তারপরও তাঁদের অধ্যবসায়ে কিসের এত অভাব ছিল, যাতে প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত সুপারিশগুলো প্রকাশ হওয়ার পরই বিএনপি ঐকমত্য কমিশন সম্পর্কে প্রতারণার অভিযোগ তুলল! একই সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার দিকেও অভিযোগের তির ছুড়ল! বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বয়ানে—জুলাই সনদের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় নোট অব ডিসেন্ট উপেক্ষা করে জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। এই কারণে নির্বাচনে কোনো রকম ব্যত্যয় ঘটলে তার দায়দায়িত্ব ড. ইউনূসকেই নিতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ঐকমত্য কমিশনের আলোচনা এবং প্রণীত সুপারিশের মধ্যে কী এমন সামঞ্জস্যহীনতা রেখে দেওয়া হয়েছে, যাতে সালাহউদ্দিন আহমদ বললেন যে কমিশনের সুপারিশে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি হবে না, জাতি বিভক্ত হবে! বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় বিএনপির প্রধান প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি যখন বলেন, ঐকমত্য কমিশনে যেসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, সেগুলো সুপারিশে নেই কিংবা বিএনপি যে জুলাই সনদে স্বাক্ষর করেছে, সুপারিশের সঙ্গে যুক্ত করা সনদ সেটি নয়, তখন তা জনপরিসরে বিশেষ কিছুর ইঙ্গিত দেয়।
আবার বিএনপির এই প্রতিক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা যায় জামায়াতের। জামায়াতের প্রতিক্রিয়ায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তারা ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশের সঙ্গে শতভাগ সহমত পোষণ করে। এখন তারা সরকারের ওপর ক্রমাগতভাবে চাপ বাড়িয়ে যাচ্ছে জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের আদেশ জারি করা এবং গণভোটের তারিখ ঘোষণার জন্য। এ ব্যাপারে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি জামায়াতের সর্বশেষ দাবি ছিল গতকাল শুক্রবার জুলাই সনদ বাস্তবায়নের আদেশ জারি করার। গত বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে জামায়াতের নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেছেন, জামায়াত রাষ্ট্র সংস্কারে দেওয়া ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাবগুলোর পূর্ণ বাস্তবায়ন চায়। সে জন্য আগামীকালের (শুক্রবার) মধ্যে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি করতে হবে। এই বক্তব্যে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশমালা নিয়ে তাদের কোনো দ্বিমত নেই।
গণভোটের বিষয়ে জামায়াতের বক্তব্য হলো—জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারির পর গণভোটের আয়োজন করতে হবে। সেটা অবশ্যই জাতীয় নির্বাচনের আগে এবং সেটি চলতি নভেম্বর মাসের মধ্যে হওয়াই সমীচীন। এ ব্যাপারে যত দেরি হবে ততই সরকার জনগণের আস্থা হারাবে। জামায়াত একই দিনে নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠান সমর্থন করে না। গণভোটের পর ফেব্রুয়ারিতেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন হতে হবে। এর মধ্যে এমন কোনো বিষয় সামনে আনা যাবে না (সরকার কিংবা কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে) যাতে ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধের নির্বাচন অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে।
জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশের বিষয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) অবস্থান অনেকটাই জামায়াতের কাছাকাছি। অবশ্য গণভোটের সময় নিয়ে জামায়াতের মতো এনসিপির কঠোর কোনো অবস্থান নেই। তারা একই দিনে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠানে যেমন রাজি, তেমনি গণভোট জাতীয় নির্বাচনের আগে হলেও তাদের আপত্তি নেই। তবে তারা চায় প্রধান উপদেষ্টা অবিলম্বে শহীদ মিনারে গিয়ে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের আদেশ ঘোষণা করবেন এবং এনসিপি সেখানেই সনদে স্বাক্ষর করবে।
জুলাই অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী এবং বর্তমানে ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিএনপির পরেই জামায়াতকে গণ্য করা হয়। অবশ্য শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর থেকেই বিভিন্ন ইস্যুতে দল দুটির মধ্যে অনৈক্যের সুর স্পষ্ট ও তীব্রতর হতে থাকে। বর্তমানে জুলাই সনদ বাস্তবায়নে ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশ ঘিরে দল দুটির অবস্থান সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে। এনসিপির অবস্থান কিছুটা ভিন্ন হলেও তা জাতীয় ঐক্যের সমার্থক নয়। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের অবস্থানও ‘হয় এদিকে নয় ওদিকে’। জুলাই অভ্যুত্থানের রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে এই যে অনৈক্য, সেটা অন্তর্বর্তী সরকারেরও মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে। সরকারের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেছেন, অভ্যুত্থানের শক্তিগুলোর মধ্যে এই অনৈক্য হতাশাব্যঞ্জক এবং সরকারের সামনে এক নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে। গত বৃহস্পতিবার তিনি অবশ্য সব পক্ষকে আশ্বস্ত করেছেন এই বলে যে গণভোটের সময় এবং জুলাই সনদ বাস্তবায়নে ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন প্রধান উপদেষ্টা নিজে এবং তা শিগগিরই নেওয়া হবে।
কিন্তু তাতেই কি অনৈক্যের অবসান এবং সব সমস্যার সমাধান হবে? যে ভিন্নমতগুলোসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জুলাই সনদে স্বাক্ষর করেছে, সেগুলোর মীমাংসা হবে কীভাবে! আবার গণভোট অনুষ্ঠানের বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো একমত হয়েছে ঠিকই। কিন্তু গণভোটের প্রশ্নটি কী হবে? ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশে যে প্রশ্নের প্রস্তাব করা হয়েছে, সেটি তো বিস্ময়কর। কমিশনের প্রশ্নটি হলো—‘আপনি কি জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ এবং ইহার তফসিল-১-এ সন্নিবেশিত সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত খসড়া বিলের প্রস্তাবসমূহের প্রতি আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছেন?’ এই প্রশ্ন থেকে ‘খসড়া বিলের’ শব্দ দুটি প্রয়োজনে বাদও দেওয়া যেতে পারে বলে কমিশন বলেছে। তবে এই প্রশ্ন গণভোটের উপযোগী নয়। কারণ, এই প্রশ্নের হ্যাঁ কিংবা না জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। গণভোটে এই প্রশ্নের হ্যাঁ জবাব দিতে হলে একজন ভোটারকে ৪৮টি প্রস্তাবের সঙ্গেই একমত হতে হবে। আর না জবাব দিতে হলেও ৪৮টি প্রস্তাবকেই না বলতে হবে, যেটা বাস্তবসম্মত নয়। এ ছাড়া জুলাই জাতীয় সনদে সংবিধান সংস্কার প্রশ্নে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যে ভিন্নমত যুক্ত হয়েছিল, গণভোটে তা বিবেচনায় না নেওয়ারও সুপারিশ করা হয়েছে। মানে জুলাই সনদের পক্ষে যদি জনগণ ভোট দেন, তবে ভিন্নমতগুলো বিবেচনায় নেওয়ার আর কোনো সুযোগ থাকবে না।
জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টির লক্ষ্যে গত ৯ মাস প্রাজ্ঞজনেরা যে কঠোর অধ্যবসায় করলেন, তার ফল কী হলো? একদিকে জাতীয় ঐক্য অধরা থেকে গেল, একই সঙ্গে কোনো সমস্যারই পূর্ণ ও স্পষ্ট সমাধান মিলল না। অবশ্য সরকার যে হাতের পাঁচ রেখে দিয়েছে, তা বোধগম্য হয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের কথায়। তিনি বলেছেন, জুলাই সনদের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হবে। আমরা ধারণা করতে পারি, সে ক্ষেত্রে হয়তো রাজনৈতিক দলগুলোকে কোনো কোনো বিষয় ছাড় দিত হবে, যা তারা এখন চাইছে না।
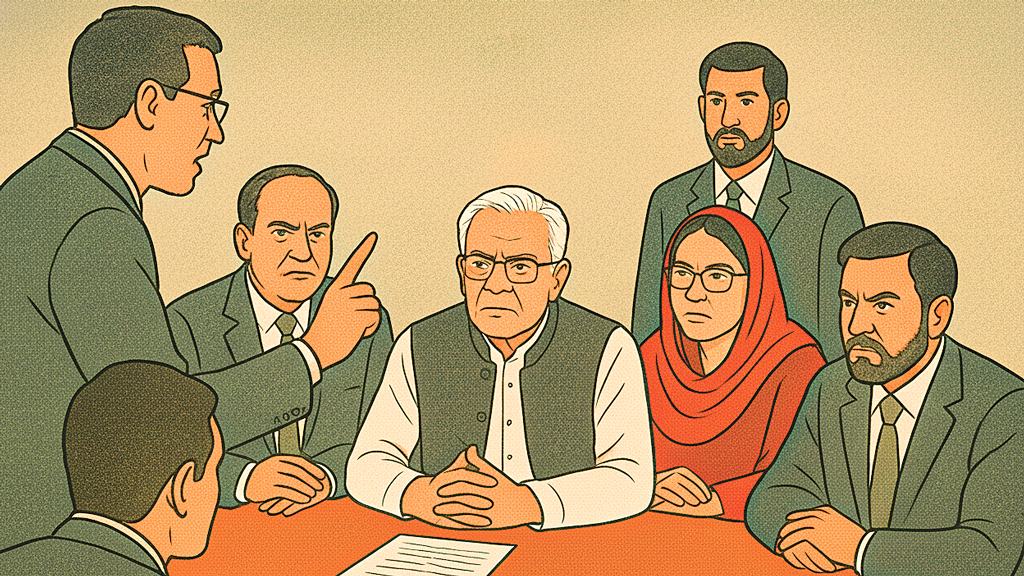
বিভাজন যেখানে ঘরে ঘরে, জনে জনে, সেখানে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া যথেষ্ট সাহসের কাজই বটে। অন্তর্বর্তী সরকার সেই সাহস দেখিয়েছিল। দেশি-প্রবাসী-বিদেশি একদল প্রাজ্ঞজনের সমন্বয়ে গঠন করেছিল জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। যদিও কমিশনের সভাপতি হিসেবে এর স্টিয়ারিং হুইল ছিল প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের হাতেই। কিন্তু বাস্তব কর্মক্ষেত্রে দীর্ঘ ২৭০ দিন ধরে ৩০টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সমন্বয় করেছেন সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের নেতৃত্বে কমিশনের অন্য সদস্যরা। জাতীয় ঐক্য গড়ার জন্য যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা প্রয়োজন, তার সবই হয়তো এই সদস্যদের ছিল বা আছে। কিন্তু তাঁদের অধ্যবসায়ে কিছু একটার যে অভাব ছিল, তা এখন স্পষ্ট। না হলে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের সুপারিশসহ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করে প্রধান উপদেষ্টার কাছে উপস্থাপন করার সঙ্গে সঙ্গে বিভেদ-বিভাজন ও অনৈক্যের আগুনে একেবারে ঘি পড়ার মতো অবস্থা হলো কেন? এ কথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে কমিশনের সভাপতি তথা প্রধান উপদেষ্টার অজ্ঞাতসারে কিংবা অনুমোদন ছাড়া এই প্রতিবেদন চূড়ান্ত হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে তিনি যেমন প্রতিবেদন গ্রহণ করেছেন, তেমনি কমিশনের সভাপতি হিসেবে ওই প্রতিবেদনে স্বাক্ষরও করেছেন।
তাহলে সবাই তো ছিলেন। তারপরও তাঁদের অধ্যবসায়ে কিসের এত অভাব ছিল, যাতে প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত সুপারিশগুলো প্রকাশ হওয়ার পরই বিএনপি ঐকমত্য কমিশন সম্পর্কে প্রতারণার অভিযোগ তুলল! একই সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার দিকেও অভিযোগের তির ছুড়ল! বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বয়ানে—জুলাই সনদের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় নোট অব ডিসেন্ট উপেক্ষা করে জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। এই কারণে নির্বাচনে কোনো রকম ব্যত্যয় ঘটলে তার দায়দায়িত্ব ড. ইউনূসকেই নিতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ঐকমত্য কমিশনের আলোচনা এবং প্রণীত সুপারিশের মধ্যে কী এমন সামঞ্জস্যহীনতা রেখে দেওয়া হয়েছে, যাতে সালাহউদ্দিন আহমদ বললেন যে কমিশনের সুপারিশে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি হবে না, জাতি বিভক্ত হবে! বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় বিএনপির প্রধান প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি যখন বলেন, ঐকমত্য কমিশনে যেসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, সেগুলো সুপারিশে নেই কিংবা বিএনপি যে জুলাই সনদে স্বাক্ষর করেছে, সুপারিশের সঙ্গে যুক্ত করা সনদ সেটি নয়, তখন তা জনপরিসরে বিশেষ কিছুর ইঙ্গিত দেয়।
আবার বিএনপির এই প্রতিক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা যায় জামায়াতের। জামায়াতের প্রতিক্রিয়ায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তারা ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশের সঙ্গে শতভাগ সহমত পোষণ করে। এখন তারা সরকারের ওপর ক্রমাগতভাবে চাপ বাড়িয়ে যাচ্ছে জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের আদেশ জারি করা এবং গণভোটের তারিখ ঘোষণার জন্য। এ ব্যাপারে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি জামায়াতের সর্বশেষ দাবি ছিল গতকাল শুক্রবার জুলাই সনদ বাস্তবায়নের আদেশ জারি করার। গত বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে জামায়াতের নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেছেন, জামায়াত রাষ্ট্র সংস্কারে দেওয়া ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাবগুলোর পূর্ণ বাস্তবায়ন চায়। সে জন্য আগামীকালের (শুক্রবার) মধ্যে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি করতে হবে। এই বক্তব্যে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশমালা নিয়ে তাদের কোনো দ্বিমত নেই।
গণভোটের বিষয়ে জামায়াতের বক্তব্য হলো—জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারির পর গণভোটের আয়োজন করতে হবে। সেটা অবশ্যই জাতীয় নির্বাচনের আগে এবং সেটি চলতি নভেম্বর মাসের মধ্যে হওয়াই সমীচীন। এ ব্যাপারে যত দেরি হবে ততই সরকার জনগণের আস্থা হারাবে। জামায়াত একই দিনে নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠান সমর্থন করে না। গণভোটের পর ফেব্রুয়ারিতেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন হতে হবে। এর মধ্যে এমন কোনো বিষয় সামনে আনা যাবে না (সরকার কিংবা কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে) যাতে ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধের নির্বাচন অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে।
জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশের বিষয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) অবস্থান অনেকটাই জামায়াতের কাছাকাছি। অবশ্য গণভোটের সময় নিয়ে জামায়াতের মতো এনসিপির কঠোর কোনো অবস্থান নেই। তারা একই দিনে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠানে যেমন রাজি, তেমনি গণভোট জাতীয় নির্বাচনের আগে হলেও তাদের আপত্তি নেই। তবে তারা চায় প্রধান উপদেষ্টা অবিলম্বে শহীদ মিনারে গিয়ে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের আদেশ ঘোষণা করবেন এবং এনসিপি সেখানেই সনদে স্বাক্ষর করবে।
জুলাই অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী এবং বর্তমানে ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিএনপির পরেই জামায়াতকে গণ্য করা হয়। অবশ্য শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর থেকেই বিভিন্ন ইস্যুতে দল দুটির মধ্যে অনৈক্যের সুর স্পষ্ট ও তীব্রতর হতে থাকে। বর্তমানে জুলাই সনদ বাস্তবায়নে ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশ ঘিরে দল দুটির অবস্থান সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে। এনসিপির অবস্থান কিছুটা ভিন্ন হলেও তা জাতীয় ঐক্যের সমার্থক নয়। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের অবস্থানও ‘হয় এদিকে নয় ওদিকে’। জুলাই অভ্যুত্থানের রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে এই যে অনৈক্য, সেটা অন্তর্বর্তী সরকারেরও মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে। সরকারের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেছেন, অভ্যুত্থানের শক্তিগুলোর মধ্যে এই অনৈক্য হতাশাব্যঞ্জক এবং সরকারের সামনে এক নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে। গত বৃহস্পতিবার তিনি অবশ্য সব পক্ষকে আশ্বস্ত করেছেন এই বলে যে গণভোটের সময় এবং জুলাই সনদ বাস্তবায়নে ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন প্রধান উপদেষ্টা নিজে এবং তা শিগগিরই নেওয়া হবে।
কিন্তু তাতেই কি অনৈক্যের অবসান এবং সব সমস্যার সমাধান হবে? যে ভিন্নমতগুলোসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জুলাই সনদে স্বাক্ষর করেছে, সেগুলোর মীমাংসা হবে কীভাবে! আবার গণভোট অনুষ্ঠানের বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো একমত হয়েছে ঠিকই। কিন্তু গণভোটের প্রশ্নটি কী হবে? ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশে যে প্রশ্নের প্রস্তাব করা হয়েছে, সেটি তো বিস্ময়কর। কমিশনের প্রশ্নটি হলো—‘আপনি কি জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ এবং ইহার তফসিল-১-এ সন্নিবেশিত সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত খসড়া বিলের প্রস্তাবসমূহের প্রতি আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছেন?’ এই প্রশ্ন থেকে ‘খসড়া বিলের’ শব্দ দুটি প্রয়োজনে বাদও দেওয়া যেতে পারে বলে কমিশন বলেছে। তবে এই প্রশ্ন গণভোটের উপযোগী নয়। কারণ, এই প্রশ্নের হ্যাঁ কিংবা না জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। গণভোটে এই প্রশ্নের হ্যাঁ জবাব দিতে হলে একজন ভোটারকে ৪৮টি প্রস্তাবের সঙ্গেই একমত হতে হবে। আর না জবাব দিতে হলেও ৪৮টি প্রস্তাবকেই না বলতে হবে, যেটা বাস্তবসম্মত নয়। এ ছাড়া জুলাই জাতীয় সনদে সংবিধান সংস্কার প্রশ্নে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যে ভিন্নমত যুক্ত হয়েছিল, গণভোটে তা বিবেচনায় না নেওয়ারও সুপারিশ করা হয়েছে। মানে জুলাই সনদের পক্ষে যদি জনগণ ভোট দেন, তবে ভিন্নমতগুলো বিবেচনায় নেওয়ার আর কোনো সুযোগ থাকবে না।
জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টির লক্ষ্যে গত ৯ মাস প্রাজ্ঞজনেরা যে কঠোর অধ্যবসায় করলেন, তার ফল কী হলো? একদিকে জাতীয় ঐক্য অধরা থেকে গেল, একই সঙ্গে কোনো সমস্যারই পূর্ণ ও স্পষ্ট সমাধান মিলল না। অবশ্য সরকার যে হাতের পাঁচ রেখে দিয়েছে, তা বোধগম্য হয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের কথায়। তিনি বলেছেন, জুলাই সনদের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হবে। আমরা ধারণা করতে পারি, সে ক্ষেত্রে হয়তো রাজনৈতিক দলগুলোকে কোনো কোনো বিষয় ছাড় দিত হবে, যা তারা এখন চাইছে না।

১৯৩৩ সালে ক্লারা জেটকিনের মৃত্যুর পর তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান লিখেছিল, ‘গ্র্যান্ডমাদার অব জার্মান কমিউনিজম’, অর্থাৎ ‘জার্মান সাম্যবাদের মাতামহ’! তাঁকে নারী দিবসের জননী বললে কি খুব ভুল হবে?
০৮ মার্চ ২০২২
এখন নাকি বানর আর শূকরের পালকেই দেখা যায় লাউয়াছড়ায়। বিরল প্রজাতির অনেক পাখি ও প্রাণী বাস করত এই সংরক্ষিত বনে। কিন্তু সেসব লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বনটিকে নিজেদের অভয়ারণ্য বলে হয়তো ভাবতে পারছে না তারা।
৬ ঘণ্টা আগে
মানুষের জীবনের শেষ অধ্যায় হলো অদৃশ্য বার্ধক্যের যাত্রা। কিন্তু সবাই বার্ধক্যের জীবনে সমান মর্যাদা পায় না। সমাজের প্রান্তিক এক শ্রেণি হলো যৌনকর্মীরা। যখন তাঁরা শেষ বয়সে পৌঁছান, তখন তাঁরা এক অনিশ্চিত জীবনের মধ্যে পড়ে যায়। যৌবনে যাঁদের দেহই ছিল আয়ের একমাত্র মূলধন, বার্ধক্যে এসে সেই দেহই যেন হয়ে...
৬ ঘণ্টা আগে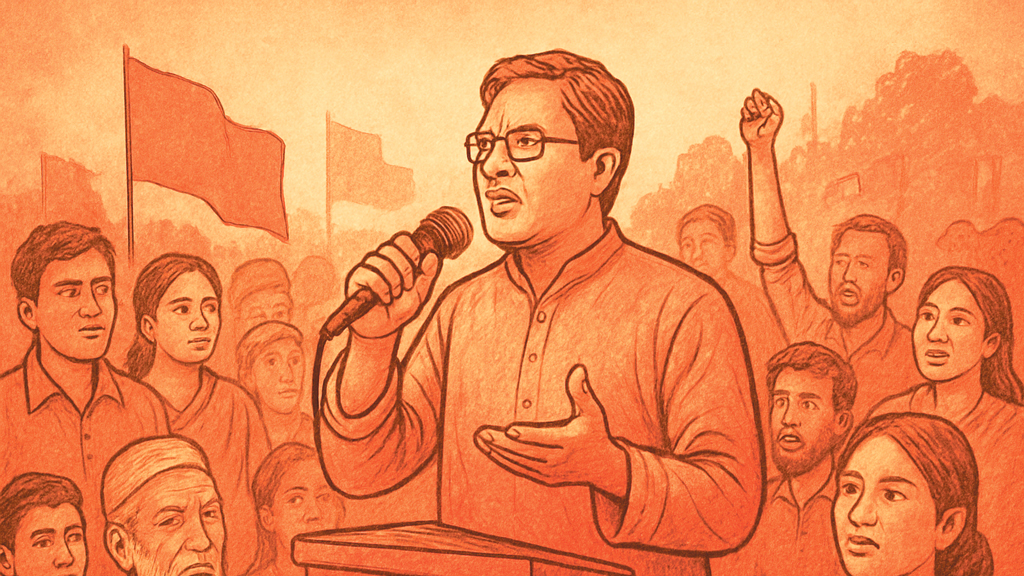
১৯৪৭-এর দেশভাগ থেকে শুরু করে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ—এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় জনগণই ছিল রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। তৎকালীন নেতারা কথা বলতেন জনগণের ভাষায় এবং তাঁদের দুঃখ, ক্ষোভ ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতেন রাজনীতিতে। কিন্তু স্বাধীনতার পরপরই অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে সামরিক শাসন...
৬ ঘণ্টা আগেহাসান আলী

মানুষের জীবনের শেষ অধ্যায় হলো অদৃশ্য বার্ধক্যের যাত্রা। কিন্তু সবাই বার্ধক্যের জীবনে সমান মর্যাদা পায় না। সমাজের প্রান্তিক এক শ্রেণি হলো যৌনকর্মীরা। যখন তাঁরা শেষ বয়সে পৌঁছান, তখন তাঁরা এক অনিশ্চিত জীবনের মধ্যে পড়ে যায়। যৌবনে যাঁদের দেহই ছিল আয়ের একমাত্র মূলধন, বার্ধক্যে এসে সেই দেহই যেন হয়ে ওঠে অবজ্ঞার প্রতীক। দক্ষিণ এশিয়ার অন্ধকার গলিপথ থেকে শুরু করে পশ্চিমা বিশ্বের নিয়ন্ত্রিত পল্লি—সবখানেই এই যৌনকর্মীর জীবনে নেমে আসে এক গভীর নিঃসঙ্গতা।
ঢাকার কোনো বস্তি কিংবা কলকাতার সোনাগাছি—সেখানে দেখা যায় মালতী বালা কিংবা রহিমা বেগমের মতো বৃদ্ধ নারীদের। যৌবনে গ্রাহকের ভিড়ে যাঁদের ঘরে আলো জ্বলত সারা রাত, আজ সেখানে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। ভাঙা চারপাইয়ে বসে তাঁরা শোনেন পাশের ঘরে তরুণীদের হাসি-আনন্দ। বয়সের কারণে কেউ তাঁদের কাছে আর আসে না। প্রায় ক্ষেত্রে দেখা যায়, সন্তান থাকলেও তাঁরা মায়ের অতীত জীবনের কারণে এবং সামাজিক লোকলজ্জার জন্য তাঁকে অস্বীকার করেন।
অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ বয়সের নারীরা অর্থকষ্টের কারণে ভিক্ষা করতে বাধ্য হন। আবার কেউ কেউ ছোটখাটো কাজও করে থাকেন। কিছু এনজিও বা সমাজকর্মী মাঝে মাঝে চাল-ডাল দেন, কিন্তু তা জীবনধারণের জন্য যথেষ্ট নয়। স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ তো দূরের কথা, বার্ধক্যজনিত অসুখ আর যৌবনের পেশার কারণে সৃষ্ট রোগ তাঁদের জীবনকে তছনছ করে দেয়।
মালতী বালার মতো এক বৃদ্ধা একদিন আমাকে বলেছিলেন, ‘যৌবনে শরীর বিক্রি করেছি পেট চালানোর জন্য, আজ বার্ধক্যে শরীরই আমাকে তাড়া করছে। তবু মরতে পারি না। কারণ, মরে যাওয়ার মতো জায়গাও নেই।’ এই কথার মধ্যেই লুকিয়ে আছে দক্ষিণ এশিয়ার হাজারো প্রবীণ যৌনকর্মীর মর্মন্তুদ কাহিনি।
অন্যদিকে ইউরোপে চিত্র ভিন্ন। বার্লিনের গ্রেটা বা আমস্টারডামের সোফিয়া—তাঁদের যৌবন কেটেছে বৈধ যৌনপল্লিতে। তাঁরা রাষ্ট্রকে কর দিয়েছেন, তাই অবসরে তাঁরা পান পেনশন ও চিকিৎসাসেবা। একটি ছোট্ট ফ্ল্যাটে একা থাকলেও তাঁদের নিত্য সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার দায়িত্ব নিয়েছে। সামাজিক সংগঠনগুলো মাঝে মাঝে তাঁদের খোঁজ নেয়, তাঁদের অভিজ্ঞতা নিয়ে বই প্রকাশিত হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক সুরক্ষা পেলেও হৃদয়ের শূন্যতা ভরাট হয় না। গ্রেটা প্রায়ই বলেন, ‘টাকা আছে, ওষুধ আছে, ফ্ল্যাট আছে; কিন্তু একাকিত্বে হৃদয়টা শুকিয়ে যায়। যৌবনের স্মৃতি আর নিঃসঙ্গতা বার্ধক্যে আমাকে তাড়া করে।’
পশ্চিমা বিশ্বে আইনি স্বীকৃতি থাকলেও আবেগগত বিচ্ছিন্নতা থেকে যায়। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নতা, সমাজের আড়ালে অতীত জীবনের ছায়া এবং বন্ধু না থাকার যন্ত্রণা তাঁদের প্রবীণ জীবন কষ্টকর হয়ে ওঠে।
দক্ষিণ এশিয়ায় প্রবীণ যৌনকর্মীর জীবন এককথায় দারিদ্র্য, কলঙ্ক ও নিঃসঙ্গতার চিত্র। পশ্চিমা বিশ্বে যেখানে বৈধতা আছে, সেখানে আর্থিক নিরাপত্তা থাকলেও আবেগগত শূন্যতা একই রকম রয়ে যায়। একদিকে ক্ষুধা, অন্যদিকে নিঃসঙ্গতা—দুটিই যেন ভিন্ন পথে একই যন্ত্রণা হয়ে ফিরে আসে।
এই যৌনকর্মীরা মানবসমাজের যে প্রান্তিক পর্যায়ে অবস্থান করে, যাঁদের কথা আসলে কেউই ভাবে না। এমনকি রাষ্ট্র-সরকারও না। অথচ তাঁদেরও হাসি-কান্না, প্রেম-অভিমান, বেঁচে থাকার অধিকার আছে। সমাজ ও রাষ্ট্র যদি তাঁদের বার্ধক্যে সম্মান ও আশ্রয় দিত, তাহলে হয়তো এই অদৃশ্য যাত্রা অনেকটাই আলোকিত হতো।
প্রবীণ যৌনকর্মীর জীবন আমাদের শেখায়—প্রতিটি মানুষ, যেই পেশায় থাকুক না কেন, বার্ধক্যে প্রাপ্য সম্মান ও সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার রাখে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র-সরকার তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না।

মানুষের জীবনের শেষ অধ্যায় হলো অদৃশ্য বার্ধক্যের যাত্রা। কিন্তু সবাই বার্ধক্যের জীবনে সমান মর্যাদা পায় না। সমাজের প্রান্তিক এক শ্রেণি হলো যৌনকর্মীরা। যখন তাঁরা শেষ বয়সে পৌঁছান, তখন তাঁরা এক অনিশ্চিত জীবনের মধ্যে পড়ে যায়। যৌবনে যাঁদের দেহই ছিল আয়ের একমাত্র মূলধন, বার্ধক্যে এসে সেই দেহই যেন হয়ে ওঠে অবজ্ঞার প্রতীক। দক্ষিণ এশিয়ার অন্ধকার গলিপথ থেকে শুরু করে পশ্চিমা বিশ্বের নিয়ন্ত্রিত পল্লি—সবখানেই এই যৌনকর্মীর জীবনে নেমে আসে এক গভীর নিঃসঙ্গতা।
ঢাকার কোনো বস্তি কিংবা কলকাতার সোনাগাছি—সেখানে দেখা যায় মালতী বালা কিংবা রহিমা বেগমের মতো বৃদ্ধ নারীদের। যৌবনে গ্রাহকের ভিড়ে যাঁদের ঘরে আলো জ্বলত সারা রাত, আজ সেখানে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। ভাঙা চারপাইয়ে বসে তাঁরা শোনেন পাশের ঘরে তরুণীদের হাসি-আনন্দ। বয়সের কারণে কেউ তাঁদের কাছে আর আসে না। প্রায় ক্ষেত্রে দেখা যায়, সন্তান থাকলেও তাঁরা মায়ের অতীত জীবনের কারণে এবং সামাজিক লোকলজ্জার জন্য তাঁকে অস্বীকার করেন।
অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ বয়সের নারীরা অর্থকষ্টের কারণে ভিক্ষা করতে বাধ্য হন। আবার কেউ কেউ ছোটখাটো কাজও করে থাকেন। কিছু এনজিও বা সমাজকর্মী মাঝে মাঝে চাল-ডাল দেন, কিন্তু তা জীবনধারণের জন্য যথেষ্ট নয়। স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ তো দূরের কথা, বার্ধক্যজনিত অসুখ আর যৌবনের পেশার কারণে সৃষ্ট রোগ তাঁদের জীবনকে তছনছ করে দেয়।
মালতী বালার মতো এক বৃদ্ধা একদিন আমাকে বলেছিলেন, ‘যৌবনে শরীর বিক্রি করেছি পেট চালানোর জন্য, আজ বার্ধক্যে শরীরই আমাকে তাড়া করছে। তবু মরতে পারি না। কারণ, মরে যাওয়ার মতো জায়গাও নেই।’ এই কথার মধ্যেই লুকিয়ে আছে দক্ষিণ এশিয়ার হাজারো প্রবীণ যৌনকর্মীর মর্মন্তুদ কাহিনি।
অন্যদিকে ইউরোপে চিত্র ভিন্ন। বার্লিনের গ্রেটা বা আমস্টারডামের সোফিয়া—তাঁদের যৌবন কেটেছে বৈধ যৌনপল্লিতে। তাঁরা রাষ্ট্রকে কর দিয়েছেন, তাই অবসরে তাঁরা পান পেনশন ও চিকিৎসাসেবা। একটি ছোট্ট ফ্ল্যাটে একা থাকলেও তাঁদের নিত্য সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার দায়িত্ব নিয়েছে। সামাজিক সংগঠনগুলো মাঝে মাঝে তাঁদের খোঁজ নেয়, তাঁদের অভিজ্ঞতা নিয়ে বই প্রকাশিত হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক সুরক্ষা পেলেও হৃদয়ের শূন্যতা ভরাট হয় না। গ্রেটা প্রায়ই বলেন, ‘টাকা আছে, ওষুধ আছে, ফ্ল্যাট আছে; কিন্তু একাকিত্বে হৃদয়টা শুকিয়ে যায়। যৌবনের স্মৃতি আর নিঃসঙ্গতা বার্ধক্যে আমাকে তাড়া করে।’
পশ্চিমা বিশ্বে আইনি স্বীকৃতি থাকলেও আবেগগত বিচ্ছিন্নতা থেকে যায়। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নতা, সমাজের আড়ালে অতীত জীবনের ছায়া এবং বন্ধু না থাকার যন্ত্রণা তাঁদের প্রবীণ জীবন কষ্টকর হয়ে ওঠে।
দক্ষিণ এশিয়ায় প্রবীণ যৌনকর্মীর জীবন এককথায় দারিদ্র্য, কলঙ্ক ও নিঃসঙ্গতার চিত্র। পশ্চিমা বিশ্বে যেখানে বৈধতা আছে, সেখানে আর্থিক নিরাপত্তা থাকলেও আবেগগত শূন্যতা একই রকম রয়ে যায়। একদিকে ক্ষুধা, অন্যদিকে নিঃসঙ্গতা—দুটিই যেন ভিন্ন পথে একই যন্ত্রণা হয়ে ফিরে আসে।
এই যৌনকর্মীরা মানবসমাজের যে প্রান্তিক পর্যায়ে অবস্থান করে, যাঁদের কথা আসলে কেউই ভাবে না। এমনকি রাষ্ট্র-সরকারও না। অথচ তাঁদেরও হাসি-কান্না, প্রেম-অভিমান, বেঁচে থাকার অধিকার আছে। সমাজ ও রাষ্ট্র যদি তাঁদের বার্ধক্যে সম্মান ও আশ্রয় দিত, তাহলে হয়তো এই অদৃশ্য যাত্রা অনেকটাই আলোকিত হতো।
প্রবীণ যৌনকর্মীর জীবন আমাদের শেখায়—প্রতিটি মানুষ, যেই পেশায় থাকুক না কেন, বার্ধক্যে প্রাপ্য সম্মান ও সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার রাখে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র-সরকার তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না।

১৯৩৩ সালে ক্লারা জেটকিনের মৃত্যুর পর তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান লিখেছিল, ‘গ্র্যান্ডমাদার অব জার্মান কমিউনিজম’, অর্থাৎ ‘জার্মান সাম্যবাদের মাতামহ’! তাঁকে নারী দিবসের জননী বললে কি খুব ভুল হবে?
০৮ মার্চ ২০২২
এখন নাকি বানর আর শূকরের পালকেই দেখা যায় লাউয়াছড়ায়। বিরল প্রজাতির অনেক পাখি ও প্রাণী বাস করত এই সংরক্ষিত বনে। কিন্তু সেসব লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বনটিকে নিজেদের অভয়ারণ্য বলে হয়তো ভাবতে পারছে না তারা।
৬ ঘণ্টা আগে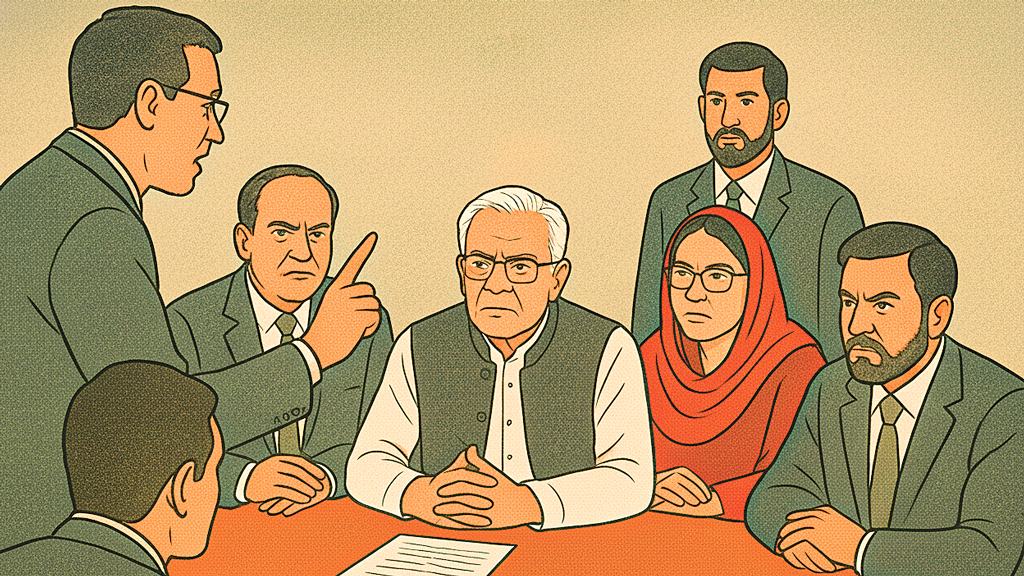
বিভাজন যেখানে ঘরে ঘরে, জনে জনে, সেখানে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া যথেষ্ট সাহসের কাজই বটে। অন্তর্বর্তী সরকার সেই সাহস দেখিয়েছিল। দেশি-প্রবাসী-বিদেশি একদল প্রাজ্ঞজনের সমন্বয়ে গঠন করেছিল জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। যদিও কমিশনের সভাপতি হিসেবে এর স্টিয়ারিং হুইল ছিল প্রধান উপদেষ্টা...
৬ ঘণ্টা আগে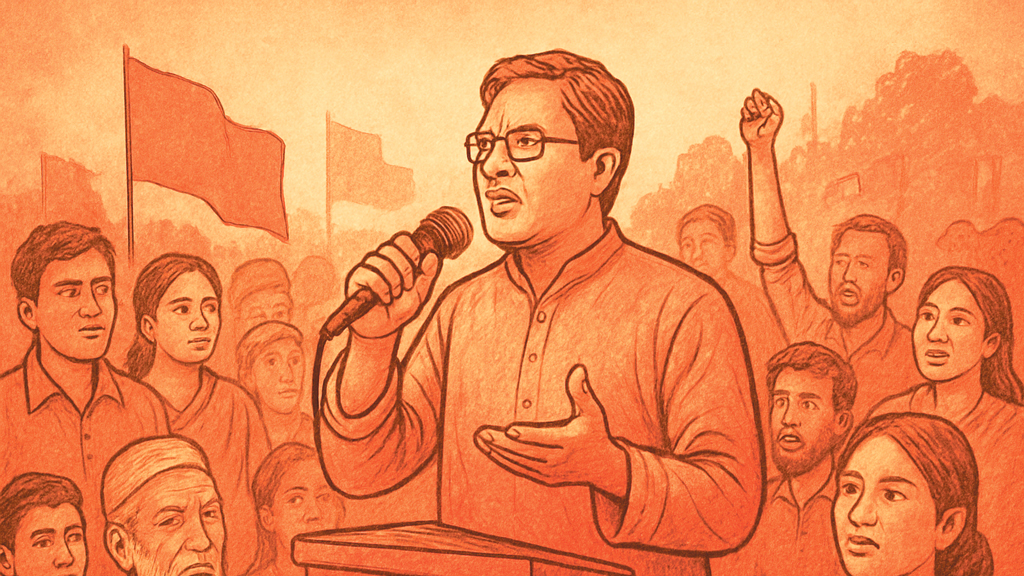
১৯৪৭-এর দেশভাগ থেকে শুরু করে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ—এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় জনগণই ছিল রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। তৎকালীন নেতারা কথা বলতেন জনগণের ভাষায় এবং তাঁদের দুঃখ, ক্ষোভ ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতেন রাজনীতিতে। কিন্তু স্বাধীনতার পরপরই অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে সামরিক শাসন...
৬ ঘণ্টা আগেমো. শাহিন আলম
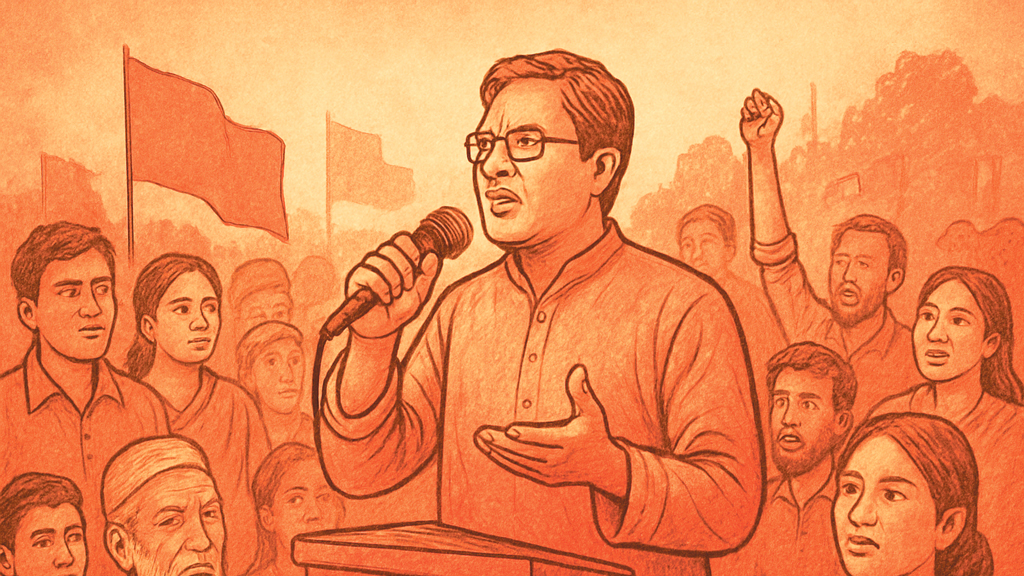
১৯৪৭-এর দেশভাগ থেকে শুরু করে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ—এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় জনগণই ছিল রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। তৎকালীন নেতারা কথা বলতেন জনগণের ভাষায় এবং তাঁদের দুঃখ, ক্ষোভ ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতেন রাজনীতিতে। কিন্তু স্বাধীনতার পরপরই অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে সামরিক শাসন এবং পরবর্তী সময়ে গণতান্ত্রিক ধারার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিটি পর্যায়ে জনগণের ভূমিকা নিম্নমুখী হলো, রাজনীতি অনেকটাই দলীয়করণ ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক হয়ে পড়ল। সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর হারিয়ে গেল প্রভাবশালী গোষ্ঠীর কাছে। ফলে রাষ্ট্র গঠনের যে স্বপ্ন ছিল জনগণের জন্য, তা অনেক সময় দলীয় কিংবা ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর সময় এসেছে, আমরা কেমন রাজনীতি চাই?
অনেক দিন থেকে দেশ ও জনগণের সেবা করার বুলি আওড়ানো অনেক রাজনীতিবিদের দেখা মেলে শুধু ভোটের মৌসুমে। যেহেতু ঘনিয়ে আসছে জাতীয় নির্বাচন, রাজনীতির মাঠ তাই এখন ভোটের শোরগোলে ব্যস্ত। যেখানে আছে প্রত্যাশা, কৌশল, আবার আশঙ্কাও। যদিও নির্বাচন কমিশন এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করেনি। তবু বিভিন্ন দলীয় ও স্বতন্ত্র সম্ভাব্য প্রার্থীরা ইতিমধ্যেই নির্বাচনী এলাকায় ছুটে বেড়াচ্ছেন। গ্রাম থেকে শহর—সব জায়গায় শুরু হয়েছে প্রচারণার তোড়জোড়। প্রার্থীরা ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন, দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি।
কিন্তু জনগণ খুব সহজে তা বিশ্বাস করছে না। কারণ, বাস্তবতা হলো, নির্বাচনের পর প্রার্থীরা অনেক সময়ই হারিয়ে যান। অতীতে দেখা গেছে, ভোটে জয়ের পর অনেক নেতা জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না।
তবে এও সত্য, অনেক নেতা এখনো আন্তরিকভাবে জনগণের কল্যাণে কাজ করার জন্য ভাবেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে দলীয় আনুগত্য ও ব্যক্তিস্বার্থের কারণে তাঁরা বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেন না। তবে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ফলে জনগণের ভাবনায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। জনগণ এখন চায় এমন রাজনীতি, যেখানে সর্বস্তরে সুশাসন, ন্যায্যতা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। অন্যদিকে রাজনীতিবিদদেরও আত্মসমালোচনার সময় এসেছে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়া মানে কেবল কাঙ্ক্ষিত আসন পাওয়া নয়, বরং জনগণের আশা ও প্রয়োজন বুঝে সেগুলোর প্রতিফলন ঘটানো। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আমাদের রাজনীতিতে এই দায়বদ্ধতা প্রায়ই অনুপস্থিত। নির্বাচনের সময় জনগণকে মনে রাখা হয়, কিন্তু ক্ষমতায় গিয়েই ভুলে যাওয়া হয় তাদের কষ্ট, তাদের স্বপ্ন।
দীর্ঘদিন ধরে জনগণকে কেবল দল ও নেতারা শুধু ভোটদাতা হিসেবে ভেবে এসেছেন। যদিও গণতন্ত্র কেবল ভোটের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি একটি অংশগ্রহণ প্রক্রিয়াও, যেখানে জনগণ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে সরকারের কাজের জবাবদিহি করবে। তবে বাংলাদেশের গণতন্ত্র এখন অনেকটাই আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এর সবচেয়ে বড় কারণ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চায় ব্যাপক ঘাটতির কারণে। তা ছাড়া, আন্তদলীয় কোন্দল এবং বিরোধীমতকে অনেক সময় দমন করার রীতিও বহুল প্রচলিত। এই বিষয়গুলোর ফলে জনগণ রাজনীতিতে অনেকাংশে আস্থা হারাচ্ছে। ফলে রাজনীতি আর জনগণের থাকছে না, হয়ে উঠছে বিশেষ গোষ্ঠীর সম্পত্তি।
আজকের রাজনীতি জনগণের জীবনের সঙ্গে কতটা সম্পর্কিত—এই প্রশ্নটি জরুরি। কেননা, রাজনীতির প্রতিটি সিদ্ধান্তই দেশের অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নেতৃত্বের সীমাবদ্ধতা ও জনগণের অংশগ্রহণের অভাব—উভয়কেই প্রতিফলিত করছে। গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জনগণ নিজস্ব মতামত দিচ্ছে, কিন্তু সেই আওয়াজ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে কতটা প্রতিফলিত হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ আছে। যখন রাজনীতি জনগণকেন্দ্রিক হয়, তখন স্থানীয় অভিজ্ঞতা ও চাহিদা নীতি প্রণয়নে প্রতিফলিত হওয়ার কথা। কিন্তু উল্টো ঘটনা ঘটে, নীতি তৈরি হয় অনেকাংশে প্রভাবশালী গোষ্ঠী এবং বাণিজ্যিক স্বার্থ অনুযায়ী।
রাজনীতির এই সংকটে তরুণদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের সবচেয়ে বড় জনগোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বেও তরুণেরা রাজনীতিতে যথাযথ প্রতিনিধিত্ব পায় না। স্থানীয় পর্যায় থেকে রাজনীতির মূলধারার আলোচনায় তারা একপ্রকার অনুপস্থিতই থেকে যায়।
তবে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। দীর্ঘদিনের স্বৈরশাসনের অবসান হয়েছে। তবে জনগণের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন আসবে, বাস্তবিক অর্থে তেমন মৌলিক পরিবর্তন প্রতিফলিত হয়নি। জনপ্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কিংবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কিছু রদবদল হয়েছে মাত্র।
তবু বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এখনো রাজনীতিতে আস্থা রাখে, বিশ্বাস করে পরিবর্তনের সম্ভাবনায়। প্রত্যাশা থাকে এমন রাজনীতির; যেখানে উন্নয়ন মানে কেবল অবকাঠামোগত সংস্কার নয়, বরং কৃষকের ন্যায্যমূল্য ও শ্রমিকের মজুরি থেকে শুরু করে যুবকের কর্মসংস্থান, প্রত্যাশিত স্বাস্থ্যসেবায় সংস্কার, পরিবহনে শৃঙ্খলা, নদী দখল বন্ধ, বাকস্বাধীনতা, নারীর নিরাপত্তা ও ন্যায্য অংশগ্রহণ এবং রাষ্ট্রের সর্বস্তরে আইনের সুশাসন নিশ্চিত হবে।
এ ছাড়া আমলাতান্ত্রিক জটিলতা থেকে পরিত্রাণ চায় জনগণ। গ্রামগঞ্জ-শহরে সর্বত্র মানুষ এখন চায় শান্তির সুবাতাস। ভোটাররা এখন আগের চেয়ে যথেষ্ট সচেতন; তারা জানে একজন সৎ ও দক্ষ জনপ্রতিনিধি পুরো এলাকার চেহারা বদলে দিতে পারেন।
এখন প্রয়োজন এমন রাজনীতি, যেখানে উন্নয়ন হবে অংশগ্রহণমূলক, সিদ্ধান্ত আসবে জনগণের মাঠঘাট থেকে, আর বাস্তবায়ন করবেন জনপ্রতিনিধি। রাজনীতি হতে হবে এমন এক চুক্তি, যেখানে ভোটের বিনিময়ে প্রতিশ্রুতি নয়, বরং বিশ্বাসের বন্ধনে সেই সম্পর্ক গড়ে উঠবে। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের পর মানুষের মনোজগতে যে পরিবর্তন এসেছে, রাজনৈতিক দলগুলোকে সেটি উপলব্ধি করতে হবে। তাদের নীতি-পরিকল্পনায় পরিবর্তনটা ধারণ করতে হবে। বুঝতে হবে যেনতেনভাবে একটা নির্বাচনই শেষ কথা নয়। রাজনৈতিক দলগুলোকে সংস্কারের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।
রাজনীতির সৌন্দর্য তখনই ফুটে ওঠে, যখন সেটি জনগণের জীবনের সঙ্গে মিশে যায়। তাই প্রয়োজন এমন নেতৃত্ব, যা জনগণকে কেবল ভোটার নয়, বরং পরিবর্তনের অংশীদার হিসেবে দেখবে। বহুমাত্রিক রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ধারণ করতে না পারলে জনগণ যে স্বপ্ন দেখছে, তা ফিকে হয়ে যাবে। তাই রাজনীতি হোক জনগণের হাতে, জনগণের স্বার্থে এবং জনগণের জন্য।
লেখক: এমফিল গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
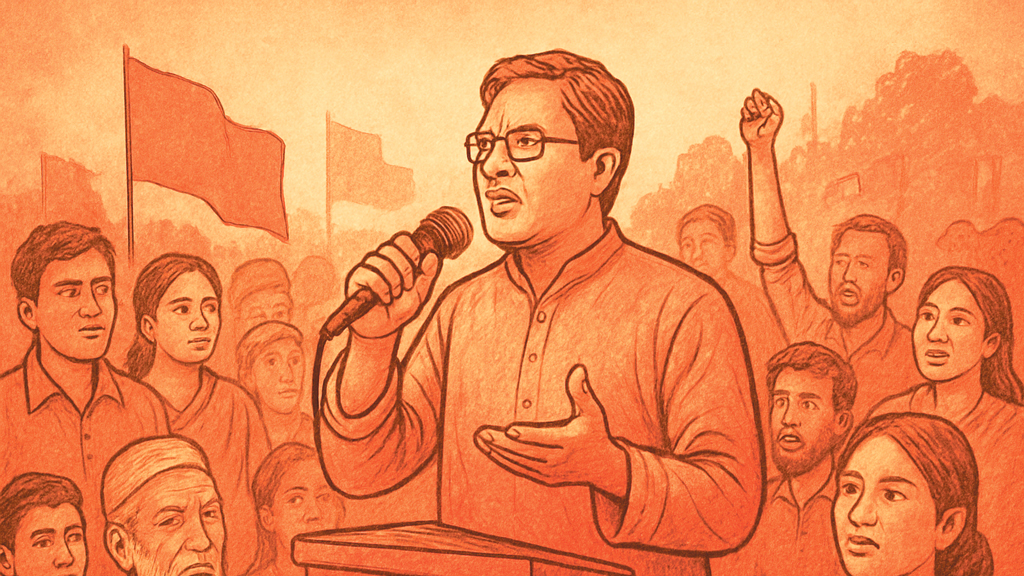
১৯৪৭-এর দেশভাগ থেকে শুরু করে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ—এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় জনগণই ছিল রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। তৎকালীন নেতারা কথা বলতেন জনগণের ভাষায় এবং তাঁদের দুঃখ, ক্ষোভ ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতেন রাজনীতিতে। কিন্তু স্বাধীনতার পরপরই অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে সামরিক শাসন এবং পরবর্তী সময়ে গণতান্ত্রিক ধারার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিটি পর্যায়ে জনগণের ভূমিকা নিম্নমুখী হলো, রাজনীতি অনেকটাই দলীয়করণ ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক হয়ে পড়ল। সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর হারিয়ে গেল প্রভাবশালী গোষ্ঠীর কাছে। ফলে রাষ্ট্র গঠনের যে স্বপ্ন ছিল জনগণের জন্য, তা অনেক সময় দলীয় কিংবা ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর সময় এসেছে, আমরা কেমন রাজনীতি চাই?
অনেক দিন থেকে দেশ ও জনগণের সেবা করার বুলি আওড়ানো অনেক রাজনীতিবিদের দেখা মেলে শুধু ভোটের মৌসুমে। যেহেতু ঘনিয়ে আসছে জাতীয় নির্বাচন, রাজনীতির মাঠ তাই এখন ভোটের শোরগোলে ব্যস্ত। যেখানে আছে প্রত্যাশা, কৌশল, আবার আশঙ্কাও। যদিও নির্বাচন কমিশন এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করেনি। তবু বিভিন্ন দলীয় ও স্বতন্ত্র সম্ভাব্য প্রার্থীরা ইতিমধ্যেই নির্বাচনী এলাকায় ছুটে বেড়াচ্ছেন। গ্রাম থেকে শহর—সব জায়গায় শুরু হয়েছে প্রচারণার তোড়জোড়। প্রার্থীরা ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন, দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি।
কিন্তু জনগণ খুব সহজে তা বিশ্বাস করছে না। কারণ, বাস্তবতা হলো, নির্বাচনের পর প্রার্থীরা অনেক সময়ই হারিয়ে যান। অতীতে দেখা গেছে, ভোটে জয়ের পর অনেক নেতা জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না।
তবে এও সত্য, অনেক নেতা এখনো আন্তরিকভাবে জনগণের কল্যাণে কাজ করার জন্য ভাবেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে দলীয় আনুগত্য ও ব্যক্তিস্বার্থের কারণে তাঁরা বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেন না। তবে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ফলে জনগণের ভাবনায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। জনগণ এখন চায় এমন রাজনীতি, যেখানে সর্বস্তরে সুশাসন, ন্যায্যতা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। অন্যদিকে রাজনীতিবিদদেরও আত্মসমালোচনার সময় এসেছে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়া মানে কেবল কাঙ্ক্ষিত আসন পাওয়া নয়, বরং জনগণের আশা ও প্রয়োজন বুঝে সেগুলোর প্রতিফলন ঘটানো। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আমাদের রাজনীতিতে এই দায়বদ্ধতা প্রায়ই অনুপস্থিত। নির্বাচনের সময় জনগণকে মনে রাখা হয়, কিন্তু ক্ষমতায় গিয়েই ভুলে যাওয়া হয় তাদের কষ্ট, তাদের স্বপ্ন।
দীর্ঘদিন ধরে জনগণকে কেবল দল ও নেতারা শুধু ভোটদাতা হিসেবে ভেবে এসেছেন। যদিও গণতন্ত্র কেবল ভোটের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি একটি অংশগ্রহণ প্রক্রিয়াও, যেখানে জনগণ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে সরকারের কাজের জবাবদিহি করবে। তবে বাংলাদেশের গণতন্ত্র এখন অনেকটাই আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এর সবচেয়ে বড় কারণ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চায় ব্যাপক ঘাটতির কারণে। তা ছাড়া, আন্তদলীয় কোন্দল এবং বিরোধীমতকে অনেক সময় দমন করার রীতিও বহুল প্রচলিত। এই বিষয়গুলোর ফলে জনগণ রাজনীতিতে অনেকাংশে আস্থা হারাচ্ছে। ফলে রাজনীতি আর জনগণের থাকছে না, হয়ে উঠছে বিশেষ গোষ্ঠীর সম্পত্তি।
আজকের রাজনীতি জনগণের জীবনের সঙ্গে কতটা সম্পর্কিত—এই প্রশ্নটি জরুরি। কেননা, রাজনীতির প্রতিটি সিদ্ধান্তই দেশের অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নেতৃত্বের সীমাবদ্ধতা ও জনগণের অংশগ্রহণের অভাব—উভয়কেই প্রতিফলিত করছে। গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জনগণ নিজস্ব মতামত দিচ্ছে, কিন্তু সেই আওয়াজ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে কতটা প্রতিফলিত হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ আছে। যখন রাজনীতি জনগণকেন্দ্রিক হয়, তখন স্থানীয় অভিজ্ঞতা ও চাহিদা নীতি প্রণয়নে প্রতিফলিত হওয়ার কথা। কিন্তু উল্টো ঘটনা ঘটে, নীতি তৈরি হয় অনেকাংশে প্রভাবশালী গোষ্ঠী এবং বাণিজ্যিক স্বার্থ অনুযায়ী।
রাজনীতির এই সংকটে তরুণদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের সবচেয়ে বড় জনগোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বেও তরুণেরা রাজনীতিতে যথাযথ প্রতিনিধিত্ব পায় না। স্থানীয় পর্যায় থেকে রাজনীতির মূলধারার আলোচনায় তারা একপ্রকার অনুপস্থিতই থেকে যায়।
তবে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। দীর্ঘদিনের স্বৈরশাসনের অবসান হয়েছে। তবে জনগণের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন আসবে, বাস্তবিক অর্থে তেমন মৌলিক পরিবর্তন প্রতিফলিত হয়নি। জনপ্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কিংবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কিছু রদবদল হয়েছে মাত্র।
তবু বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এখনো রাজনীতিতে আস্থা রাখে, বিশ্বাস করে পরিবর্তনের সম্ভাবনায়। প্রত্যাশা থাকে এমন রাজনীতির; যেখানে উন্নয়ন মানে কেবল অবকাঠামোগত সংস্কার নয়, বরং কৃষকের ন্যায্যমূল্য ও শ্রমিকের মজুরি থেকে শুরু করে যুবকের কর্মসংস্থান, প্রত্যাশিত স্বাস্থ্যসেবায় সংস্কার, পরিবহনে শৃঙ্খলা, নদী দখল বন্ধ, বাকস্বাধীনতা, নারীর নিরাপত্তা ও ন্যায্য অংশগ্রহণ এবং রাষ্ট্রের সর্বস্তরে আইনের সুশাসন নিশ্চিত হবে।
এ ছাড়া আমলাতান্ত্রিক জটিলতা থেকে পরিত্রাণ চায় জনগণ। গ্রামগঞ্জ-শহরে সর্বত্র মানুষ এখন চায় শান্তির সুবাতাস। ভোটাররা এখন আগের চেয়ে যথেষ্ট সচেতন; তারা জানে একজন সৎ ও দক্ষ জনপ্রতিনিধি পুরো এলাকার চেহারা বদলে দিতে পারেন।
এখন প্রয়োজন এমন রাজনীতি, যেখানে উন্নয়ন হবে অংশগ্রহণমূলক, সিদ্ধান্ত আসবে জনগণের মাঠঘাট থেকে, আর বাস্তবায়ন করবেন জনপ্রতিনিধি। রাজনীতি হতে হবে এমন এক চুক্তি, যেখানে ভোটের বিনিময়ে প্রতিশ্রুতি নয়, বরং বিশ্বাসের বন্ধনে সেই সম্পর্ক গড়ে উঠবে। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের পর মানুষের মনোজগতে যে পরিবর্তন এসেছে, রাজনৈতিক দলগুলোকে সেটি উপলব্ধি করতে হবে। তাদের নীতি-পরিকল্পনায় পরিবর্তনটা ধারণ করতে হবে। বুঝতে হবে যেনতেনভাবে একটা নির্বাচনই শেষ কথা নয়। রাজনৈতিক দলগুলোকে সংস্কারের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।
রাজনীতির সৌন্দর্য তখনই ফুটে ওঠে, যখন সেটি জনগণের জীবনের সঙ্গে মিশে যায়। তাই প্রয়োজন এমন নেতৃত্ব, যা জনগণকে কেবল ভোটার নয়, বরং পরিবর্তনের অংশীদার হিসেবে দেখবে। বহুমাত্রিক রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ধারণ করতে না পারলে জনগণ যে স্বপ্ন দেখছে, তা ফিকে হয়ে যাবে। তাই রাজনীতি হোক জনগণের হাতে, জনগণের স্বার্থে এবং জনগণের জন্য।
লেখক: এমফিল গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৩৩ সালে ক্লারা জেটকিনের মৃত্যুর পর তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান লিখেছিল, ‘গ্র্যান্ডমাদার অব জার্মান কমিউনিজম’, অর্থাৎ ‘জার্মান সাম্যবাদের মাতামহ’! তাঁকে নারী দিবসের জননী বললে কি খুব ভুল হবে?
০৮ মার্চ ২০২২
এখন নাকি বানর আর শূকরের পালকেই দেখা যায় লাউয়াছড়ায়। বিরল প্রজাতির অনেক পাখি ও প্রাণী বাস করত এই সংরক্ষিত বনে। কিন্তু সেসব লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বনটিকে নিজেদের অভয়ারণ্য বলে হয়তো ভাবতে পারছে না তারা।
৬ ঘণ্টা আগে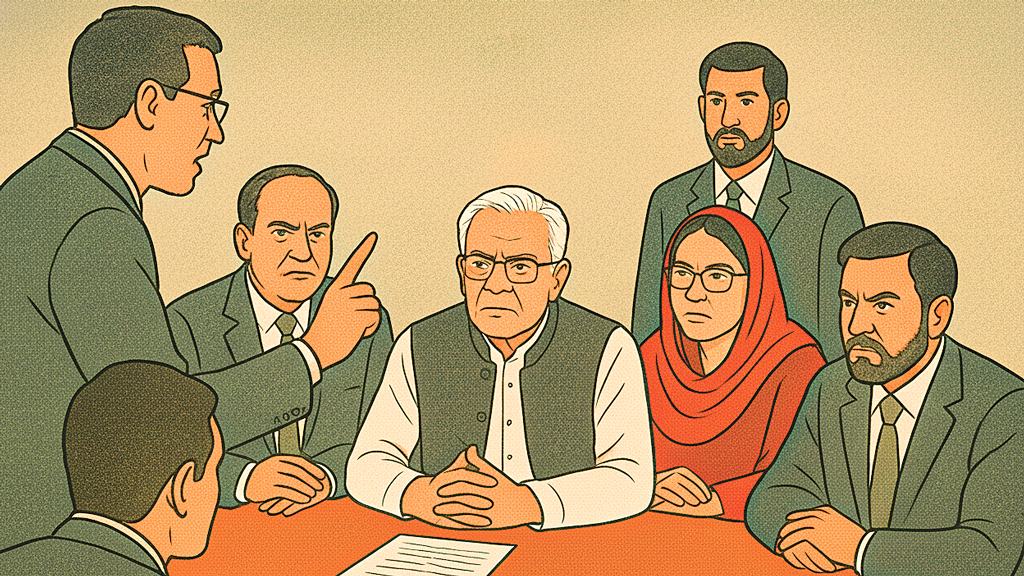
বিভাজন যেখানে ঘরে ঘরে, জনে জনে, সেখানে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া যথেষ্ট সাহসের কাজই বটে। অন্তর্বর্তী সরকার সেই সাহস দেখিয়েছিল। দেশি-প্রবাসী-বিদেশি একদল প্রাজ্ঞজনের সমন্বয়ে গঠন করেছিল জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। যদিও কমিশনের সভাপতি হিসেবে এর স্টিয়ারিং হুইল ছিল প্রধান উপদেষ্টা...
৬ ঘণ্টা আগে
মানুষের জীবনের শেষ অধ্যায় হলো অদৃশ্য বার্ধক্যের যাত্রা। কিন্তু সবাই বার্ধক্যের জীবনে সমান মর্যাদা পায় না। সমাজের প্রান্তিক এক শ্রেণি হলো যৌনকর্মীরা। যখন তাঁরা শেষ বয়সে পৌঁছান, তখন তাঁরা এক অনিশ্চিত জীবনের মধ্যে পড়ে যায়। যৌবনে যাঁদের দেহই ছিল আয়ের একমাত্র মূলধন, বার্ধক্যে এসে সেই দেহই যেন হয়ে...
৬ ঘণ্টা আগে