দেশ ও দশের সেবাই ছিল একসময় রাজনীতির মূল ভাবনা। সেই ভাবনা আমাদের রাজনীতি থেকে দূরে সরে গেছে। সেখানে আবার রাজনীতি ফিরে যাবে—এ রকম আশা এখন পর্যন্ত দুরাশা।
জাহীদ রেজা নূর

আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে এবং নির্বাচিত সরকার জনগণের ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে দেশ পরিচালনা করবে—এ রকম বিশ্বাস নানা কারণেই দোদুল্যমান হয়ে উঠছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন শর্ত আরোপ করায় নির্বাচন নিয়ে একটা ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে। নির্বাচন হলে যে দলটির জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল, তারা এরই মধ্যে এমন সব কাণ্ডের জন্ম দিচ্ছে, যাতে তাদের হাতে গণতন্ত্র কতটা নিরাপদ, তা নিয়েও প্রশ্ন জাগছে। তরুণদের নতুন যে দলটিকে নিয়ে আগ্রহী হয়েছিল জনগণ, পরবর্তীকালে সেই দলের কারও কারও আচরণে সেই আশা খুব বেশি টিকে থাকেনি।
সমাজের নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করে বলা যায়, সমাজে পরমতসহিষ্ণুতা কমেছে। রাজনীতির মাঠে ঘৃণা এসে রাজনৈতিক পরিবেশ নষ্ট করছে। সবচেয়ে বড় আঘাতটা এসেছে মুক্তিযুদ্ধের ওপর। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ক্ষমতাবলয়ে থাকা অনেকেই এমন সব কথা বলছেন, যার প্রকৃত অর্থ বোঝা দুষ্কর। সব মিলিয়ে যে লেজেগোবরে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে বের হওয়ার উপায় কী, সেটা অনেকেই বুঝে উঠতে পারছে না।
সাধারণ মানুষ আদতে ক্ষমতাহীন—একটি দিন ছাড়া। কেবল নির্বাচনের দিনেই সে ভোট দিতে এবং তার মতামত স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করতে পারে। সাধারণ মানুষের জন্য নির্বাচনী আবহ তৈরি করে দেওয়া যায় আইনের শাসন কায়েম করে। অস্বীকার করা যাবে না, ভোটার নির্ভয়ে ভোটকেন্দ্রে যাবেন এবং নিজ পছন্দে ভোট দেবেন, এই বিশ্বাস বহুকাল আগেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ‘জোর যার মুল্লুক তার’ আবহ নির্বাচনের মাঠে বিরাজ করে। এখন পর্যন্ত এমন কোনো সরকার আসেনি, যারা ভোটের মাঠে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে চায়নি।
তত্ত্বাবধায়ক সরকারগুলোর আমল কিছুটা আশার আলো দেখিয়েছিল বটে, কিন্তু রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের সময় নানা রকম টালবাহানা তৈরি করে ব্যবস্থাটাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছিলেন। এরপর আওয়ামী লীগ আমলে তো তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাই বাতিল করা হলো। ফিরে এল ক্ষমতাসীন সরকার স্থিত থাকা অবস্থায় নির্বাচন, যার পরিণতিতে কী হয়েছে, সেটা সবাই দেখেছে। পরপর তিনটি নির্বাচন হয়েছে, যা ছিল প্রহসনের অপর নাম। সেসব নির্বাচনে বেশির ভাগ মানুষই ভোটকেন্দ্রে যাওয়া থেকে বিরত থেকেছে। নির্বাচন বলতে যা বোঝায়, তার আয়োজন করা হয়নি।
২. আমরা যে গণতান্ত্রিক সমাজের কথা ভাবি, সেই সমাজ গড়ে তুলতে হলে যে নিষ্ঠা, সততা, আদর্শের প্রতি বিশ্বাস থাকা দরকার, তা কি বিরাজ করছে? মোটা দাগে গণতন্ত্র হয়ে গেছে নির্বাচনের মাধ্যমে একটি দলকে ক্ষমতায় বসানো। এরপর সেই দল তার নিজের মতো করে দেশ চালাবে। দেশ চালানোর সময় তার দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়ন করা হলো কি হলো না, তা নিয়ে আর না ভাবলেও চলবে। এ দেশে মনোনয়ন-বাণিজ্য নিয়ে কত কথা বাতাসে উড়ে বেড়ায়, তার কি ইয়ত্তা আছে? মনোনয়ন পেতে হলে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢালতে হয় পার্টির মধ্যে—নির্বাচনের সময় এ রকম কথাই তো শোনা যায়।
তৃণমূলে খাঁটি রাজনীতিবিদদের এড়িয়ে টাকার মালিকদের যখন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি করা শুরু হলো, তখন থেকেই ক্ষমতার রাজনীতি প্রবল হয়েছে। সংসদ ভরে গেছে টাকাওয়ালা মানুষে। দেখা গেছে, যে অর্থ খরচ করে তাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন, সেই অর্থের কয়েক গুণ (কয়েক শ বা কয়েক হাজার গুণ নাই-বা বললাম) উঠিয়ে নেওয়াটাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা (অর্থাৎ, মনোনয়ন পাওয়ার জন্য অর্থ ব্যয়) এবং নির্বাচিত হওয়া—দুটোই হয়ে উঠেছে ব্যবসা। দেশ ও দশের সেবাই ছিল একসময় রাজনীতির মূল ভাবনা। সেই ভাবনা আমাদের রাজনীতি থেকে দূরে সরে গেছে। সেখানে আবার রাজনীতি ফিরে যাবে—এ রকম আশা এখন পর্যন্ত দুরাশা।
৩. লক্ষ করে দেখবেন, গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলার সময় প্রত্যেকে গণতন্ত্রের মৌলিক দিকগুলো নিয়েই কথা বলেন। কথা শুনে মনে হয়, গণতন্ত্র তাঁর হাতেই সুরক্ষিত থাকবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় শাসনক্ষমতার উৎস জনগণ—এ কথা কতবার কত মুখে শোনা হয়েছে! কিন্তু বাস্তবে কী দেখা গেছে? গণতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করছি। সচেতন পাঠক তারই আলোকে নিজেই বিশ্লেষণ করবেন, আমরা রাষ্ট্রকে গণতন্ত্রের কতটা উপহার দিতে পেরেছি।
প্রথমত, গণতন্ত্রে জনগণ ভোট প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গনির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক সবার থাকবে ভোটাধিকার। জনগণ ও গণমাধ্যম স্বাধীনভাবে তাদের মত প্রকাশ করবে। সরকারের সমালোচনা করলে সরকারপক্ষ তেড়ে আসবে না, বরং সমালোচনার আলোকে নিজ ভুলগুলো শুধরে নেবে। তথ্য পাওয়া ও তা প্রচার করার অধিকার থাকতে হবে নাগরিকের। প্রচলিত আইনের বাইরে কেউ থাকবে না। একজন সাধারণ মানুষের জন্য যে আইন, একজন জনপ্রতিনিধি বা সরকারপ্রধানের জন্যও একই আইন প্রচলিত থাকবে। আইন ভঙ্গ করলে প্রত্যেককেই বিচার ও শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। বিচার বিভাগ কাজ করবে স্বাধীনভাবে।
বহুদলীয় গণতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে, নিবন্ধিত সব দলই নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে। নিয়মিতভাবে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের আয়োজন করতে হবে। এসব কথা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রমাত্রই জানেন।
নির্বাচন গণতন্ত্রের একটিমাত্র দিক হলেও আমরা যেন গোড়া থেকেই শুধু নির্বাচনে আটকে আছি। নির্বাচন যথাযথভাবে হলেই গণতন্ত্র রক্ষা পেল—এ রকম ভাবনাও প্রচলিত। গণতন্ত্র সমুন্নত রাখতে হলে যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, মানবাধিকারের নিশ্চয়তা, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রয়োজন আছে, সে কথা বেমালুম ভুলে যাই আমরা। সরকারে থাকেন যাঁরা, তাঁরা গণতন্ত্রের জন্য দরকারি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে খুব একটা উচ্চবাচ্য করেন না। অনির্বাচিত সরকার তো বটেই, নির্বাচিত সরকারও এসব অধিকার পাশ কাটিয়ে যেতে পছন্দ করে।
৪. গণতন্ত্র থেকে স্বৈরতন্ত্রের দূরত্ব বিঘতখানেক বা তার চেয়েও কম। গণতন্ত্রে ক্ষমতার উৎস জনগণ, স্বৈরতন্ত্রে এক ব্যক্তি বা একটি দল। কিন্তু গণতন্ত্রেও এক ব্যক্তি এমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেন, যা গণতন্ত্রের মধ্যে স্বৈরতন্ত্রকে ফুটিয়ে তুলতে পারে। গণতন্ত্রের মধ্যে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করা হলে তা স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবেরই প্রকাশ। বিভিন্নভাবে সরকার মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করে থাকে। আমাদের সাংবাদিকতা জগতে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে। পাকিস্তান আমলে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার কয়েকটি লেখা এখানে প্রণিধানযোগ্য। স্বাধীনতার পরে উত্থিত সাংবাদিকতার সমস্যাগুলো ও তার প্রতিকারের উপায় সেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ, সেই সমস্যাগুলো এখনো আমরা কাটিয়ে উঠতে পারিনি।
৫. এই মুহূর্তে আমাদের গণতন্ত্রের সংকটের তিনটি বিষয়ে কথা বলি। প্রথমত, শিক্ষা। প্রাথমিক স্তর থেকে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাতে যুক্তিসম্মতভাবে ভাববার ক্ষমতা জন্মানোর মতো উপাদান থাকতে হবে। পরমতসহিষ্ণুতার শিক্ষা থাকতে হবে। আমাদের দেশে প্রকৃত শিক্ষক তৈরি করা খুব প্রয়োজন। তবে সংকট এখানেও আছে। শিক্ষা দেওয়ার সময় সততা, নৈতিকতার যে কথা বলা হবে, বাস্তবে যদি অসৎ ও অনৈতিক ব্যক্তিরই জয়জয়কার দেখা যায়, তাহলে সেই শিক্ষা কোনো কাজে লাগবে না। শিক্ষিত মানুষ তার যৌক্তিক মন কাজে লাগিয়ে এই সংকটকে বিদায় করবে। এর জন্য দূরবর্তী লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে।
দ্বিতীয় বিষয়টি এখান থেকেই উঠে আসে। রাজনীতিবিদেরা যদি দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন, বদলি-বাণিজ্য, দরপত্র-বাণিজ্য, ব্যাংকের টাকা আত্মসাৎসহ নানা অপকর্মে যুক্ত হয়ে পড়েন, তখন জনগণের মধ্যে যে অনাস্থা তৈরি হয়, তাতে গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা নড়ে যায়। এই সুযোগে উগ্র রাজনীতি ঢুকে যেতে পারে রাষ্ট্রকাঠামোয়। এই দিকে নজর রাখা জরুরি।
তৃতীয় বিষয়টিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার এতটাই বেড়েছে যে তার প্রভাব পড়েছে গোটা দেশের মানুষের ওপর। সংবাদপত্র বা ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে ছাপিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। সংবাদ সেখানে সহজেই পাওয়া যায়। ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটক ব্যবহারে সতর্কতা প্রয়োজন। এই মাধ্যমগুলোয় যে ধরনের উগ্র ভাষা ব্যবহার করা হয়, অসত্য তথ্য প্রদান করে উসকে দেওয়া হয়, তা মানুষের চিন্তা পদ্ধতিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। সাধারণ মানুষের পক্ষে এই অশুভ ও অসত্য প্রচারণা শনাক্ত করা কঠিন হয়। ফলে নেটজুড়ে যে অসত্য ছড়ানো হয়, উসকানি দেওয়া হয়, তা অনেক ক্ষেত্রেই গণতন্ত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে দেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র উপহার পাবে, সে কথা ভাবতে ভালো লাগে। কিন্তু এই ভাবনা কতটা বাস্তবসম্মত, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়।
লেখক: উপসম্পাদক, আজকের পত্রিকা

আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে এবং নির্বাচিত সরকার জনগণের ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে দেশ পরিচালনা করবে—এ রকম বিশ্বাস নানা কারণেই দোদুল্যমান হয়ে উঠছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন শর্ত আরোপ করায় নির্বাচন নিয়ে একটা ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে। নির্বাচন হলে যে দলটির জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল, তারা এরই মধ্যে এমন সব কাণ্ডের জন্ম দিচ্ছে, যাতে তাদের হাতে গণতন্ত্র কতটা নিরাপদ, তা নিয়েও প্রশ্ন জাগছে। তরুণদের নতুন যে দলটিকে নিয়ে আগ্রহী হয়েছিল জনগণ, পরবর্তীকালে সেই দলের কারও কারও আচরণে সেই আশা খুব বেশি টিকে থাকেনি।
সমাজের নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করে বলা যায়, সমাজে পরমতসহিষ্ণুতা কমেছে। রাজনীতির মাঠে ঘৃণা এসে রাজনৈতিক পরিবেশ নষ্ট করছে। সবচেয়ে বড় আঘাতটা এসেছে মুক্তিযুদ্ধের ওপর। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ক্ষমতাবলয়ে থাকা অনেকেই এমন সব কথা বলছেন, যার প্রকৃত অর্থ বোঝা দুষ্কর। সব মিলিয়ে যে লেজেগোবরে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে বের হওয়ার উপায় কী, সেটা অনেকেই বুঝে উঠতে পারছে না।
সাধারণ মানুষ আদতে ক্ষমতাহীন—একটি দিন ছাড়া। কেবল নির্বাচনের দিনেই সে ভোট দিতে এবং তার মতামত স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করতে পারে। সাধারণ মানুষের জন্য নির্বাচনী আবহ তৈরি করে দেওয়া যায় আইনের শাসন কায়েম করে। অস্বীকার করা যাবে না, ভোটার নির্ভয়ে ভোটকেন্দ্রে যাবেন এবং নিজ পছন্দে ভোট দেবেন, এই বিশ্বাস বহুকাল আগেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ‘জোর যার মুল্লুক তার’ আবহ নির্বাচনের মাঠে বিরাজ করে। এখন পর্যন্ত এমন কোনো সরকার আসেনি, যারা ভোটের মাঠে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে চায়নি।
তত্ত্বাবধায়ক সরকারগুলোর আমল কিছুটা আশার আলো দেখিয়েছিল বটে, কিন্তু রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের সময় নানা রকম টালবাহানা তৈরি করে ব্যবস্থাটাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছিলেন। এরপর আওয়ামী লীগ আমলে তো তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাই বাতিল করা হলো। ফিরে এল ক্ষমতাসীন সরকার স্থিত থাকা অবস্থায় নির্বাচন, যার পরিণতিতে কী হয়েছে, সেটা সবাই দেখেছে। পরপর তিনটি নির্বাচন হয়েছে, যা ছিল প্রহসনের অপর নাম। সেসব নির্বাচনে বেশির ভাগ মানুষই ভোটকেন্দ্রে যাওয়া থেকে বিরত থেকেছে। নির্বাচন বলতে যা বোঝায়, তার আয়োজন করা হয়নি।
২. আমরা যে গণতান্ত্রিক সমাজের কথা ভাবি, সেই সমাজ গড়ে তুলতে হলে যে নিষ্ঠা, সততা, আদর্শের প্রতি বিশ্বাস থাকা দরকার, তা কি বিরাজ করছে? মোটা দাগে গণতন্ত্র হয়ে গেছে নির্বাচনের মাধ্যমে একটি দলকে ক্ষমতায় বসানো। এরপর সেই দল তার নিজের মতো করে দেশ চালাবে। দেশ চালানোর সময় তার দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়ন করা হলো কি হলো না, তা নিয়ে আর না ভাবলেও চলবে। এ দেশে মনোনয়ন-বাণিজ্য নিয়ে কত কথা বাতাসে উড়ে বেড়ায়, তার কি ইয়ত্তা আছে? মনোনয়ন পেতে হলে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢালতে হয় পার্টির মধ্যে—নির্বাচনের সময় এ রকম কথাই তো শোনা যায়।
তৃণমূলে খাঁটি রাজনীতিবিদদের এড়িয়ে টাকার মালিকদের যখন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি করা শুরু হলো, তখন থেকেই ক্ষমতার রাজনীতি প্রবল হয়েছে। সংসদ ভরে গেছে টাকাওয়ালা মানুষে। দেখা গেছে, যে অর্থ খরচ করে তাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন, সেই অর্থের কয়েক গুণ (কয়েক শ বা কয়েক হাজার গুণ নাই-বা বললাম) উঠিয়ে নেওয়াটাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা (অর্থাৎ, মনোনয়ন পাওয়ার জন্য অর্থ ব্যয়) এবং নির্বাচিত হওয়া—দুটোই হয়ে উঠেছে ব্যবসা। দেশ ও দশের সেবাই ছিল একসময় রাজনীতির মূল ভাবনা। সেই ভাবনা আমাদের রাজনীতি থেকে দূরে সরে গেছে। সেখানে আবার রাজনীতি ফিরে যাবে—এ রকম আশা এখন পর্যন্ত দুরাশা।
৩. লক্ষ করে দেখবেন, গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলার সময় প্রত্যেকে গণতন্ত্রের মৌলিক দিকগুলো নিয়েই কথা বলেন। কথা শুনে মনে হয়, গণতন্ত্র তাঁর হাতেই সুরক্ষিত থাকবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় শাসনক্ষমতার উৎস জনগণ—এ কথা কতবার কত মুখে শোনা হয়েছে! কিন্তু বাস্তবে কী দেখা গেছে? গণতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করছি। সচেতন পাঠক তারই আলোকে নিজেই বিশ্লেষণ করবেন, আমরা রাষ্ট্রকে গণতন্ত্রের কতটা উপহার দিতে পেরেছি।
প্রথমত, গণতন্ত্রে জনগণ ভোট প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গনির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক সবার থাকবে ভোটাধিকার। জনগণ ও গণমাধ্যম স্বাধীনভাবে তাদের মত প্রকাশ করবে। সরকারের সমালোচনা করলে সরকারপক্ষ তেড়ে আসবে না, বরং সমালোচনার আলোকে নিজ ভুলগুলো শুধরে নেবে। তথ্য পাওয়া ও তা প্রচার করার অধিকার থাকতে হবে নাগরিকের। প্রচলিত আইনের বাইরে কেউ থাকবে না। একজন সাধারণ মানুষের জন্য যে আইন, একজন জনপ্রতিনিধি বা সরকারপ্রধানের জন্যও একই আইন প্রচলিত থাকবে। আইন ভঙ্গ করলে প্রত্যেককেই বিচার ও শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। বিচার বিভাগ কাজ করবে স্বাধীনভাবে।
বহুদলীয় গণতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে, নিবন্ধিত সব দলই নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে। নিয়মিতভাবে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের আয়োজন করতে হবে। এসব কথা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রমাত্রই জানেন।
নির্বাচন গণতন্ত্রের একটিমাত্র দিক হলেও আমরা যেন গোড়া থেকেই শুধু নির্বাচনে আটকে আছি। নির্বাচন যথাযথভাবে হলেই গণতন্ত্র রক্ষা পেল—এ রকম ভাবনাও প্রচলিত। গণতন্ত্র সমুন্নত রাখতে হলে যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, মানবাধিকারের নিশ্চয়তা, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রয়োজন আছে, সে কথা বেমালুম ভুলে যাই আমরা। সরকারে থাকেন যাঁরা, তাঁরা গণতন্ত্রের জন্য দরকারি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে খুব একটা উচ্চবাচ্য করেন না। অনির্বাচিত সরকার তো বটেই, নির্বাচিত সরকারও এসব অধিকার পাশ কাটিয়ে যেতে পছন্দ করে।
৪. গণতন্ত্র থেকে স্বৈরতন্ত্রের দূরত্ব বিঘতখানেক বা তার চেয়েও কম। গণতন্ত্রে ক্ষমতার উৎস জনগণ, স্বৈরতন্ত্রে এক ব্যক্তি বা একটি দল। কিন্তু গণতন্ত্রেও এক ব্যক্তি এমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেন, যা গণতন্ত্রের মধ্যে স্বৈরতন্ত্রকে ফুটিয়ে তুলতে পারে। গণতন্ত্রের মধ্যে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করা হলে তা স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবেরই প্রকাশ। বিভিন্নভাবে সরকার মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করে থাকে। আমাদের সাংবাদিকতা জগতে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে। পাকিস্তান আমলে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার কয়েকটি লেখা এখানে প্রণিধানযোগ্য। স্বাধীনতার পরে উত্থিত সাংবাদিকতার সমস্যাগুলো ও তার প্রতিকারের উপায় সেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ, সেই সমস্যাগুলো এখনো আমরা কাটিয়ে উঠতে পারিনি।
৫. এই মুহূর্তে আমাদের গণতন্ত্রের সংকটের তিনটি বিষয়ে কথা বলি। প্রথমত, শিক্ষা। প্রাথমিক স্তর থেকে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাতে যুক্তিসম্মতভাবে ভাববার ক্ষমতা জন্মানোর মতো উপাদান থাকতে হবে। পরমতসহিষ্ণুতার শিক্ষা থাকতে হবে। আমাদের দেশে প্রকৃত শিক্ষক তৈরি করা খুব প্রয়োজন। তবে সংকট এখানেও আছে। শিক্ষা দেওয়ার সময় সততা, নৈতিকতার যে কথা বলা হবে, বাস্তবে যদি অসৎ ও অনৈতিক ব্যক্তিরই জয়জয়কার দেখা যায়, তাহলে সেই শিক্ষা কোনো কাজে লাগবে না। শিক্ষিত মানুষ তার যৌক্তিক মন কাজে লাগিয়ে এই সংকটকে বিদায় করবে। এর জন্য দূরবর্তী লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে।
দ্বিতীয় বিষয়টি এখান থেকেই উঠে আসে। রাজনীতিবিদেরা যদি দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন, বদলি-বাণিজ্য, দরপত্র-বাণিজ্য, ব্যাংকের টাকা আত্মসাৎসহ নানা অপকর্মে যুক্ত হয়ে পড়েন, তখন জনগণের মধ্যে যে অনাস্থা তৈরি হয়, তাতে গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা নড়ে যায়। এই সুযোগে উগ্র রাজনীতি ঢুকে যেতে পারে রাষ্ট্রকাঠামোয়। এই দিকে নজর রাখা জরুরি।
তৃতীয় বিষয়টিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার এতটাই বেড়েছে যে তার প্রভাব পড়েছে গোটা দেশের মানুষের ওপর। সংবাদপত্র বা ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে ছাপিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। সংবাদ সেখানে সহজেই পাওয়া যায়। ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটক ব্যবহারে সতর্কতা প্রয়োজন। এই মাধ্যমগুলোয় যে ধরনের উগ্র ভাষা ব্যবহার করা হয়, অসত্য তথ্য প্রদান করে উসকে দেওয়া হয়, তা মানুষের চিন্তা পদ্ধতিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। সাধারণ মানুষের পক্ষে এই অশুভ ও অসত্য প্রচারণা শনাক্ত করা কঠিন হয়। ফলে নেটজুড়ে যে অসত্য ছড়ানো হয়, উসকানি দেওয়া হয়, তা অনেক ক্ষেত্রেই গণতন্ত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে দেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র উপহার পাবে, সে কথা ভাবতে ভালো লাগে। কিন্তু এই ভাবনা কতটা বাস্তবসম্মত, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়।
লেখক: উপসম্পাদক, আজকের পত্রিকা

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হিন্দু-মুসলমান বিরোধ প্রসঙ্গে গালাগালিকে গলাগলিতে রূপান্তরিত করতে বলেছিলেন একদা। তাঁর এই পরামর্শ কতটা কাজে লেগেছে, তা নিয়ে আর মন্তব্য না করাই ভালো। ন্যূনতম সহনশীলতারও মৃত্যু হয়েছে কি না, তা নিয়েও ভাবছে মানুষ। রাজনীতির মাঠে প্রতিপক্ষকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি...
৮ ঘণ্টা আগে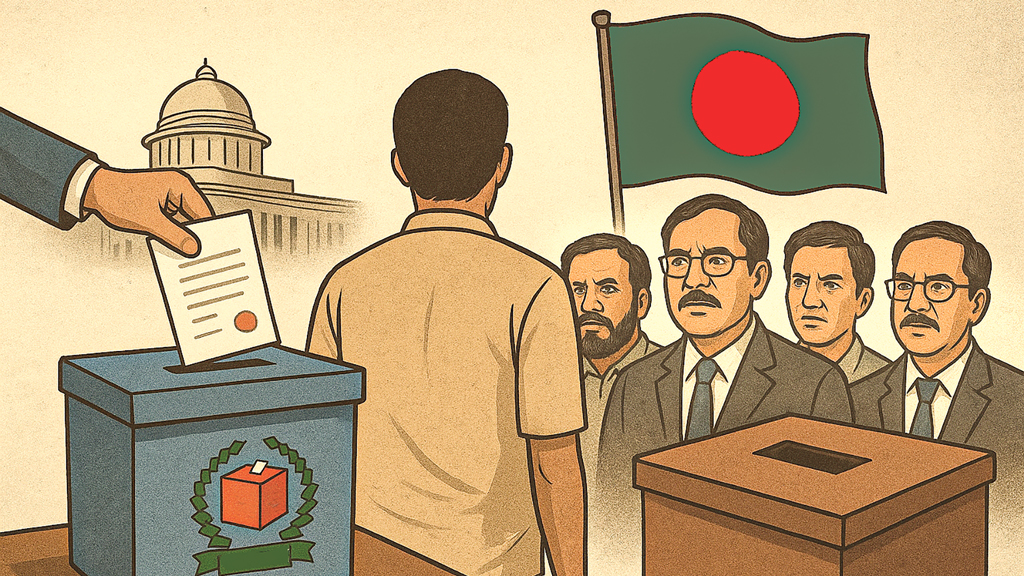
আগামী বছর ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে, পবিত্র রমজানের আগে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত বলেই ধরে নেওয়া যায়। যদিও দেশে-বিদেশে নির্বাচন নিয়ে ভিন্নতর জল্পনাও আছে। বিশেষ করে প্রবাসী কয়েকজন ইউটিউবার নানাভাবে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে নিশ্চিত নির্বাচনের বিষয়ে জনপরিসরে একটি সংশয় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।
৮ ঘণ্টা আগে
পৃথিবীর বহু দেশে শিক্ষকের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা উচ্চতর হলেও, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ চিত্র ভালো নয়। বিশেষ করে বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এ চিত্র বেশ হতাশাজনক ও বেদনাদায়ক। দুঃখজনক হলেও সত্য যে দীর্ঘদিন ধরে চলমান এ দুরবস্থা দূরীকরণে কোনো সরকারই কোনো আন্তরিকতা দেখায়নি।
৮ ঘণ্টা আগে
সমাজের অলিগলি, শহর থেকে প্রান্তরে আজ যেন একটিই মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে—‘জিপিএ-৫ পেলেই জীবন সফল’। অভিভাবকের চোখে সন্তানের সফলতা মাপা হয় সেই একটিমাত্র অঙ্কে। কিন্তু প্রশ্ন, একটি ফলাফল, একটি সংখ্যাই কি সত্যিই নির্ধারণ করতে পারে একজন মানুষের মেধা, মানসিকতা কিংবা ভবিষ্যৎ? মানুষের জীবনের গল্প কখনোই...
৮ ঘণ্টা আগে