শিক্ষা বাজেট ২০২৫-২৬
মোশাররফ তানসেন
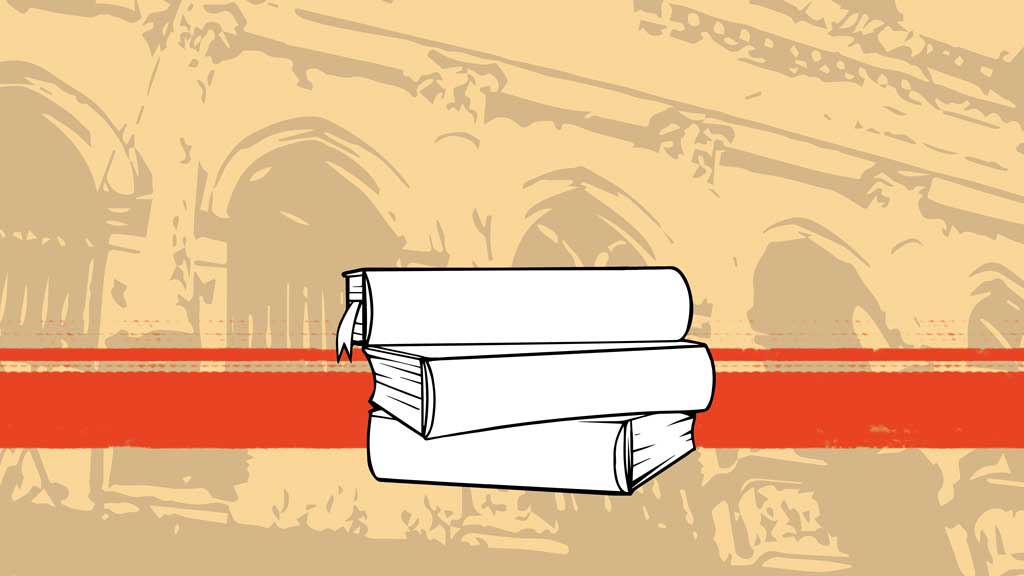
শিক্ষা শুধু একটি মৌলিক অধিকার নয়, এটি ব্যক্তি ও জাতির ক্ষমতায়নের সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো একটি তরুণ ও জনবহুল দেশে, যেখানে জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ ২৫ বছরের নিচে, সেখানে শিক্ষায় বিনিয়োগ কেবল মানবিক দায়িত্ব নয়, এটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষা খাতে ৯৫,৬৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা আগের বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ২৭ শতাংশ বেশি। এটি নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক অগ্রগতি। কিন্তু বরাদ্দ বাড়ার পাশাপাশি প্রশ্ন উঠেছে—এই অর্থের ব্যবহারে কি কোনো গুণগত পরিবর্তন এসেছে?
বাজেট কাঠামোর মধ্যে কি দৃষ্টিভঙ্গির কোনো রূপান্তর ঘটেছে?
বিশ্বের উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা অনুসরণ করে ইউনেসকো যেখানে জাতীয় বাজেটের ২০ এবং জিডিপির ৬ শতাংশ শিক্ষায় ব্যয় করার সুপারিশ করেছে, সেখানে বাংলাদেশ এখনো পিছিয়ে রয়েছে। এবারের বাজেটে শিক্ষায় বরাদ্দ জাতীয় বাজেটের ১২ দশমিক ১ এবং জিডিপির মাত্র ২ দশমিক ১ শতাংশ। এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায়, শুধু বরাদ্দ বাড়লেই উন্নয়নের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না—প্রয়োজন পরিকল্পিত ও দৃষ্টিভঙ্গিনির্ভর ব্যয়।
বরাদ্দের বাস্তব ব্যবহার ও কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ
শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়লেও প্রতিবছর বাজেটের ১৫-২০ শতাংশ অর্থ অব্যবহৃত থেকে যায়। এই অব্যবহৃত অর্থ ব্যবহারে প্রধান বাধা হলো পরিকল্পনার অভাব, প্রশাসনিক জটিলতা, দক্ষ জনবল ও স্থানীয় পর্যায়ে যথাযথ কাঠামোর অভাব। প্রকল্প গ্রহণের পর অনুমোদন, বাজেট ছাড়, সরবরাহ ক্রয় এবং বাস্তবায়নপ্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি উপজেলা ও বিদ্যালয় পর্যায়ে প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা ও কর্মীর ঘাটতি প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যাঘাত ঘটায়।
ফলে অনেক সময় দেখা যায়, শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের অর্থ বরাদ্দ থাকলেও ভবন হয় না, শিক্ষক পদ সৃষ্টি হলেও নিয়োগ হয় না, পাঠ্যবই মুদ্রণের টাকা থাকলেও সঠিক সময়ে বই পৌঁছায় না। প্রযুক্তি কেনা হলেও ব্যবহারের পরিবেশ সৃষ্টি হয় না। এ সমস্যা কাটাতে স্থানীয় শিক্ষা অফিস ও প্রধান শিক্ষকদের জন্য বাজেট ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, পর্যাপ্ত কারিগরি সহায়তা এবং একটি শক্তিশালী মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি।
তিন ধারায় বিভক্ত শিক্ষাব্যবস্থা
বাংলাদেশের শিক্ষা এখনো তিনটি ভিন্ন ধারায় বিভক্ত—বাংলা মাধ্যম, ইংরেজি মাধ্যম ও মাদ্রাসা। এর বাইরে ব্যক্তি সাহায্যে চলে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা, যেখানে কোনো রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ নেই। এই বিভাজন শুধু শিক্ষার পদ্ধতিগত পার্থক্য নয়, এটি ভবিষ্যতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করছে। ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিক কারিকুলাম ও সুযোগ-সুবিধা পায়, যা তাদের গ্লোবাল মার্কেটে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে রাখে। অন্যদিকে মাদ্রাসাশিক্ষার্থীরা ধর্মীয় শিক্ষা
পেলেও আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষতার ঘাটতিতে চাকরির বাজারে পিছিয়ে পড়ে। বাংলা মাধ্যমের শিক্ষার্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও, তাদের জন্য মানসম্পন্ন অবকাঠামো ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক অনেক সময়ই অনুপস্থিত।
এই বিভাজন দূর করতে হলে দরকার একটি একীভূত জাতীয় শিক্ষানীতি ও কারিকুলাম, যা সব শিক্ষার্থীকে সমান সুযোগ দেবে। এর মাধ্যমে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ঐক্যবদ্ধ সমাজ গঠনের ভিত্তি তৈরি হবে। দুঃখজনকভাবে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে এ বিভাজন দূরীকরণের জন্য কোনো নির্দিষ্ট বরাদ্দ বা কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়নি।
জলবায়ু সহনশীল শিক্ষা: বিলাসিতা নয়, প্রয়োজন
বাংলাদেশ একটি জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। উপকূলীয় অঞ্চল, চর, হাওর, পাহাড় ও নদীভাঙনপ্রবণ এলাকার শিশুরা প্রায়ই প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। দুর্যোগে বিদ্যালয় ধ্বংস হয়, পাঠদান বন্ধ হয় এবং শিক্ষার ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়। অথচ বাজেটে এই শিশুদের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো বরাদ্দ বা কার্যকর কৌশল নেই।
জলবায়ু সহনশীল শিক্ষা মানে শুধু টেকসই অবকাঠামো নয়; এটি প্রযুক্তিনির্ভর বিকল্প শিক্ষা, নৌ-বিদ্যালয়, মোবাইল স্কুল এবং দুর্যোগ-প্রস্তুতির পরিকল্পনাকে অন্তর্ভুক্ত করে। শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য, পুনর্বাসন এবং ঝুঁকি হ্রাসের দিকগুলো বাজেট পরিকল্পনার অংশ হওয়া উচিত। তাই এখন সময়, জলবায়ু সহনশীল শিক্ষায় পরিকল্পিত ও ধারাবাহিক বিনিয়োগকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার।
গুণগত শিক্ষার জন্য কী প্রয়োজন?
শিক্ষায় গুণগত মানের চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভর্তির হার যতই বাড়ুক, শিক্ষার্থীরা কী শিখছে এবং শেখা জীবনে কতটা প্রযোজ্য হচ্ছে, সেটিই মূল প্রশ্ন। গুণগত শিক্ষার জন্য প্রয়োজন অন্তত তিনটি প্রধান পদক্ষেপ:
১. শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও পেশাগত উন্নয়ন: দক্ষ ও প্রেরণাদায়ী শিক্ষক ছাড়া শিক্ষার মানোন্নয়ন
সম্ভব নয়। এই বাজেটে নিয়মিত প্রশিক্ষণ, মূল্যায়ন এবং পেশাগত সহায়তার জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ থাকা উচিত ছিল।
২. আধুনিক পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাসামগ্রী: বর্তমান পাঠ্যবই অনেকাংশে পুরোনো ও শিশুর চিন্তাশক্তি বিকাশে অপ্রতুল। একটি সময়োপযোগী, অংশগ্রহণমূলক ও প্রযুক্তিনির্ভর পাঠ্যক্রম তৈরি করা দরকার।
৩. নিরাপদ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার পরিবেশ: প্রান্তিক ও বৈষম্যের শিকার শিক্ষার্থীদের জন্য এমন শ্রেণিকক্ষ দরকার, যেখানে তারা নিরাপদ ও মর্যাদার সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।
বাজেট হোক একটি ভবিষ্যৎমুখী বিনিয়োগ
২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি একটি স্বাগতযোগ্য পদক্ষেপ; কিন্তু এটি তখনই অর্থবহ হবে যখন সেই অর্থ পরিকল্পিত, দক্ষ ও অন্তর্ভুক্তিমূলকভাবে ব্যয় হবে। এখনই সময় কাঠামোগত দুর্বলতা দূর করা, প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা এবং একটি একীভূত জাতীয় শিক্ষানীতির ভিত্তি গড়ে তোলা। যেন এই বাজেট কেবল সংখ্যার খেলা না হয়ে একটি দূরদর্শী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার রূপরেখা হয়ে ওঠে।
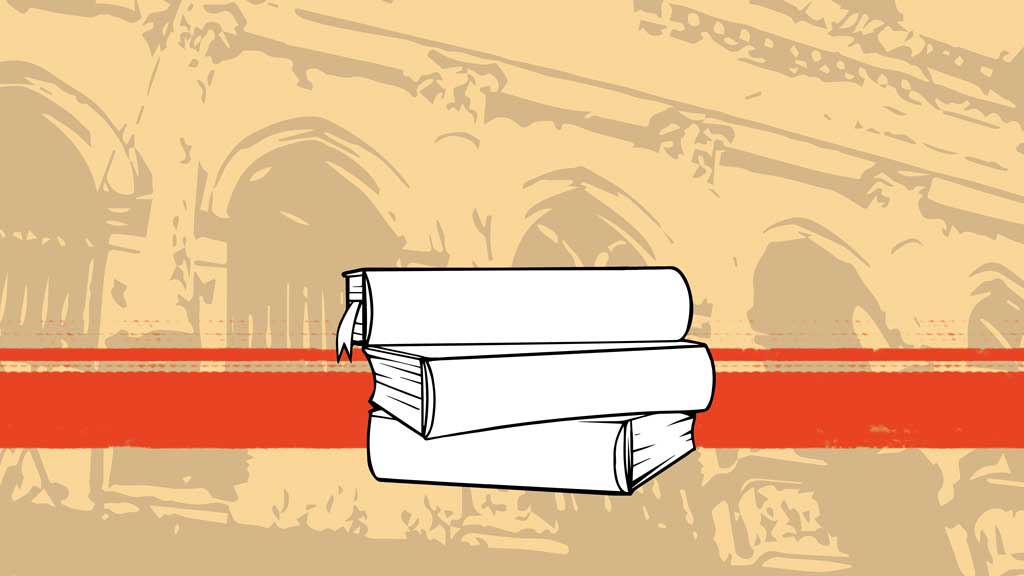
শিক্ষা শুধু একটি মৌলিক অধিকার নয়, এটি ব্যক্তি ও জাতির ক্ষমতায়নের সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো একটি তরুণ ও জনবহুল দেশে, যেখানে জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ ২৫ বছরের নিচে, সেখানে শিক্ষায় বিনিয়োগ কেবল মানবিক দায়িত্ব নয়, এটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষা খাতে ৯৫,৬৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা আগের বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ২৭ শতাংশ বেশি। এটি নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক অগ্রগতি। কিন্তু বরাদ্দ বাড়ার পাশাপাশি প্রশ্ন উঠেছে—এই অর্থের ব্যবহারে কি কোনো গুণগত পরিবর্তন এসেছে?
বাজেট কাঠামোর মধ্যে কি দৃষ্টিভঙ্গির কোনো রূপান্তর ঘটেছে?
বিশ্বের উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা অনুসরণ করে ইউনেসকো যেখানে জাতীয় বাজেটের ২০ এবং জিডিপির ৬ শতাংশ শিক্ষায় ব্যয় করার সুপারিশ করেছে, সেখানে বাংলাদেশ এখনো পিছিয়ে রয়েছে। এবারের বাজেটে শিক্ষায় বরাদ্দ জাতীয় বাজেটের ১২ দশমিক ১ এবং জিডিপির মাত্র ২ দশমিক ১ শতাংশ। এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায়, শুধু বরাদ্দ বাড়লেই উন্নয়নের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না—প্রয়োজন পরিকল্পিত ও দৃষ্টিভঙ্গিনির্ভর ব্যয়।
বরাদ্দের বাস্তব ব্যবহার ও কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ
শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়লেও প্রতিবছর বাজেটের ১৫-২০ শতাংশ অর্থ অব্যবহৃত থেকে যায়। এই অব্যবহৃত অর্থ ব্যবহারে প্রধান বাধা হলো পরিকল্পনার অভাব, প্রশাসনিক জটিলতা, দক্ষ জনবল ও স্থানীয় পর্যায়ে যথাযথ কাঠামোর অভাব। প্রকল্প গ্রহণের পর অনুমোদন, বাজেট ছাড়, সরবরাহ ক্রয় এবং বাস্তবায়নপ্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি উপজেলা ও বিদ্যালয় পর্যায়ে প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা ও কর্মীর ঘাটতি প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যাঘাত ঘটায়।
ফলে অনেক সময় দেখা যায়, শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের অর্থ বরাদ্দ থাকলেও ভবন হয় না, শিক্ষক পদ সৃষ্টি হলেও নিয়োগ হয় না, পাঠ্যবই মুদ্রণের টাকা থাকলেও সঠিক সময়ে বই পৌঁছায় না। প্রযুক্তি কেনা হলেও ব্যবহারের পরিবেশ সৃষ্টি হয় না। এ সমস্যা কাটাতে স্থানীয় শিক্ষা অফিস ও প্রধান শিক্ষকদের জন্য বাজেট ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, পর্যাপ্ত কারিগরি সহায়তা এবং একটি শক্তিশালী মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি।
তিন ধারায় বিভক্ত শিক্ষাব্যবস্থা
বাংলাদেশের শিক্ষা এখনো তিনটি ভিন্ন ধারায় বিভক্ত—বাংলা মাধ্যম, ইংরেজি মাধ্যম ও মাদ্রাসা। এর বাইরে ব্যক্তি সাহায্যে চলে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা, যেখানে কোনো রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ নেই। এই বিভাজন শুধু শিক্ষার পদ্ধতিগত পার্থক্য নয়, এটি ভবিষ্যতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করছে। ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিক কারিকুলাম ও সুযোগ-সুবিধা পায়, যা তাদের গ্লোবাল মার্কেটে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে রাখে। অন্যদিকে মাদ্রাসাশিক্ষার্থীরা ধর্মীয় শিক্ষা
পেলেও আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষতার ঘাটতিতে চাকরির বাজারে পিছিয়ে পড়ে। বাংলা মাধ্যমের শিক্ষার্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও, তাদের জন্য মানসম্পন্ন অবকাঠামো ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক অনেক সময়ই অনুপস্থিত।
এই বিভাজন দূর করতে হলে দরকার একটি একীভূত জাতীয় শিক্ষানীতি ও কারিকুলাম, যা সব শিক্ষার্থীকে সমান সুযোগ দেবে। এর মাধ্যমে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ঐক্যবদ্ধ সমাজ গঠনের ভিত্তি তৈরি হবে। দুঃখজনকভাবে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে এ বিভাজন দূরীকরণের জন্য কোনো নির্দিষ্ট বরাদ্দ বা কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়নি।
জলবায়ু সহনশীল শিক্ষা: বিলাসিতা নয়, প্রয়োজন
বাংলাদেশ একটি জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। উপকূলীয় অঞ্চল, চর, হাওর, পাহাড় ও নদীভাঙনপ্রবণ এলাকার শিশুরা প্রায়ই প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। দুর্যোগে বিদ্যালয় ধ্বংস হয়, পাঠদান বন্ধ হয় এবং শিক্ষার ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়। অথচ বাজেটে এই শিশুদের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো বরাদ্দ বা কার্যকর কৌশল নেই।
জলবায়ু সহনশীল শিক্ষা মানে শুধু টেকসই অবকাঠামো নয়; এটি প্রযুক্তিনির্ভর বিকল্প শিক্ষা, নৌ-বিদ্যালয়, মোবাইল স্কুল এবং দুর্যোগ-প্রস্তুতির পরিকল্পনাকে অন্তর্ভুক্ত করে। শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য, পুনর্বাসন এবং ঝুঁকি হ্রাসের দিকগুলো বাজেট পরিকল্পনার অংশ হওয়া উচিত। তাই এখন সময়, জলবায়ু সহনশীল শিক্ষায় পরিকল্পিত ও ধারাবাহিক বিনিয়োগকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার।
গুণগত শিক্ষার জন্য কী প্রয়োজন?
শিক্ষায় গুণগত মানের চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভর্তির হার যতই বাড়ুক, শিক্ষার্থীরা কী শিখছে এবং শেখা জীবনে কতটা প্রযোজ্য হচ্ছে, সেটিই মূল প্রশ্ন। গুণগত শিক্ষার জন্য প্রয়োজন অন্তত তিনটি প্রধান পদক্ষেপ:
১. শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও পেশাগত উন্নয়ন: দক্ষ ও প্রেরণাদায়ী শিক্ষক ছাড়া শিক্ষার মানোন্নয়ন
সম্ভব নয়। এই বাজেটে নিয়মিত প্রশিক্ষণ, মূল্যায়ন এবং পেশাগত সহায়তার জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ থাকা উচিত ছিল।
২. আধুনিক পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাসামগ্রী: বর্তমান পাঠ্যবই অনেকাংশে পুরোনো ও শিশুর চিন্তাশক্তি বিকাশে অপ্রতুল। একটি সময়োপযোগী, অংশগ্রহণমূলক ও প্রযুক্তিনির্ভর পাঠ্যক্রম তৈরি করা দরকার।
৩. নিরাপদ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার পরিবেশ: প্রান্তিক ও বৈষম্যের শিকার শিক্ষার্থীদের জন্য এমন শ্রেণিকক্ষ দরকার, যেখানে তারা নিরাপদ ও মর্যাদার সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।
বাজেট হোক একটি ভবিষ্যৎমুখী বিনিয়োগ
২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি একটি স্বাগতযোগ্য পদক্ষেপ; কিন্তু এটি তখনই অর্থবহ হবে যখন সেই অর্থ পরিকল্পিত, দক্ষ ও অন্তর্ভুক্তিমূলকভাবে ব্যয় হবে। এখনই সময় কাঠামোগত দুর্বলতা দূর করা, প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা এবং একটি একীভূত জাতীয় শিক্ষানীতির ভিত্তি গড়ে তোলা। যেন এই বাজেট কেবল সংখ্যার খেলা না হয়ে একটি দূরদর্শী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার রূপরেখা হয়ে ওঠে।

ডা. মুশতাক হোসেন এরশাদবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা, ডাকসুর সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং বাংলাদেশ জাসদের স্থায়ী কমিটির সদস্য। তিনি কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করেছেন। পেশাজীবনে রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ছিলেন।
১ দিন আগে
কুড়িল বিশ্বরোডের ফুটওভারব্রিজে দাঁড়িয়ে একটি খালের চমৎকার শোভা দেখে মুগ্ধ হচ্ছিলাম। ঢাকার বুকে এত সুন্দর একটা খাল! ধনুকের মতো বাঁক খেয়ে চলে গেছে দূরে, দুই পাড়ে হাঁটার রাস্তা। রাস্তা আর খালের পানির মাঝে সবুজ ঢাল সিঙ্গাপুর ডেইজির শায়িত লতায় আচ্ছাদিত।
১ দিন আগে
পিরোজপুরের নেছারাবাদে যে ঘটনা ঘটেছে, তার জন্য ইউএনও সাহেব ধন্যবাদ পেতেই পারেন। সেখানে একটি বিয়ের দাওয়াতে গিয়েছিলেন তিনি সপরিবারে। কিন্তু যখন জানতে পারলেন, বিয়ের কনে প্রাপ্তবয়স্ক নয়, তখন তিনি না খেয়েই ফিরে আসেন। এবং তিনি ফিরে আসায় কাজিও বিয়ে পড়াননি। ফলে এই বাল্যবিবাহ হয়নি।
১ দিন আগে
মিরপুরের শিয়ালবাড়ী এলাকায় একটি রাসায়নিক গুদামে আগুন লাগার পর যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল, সে কথা সবাই এখন জানেন। যাঁরা স্বজন হারিয়েছেন, তাঁরা জানেন এটা তাঁদের পরিবারের জন্য কত বড় ক্ষতি। নিহতদের পরিবার ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে কি না, তাদের জীবনে স্থিতি ফিরিয়ে আনতে কী করা দরকার...
২ দিন আগে
ডা. মুশতাক হোসেন এরশাদবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা, ডাকসুর সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং বাংলাদেশ জাসদের স্থায়ী কমিটির সদস্য। তিনি কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করেছেন। পেশাজীবনে রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ছিলেন। সিপিবি, বাসদ, বাসদ (মার্ক্সবাদী) ও বাংলাদেশ জাসদ—এ চারটি বামপন্থী দল জুলাই সনদে স্বাক্ষর না করার কারণ নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন আজকের পত্রিকার মাসুদ রানা।
মাসুদ রানা

আপনারা কেন জুলাই সনদে স্বাক্ষর না করার সিদ্ধান্ত নিলেন? আপনাদের মূল আপত্তিগুলো কী ছিল?
আমাদের প্রথম আপত্তি ছিল ‘নোট অব ডিসেন্ট’ বা ভিন্নমত সংযুক্ত না করা। যেসব বিষয়ে সবাই মিলে একমত হয়েছি বা মোটামুটি একমত হয়েছি, সেসব যুক্ত করা ছাড়া আমরা স্বাক্ষর করব না। যেহেতু ‘নোট অব ডিসেন্ট’সহ কিছু বিষয়ে আপত্তি ছিল, সেটা স্বাক্ষর করলে তো মেনে নেওয়া হতো। সেটা জাতীয় সংসদে হলে অন্য কথা ছিল বা কোনো রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে সেটা হতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সেটা মেনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ঐকমত্য কমিশন সে রকম কোনো ফোরাম না। এটা হচ্ছে রাজনৈতিকভাবে ঐকমত্যে আসার জন্য একটা চেষ্টা, একটা উদ্যোগ।
জুলাই সনদ তৈরি করার সময় এর পটভূমি ধরে আমরা ইতিহাসকে সঠিকভাবে লেখার জন্য বারবার ইনপুট দিয়েছি। আমাদের দলসহ অন্য দলের নেতারা সেটা বলেছেন। কিন্তু সনদে নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানকে পুরোপুরি গায়েব করে দেওয়া হয়েছে। যদিও ছোট ছোট অনেক ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টা কীভাবে এল, সেটা তো থাকা দরকার এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট তো থাকতে হবে। যদিও বিশাল আকারে ইতিহাস লেখার জায়গা এটা না। শেষে আসবে চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের ঘটনা। এর মধ্যে মাঝখানের ঘটনাগুলো শুধু উল্লেখ করলেই চলত। সেটা তো করা হয়নি। যাঁরা খসড়াটি করেছেন, তাঁদের আমি অবশ্যই অযোগ্য বলব না। একেকজনের কথায় একেকটা বিষয় ঢুকে গেছে। কারও সঙ্গে তাঁরা বিতর্ক করেননি। ফলে আমাদের বক্তব্যগুলোকে বেমালুম বাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা মনে করেছেন, আমাদের বক্তব্য বাদ দিলে বুঝি কোনো সমস্যা হবে না। আবার কোনো কোনো দল যা-ই বলেছে, সেটাই তাঁরা রেখেছেন; যেখানে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অসম্পূর্ণ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বক্তব্য একপেশে হয়েছে।
আবার অঙ্গীকারনামায় উল্লেখ করা হয়েছে, এই সনদ বাস্তবায়নের জন্য পরিপূর্ণভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকতে হবে। আমাদের কথা হলো, এই সনদ পরিপূর্ণ হলে সেখানে ‘নোট অব ডিসেন্ট’গুলো লিপিবদ্ধ থাকত। কিন্তু সেসব রাখা হয়নি। সনদের ভেতরে আবার তাঁরা লিখেছেন—যে দল সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে, ‘নোট অব ডিসেন্ট’ ছাড়া কাজ করতে পারবে। যারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না, তারাও তো কাজ করবে। তারা প্রয়োজনবোধে একমত না হলে সংসদ ত্যাগ করবে। নতুবা সংসদের বাইরে সভা-সমাবেশের মাধ্যমে জনগণের কাছে মতামত তুলে ধরবে। এসব তো ম্যান্ডেট পাওয়া না-পাওয়ার ওপর নির্ভর করে না।
এটা তো বিএনপির ভাষা। বিএনপি মনে করে, তারা ম্যান্ডেট নিয়ে আগামী সংসদে যাবে। সেটা ভালো কথা। কিন্তু আমরা ম্যান্ডেট পাব কি পাব না সেটা ভিন্ন কথা। আমরা ‘নোট অব ডিসেন্ট’ দিয়েছি চুপ না থাকার জন্য। আমরা যেমনভাবে সংসদের ভেতরে কথা বলব, তেমনি সংসদের বাইরেও কথা বলব। আমরা আবার রাজপথে আন্দোলনও করব। সবকিছু মিলিয়ে আমরা কয়েকটি বামপন্থী দল জুলাই সনদে স্বাক্ষর করিনি।
তবে আমরা সংবাদ সম্মেলন করে বলেছি, যেসব বিষয়ে আমরা সহমত জ্ঞাপন করেছি (সেটার রেকর্ড আছে) সেটা খুব ভালো কাজ হয়েছে। আমরা ঐকমত্য কমিশনকে ধন্যবাদ জানাই যে সাংবিধানিক প্রশ্ন, আইনের প্রশ্নসহ সংস্কার নিয়ে সব রাজনৈতিক দলের মতামত নিয়ে তারা একটা ঐতিহাসিক দলিল তৈরি করতে পেরেছে। এই দলিল থেকে বোঝা যাবে, কোন দলের কী দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু আমরা বলেছি, গায়ের জোরে সংবিধান বাতিল করার দাবি—এটা অসাংবিধানিক অপরাধ। আমরা মনে করি, সংবিধান বাতিল করার দাবি তোলা যাবে এবং নতুন সংবিধান করার দাবিও তোলা যাবে—সেটা রাষ্ট্রদ্রোহ হবে না। কিন্তু অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে যদি বাতিল করতে চায়, সেটা অবশ্যই রাষ্ট্রদ্রোহ অপরাধ। তারা ৭ (ক) ধারার বাতিল করার প্রস্তাব করেছে। এটা নিয়ে আমরা আপত্তি করেছি। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টে উচ্চকক্ষে আমরা পিআর পদ্ধতির পক্ষে, কিন্তু দুই বাসদ ও সিপিবি উচ্চকক্ষে পিআরের পক্ষে না।
তবে আমরা যে কয়েকটি বাম দল এসব বিষয়ে একমত হয়েছি, আমরা আগামী দিনে সংসদের ভেতরে ও বাইরে এসব নিয়ে সংগ্রাম এবং রাজনৈতিকভাবে জনমত গঠনের কাজ করব। সেটা আমরা অঙ্গীকার করেছি।
এরপর আপনারা একটা স্মারকলিপি দিয়েছেন। এটা দেওয়ার কারণ কী?
আমরা কেন জুলাই সনদে স্বাক্ষর করলাম না, সেটা নিয়ে আমরা একটা সংবাদ সম্মেলন করেছি। সেই সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্যটা আমাদের দুজন প্রতিনিধি হাতে হাতে ঐকমত্য কমিশনের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।
স্মারকলিপি দেওয়ার পর ঐকমত্য কমিশনের বক্তব্য কী?
তারা বলেছে, আপনারা অনেক কষ্ট করে, সময় নিয়ে বক্তব্য বা নোট দিয়েছেন, আপনারা এটার অংশীদার হন। আমরা বলেছি, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আর বিএনপির দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়। জাতীয় সংসদে সিদ্ধান্ত হওয়ার আগে কেন আমরা আত্মসমর্পণ করব মৌলিক, দার্শনিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নে? বিএনপি যেমন প্রত্যাশা করছে, তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে। তারাসহ তাদের মিত্ররা দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পাবে। তারা যেসব নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছে, সেগুলোতে তারা পক্ষে নিতে পারে। কিন্তু সংসদে যাওয়ার আগেই আমাদের মেনে নিতে হবে, সংবিধান বাতিলের ১৪ ধারা রাষ্ট্রদ্রোহ অপরাধ না, নারী ১০০ আসনে সরাসরি নির্বাচনের দরকার নেই, সংবিধানের ১৫০ (২) ধারা মতে শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণ না থাকা—এ বিষয়গুলো এড়িয়ে গিয়ে তো আমরা সনদে স্বাক্ষর করে দাসখত দিতে পারি না। এই ফাঁদেও পা দিতে পারি না। আমরা স্পষ্ট করে বলেছি, এসব বিষয় যদি সংশোধন না করা হয়, তাহলে আমরা জুলাই সনদে স্বাক্ষর করতে পারি না।
এনসিপি সনদের বাস্তবায়নের পদ্ধতির প্রশ্ন নিয়ে স্বাক্ষর করেনি। এটাকে আপনারা কীভাবে দেখেন?
তাদের তো সনদ নিয়ে কোনো দাবি নেই। তারা সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে চাপ সৃষ্টি করছে। আমাদের তো সনদের খসড়া নিয়েই আপত্তি। কিন্তু তাদের কোনো আপত্তি নেই। তারা শুধু বাস্তবায়ন পদ্ধতির বিতর্ক তুলে স্বাক্ষর করেনি।
আপনি নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম নেতা ছিলেন। সে সময়ে তিন জোটের রূপরেখাকে পরবর্তীকালে ক্ষমতাসীন কোনো দলই গুরুত্ব দেয়নি। এখন আপনি জুলাই সনদ নিয়ে কতটা আশাবাদী?
নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের তিন জোটের রূপরেখাকে নির্দিষ্ট করে সংবিধানের সঙ্গে আপগ্রেড করা হয়নি। সে সময় যে তিনটি জোট এই রূপরেখাতে স্বাক্ষর করেছিল, তারা কিন্তু পরবর্তী সময়ে তার অনেক কিছুই মানেনি। তারা সেখানকার রাজনৈতিক অঙ্গীকারও পালন করেনি। তা ছাড়া, এটার কোনো আইনি রূপও দেওয়া হয়নি। কথা ছিল তারা পরস্পরের প্রতি কোনো বৈরী আচরণ করবে না। সেই রাজনৈতিক অঙ্গীকারও পালন করেনি। পরস্পর পরস্পরকে ধ্বংস করার জন্য এক দল অন্য দলের প্রতি বিরূপ আচরণ করেছে। এগুলোকে কোনোভাবেই রাজনৈতিক আচরণ বা সাংবিধানিক আইন মেনে চলা বলা যায় না।
কিন্তু এবারের জুলাই সনদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, এর ধারা ও উপধারা ধরে বিতর্ক করে কে পক্ষে আছে আর কে বিপক্ষে আছে, তা নিয়ে কথা বলার সুযোগ হয়েছে। সে কারণে বলতে চাই, নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের তিন জোটের রূপরেখার সঙ্গে এবারের জুলাই সনদটা অনেক অগ্রসর দলিল বলতে হবে। কোনো দল যদি এর কোনো বক্তব্য সুনির্দিষ্টভাবে পালন করতে না চায়, তাহলে সব রাজনৈতিক দল তার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে যাবে। জুলাই সনদ একেবারেই সুনির্দিষ্ট। কিন্তু নব্বইয়ের রূপরেখা এভাবে সুনির্দিষ্ট ছিল না। আবার সেই রূপরেখার মধ্যে কোনো গভীরতা ছিল না। তারপরেও যে কিছু হয়নি, সেটা বলা যাবে না। কারণ, নব্বইয়ের পরে সব দল কিন্তু সংসদীয় সরকার পদ্ধতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। যদিও পরবর্তী সময়ে সেই সংসদীয় সরকার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার পরেও নানা অঘটন ঘটেছে।
বাংলাদেশের রাজনীতি আসলে কোন দিকে যাচ্ছে?
এখন দ্রুত দরকার একটা সংসদ নির্বাচন করা। যে নির্বাচিত সরকার জনগণের কাছে জবাবদিহি করবে। এখন কোনো জবাবদিহি করা যাচ্ছে না। আমরা যেভাবে গত স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে পেরেছি, এখন কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে তা করতে পারছি না। এখন কোনো বিষয়ে সরকারের কাছে অভিযোগ উত্থাপন করলে তারা বলে, কোনো কিছু আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। আবার পুলিশও একই কথা বলছে।
রাজনৈতিক দলগুলো দেশটাকে ভাগাভাগি করার মতো করে কথা বলছে। এক দল আরেক দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে, আবার সবাই মিলে ঐকমত্য কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে। এখানে এখন একটা আজব পরিস্থিতি বিরাজ করছে। মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা দেওয়ার নিশ্চয়তা এ সরকার দিতে পারছে না। এ জন্য নির্বাচন করা দরকার। যদিও সুষ্ঠু নির্বাচন করা নিয়ে অনেকে শঙ্কা প্রকাশ করছেন। তারপরও নির্বাচনের মাধ্যমে যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন, তখন আমরা একটা রাজনৈতিক ব্যাকরণের মধ্যে প্রবেশ করতে পারব।
নির্বাচিত সরকার ভালো কাজ করলে পক্ষে থাকব আর মন্দ কাজ করলে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করব। আগে থেকে বলা সম্ভব নয়, যারা দায়িত্বে থাকবে তারা কতটুকু পারছে বা পারছে না। তারা যদি জনগণের পক্ষে না থাকে, তাহলে প্রয়োজনে আগাম নির্বাচন দাবি করব।
সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
আপনাকেও ধন্যবাদ।
আপনারা কেন জুলাই সনদে স্বাক্ষর না করার সিদ্ধান্ত নিলেন? আপনাদের মূল আপত্তিগুলো কী ছিল?
আমাদের প্রথম আপত্তি ছিল ‘নোট অব ডিসেন্ট’ বা ভিন্নমত সংযুক্ত না করা। যেসব বিষয়ে সবাই মিলে একমত হয়েছি বা মোটামুটি একমত হয়েছি, সেসব যুক্ত করা ছাড়া আমরা স্বাক্ষর করব না। যেহেতু ‘নোট অব ডিসেন্ট’সহ কিছু বিষয়ে আপত্তি ছিল, সেটা স্বাক্ষর করলে তো মেনে নেওয়া হতো। সেটা জাতীয় সংসদে হলে অন্য কথা ছিল বা কোনো রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে সেটা হতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সেটা মেনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ঐকমত্য কমিশন সে রকম কোনো ফোরাম না। এটা হচ্ছে রাজনৈতিকভাবে ঐকমত্যে আসার জন্য একটা চেষ্টা, একটা উদ্যোগ।
জুলাই সনদ তৈরি করার সময় এর পটভূমি ধরে আমরা ইতিহাসকে সঠিকভাবে লেখার জন্য বারবার ইনপুট দিয়েছি। আমাদের দলসহ অন্য দলের নেতারা সেটা বলেছেন। কিন্তু সনদে নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানকে পুরোপুরি গায়েব করে দেওয়া হয়েছে। যদিও ছোট ছোট অনেক ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টা কীভাবে এল, সেটা তো থাকা দরকার এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট তো থাকতে হবে। যদিও বিশাল আকারে ইতিহাস লেখার জায়গা এটা না। শেষে আসবে চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের ঘটনা। এর মধ্যে মাঝখানের ঘটনাগুলো শুধু উল্লেখ করলেই চলত। সেটা তো করা হয়নি। যাঁরা খসড়াটি করেছেন, তাঁদের আমি অবশ্যই অযোগ্য বলব না। একেকজনের কথায় একেকটা বিষয় ঢুকে গেছে। কারও সঙ্গে তাঁরা বিতর্ক করেননি। ফলে আমাদের বক্তব্যগুলোকে বেমালুম বাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা মনে করেছেন, আমাদের বক্তব্য বাদ দিলে বুঝি কোনো সমস্যা হবে না। আবার কোনো কোনো দল যা-ই বলেছে, সেটাই তাঁরা রেখেছেন; যেখানে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অসম্পূর্ণ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বক্তব্য একপেশে হয়েছে।
আবার অঙ্গীকারনামায় উল্লেখ করা হয়েছে, এই সনদ বাস্তবায়নের জন্য পরিপূর্ণভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকতে হবে। আমাদের কথা হলো, এই সনদ পরিপূর্ণ হলে সেখানে ‘নোট অব ডিসেন্ট’গুলো লিপিবদ্ধ থাকত। কিন্তু সেসব রাখা হয়নি। সনদের ভেতরে আবার তাঁরা লিখেছেন—যে দল সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে, ‘নোট অব ডিসেন্ট’ ছাড়া কাজ করতে পারবে। যারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না, তারাও তো কাজ করবে। তারা প্রয়োজনবোধে একমত না হলে সংসদ ত্যাগ করবে। নতুবা সংসদের বাইরে সভা-সমাবেশের মাধ্যমে জনগণের কাছে মতামত তুলে ধরবে। এসব তো ম্যান্ডেট পাওয়া না-পাওয়ার ওপর নির্ভর করে না।
এটা তো বিএনপির ভাষা। বিএনপি মনে করে, তারা ম্যান্ডেট নিয়ে আগামী সংসদে যাবে। সেটা ভালো কথা। কিন্তু আমরা ম্যান্ডেট পাব কি পাব না সেটা ভিন্ন কথা। আমরা ‘নোট অব ডিসেন্ট’ দিয়েছি চুপ না থাকার জন্য। আমরা যেমনভাবে সংসদের ভেতরে কথা বলব, তেমনি সংসদের বাইরেও কথা বলব। আমরা আবার রাজপথে আন্দোলনও করব। সবকিছু মিলিয়ে আমরা কয়েকটি বামপন্থী দল জুলাই সনদে স্বাক্ষর করিনি।
তবে আমরা সংবাদ সম্মেলন করে বলেছি, যেসব বিষয়ে আমরা সহমত জ্ঞাপন করেছি (সেটার রেকর্ড আছে) সেটা খুব ভালো কাজ হয়েছে। আমরা ঐকমত্য কমিশনকে ধন্যবাদ জানাই যে সাংবিধানিক প্রশ্ন, আইনের প্রশ্নসহ সংস্কার নিয়ে সব রাজনৈতিক দলের মতামত নিয়ে তারা একটা ঐতিহাসিক দলিল তৈরি করতে পেরেছে। এই দলিল থেকে বোঝা যাবে, কোন দলের কী দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু আমরা বলেছি, গায়ের জোরে সংবিধান বাতিল করার দাবি—এটা অসাংবিধানিক অপরাধ। আমরা মনে করি, সংবিধান বাতিল করার দাবি তোলা যাবে এবং নতুন সংবিধান করার দাবিও তোলা যাবে—সেটা রাষ্ট্রদ্রোহ হবে না। কিন্তু অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে যদি বাতিল করতে চায়, সেটা অবশ্যই রাষ্ট্রদ্রোহ অপরাধ। তারা ৭ (ক) ধারার বাতিল করার প্রস্তাব করেছে। এটা নিয়ে আমরা আপত্তি করেছি। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টে উচ্চকক্ষে আমরা পিআর পদ্ধতির পক্ষে, কিন্তু দুই বাসদ ও সিপিবি উচ্চকক্ষে পিআরের পক্ষে না।
তবে আমরা যে কয়েকটি বাম দল এসব বিষয়ে একমত হয়েছি, আমরা আগামী দিনে সংসদের ভেতরে ও বাইরে এসব নিয়ে সংগ্রাম এবং রাজনৈতিকভাবে জনমত গঠনের কাজ করব। সেটা আমরা অঙ্গীকার করেছি।
এরপর আপনারা একটা স্মারকলিপি দিয়েছেন। এটা দেওয়ার কারণ কী?
আমরা কেন জুলাই সনদে স্বাক্ষর করলাম না, সেটা নিয়ে আমরা একটা সংবাদ সম্মেলন করেছি। সেই সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্যটা আমাদের দুজন প্রতিনিধি হাতে হাতে ঐকমত্য কমিশনের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।
স্মারকলিপি দেওয়ার পর ঐকমত্য কমিশনের বক্তব্য কী?
তারা বলেছে, আপনারা অনেক কষ্ট করে, সময় নিয়ে বক্তব্য বা নোট দিয়েছেন, আপনারা এটার অংশীদার হন। আমরা বলেছি, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আর বিএনপির দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়। জাতীয় সংসদে সিদ্ধান্ত হওয়ার আগে কেন আমরা আত্মসমর্পণ করব মৌলিক, দার্শনিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নে? বিএনপি যেমন প্রত্যাশা করছে, তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে। তারাসহ তাদের মিত্ররা দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পাবে। তারা যেসব নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছে, সেগুলোতে তারা পক্ষে নিতে পারে। কিন্তু সংসদে যাওয়ার আগেই আমাদের মেনে নিতে হবে, সংবিধান বাতিলের ১৪ ধারা রাষ্ট্রদ্রোহ অপরাধ না, নারী ১০০ আসনে সরাসরি নির্বাচনের দরকার নেই, সংবিধানের ১৫০ (২) ধারা মতে শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণ না থাকা—এ বিষয়গুলো এড়িয়ে গিয়ে তো আমরা সনদে স্বাক্ষর করে দাসখত দিতে পারি না। এই ফাঁদেও পা দিতে পারি না। আমরা স্পষ্ট করে বলেছি, এসব বিষয় যদি সংশোধন না করা হয়, তাহলে আমরা জুলাই সনদে স্বাক্ষর করতে পারি না।
এনসিপি সনদের বাস্তবায়নের পদ্ধতির প্রশ্ন নিয়ে স্বাক্ষর করেনি। এটাকে আপনারা কীভাবে দেখেন?
তাদের তো সনদ নিয়ে কোনো দাবি নেই। তারা সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে চাপ সৃষ্টি করছে। আমাদের তো সনদের খসড়া নিয়েই আপত্তি। কিন্তু তাদের কোনো আপত্তি নেই। তারা শুধু বাস্তবায়ন পদ্ধতির বিতর্ক তুলে স্বাক্ষর করেনি।
আপনি নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম নেতা ছিলেন। সে সময়ে তিন জোটের রূপরেখাকে পরবর্তীকালে ক্ষমতাসীন কোনো দলই গুরুত্ব দেয়নি। এখন আপনি জুলাই সনদ নিয়ে কতটা আশাবাদী?
নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের তিন জোটের রূপরেখাকে নির্দিষ্ট করে সংবিধানের সঙ্গে আপগ্রেড করা হয়নি। সে সময় যে তিনটি জোট এই রূপরেখাতে স্বাক্ষর করেছিল, তারা কিন্তু পরবর্তী সময়ে তার অনেক কিছুই মানেনি। তারা সেখানকার রাজনৈতিক অঙ্গীকারও পালন করেনি। তা ছাড়া, এটার কোনো আইনি রূপও দেওয়া হয়নি। কথা ছিল তারা পরস্পরের প্রতি কোনো বৈরী আচরণ করবে না। সেই রাজনৈতিক অঙ্গীকারও পালন করেনি। পরস্পর পরস্পরকে ধ্বংস করার জন্য এক দল অন্য দলের প্রতি বিরূপ আচরণ করেছে। এগুলোকে কোনোভাবেই রাজনৈতিক আচরণ বা সাংবিধানিক আইন মেনে চলা বলা যায় না।
কিন্তু এবারের জুলাই সনদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, এর ধারা ও উপধারা ধরে বিতর্ক করে কে পক্ষে আছে আর কে বিপক্ষে আছে, তা নিয়ে কথা বলার সুযোগ হয়েছে। সে কারণে বলতে চাই, নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের তিন জোটের রূপরেখার সঙ্গে এবারের জুলাই সনদটা অনেক অগ্রসর দলিল বলতে হবে। কোনো দল যদি এর কোনো বক্তব্য সুনির্দিষ্টভাবে পালন করতে না চায়, তাহলে সব রাজনৈতিক দল তার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে যাবে। জুলাই সনদ একেবারেই সুনির্দিষ্ট। কিন্তু নব্বইয়ের রূপরেখা এভাবে সুনির্দিষ্ট ছিল না। আবার সেই রূপরেখার মধ্যে কোনো গভীরতা ছিল না। তারপরেও যে কিছু হয়নি, সেটা বলা যাবে না। কারণ, নব্বইয়ের পরে সব দল কিন্তু সংসদীয় সরকার পদ্ধতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। যদিও পরবর্তী সময়ে সেই সংসদীয় সরকার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার পরেও নানা অঘটন ঘটেছে।
বাংলাদেশের রাজনীতি আসলে কোন দিকে যাচ্ছে?
এখন দ্রুত দরকার একটা সংসদ নির্বাচন করা। যে নির্বাচিত সরকার জনগণের কাছে জবাবদিহি করবে। এখন কোনো জবাবদিহি করা যাচ্ছে না। আমরা যেভাবে গত স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে পেরেছি, এখন কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে তা করতে পারছি না। এখন কোনো বিষয়ে সরকারের কাছে অভিযোগ উত্থাপন করলে তারা বলে, কোনো কিছু আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। আবার পুলিশও একই কথা বলছে।
রাজনৈতিক দলগুলো দেশটাকে ভাগাভাগি করার মতো করে কথা বলছে। এক দল আরেক দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে, আবার সবাই মিলে ঐকমত্য কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে। এখানে এখন একটা আজব পরিস্থিতি বিরাজ করছে। মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা দেওয়ার নিশ্চয়তা এ সরকার দিতে পারছে না। এ জন্য নির্বাচন করা দরকার। যদিও সুষ্ঠু নির্বাচন করা নিয়ে অনেকে শঙ্কা প্রকাশ করছেন। তারপরও নির্বাচনের মাধ্যমে যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন, তখন আমরা একটা রাজনৈতিক ব্যাকরণের মধ্যে প্রবেশ করতে পারব।
নির্বাচিত সরকার ভালো কাজ করলে পক্ষে থাকব আর মন্দ কাজ করলে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করব। আগে থেকে বলা সম্ভব নয়, যারা দায়িত্বে থাকবে তারা কতটুকু পারছে বা পারছে না। তারা যদি জনগণের পক্ষে না থাকে, তাহলে প্রয়োজনে আগাম নির্বাচন দাবি করব।
সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
আপনাকেও ধন্যবাদ।
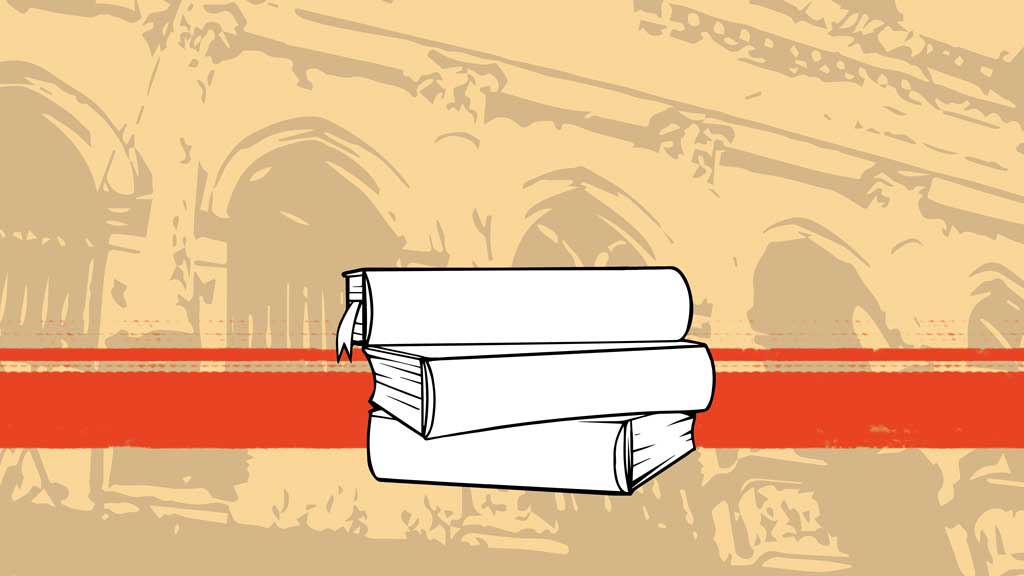
শিক্ষা শুধু একটি মৌলিক অধিকার নয়, এটি ব্যক্তি ও জাতির ক্ষমতায়নের সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো একটি তরুণ ও জনবহুল দেশে, যেখানে জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ ২৫ বছরের নিচে, সেখানে শিক্ষায় বিনিয়োগ কেবল মানবিক দায়িত্ব নয়, এটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি।
২৮ জুন ২০২৫
কুড়িল বিশ্বরোডের ফুটওভারব্রিজে দাঁড়িয়ে একটি খালের চমৎকার শোভা দেখে মুগ্ধ হচ্ছিলাম। ঢাকার বুকে এত সুন্দর একটা খাল! ধনুকের মতো বাঁক খেয়ে চলে গেছে দূরে, দুই পাড়ে হাঁটার রাস্তা। রাস্তা আর খালের পানির মাঝে সবুজ ঢাল সিঙ্গাপুর ডেইজির শায়িত লতায় আচ্ছাদিত।
১ দিন আগে
পিরোজপুরের নেছারাবাদে যে ঘটনা ঘটেছে, তার জন্য ইউএনও সাহেব ধন্যবাদ পেতেই পারেন। সেখানে একটি বিয়ের দাওয়াতে গিয়েছিলেন তিনি সপরিবারে। কিন্তু যখন জানতে পারলেন, বিয়ের কনে প্রাপ্তবয়স্ক নয়, তখন তিনি না খেয়েই ফিরে আসেন। এবং তিনি ফিরে আসায় কাজিও বিয়ে পড়াননি। ফলে এই বাল্যবিবাহ হয়নি।
১ দিন আগে
মিরপুরের শিয়ালবাড়ী এলাকায় একটি রাসায়নিক গুদামে আগুন লাগার পর যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল, সে কথা সবাই এখন জানেন। যাঁরা স্বজন হারিয়েছেন, তাঁরা জানেন এটা তাঁদের পরিবারের জন্য কত বড় ক্ষতি। নিহতদের পরিবার ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে কি না, তাদের জীবনে স্থিতি ফিরিয়ে আনতে কী করা দরকার...
২ দিন আগেমৃত্যুঞ্জয় রায়

কুড়িল বিশ্বরোডের ফুটওভারব্রিজে দাঁড়িয়ে একটি খালের চমৎকার শোভা দেখে মুগ্ধ হচ্ছিলাম। ঢাকার বুকে এত সুন্দর একটা খাল! ধনুকের মতো বাঁক খেয়ে চলে গেছে দূরে, দুই পাড়ে হাঁটার রাস্তা। রাস্তা আর খালের পানির মাঝে সবুজ ঢাল সিঙ্গাপুর ডেইজির শায়িত লতায় আচ্ছাদিত। আহা, কী পরিষ্কার সেই খালের জল, কোথাও একটা শুকনো পাতা পড়ে নেই জলের ওপর। খালের পাড়ে স্বর্ণচাঁপা, বকুল, কাঠবাদাম, চালতা, ছাতিম গাছগুলোর ছত্রবৎ পত্রাচ্ছাদন, গোড়া বাঁধানো নারকেলগাছের সারি। খালের জলে সাঁতরে বেড়াচ্ছে, লাফ দিচ্ছে মাছেরা। মাঝে মাঝে পাড়ে রয়েছে জলের ওপর বাড়ানো জেটির মতো রেলিংঘেরা পাকা চাতাল, যার ওপর দাঁড়িয়ে জলের কাছে যাওয়া যায়, খালের জলে বড়শি ফেলে মাছ ধরা যায়। ওপরে হেমন্তের ঝকঝকে নীল আকাশ, রোদের ঝিলিক। খালের পশ্চিম পাড়ে একটি অভিজাত এলাকার মনোরম ভবন। দেখে মনে হচ্ছে, এ যেন ঢাকা শহর নয়—নেদারল্যান্ডসের কোনো এক জায়গা।
নেদারল্যান্ডসের গিথুর্ন গ্রামের ছবি যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা হয়তো জানেন, সেই গ্রামে গাড়ি চালানোর মতো কোনো রাস্তা নেই, আছে গ্রামজুড়ে চলাচলের জন্য চমৎকার খাল আর হাঁটার পথ। একটা গ্রামে কোনো গাড়ির রাস্তা নেই, খাল ও খালের ওপর আছে ১৭০টির বেশি সেতু। বৈদ্যুতিক নৌকায় করে সেই গ্রামের অধিবাসীরা এখান থেকে সেখানে যায়। আহা, গাড়ি ও জ্বালানির দূষণমুক্ত কী শান্ত মনোরম সে গ্রাম! খালের পাড় বাঁধানো, দুই পাড়ে থাকা অনুচ্চ ঘরবাড়ি, আঙিনার কোথাও কোনো খোলা মাটি নেই, পুরোটাই সবুজ কার্পেটের মতো ঘাসে ঢাকা, মাঝে মাঝে ফুলগাছের ঝোপ। যেন সে এক স্বপ্নের জায়গা, পৃথিবীর বুকেই স্বর্গের শোভা। ঢাকার এ জায়গাটি দেখেও সেই গিথুর্ন গ্রামের ছবিটা চোখে ভাসছিল। ধন্যবাদ ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনকে—নিকুঞ্জ খালের এমন সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য।
আহা রে, ঢাকা শহরের সব খাল যদি এরূপ সুন্দর হতো! এ কথা ভাবতেই মনের মধ্যে ভেসে উঠল এর বিপরীত দৃশ্য। খাল দখল করতে করতে সেগুলো সংকুচিত হয়ে পড়েছে। যতটুকু অবশিষ্ট আছে, সেগুলোও হয়ে পড়েছে ময়লার ভাগাড়, কচুরিপানা ও ঝোপঝাড়ে ভরা মশককুলের অভয়ারণ্য। বিভিন্ন কলকারখানার বর্জ্য নির্গমনের নিকাশনালার মতো ব্যবহৃত হচ্ছে কোনো কোনো খাল। পচা দুর্গন্ধযুক্ত অস্বাস্থ্যকর সেই পরিবেশেই কেটে যাচ্ছে পথচারী ও এলাকাবাসীর দিনকাল। খালগুলো যেভাবে মরতে বসেছে, তাতে আগামী ১০ বছরও লাগবে না ঢাকা শহর খালশূন্য হতে। ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী ঢাকা শহরে খালের সংখ্যা ৪৭টি। রিভার অ্যান্ড ডেল্টা সেন্টারের গবেষণা অনুযায়ী ৫৬টি। ড্যাপেও খালের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে ৪৩টি।
ধরা হয়, অতীতে ঢাকা শহরে ৪৭টি খাল সচল ছিল। শহরের চারপাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ ও বালু নদের সঙ্গে যুক্ত ছিল সেসব খাল। নৌকা ও নৌযান চলত সেসব খালে। পণ্য পরিবহন ও লোক চলাচলে সে সময় খালগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখত। একসময় শাহবাগ থেকে মগবাজার পর্যন্ত একটি খাল ছিল—পরীবাগ খাল। ঢাকা ওয়াসার মানচিত্রে তার অস্তিত্বের কথা জানা যায়। সেই খাল আর এখন নেই। এভাবে ধোলাই খাল, রায়েরবাজার, গোপীবাগ, নারিন্দা, সেগুনবাগিচা, কাঁঠালবাগান, ধানমন্ডি ইত্যাদি খালগুলোরও এখন আর অস্তিত্ব নেই। ধানমন্ডি লেকটাই একসময় ছিল খাল, হাতিরঝিলের খালে পিলখানা থেকে হাতির পালকে নিয়ে যাওয়া হতো গোসল করাতে। মোগল শাসকেরা ঢাকা শহরে বহুসংখ্যক খাল থাকায় ঢাকাকে রাজধানী করার চিন্তা করেছিল, খালগুলো তাদের চলাচল ও প্রতিরক্ষার জন্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ। শহরের জলাবদ্ধতা দূর ও পানি নিষ্কাশনের জন্যও ছিল সেগুলো সহায়ক। সেসব এখন ইতিহাস। এখন এক ঘণ্টা বৃষ্টি হলেই ঢাকা শহরের অনেক এলাকায় হাঁটুপানি জমে যায়।
ঢাকা শহরের সব খাল উদ্ধার করা প্রথম কাজ। উদ্ধারের পর সেসব খালের দুই পাড়ে ওয়াকওয়ে বা হাঁটার পথ তৈরি ও বাহারি গাছপালা লাগিয়ে সুশোভন করা দ্বিতীয় কাজ। তৃতীয় কাজ হলো খালগুলোতে নিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যাটারি, বিদ্যুৎ ও হস্তচালিত নৌযান চালনার উদ্যোগ নেওয়া। জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক কোনো নৌযান সেসব খালে চলাচলের অনুমতি না দেওয়া হবে খালের জলজ জীবগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা এবং দূষণ কমানোর গুরুত্বপূর্ণ উপায়। ওয়াকওয়ে যেন শুধু ওয়াক তথা হাঁটার জন্যই ব্যবহৃত হয়, সে রাস্তায় যেন কোনো গাড়ি বা মোটরসাইকেল না চলে। সবশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো খাল এবং তার চারপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত রাখতে উত্তম ব্যবস্থাপনার চর্চা অব্যাহত রাখা। খাল ব্যবহারকারী থেকে শুরু করে সেখানকার সব অংশীজনের সক্রিয় অংশগ্রহণই এসব ব্যবস্থাপনাকে সুচারুরূপে বাস্তবায়নের মূল সূত্র, এর সঙ্গে থাকবে সঠিক পরিকল্পনা ও নির্দেশনা, উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনার প্রচারণা। এ কাজে দরকার রাষ্ট্রীয় বা সরকারের সদিচ্ছা ও সিদ্ধান্ত, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণ, রাজনৈতিক ঐকমত্য এবং জনগণের অংশগ্রহণ। অনেক তরুণ এখন স্বেচ্ছাসেবী হয়ে এরূপ কাজে অংশ নিতে আগ্রহী। তাদের উৎসাহিত করে নিরাপদভাবে কাজের সুযোগ করে দিতে হবে। সিটি করপোরেশনের নির্ধারিত মালি ও পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা কাজ করবেন জবাবদিহির মধ্যে, স্বেচ্ছাসেবীদের সঙ্গে মিলেমিশে। শোভাবর্ধনের চারাগুলোর ব্যবস্থা করতে হবে সিটি করপোরেশনগুলোকেই। তবে এককভাবে শুধু দুই সিটি করপোরেশনের ওপর সম্পূর্ণ বিষয়টি চাপিয়ে দিলে হবে না। খালগুলোর দখলদারেরা অনেক শক্তিশালী, নিশ্চিত যে তাঁরা কেউই সেসব খালের দখল স্বেচ্ছায় ছাড়বেন না। দখলমুক্ত করার জন্য জোর প্রশাসনিক প্রচেষ্টা ও আইন প্রয়োগ করা দরকার।
প্রকৃতিতে প্রবহমান নদী আর খালগুলো হলো আমাদের দেহের শিরা-উপশিরার মতো। একটি ভূখণ্ডের জীবনরেখা বলা হয় এসব জলস্রোতকে। প্রবহমান এসব জলাশয় যেমন জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি মাটিসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্যও সহায়ক। ঢাকা শহরের প্রায় দুই কোটি মানুষের স্বাস্থ্যের কথা ভেবেও খালগুলোকে সচল করা দরকার। বর্তমানে ঢাকা শহরে ২৬টি খালের অস্তিত্ব চোখে দেখা গেলেও বাকি ২১টি খাল নেই। কোথায় কোথায় সেসব খাল ছিল, তা নিশ্চয় অতীতের মানচিত্রগুলোতে পাওয়া যাবে। সেগুলো আদৌ উদ্ধার বা দখলমুক্ত করা যাবে, তা দুরাশা। উদ্ধার করা গেলে সেগুলো খনন করে সচল ও শোভাময় করা উচিত। জার্মানির বার্লিন শহরে খালে করে ক্যানালক্রুজ করার সময় খালপাড়ের দুই পাশের বিভিন্ন স্থাপনা ও নাগরিক সৌন্দর্য, সেতু, রেস্তোরাঁ দেখতে দেখতে অভিভূত হতাম। ভাবতাম, জলের দেশ, নদীর দেশ, খালের দেশ বাংলাদেশ; অথচ সে দেশের শহরগুলোর খালে কেন এ রকম নৌ-পর্যটন করা যাবে না?
খালপাড় ভেঙে যাতে কোনো নগরবাসীর এক ফুট জমিও নষ্ট না হয়, সে জন্য ভেনিস, কোপেনহেগেন, প্যারিস ইত্যাদি শহরের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া খাল ও নদীর দুই পাড় যেভাবে পাকা করে বাঁধাই করে রাখা হয়েছে, সেভাবে আমাদের প্রবহমান খালগুলোর পাড়ও বেঁধে দেওয়া যায়। নগরীর খালগুলো নিয়ে একটি চমৎকার পরিকল্পনার সুযোগ রয়েছে ড্যাপ বাস্তবায়নের কারণে। চলাচল, পরিবহন, জলাবদ্ধতা নিরসন, দূষণ হ্রাস, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পর্যটন, সৌন্দর্যবর্ধন, স্থানীয় মানুষের আয়বর্ধন, পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদির জন্য এ ধরনের পরিকল্পনা ও জরিপকাজ নিশ্চয় সহায়ক হবে। সবার মনে রাখা উচিত, প্রাকৃতিক প্রবাহকে রুদ্ধ করার অধিকার কারও নেই, তার ফল কখনো ভালো হয় না। এ নিয়ে কোনো খণ্ডিত পরিকল্পনা নয়, নিতে হবে সমন্বিত সামগ্রিক পরিকল্পনা। তাহলে আমরাও দেখতে পাব একটি মনোরম মহানগর, সুশোভিত খালসমৃদ্ধ একটি সুশোভন পরিবেশ। কুড়িল বিশ্বরোডের কাছে নিকুঞ্জ খালটি যদি এত সুন্দর করা যায়, সুন্দর রাখা যায়, তাহলে অন্যগুলো কেন এরূপ সুন্দর হবে না?
মৃত্যুঞ্জয় রায়, কৃষিবিদ ও প্রকৃতিবিষয়ক লেখক
আরও খবর পড়ুন:

কুড়িল বিশ্বরোডের ফুটওভারব্রিজে দাঁড়িয়ে একটি খালের চমৎকার শোভা দেখে মুগ্ধ হচ্ছিলাম। ঢাকার বুকে এত সুন্দর একটা খাল! ধনুকের মতো বাঁক খেয়ে চলে গেছে দূরে, দুই পাড়ে হাঁটার রাস্তা। রাস্তা আর খালের পানির মাঝে সবুজ ঢাল সিঙ্গাপুর ডেইজির শায়িত লতায় আচ্ছাদিত। আহা, কী পরিষ্কার সেই খালের জল, কোথাও একটা শুকনো পাতা পড়ে নেই জলের ওপর। খালের পাড়ে স্বর্ণচাঁপা, বকুল, কাঠবাদাম, চালতা, ছাতিম গাছগুলোর ছত্রবৎ পত্রাচ্ছাদন, গোড়া বাঁধানো নারকেলগাছের সারি। খালের জলে সাঁতরে বেড়াচ্ছে, লাফ দিচ্ছে মাছেরা। মাঝে মাঝে পাড়ে রয়েছে জলের ওপর বাড়ানো জেটির মতো রেলিংঘেরা পাকা চাতাল, যার ওপর দাঁড়িয়ে জলের কাছে যাওয়া যায়, খালের জলে বড়শি ফেলে মাছ ধরা যায়। ওপরে হেমন্তের ঝকঝকে নীল আকাশ, রোদের ঝিলিক। খালের পশ্চিম পাড়ে একটি অভিজাত এলাকার মনোরম ভবন। দেখে মনে হচ্ছে, এ যেন ঢাকা শহর নয়—নেদারল্যান্ডসের কোনো এক জায়গা।
নেদারল্যান্ডসের গিথুর্ন গ্রামের ছবি যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা হয়তো জানেন, সেই গ্রামে গাড়ি চালানোর মতো কোনো রাস্তা নেই, আছে গ্রামজুড়ে চলাচলের জন্য চমৎকার খাল আর হাঁটার পথ। একটা গ্রামে কোনো গাড়ির রাস্তা নেই, খাল ও খালের ওপর আছে ১৭০টির বেশি সেতু। বৈদ্যুতিক নৌকায় করে সেই গ্রামের অধিবাসীরা এখান থেকে সেখানে যায়। আহা, গাড়ি ও জ্বালানির দূষণমুক্ত কী শান্ত মনোরম সে গ্রাম! খালের পাড় বাঁধানো, দুই পাড়ে থাকা অনুচ্চ ঘরবাড়ি, আঙিনার কোথাও কোনো খোলা মাটি নেই, পুরোটাই সবুজ কার্পেটের মতো ঘাসে ঢাকা, মাঝে মাঝে ফুলগাছের ঝোপ। যেন সে এক স্বপ্নের জায়গা, পৃথিবীর বুকেই স্বর্গের শোভা। ঢাকার এ জায়গাটি দেখেও সেই গিথুর্ন গ্রামের ছবিটা চোখে ভাসছিল। ধন্যবাদ ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনকে—নিকুঞ্জ খালের এমন সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য।
আহা রে, ঢাকা শহরের সব খাল যদি এরূপ সুন্দর হতো! এ কথা ভাবতেই মনের মধ্যে ভেসে উঠল এর বিপরীত দৃশ্য। খাল দখল করতে করতে সেগুলো সংকুচিত হয়ে পড়েছে। যতটুকু অবশিষ্ট আছে, সেগুলোও হয়ে পড়েছে ময়লার ভাগাড়, কচুরিপানা ও ঝোপঝাড়ে ভরা মশককুলের অভয়ারণ্য। বিভিন্ন কলকারখানার বর্জ্য নির্গমনের নিকাশনালার মতো ব্যবহৃত হচ্ছে কোনো কোনো খাল। পচা দুর্গন্ধযুক্ত অস্বাস্থ্যকর সেই পরিবেশেই কেটে যাচ্ছে পথচারী ও এলাকাবাসীর দিনকাল। খালগুলো যেভাবে মরতে বসেছে, তাতে আগামী ১০ বছরও লাগবে না ঢাকা শহর খালশূন্য হতে। ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী ঢাকা শহরে খালের সংখ্যা ৪৭টি। রিভার অ্যান্ড ডেল্টা সেন্টারের গবেষণা অনুযায়ী ৫৬টি। ড্যাপেও খালের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে ৪৩টি।
ধরা হয়, অতীতে ঢাকা শহরে ৪৭টি খাল সচল ছিল। শহরের চারপাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ ও বালু নদের সঙ্গে যুক্ত ছিল সেসব খাল। নৌকা ও নৌযান চলত সেসব খালে। পণ্য পরিবহন ও লোক চলাচলে সে সময় খালগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখত। একসময় শাহবাগ থেকে মগবাজার পর্যন্ত একটি খাল ছিল—পরীবাগ খাল। ঢাকা ওয়াসার মানচিত্রে তার অস্তিত্বের কথা জানা যায়। সেই খাল আর এখন নেই। এভাবে ধোলাই খাল, রায়েরবাজার, গোপীবাগ, নারিন্দা, সেগুনবাগিচা, কাঁঠালবাগান, ধানমন্ডি ইত্যাদি খালগুলোরও এখন আর অস্তিত্ব নেই। ধানমন্ডি লেকটাই একসময় ছিল খাল, হাতিরঝিলের খালে পিলখানা থেকে হাতির পালকে নিয়ে যাওয়া হতো গোসল করাতে। মোগল শাসকেরা ঢাকা শহরে বহুসংখ্যক খাল থাকায় ঢাকাকে রাজধানী করার চিন্তা করেছিল, খালগুলো তাদের চলাচল ও প্রতিরক্ষার জন্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ। শহরের জলাবদ্ধতা দূর ও পানি নিষ্কাশনের জন্যও ছিল সেগুলো সহায়ক। সেসব এখন ইতিহাস। এখন এক ঘণ্টা বৃষ্টি হলেই ঢাকা শহরের অনেক এলাকায় হাঁটুপানি জমে যায়।
ঢাকা শহরের সব খাল উদ্ধার করা প্রথম কাজ। উদ্ধারের পর সেসব খালের দুই পাড়ে ওয়াকওয়ে বা হাঁটার পথ তৈরি ও বাহারি গাছপালা লাগিয়ে সুশোভন করা দ্বিতীয় কাজ। তৃতীয় কাজ হলো খালগুলোতে নিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যাটারি, বিদ্যুৎ ও হস্তচালিত নৌযান চালনার উদ্যোগ নেওয়া। জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক কোনো নৌযান সেসব খালে চলাচলের অনুমতি না দেওয়া হবে খালের জলজ জীবগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা এবং দূষণ কমানোর গুরুত্বপূর্ণ উপায়। ওয়াকওয়ে যেন শুধু ওয়াক তথা হাঁটার জন্যই ব্যবহৃত হয়, সে রাস্তায় যেন কোনো গাড়ি বা মোটরসাইকেল না চলে। সবশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো খাল এবং তার চারপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত রাখতে উত্তম ব্যবস্থাপনার চর্চা অব্যাহত রাখা। খাল ব্যবহারকারী থেকে শুরু করে সেখানকার সব অংশীজনের সক্রিয় অংশগ্রহণই এসব ব্যবস্থাপনাকে সুচারুরূপে বাস্তবায়নের মূল সূত্র, এর সঙ্গে থাকবে সঠিক পরিকল্পনা ও নির্দেশনা, উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনার প্রচারণা। এ কাজে দরকার রাষ্ট্রীয় বা সরকারের সদিচ্ছা ও সিদ্ধান্ত, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণ, রাজনৈতিক ঐকমত্য এবং জনগণের অংশগ্রহণ। অনেক তরুণ এখন স্বেচ্ছাসেবী হয়ে এরূপ কাজে অংশ নিতে আগ্রহী। তাদের উৎসাহিত করে নিরাপদভাবে কাজের সুযোগ করে দিতে হবে। সিটি করপোরেশনের নির্ধারিত মালি ও পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা কাজ করবেন জবাবদিহির মধ্যে, স্বেচ্ছাসেবীদের সঙ্গে মিলেমিশে। শোভাবর্ধনের চারাগুলোর ব্যবস্থা করতে হবে সিটি করপোরেশনগুলোকেই। তবে এককভাবে শুধু দুই সিটি করপোরেশনের ওপর সম্পূর্ণ বিষয়টি চাপিয়ে দিলে হবে না। খালগুলোর দখলদারেরা অনেক শক্তিশালী, নিশ্চিত যে তাঁরা কেউই সেসব খালের দখল স্বেচ্ছায় ছাড়বেন না। দখলমুক্ত করার জন্য জোর প্রশাসনিক প্রচেষ্টা ও আইন প্রয়োগ করা দরকার।
প্রকৃতিতে প্রবহমান নদী আর খালগুলো হলো আমাদের দেহের শিরা-উপশিরার মতো। একটি ভূখণ্ডের জীবনরেখা বলা হয় এসব জলস্রোতকে। প্রবহমান এসব জলাশয় যেমন জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি মাটিসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্যও সহায়ক। ঢাকা শহরের প্রায় দুই কোটি মানুষের স্বাস্থ্যের কথা ভেবেও খালগুলোকে সচল করা দরকার। বর্তমানে ঢাকা শহরে ২৬টি খালের অস্তিত্ব চোখে দেখা গেলেও বাকি ২১টি খাল নেই। কোথায় কোথায় সেসব খাল ছিল, তা নিশ্চয় অতীতের মানচিত্রগুলোতে পাওয়া যাবে। সেগুলো আদৌ উদ্ধার বা দখলমুক্ত করা যাবে, তা দুরাশা। উদ্ধার করা গেলে সেগুলো খনন করে সচল ও শোভাময় করা উচিত। জার্মানির বার্লিন শহরে খালে করে ক্যানালক্রুজ করার সময় খালপাড়ের দুই পাশের বিভিন্ন স্থাপনা ও নাগরিক সৌন্দর্য, সেতু, রেস্তোরাঁ দেখতে দেখতে অভিভূত হতাম। ভাবতাম, জলের দেশ, নদীর দেশ, খালের দেশ বাংলাদেশ; অথচ সে দেশের শহরগুলোর খালে কেন এ রকম নৌ-পর্যটন করা যাবে না?
খালপাড় ভেঙে যাতে কোনো নগরবাসীর এক ফুট জমিও নষ্ট না হয়, সে জন্য ভেনিস, কোপেনহেগেন, প্যারিস ইত্যাদি শহরের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া খাল ও নদীর দুই পাড় যেভাবে পাকা করে বাঁধাই করে রাখা হয়েছে, সেভাবে আমাদের প্রবহমান খালগুলোর পাড়ও বেঁধে দেওয়া যায়। নগরীর খালগুলো নিয়ে একটি চমৎকার পরিকল্পনার সুযোগ রয়েছে ড্যাপ বাস্তবায়নের কারণে। চলাচল, পরিবহন, জলাবদ্ধতা নিরসন, দূষণ হ্রাস, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পর্যটন, সৌন্দর্যবর্ধন, স্থানীয় মানুষের আয়বর্ধন, পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদির জন্য এ ধরনের পরিকল্পনা ও জরিপকাজ নিশ্চয় সহায়ক হবে। সবার মনে রাখা উচিত, প্রাকৃতিক প্রবাহকে রুদ্ধ করার অধিকার কারও নেই, তার ফল কখনো ভালো হয় না। এ নিয়ে কোনো খণ্ডিত পরিকল্পনা নয়, নিতে হবে সমন্বিত সামগ্রিক পরিকল্পনা। তাহলে আমরাও দেখতে পাব একটি মনোরম মহানগর, সুশোভিত খালসমৃদ্ধ একটি সুশোভন পরিবেশ। কুড়িল বিশ্বরোডের কাছে নিকুঞ্জ খালটি যদি এত সুন্দর করা যায়, সুন্দর রাখা যায়, তাহলে অন্যগুলো কেন এরূপ সুন্দর হবে না?
মৃত্যুঞ্জয় রায়, কৃষিবিদ ও প্রকৃতিবিষয়ক লেখক
আরও খবর পড়ুন:
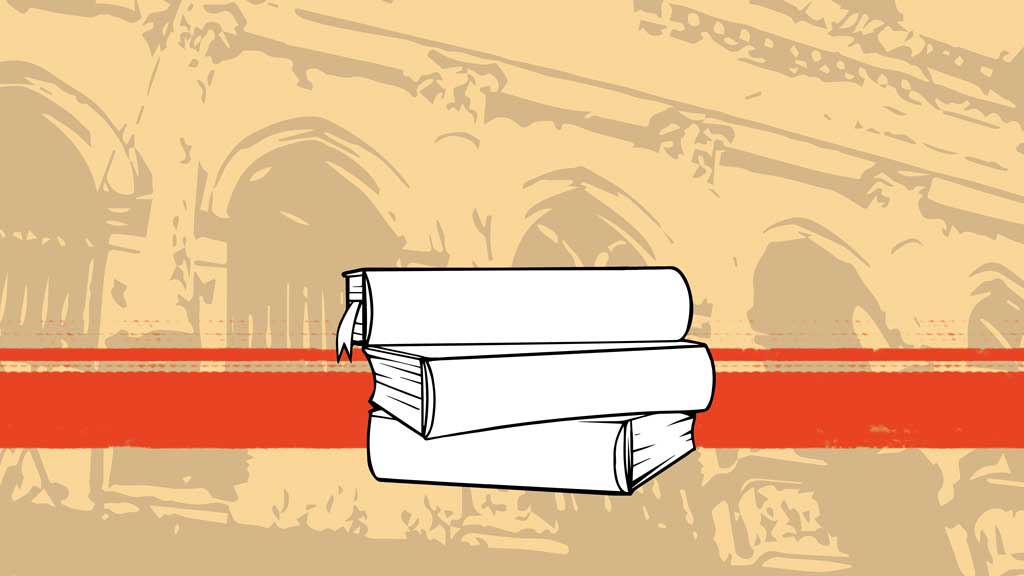
শিক্ষা শুধু একটি মৌলিক অধিকার নয়, এটি ব্যক্তি ও জাতির ক্ষমতায়নের সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো একটি তরুণ ও জনবহুল দেশে, যেখানে জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ ২৫ বছরের নিচে, সেখানে শিক্ষায় বিনিয়োগ কেবল মানবিক দায়িত্ব নয়, এটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি।
২৮ জুন ২০২৫
ডা. মুশতাক হোসেন এরশাদবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা, ডাকসুর সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং বাংলাদেশ জাসদের স্থায়ী কমিটির সদস্য। তিনি কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করেছেন। পেশাজীবনে রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ছিলেন।
১ দিন আগে
পিরোজপুরের নেছারাবাদে যে ঘটনা ঘটেছে, তার জন্য ইউএনও সাহেব ধন্যবাদ পেতেই পারেন। সেখানে একটি বিয়ের দাওয়াতে গিয়েছিলেন তিনি সপরিবারে। কিন্তু যখন জানতে পারলেন, বিয়ের কনে প্রাপ্তবয়স্ক নয়, তখন তিনি না খেয়েই ফিরে আসেন। এবং তিনি ফিরে আসায় কাজিও বিয়ে পড়াননি। ফলে এই বাল্যবিবাহ হয়নি।
১ দিন আগে
মিরপুরের শিয়ালবাড়ী এলাকায় একটি রাসায়নিক গুদামে আগুন লাগার পর যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল, সে কথা সবাই এখন জানেন। যাঁরা স্বজন হারিয়েছেন, তাঁরা জানেন এটা তাঁদের পরিবারের জন্য কত বড় ক্ষতি। নিহতদের পরিবার ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে কি না, তাদের জীবনে স্থিতি ফিরিয়ে আনতে কী করা দরকার...
২ দিন আগেসম্পাদকীয়

পিরোজপুরের নেছারাবাদে যে ঘটনা ঘটেছে, তার জন্য ইউএনও সাহেব ধন্যবাদ পেতেই পারেন। সেখানে একটি বিয়ের দাওয়াতে গিয়েছিলেন তিনি সপরিবারে। কিন্তু যখন জানতে পারলেন, বিয়ের কনে প্রাপ্তবয়স্ক নয়, তখন তিনি না খেয়েই ফিরে আসেন। এবং তিনি ফিরে আসায় কাজিও বিয়ে পড়াননি। ফলে এই বাল্যবিবাহ হয়নি।
বহু প্রচার করার পরও কোথাও কোথাও অপ্রাপ্তবয়স্ক নারী বা পুরুষের বিয়ে দেওয়া হচ্ছে পরিবারের পক্ষ থেকে। কোথাও কোথাও সচেতনতা তৈরি হচ্ছে, কোথাও কোথাও তৈরি হচ্ছে না। অনেকে ভুলে যাচ্ছেন, কেন অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের বিয়ের পিঁড়িতে না বসানোই মঙ্গল।
বাল্যবিবাহের শিকার অল্প বয়সী মেয়েরা শারীরিক ও মানসিকভাবে বিয়ের জন্য প্রস্তুত থাকে না। এতে মাতৃমৃত্যু, শিশুমৃত্যু, পুষ্টিহীনতা এবং প্রসবজনিত জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কম বয়সে সন্তানের মা হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের পক্ষে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে এবং অনেক সময় তারা শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ঝরে পড়ে। সমাজের একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ নষ্ট হয়। আত্মনির্ভরশীল হতে না পারার কারণে সংসারে নানা ধরনের সংকটে তাদের পড়তে হয়। শিক্ষাবঞ্চিত ও অল্প বয়সে সংসার শুরু করা মেয়েরা সাধারণত আর্থিকভাবে নির্ভরশীল থাকে। এতে পরিবারে দারিদ্র্য দূর হয় না, বরং প্রজন্মের পর প্রজন্ম তা চলতে থাকে।
এতে যে নারীর অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, সেটাও বিবেচনায় আনা দরকার। বাল্যবিবাহের কারণে একটি মেয়ে নিজস্ব মতামত-সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এবং স্বাধীন জীবনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারে। সামাজিকভাবে সে হেয় হতে থাকে। সংসারে তার মতামতের কোনো মূল্য থাকে না। পুরুষশাসিত সমাজে এমনিতেই মেয়েরা থাকে কোণঠাসা হয়ে, বাল্যবিবাহের শিকার মেয়েটি সে ক্ষেত্রে আরও ভঙ্গুর অবস্থায় থাকে। এ যেন তার ব্যাপারে সামাজিক নিপীড়নের জন্য একটি মুক্ত জায়গা হয়ে দেখা দেয়।
একজন মানুষ যেন মুক্ত, স্বাধীন চিন্তার অধিকারী হয়ে বেড়ে উঠতে পারে, সমাজে অর্থনৈতিক অবদান রাখার মতো করে নিজেকে তৈরি করে নিতে পারে, সেসব দিক বিবেচনা করা না হলে সংকটে পড়ে রাষ্ট্র।
পিরোজপুরের নেছারাবাদের ঘটনাটি আশার আলো জাগায়। যদিও ইউএনও বিয়ের অনুষ্ঠানে বাধা দেননি, তবু তিনি সেখানে অংশ না নিয়ে প্রতিবাদস্বরূপ চলে যাওয়ায় বিয়েটা হয়নি বলে একটি ভালো কাজ হয়েছে। যখন সমাজের একটি বড় অংশ অল্প বয়সে বিবাহ ও মাতৃত্বে জড়িয়ে পড়ে, তখন তারা কর্মক্ষম নাগরিক হিসেবে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে না। ফলে জাতির অগ্রগতিতেও বাধা সৃষ্টি হয়। অপ্রাপ্তবয়স্ক যে মেয়েটি অভিভাবকদের কারণে বাল্যবিবাহের শিকার হচ্ছিল, এখন হয়তোবা সে তা থেকে মুক্ত হবে। অভিভাবকেরাও সচেতন হয়ে এই শিশুকে শারীরিক, মানসিক, শিক্ষাগত ও সামাজিক সুরক্ষা দিতে পারেন। তাতে একটি সমৃদ্ধ ও সমানাধিকারের সমাজ গঠিত হওয়ার পথে তাঁরা অবদান রাখতে পারেন।
আরও খবর পড়ুন:

পিরোজপুরের নেছারাবাদে যে ঘটনা ঘটেছে, তার জন্য ইউএনও সাহেব ধন্যবাদ পেতেই পারেন। সেখানে একটি বিয়ের দাওয়াতে গিয়েছিলেন তিনি সপরিবারে। কিন্তু যখন জানতে পারলেন, বিয়ের কনে প্রাপ্তবয়স্ক নয়, তখন তিনি না খেয়েই ফিরে আসেন। এবং তিনি ফিরে আসায় কাজিও বিয়ে পড়াননি। ফলে এই বাল্যবিবাহ হয়নি।
বহু প্রচার করার পরও কোথাও কোথাও অপ্রাপ্তবয়স্ক নারী বা পুরুষের বিয়ে দেওয়া হচ্ছে পরিবারের পক্ষ থেকে। কোথাও কোথাও সচেতনতা তৈরি হচ্ছে, কোথাও কোথাও তৈরি হচ্ছে না। অনেকে ভুলে যাচ্ছেন, কেন অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের বিয়ের পিঁড়িতে না বসানোই মঙ্গল।
বাল্যবিবাহের শিকার অল্প বয়সী মেয়েরা শারীরিক ও মানসিকভাবে বিয়ের জন্য প্রস্তুত থাকে না। এতে মাতৃমৃত্যু, শিশুমৃত্যু, পুষ্টিহীনতা এবং প্রসবজনিত জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কম বয়সে সন্তানের মা হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের পক্ষে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে এবং অনেক সময় তারা শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ঝরে পড়ে। সমাজের একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ নষ্ট হয়। আত্মনির্ভরশীল হতে না পারার কারণে সংসারে নানা ধরনের সংকটে তাদের পড়তে হয়। শিক্ষাবঞ্চিত ও অল্প বয়সে সংসার শুরু করা মেয়েরা সাধারণত আর্থিকভাবে নির্ভরশীল থাকে। এতে পরিবারে দারিদ্র্য দূর হয় না, বরং প্রজন্মের পর প্রজন্ম তা চলতে থাকে।
এতে যে নারীর অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, সেটাও বিবেচনায় আনা দরকার। বাল্যবিবাহের কারণে একটি মেয়ে নিজস্ব মতামত-সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এবং স্বাধীন জীবনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারে। সামাজিকভাবে সে হেয় হতে থাকে। সংসারে তার মতামতের কোনো মূল্য থাকে না। পুরুষশাসিত সমাজে এমনিতেই মেয়েরা থাকে কোণঠাসা হয়ে, বাল্যবিবাহের শিকার মেয়েটি সে ক্ষেত্রে আরও ভঙ্গুর অবস্থায় থাকে। এ যেন তার ব্যাপারে সামাজিক নিপীড়নের জন্য একটি মুক্ত জায়গা হয়ে দেখা দেয়।
একজন মানুষ যেন মুক্ত, স্বাধীন চিন্তার অধিকারী হয়ে বেড়ে উঠতে পারে, সমাজে অর্থনৈতিক অবদান রাখার মতো করে নিজেকে তৈরি করে নিতে পারে, সেসব দিক বিবেচনা করা না হলে সংকটে পড়ে রাষ্ট্র।
পিরোজপুরের নেছারাবাদের ঘটনাটি আশার আলো জাগায়। যদিও ইউএনও বিয়ের অনুষ্ঠানে বাধা দেননি, তবু তিনি সেখানে অংশ না নিয়ে প্রতিবাদস্বরূপ চলে যাওয়ায় বিয়েটা হয়নি বলে একটি ভালো কাজ হয়েছে। যখন সমাজের একটি বড় অংশ অল্প বয়সে বিবাহ ও মাতৃত্বে জড়িয়ে পড়ে, তখন তারা কর্মক্ষম নাগরিক হিসেবে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে না। ফলে জাতির অগ্রগতিতেও বাধা সৃষ্টি হয়। অপ্রাপ্তবয়স্ক যে মেয়েটি অভিভাবকদের কারণে বাল্যবিবাহের শিকার হচ্ছিল, এখন হয়তোবা সে তা থেকে মুক্ত হবে। অভিভাবকেরাও সচেতন হয়ে এই শিশুকে শারীরিক, মানসিক, শিক্ষাগত ও সামাজিক সুরক্ষা দিতে পারেন। তাতে একটি সমৃদ্ধ ও সমানাধিকারের সমাজ গঠিত হওয়ার পথে তাঁরা অবদান রাখতে পারেন।
আরও খবর পড়ুন:
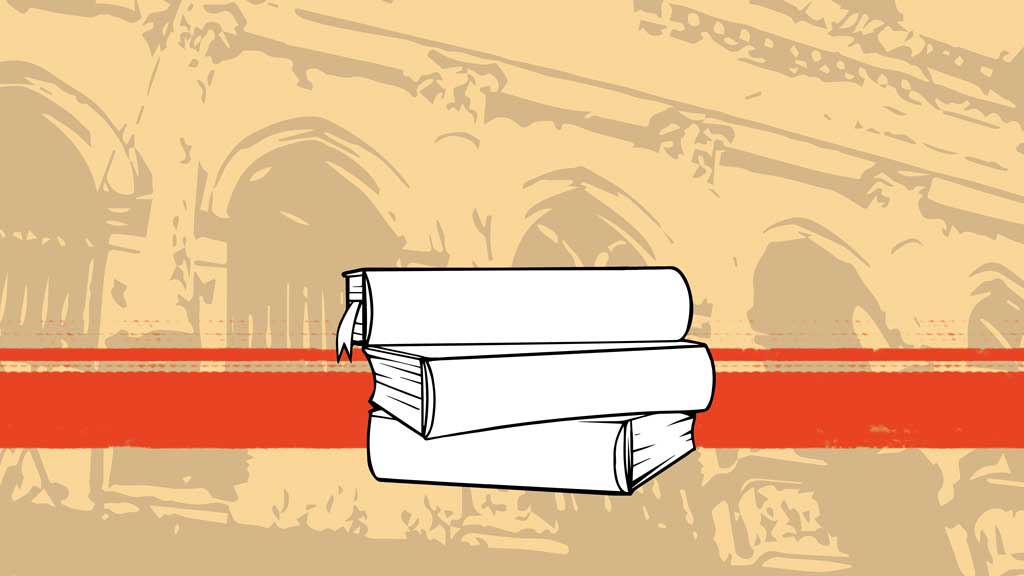
শিক্ষা শুধু একটি মৌলিক অধিকার নয়, এটি ব্যক্তি ও জাতির ক্ষমতায়নের সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো একটি তরুণ ও জনবহুল দেশে, যেখানে জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ ২৫ বছরের নিচে, সেখানে শিক্ষায় বিনিয়োগ কেবল মানবিক দায়িত্ব নয়, এটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি।
২৮ জুন ২০২৫
ডা. মুশতাক হোসেন এরশাদবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা, ডাকসুর সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং বাংলাদেশ জাসদের স্থায়ী কমিটির সদস্য। তিনি কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করেছেন। পেশাজীবনে রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ছিলেন।
১ দিন আগে
কুড়িল বিশ্বরোডের ফুটওভারব্রিজে দাঁড়িয়ে একটি খালের চমৎকার শোভা দেখে মুগ্ধ হচ্ছিলাম। ঢাকার বুকে এত সুন্দর একটা খাল! ধনুকের মতো বাঁক খেয়ে চলে গেছে দূরে, দুই পাড়ে হাঁটার রাস্তা। রাস্তা আর খালের পানির মাঝে সবুজ ঢাল সিঙ্গাপুর ডেইজির শায়িত লতায় আচ্ছাদিত।
১ দিন আগে
মিরপুরের শিয়ালবাড়ী এলাকায় একটি রাসায়নিক গুদামে আগুন লাগার পর যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল, সে কথা সবাই এখন জানেন। যাঁরা স্বজন হারিয়েছেন, তাঁরা জানেন এটা তাঁদের পরিবারের জন্য কত বড় ক্ষতি। নিহতদের পরিবার ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে কি না, তাদের জীবনে স্থিতি ফিরিয়ে আনতে কী করা দরকার...
২ দিন আগেসম্পাদকীয়

মিরপুরের শিয়ালবাড়ী এলাকায় একটি রাসায়নিক গুদামে আগুন লাগার পর যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল, সে কথা সবাই এখন জানেন। যাঁরা স্বজন হারিয়েছেন, তাঁরা জানেন এটা তাঁদের পরিবারের জন্য কত বড় ক্ষতি। নিহতদের পরিবার ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে কি না, তাদের জীবনে স্থিতি ফিরিয়ে আনতে কী করা দরকার—তা নিয়ে সংশ্লিষ্টরা নিশ্চয়ই ভাববেন। এ রকম একটা অবস্থায় দুর্ঘটনা-পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে খুব কম মানুষই মাথা ঘামায়। দুর্ঘটনা-পরবর্তী সময়টিতে স্থানীয় পরিবেশ ও পরিস্থিতি যে মোটেও অনুকূল থাকে না, সেটা বোঝা দরকার।
সম্প্রতি আমাদের প্রতিবেদক শিয়ালবাড়ীর ক্ষতিগ্রস্ত রাসায়নিক গুদামে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখেছেন, এতগুলো দিন পার হওয়ার পরও বিষাক্ত রাসায়নিকের কারণে এখনো অসুস্থ হচ্ছে মানুষ। রাসায়নিকের ড্রাম থেকে নির্গত বিষাক্ত গ্যাস ও ধোঁয়া মানুষকে অসুস্থ করে দিচ্ছে। অসুস্থদের মধ্যে শিশু ও বৃদ্ধরা রয়েছেন ঝুঁকির মধ্যে। প্রায়ই দেখা যায়, একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর দু-এক দিন সংবাদপত্রে রিপোর্ট হয়, তারপর একসময় সেটা ভুলে যায় মানুষ। কিন্তু যে মানুষেরা ভুক্তভোগী, তাদের প্রতিটি দিনই যে কাটছে ভয়ংকর রাসায়নিকের সঙ্গে লড়াই করে, সে খবর কয়জন রাখে?
চিকিৎসকেরা বলেছেন, অগ্নিকাণ্ডের কয়েক দিন পরও বিষাক্ত গ্যাস ও ধোঁয়ার ঘনত্ব বেশি থাকে। পরে ধীরে ধীরে তা কমে যায়। মাটিতে পড়ে থাকা রাসায়নিক দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ ভুক্তভোগীর শরীরে ঢোকে। ঘন ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ার কারণে বাতাসে ভাসমান ক্ষুদ্র ধূলিকণা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে যায়। এই কারণে ভবিষ্যতেও তা বিপদ সৃষ্টি করতে পারে।
বিষাক্ত কণিকা বা গ্যাস মানবদেহে ঢোকে শ্বাসের মাধ্যমে, ত্বকের মাধ্যমে এবং খাদ্যের মাধ্যমে। এই গ্যাস অ্যাজমা, কাশি, গলাজ্বলা বা শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। চোখ আর ত্বকও তাতে আক্রান্ত হতে পারে। তৈরি হতে পারে মাথাব্যথা, বমি ও ক্লান্তির মতো ঘটনা। ভারী ধাতু দীর্ঘ মেয়াদে স্নায়ুতন্ত্র দুর্বল করে দেয়। তাতে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে।
শিয়ালবাড়ীর দুর্ঘটনাস্থলের অন্তত এক হাজার গজ পর্যন্ত এলাকায় বাতাসে এখনো পোড়া জিনিস ও গ্যাসের মতো কটু গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। তাতে মনে হয়, এই এলাকার মানুষের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি এখনো রয়েছে সংকটের মুখে।
আমরা সবাই জানি, স্বাস্থ্য আমাদের মৌলিক অধিকারের একটি। কিন্তু দেশের মানুষ এ কথাও জানে, সেই মৌলিক অধিকার সব সময় সমুন্নত রাখা হয় না। রাসায়নিক গুদামে অগ্নিকাণ্ড ঘটলে কীভাবে তার মোকাবিলা করতে হবে, তার পূর্বপ্রস্তুতি কয়টি গুদামে আছে? এসব জায়গায় কি নিয়মিত ইন্সপেকশন হয়? শুধু গুদাম কেন, কারখানাগুলোয় কি সঠিক নিরাপত্তাব্যবস্থা রয়েছে? শ্রমিকেরা কি নিরাপদে তাঁদের কাজ করে যেতে পারেন?
এসব দুর্ঘটনায় মূলত সমাজের নিচুতলার মানুষেরা বিপদে পড়েন। তাঁদের পাশে যদি দাঁড়ানো না হয়, তাহলে বুঝতে হবে, শিল্প-ব্যবস্থাপনায় যে ঘাটতি আছে, তা নিরসনের কোনো চিন্তা কারও নেই।

মিরপুরের শিয়ালবাড়ী এলাকায় একটি রাসায়নিক গুদামে আগুন লাগার পর যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল, সে কথা সবাই এখন জানেন। যাঁরা স্বজন হারিয়েছেন, তাঁরা জানেন এটা তাঁদের পরিবারের জন্য কত বড় ক্ষতি। নিহতদের পরিবার ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে কি না, তাদের জীবনে স্থিতি ফিরিয়ে আনতে কী করা দরকার—তা নিয়ে সংশ্লিষ্টরা নিশ্চয়ই ভাববেন। এ রকম একটা অবস্থায় দুর্ঘটনা-পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে খুব কম মানুষই মাথা ঘামায়। দুর্ঘটনা-পরবর্তী সময়টিতে স্থানীয় পরিবেশ ও পরিস্থিতি যে মোটেও অনুকূল থাকে না, সেটা বোঝা দরকার।
সম্প্রতি আমাদের প্রতিবেদক শিয়ালবাড়ীর ক্ষতিগ্রস্ত রাসায়নিক গুদামে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখেছেন, এতগুলো দিন পার হওয়ার পরও বিষাক্ত রাসায়নিকের কারণে এখনো অসুস্থ হচ্ছে মানুষ। রাসায়নিকের ড্রাম থেকে নির্গত বিষাক্ত গ্যাস ও ধোঁয়া মানুষকে অসুস্থ করে দিচ্ছে। অসুস্থদের মধ্যে শিশু ও বৃদ্ধরা রয়েছেন ঝুঁকির মধ্যে। প্রায়ই দেখা যায়, একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর দু-এক দিন সংবাদপত্রে রিপোর্ট হয়, তারপর একসময় সেটা ভুলে যায় মানুষ। কিন্তু যে মানুষেরা ভুক্তভোগী, তাদের প্রতিটি দিনই যে কাটছে ভয়ংকর রাসায়নিকের সঙ্গে লড়াই করে, সে খবর কয়জন রাখে?
চিকিৎসকেরা বলেছেন, অগ্নিকাণ্ডের কয়েক দিন পরও বিষাক্ত গ্যাস ও ধোঁয়ার ঘনত্ব বেশি থাকে। পরে ধীরে ধীরে তা কমে যায়। মাটিতে পড়ে থাকা রাসায়নিক দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ ভুক্তভোগীর শরীরে ঢোকে। ঘন ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ার কারণে বাতাসে ভাসমান ক্ষুদ্র ধূলিকণা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে যায়। এই কারণে ভবিষ্যতেও তা বিপদ সৃষ্টি করতে পারে।
বিষাক্ত কণিকা বা গ্যাস মানবদেহে ঢোকে শ্বাসের মাধ্যমে, ত্বকের মাধ্যমে এবং খাদ্যের মাধ্যমে। এই গ্যাস অ্যাজমা, কাশি, গলাজ্বলা বা শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। চোখ আর ত্বকও তাতে আক্রান্ত হতে পারে। তৈরি হতে পারে মাথাব্যথা, বমি ও ক্লান্তির মতো ঘটনা। ভারী ধাতু দীর্ঘ মেয়াদে স্নায়ুতন্ত্র দুর্বল করে দেয়। তাতে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে।
শিয়ালবাড়ীর দুর্ঘটনাস্থলের অন্তত এক হাজার গজ পর্যন্ত এলাকায় বাতাসে এখনো পোড়া জিনিস ও গ্যাসের মতো কটু গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। তাতে মনে হয়, এই এলাকার মানুষের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি এখনো রয়েছে সংকটের মুখে।
আমরা সবাই জানি, স্বাস্থ্য আমাদের মৌলিক অধিকারের একটি। কিন্তু দেশের মানুষ এ কথাও জানে, সেই মৌলিক অধিকার সব সময় সমুন্নত রাখা হয় না। রাসায়নিক গুদামে অগ্নিকাণ্ড ঘটলে কীভাবে তার মোকাবিলা করতে হবে, তার পূর্বপ্রস্তুতি কয়টি গুদামে আছে? এসব জায়গায় কি নিয়মিত ইন্সপেকশন হয়? শুধু গুদাম কেন, কারখানাগুলোয় কি সঠিক নিরাপত্তাব্যবস্থা রয়েছে? শ্রমিকেরা কি নিরাপদে তাঁদের কাজ করে যেতে পারেন?
এসব দুর্ঘটনায় মূলত সমাজের নিচুতলার মানুষেরা বিপদে পড়েন। তাঁদের পাশে যদি দাঁড়ানো না হয়, তাহলে বুঝতে হবে, শিল্প-ব্যবস্থাপনায় যে ঘাটতি আছে, তা নিরসনের কোনো চিন্তা কারও নেই।
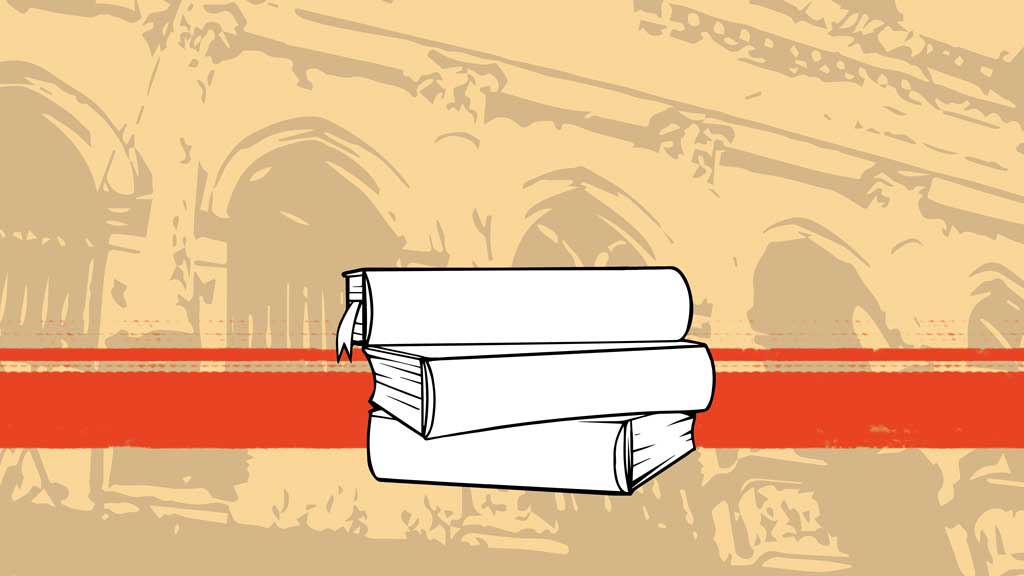
শিক্ষা শুধু একটি মৌলিক অধিকার নয়, এটি ব্যক্তি ও জাতির ক্ষমতায়নের সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো একটি তরুণ ও জনবহুল দেশে, যেখানে জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ ২৫ বছরের নিচে, সেখানে শিক্ষায় বিনিয়োগ কেবল মানবিক দায়িত্ব নয়, এটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি।
২৮ জুন ২০২৫
ডা. মুশতাক হোসেন এরশাদবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা, ডাকসুর সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং বাংলাদেশ জাসদের স্থায়ী কমিটির সদস্য। তিনি কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করেছেন। পেশাজীবনে রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ছিলেন।
১ দিন আগে
কুড়িল বিশ্বরোডের ফুটওভারব্রিজে দাঁড়িয়ে একটি খালের চমৎকার শোভা দেখে মুগ্ধ হচ্ছিলাম। ঢাকার বুকে এত সুন্দর একটা খাল! ধনুকের মতো বাঁক খেয়ে চলে গেছে দূরে, দুই পাড়ে হাঁটার রাস্তা। রাস্তা আর খালের পানির মাঝে সবুজ ঢাল সিঙ্গাপুর ডেইজির শায়িত লতায় আচ্ছাদিত।
১ দিন আগে
পিরোজপুরের নেছারাবাদে যে ঘটনা ঘটেছে, তার জন্য ইউএনও সাহেব ধন্যবাদ পেতেই পারেন। সেখানে একটি বিয়ের দাওয়াতে গিয়েছিলেন তিনি সপরিবারে। কিন্তু যখন জানতে পারলেন, বিয়ের কনে প্রাপ্তবয়স্ক নয়, তখন তিনি না খেয়েই ফিরে আসেন। এবং তিনি ফিরে আসায় কাজিও বিয়ে পড়াননি। ফলে এই বাল্যবিবাহ হয়নি।
১ দিন আগে