জাহীদ রেজা নূর

ঘটনাবলি এত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে যে কোন ঘটনার সঙ্গে কোন ঘটনাকে মিলিয়ে একটা যুক্তিসংগত সিদ্ধান্তে আসা যাবে, তা একেবারেই বোঝা যাচ্ছে না। কে কার পক্ষ নিচ্ছে এবং কে কোন পক্ষ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিচ্ছে, সেটাও প্রশ্নসাপেক্ষ। এ রকম একটি অবস্থায় মূল ঘটনাগুলো থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা করাই উত্তম। দূর থেকে বিষয়টিকে ভালোভাবে দেখা যায়।
এই পর্যায়ে আমার মতো একজন রাজনীতি-অনভিজ্ঞ মানুষ রাজনীতির বাণী না শুনিয়ে বরং উচিত হবে অন্য বিষয়ে আলোকপাত করা।
খুলনা শহরে বেড়াতে এসে প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যেও ভোরবেলায় শহীদ হাদিস পার্কে স্বাস্থ্য উদ্ধারে আসা মানুষের সংখ্যা বুঝিয়ে দেয়, রাজনৈতিক ডামাডোল বা কোলাহলের বাইরেও একটা জগৎ আছে। তবে ব্যায়াম ও হাঁটাচলার মাঝেই টুকরো টুকরো যে কথাগুলো কানে আসে, তাতে রাজনীতি একেবারেই থাকে না, এমন নয়। এবং সেই রাজনীতি স্থানীয় পর্যায় থেকে বাড়তে বাড়তে জাতীয় পর্যায়ে উপনীত হয়। তবে তা কখনোই চিৎকার-চেঁচামেচিতে পরিণত হয় না। সবাই বুঝে গেছে, এই মুহূর্তে কোন কথা বললে কোন পরিণতি হবে, সেটা যেহেতু অজানা, তাই সেলফ সেন্সরশিপ আরোপ করার মধ্যেই বেঁচে থাকার সার্থকতা রয়েছে।
খুলনাবাসী কারও কারও সঙ্গে যেসব কথা হয়েছে, তাতে শহরের নানা ধরনের অসংগতি এবং নানা ধরনের প্রত্যাশার বিষয়গুলোও উঠে এসেছে। কেউ কেউ বলার চেষ্টা করেছেন, সরকারি যে বাসভবনগুলো রয়েছে বিশাল এলাকাজুড়ে, সেগুলো ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে অনেক জায়গার সংস্থান হতে পারত। কেন একজন বড় সরকারি কর্মকর্তার বিশাল বড় এলাকাজুড়ে বাড়ি থাকবে, সেই প্রশ্ন তুলেছেন কেউ কেউ। চলতি পথে একজন সতীর্থ আলী আজগর লবির বাড়িটি দেখিয়ে বললেন, এখন এই বাড়ি আবার সক্রিয় হচ্ছে।
একটি ছোট বাজারে অদ্ভুত এক দেয়াললিখন দেখা গেল। দেখে আনন্দ হলো, তেমনি বিষাদ এসেও ভর করল মনে।
দেয়াললিখনটা হলো, ‘২০ বছরে হয়নি যে সমস্যার সমাধান, তা আর হবে না এটা জেনে গেছে ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের জনগণ’।
আমার কাছে ভাষ্যটি অভিনব লাগল। এভাবেও যে প্রতিবাদ করা যায়, সেটা আমার জানা ছিল না। আমার কাছে খুবই শৈল্পিক মনে হয়েছে প্রতিবাদের ধরনটি। চারদিকে যখন মার মার কাট কাট, একে ধর, ওকে জবাই কর ইত্যাদি স্লোগানের কারণে চিত্ত বিচলিত হচ্ছে, তখন এ রকম একটি শ্লেষ বা ব্যঙ্গ যে কত উচ্চাঙ্গের বার্তা দেয়, সেটা নতুন করে বলে দিতে হবে না।
খুলনার এই ২৩ নম্বর ওয়ার্ডটি কোথায়, কী সমস্যা আছে এখানে, তার কিছুই আমার জানা নেই। কিন্তু এই এলাকার মানুষ একটি নতুন ধরনের প্রতিবাদের ভাষা আবিষ্কার করেছে, এটা জেনে ভালো লাগল।
খুলনা শহরে এখন কটা সিনেমা হল রয়েছে, তা আমার জানা নেই। কিন্তু অন্তত দুটি সিনেমা হল দেখলাম, যেগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিনোদনের জন্য মফস্বল শহরের সিনেমা হলগুলো অপাঙ্ক্তেয় হয়ে গেল কি না, সেই প্রশ্ন চাইলেও এড়ানো যাবে না। আমরা তো দেখেছি, আমাদের সাংস্কৃতিক অর্জনের অনেক কিছুই নানাভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। এটাও তারই একটি লক্ষণ বলে মনে করলে ভুল হবে না। তবে এ কথাও ঠিক, সবার হাতে একটা করে স্মার্টফোন থাকায় সিনেমা দেখার চাহিদা সেখানেই মিটিয়ে ফেলা যায়। তাই দল বেঁধে সিনেমা হলে যাওয়ার উৎসবে ভাটা পড়েছে।
আমাদের দেশে সাংস্কৃতিক চর্চা দিনে দিনে কমেছে, এটা সত্য। আগে যেরকম মুদিদোকানেও আধুনিক গান কিংবা সিনেমার গান বাজত, এখন কি আর সেরকম কিছু শোনা যায়? পরমতসহিষ্ণু হতে হলে সাংস্কৃতিক চর্চা মজ্জাগতভাবে রক্তের মধ্যে থাকতে হয় এবং তা গড়ে ওঠে পরিবার ও সমাজে প্রবাহিত আচার-আচরণ প্রভৃতির মাধ্যমে, সে কথা ধীরে ধীরে ভুলে যাচ্ছে মানুষ। তাই শুধু পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের দিকেই নজর দিচ্ছেন অভিভাবকেরা, শিক্ষকেরাও শিক্ষার্থীদের মনকর্ষণ না করে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার দিকেই নজর দিচ্ছেন এবং কখনো কখনো সেই পথ দেখিয়ে দেওয়ার জন্য কোচিংয়ের মাধ্যমে কামিয়ে নিচ্ছেন টুপাইস।
খুলনার মানুষ কি এখনো সিনেমা দেখতে যায়? চোখের সামনেই তো অন্তত দুটি মৃত সিনেমা হল দেখতে হয়েছে। কটা টিকে আছে শহরে? পিকচার প্যালেস আর সোসাইটি নামের সিনেমা হলগুলোর জিন্দা লাশ দেখলাম রাস্তায়।
প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা রতন সেন যেখানে খুন হয়েছিলেন, সেখানে রয়েছে একটি স্মৃতিস্তম্ভ। সেখানে একটি ফলকে লেখা রয়েছে: ‘মানব রতন তুমি চির মানব সাথী!’
২.
শহীদ হাদিস পার্কে দ্বিতীয় দিন হাঁটতে গিয়ে ব্যায়াম করছিলেন যাঁরা, তাঁদের কথাবার্তায় আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার বিষয়টি উঠে আসছিল। লেখার শুরুতেই বলেছি, এখন দেশে যে ঘটনাগুলো ঘটছে, তা আসলে সময়ের ব্যবধান থেকে দেখতে হবে। নইলে মূল ঘটনা বোঝা যাবে না।
প্রধান উপদেষ্টার বাসায় যাওয়ার সামনের রাস্তাটায় কোনো ধরনের আন্দোলন করা যাবে না—এ রকম একটি নিষেধাজ্ঞা থাকার পরও কীভাবে সেখানে বিক্ষোভকারীরা জড়ো হলো, তা নিয়ে নানা ধরনের মুখরোচক কথাবার্তা শোনা গেল। একজন বললেন, সরকার যে কাজটি করতে চায়, সেটা এই বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে তাদের নির্দেশনা দিয়ে দেয়। এরপর এমন একটা ভাব করে যে চাপের মুখে পড়ে তারা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। কেউ কেউ বলছেন, এটা পাতানো খেলা।
এ কথার প্রতিবাদও করছেন কেউ কেউ। কিন্তু এমন কাউকে কোথাও পাওয়া গেল না, যাঁরা বললেন, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর কোনো একটা আশাবাদী ঘটনা ঘটতে দেখেছেন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আওয়ামী লীগ সরকারের যেসব কাজকে ফ্যাসিবাদী বলা হয়েছিল, এ সময়েও একই ধরনের কাজ হচ্ছে কি না, সেই প্রশ্ন তুললেন কেউ কেউ।
আওয়ামী লীগ নির্বাহী আদেশে জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ করেছিল বলে যাঁরা সমালোচনা করতেন, একই ঘটনা আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঘটায় তাঁরা কোন মনোভাব পোষণ করেন, সেটাও জানতে চাইলেন কেউ কেউ। এবং হাস্যচ্ছলে কেউ কেউ বললেন, ‘যে যায় লঙ্কায়, সে হয় রাবণ।’
৩.
কোনো রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে সেই দলকে কি কবর দেওয়া যায়? জামায়াতে ইসলামীকে কি আওয়ামী লীগ রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে পেরেছে? বরং আওয়ামী লীগের রাজনীতি এই মুহূর্তে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলে সেই রাজনীতি অন্য কোনো না কোনোভাবে রাষ্ট্রের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করবে। কোন ফর্মে সেটা আসবে, তা এখনই বলে দেওয়া যাবে না। সরকারবিরোধী আন্দোলনের সময় যেভাবে সরকারি দলের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে ছিল শিবিরের ছেলেরা, সেভাবেই ছাত্রলীগ কিংবা আওয়ামী লীগ কার ভেতরে ঢুকে যাবে, তা আগাম বলা যাবে না। জোর করে কারও মুখ বন্ধ রাখা গণতন্ত্রের ভাষা নয়। প্রশ্ন হলো, এই দেশ গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে কার্যক্রম চালালেও মূলত গণতান্ত্রিক অবয়বের মধ্যে নানা সময়ে স্বৈরাচার ভর করেছিল। এমন কোনো রাজনৈতিক সংগঠন দেখানো যাবে না, যাদের মধ্যে ক্ষমতার রেষারেষি নেই, অন্যকে গলা টিপে হত্যা করার প্রবণতা নেই। ক্ষমতায় থাকুক আর না থাকুক, ক্ষমতা দেখানোর সুযোগ থাকলেই প্রয়োগ করা যে কত সহজ, সেই উদাহরণ দিতে খুব বেশি দূর যেতে হবে না।
৪.
আজই হোয়াটসঅ্যাপে এক মিনিট এক সেকেন্ডের একটি ভিডিও দেখে মন ভালো হয়ে গেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয়ের ৮০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ভিডিওটি। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের যেসব গুরুত্বপূর্ণ ভাস্কর্য রয়েছে, সেই ভাস্কর্যের চরিত্রগুলো নেমে এসে মানুষের কাতারে দাঁড়াচ্ছে, মানুষের সঙ্গে ভাব বিনিময় করছে—এই হচ্ছে মূল থিম। এখন সোভিয়েত ইউনিয়ন নেই, সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখে না রাশিয়া, কিন্তু সম্মিলিত সেই বিজয়কে তারা হৃদয়ে ধারণ করে। এই বিজয়ে পুরো জাতি গর্বিত।
আমাদের দুর্ভাগ্য হলো, বিজয় অর্জনের পরপরই বিজয়ের পরাজয় ঘটে গেছে। আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, পরমতসহিষ্ণুতা, মানবতা ইত্যাদি থেকে আমরা ধীরে ধীরে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিয়েছি। পশুশক্তিকেই ভেবেছি আদ্যাশক্তি। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্রকেই সবচেয়ে কলুষিত করেছি। মুক্তিযুদ্ধে যারা পরাজিত হয়েছিল, তারা একবারের জন্য ভাবেনি যে জাতির কাছে তাদের ক্ষমা চাইতে হবে। অথচ তাদের একসময় রাজনীতি করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। সেই বোঝা বইতে বইতে জাতি এখন আর তা নিয়ে মোটেই বিচলিত নয়। ভুলে গেছে সেসব।
জনগণের বিজয়কে কুক্ষিগত করা কারও জন্যই শোভন নয়। অথচ আমাদের জাতি বারবার সেটাও দেখেছে। শতচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বিজয়ীদের ঐক্য। এবং যেকোনো জায়গায় নিজেদের ক্ষমতার প্রকাশ দেখাতে গিয়ে নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের বিশালতাকেও খেলো করে ফেলা হয়েছে। ফলে যদি কেউ মনে করে যে তরুণেরা সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে, তারা যা ভাববে সেটাই ঠিক পথ, তাহলে সেই ভাবনার মধ্যে কতটা সত্য থাকবে, সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে। কারণ, অজস্র আবর্জনার মধ্য থেকে সত্য তুলে ধরার জন্য যে প্রয়াস প্রয়োজন, তা নিজের মেধা ও পরিশ্রম দিয়ে অর্জন করার পথে কজন হাঁটবে? যদি নেতৃত্বের মধ্যেই গলদ থাকে, তাহলে এগিয়ে যাওয়া খুব কঠিন।
এখন অনেকেই প্রশ্ন করতে পারে, যে সংস্কারের কথা বলা হলো, তা আসলে করবে কে? প্রশ্ন করতে পারে, মেধা ও অভিজ্ঞতার মধ্যে মিলন না ঘটলে যে অরাজকতা সৃষ্টি হবে, তার দায়ভার কে নেবে? প্রশ্ন করতে পারে, ১৯৭১ সালকে মূল্য দেওয়ার ধরন দেখেই দুষ্কৃতকারীদের মতলব বোঝা যায় এবং বোঝা যায় মূলত দেশপ্রেমী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটছে কি না। এই প্রশ্নগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গায়ের জোরে যা করা যায়, ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে আঁতাত করে যা করা যায়, ইতিহাসের বিচারের জন্য একসময় তা কাঠগড়ায় দাঁড়াবেই।
কিন্তু সেই বিচারের জন্য ভাবনা ও চিন্তাশীলতার যে গভীরতা প্রয়োজন, সেটা না থাকলে কী হবে, তা কেউ বিবেচনা করে দেখছে না এখনো। মূল ভয়ের কারণ সেটাই।

ঘটনাবলি এত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে যে কোন ঘটনার সঙ্গে কোন ঘটনাকে মিলিয়ে একটা যুক্তিসংগত সিদ্ধান্তে আসা যাবে, তা একেবারেই বোঝা যাচ্ছে না। কে কার পক্ষ নিচ্ছে এবং কে কোন পক্ষ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিচ্ছে, সেটাও প্রশ্নসাপেক্ষ। এ রকম একটি অবস্থায় মূল ঘটনাগুলো থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা করাই উত্তম। দূর থেকে বিষয়টিকে ভালোভাবে দেখা যায়।
এই পর্যায়ে আমার মতো একজন রাজনীতি-অনভিজ্ঞ মানুষ রাজনীতির বাণী না শুনিয়ে বরং উচিত হবে অন্য বিষয়ে আলোকপাত করা।
খুলনা শহরে বেড়াতে এসে প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যেও ভোরবেলায় শহীদ হাদিস পার্কে স্বাস্থ্য উদ্ধারে আসা মানুষের সংখ্যা বুঝিয়ে দেয়, রাজনৈতিক ডামাডোল বা কোলাহলের বাইরেও একটা জগৎ আছে। তবে ব্যায়াম ও হাঁটাচলার মাঝেই টুকরো টুকরো যে কথাগুলো কানে আসে, তাতে রাজনীতি একেবারেই থাকে না, এমন নয়। এবং সেই রাজনীতি স্থানীয় পর্যায় থেকে বাড়তে বাড়তে জাতীয় পর্যায়ে উপনীত হয়। তবে তা কখনোই চিৎকার-চেঁচামেচিতে পরিণত হয় না। সবাই বুঝে গেছে, এই মুহূর্তে কোন কথা বললে কোন পরিণতি হবে, সেটা যেহেতু অজানা, তাই সেলফ সেন্সরশিপ আরোপ করার মধ্যেই বেঁচে থাকার সার্থকতা রয়েছে।
খুলনাবাসী কারও কারও সঙ্গে যেসব কথা হয়েছে, তাতে শহরের নানা ধরনের অসংগতি এবং নানা ধরনের প্রত্যাশার বিষয়গুলোও উঠে এসেছে। কেউ কেউ বলার চেষ্টা করেছেন, সরকারি যে বাসভবনগুলো রয়েছে বিশাল এলাকাজুড়ে, সেগুলো ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে অনেক জায়গার সংস্থান হতে পারত। কেন একজন বড় সরকারি কর্মকর্তার বিশাল বড় এলাকাজুড়ে বাড়ি থাকবে, সেই প্রশ্ন তুলেছেন কেউ কেউ। চলতি পথে একজন সতীর্থ আলী আজগর লবির বাড়িটি দেখিয়ে বললেন, এখন এই বাড়ি আবার সক্রিয় হচ্ছে।
একটি ছোট বাজারে অদ্ভুত এক দেয়াললিখন দেখা গেল। দেখে আনন্দ হলো, তেমনি বিষাদ এসেও ভর করল মনে।
দেয়াললিখনটা হলো, ‘২০ বছরে হয়নি যে সমস্যার সমাধান, তা আর হবে না এটা জেনে গেছে ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের জনগণ’।
আমার কাছে ভাষ্যটি অভিনব লাগল। এভাবেও যে প্রতিবাদ করা যায়, সেটা আমার জানা ছিল না। আমার কাছে খুবই শৈল্পিক মনে হয়েছে প্রতিবাদের ধরনটি। চারদিকে যখন মার মার কাট কাট, একে ধর, ওকে জবাই কর ইত্যাদি স্লোগানের কারণে চিত্ত বিচলিত হচ্ছে, তখন এ রকম একটি শ্লেষ বা ব্যঙ্গ যে কত উচ্চাঙ্গের বার্তা দেয়, সেটা নতুন করে বলে দিতে হবে না।
খুলনার এই ২৩ নম্বর ওয়ার্ডটি কোথায়, কী সমস্যা আছে এখানে, তার কিছুই আমার জানা নেই। কিন্তু এই এলাকার মানুষ একটি নতুন ধরনের প্রতিবাদের ভাষা আবিষ্কার করেছে, এটা জেনে ভালো লাগল।
খুলনা শহরে এখন কটা সিনেমা হল রয়েছে, তা আমার জানা নেই। কিন্তু অন্তত দুটি সিনেমা হল দেখলাম, যেগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিনোদনের জন্য মফস্বল শহরের সিনেমা হলগুলো অপাঙ্ক্তেয় হয়ে গেল কি না, সেই প্রশ্ন চাইলেও এড়ানো যাবে না। আমরা তো দেখেছি, আমাদের সাংস্কৃতিক অর্জনের অনেক কিছুই নানাভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। এটাও তারই একটি লক্ষণ বলে মনে করলে ভুল হবে না। তবে এ কথাও ঠিক, সবার হাতে একটা করে স্মার্টফোন থাকায় সিনেমা দেখার চাহিদা সেখানেই মিটিয়ে ফেলা যায়। তাই দল বেঁধে সিনেমা হলে যাওয়ার উৎসবে ভাটা পড়েছে।
আমাদের দেশে সাংস্কৃতিক চর্চা দিনে দিনে কমেছে, এটা সত্য। আগে যেরকম মুদিদোকানেও আধুনিক গান কিংবা সিনেমার গান বাজত, এখন কি আর সেরকম কিছু শোনা যায়? পরমতসহিষ্ণু হতে হলে সাংস্কৃতিক চর্চা মজ্জাগতভাবে রক্তের মধ্যে থাকতে হয় এবং তা গড়ে ওঠে পরিবার ও সমাজে প্রবাহিত আচার-আচরণ প্রভৃতির মাধ্যমে, সে কথা ধীরে ধীরে ভুলে যাচ্ছে মানুষ। তাই শুধু পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের দিকেই নজর দিচ্ছেন অভিভাবকেরা, শিক্ষকেরাও শিক্ষার্থীদের মনকর্ষণ না করে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার দিকেই নজর দিচ্ছেন এবং কখনো কখনো সেই পথ দেখিয়ে দেওয়ার জন্য কোচিংয়ের মাধ্যমে কামিয়ে নিচ্ছেন টুপাইস।
খুলনার মানুষ কি এখনো সিনেমা দেখতে যায়? চোখের সামনেই তো অন্তত দুটি মৃত সিনেমা হল দেখতে হয়েছে। কটা টিকে আছে শহরে? পিকচার প্যালেস আর সোসাইটি নামের সিনেমা হলগুলোর জিন্দা লাশ দেখলাম রাস্তায়।
প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা রতন সেন যেখানে খুন হয়েছিলেন, সেখানে রয়েছে একটি স্মৃতিস্তম্ভ। সেখানে একটি ফলকে লেখা রয়েছে: ‘মানব রতন তুমি চির মানব সাথী!’
২.
শহীদ হাদিস পার্কে দ্বিতীয় দিন হাঁটতে গিয়ে ব্যায়াম করছিলেন যাঁরা, তাঁদের কথাবার্তায় আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার বিষয়টি উঠে আসছিল। লেখার শুরুতেই বলেছি, এখন দেশে যে ঘটনাগুলো ঘটছে, তা আসলে সময়ের ব্যবধান থেকে দেখতে হবে। নইলে মূল ঘটনা বোঝা যাবে না।
প্রধান উপদেষ্টার বাসায় যাওয়ার সামনের রাস্তাটায় কোনো ধরনের আন্দোলন করা যাবে না—এ রকম একটি নিষেধাজ্ঞা থাকার পরও কীভাবে সেখানে বিক্ষোভকারীরা জড়ো হলো, তা নিয়ে নানা ধরনের মুখরোচক কথাবার্তা শোনা গেল। একজন বললেন, সরকার যে কাজটি করতে চায়, সেটা এই বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে তাদের নির্দেশনা দিয়ে দেয়। এরপর এমন একটা ভাব করে যে চাপের মুখে পড়ে তারা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। কেউ কেউ বলছেন, এটা পাতানো খেলা।
এ কথার প্রতিবাদও করছেন কেউ কেউ। কিন্তু এমন কাউকে কোথাও পাওয়া গেল না, যাঁরা বললেন, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর কোনো একটা আশাবাদী ঘটনা ঘটতে দেখেছেন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আওয়ামী লীগ সরকারের যেসব কাজকে ফ্যাসিবাদী বলা হয়েছিল, এ সময়েও একই ধরনের কাজ হচ্ছে কি না, সেই প্রশ্ন তুললেন কেউ কেউ।
আওয়ামী লীগ নির্বাহী আদেশে জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ করেছিল বলে যাঁরা সমালোচনা করতেন, একই ঘটনা আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঘটায় তাঁরা কোন মনোভাব পোষণ করেন, সেটাও জানতে চাইলেন কেউ কেউ। এবং হাস্যচ্ছলে কেউ কেউ বললেন, ‘যে যায় লঙ্কায়, সে হয় রাবণ।’
৩.
কোনো রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে সেই দলকে কি কবর দেওয়া যায়? জামায়াতে ইসলামীকে কি আওয়ামী লীগ রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে পেরেছে? বরং আওয়ামী লীগের রাজনীতি এই মুহূর্তে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলে সেই রাজনীতি অন্য কোনো না কোনোভাবে রাষ্ট্রের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করবে। কোন ফর্মে সেটা আসবে, তা এখনই বলে দেওয়া যাবে না। সরকারবিরোধী আন্দোলনের সময় যেভাবে সরকারি দলের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে ছিল শিবিরের ছেলেরা, সেভাবেই ছাত্রলীগ কিংবা আওয়ামী লীগ কার ভেতরে ঢুকে যাবে, তা আগাম বলা যাবে না। জোর করে কারও মুখ বন্ধ রাখা গণতন্ত্রের ভাষা নয়। প্রশ্ন হলো, এই দেশ গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে কার্যক্রম চালালেও মূলত গণতান্ত্রিক অবয়বের মধ্যে নানা সময়ে স্বৈরাচার ভর করেছিল। এমন কোনো রাজনৈতিক সংগঠন দেখানো যাবে না, যাদের মধ্যে ক্ষমতার রেষারেষি নেই, অন্যকে গলা টিপে হত্যা করার প্রবণতা নেই। ক্ষমতায় থাকুক আর না থাকুক, ক্ষমতা দেখানোর সুযোগ থাকলেই প্রয়োগ করা যে কত সহজ, সেই উদাহরণ দিতে খুব বেশি দূর যেতে হবে না।
৪.
আজই হোয়াটসঅ্যাপে এক মিনিট এক সেকেন্ডের একটি ভিডিও দেখে মন ভালো হয়ে গেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয়ের ৮০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ভিডিওটি। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের যেসব গুরুত্বপূর্ণ ভাস্কর্য রয়েছে, সেই ভাস্কর্যের চরিত্রগুলো নেমে এসে মানুষের কাতারে দাঁড়াচ্ছে, মানুষের সঙ্গে ভাব বিনিময় করছে—এই হচ্ছে মূল থিম। এখন সোভিয়েত ইউনিয়ন নেই, সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখে না রাশিয়া, কিন্তু সম্মিলিত সেই বিজয়কে তারা হৃদয়ে ধারণ করে। এই বিজয়ে পুরো জাতি গর্বিত।
আমাদের দুর্ভাগ্য হলো, বিজয় অর্জনের পরপরই বিজয়ের পরাজয় ঘটে গেছে। আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, পরমতসহিষ্ণুতা, মানবতা ইত্যাদি থেকে আমরা ধীরে ধীরে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিয়েছি। পশুশক্তিকেই ভেবেছি আদ্যাশক্তি। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্রকেই সবচেয়ে কলুষিত করেছি। মুক্তিযুদ্ধে যারা পরাজিত হয়েছিল, তারা একবারের জন্য ভাবেনি যে জাতির কাছে তাদের ক্ষমা চাইতে হবে। অথচ তাদের একসময় রাজনীতি করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। সেই বোঝা বইতে বইতে জাতি এখন আর তা নিয়ে মোটেই বিচলিত নয়। ভুলে গেছে সেসব।
জনগণের বিজয়কে কুক্ষিগত করা কারও জন্যই শোভন নয়। অথচ আমাদের জাতি বারবার সেটাও দেখেছে। শতচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বিজয়ীদের ঐক্য। এবং যেকোনো জায়গায় নিজেদের ক্ষমতার প্রকাশ দেখাতে গিয়ে নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের বিশালতাকেও খেলো করে ফেলা হয়েছে। ফলে যদি কেউ মনে করে যে তরুণেরা সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে, তারা যা ভাববে সেটাই ঠিক পথ, তাহলে সেই ভাবনার মধ্যে কতটা সত্য থাকবে, সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে। কারণ, অজস্র আবর্জনার মধ্য থেকে সত্য তুলে ধরার জন্য যে প্রয়াস প্রয়োজন, তা নিজের মেধা ও পরিশ্রম দিয়ে অর্জন করার পথে কজন হাঁটবে? যদি নেতৃত্বের মধ্যেই গলদ থাকে, তাহলে এগিয়ে যাওয়া খুব কঠিন।
এখন অনেকেই প্রশ্ন করতে পারে, যে সংস্কারের কথা বলা হলো, তা আসলে করবে কে? প্রশ্ন করতে পারে, মেধা ও অভিজ্ঞতার মধ্যে মিলন না ঘটলে যে অরাজকতা সৃষ্টি হবে, তার দায়ভার কে নেবে? প্রশ্ন করতে পারে, ১৯৭১ সালকে মূল্য দেওয়ার ধরন দেখেই দুষ্কৃতকারীদের মতলব বোঝা যায় এবং বোঝা যায় মূলত দেশপ্রেমী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটছে কি না। এই প্রশ্নগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গায়ের জোরে যা করা যায়, ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে আঁতাত করে যা করা যায়, ইতিহাসের বিচারের জন্য একসময় তা কাঠগড়ায় দাঁড়াবেই।
কিন্তু সেই বিচারের জন্য ভাবনা ও চিন্তাশীলতার যে গভীরতা প্রয়োজন, সেটা না থাকলে কী হবে, তা কেউ বিবেচনা করে দেখছে না এখনো। মূল ভয়ের কারণ সেটাই।

প্রায়ই ‘সংস্কৃতি’ শব্দ একটি সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। মনে করা হয় যে শিল্প-সাহিত্য-সংগীতই সংস্কৃতির সমার্থক। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সংস্কৃতি ধারণাটি পুরো জীবনধারা ও জীবনবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত, চিন্তা-চেতনা এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত। সংস্কৃতির মতো ‘গণতন্ত্র’ ধারণাকেও সীমাবদ্ধ একটি প্রেক্ষাপট থেকে দেখতে আমর
৮ ঘণ্টা আগে
ক্ষমতায় গেলে নারীদের কর্মঘণ্টা আট ঘণ্টা থেকে কমিয়ে পাঁচ ঘণ্টা করা হবে—সম্প্রতি এমন এক ঘোষণা এসেছে। কথাটা প্রথমে শুনলে অনেকের কাছে হয়তো ভালোই লাগবে। কিন্তু একটু গভীরে তাকালে বোঝা যায়, এই কথার আড়ালে লুকিয়ে আছে বিপজ্জনক এক চিন্তা—নারীকে আবার ঘরে ফেরানোর, তাঁকে কর্মক্ষেত্র থেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে দেওয়ার এক
৮ ঘণ্টা আগে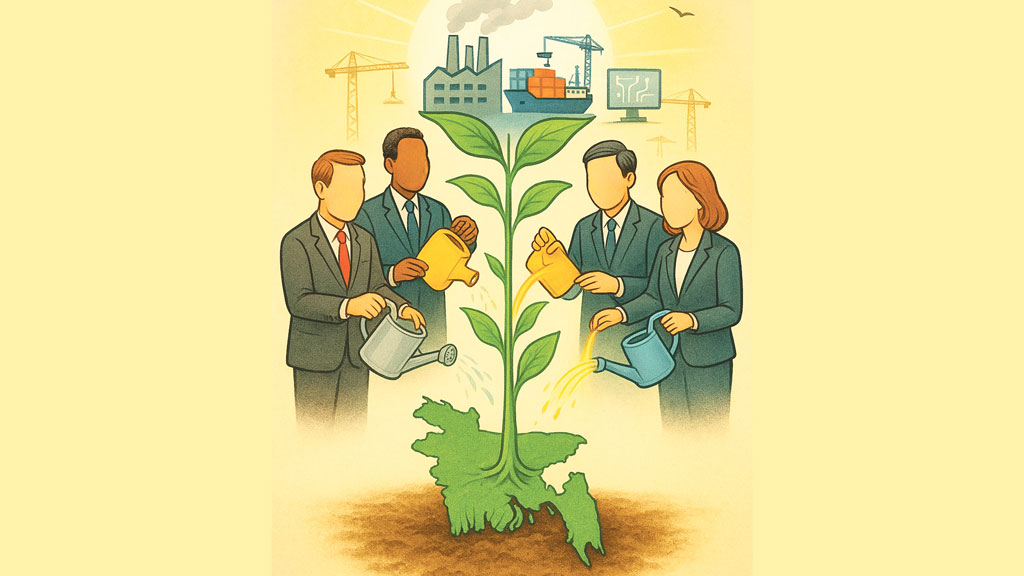
একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি হলো বিদেশি বিনিয়োগ। এই বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে যেকোনো দেশ রপ্তানির পরিমাণ বাড়িয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।
৮ ঘণ্টা আগে
‘ইট মারলে পাটকেলটি খেতে হয়’ প্রবাদটির যথাযথ উদাহরণ দিয়েছেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং সিটি ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা। তাঁরা অবশ্য এক হয়ে কাউকে পাটকেল মারেননি, বরং একে অপরকে দোষারোপ করে পাটকেল ছুড়েছেন।
৮ ঘণ্টা আগেবৃহত্তর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ তখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, যদি অন্য জাতি, সম্প্রদায়, ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল হই, মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তা নিয়ে তাদের গ্রহণ এবং কোনো রকমের মানসিক কূপমণ্ডূকতার শিকার না হই।
সেলিম জাহান

প্রায়ই ‘সংস্কৃতি’ শব্দ একটি সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। মনে করা হয় যে শিল্প-সাহিত্য-সংগীতই সংস্কৃতির সমার্থক। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সংস্কৃতি ধারণাটি পুরো জীবনধারা ও জীবনবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত, চিন্তা-চেতনা এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত। সংস্কৃতির মতো ‘গণতন্ত্র’ ধারণাকেও সীমাবদ্ধ একটি প্রেক্ষাপট থেকে দেখতে আমরা অভ্যস্ত। মনে করা হয়, এ ধারণা রাষ্ট্রবিজ্ঞান-সম্পৃক্ত। একটি দেশে বহু দলবিশিষ্ট সাধারণ নির্বাচনসহ একটি বেসামরিক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলেই তাকে অনেক সময় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে অভিহিত করা হয়।
একাধিক রাজনৈতিক দল, বেসামরিক সরকার, মুক্ত নির্বাচন, একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আবশ্যকীয় শর্ত নিঃসন্দেহে, কিন্তু পর্যাপ্ত শর্ত নয়। একই রকমভাবে সর্বজনীন মানবাধিকারও গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত, কিন্তু পর্যাপ্ত শর্ত নয়। আসলে গণতন্ত্র শুধু সর্বজনীন মানবাধিকার, রাষ্ট্রব্যবস্থা কিংবা রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এর প্রকৃত সংজ্ঞা আরও ব্যাপক।
গণতন্ত্রের এ-জাতীয় বৃহত্তর একটি সংজ্ঞা গ্রহণ করলে কয়েকটি বিষয় খুব স্পষ্ট হয়ে পড়ে। প্রথমত, গণতন্ত্র বিষয়টি শুধু সীমাবদ্ধ কিছু রাষ্ট্রবিজ্ঞানসম্মত কাঠামো কিংবা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ নয়, এটি একটি মূল্যবোধ বা সংস্কৃতির অঙ্গ। দ্বিতীয়ত, পুরো বিষয়টি স্থবির কোনো চেতনা নয়, বরং একটি গতিময় প্রক্রিয়া। তৃতীয়ত, গণতন্ত্রের অভীষ্ট লক্ষ্য পুরোপুরিভাবে কখনোই অর্জনীয় নয়; বরং সে লক্ষ্যের নিকটতর হওয়াটাই গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথযাত্রা। চতুর্থত, গণতন্ত্রে সন্তুষ্টির অবকাশ নেই, আছে সংগ্রামের দীর্ঘ পথ। পঞ্চমত, শুধু রাজনৈতিক গণতন্ত্রই নয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক গণতন্ত্র, সাংস্কৃতিক গণতন্ত্রের লড়াইও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের অংশ।
যখন গণতন্ত্রকে বৃহত্তর আঙ্গিকের গতিময় একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা হয়, তখনই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে গণতন্ত্রের একটি সংস্কৃতি আছে, যা তাৎক্ষণিকভাবে রাষ্ট্রীয় কিছু নীতিমালা বা ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্জন করা যায় না। গণতন্ত্র একটি মূল্যবোধের বিষয়, যার নিরন্তর চর্চা প্রয়োজন, শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নয়, ব্যক্তি এবং সমাজজীবনেও। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অবিরাম চর্চার মাধ্যমেই একটি জাতির গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের পটভূমি গড়ে ওঠে এবং বজায়যোগ্য রূপ গ্রহণ করে।
গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রথম পাদপীঠই হচ্ছে ব্যক্তি-মানুষ। একজন ব্যক্তি হিসেবে আমি কি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, নাকি আমার মাঝে একজন স্বৈরাচারী প্রভু বিরাজ করছে? আমি নিজের কথা বলতে যতটা উৎসাহী, অন্যের কথা শুনতে কি ততটা আগ্রহী? পরিবারের মধ্যে আমার মতামত অন্য সদস্যদের ওপরে চাপিয়ে দিতে চাই? আমার কথাই কি শেষ কথা বলে মনে করি? প্রত্যেক ব্যক্তি-মানুষের চিন্তাধারা এবং কর্মকাণ্ডের একটি বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন প্রয়োজন, যাতে বোঝা যায়, সেই ব্যক্তিমানুষ কি গণতান্ত্রিক নাকি স্বেচ্ছাচারী। ব্যক্তি হিসেবে যদি স্বৈরাচারী চিন্তাচেতনার অধিকারী হই, তাহলে কেমন করে আমি প্রত্যাশা করি, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সুসংরক্ষিত থাকবে? রাষ্ট্র তো ব্যক্তিনিরপেক্ষ কোনো নিরঙ্কুশ অস্তিত্ব নয়।
কর্মক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে বুঝতে হবে, কর্মপ্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন, চিন্তাধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ কতটা বিরাজ করে। প্রায়ই চোখে পড়ে, কর্মক্ষেত্রে অধস্তনদের আমরা দাস ভাবতেই অভ্যস্ত, আবার আমাদের ঊর্ধ্বতনদের প্রায়ই ভাবি দেবতা হিসেবে। এ দুটি দৃষ্টিভঙ্গিই অগণতান্ত্রিক। কর্মক্ষেত্রে কেউ যে কাজই করুক না কেন, মানুষ হিসেবে প্রত্যেকেই সমান এবং সম্মান পাওয়ার যোগ্য। বহুক্ষেত্রে চোখে পড়ে যে কর্মক্ষেত্রের বাইরে যখন সহকর্মীদের সঙ্গে সামাজিকভাবে মেলামেশা হয়, তখনো কর্মক্ষেত্রের আমলাতান্ত্রিক বিভাজনটি বজায় থাকে। অগণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চরম পরাকাষ্ঠা।
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের ক্ষেত্রেও অগণতান্ত্রিক বিবেচনা এবং প্রক্রিয়া প্রবলভাবে কাজ করে। সংগঠন করার মানেই সভাপতির পদটি দখল করা নয়, কিংবা আমার স্বজনদের জন্য সুবিধা আদায় নয়। অন্যের যোগ্যতার মর্যাদা দেওয়াও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অংশ। সামাজিক বিভিন্ন অঙ্গনে ও সংগঠনে সবার অধিকার মান্য করা, অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা এবং নিজের অহংবোধকে অগ্রাধিকার না দিয়ে যৌথভাবে কাজ করার মানসিকতা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পূর্বশর্ত।
রাজনীতির ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের আধার হওয়া উচিত রাজনৈতিক সংগঠনের। অথচ গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অনুপস্থিতি সবচেয়ে প্রকট রাজনৈতিক দলগুলোতেই। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, পরমতসহিষ্ণুতার অভাব বড় বেশি। বিপক্ষ দলগুলোর মতপ্রকাশের অধিকার, তাদের কণ্ঠস্বরের স্বাধীনতা অস্বীকার করে ক্ষমতাসীন দল। একটি দলের মধ্যেও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও কর্মকাণ্ডের বড় অভাব। সব গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে বিনষ্ট করে সেখানে দলনেতাকেই চূড়ান্ত ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোতে নীতি নয়, ব্যক্তিপূজাই বেশির ভাগ কাজ নিয়ন্ত্রণ করছে। বহু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, গণতান্ত্রিক একটি প্রক্রিয়া মেনে চলার পরিবর্তে বিভিন্ন সাংগঠনিক সিদ্ধান্তে চূড়ান্ত ক্ষমতা দলপ্রধানের অগণতান্ত্রিক হওয়ার সুযোগ অত্যন্ত বেশি।
রাজনীতির ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চরম অবমূল্যায়ন তখনই ঘটেছে, যখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তরুণসমাজের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছে, ছাত্রসংগঠনগুলোর স্বাধীন সত্তার বিলুপ্তি ঘটিয়ে তাদের রাজনৈতিক দলগুলোর লেজুড়ে পরিণত করা হলো। তরুণসমাজের চরিত্র হননে প্রয়াসী হয়ে হত্যা করা হয়েছে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির ভবিষ্যৎকেও।
অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে অর্থনৈতিক সুযোগের ক্ষেত্রে সবার সমান অধিকার, সম্পদে সমান সুযোগ এবং অর্থনৈতিক সমতার নিশ্চিতকরণ। এসবের মাধ্যমেই সামাজিক ন্যায্যতা অর্জন করা সম্ভব। এই পুরো প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের একটি ভূমিকা আছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চরম এক বিপর্যয় ঘটে, যখন সব অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা ভেঙে ফেলা হয় এবং অর্থনৈতিক জবাবদিহি ও দায়বদ্ধতাকে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়।
বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ তখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, যদি অন্য জাতি, সম্প্রদায়, ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল হই, মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তা নিয়ে তাদের গ্রহণ এবং কোনো রকমের মানসিক কূপমণ্ডূকতার শিকার না হই। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর স্বকীয়তা এবং স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি এবার সবার প্রতি সৌহার্দ্য সাংস্কৃতিক গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। আমরা সবাই সমান, কিন্তু সবাই এক নই।
গণতন্ত্রের পথযাত্রা খুব মসৃণ নয়। এর জন্য চাই গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পরিবেশ এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের নিরন্তর চর্চা—ব্যক্তিজীবনে, সমাজজীবনে এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির জন্য পর্যাপ্ত প্রেক্ষাপট তৈরি করতে পারে গণতন্ত্রের জন্য নিরন্তর সংগ্রাম।
লেখক: অর্থনীতিবিদ

প্রায়ই ‘সংস্কৃতি’ শব্দ একটি সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। মনে করা হয় যে শিল্প-সাহিত্য-সংগীতই সংস্কৃতির সমার্থক। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সংস্কৃতি ধারণাটি পুরো জীবনধারা ও জীবনবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত, চিন্তা-চেতনা এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত। সংস্কৃতির মতো ‘গণতন্ত্র’ ধারণাকেও সীমাবদ্ধ একটি প্রেক্ষাপট থেকে দেখতে আমরা অভ্যস্ত। মনে করা হয়, এ ধারণা রাষ্ট্রবিজ্ঞান-সম্পৃক্ত। একটি দেশে বহু দলবিশিষ্ট সাধারণ নির্বাচনসহ একটি বেসামরিক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলেই তাকে অনেক সময় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে অভিহিত করা হয়।
একাধিক রাজনৈতিক দল, বেসামরিক সরকার, মুক্ত নির্বাচন, একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আবশ্যকীয় শর্ত নিঃসন্দেহে, কিন্তু পর্যাপ্ত শর্ত নয়। একই রকমভাবে সর্বজনীন মানবাধিকারও গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত, কিন্তু পর্যাপ্ত শর্ত নয়। আসলে গণতন্ত্র শুধু সর্বজনীন মানবাধিকার, রাষ্ট্রব্যবস্থা কিংবা রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এর প্রকৃত সংজ্ঞা আরও ব্যাপক।
গণতন্ত্রের এ-জাতীয় বৃহত্তর একটি সংজ্ঞা গ্রহণ করলে কয়েকটি বিষয় খুব স্পষ্ট হয়ে পড়ে। প্রথমত, গণতন্ত্র বিষয়টি শুধু সীমাবদ্ধ কিছু রাষ্ট্রবিজ্ঞানসম্মত কাঠামো কিংবা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ নয়, এটি একটি মূল্যবোধ বা সংস্কৃতির অঙ্গ। দ্বিতীয়ত, পুরো বিষয়টি স্থবির কোনো চেতনা নয়, বরং একটি গতিময় প্রক্রিয়া। তৃতীয়ত, গণতন্ত্রের অভীষ্ট লক্ষ্য পুরোপুরিভাবে কখনোই অর্জনীয় নয়; বরং সে লক্ষ্যের নিকটতর হওয়াটাই গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথযাত্রা। চতুর্থত, গণতন্ত্রে সন্তুষ্টির অবকাশ নেই, আছে সংগ্রামের দীর্ঘ পথ। পঞ্চমত, শুধু রাজনৈতিক গণতন্ত্রই নয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক গণতন্ত্র, সাংস্কৃতিক গণতন্ত্রের লড়াইও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের অংশ।
যখন গণতন্ত্রকে বৃহত্তর আঙ্গিকের গতিময় একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা হয়, তখনই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে গণতন্ত্রের একটি সংস্কৃতি আছে, যা তাৎক্ষণিকভাবে রাষ্ট্রীয় কিছু নীতিমালা বা ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্জন করা যায় না। গণতন্ত্র একটি মূল্যবোধের বিষয়, যার নিরন্তর চর্চা প্রয়োজন, শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নয়, ব্যক্তি এবং সমাজজীবনেও। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অবিরাম চর্চার মাধ্যমেই একটি জাতির গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের পটভূমি গড়ে ওঠে এবং বজায়যোগ্য রূপ গ্রহণ করে।
গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রথম পাদপীঠই হচ্ছে ব্যক্তি-মানুষ। একজন ব্যক্তি হিসেবে আমি কি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, নাকি আমার মাঝে একজন স্বৈরাচারী প্রভু বিরাজ করছে? আমি নিজের কথা বলতে যতটা উৎসাহী, অন্যের কথা শুনতে কি ততটা আগ্রহী? পরিবারের মধ্যে আমার মতামত অন্য সদস্যদের ওপরে চাপিয়ে দিতে চাই? আমার কথাই কি শেষ কথা বলে মনে করি? প্রত্যেক ব্যক্তি-মানুষের চিন্তাধারা এবং কর্মকাণ্ডের একটি বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন প্রয়োজন, যাতে বোঝা যায়, সেই ব্যক্তিমানুষ কি গণতান্ত্রিক নাকি স্বেচ্ছাচারী। ব্যক্তি হিসেবে যদি স্বৈরাচারী চিন্তাচেতনার অধিকারী হই, তাহলে কেমন করে আমি প্রত্যাশা করি, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সুসংরক্ষিত থাকবে? রাষ্ট্র তো ব্যক্তিনিরপেক্ষ কোনো নিরঙ্কুশ অস্তিত্ব নয়।
কর্মক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে বুঝতে হবে, কর্মপ্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন, চিন্তাধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ কতটা বিরাজ করে। প্রায়ই চোখে পড়ে, কর্মক্ষেত্রে অধস্তনদের আমরা দাস ভাবতেই অভ্যস্ত, আবার আমাদের ঊর্ধ্বতনদের প্রায়ই ভাবি দেবতা হিসেবে। এ দুটি দৃষ্টিভঙ্গিই অগণতান্ত্রিক। কর্মক্ষেত্রে কেউ যে কাজই করুক না কেন, মানুষ হিসেবে প্রত্যেকেই সমান এবং সম্মান পাওয়ার যোগ্য। বহুক্ষেত্রে চোখে পড়ে যে কর্মক্ষেত্রের বাইরে যখন সহকর্মীদের সঙ্গে সামাজিকভাবে মেলামেশা হয়, তখনো কর্মক্ষেত্রের আমলাতান্ত্রিক বিভাজনটি বজায় থাকে। অগণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চরম পরাকাষ্ঠা।
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের ক্ষেত্রেও অগণতান্ত্রিক বিবেচনা এবং প্রক্রিয়া প্রবলভাবে কাজ করে। সংগঠন করার মানেই সভাপতির পদটি দখল করা নয়, কিংবা আমার স্বজনদের জন্য সুবিধা আদায় নয়। অন্যের যোগ্যতার মর্যাদা দেওয়াও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অংশ। সামাজিক বিভিন্ন অঙ্গনে ও সংগঠনে সবার অধিকার মান্য করা, অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা এবং নিজের অহংবোধকে অগ্রাধিকার না দিয়ে যৌথভাবে কাজ করার মানসিকতা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পূর্বশর্ত।
রাজনীতির ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের আধার হওয়া উচিত রাজনৈতিক সংগঠনের। অথচ গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অনুপস্থিতি সবচেয়ে প্রকট রাজনৈতিক দলগুলোতেই। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, পরমতসহিষ্ণুতার অভাব বড় বেশি। বিপক্ষ দলগুলোর মতপ্রকাশের অধিকার, তাদের কণ্ঠস্বরের স্বাধীনতা অস্বীকার করে ক্ষমতাসীন দল। একটি দলের মধ্যেও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও কর্মকাণ্ডের বড় অভাব। সব গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে বিনষ্ট করে সেখানে দলনেতাকেই চূড়ান্ত ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোতে নীতি নয়, ব্যক্তিপূজাই বেশির ভাগ কাজ নিয়ন্ত্রণ করছে। বহু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, গণতান্ত্রিক একটি প্রক্রিয়া মেনে চলার পরিবর্তে বিভিন্ন সাংগঠনিক সিদ্ধান্তে চূড়ান্ত ক্ষমতা দলপ্রধানের অগণতান্ত্রিক হওয়ার সুযোগ অত্যন্ত বেশি।
রাজনীতির ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চরম অবমূল্যায়ন তখনই ঘটেছে, যখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তরুণসমাজের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছে, ছাত্রসংগঠনগুলোর স্বাধীন সত্তার বিলুপ্তি ঘটিয়ে তাদের রাজনৈতিক দলগুলোর লেজুড়ে পরিণত করা হলো। তরুণসমাজের চরিত্র হননে প্রয়াসী হয়ে হত্যা করা হয়েছে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির ভবিষ্যৎকেও।
অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে অর্থনৈতিক সুযোগের ক্ষেত্রে সবার সমান অধিকার, সম্পদে সমান সুযোগ এবং অর্থনৈতিক সমতার নিশ্চিতকরণ। এসবের মাধ্যমেই সামাজিক ন্যায্যতা অর্জন করা সম্ভব। এই পুরো প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের একটি ভূমিকা আছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চরম এক বিপর্যয় ঘটে, যখন সব অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা ভেঙে ফেলা হয় এবং অর্থনৈতিক জবাবদিহি ও দায়বদ্ধতাকে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়।
বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ তখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, যদি অন্য জাতি, সম্প্রদায়, ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল হই, মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তা নিয়ে তাদের গ্রহণ এবং কোনো রকমের মানসিক কূপমণ্ডূকতার শিকার না হই। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর স্বকীয়তা এবং স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি এবার সবার প্রতি সৌহার্দ্য সাংস্কৃতিক গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। আমরা সবাই সমান, কিন্তু সবাই এক নই।
গণতন্ত্রের পথযাত্রা খুব মসৃণ নয়। এর জন্য চাই গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পরিবেশ এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের নিরন্তর চর্চা—ব্যক্তিজীবনে, সমাজজীবনে এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির জন্য পর্যাপ্ত প্রেক্ষাপট তৈরি করতে পারে গণতন্ত্রের জন্য নিরন্তর সংগ্রাম।
লেখক: অর্থনীতিবিদ

ঘটনাবলি এত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে যে কোন ঘটনার সঙ্গে কোন ঘটনাকে মিলিয়ে একটা যুক্তিসংগত সিদ্ধান্তে আসা যাবে, তা একেবারেই বোঝা যাচ্ছে না। কে কার পক্ষ নিচ্ছে এবং কে কোন পক্ষ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিচ্ছে, সেটাও প্রশ্নসাপেক্ষ। এ রকম একটি অবস্থায় মূল ঘটনাগুলো থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে বিষয়গুলো সম্পর্কে
১২ মে ২০২৫
ক্ষমতায় গেলে নারীদের কর্মঘণ্টা আট ঘণ্টা থেকে কমিয়ে পাঁচ ঘণ্টা করা হবে—সম্প্রতি এমন এক ঘোষণা এসেছে। কথাটা প্রথমে শুনলে অনেকের কাছে হয়তো ভালোই লাগবে। কিন্তু একটু গভীরে তাকালে বোঝা যায়, এই কথার আড়ালে লুকিয়ে আছে বিপজ্জনক এক চিন্তা—নারীকে আবার ঘরে ফেরানোর, তাঁকে কর্মক্ষেত্র থেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে দেওয়ার এক
৮ ঘণ্টা আগে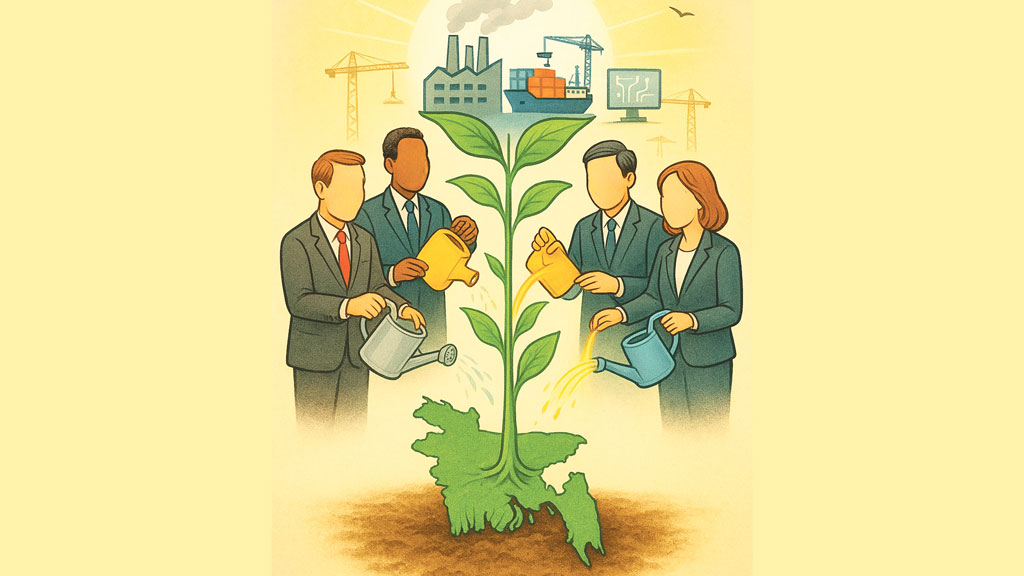
একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি হলো বিদেশি বিনিয়োগ। এই বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে যেকোনো দেশ রপ্তানির পরিমাণ বাড়িয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।
৮ ঘণ্টা আগে
‘ইট মারলে পাটকেলটি খেতে হয়’ প্রবাদটির যথাযথ উদাহরণ দিয়েছেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং সিটি ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা। তাঁরা অবশ্য এক হয়ে কাউকে পাটকেল মারেননি, বরং একে অপরকে দোষারোপ করে পাটকেল ছুড়েছেন।
৮ ঘণ্টা আগেনুসরাত রুষা

ক্ষমতায় গেলে নারীদের কর্মঘণ্টা আট ঘণ্টা থেকে কমিয়ে পাঁচ ঘণ্টা করা হবে—সম্প্রতি এমন এক ঘোষণা এসেছে। কথাটা প্রথমে শুনলে অনেকের কাছে হয়তো ভালোই লাগবে। কিন্তু একটু গভীরে তাকালে বোঝা যায়, এই কথার আড়ালে লুকিয়ে আছে বিপজ্জনক এক চিন্তা—নারীকে আবার ঘরে ফেরানোর, তাঁকে কর্মক্ষেত্র থেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে দেওয়ার এক নরম কৌশল।
প্রথমেই প্রশ্ন আসে, পাঁচ ঘণ্টা কাজ করলে কি নারী আট ঘণ্টার সমান বেতন পাবেন? যদি উত্তর হয় হ্যাঁ, তাহলে শ্রমবাজারের বাস্তব চিত্র কী দাঁড়াবে? বেসরকারি খাতে মালিকেরা কি সমান বেতনে অর্ধেক সময় কাজ করা কর্মীকে রাখতে চাইবেন? তাঁরা সহজেই বলবেন, ‘একই বেতনে পুরুষ আট ঘণ্টা কাজ দিচ্ছেন, তাহলে নারীকে কেন নেব?’ ফলাফল খুব সহজ—নারীদের জন্য চাকরির সুযোগ আরও কমে যাবে, কর্মজীবী নারীর সংখ্যা কমবে, অনেক ক্ষেত্রে নারীকে অদক্ষ কিংবা ‘অর্ধেক সময়ের কর্মী’ হিসেবে দেখবে প্রতিষ্ঠানগুলো। আর যদি বলা হয়, পাঁচ ঘণ্টা কাজের জন্য বেতনও কমবে, তাহলে তো নারী আর্থিকভাবে আরও সমস্যায় পড়ে যাবে। এই পরিস্থিতিতে নারীকে ঘরে ফেরানো, তাঁর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সংকুচিত করা, তাঁর পেশাগত অবস্থান দুর্বল করা—সবই অনিবার্য হয়ে উঠবে।
নারী অফিসে বা কারখানায় কাজ করার পর বাসার পুরো কাজও তাঁকে করতে হয়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সংসার, সন্তান, বৃদ্ধ বাবা-মা, স্বামীর যত্ন—সবকিছুই তাঁর সময়, পরিশ্রম ও মানসিক শক্তি দিয়ে টিকে থাকে। সেই নারীর জন্য যদি কর্মঘণ্টা কমানোর নামে তাঁর আয় কমিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তিনি আরও বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়বেন পরিবারের ওপর। দিনে পাঁচ ঘণ্টা বাইরে কাজ, বাকি সময় ঘরে বিনা পয়সায় খাটুনি—এটাই কি তবে সেই ‘নারীবান্ধব’ নীতি? নারীকে যেন ঘরে আরও তিন ঘণ্টা বেশি কাজ করানো যায়, অথচ তাঁর শ্রমের আর্থিক মূল্য না দিতে হয়—এই নীতি মূলত তেমন এক কৌশল।
নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন কখনোই কাজের সময় কমিয়ে আনা নয়; তাঁর কাজের পরিবেশকে নিরাপদ ও সহায়ক করা উচিত। কর্মক্ষেত্রে শিশুসন্তানসহ নারীরা যেন নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারেন, সে জন্য চাইল্ড কেয়ার বা ডে-কেয়ার সেন্টার থাকা জরুরি। নারীরা যেন অফিসে বা কারখানায় যাতায়াতের সময় হয়রানির শিকার না হন, তা নিশ্চিত করতে হবে নিরাপদ পরিবহনব্যবস্থার মাধ্যমে। মাতৃত্বকালীন ছুটি, বেতনসহ ছুটি, স্বাস্থ্যবিমা—এসব ন্যূনতম অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হওয়া দরকার। আর কর্মক্ষেত্রে নারী যেন শুধু উপস্থিত থাকেন না, সিদ্ধান্ত গ্রহণেও অংশ নেন—এই লক্ষ্যেই নেতৃত্বের জায়গায় নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে।
কিন্তু যেসব দল নারীর স্বাধীনতা ও কর্মজীবনকে বরাবরই সন্দেহের চোখে দেখে, তারা কখনোই এই বাস্তব সমাধানগুলোতে আগ্রহ দেখায় না। তারা নারীকে ঘরে রাখতেই চায়—অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল, সামাজিকভাবে নীরব এবং রাজনৈতিকভাবে অদৃশ্য এক অবস্থায়। তাদের চোখে নারী যেন এক ‘রক্ষা’ করার বস্তু, যার স্বাধীনতা নয়, শাসন দরকার। তাই তারা মাঝে মাঝে এমন ‘সহানুভূতির’ ভাষা ব্যবহার করে, যা আসলে শাসনের অন্য রূপ। কর্মঘণ্টা কমানো তারই উদাহরণ। এর মাধ্যমে বলা হচ্ছে, নারী দুর্বল, নারী দীর্ঘ সময় কাজ করতে পারেন
না, তাঁকে ‘ছাড়’ দিতে হবে। অথচ সত্য হলো—নারী পুরুষের মতোই পরিশ্রমী, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দ্বিগুণ দায়িত্ব পালন করেন।
এই ধরনের নীতির পেছনে রাজনৈতিক অভিপ্রায়ও স্পষ্ট। নারী যদি কর্মজীবন থেকে সরে আসেন, তাহলে তাঁর আর্থিক স্বাধীনতা হারায়। অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল মানুষ রাজনৈতিকভাবে নীরব হয়ে পড়ে। যাঁরা সমাজে প্রশ্ন তোলেন, অন্যায় দেখে প্রতিবাদ করেন, তাঁরা সাধারণত নিজের শ্রমের মূল্য জানেন, নিজের উপার্জনে আত্মমর্যাদা পান। তাই নারীর কণ্ঠ রুদ্ধ করতে হলে, আগে তাঁর আয়ের পথ রুদ্ধ করতে হয়। এই নীতিই সেটি—‘সহানুভূতি’র নামে তাঁকে সমাজ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পথ তৈরি করে।
বাংলাদেশে গত দুই দশকে কর্মজীবী নারীর সংখ্যা বেড়েছে, বিশেষত পোশাকশিল্প, ব্যাংক, মিডিয়া, প্রশাসন, এমনকি শিক্ষাক্ষেত্রেও নারীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছেন। এই পরিবর্তনই অনেকের চোখে আতঙ্কের কারণ। যারা মনে করে, নারীর জায়গা ঘর, তাঁর জীবন শুধু পরিবার ও সন্তান ঘিরে, তারা এই অগ্রগতি মেনে নিতে পারে না। তাই নারীকে ঘরে ফেরানোর নতুন নতুন যুক্তি খোঁজা হয়। কখনো ধর্মের নামে, কখনো সংস্কৃতির নামে, কখনো আবার ‘নারীর সুরক্ষা’র নামে। বাস্তবে কিন্তু লক্ষ্য একটাই—নারী যেন ঘরে থাকেন, তাঁর স্বাধীনতা যেন নিয়ন্ত্রণে থাকে।
নারী যদি কর্মক্ষেত্রে থাকেন, নিজের উপার্জন করেন, সিদ্ধান্ত নিতে শেখেন—তাহলে সমাজের ক্ষমতার ভারসাম্য বদলায়। সেটাই তাদের ভয়। তাই তারা এমন নীতি প্রস্তাব করে, যা নারীকে নরমভাবে প্রান্তে ঠেলে দেয়। কর্মঘণ্টা কমানো সেই প্রান্তিকীকরণের আরেক রূপ।
নারীর জন্য প্রকৃত নীতি হবে সেই নীতি, যা তাঁকে সমান সুযোগ দেয়, তাঁর কাজের মর্যাদা নিশ্চিত করে, তাঁর নিরাপত্তা এবং নেতৃত্বের পথ খুলে দেয়। নারীকে ‘দুর্বল’ হিসেবে নয়, ‘সমান নাগরিক’ হিসেবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিই একটি সভ্য সমাজের পরিচায়ক। আজ আমাদের দরকার সেই স্পষ্ট অবস্থান—নারীর নামে প্রতারণা নয়, প্রকৃত সমতা চাই।
লেখক: শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ক্ষমতায় গেলে নারীদের কর্মঘণ্টা আট ঘণ্টা থেকে কমিয়ে পাঁচ ঘণ্টা করা হবে—সম্প্রতি এমন এক ঘোষণা এসেছে। কথাটা প্রথমে শুনলে অনেকের কাছে হয়তো ভালোই লাগবে। কিন্তু একটু গভীরে তাকালে বোঝা যায়, এই কথার আড়ালে লুকিয়ে আছে বিপজ্জনক এক চিন্তা—নারীকে আবার ঘরে ফেরানোর, তাঁকে কর্মক্ষেত্র থেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে দেওয়ার এক নরম কৌশল।
প্রথমেই প্রশ্ন আসে, পাঁচ ঘণ্টা কাজ করলে কি নারী আট ঘণ্টার সমান বেতন পাবেন? যদি উত্তর হয় হ্যাঁ, তাহলে শ্রমবাজারের বাস্তব চিত্র কী দাঁড়াবে? বেসরকারি খাতে মালিকেরা কি সমান বেতনে অর্ধেক সময় কাজ করা কর্মীকে রাখতে চাইবেন? তাঁরা সহজেই বলবেন, ‘একই বেতনে পুরুষ আট ঘণ্টা কাজ দিচ্ছেন, তাহলে নারীকে কেন নেব?’ ফলাফল খুব সহজ—নারীদের জন্য চাকরির সুযোগ আরও কমে যাবে, কর্মজীবী নারীর সংখ্যা কমবে, অনেক ক্ষেত্রে নারীকে অদক্ষ কিংবা ‘অর্ধেক সময়ের কর্মী’ হিসেবে দেখবে প্রতিষ্ঠানগুলো। আর যদি বলা হয়, পাঁচ ঘণ্টা কাজের জন্য বেতনও কমবে, তাহলে তো নারী আর্থিকভাবে আরও সমস্যায় পড়ে যাবে। এই পরিস্থিতিতে নারীকে ঘরে ফেরানো, তাঁর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সংকুচিত করা, তাঁর পেশাগত অবস্থান দুর্বল করা—সবই অনিবার্য হয়ে উঠবে।
নারী অফিসে বা কারখানায় কাজ করার পর বাসার পুরো কাজও তাঁকে করতে হয়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সংসার, সন্তান, বৃদ্ধ বাবা-মা, স্বামীর যত্ন—সবকিছুই তাঁর সময়, পরিশ্রম ও মানসিক শক্তি দিয়ে টিকে থাকে। সেই নারীর জন্য যদি কর্মঘণ্টা কমানোর নামে তাঁর আয় কমিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তিনি আরও বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়বেন পরিবারের ওপর। দিনে পাঁচ ঘণ্টা বাইরে কাজ, বাকি সময় ঘরে বিনা পয়সায় খাটুনি—এটাই কি তবে সেই ‘নারীবান্ধব’ নীতি? নারীকে যেন ঘরে আরও তিন ঘণ্টা বেশি কাজ করানো যায়, অথচ তাঁর শ্রমের আর্থিক মূল্য না দিতে হয়—এই নীতি মূলত তেমন এক কৌশল।
নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন কখনোই কাজের সময় কমিয়ে আনা নয়; তাঁর কাজের পরিবেশকে নিরাপদ ও সহায়ক করা উচিত। কর্মক্ষেত্রে শিশুসন্তানসহ নারীরা যেন নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারেন, সে জন্য চাইল্ড কেয়ার বা ডে-কেয়ার সেন্টার থাকা জরুরি। নারীরা যেন অফিসে বা কারখানায় যাতায়াতের সময় হয়রানির শিকার না হন, তা নিশ্চিত করতে হবে নিরাপদ পরিবহনব্যবস্থার মাধ্যমে। মাতৃত্বকালীন ছুটি, বেতনসহ ছুটি, স্বাস্থ্যবিমা—এসব ন্যূনতম অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হওয়া দরকার। আর কর্মক্ষেত্রে নারী যেন শুধু উপস্থিত থাকেন না, সিদ্ধান্ত গ্রহণেও অংশ নেন—এই লক্ষ্যেই নেতৃত্বের জায়গায় নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে।
কিন্তু যেসব দল নারীর স্বাধীনতা ও কর্মজীবনকে বরাবরই সন্দেহের চোখে দেখে, তারা কখনোই এই বাস্তব সমাধানগুলোতে আগ্রহ দেখায় না। তারা নারীকে ঘরে রাখতেই চায়—অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল, সামাজিকভাবে নীরব এবং রাজনৈতিকভাবে অদৃশ্য এক অবস্থায়। তাদের চোখে নারী যেন এক ‘রক্ষা’ করার বস্তু, যার স্বাধীনতা নয়, শাসন দরকার। তাই তারা মাঝে মাঝে এমন ‘সহানুভূতির’ ভাষা ব্যবহার করে, যা আসলে শাসনের অন্য রূপ। কর্মঘণ্টা কমানো তারই উদাহরণ। এর মাধ্যমে বলা হচ্ছে, নারী দুর্বল, নারী দীর্ঘ সময় কাজ করতে পারেন
না, তাঁকে ‘ছাড়’ দিতে হবে। অথচ সত্য হলো—নারী পুরুষের মতোই পরিশ্রমী, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দ্বিগুণ দায়িত্ব পালন করেন।
এই ধরনের নীতির পেছনে রাজনৈতিক অভিপ্রায়ও স্পষ্ট। নারী যদি কর্মজীবন থেকে সরে আসেন, তাহলে তাঁর আর্থিক স্বাধীনতা হারায়। অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল মানুষ রাজনৈতিকভাবে নীরব হয়ে পড়ে। যাঁরা সমাজে প্রশ্ন তোলেন, অন্যায় দেখে প্রতিবাদ করেন, তাঁরা সাধারণত নিজের শ্রমের মূল্য জানেন, নিজের উপার্জনে আত্মমর্যাদা পান। তাই নারীর কণ্ঠ রুদ্ধ করতে হলে, আগে তাঁর আয়ের পথ রুদ্ধ করতে হয়। এই নীতিই সেটি—‘সহানুভূতি’র নামে তাঁকে সমাজ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পথ তৈরি করে।
বাংলাদেশে গত দুই দশকে কর্মজীবী নারীর সংখ্যা বেড়েছে, বিশেষত পোশাকশিল্প, ব্যাংক, মিডিয়া, প্রশাসন, এমনকি শিক্ষাক্ষেত্রেও নারীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছেন। এই পরিবর্তনই অনেকের চোখে আতঙ্কের কারণ। যারা মনে করে, নারীর জায়গা ঘর, তাঁর জীবন শুধু পরিবার ও সন্তান ঘিরে, তারা এই অগ্রগতি মেনে নিতে পারে না। তাই নারীকে ঘরে ফেরানোর নতুন নতুন যুক্তি খোঁজা হয়। কখনো ধর্মের নামে, কখনো সংস্কৃতির নামে, কখনো আবার ‘নারীর সুরক্ষা’র নামে। বাস্তবে কিন্তু লক্ষ্য একটাই—নারী যেন ঘরে থাকেন, তাঁর স্বাধীনতা যেন নিয়ন্ত্রণে থাকে।
নারী যদি কর্মক্ষেত্রে থাকেন, নিজের উপার্জন করেন, সিদ্ধান্ত নিতে শেখেন—তাহলে সমাজের ক্ষমতার ভারসাম্য বদলায়। সেটাই তাদের ভয়। তাই তারা এমন নীতি প্রস্তাব করে, যা নারীকে নরমভাবে প্রান্তে ঠেলে দেয়। কর্মঘণ্টা কমানো সেই প্রান্তিকীকরণের আরেক রূপ।
নারীর জন্য প্রকৃত নীতি হবে সেই নীতি, যা তাঁকে সমান সুযোগ দেয়, তাঁর কাজের মর্যাদা নিশ্চিত করে, তাঁর নিরাপত্তা এবং নেতৃত্বের পথ খুলে দেয়। নারীকে ‘দুর্বল’ হিসেবে নয়, ‘সমান নাগরিক’ হিসেবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিই একটি সভ্য সমাজের পরিচায়ক। আজ আমাদের দরকার সেই স্পষ্ট অবস্থান—নারীর নামে প্রতারণা নয়, প্রকৃত সমতা চাই।
লেখক: শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঘটনাবলি এত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে যে কোন ঘটনার সঙ্গে কোন ঘটনাকে মিলিয়ে একটা যুক্তিসংগত সিদ্ধান্তে আসা যাবে, তা একেবারেই বোঝা যাচ্ছে না। কে কার পক্ষ নিচ্ছে এবং কে কোন পক্ষ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিচ্ছে, সেটাও প্রশ্নসাপেক্ষ। এ রকম একটি অবস্থায় মূল ঘটনাগুলো থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে বিষয়গুলো সম্পর্কে
১২ মে ২০২৫
প্রায়ই ‘সংস্কৃতি’ শব্দ একটি সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। মনে করা হয় যে শিল্প-সাহিত্য-সংগীতই সংস্কৃতির সমার্থক। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সংস্কৃতি ধারণাটি পুরো জীবনধারা ও জীবনবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত, চিন্তা-চেতনা এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত। সংস্কৃতির মতো ‘গণতন্ত্র’ ধারণাকেও সীমাবদ্ধ একটি প্রেক্ষাপট থেকে দেখতে আমর
৮ ঘণ্টা আগে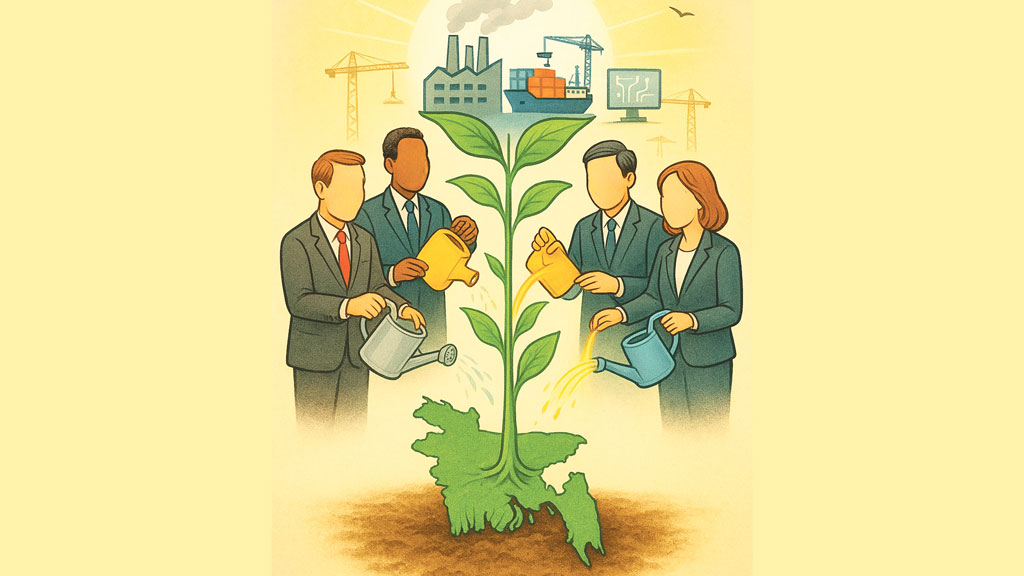
একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি হলো বিদেশি বিনিয়োগ। এই বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে যেকোনো দেশ রপ্তানির পরিমাণ বাড়িয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।
৮ ঘণ্টা আগে
‘ইট মারলে পাটকেলটি খেতে হয়’ প্রবাদটির যথাযথ উদাহরণ দিয়েছেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং সিটি ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা। তাঁরা অবশ্য এক হয়ে কাউকে পাটকেল মারেননি, বরং একে অপরকে দোষারোপ করে পাটকেল ছুড়েছেন।
৮ ঘণ্টা আগেরিয়াদ হোসেন
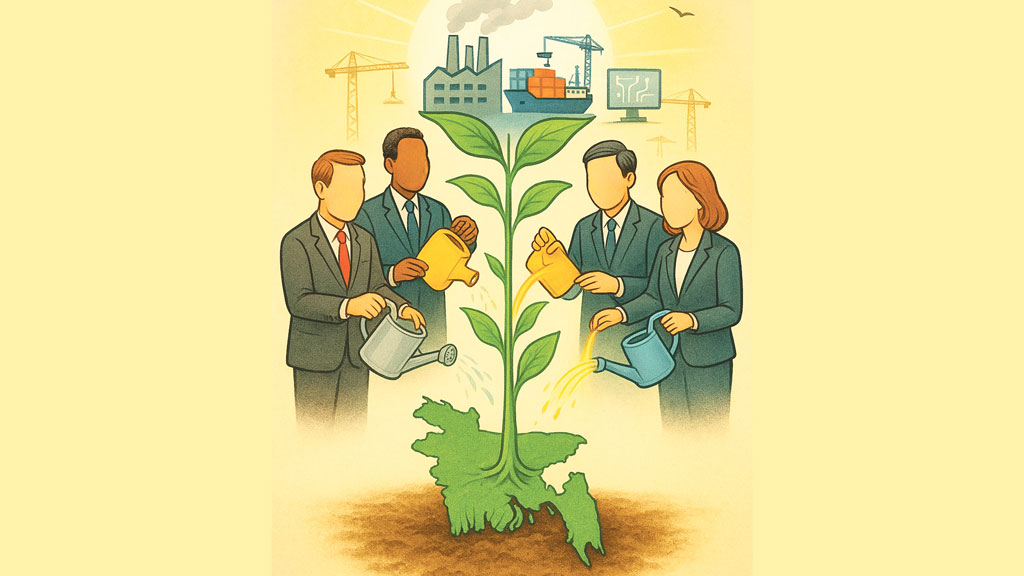
একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি হলো বিদেশি বিনিয়োগ। এই বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে যেকোনো দেশ রপ্তানির পরিমাণ বাড়িয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।
অন্য দেশের কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানি যখন আমাদের দেশে বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে, তখন দেশের অর্থনীতি আরও সচল হয়ে ওঠে। শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নতুন নতুন পণ্য উৎপাদিত হয়, মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। এতে অর্থনীতিতে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে শুরু করে।
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিভিন্ন খাতের অবকাঠামো উন্নয়নেও বিদেশি বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্বে আসার পর থেকে বিদেশি বিনিয়োগ নেই বললেই চলে। একই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বেকারত্বের সংখ্যা বেড়েছে। তবে আশার কথা, বিদেশি বিনিয়োগে আবারও সুদিন ফিরতে শুরু করেছে। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত মোট প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৬১ দশমিক ৫ শতাংশ বেড়েছে। এর পরিমাণ যেন ক্রমাগত বাড়তে থাকে, সেদিকে মনোযোগ দেওয়া জরুরি। তার জন্য দেশের নীতিনির্ধারণী মহলসহ সংশ্লিষ্টদের আরও মনোযোগী হওয়া দরকার। বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এখনো যেসব জায়গায় প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, সেগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। বিদেশি বিনিয়োগের পরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
সাধারণত বাইরে থেকে কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানি সব সময় লাভজনক ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে চায়। বিদেশিরা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সহজ উপায়,
নিশ্চিত এবং ঝুঁকিমুক্ত পরিবেশ চায়। কিন্তু যখন তারা দেখে, বিনিয়োগ করলে ব্যবসায় ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে কিংবা সেখানে ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য যথেষ্ট অনুকূল পরিবেশ নেই, তখন তারা বিনিয়োগে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তারা সেসব দেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করে।
বিদেশি কোম্পানিগুলোর কাছে যখন বিনিয়োগের একাধিক বিকল্প জায়গা থাকে; তখন তারা পছন্দমতো দেশ নির্বাচন করে সেখানে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। যেহেতু সব প্রতিকূলতা কাটিয়ে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আমাদের দেশে বিনিয়োগে উৎসাহিত হচ্ছে, তাদের এই আস্থার জায়গাটা আমাদের যেকোনো মূল্যে নিশ্চিত করতে হবে। কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে যাতে তারা নিরুৎসাহিত না হয়, সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে। আমরা দেখেছি, বিগত বছরগুলোতে
বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে যেসব খাতে, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো পোশাকশিল্প এবং রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল। যে খাতে উৎপাদন বাড়িয়ে রপ্তানি পণ্য বৃদ্ধির পাশাপাশি আমরা বেকার মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করতে পেরেছি।
এ জন্য এসব খাতে তারা যেন পরবর্তী সময়ে আরও বেশি বিনিয়োগ করে, সেই জায়গাগুলোতে আমাদের কাজ করতে হবে।
একটি সূত্র মতে, এ বছর অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট সামিটের মতো কিছু আয়োজনে পোশাক ও টেক্সটাইল খাতে নতুন কিছু বিনিয়োগের ঘোষণা এসেছে। ফলে আমাদের উৎপাদন বাড়ার পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও এগিয়ে যাব। আন্তর্জাতিকভাবে পোশাকশিল্পের বাজার আরও সমৃদ্ধ হবে। সর্বোপরি আমাদের পোশাকশিল্পের জন্য এমন ঘোষণা দেশের অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি অর্জনে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।
বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান মতে, ২০২২ সালে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৬৭০ দশমিক ৭ মিলিয়ন ডলার, যা পরবর্তী ২০২৩ সালে বেড়ে হয় ৯২৪ দশমিক ৪ মিলিয়ন ডলার। তবে ২০২৪ সালে এই বিনিয়োগের পরিমাণ কিছুটা কমে ৬৭৬ দশমিক ৬ মিলিয়ন ডলারে নেমে আসে। কিন্তু সবশেষ ২০২৫ সালের প্রথম ছয় মাসে আবার বিদেশি বিনিয়োগ বেড়ে গিয়ে ১ হাজার ৯২ দশমিক ৯ মিলিয়ন ডলারে এসে দাঁড়িয়েছে। তাহলে নির্দ্বিধায় বলা যায়, ধীরে ধীরে বিদেশি বিনিয়োগে আমাদের সুদিন ফিরতে শুরু করেছে।
এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সরকারি-বেসরকারি এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত সব প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। আমরা জানি, আমাদের দেশে দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিদেশি বিনিয়োগের অন্যতম অন্তরায়। তাই দুর্নীতি ঠেকাতে এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। বিনিয়োগকারীরা যাতে সহজে এবং দ্রুততম সময়ে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে, তার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। তাদের বিনিয়োগ করা কোনো প্রতিষ্ঠানে সমস্যা অথবা প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে তা দ্রুততার সঙ্গে সমাধান করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকতে হবে। সর্বোপরি আমরা আশা রাখি, আমাদের দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়াতে এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আরও উৎসাহিত করতে বিনিয়োগবান্ধব আইনি পরিবেশ তৈরিতে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর আরও বেশি সচেতনতা অবলম্বন করবে।
লেখক: শিক্ষার্থী, সরকারি বিএল কলেজ
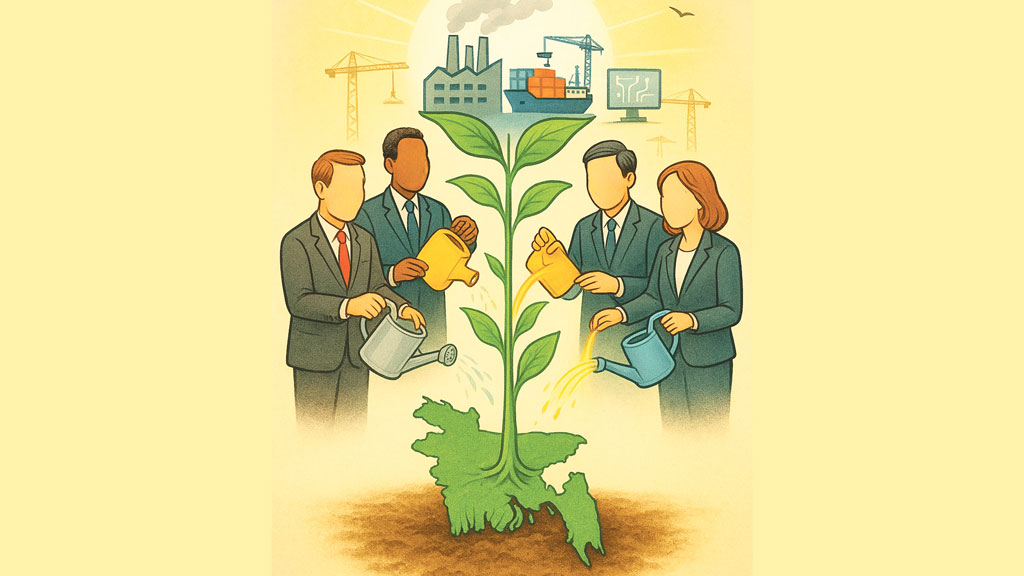
একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি হলো বিদেশি বিনিয়োগ। এই বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে যেকোনো দেশ রপ্তানির পরিমাণ বাড়িয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।
অন্য দেশের কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানি যখন আমাদের দেশে বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে, তখন দেশের অর্থনীতি আরও সচল হয়ে ওঠে। শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নতুন নতুন পণ্য উৎপাদিত হয়, মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। এতে অর্থনীতিতে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে শুরু করে।
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিভিন্ন খাতের অবকাঠামো উন্নয়নেও বিদেশি বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্বে আসার পর থেকে বিদেশি বিনিয়োগ নেই বললেই চলে। একই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বেকারত্বের সংখ্যা বেড়েছে। তবে আশার কথা, বিদেশি বিনিয়োগে আবারও সুদিন ফিরতে শুরু করেছে। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত মোট প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৬১ দশমিক ৫ শতাংশ বেড়েছে। এর পরিমাণ যেন ক্রমাগত বাড়তে থাকে, সেদিকে মনোযোগ দেওয়া জরুরি। তার জন্য দেশের নীতিনির্ধারণী মহলসহ সংশ্লিষ্টদের আরও মনোযোগী হওয়া দরকার। বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এখনো যেসব জায়গায় প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, সেগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। বিদেশি বিনিয়োগের পরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
সাধারণত বাইরে থেকে কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানি সব সময় লাভজনক ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে চায়। বিদেশিরা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সহজ উপায়,
নিশ্চিত এবং ঝুঁকিমুক্ত পরিবেশ চায়। কিন্তু যখন তারা দেখে, বিনিয়োগ করলে ব্যবসায় ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে কিংবা সেখানে ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য যথেষ্ট অনুকূল পরিবেশ নেই, তখন তারা বিনিয়োগে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তারা সেসব দেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করে।
বিদেশি কোম্পানিগুলোর কাছে যখন বিনিয়োগের একাধিক বিকল্প জায়গা থাকে; তখন তারা পছন্দমতো দেশ নির্বাচন করে সেখানে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। যেহেতু সব প্রতিকূলতা কাটিয়ে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আমাদের দেশে বিনিয়োগে উৎসাহিত হচ্ছে, তাদের এই আস্থার জায়গাটা আমাদের যেকোনো মূল্যে নিশ্চিত করতে হবে। কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে যাতে তারা নিরুৎসাহিত না হয়, সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে। আমরা দেখেছি, বিগত বছরগুলোতে
বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে যেসব খাতে, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো পোশাকশিল্প এবং রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল। যে খাতে উৎপাদন বাড়িয়ে রপ্তানি পণ্য বৃদ্ধির পাশাপাশি আমরা বেকার মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করতে পেরেছি।
এ জন্য এসব খাতে তারা যেন পরবর্তী সময়ে আরও বেশি বিনিয়োগ করে, সেই জায়গাগুলোতে আমাদের কাজ করতে হবে।
একটি সূত্র মতে, এ বছর অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট সামিটের মতো কিছু আয়োজনে পোশাক ও টেক্সটাইল খাতে নতুন কিছু বিনিয়োগের ঘোষণা এসেছে। ফলে আমাদের উৎপাদন বাড়ার পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও এগিয়ে যাব। আন্তর্জাতিকভাবে পোশাকশিল্পের বাজার আরও সমৃদ্ধ হবে। সর্বোপরি আমাদের পোশাকশিল্পের জন্য এমন ঘোষণা দেশের অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি অর্জনে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।
বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান মতে, ২০২২ সালে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৬৭০ দশমিক ৭ মিলিয়ন ডলার, যা পরবর্তী ২০২৩ সালে বেড়ে হয় ৯২৪ দশমিক ৪ মিলিয়ন ডলার। তবে ২০২৪ সালে এই বিনিয়োগের পরিমাণ কিছুটা কমে ৬৭৬ দশমিক ৬ মিলিয়ন ডলারে নেমে আসে। কিন্তু সবশেষ ২০২৫ সালের প্রথম ছয় মাসে আবার বিদেশি বিনিয়োগ বেড়ে গিয়ে ১ হাজার ৯২ দশমিক ৯ মিলিয়ন ডলারে এসে দাঁড়িয়েছে। তাহলে নির্দ্বিধায় বলা যায়, ধীরে ধীরে বিদেশি বিনিয়োগে আমাদের সুদিন ফিরতে শুরু করেছে।
এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সরকারি-বেসরকারি এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত সব প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। আমরা জানি, আমাদের দেশে দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিদেশি বিনিয়োগের অন্যতম অন্তরায়। তাই দুর্নীতি ঠেকাতে এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। বিনিয়োগকারীরা যাতে সহজে এবং দ্রুততম সময়ে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে, তার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। তাদের বিনিয়োগ করা কোনো প্রতিষ্ঠানে সমস্যা অথবা প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে তা দ্রুততার সঙ্গে সমাধান করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকতে হবে। সর্বোপরি আমরা আশা রাখি, আমাদের দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়াতে এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আরও উৎসাহিত করতে বিনিয়োগবান্ধব আইনি পরিবেশ তৈরিতে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর আরও বেশি সচেতনতা অবলম্বন করবে।
লেখক: শিক্ষার্থী, সরকারি বিএল কলেজ

ঘটনাবলি এত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে যে কোন ঘটনার সঙ্গে কোন ঘটনাকে মিলিয়ে একটা যুক্তিসংগত সিদ্ধান্তে আসা যাবে, তা একেবারেই বোঝা যাচ্ছে না। কে কার পক্ষ নিচ্ছে এবং কে কোন পক্ষ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিচ্ছে, সেটাও প্রশ্নসাপেক্ষ। এ রকম একটি অবস্থায় মূল ঘটনাগুলো থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে বিষয়গুলো সম্পর্কে
১২ মে ২০২৫
প্রায়ই ‘সংস্কৃতি’ শব্দ একটি সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। মনে করা হয় যে শিল্প-সাহিত্য-সংগীতই সংস্কৃতির সমার্থক। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সংস্কৃতি ধারণাটি পুরো জীবনধারা ও জীবনবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত, চিন্তা-চেতনা এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত। সংস্কৃতির মতো ‘গণতন্ত্র’ ধারণাকেও সীমাবদ্ধ একটি প্রেক্ষাপট থেকে দেখতে আমর
৮ ঘণ্টা আগে
ক্ষমতায় গেলে নারীদের কর্মঘণ্টা আট ঘণ্টা থেকে কমিয়ে পাঁচ ঘণ্টা করা হবে—সম্প্রতি এমন এক ঘোষণা এসেছে। কথাটা প্রথমে শুনলে অনেকের কাছে হয়তো ভালোই লাগবে। কিন্তু একটু গভীরে তাকালে বোঝা যায়, এই কথার আড়ালে লুকিয়ে আছে বিপজ্জনক এক চিন্তা—নারীকে আবার ঘরে ফেরানোর, তাঁকে কর্মক্ষেত্র থেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে দেওয়ার এক
৮ ঘণ্টা আগে
‘ইট মারলে পাটকেলটি খেতে হয়’ প্রবাদটির যথাযথ উদাহরণ দিয়েছেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং সিটি ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা। তাঁরা অবশ্য এক হয়ে কাউকে পাটকেল মারেননি, বরং একে অপরকে দোষারোপ করে পাটকেল ছুড়েছেন।
৮ ঘণ্টা আগেসম্পাদকীয়

‘ইট মারলে পাটকেলটি খেতে হয়’ প্রবাদটির যথাযথ উদাহরণ দিয়েছেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং সিটি ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা। তাঁরা অবশ্য এক হয়ে কাউকে পাটকেল মারেননি, বরং একে অপরকে দোষারোপ করে পাটকেল ছুড়েছেন। দুই দিন ধরে সংবাদমাধ্যমের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও এই দুই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আলোচনা চলছে। ২৮ অক্টোবর আজকের পত্রিকার প্রথম পাতার এ-সংক্রান্ত খবরটি পড়লেই বিস্তারিত জানা যায়।
এরই মধ্যে অসংখ্য পাঠক জেনে গেছেন, থুতুকাণ্ডের জের ধরে সাভারের বিরুলিয়ায় অবস্থিত দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হয় ২৬ অক্টোবর, রোববার দিবাগত রাতে। রোববার রাতে খাগান এলাকায় ড্যাফোডিলের শিক্ষার্থীদের ভাড়া বাসা ‘ব্যাচেলর প্যারাডাইস হোস্টেল’-এর পাশে
বসে ছিলেন সিটির শিক্ষার্থীরা। এমন সময় সিটির এক শিক্ষার্থী অসতর্কতাবশত থুতু ফেললে তা
পাশ দিয়ে যাওয়া ড্যাফোডিলের এক শিক্ষার্থীর গায়ে লাগে। সেখানে উভয় পক্ষের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। পরে সিটি ইউনিভার্সিটির প্রায় অর্ধশত শিক্ষার্থী দেশীয় অস্ত্র ও ইটপাটকেল নিয়ে ড্যাফোডিলের শিক্ষার্থীদের ওই বাসায় হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করেন।
এই হামলার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ড্যাফোডিলের শিক্ষার্থীরা ঘটনাস্থলে জড়ো হন এবং দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া চলে। ড্যাফোডিল কর্তৃপক্ষ সিটি ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে সমাধানের চেষ্টা করার সময় সিটি ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির এক শিক্ষার্থীকে মারধর করেন। ওই খবর ছড়িয়ে পড়লে ড্যাফোডিলের শিক্ষার্থীরা সিটি ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসের ভেতরে ঢুকে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেন। সিটির শিক্ষার্থীরা ড্যাফোডিলের কিছু শিক্ষার্থীকে জিম্মি ও মারধর করেন এবং পরে ছেড়ে দেন। পুরো ঘটনায় দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের দেড় শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হন।
থুতু ফেলার তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই প্রতিবেশী প্রতিষ্ঠানের তরুণ শিক্ষার্থীরা যে লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়ে ফেললেন, তা কোনোভাবেই কাম্য নয়। অসতর্কতাবশত যে শিক্ষার্থী থুতু ফেললেন, তিনি ‘দুঃখিত’ বললে এবং যাঁর গায়ে থুতু লেগেছে, তিনি তাঁকে ক্ষমা করে দিলে তখনই ল্যাঠা চুকে যেত। কিন্তু কী এক অস্থির জাতিতে পরিণত হয়েছি আমরা! ইটপাটকেলের প্রবাদটির উদাহরণ দিতে পারলেও, ‘ক্ষমা মহৎ গুণ’, এই আদর্শ বাক্যকে চর্চা করতে পারি না; শুধু আত্মস্থ করেই মনে করি দায়িত্ব শেষ।
ক্ষমা যেমন একটি গুণ, তেমনি সদ্ব্যবহার এবং ধৈর্যও। উচ্চশিক্ষার দুটি প্রতিষ্ঠানের কোনো কোনো শিক্ষার্থী যখন অসদাচরণ এবং অধৈর্যের পরিচয় দেন, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড করেন, তখন তা দুঃখজনক। যদি কেউ কারও ওপর অন্যায়ভাবে হামলা করে, তাহলে সেটি ফৌজদারি অপরাধ। ভুক্তভোগী আইনের আশ্রয় নিতে পারে, আইন নিজের হাতে তুলে নিতে পারে না।
দুই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা যখন সামান্য থুতুকাণ্ডকে লঙ্কাকাণ্ডে পরিণত করতে পারেন, তাহলে সেই থুতু এসে আসলে কার গায়ে পড়ে?
ওই শিক্ষার্থীদের পরিবার, যেখানে আদর্শ শিক্ষা দেওয়া হয়; তাঁদের শিক্ষক, যাঁরা সুশিক্ষা দানে ব্রতী, নাকি নিজেদের ওপর?
আচ্ছা, শৈশব থেকে ‘সদাচার’বিষয়ক পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ গড়ে দেওয়া যায় না?

‘ইট মারলে পাটকেলটি খেতে হয়’ প্রবাদটির যথাযথ উদাহরণ দিয়েছেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং সিটি ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা। তাঁরা অবশ্য এক হয়ে কাউকে পাটকেল মারেননি, বরং একে অপরকে দোষারোপ করে পাটকেল ছুড়েছেন। দুই দিন ধরে সংবাদমাধ্যমের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও এই দুই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আলোচনা চলছে। ২৮ অক্টোবর আজকের পত্রিকার প্রথম পাতার এ-সংক্রান্ত খবরটি পড়লেই বিস্তারিত জানা যায়।
এরই মধ্যে অসংখ্য পাঠক জেনে গেছেন, থুতুকাণ্ডের জের ধরে সাভারের বিরুলিয়ায় অবস্থিত দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হয় ২৬ অক্টোবর, রোববার দিবাগত রাতে। রোববার রাতে খাগান এলাকায় ড্যাফোডিলের শিক্ষার্থীদের ভাড়া বাসা ‘ব্যাচেলর প্যারাডাইস হোস্টেল’-এর পাশে
বসে ছিলেন সিটির শিক্ষার্থীরা। এমন সময় সিটির এক শিক্ষার্থী অসতর্কতাবশত থুতু ফেললে তা
পাশ দিয়ে যাওয়া ড্যাফোডিলের এক শিক্ষার্থীর গায়ে লাগে। সেখানে উভয় পক্ষের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। পরে সিটি ইউনিভার্সিটির প্রায় অর্ধশত শিক্ষার্থী দেশীয় অস্ত্র ও ইটপাটকেল নিয়ে ড্যাফোডিলের শিক্ষার্থীদের ওই বাসায় হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করেন।
এই হামলার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ড্যাফোডিলের শিক্ষার্থীরা ঘটনাস্থলে জড়ো হন এবং দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া চলে। ড্যাফোডিল কর্তৃপক্ষ সিটি ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে সমাধানের চেষ্টা করার সময় সিটি ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির এক শিক্ষার্থীকে মারধর করেন। ওই খবর ছড়িয়ে পড়লে ড্যাফোডিলের শিক্ষার্থীরা সিটি ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসের ভেতরে ঢুকে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেন। সিটির শিক্ষার্থীরা ড্যাফোডিলের কিছু শিক্ষার্থীকে জিম্মি ও মারধর করেন এবং পরে ছেড়ে দেন। পুরো ঘটনায় দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের দেড় শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হন।
থুতু ফেলার তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই প্রতিবেশী প্রতিষ্ঠানের তরুণ শিক্ষার্থীরা যে লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়ে ফেললেন, তা কোনোভাবেই কাম্য নয়। অসতর্কতাবশত যে শিক্ষার্থী থুতু ফেললেন, তিনি ‘দুঃখিত’ বললে এবং যাঁর গায়ে থুতু লেগেছে, তিনি তাঁকে ক্ষমা করে দিলে তখনই ল্যাঠা চুকে যেত। কিন্তু কী এক অস্থির জাতিতে পরিণত হয়েছি আমরা! ইটপাটকেলের প্রবাদটির উদাহরণ দিতে পারলেও, ‘ক্ষমা মহৎ গুণ’, এই আদর্শ বাক্যকে চর্চা করতে পারি না; শুধু আত্মস্থ করেই মনে করি দায়িত্ব শেষ।
ক্ষমা যেমন একটি গুণ, তেমনি সদ্ব্যবহার এবং ধৈর্যও। উচ্চশিক্ষার দুটি প্রতিষ্ঠানের কোনো কোনো শিক্ষার্থী যখন অসদাচরণ এবং অধৈর্যের পরিচয় দেন, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড করেন, তখন তা দুঃখজনক। যদি কেউ কারও ওপর অন্যায়ভাবে হামলা করে, তাহলে সেটি ফৌজদারি অপরাধ। ভুক্তভোগী আইনের আশ্রয় নিতে পারে, আইন নিজের হাতে তুলে নিতে পারে না।
দুই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা যখন সামান্য থুতুকাণ্ডকে লঙ্কাকাণ্ডে পরিণত করতে পারেন, তাহলে সেই থুতু এসে আসলে কার গায়ে পড়ে?
ওই শিক্ষার্থীদের পরিবার, যেখানে আদর্শ শিক্ষা দেওয়া হয়; তাঁদের শিক্ষক, যাঁরা সুশিক্ষা দানে ব্রতী, নাকি নিজেদের ওপর?
আচ্ছা, শৈশব থেকে ‘সদাচার’বিষয়ক পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ গড়ে দেওয়া যায় না?

ঘটনাবলি এত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে যে কোন ঘটনার সঙ্গে কোন ঘটনাকে মিলিয়ে একটা যুক্তিসংগত সিদ্ধান্তে আসা যাবে, তা একেবারেই বোঝা যাচ্ছে না। কে কার পক্ষ নিচ্ছে এবং কে কোন পক্ষ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিচ্ছে, সেটাও প্রশ্নসাপেক্ষ। এ রকম একটি অবস্থায় মূল ঘটনাগুলো থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে বিষয়গুলো সম্পর্কে
১২ মে ২০২৫
প্রায়ই ‘সংস্কৃতি’ শব্দ একটি সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। মনে করা হয় যে শিল্প-সাহিত্য-সংগীতই সংস্কৃতির সমার্থক। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সংস্কৃতি ধারণাটি পুরো জীবনধারা ও জীবনবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত, চিন্তা-চেতনা এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত। সংস্কৃতির মতো ‘গণতন্ত্র’ ধারণাকেও সীমাবদ্ধ একটি প্রেক্ষাপট থেকে দেখতে আমর
৮ ঘণ্টা আগে
ক্ষমতায় গেলে নারীদের কর্মঘণ্টা আট ঘণ্টা থেকে কমিয়ে পাঁচ ঘণ্টা করা হবে—সম্প্রতি এমন এক ঘোষণা এসেছে। কথাটা প্রথমে শুনলে অনেকের কাছে হয়তো ভালোই লাগবে। কিন্তু একটু গভীরে তাকালে বোঝা যায়, এই কথার আড়ালে লুকিয়ে আছে বিপজ্জনক এক চিন্তা—নারীকে আবার ঘরে ফেরানোর, তাঁকে কর্মক্ষেত্র থেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে দেওয়ার এক
৮ ঘণ্টা আগে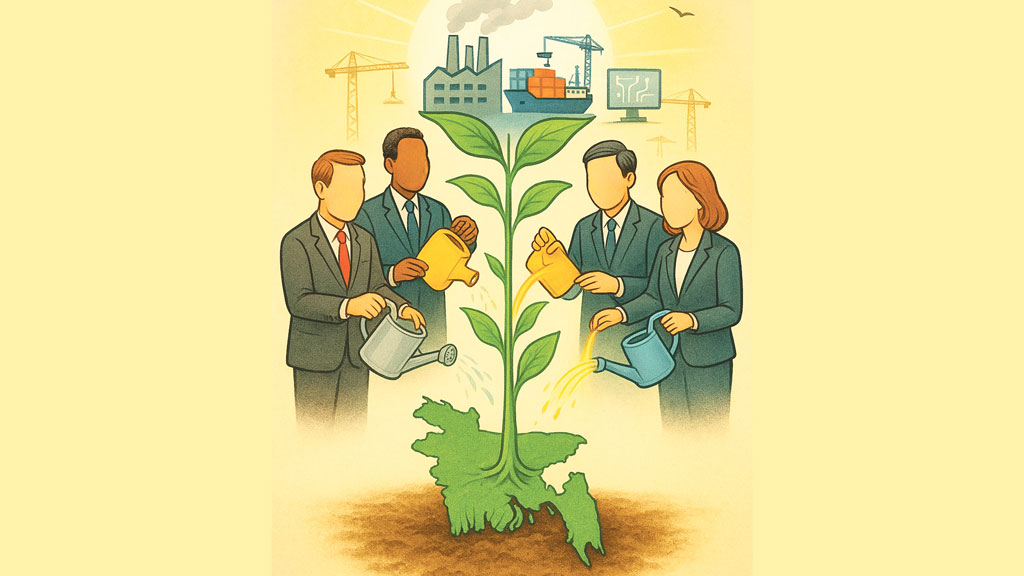
একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি হলো বিদেশি বিনিয়োগ। এই বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে যেকোনো দেশ রপ্তানির পরিমাণ বাড়িয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।
৮ ঘণ্টা আগে