
ড. সাজ্জাদ সিদ্দিকী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। বর্তমানে তিনি বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কারণ এবং প্রতিকার নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন আজকের পত্রিকার মাসুদ রানা।
মাসুদ রানা

মব জাস্টিসের পর আবার হঠাৎ করে ঢাকাসহ সারা দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার কারণ কী?
আমাদের জাতিগত সমস্যা হচ্ছে, আমরা শব্দে আটকে যাই। শব্দ নিয়ে আমরা বেশি পরিমাণে মাতোয়ারা হয়ে যাই এবং তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়ি। মব জাস্টিস তেমনি একটা ভুল শব্দ। মব কখনো জাস্টিসকে এনশিউর করে না। এটাকে ‘মব ভায়োলেন্স’ বলাটাই যৌক্তিক। মবের ঘটনা ঘটিয়ে একটা সংঘবদ্ধ গ্রুপ পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি করে আইন নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে। আসলে তাদের আইনি কাঠামোর মধ্যে দেখতে হবে। এ জন্য আমার মতে, এই ধরনের ঘটনাসমূহকে ‘মব জাস্টিস’ না বলে ‘মব ভায়োলেন্স’ বলা অধিকতর শ্রেয়।
‘মব ভায়োলেন্স’ শেষ হতে না হতেই আমরা এখন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে দেখছি। তবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য আমাদের যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করার দরকার ছিল তা আমরা করতে পারছি না, সেটা আগে স্বীকার করে নিতে হবে। কেন পারছি না, তার কারণও খুঁজে বের করতে হবে। এরপর একটা সময় উপযোগী সিদ্ধ হস্তে সেসবকে পরিশীলিত করতে হবে।
দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রধান দায়িত্ব পুলিশ বাহিনীর। অন্যদিকে, বহিঃশক্তির আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো সশস্ত্র বাহিনীর। বর্তমানে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দায়িত্ব পালনের জন্য পুলিশ বাহিনী যথাযথ অবস্থায় নেই। নিকট অতীত কৃতকর্মের জন্য পুলিশ অনেক ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে নির্লিপ্ত। বাহিনীর অনেক সদস্য নিরাপত্তাহীনতার মধ্যেও সময় পার করছেন। কারও কারও বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া চলমান। তাই বেশির ভাগ পুলিশ সদস্য পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হচ্ছেন।
আমার নিজের একটা অভিজ্ঞতা বলি, কয়েক দিন আগে আমি একটি পুলিশ ফাঁড়ির সামনে রং সাইডে একটা গাড়ি পার্ক করে থাকতে দেখি। আমি সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর নিকটবর্তী পুলিশকে ব্যাপারটা বলি। তিনি তখন বললেন, ‘স্যার, আমরা এ কাজ সমাধান করতে পারব না।’ কেন পারবেন না—আমার এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, ‘ওই গাড়িওয়ালা তাঁর ক্ষমতা দেখিয়ে আমাদের ধমকাতেও পারেন। কারণ, আমাদের এখন দেখার কেউ নেই।’ অর্থাৎ পুলিশকে আমরা এখন একটা অসহায় অবস্থার মধ্যে রেখে দিয়েছি। পুলিশকে এই অসহায় অবস্থায় রেখে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করা সম্ভব নয়। মব ভায়োলেন্সের পর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করা সম্ভব হচ্ছে না, এর অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে পুলিশের ওপর সাধারণ জনগণের আস্থার চূড়ান্ত ঘাটতি।
সেটা কেন করা সম্ভব হচ্ছে না?
লম্বা সময় ধরে পূর্ববর্তী সরকারের অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অধীনে থাকার ফলে দেশের সব প্রতিষ্ঠান ক্রমেই অগণতান্ত্রিক হয়ে উঠেছিল। এই ব্যবস্থাপনার সমাপ্তি ঘটলেও বর্তমানে আগের আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করতে পারছেন না। এই আত্মবিশ্বাস না থাকাই দায়িত্ব পালনে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারও তাদের মূল ধারায় ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ এবং এ কাজে সরকারের অনাগ্রহ স্পষ্ট। নিরাপত্তাহীন ব্যক্তির পক্ষে অন্যের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করা সম্ভব নয়। তাই তাকে ভরসার আওতায় আনতে হলে ওপর থেকে প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য নতুন করে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাকে প্রস্তুত করা প্রয়োজন।
আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দেশের দাগি সন্ত্রাসীদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তারা ছাড়া পাওয়ার পর থেকে বিভিন্ন জায়গায় চাঁদাবাজির ঘটনা ঘটেছিল। এখনকার পরিস্থিতির জন্য তারা দায়ী নয় কি?
আমরা যখন কোনো ঘটনাকে কারণ-পরম্পরার ভিত্তিতে দেখি, তখন একটি নির্দিষ্ট মাত্রা (ডাইমেনশন) থেকেই মূল্যায়ন করি, যা বিভ্রান্তিকর হতে পারে। এসব ঘটনা বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা উচিত। আমাদের দেশে দ্বি-দলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার ফলে দুই প্রধান দলেই ভালো ও মন্দ উভয় ধরনের মানুষ রয়েছে। তাই শুধু দাগি আসামিদের মুক্তি পাওয়াকে অপরাধ বৃদ্ধির একমাত্র কারণ হিসেবে দেখাটা সঠিক হবে না।
আমাদের দেশে পুঁজিবাজার অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণে একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট কাজ করে, যার কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম নেই। একইভাবে, তাদের রাজনৈতিক পরিচয়ও মুখ্য হয়ে ওঠে না। বরং আগে যারা চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণ করত, পরিস্থিতির পরিবর্তনের পর সেই জায়গাটি এখন বিএনপি-জামায়াতসহ আরও কিছু গোষ্ঠীর হাতে চলে গেছে। আওয়ামী লীগের অনেক নেতা-কর্মী জেলে ছিলেন; তাঁরা মুক্তি পেয়েছেন কি না, তা আমাদের জানা নেই। তবে যাঁরা মুক্তি পেয়েছেন, তাঁরাই যে চাঁদাবাজিসহ অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী—এমনটি সরাসরি বলা যাবে না। কারণ, অতীতে যারা ক্ষমতায় ছিল এবং যারা ছিল না, তাদের মধ্যেও অনেক ক্ষেত্রে একধরনের সমঝোতা ছিল। তাদের মধ্যে গোপন চুক্তি হওয়া অসম্ভব কিছু না, যার মূলমন্ত্র এমন হতে পারে যে, ‘তোমরা এই সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করো, বিনিময়ে আমাদের নিরাপত্তা কিংবা আশ্রয় দাও।’ মূলত, এই রকম পারস্পরিক বোঝাপড়ার কারণে আমরা সিন্ডিকেটের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে পারছি না বলেই আমার ব্যক্তিগত ধারণা।
‘অপারেশন ডেভিল হান্ট’ নামে একটি বিশেষ অভিযান চলমান থাকার পরেও কেন এ অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো?
একটা কথা আছে, ‘যতটা গর্জে, ততটা বর্ষে না’। আসলে ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট’ যতটা নামে ততটা কাজের না। পুলিশকে মেইনস্ট্রিমে না আনা পর্যন্ত কোনো কাজই হবে না। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার কাজে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের ভূমিকা কোনোকালেই সন্তোষজনক ছিল না।
এখন পুলিশ কেন এত দিন ধরে কার্যকরভাবে কাজ করতে পারছে না? অনেকের অভিযোগ, আগের সরকারের মাত্রাতিরিক্ত দলীয় সম্পৃক্ততার কারণেই পুলিশ স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারছে না। তবে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং অভ্যন্তরীণ পরিবেশ স্বাভাবিক করতে পুলিশের বিকল্প নেই। এ জন্য তাদের জনগণের আস্থার মধ্যে আনতে হবে, যা নির্দিষ্ট নীতিমালা গ্রহণের মাধ্যমে করা যেতে পারে। একটি সম্ভাব্য নীতির অংশ হিসেবে পুলিশ বাহিনীকে কয়েকটি ভিন্ন ক্লাস্টারে ভাগ করা যেতে পারে—
১. যারা আগের সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় স্বপ্রণোদিত হয়ে আইন নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল।
২. যারা কেবল সরকারের নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য ছিল।
৩. যারা অপেক্ষাকৃত কম মাত্রায় অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিল।
এরপর, যারা সবচেয়ে বেশি অপরাধে জড়িত ছিল, তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। অপেক্ষাকৃত কম সম্পৃক্তদের কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে পুনরায় কাজে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে। বাকিদের পেশাদারত্ব ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে জনগণের আস্থার মধ্যে ফিরিয়ে আনতে হবে।
এই প্রক্রিয়া পুলিশের কার্যকারিতা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সহায়ক হতে পারে। এ ছাড়া পুলিশ বাহিনীকে কাজের মধ্যে সক্রিয় না করে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না। এখন ডেভিল হান্ট বা অন্য কোনো নামে অভিযান করা হোক না কেন, তা কার্যকর করা সম্ভব হবে না।
বিগত সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতো করে এ সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাও আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক থাকার কথা বলেছেন। কিন্তু পরিস্থিতি তো আসলেই স্বাভাবিক না। তাহলে এসব ঘটনার দায় কার?
এ ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ টার্ম ব্যবহার করা প্রয়োজন, যা হলো ‘আনজাস্ট স্ট্যাটাস কো’। আগের সরকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ছোটখাটো ঘটনাগুলো এড়িয়ে যেত। যদি বর্তমান সরকারও একই নীতি অনুসরণ করে, তাহলে সেটাকেই ‘আনজাস্ট স্ট্যাটাস কো’ অব্যাহতকরণ বলা যেতে পারে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।
তবে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা দরকার—বর্তমান সরকার নির্বাচিত সরকার নয়, বরং এটি একটি আপৎকালীন সরকার (ক্রাইসিস টাইম)। এই সরকারকে ‘কেয়ারটেকার সরকার’ কিংবা অন্তর্বর্তী সরকার না বলে ‘আপৎকালীন সরকার’ বলা অধিকতর উপযুক্ত। ফলে এ সরকারের দায়বদ্ধতা ও ভূমিকা বিগত সরকারের তুলনায় অনেকটাই ভিন্ন হতে হবে।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরিচালনার জন্য যে ধরনের সক্ষম নেতৃত্ব প্রয়োজন, তা বর্তমানে অনুপস্থিত। আমার মতে, এম সাখাওয়াত হোসেন অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য যথাযথ ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, একটি ছোট ইস্যুকে কেন্দ্র করে তাঁকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এখানে একজন যোগ্য ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেওয়া অতীব জরুরি। পাশাপাশি, পুলিশ বাহিনীকে সক্রিয় ও জনমুখী করার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায়, ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট’ নামক অভিযান পরিচালনা করেও কোনো ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া যাবে না। বর্তমান সরকার যদি চাঁদাবাজি ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তারাও আগের সরকারের মতো গণধিক্কারের শিকার হবে এবং কখনোই সাধুবাদ পাবে না। কারণ, এই সরকার গঠিত হয়েছে মানুষের রক্তের বিনিময়ে। তাই জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।
বিচারহীনতা এবং দুর্বল আইন প্রয়োগের এসব ঘটনা বারবার ঘটছে। অন্তর্বর্তী সরকার এসব ঘটনা নিয়ন্ত্রণে কেন ব্যর্থ হচ্ছে?
আমরা বিচারহীনতার কথা প্রায়ই উল্লেখ করি। তবে বাংলাদেশে বিচারহীনতা নিয়ে প্রচলিত ধারণা পুরোপুরি সঠিক নয়। আমাদের মূল সমস্যা হলো আমরা সামাজিক ন্যায়বিচার সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। ধরুন, আপনাকে কোনো দায়িত্ব দেওয়া হলো। সে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আপনি যদি পক্ষপাতদুষ্ট হন, তবে আপনি নিজেই একটি পক্ষপাতমূলক কাঠামো তৈরি করবেন। এটি আমাদের সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন। শহুরে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যে হীনম্মন্যতা ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে, তা বিচারপ্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। যদি দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতেন, তাহলে বিচারহীনতা নিয়ে যে অভিযোগ করা হয়, সেটি এত প্রকট হতো না। এ ক্ষেত্রে শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণির দায় সবচেয়ে বেশি। আমরা সঠিক ব্যক্তিকে সঠিক জায়গায় দায়িত্ব দিই না; বরং তথাকথিত জনপ্রিয়তার বিবেচনায় সিদ্ধান্ত নিই। ফলে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি রাজনৈতিক, পারিবারিক বা ব্যক্তিগত প্রভাবের কারণে পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়েন। এ কারণেই আমাদের সমাজে কার্যকর কোনো কাঠামো গড়ে উঠছে না। ফলে বিভিন্ন ঘটনার দায় নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।
যদি দায়িত্বপ্রাপ্তদের জবাবদিহির আওতায় আনা যেত, তবে আমাদের দেশে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একধরনের বিপ্লব ঘটানো সম্ভব হতো। তবে বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়; বরং পুরো সমাজকে একটি কার্যকর কাঠামোর মধ্যে আনতে হবে।
মব জাস্টিসের পর আবার হঠাৎ করে ঢাকাসহ সারা দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার কারণ কী?
আমাদের জাতিগত সমস্যা হচ্ছে, আমরা শব্দে আটকে যাই। শব্দ নিয়ে আমরা বেশি পরিমাণে মাতোয়ারা হয়ে যাই এবং তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়ি। মব জাস্টিস তেমনি একটা ভুল শব্দ। মব কখনো জাস্টিসকে এনশিউর করে না। এটাকে ‘মব ভায়োলেন্স’ বলাটাই যৌক্তিক। মবের ঘটনা ঘটিয়ে একটা সংঘবদ্ধ গ্রুপ পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি করে আইন নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে। আসলে তাদের আইনি কাঠামোর মধ্যে দেখতে হবে। এ জন্য আমার মতে, এই ধরনের ঘটনাসমূহকে ‘মব জাস্টিস’ না বলে ‘মব ভায়োলেন্স’ বলা অধিকতর শ্রেয়।
‘মব ভায়োলেন্স’ শেষ হতে না হতেই আমরা এখন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে দেখছি। তবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য আমাদের যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করার দরকার ছিল তা আমরা করতে পারছি না, সেটা আগে স্বীকার করে নিতে হবে। কেন পারছি না, তার কারণও খুঁজে বের করতে হবে। এরপর একটা সময় উপযোগী সিদ্ধ হস্তে সেসবকে পরিশীলিত করতে হবে।
দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রধান দায়িত্ব পুলিশ বাহিনীর। অন্যদিকে, বহিঃশক্তির আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো সশস্ত্র বাহিনীর। বর্তমানে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দায়িত্ব পালনের জন্য পুলিশ বাহিনী যথাযথ অবস্থায় নেই। নিকট অতীত কৃতকর্মের জন্য পুলিশ অনেক ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে নির্লিপ্ত। বাহিনীর অনেক সদস্য নিরাপত্তাহীনতার মধ্যেও সময় পার করছেন। কারও কারও বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া চলমান। তাই বেশির ভাগ পুলিশ সদস্য পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হচ্ছেন।
আমার নিজের একটা অভিজ্ঞতা বলি, কয়েক দিন আগে আমি একটি পুলিশ ফাঁড়ির সামনে রং সাইডে একটা গাড়ি পার্ক করে থাকতে দেখি। আমি সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর নিকটবর্তী পুলিশকে ব্যাপারটা বলি। তিনি তখন বললেন, ‘স্যার, আমরা এ কাজ সমাধান করতে পারব না।’ কেন পারবেন না—আমার এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, ‘ওই গাড়িওয়ালা তাঁর ক্ষমতা দেখিয়ে আমাদের ধমকাতেও পারেন। কারণ, আমাদের এখন দেখার কেউ নেই।’ অর্থাৎ পুলিশকে আমরা এখন একটা অসহায় অবস্থার মধ্যে রেখে দিয়েছি। পুলিশকে এই অসহায় অবস্থায় রেখে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করা সম্ভব নয়। মব ভায়োলেন্সের পর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করা সম্ভব হচ্ছে না, এর অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে পুলিশের ওপর সাধারণ জনগণের আস্থার চূড়ান্ত ঘাটতি।
সেটা কেন করা সম্ভব হচ্ছে না?
লম্বা সময় ধরে পূর্ববর্তী সরকারের অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অধীনে থাকার ফলে দেশের সব প্রতিষ্ঠান ক্রমেই অগণতান্ত্রিক হয়ে উঠেছিল। এই ব্যবস্থাপনার সমাপ্তি ঘটলেও বর্তমানে আগের আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করতে পারছেন না। এই আত্মবিশ্বাস না থাকাই দায়িত্ব পালনে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারও তাদের মূল ধারায় ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ এবং এ কাজে সরকারের অনাগ্রহ স্পষ্ট। নিরাপত্তাহীন ব্যক্তির পক্ষে অন্যের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করা সম্ভব নয়। তাই তাকে ভরসার আওতায় আনতে হলে ওপর থেকে প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য নতুন করে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাকে প্রস্তুত করা প্রয়োজন।
আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দেশের দাগি সন্ত্রাসীদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তারা ছাড়া পাওয়ার পর থেকে বিভিন্ন জায়গায় চাঁদাবাজির ঘটনা ঘটেছিল। এখনকার পরিস্থিতির জন্য তারা দায়ী নয় কি?
আমরা যখন কোনো ঘটনাকে কারণ-পরম্পরার ভিত্তিতে দেখি, তখন একটি নির্দিষ্ট মাত্রা (ডাইমেনশন) থেকেই মূল্যায়ন করি, যা বিভ্রান্তিকর হতে পারে। এসব ঘটনা বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা উচিত। আমাদের দেশে দ্বি-দলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার ফলে দুই প্রধান দলেই ভালো ও মন্দ উভয় ধরনের মানুষ রয়েছে। তাই শুধু দাগি আসামিদের মুক্তি পাওয়াকে অপরাধ বৃদ্ধির একমাত্র কারণ হিসেবে দেখাটা সঠিক হবে না।
আমাদের দেশে পুঁজিবাজার অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণে একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট কাজ করে, যার কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম নেই। একইভাবে, তাদের রাজনৈতিক পরিচয়ও মুখ্য হয়ে ওঠে না। বরং আগে যারা চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণ করত, পরিস্থিতির পরিবর্তনের পর সেই জায়গাটি এখন বিএনপি-জামায়াতসহ আরও কিছু গোষ্ঠীর হাতে চলে গেছে। আওয়ামী লীগের অনেক নেতা-কর্মী জেলে ছিলেন; তাঁরা মুক্তি পেয়েছেন কি না, তা আমাদের জানা নেই। তবে যাঁরা মুক্তি পেয়েছেন, তাঁরাই যে চাঁদাবাজিসহ অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী—এমনটি সরাসরি বলা যাবে না। কারণ, অতীতে যারা ক্ষমতায় ছিল এবং যারা ছিল না, তাদের মধ্যেও অনেক ক্ষেত্রে একধরনের সমঝোতা ছিল। তাদের মধ্যে গোপন চুক্তি হওয়া অসম্ভব কিছু না, যার মূলমন্ত্র এমন হতে পারে যে, ‘তোমরা এই সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করো, বিনিময়ে আমাদের নিরাপত্তা কিংবা আশ্রয় দাও।’ মূলত, এই রকম পারস্পরিক বোঝাপড়ার কারণে আমরা সিন্ডিকেটের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে পারছি না বলেই আমার ব্যক্তিগত ধারণা।
‘অপারেশন ডেভিল হান্ট’ নামে একটি বিশেষ অভিযান চলমান থাকার পরেও কেন এ অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো?
একটা কথা আছে, ‘যতটা গর্জে, ততটা বর্ষে না’। আসলে ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট’ যতটা নামে ততটা কাজের না। পুলিশকে মেইনস্ট্রিমে না আনা পর্যন্ত কোনো কাজই হবে না। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার কাজে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের ভূমিকা কোনোকালেই সন্তোষজনক ছিল না।
এখন পুলিশ কেন এত দিন ধরে কার্যকরভাবে কাজ করতে পারছে না? অনেকের অভিযোগ, আগের সরকারের মাত্রাতিরিক্ত দলীয় সম্পৃক্ততার কারণেই পুলিশ স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারছে না। তবে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং অভ্যন্তরীণ পরিবেশ স্বাভাবিক করতে পুলিশের বিকল্প নেই। এ জন্য তাদের জনগণের আস্থার মধ্যে আনতে হবে, যা নির্দিষ্ট নীতিমালা গ্রহণের মাধ্যমে করা যেতে পারে। একটি সম্ভাব্য নীতির অংশ হিসেবে পুলিশ বাহিনীকে কয়েকটি ভিন্ন ক্লাস্টারে ভাগ করা যেতে পারে—
১. যারা আগের সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় স্বপ্রণোদিত হয়ে আইন নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল।
২. যারা কেবল সরকারের নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য ছিল।
৩. যারা অপেক্ষাকৃত কম মাত্রায় অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিল।
এরপর, যারা সবচেয়ে বেশি অপরাধে জড়িত ছিল, তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। অপেক্ষাকৃত কম সম্পৃক্তদের কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে পুনরায় কাজে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে। বাকিদের পেশাদারত্ব ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে জনগণের আস্থার মধ্যে ফিরিয়ে আনতে হবে।
এই প্রক্রিয়া পুলিশের কার্যকারিতা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সহায়ক হতে পারে। এ ছাড়া পুলিশ বাহিনীকে কাজের মধ্যে সক্রিয় না করে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না। এখন ডেভিল হান্ট বা অন্য কোনো নামে অভিযান করা হোক না কেন, তা কার্যকর করা সম্ভব হবে না।
বিগত সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতো করে এ সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাও আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক থাকার কথা বলেছেন। কিন্তু পরিস্থিতি তো আসলেই স্বাভাবিক না। তাহলে এসব ঘটনার দায় কার?
এ ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ টার্ম ব্যবহার করা প্রয়োজন, যা হলো ‘আনজাস্ট স্ট্যাটাস কো’। আগের সরকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ছোটখাটো ঘটনাগুলো এড়িয়ে যেত। যদি বর্তমান সরকারও একই নীতি অনুসরণ করে, তাহলে সেটাকেই ‘আনজাস্ট স্ট্যাটাস কো’ অব্যাহতকরণ বলা যেতে পারে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।
তবে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা দরকার—বর্তমান সরকার নির্বাচিত সরকার নয়, বরং এটি একটি আপৎকালীন সরকার (ক্রাইসিস টাইম)। এই সরকারকে ‘কেয়ারটেকার সরকার’ কিংবা অন্তর্বর্তী সরকার না বলে ‘আপৎকালীন সরকার’ বলা অধিকতর উপযুক্ত। ফলে এ সরকারের দায়বদ্ধতা ও ভূমিকা বিগত সরকারের তুলনায় অনেকটাই ভিন্ন হতে হবে।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরিচালনার জন্য যে ধরনের সক্ষম নেতৃত্ব প্রয়োজন, তা বর্তমানে অনুপস্থিত। আমার মতে, এম সাখাওয়াত হোসেন অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য যথাযথ ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, একটি ছোট ইস্যুকে কেন্দ্র করে তাঁকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এখানে একজন যোগ্য ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেওয়া অতীব জরুরি। পাশাপাশি, পুলিশ বাহিনীকে সক্রিয় ও জনমুখী করার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায়, ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট’ নামক অভিযান পরিচালনা করেও কোনো ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া যাবে না। বর্তমান সরকার যদি চাঁদাবাজি ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তারাও আগের সরকারের মতো গণধিক্কারের শিকার হবে এবং কখনোই সাধুবাদ পাবে না। কারণ, এই সরকার গঠিত হয়েছে মানুষের রক্তের বিনিময়ে। তাই জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।
বিচারহীনতা এবং দুর্বল আইন প্রয়োগের এসব ঘটনা বারবার ঘটছে। অন্তর্বর্তী সরকার এসব ঘটনা নিয়ন্ত্রণে কেন ব্যর্থ হচ্ছে?
আমরা বিচারহীনতার কথা প্রায়ই উল্লেখ করি। তবে বাংলাদেশে বিচারহীনতা নিয়ে প্রচলিত ধারণা পুরোপুরি সঠিক নয়। আমাদের মূল সমস্যা হলো আমরা সামাজিক ন্যায়বিচার সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। ধরুন, আপনাকে কোনো দায়িত্ব দেওয়া হলো। সে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আপনি যদি পক্ষপাতদুষ্ট হন, তবে আপনি নিজেই একটি পক্ষপাতমূলক কাঠামো তৈরি করবেন। এটি আমাদের সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন। শহুরে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যে হীনম্মন্যতা ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে, তা বিচারপ্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। যদি দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতেন, তাহলে বিচারহীনতা নিয়ে যে অভিযোগ করা হয়, সেটি এত প্রকট হতো না। এ ক্ষেত্রে শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণির দায় সবচেয়ে বেশি। আমরা সঠিক ব্যক্তিকে সঠিক জায়গায় দায়িত্ব দিই না; বরং তথাকথিত জনপ্রিয়তার বিবেচনায় সিদ্ধান্ত নিই। ফলে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি রাজনৈতিক, পারিবারিক বা ব্যক্তিগত প্রভাবের কারণে পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়েন। এ কারণেই আমাদের সমাজে কার্যকর কোনো কাঠামো গড়ে উঠছে না। ফলে বিভিন্ন ঘটনার দায় নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।
যদি দায়িত্বপ্রাপ্তদের জবাবদিহির আওতায় আনা যেত, তবে আমাদের দেশে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একধরনের বিপ্লব ঘটানো সম্ভব হতো। তবে বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়; বরং পুরো সমাজকে একটি কার্যকর কাঠামোর মধ্যে আনতে হবে।

প্রায়ই ‘সংস্কৃতি’ শব্দ একটি সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। মনে করা হয় যে শিল্প-সাহিত্য-সংগীতই সংস্কৃতির সমার্থক। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সংস্কৃতি ধারণাটি পুরো জীবনধারা ও জীবনবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত, চিন্তা-চেতনা এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত। সংস্কৃতির মতো ‘গণতন্ত্র’ ধারণাকেও সীমাবদ্ধ একটি প্রেক্ষাপট থেকে দেখতে আমর
৫ ঘণ্টা আগে
ক্ষমতায় গেলে নারীদের কর্মঘণ্টা আট ঘণ্টা থেকে কমিয়ে পাঁচ ঘণ্টা করা হবে—সম্প্রতি এমন এক ঘোষণা এসেছে। কথাটা প্রথমে শুনলে অনেকের কাছে হয়তো ভালোই লাগবে। কিন্তু একটু গভীরে তাকালে বোঝা যায়, এই কথার আড়ালে লুকিয়ে আছে বিপজ্জনক এক চিন্তা—নারীকে আবার ঘরে ফেরানোর, তাঁকে কর্মক্ষেত্র থেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে দেওয়ার এক
৫ ঘণ্টা আগে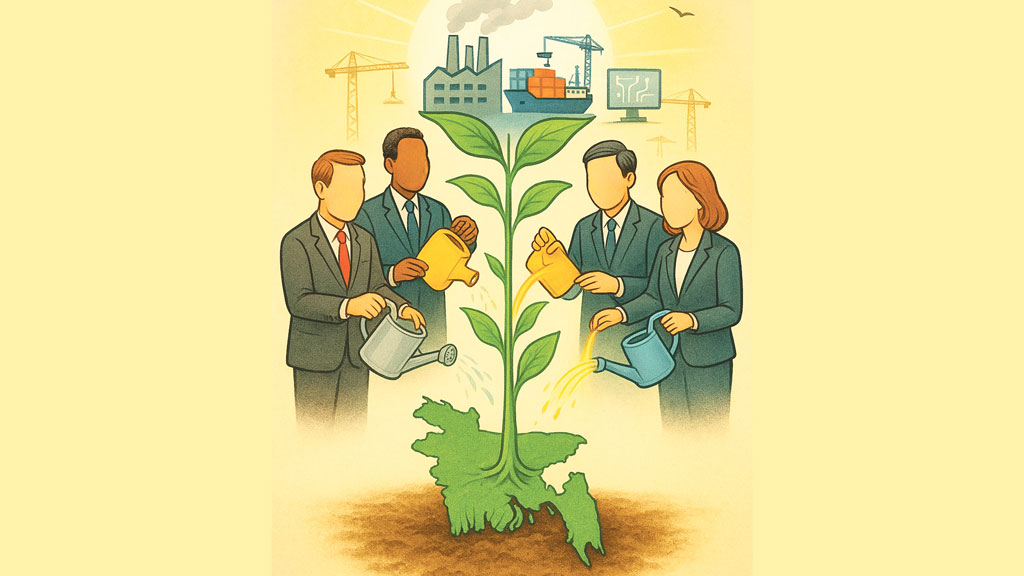
একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি হলো বিদেশি বিনিয়োগ। এই বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে যেকোনো দেশ রপ্তানির পরিমাণ বাড়িয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।
৫ ঘণ্টা আগে
‘ইট মারলে পাটকেলটি খেতে হয়’ প্রবাদটির যথাযথ উদাহরণ দিয়েছেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং সিটি ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা। তাঁরা অবশ্য এক হয়ে কাউকে পাটকেল মারেননি, বরং একে অপরকে দোষারোপ করে পাটকেল ছুড়েছেন।
৫ ঘণ্টা আগেবৃহত্তর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ তখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, যদি অন্য জাতি, সম্প্রদায়, ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল হই, মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তা নিয়ে তাদের গ্রহণ এবং কোনো রকমের মানসিক কূপমণ্ডূকতার শিকার না হই।
সেলিম জাহান

প্রায়ই ‘সংস্কৃতি’ শব্দ একটি সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। মনে করা হয় যে শিল্প-সাহিত্য-সংগীতই সংস্কৃতির সমার্থক। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সংস্কৃতি ধারণাটি পুরো জীবনধারা ও জীবনবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত, চিন্তা-চেতনা এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত। সংস্কৃতির মতো ‘গণতন্ত্র’ ধারণাকেও সীমাবদ্ধ একটি প্রেক্ষাপট থেকে দেখতে আমরা অভ্যস্ত। মনে করা হয়, এ ধারণা রাষ্ট্রবিজ্ঞান-সম্পৃক্ত। একটি দেশে বহু দলবিশিষ্ট সাধারণ নির্বাচনসহ একটি বেসামরিক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলেই তাকে অনেক সময় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে অভিহিত করা হয়।
একাধিক রাজনৈতিক দল, বেসামরিক সরকার, মুক্ত নির্বাচন, একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আবশ্যকীয় শর্ত নিঃসন্দেহে, কিন্তু পর্যাপ্ত শর্ত নয়। একই রকমভাবে সর্বজনীন মানবাধিকারও গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত, কিন্তু পর্যাপ্ত শর্ত নয়। আসলে গণতন্ত্র শুধু সর্বজনীন মানবাধিকার, রাষ্ট্রব্যবস্থা কিংবা রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এর প্রকৃত সংজ্ঞা আরও ব্যাপক।
গণতন্ত্রের এ-জাতীয় বৃহত্তর একটি সংজ্ঞা গ্রহণ করলে কয়েকটি বিষয় খুব স্পষ্ট হয়ে পড়ে। প্রথমত, গণতন্ত্র বিষয়টি শুধু সীমাবদ্ধ কিছু রাষ্ট্রবিজ্ঞানসম্মত কাঠামো কিংবা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ নয়, এটি একটি মূল্যবোধ বা সংস্কৃতির অঙ্গ। দ্বিতীয়ত, পুরো বিষয়টি স্থবির কোনো চেতনা নয়, বরং একটি গতিময় প্রক্রিয়া। তৃতীয়ত, গণতন্ত্রের অভীষ্ট লক্ষ্য পুরোপুরিভাবে কখনোই অর্জনীয় নয়; বরং সে লক্ষ্যের নিকটতর হওয়াটাই গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথযাত্রা। চতুর্থত, গণতন্ত্রে সন্তুষ্টির অবকাশ নেই, আছে সংগ্রামের দীর্ঘ পথ। পঞ্চমত, শুধু রাজনৈতিক গণতন্ত্রই নয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক গণতন্ত্র, সাংস্কৃতিক গণতন্ত্রের লড়াইও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের অংশ।
যখন গণতন্ত্রকে বৃহত্তর আঙ্গিকের গতিময় একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা হয়, তখনই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে গণতন্ত্রের একটি সংস্কৃতি আছে, যা তাৎক্ষণিকভাবে রাষ্ট্রীয় কিছু নীতিমালা বা ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্জন করা যায় না। গণতন্ত্র একটি মূল্যবোধের বিষয়, যার নিরন্তর চর্চা প্রয়োজন, শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নয়, ব্যক্তি এবং সমাজজীবনেও। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অবিরাম চর্চার মাধ্যমেই একটি জাতির গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের পটভূমি গড়ে ওঠে এবং বজায়যোগ্য রূপ গ্রহণ করে।
গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রথম পাদপীঠই হচ্ছে ব্যক্তি-মানুষ। একজন ব্যক্তি হিসেবে আমি কি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, নাকি আমার মাঝে একজন স্বৈরাচারী প্রভু বিরাজ করছে? আমি নিজের কথা বলতে যতটা উৎসাহী, অন্যের কথা শুনতে কি ততটা আগ্রহী? পরিবারের মধ্যে আমার মতামত অন্য সদস্যদের ওপরে চাপিয়ে দিতে চাই? আমার কথাই কি শেষ কথা বলে মনে করি? প্রত্যেক ব্যক্তি-মানুষের চিন্তাধারা এবং কর্মকাণ্ডের একটি বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন প্রয়োজন, যাতে বোঝা যায়, সেই ব্যক্তিমানুষ কি গণতান্ত্রিক নাকি স্বেচ্ছাচারী। ব্যক্তি হিসেবে যদি স্বৈরাচারী চিন্তাচেতনার অধিকারী হই, তাহলে কেমন করে আমি প্রত্যাশা করি, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সুসংরক্ষিত থাকবে? রাষ্ট্র তো ব্যক্তিনিরপেক্ষ কোনো নিরঙ্কুশ অস্তিত্ব নয়।
কর্মক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে বুঝতে হবে, কর্মপ্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন, চিন্তাধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ কতটা বিরাজ করে। প্রায়ই চোখে পড়ে, কর্মক্ষেত্রে অধস্তনদের আমরা দাস ভাবতেই অভ্যস্ত, আবার আমাদের ঊর্ধ্বতনদের প্রায়ই ভাবি দেবতা হিসেবে। এ দুটি দৃষ্টিভঙ্গিই অগণতান্ত্রিক। কর্মক্ষেত্রে কেউ যে কাজই করুক না কেন, মানুষ হিসেবে প্রত্যেকেই সমান এবং সম্মান পাওয়ার যোগ্য। বহুক্ষেত্রে চোখে পড়ে যে কর্মক্ষেত্রের বাইরে যখন সহকর্মীদের সঙ্গে সামাজিকভাবে মেলামেশা হয়, তখনো কর্মক্ষেত্রের আমলাতান্ত্রিক বিভাজনটি বজায় থাকে। অগণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চরম পরাকাষ্ঠা।
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের ক্ষেত্রেও অগণতান্ত্রিক বিবেচনা এবং প্রক্রিয়া প্রবলভাবে কাজ করে। সংগঠন করার মানেই সভাপতির পদটি দখল করা নয়, কিংবা আমার স্বজনদের জন্য সুবিধা আদায় নয়। অন্যের যোগ্যতার মর্যাদা দেওয়াও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অংশ। সামাজিক বিভিন্ন অঙ্গনে ও সংগঠনে সবার অধিকার মান্য করা, অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা এবং নিজের অহংবোধকে অগ্রাধিকার না দিয়ে যৌথভাবে কাজ করার মানসিকতা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পূর্বশর্ত।
রাজনীতির ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের আধার হওয়া উচিত রাজনৈতিক সংগঠনের। অথচ গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অনুপস্থিতি সবচেয়ে প্রকট রাজনৈতিক দলগুলোতেই। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, পরমতসহিষ্ণুতার অভাব বড় বেশি। বিপক্ষ দলগুলোর মতপ্রকাশের অধিকার, তাদের কণ্ঠস্বরের স্বাধীনতা অস্বীকার করে ক্ষমতাসীন দল। একটি দলের মধ্যেও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও কর্মকাণ্ডের বড় অভাব। সব গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে বিনষ্ট করে সেখানে দলনেতাকেই চূড়ান্ত ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোতে নীতি নয়, ব্যক্তিপূজাই বেশির ভাগ কাজ নিয়ন্ত্রণ করছে। বহু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, গণতান্ত্রিক একটি প্রক্রিয়া মেনে চলার পরিবর্তে বিভিন্ন সাংগঠনিক সিদ্ধান্তে চূড়ান্ত ক্ষমতা দলপ্রধানের অগণতান্ত্রিক হওয়ার সুযোগ অত্যন্ত বেশি।
রাজনীতির ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চরম অবমূল্যায়ন তখনই ঘটেছে, যখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তরুণসমাজের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছে, ছাত্রসংগঠনগুলোর স্বাধীন সত্তার বিলুপ্তি ঘটিয়ে তাদের রাজনৈতিক দলগুলোর লেজুড়ে পরিণত করা হলো। তরুণসমাজের চরিত্র হননে প্রয়াসী হয়ে হত্যা করা হয়েছে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির ভবিষ্যৎকেও।
অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে অর্থনৈতিক সুযোগের ক্ষেত্রে সবার সমান অধিকার, সম্পদে সমান সুযোগ এবং অর্থনৈতিক সমতার নিশ্চিতকরণ। এসবের মাধ্যমেই সামাজিক ন্যায্যতা অর্জন করা সম্ভব। এই পুরো প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের একটি ভূমিকা আছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চরম এক বিপর্যয় ঘটে, যখন সব অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা ভেঙে ফেলা হয় এবং অর্থনৈতিক জবাবদিহি ও দায়বদ্ধতাকে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়।
বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ তখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, যদি অন্য জাতি, সম্প্রদায়, ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল হই, মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তা নিয়ে তাদের গ্রহণ এবং কোনো রকমের মানসিক কূপমণ্ডূকতার শিকার না হই। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর স্বকীয়তা এবং স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি এবার সবার প্রতি সৌহার্দ্য সাংস্কৃতিক গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। আমরা সবাই সমান, কিন্তু সবাই এক নই।
গণতন্ত্রের পথযাত্রা খুব মসৃণ নয়। এর জন্য চাই গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পরিবেশ এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের নিরন্তর চর্চা—ব্যক্তিজীবনে, সমাজজীবনে এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির জন্য পর্যাপ্ত প্রেক্ষাপট তৈরি করতে পারে গণতন্ত্রের জন্য নিরন্তর সংগ্রাম।
লেখক: অর্থনীতিবিদ

প্রায়ই ‘সংস্কৃতি’ শব্দ একটি সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। মনে করা হয় যে শিল্প-সাহিত্য-সংগীতই সংস্কৃতির সমার্থক। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সংস্কৃতি ধারণাটি পুরো জীবনধারা ও জীবনবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত, চিন্তা-চেতনা এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত। সংস্কৃতির মতো ‘গণতন্ত্র’ ধারণাকেও সীমাবদ্ধ একটি প্রেক্ষাপট থেকে দেখতে আমরা অভ্যস্ত। মনে করা হয়, এ ধারণা রাষ্ট্রবিজ্ঞান-সম্পৃক্ত। একটি দেশে বহু দলবিশিষ্ট সাধারণ নির্বাচনসহ একটি বেসামরিক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলেই তাকে অনেক সময় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে অভিহিত করা হয়।
একাধিক রাজনৈতিক দল, বেসামরিক সরকার, মুক্ত নির্বাচন, একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আবশ্যকীয় শর্ত নিঃসন্দেহে, কিন্তু পর্যাপ্ত শর্ত নয়। একই রকমভাবে সর্বজনীন মানবাধিকারও গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত, কিন্তু পর্যাপ্ত শর্ত নয়। আসলে গণতন্ত্র শুধু সর্বজনীন মানবাধিকার, রাষ্ট্রব্যবস্থা কিংবা রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এর প্রকৃত সংজ্ঞা আরও ব্যাপক।
গণতন্ত্রের এ-জাতীয় বৃহত্তর একটি সংজ্ঞা গ্রহণ করলে কয়েকটি বিষয় খুব স্পষ্ট হয়ে পড়ে। প্রথমত, গণতন্ত্র বিষয়টি শুধু সীমাবদ্ধ কিছু রাষ্ট্রবিজ্ঞানসম্মত কাঠামো কিংবা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ নয়, এটি একটি মূল্যবোধ বা সংস্কৃতির অঙ্গ। দ্বিতীয়ত, পুরো বিষয়টি স্থবির কোনো চেতনা নয়, বরং একটি গতিময় প্রক্রিয়া। তৃতীয়ত, গণতন্ত্রের অভীষ্ট লক্ষ্য পুরোপুরিভাবে কখনোই অর্জনীয় নয়; বরং সে লক্ষ্যের নিকটতর হওয়াটাই গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথযাত্রা। চতুর্থত, গণতন্ত্রে সন্তুষ্টির অবকাশ নেই, আছে সংগ্রামের দীর্ঘ পথ। পঞ্চমত, শুধু রাজনৈতিক গণতন্ত্রই নয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক গণতন্ত্র, সাংস্কৃতিক গণতন্ত্রের লড়াইও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের অংশ।
যখন গণতন্ত্রকে বৃহত্তর আঙ্গিকের গতিময় একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা হয়, তখনই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে গণতন্ত্রের একটি সংস্কৃতি আছে, যা তাৎক্ষণিকভাবে রাষ্ট্রীয় কিছু নীতিমালা বা ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্জন করা যায় না। গণতন্ত্র একটি মূল্যবোধের বিষয়, যার নিরন্তর চর্চা প্রয়োজন, শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নয়, ব্যক্তি এবং সমাজজীবনেও। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অবিরাম চর্চার মাধ্যমেই একটি জাতির গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের পটভূমি গড়ে ওঠে এবং বজায়যোগ্য রূপ গ্রহণ করে।
গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রথম পাদপীঠই হচ্ছে ব্যক্তি-মানুষ। একজন ব্যক্তি হিসেবে আমি কি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, নাকি আমার মাঝে একজন স্বৈরাচারী প্রভু বিরাজ করছে? আমি নিজের কথা বলতে যতটা উৎসাহী, অন্যের কথা শুনতে কি ততটা আগ্রহী? পরিবারের মধ্যে আমার মতামত অন্য সদস্যদের ওপরে চাপিয়ে দিতে চাই? আমার কথাই কি শেষ কথা বলে মনে করি? প্রত্যেক ব্যক্তি-মানুষের চিন্তাধারা এবং কর্মকাণ্ডের একটি বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন প্রয়োজন, যাতে বোঝা যায়, সেই ব্যক্তিমানুষ কি গণতান্ত্রিক নাকি স্বেচ্ছাচারী। ব্যক্তি হিসেবে যদি স্বৈরাচারী চিন্তাচেতনার অধিকারী হই, তাহলে কেমন করে আমি প্রত্যাশা করি, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সুসংরক্ষিত থাকবে? রাষ্ট্র তো ব্যক্তিনিরপেক্ষ কোনো নিরঙ্কুশ অস্তিত্ব নয়।
কর্মক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে বুঝতে হবে, কর্মপ্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন, চিন্তাধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ কতটা বিরাজ করে। প্রায়ই চোখে পড়ে, কর্মক্ষেত্রে অধস্তনদের আমরা দাস ভাবতেই অভ্যস্ত, আবার আমাদের ঊর্ধ্বতনদের প্রায়ই ভাবি দেবতা হিসেবে। এ দুটি দৃষ্টিভঙ্গিই অগণতান্ত্রিক। কর্মক্ষেত্রে কেউ যে কাজই করুক না কেন, মানুষ হিসেবে প্রত্যেকেই সমান এবং সম্মান পাওয়ার যোগ্য। বহুক্ষেত্রে চোখে পড়ে যে কর্মক্ষেত্রের বাইরে যখন সহকর্মীদের সঙ্গে সামাজিকভাবে মেলামেশা হয়, তখনো কর্মক্ষেত্রের আমলাতান্ত্রিক বিভাজনটি বজায় থাকে। অগণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চরম পরাকাষ্ঠা।
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের ক্ষেত্রেও অগণতান্ত্রিক বিবেচনা এবং প্রক্রিয়া প্রবলভাবে কাজ করে। সংগঠন করার মানেই সভাপতির পদটি দখল করা নয়, কিংবা আমার স্বজনদের জন্য সুবিধা আদায় নয়। অন্যের যোগ্যতার মর্যাদা দেওয়াও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অংশ। সামাজিক বিভিন্ন অঙ্গনে ও সংগঠনে সবার অধিকার মান্য করা, অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা এবং নিজের অহংবোধকে অগ্রাধিকার না দিয়ে যৌথভাবে কাজ করার মানসিকতা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পূর্বশর্ত।
রাজনীতির ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের আধার হওয়া উচিত রাজনৈতিক সংগঠনের। অথচ গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অনুপস্থিতি সবচেয়ে প্রকট রাজনৈতিক দলগুলোতেই। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, পরমতসহিষ্ণুতার অভাব বড় বেশি। বিপক্ষ দলগুলোর মতপ্রকাশের অধিকার, তাদের কণ্ঠস্বরের স্বাধীনতা অস্বীকার করে ক্ষমতাসীন দল। একটি দলের মধ্যেও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও কর্মকাণ্ডের বড় অভাব। সব গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে বিনষ্ট করে সেখানে দলনেতাকেই চূড়ান্ত ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোতে নীতি নয়, ব্যক্তিপূজাই বেশির ভাগ কাজ নিয়ন্ত্রণ করছে। বহু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, গণতান্ত্রিক একটি প্রক্রিয়া মেনে চলার পরিবর্তে বিভিন্ন সাংগঠনিক সিদ্ধান্তে চূড়ান্ত ক্ষমতা দলপ্রধানের অগণতান্ত্রিক হওয়ার সুযোগ অত্যন্ত বেশি।
রাজনীতির ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চরম অবমূল্যায়ন তখনই ঘটেছে, যখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তরুণসমাজের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছে, ছাত্রসংগঠনগুলোর স্বাধীন সত্তার বিলুপ্তি ঘটিয়ে তাদের রাজনৈতিক দলগুলোর লেজুড়ে পরিণত করা হলো। তরুণসমাজের চরিত্র হননে প্রয়াসী হয়ে হত্যা করা হয়েছে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির ভবিষ্যৎকেও।
অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে অর্থনৈতিক সুযোগের ক্ষেত্রে সবার সমান অধিকার, সম্পদে সমান সুযোগ এবং অর্থনৈতিক সমতার নিশ্চিতকরণ। এসবের মাধ্যমেই সামাজিক ন্যায্যতা অর্জন করা সম্ভব। এই পুরো প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের একটি ভূমিকা আছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চরম এক বিপর্যয় ঘটে, যখন সব অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা ভেঙে ফেলা হয় এবং অর্থনৈতিক জবাবদিহি ও দায়বদ্ধতাকে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়।
বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ তখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, যদি অন্য জাতি, সম্প্রদায়, ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল হই, মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তা নিয়ে তাদের গ্রহণ এবং কোনো রকমের মানসিক কূপমণ্ডূকতার শিকার না হই। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর স্বকীয়তা এবং স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি এবার সবার প্রতি সৌহার্দ্য সাংস্কৃতিক গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। আমরা সবাই সমান, কিন্তু সবাই এক নই।
গণতন্ত্রের পথযাত্রা খুব মসৃণ নয়। এর জন্য চাই গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পরিবেশ এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের নিরন্তর চর্চা—ব্যক্তিজীবনে, সমাজজীবনে এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির জন্য পর্যাপ্ত প্রেক্ষাপট তৈরি করতে পারে গণতন্ত্রের জন্য নিরন্তর সংগ্রাম।
লেখক: অর্থনীতিবিদ

ড. সাজ্জাদ সিদ্দিকী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। বর্তমানে তিনি বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কারণ এবং প্রতিকার নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন...
০২ মার্চ ২০২৫
ক্ষমতায় গেলে নারীদের কর্মঘণ্টা আট ঘণ্টা থেকে কমিয়ে পাঁচ ঘণ্টা করা হবে—সম্প্রতি এমন এক ঘোষণা এসেছে। কথাটা প্রথমে শুনলে অনেকের কাছে হয়তো ভালোই লাগবে। কিন্তু একটু গভীরে তাকালে বোঝা যায়, এই কথার আড়ালে লুকিয়ে আছে বিপজ্জনক এক চিন্তা—নারীকে আবার ঘরে ফেরানোর, তাঁকে কর্মক্ষেত্র থেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে দেওয়ার এক
৫ ঘণ্টা আগে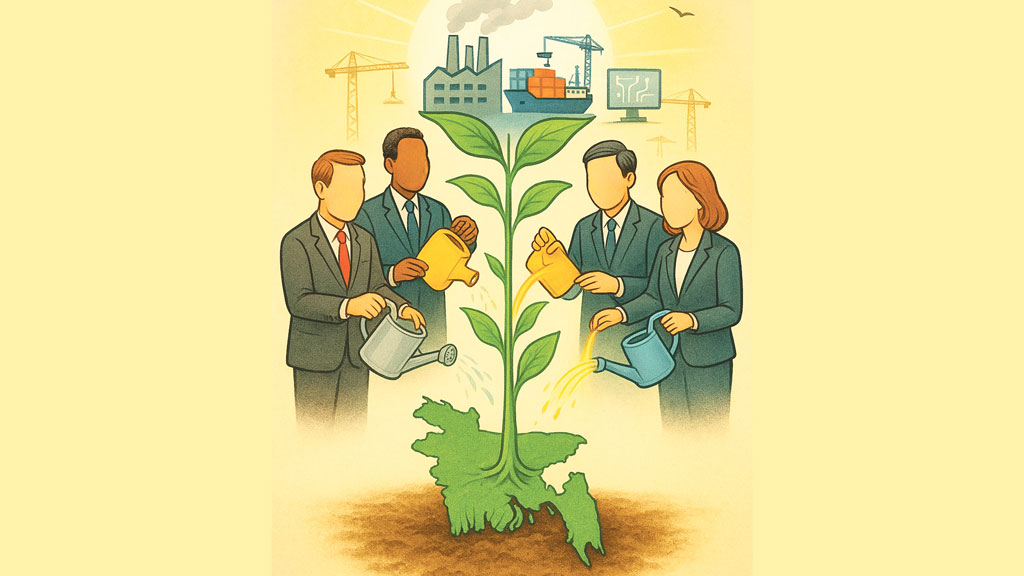
একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি হলো বিদেশি বিনিয়োগ। এই বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে যেকোনো দেশ রপ্তানির পরিমাণ বাড়িয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।
৫ ঘণ্টা আগে
‘ইট মারলে পাটকেলটি খেতে হয়’ প্রবাদটির যথাযথ উদাহরণ দিয়েছেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং সিটি ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা। তাঁরা অবশ্য এক হয়ে কাউকে পাটকেল মারেননি, বরং একে অপরকে দোষারোপ করে পাটকেল ছুড়েছেন।
৫ ঘণ্টা আগেনুসরাত রুষা

ক্ষমতায় গেলে নারীদের কর্মঘণ্টা আট ঘণ্টা থেকে কমিয়ে পাঁচ ঘণ্টা করা হবে—সম্প্রতি এমন এক ঘোষণা এসেছে। কথাটা প্রথমে শুনলে অনেকের কাছে হয়তো ভালোই লাগবে। কিন্তু একটু গভীরে তাকালে বোঝা যায়, এই কথার আড়ালে লুকিয়ে আছে বিপজ্জনক এক চিন্তা—নারীকে আবার ঘরে ফেরানোর, তাঁকে কর্মক্ষেত্র থেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে দেওয়ার এক নরম কৌশল।
প্রথমেই প্রশ্ন আসে, পাঁচ ঘণ্টা কাজ করলে কি নারী আট ঘণ্টার সমান বেতন পাবেন? যদি উত্তর হয় হ্যাঁ, তাহলে শ্রমবাজারের বাস্তব চিত্র কী দাঁড়াবে? বেসরকারি খাতে মালিকেরা কি সমান বেতনে অর্ধেক সময় কাজ করা কর্মীকে রাখতে চাইবেন? তাঁরা সহজেই বলবেন, ‘একই বেতনে পুরুষ আট ঘণ্টা কাজ দিচ্ছেন, তাহলে নারীকে কেন নেব?’ ফলাফল খুব সহজ—নারীদের জন্য চাকরির সুযোগ আরও কমে যাবে, কর্মজীবী নারীর সংখ্যা কমবে, অনেক ক্ষেত্রে নারীকে অদক্ষ কিংবা ‘অর্ধেক সময়ের কর্মী’ হিসেবে দেখবে প্রতিষ্ঠানগুলো। আর যদি বলা হয়, পাঁচ ঘণ্টা কাজের জন্য বেতনও কমবে, তাহলে তো নারী আর্থিকভাবে আরও সমস্যায় পড়ে যাবে। এই পরিস্থিতিতে নারীকে ঘরে ফেরানো, তাঁর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সংকুচিত করা, তাঁর পেশাগত অবস্থান দুর্বল করা—সবই অনিবার্য হয়ে উঠবে।
নারী অফিসে বা কারখানায় কাজ করার পর বাসার পুরো কাজও তাঁকে করতে হয়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সংসার, সন্তান, বৃদ্ধ বাবা-মা, স্বামীর যত্ন—সবকিছুই তাঁর সময়, পরিশ্রম ও মানসিক শক্তি দিয়ে টিকে থাকে। সেই নারীর জন্য যদি কর্মঘণ্টা কমানোর নামে তাঁর আয় কমিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তিনি আরও বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়বেন পরিবারের ওপর। দিনে পাঁচ ঘণ্টা বাইরে কাজ, বাকি সময় ঘরে বিনা পয়সায় খাটুনি—এটাই কি তবে সেই ‘নারীবান্ধব’ নীতি? নারীকে যেন ঘরে আরও তিন ঘণ্টা বেশি কাজ করানো যায়, অথচ তাঁর শ্রমের আর্থিক মূল্য না দিতে হয়—এই নীতি মূলত তেমন এক কৌশল।
নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন কখনোই কাজের সময় কমিয়ে আনা নয়; তাঁর কাজের পরিবেশকে নিরাপদ ও সহায়ক করা উচিত। কর্মক্ষেত্রে শিশুসন্তানসহ নারীরা যেন নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারেন, সে জন্য চাইল্ড কেয়ার বা ডে-কেয়ার সেন্টার থাকা জরুরি। নারীরা যেন অফিসে বা কারখানায় যাতায়াতের সময় হয়রানির শিকার না হন, তা নিশ্চিত করতে হবে নিরাপদ পরিবহনব্যবস্থার মাধ্যমে। মাতৃত্বকালীন ছুটি, বেতনসহ ছুটি, স্বাস্থ্যবিমা—এসব ন্যূনতম অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হওয়া দরকার। আর কর্মক্ষেত্রে নারী যেন শুধু উপস্থিত থাকেন না, সিদ্ধান্ত গ্রহণেও অংশ নেন—এই লক্ষ্যেই নেতৃত্বের জায়গায় নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে।
কিন্তু যেসব দল নারীর স্বাধীনতা ও কর্মজীবনকে বরাবরই সন্দেহের চোখে দেখে, তারা কখনোই এই বাস্তব সমাধানগুলোতে আগ্রহ দেখায় না। তারা নারীকে ঘরে রাখতেই চায়—অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল, সামাজিকভাবে নীরব এবং রাজনৈতিকভাবে অদৃশ্য এক অবস্থায়। তাদের চোখে নারী যেন এক ‘রক্ষা’ করার বস্তু, যার স্বাধীনতা নয়, শাসন দরকার। তাই তারা মাঝে মাঝে এমন ‘সহানুভূতির’ ভাষা ব্যবহার করে, যা আসলে শাসনের অন্য রূপ। কর্মঘণ্টা কমানো তারই উদাহরণ। এর মাধ্যমে বলা হচ্ছে, নারী দুর্বল, নারী দীর্ঘ সময় কাজ করতে পারেন
না, তাঁকে ‘ছাড়’ দিতে হবে। অথচ সত্য হলো—নারী পুরুষের মতোই পরিশ্রমী, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দ্বিগুণ দায়িত্ব পালন করেন।
এই ধরনের নীতির পেছনে রাজনৈতিক অভিপ্রায়ও স্পষ্ট। নারী যদি কর্মজীবন থেকে সরে আসেন, তাহলে তাঁর আর্থিক স্বাধীনতা হারায়। অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল মানুষ রাজনৈতিকভাবে নীরব হয়ে পড়ে। যাঁরা সমাজে প্রশ্ন তোলেন, অন্যায় দেখে প্রতিবাদ করেন, তাঁরা সাধারণত নিজের শ্রমের মূল্য জানেন, নিজের উপার্জনে আত্মমর্যাদা পান। তাই নারীর কণ্ঠ রুদ্ধ করতে হলে, আগে তাঁর আয়ের পথ রুদ্ধ করতে হয়। এই নীতিই সেটি—‘সহানুভূতি’র নামে তাঁকে সমাজ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পথ তৈরি করে।
বাংলাদেশে গত দুই দশকে কর্মজীবী নারীর সংখ্যা বেড়েছে, বিশেষত পোশাকশিল্প, ব্যাংক, মিডিয়া, প্রশাসন, এমনকি শিক্ষাক্ষেত্রেও নারীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছেন। এই পরিবর্তনই অনেকের চোখে আতঙ্কের কারণ। যারা মনে করে, নারীর জায়গা ঘর, তাঁর জীবন শুধু পরিবার ও সন্তান ঘিরে, তারা এই অগ্রগতি মেনে নিতে পারে না। তাই নারীকে ঘরে ফেরানোর নতুন নতুন যুক্তি খোঁজা হয়। কখনো ধর্মের নামে, কখনো সংস্কৃতির নামে, কখনো আবার ‘নারীর সুরক্ষা’র নামে। বাস্তবে কিন্তু লক্ষ্য একটাই—নারী যেন ঘরে থাকেন, তাঁর স্বাধীনতা যেন নিয়ন্ত্রণে থাকে।
নারী যদি কর্মক্ষেত্রে থাকেন, নিজের উপার্জন করেন, সিদ্ধান্ত নিতে শেখেন—তাহলে সমাজের ক্ষমতার ভারসাম্য বদলায়। সেটাই তাদের ভয়। তাই তারা এমন নীতি প্রস্তাব করে, যা নারীকে নরমভাবে প্রান্তে ঠেলে দেয়। কর্মঘণ্টা কমানো সেই প্রান্তিকীকরণের আরেক রূপ।
নারীর জন্য প্রকৃত নীতি হবে সেই নীতি, যা তাঁকে সমান সুযোগ দেয়, তাঁর কাজের মর্যাদা নিশ্চিত করে, তাঁর নিরাপত্তা এবং নেতৃত্বের পথ খুলে দেয়। নারীকে ‘দুর্বল’ হিসেবে নয়, ‘সমান নাগরিক’ হিসেবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিই একটি সভ্য সমাজের পরিচায়ক। আজ আমাদের দরকার সেই স্পষ্ট অবস্থান—নারীর নামে প্রতারণা নয়, প্রকৃত সমতা চাই।
লেখক: শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ক্ষমতায় গেলে নারীদের কর্মঘণ্টা আট ঘণ্টা থেকে কমিয়ে পাঁচ ঘণ্টা করা হবে—সম্প্রতি এমন এক ঘোষণা এসেছে। কথাটা প্রথমে শুনলে অনেকের কাছে হয়তো ভালোই লাগবে। কিন্তু একটু গভীরে তাকালে বোঝা যায়, এই কথার আড়ালে লুকিয়ে আছে বিপজ্জনক এক চিন্তা—নারীকে আবার ঘরে ফেরানোর, তাঁকে কর্মক্ষেত্র থেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে দেওয়ার এক নরম কৌশল।
প্রথমেই প্রশ্ন আসে, পাঁচ ঘণ্টা কাজ করলে কি নারী আট ঘণ্টার সমান বেতন পাবেন? যদি উত্তর হয় হ্যাঁ, তাহলে শ্রমবাজারের বাস্তব চিত্র কী দাঁড়াবে? বেসরকারি খাতে মালিকেরা কি সমান বেতনে অর্ধেক সময় কাজ করা কর্মীকে রাখতে চাইবেন? তাঁরা সহজেই বলবেন, ‘একই বেতনে পুরুষ আট ঘণ্টা কাজ দিচ্ছেন, তাহলে নারীকে কেন নেব?’ ফলাফল খুব সহজ—নারীদের জন্য চাকরির সুযোগ আরও কমে যাবে, কর্মজীবী নারীর সংখ্যা কমবে, অনেক ক্ষেত্রে নারীকে অদক্ষ কিংবা ‘অর্ধেক সময়ের কর্মী’ হিসেবে দেখবে প্রতিষ্ঠানগুলো। আর যদি বলা হয়, পাঁচ ঘণ্টা কাজের জন্য বেতনও কমবে, তাহলে তো নারী আর্থিকভাবে আরও সমস্যায় পড়ে যাবে। এই পরিস্থিতিতে নারীকে ঘরে ফেরানো, তাঁর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সংকুচিত করা, তাঁর পেশাগত অবস্থান দুর্বল করা—সবই অনিবার্য হয়ে উঠবে।
নারী অফিসে বা কারখানায় কাজ করার পর বাসার পুরো কাজও তাঁকে করতে হয়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সংসার, সন্তান, বৃদ্ধ বাবা-মা, স্বামীর যত্ন—সবকিছুই তাঁর সময়, পরিশ্রম ও মানসিক শক্তি দিয়ে টিকে থাকে। সেই নারীর জন্য যদি কর্মঘণ্টা কমানোর নামে তাঁর আয় কমিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তিনি আরও বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়বেন পরিবারের ওপর। দিনে পাঁচ ঘণ্টা বাইরে কাজ, বাকি সময় ঘরে বিনা পয়সায় খাটুনি—এটাই কি তবে সেই ‘নারীবান্ধব’ নীতি? নারীকে যেন ঘরে আরও তিন ঘণ্টা বেশি কাজ করানো যায়, অথচ তাঁর শ্রমের আর্থিক মূল্য না দিতে হয়—এই নীতি মূলত তেমন এক কৌশল।
নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন কখনোই কাজের সময় কমিয়ে আনা নয়; তাঁর কাজের পরিবেশকে নিরাপদ ও সহায়ক করা উচিত। কর্মক্ষেত্রে শিশুসন্তানসহ নারীরা যেন নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারেন, সে জন্য চাইল্ড কেয়ার বা ডে-কেয়ার সেন্টার থাকা জরুরি। নারীরা যেন অফিসে বা কারখানায় যাতায়াতের সময় হয়রানির শিকার না হন, তা নিশ্চিত করতে হবে নিরাপদ পরিবহনব্যবস্থার মাধ্যমে। মাতৃত্বকালীন ছুটি, বেতনসহ ছুটি, স্বাস্থ্যবিমা—এসব ন্যূনতম অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হওয়া দরকার। আর কর্মক্ষেত্রে নারী যেন শুধু উপস্থিত থাকেন না, সিদ্ধান্ত গ্রহণেও অংশ নেন—এই লক্ষ্যেই নেতৃত্বের জায়গায় নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে।
কিন্তু যেসব দল নারীর স্বাধীনতা ও কর্মজীবনকে বরাবরই সন্দেহের চোখে দেখে, তারা কখনোই এই বাস্তব সমাধানগুলোতে আগ্রহ দেখায় না। তারা নারীকে ঘরে রাখতেই চায়—অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল, সামাজিকভাবে নীরব এবং রাজনৈতিকভাবে অদৃশ্য এক অবস্থায়। তাদের চোখে নারী যেন এক ‘রক্ষা’ করার বস্তু, যার স্বাধীনতা নয়, শাসন দরকার। তাই তারা মাঝে মাঝে এমন ‘সহানুভূতির’ ভাষা ব্যবহার করে, যা আসলে শাসনের অন্য রূপ। কর্মঘণ্টা কমানো তারই উদাহরণ। এর মাধ্যমে বলা হচ্ছে, নারী দুর্বল, নারী দীর্ঘ সময় কাজ করতে পারেন
না, তাঁকে ‘ছাড়’ দিতে হবে। অথচ সত্য হলো—নারী পুরুষের মতোই পরিশ্রমী, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দ্বিগুণ দায়িত্ব পালন করেন।
এই ধরনের নীতির পেছনে রাজনৈতিক অভিপ্রায়ও স্পষ্ট। নারী যদি কর্মজীবন থেকে সরে আসেন, তাহলে তাঁর আর্থিক স্বাধীনতা হারায়। অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল মানুষ রাজনৈতিকভাবে নীরব হয়ে পড়ে। যাঁরা সমাজে প্রশ্ন তোলেন, অন্যায় দেখে প্রতিবাদ করেন, তাঁরা সাধারণত নিজের শ্রমের মূল্য জানেন, নিজের উপার্জনে আত্মমর্যাদা পান। তাই নারীর কণ্ঠ রুদ্ধ করতে হলে, আগে তাঁর আয়ের পথ রুদ্ধ করতে হয়। এই নীতিই সেটি—‘সহানুভূতি’র নামে তাঁকে সমাজ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পথ তৈরি করে।
বাংলাদেশে গত দুই দশকে কর্মজীবী নারীর সংখ্যা বেড়েছে, বিশেষত পোশাকশিল্প, ব্যাংক, মিডিয়া, প্রশাসন, এমনকি শিক্ষাক্ষেত্রেও নারীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছেন। এই পরিবর্তনই অনেকের চোখে আতঙ্কের কারণ। যারা মনে করে, নারীর জায়গা ঘর, তাঁর জীবন শুধু পরিবার ও সন্তান ঘিরে, তারা এই অগ্রগতি মেনে নিতে পারে না। তাই নারীকে ঘরে ফেরানোর নতুন নতুন যুক্তি খোঁজা হয়। কখনো ধর্মের নামে, কখনো সংস্কৃতির নামে, কখনো আবার ‘নারীর সুরক্ষা’র নামে। বাস্তবে কিন্তু লক্ষ্য একটাই—নারী যেন ঘরে থাকেন, তাঁর স্বাধীনতা যেন নিয়ন্ত্রণে থাকে।
নারী যদি কর্মক্ষেত্রে থাকেন, নিজের উপার্জন করেন, সিদ্ধান্ত নিতে শেখেন—তাহলে সমাজের ক্ষমতার ভারসাম্য বদলায়। সেটাই তাদের ভয়। তাই তারা এমন নীতি প্রস্তাব করে, যা নারীকে নরমভাবে প্রান্তে ঠেলে দেয়। কর্মঘণ্টা কমানো সেই প্রান্তিকীকরণের আরেক রূপ।
নারীর জন্য প্রকৃত নীতি হবে সেই নীতি, যা তাঁকে সমান সুযোগ দেয়, তাঁর কাজের মর্যাদা নিশ্চিত করে, তাঁর নিরাপত্তা এবং নেতৃত্বের পথ খুলে দেয়। নারীকে ‘দুর্বল’ হিসেবে নয়, ‘সমান নাগরিক’ হিসেবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিই একটি সভ্য সমাজের পরিচায়ক। আজ আমাদের দরকার সেই স্পষ্ট অবস্থান—নারীর নামে প্রতারণা নয়, প্রকৃত সমতা চাই।
লেখক: শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. সাজ্জাদ সিদ্দিকী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। বর্তমানে তিনি বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কারণ এবং প্রতিকার নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন...
০২ মার্চ ২০২৫
প্রায়ই ‘সংস্কৃতি’ শব্দ একটি সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। মনে করা হয় যে শিল্প-সাহিত্য-সংগীতই সংস্কৃতির সমার্থক। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সংস্কৃতি ধারণাটি পুরো জীবনধারা ও জীবনবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত, চিন্তা-চেতনা এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত। সংস্কৃতির মতো ‘গণতন্ত্র’ ধারণাকেও সীমাবদ্ধ একটি প্রেক্ষাপট থেকে দেখতে আমর
৫ ঘণ্টা আগে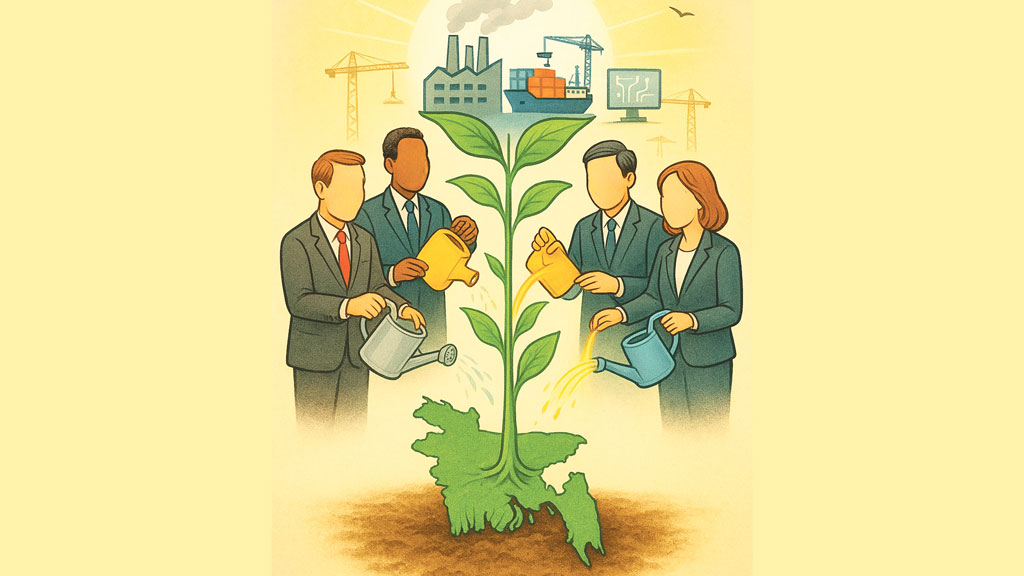
একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি হলো বিদেশি বিনিয়োগ। এই বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে যেকোনো দেশ রপ্তানির পরিমাণ বাড়িয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।
৫ ঘণ্টা আগে
‘ইট মারলে পাটকেলটি খেতে হয়’ প্রবাদটির যথাযথ উদাহরণ দিয়েছেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং সিটি ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা। তাঁরা অবশ্য এক হয়ে কাউকে পাটকেল মারেননি, বরং একে অপরকে দোষারোপ করে পাটকেল ছুড়েছেন।
৫ ঘণ্টা আগেরিয়াদ হোসেন
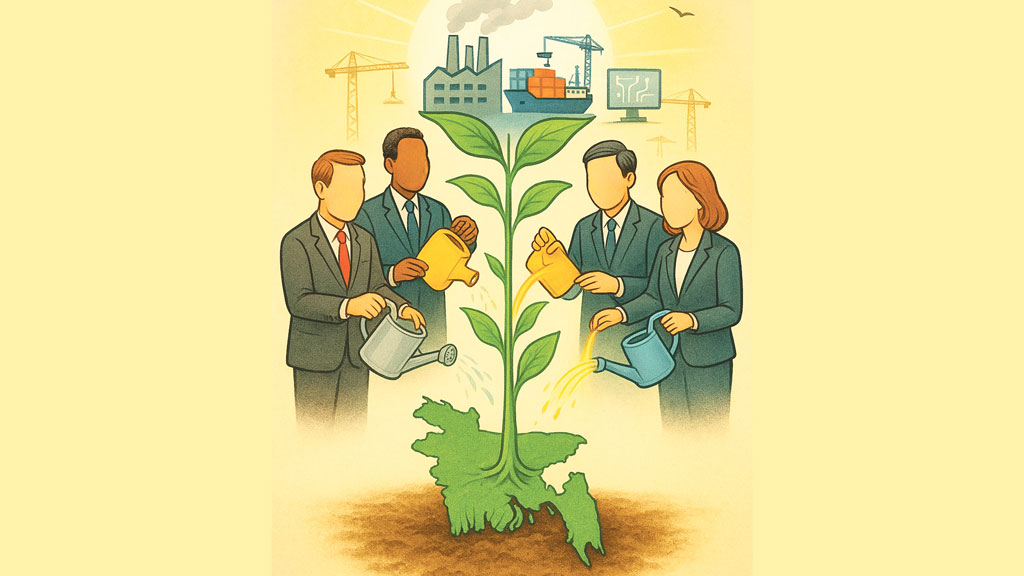
একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি হলো বিদেশি বিনিয়োগ। এই বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে যেকোনো দেশ রপ্তানির পরিমাণ বাড়িয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।
অন্য দেশের কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানি যখন আমাদের দেশে বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে, তখন দেশের অর্থনীতি আরও সচল হয়ে ওঠে। শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নতুন নতুন পণ্য উৎপাদিত হয়, মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। এতে অর্থনীতিতে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে শুরু করে।
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিভিন্ন খাতের অবকাঠামো উন্নয়নেও বিদেশি বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্বে আসার পর থেকে বিদেশি বিনিয়োগ নেই বললেই চলে। একই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বেকারত্বের সংখ্যা বেড়েছে। তবে আশার কথা, বিদেশি বিনিয়োগে আবারও সুদিন ফিরতে শুরু করেছে। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত মোট প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৬১ দশমিক ৫ শতাংশ বেড়েছে। এর পরিমাণ যেন ক্রমাগত বাড়তে থাকে, সেদিকে মনোযোগ দেওয়া জরুরি। তার জন্য দেশের নীতিনির্ধারণী মহলসহ সংশ্লিষ্টদের আরও মনোযোগী হওয়া দরকার। বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এখনো যেসব জায়গায় প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, সেগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। বিদেশি বিনিয়োগের পরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
সাধারণত বাইরে থেকে কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানি সব সময় লাভজনক ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে চায়। বিদেশিরা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সহজ উপায়,
নিশ্চিত এবং ঝুঁকিমুক্ত পরিবেশ চায়। কিন্তু যখন তারা দেখে, বিনিয়োগ করলে ব্যবসায় ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে কিংবা সেখানে ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য যথেষ্ট অনুকূল পরিবেশ নেই, তখন তারা বিনিয়োগে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তারা সেসব দেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করে।
বিদেশি কোম্পানিগুলোর কাছে যখন বিনিয়োগের একাধিক বিকল্প জায়গা থাকে; তখন তারা পছন্দমতো দেশ নির্বাচন করে সেখানে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। যেহেতু সব প্রতিকূলতা কাটিয়ে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আমাদের দেশে বিনিয়োগে উৎসাহিত হচ্ছে, তাদের এই আস্থার জায়গাটা আমাদের যেকোনো মূল্যে নিশ্চিত করতে হবে। কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে যাতে তারা নিরুৎসাহিত না হয়, সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে। আমরা দেখেছি, বিগত বছরগুলোতে
বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে যেসব খাতে, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো পোশাকশিল্প এবং রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল। যে খাতে উৎপাদন বাড়িয়ে রপ্তানি পণ্য বৃদ্ধির পাশাপাশি আমরা বেকার মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করতে পেরেছি।
এ জন্য এসব খাতে তারা যেন পরবর্তী সময়ে আরও বেশি বিনিয়োগ করে, সেই জায়গাগুলোতে আমাদের কাজ করতে হবে।
একটি সূত্র মতে, এ বছর অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট সামিটের মতো কিছু আয়োজনে পোশাক ও টেক্সটাইল খাতে নতুন কিছু বিনিয়োগের ঘোষণা এসেছে। ফলে আমাদের উৎপাদন বাড়ার পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও এগিয়ে যাব। আন্তর্জাতিকভাবে পোশাকশিল্পের বাজার আরও সমৃদ্ধ হবে। সর্বোপরি আমাদের পোশাকশিল্পের জন্য এমন ঘোষণা দেশের অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি অর্জনে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।
বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান মতে, ২০২২ সালে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৬৭০ দশমিক ৭ মিলিয়ন ডলার, যা পরবর্তী ২০২৩ সালে বেড়ে হয় ৯২৪ দশমিক ৪ মিলিয়ন ডলার। তবে ২০২৪ সালে এই বিনিয়োগের পরিমাণ কিছুটা কমে ৬৭৬ দশমিক ৬ মিলিয়ন ডলারে নেমে আসে। কিন্তু সবশেষ ২০২৫ সালের প্রথম ছয় মাসে আবার বিদেশি বিনিয়োগ বেড়ে গিয়ে ১ হাজার ৯২ দশমিক ৯ মিলিয়ন ডলারে এসে দাঁড়িয়েছে। তাহলে নির্দ্বিধায় বলা যায়, ধীরে ধীরে বিদেশি বিনিয়োগে আমাদের সুদিন ফিরতে শুরু করেছে।
এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সরকারি-বেসরকারি এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত সব প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। আমরা জানি, আমাদের দেশে দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিদেশি বিনিয়োগের অন্যতম অন্তরায়। তাই দুর্নীতি ঠেকাতে এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। বিনিয়োগকারীরা যাতে সহজে এবং দ্রুততম সময়ে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে, তার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। তাদের বিনিয়োগ করা কোনো প্রতিষ্ঠানে সমস্যা অথবা প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে তা দ্রুততার সঙ্গে সমাধান করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকতে হবে। সর্বোপরি আমরা আশা রাখি, আমাদের দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়াতে এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আরও উৎসাহিত করতে বিনিয়োগবান্ধব আইনি পরিবেশ তৈরিতে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর আরও বেশি সচেতনতা অবলম্বন করবে।
লেখক: শিক্ষার্থী, সরকারি বিএল কলেজ
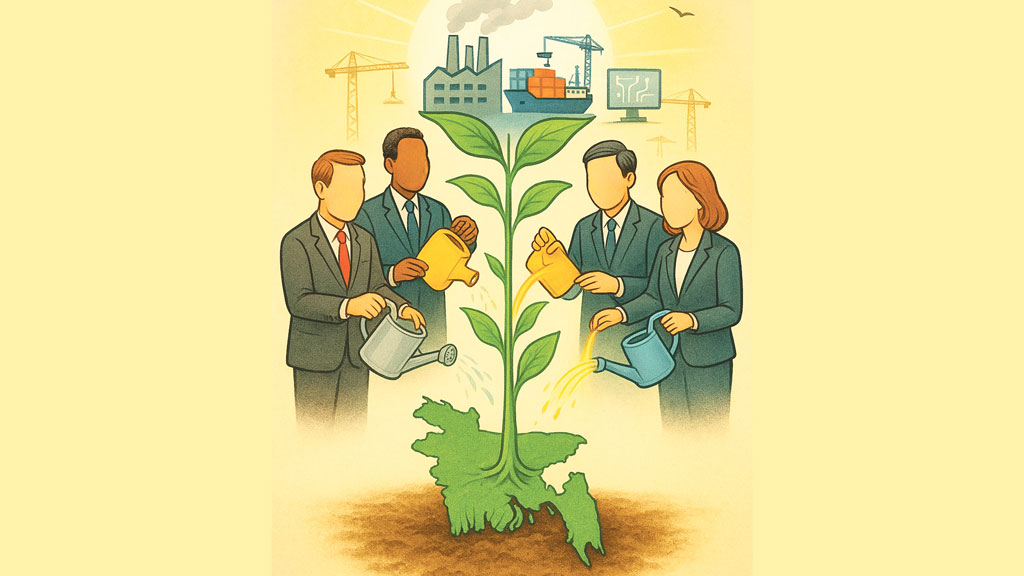
একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি হলো বিদেশি বিনিয়োগ। এই বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে যেকোনো দেশ রপ্তানির পরিমাণ বাড়িয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।
অন্য দেশের কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানি যখন আমাদের দেশে বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে, তখন দেশের অর্থনীতি আরও সচল হয়ে ওঠে। শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নতুন নতুন পণ্য উৎপাদিত হয়, মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। এতে অর্থনীতিতে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে শুরু করে।
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিভিন্ন খাতের অবকাঠামো উন্নয়নেও বিদেশি বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্বে আসার পর থেকে বিদেশি বিনিয়োগ নেই বললেই চলে। একই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বেকারত্বের সংখ্যা বেড়েছে। তবে আশার কথা, বিদেশি বিনিয়োগে আবারও সুদিন ফিরতে শুরু করেছে। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত মোট প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৬১ দশমিক ৫ শতাংশ বেড়েছে। এর পরিমাণ যেন ক্রমাগত বাড়তে থাকে, সেদিকে মনোযোগ দেওয়া জরুরি। তার জন্য দেশের নীতিনির্ধারণী মহলসহ সংশ্লিষ্টদের আরও মনোযোগী হওয়া দরকার। বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এখনো যেসব জায়গায় প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, সেগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। বিদেশি বিনিয়োগের পরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
সাধারণত বাইরে থেকে কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানি সব সময় লাভজনক ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে চায়। বিদেশিরা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সহজ উপায়,
নিশ্চিত এবং ঝুঁকিমুক্ত পরিবেশ চায়। কিন্তু যখন তারা দেখে, বিনিয়োগ করলে ব্যবসায় ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে কিংবা সেখানে ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য যথেষ্ট অনুকূল পরিবেশ নেই, তখন তারা বিনিয়োগে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তারা সেসব দেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করে।
বিদেশি কোম্পানিগুলোর কাছে যখন বিনিয়োগের একাধিক বিকল্প জায়গা থাকে; তখন তারা পছন্দমতো দেশ নির্বাচন করে সেখানে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। যেহেতু সব প্রতিকূলতা কাটিয়ে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আমাদের দেশে বিনিয়োগে উৎসাহিত হচ্ছে, তাদের এই আস্থার জায়গাটা আমাদের যেকোনো মূল্যে নিশ্চিত করতে হবে। কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে যাতে তারা নিরুৎসাহিত না হয়, সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে। আমরা দেখেছি, বিগত বছরগুলোতে
বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে যেসব খাতে, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো পোশাকশিল্প এবং রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল। যে খাতে উৎপাদন বাড়িয়ে রপ্তানি পণ্য বৃদ্ধির পাশাপাশি আমরা বেকার মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করতে পেরেছি।
এ জন্য এসব খাতে তারা যেন পরবর্তী সময়ে আরও বেশি বিনিয়োগ করে, সেই জায়গাগুলোতে আমাদের কাজ করতে হবে।
একটি সূত্র মতে, এ বছর অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট সামিটের মতো কিছু আয়োজনে পোশাক ও টেক্সটাইল খাতে নতুন কিছু বিনিয়োগের ঘোষণা এসেছে। ফলে আমাদের উৎপাদন বাড়ার পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও এগিয়ে যাব। আন্তর্জাতিকভাবে পোশাকশিল্পের বাজার আরও সমৃদ্ধ হবে। সর্বোপরি আমাদের পোশাকশিল্পের জন্য এমন ঘোষণা দেশের অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি অর্জনে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।
বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান মতে, ২০২২ সালে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৬৭০ দশমিক ৭ মিলিয়ন ডলার, যা পরবর্তী ২০২৩ সালে বেড়ে হয় ৯২৪ দশমিক ৪ মিলিয়ন ডলার। তবে ২০২৪ সালে এই বিনিয়োগের পরিমাণ কিছুটা কমে ৬৭৬ দশমিক ৬ মিলিয়ন ডলারে নেমে আসে। কিন্তু সবশেষ ২০২৫ সালের প্রথম ছয় মাসে আবার বিদেশি বিনিয়োগ বেড়ে গিয়ে ১ হাজার ৯২ দশমিক ৯ মিলিয়ন ডলারে এসে দাঁড়িয়েছে। তাহলে নির্দ্বিধায় বলা যায়, ধীরে ধীরে বিদেশি বিনিয়োগে আমাদের সুদিন ফিরতে শুরু করেছে।
এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সরকারি-বেসরকারি এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত সব প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। আমরা জানি, আমাদের দেশে দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিদেশি বিনিয়োগের অন্যতম অন্তরায়। তাই দুর্নীতি ঠেকাতে এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। বিনিয়োগকারীরা যাতে সহজে এবং দ্রুততম সময়ে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে, তার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। তাদের বিনিয়োগ করা কোনো প্রতিষ্ঠানে সমস্যা অথবা প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে তা দ্রুততার সঙ্গে সমাধান করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকতে হবে। সর্বোপরি আমরা আশা রাখি, আমাদের দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়াতে এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আরও উৎসাহিত করতে বিনিয়োগবান্ধব আইনি পরিবেশ তৈরিতে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর আরও বেশি সচেতনতা অবলম্বন করবে।
লেখক: শিক্ষার্থী, সরকারি বিএল কলেজ

ড. সাজ্জাদ সিদ্দিকী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। বর্তমানে তিনি বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কারণ এবং প্রতিকার নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন...
০২ মার্চ ২০২৫
প্রায়ই ‘সংস্কৃতি’ শব্দ একটি সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। মনে করা হয় যে শিল্প-সাহিত্য-সংগীতই সংস্কৃতির সমার্থক। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সংস্কৃতি ধারণাটি পুরো জীবনধারা ও জীবনবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত, চিন্তা-চেতনা এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত। সংস্কৃতির মতো ‘গণতন্ত্র’ ধারণাকেও সীমাবদ্ধ একটি প্রেক্ষাপট থেকে দেখতে আমর
৫ ঘণ্টা আগে
ক্ষমতায় গেলে নারীদের কর্মঘণ্টা আট ঘণ্টা থেকে কমিয়ে পাঁচ ঘণ্টা করা হবে—সম্প্রতি এমন এক ঘোষণা এসেছে। কথাটা প্রথমে শুনলে অনেকের কাছে হয়তো ভালোই লাগবে। কিন্তু একটু গভীরে তাকালে বোঝা যায়, এই কথার আড়ালে লুকিয়ে আছে বিপজ্জনক এক চিন্তা—নারীকে আবার ঘরে ফেরানোর, তাঁকে কর্মক্ষেত্র থেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে দেওয়ার এক
৫ ঘণ্টা আগে
‘ইট মারলে পাটকেলটি খেতে হয়’ প্রবাদটির যথাযথ উদাহরণ দিয়েছেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং সিটি ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা। তাঁরা অবশ্য এক হয়ে কাউকে পাটকেল মারেননি, বরং একে অপরকে দোষারোপ করে পাটকেল ছুড়েছেন।
৫ ঘণ্টা আগেসম্পাদকীয়

‘ইট মারলে পাটকেলটি খেতে হয়’ প্রবাদটির যথাযথ উদাহরণ দিয়েছেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং সিটি ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা। তাঁরা অবশ্য এক হয়ে কাউকে পাটকেল মারেননি, বরং একে অপরকে দোষারোপ করে পাটকেল ছুড়েছেন। দুই দিন ধরে সংবাদমাধ্যমের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও এই দুই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আলোচনা চলছে। ২৮ অক্টোবর আজকের পত্রিকার প্রথম পাতার এ-সংক্রান্ত খবরটি পড়লেই বিস্তারিত জানা যায়।
এরই মধ্যে অসংখ্য পাঠক জেনে গেছেন, থুতুকাণ্ডের জের ধরে সাভারের বিরুলিয়ায় অবস্থিত দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হয় ২৬ অক্টোবর, রোববার দিবাগত রাতে। রোববার রাতে খাগান এলাকায় ড্যাফোডিলের শিক্ষার্থীদের ভাড়া বাসা ‘ব্যাচেলর প্যারাডাইস হোস্টেল’-এর পাশে
বসে ছিলেন সিটির শিক্ষার্থীরা। এমন সময় সিটির এক শিক্ষার্থী অসতর্কতাবশত থুতু ফেললে তা
পাশ দিয়ে যাওয়া ড্যাফোডিলের এক শিক্ষার্থীর গায়ে লাগে। সেখানে উভয় পক্ষের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। পরে সিটি ইউনিভার্সিটির প্রায় অর্ধশত শিক্ষার্থী দেশীয় অস্ত্র ও ইটপাটকেল নিয়ে ড্যাফোডিলের শিক্ষার্থীদের ওই বাসায় হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করেন।
এই হামলার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ড্যাফোডিলের শিক্ষার্থীরা ঘটনাস্থলে জড়ো হন এবং দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া চলে। ড্যাফোডিল কর্তৃপক্ষ সিটি ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে সমাধানের চেষ্টা করার সময় সিটি ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির এক শিক্ষার্থীকে মারধর করেন। ওই খবর ছড়িয়ে পড়লে ড্যাফোডিলের শিক্ষার্থীরা সিটি ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসের ভেতরে ঢুকে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেন। সিটির শিক্ষার্থীরা ড্যাফোডিলের কিছু শিক্ষার্থীকে জিম্মি ও মারধর করেন এবং পরে ছেড়ে দেন। পুরো ঘটনায় দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের দেড় শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হন।
থুতু ফেলার তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই প্রতিবেশী প্রতিষ্ঠানের তরুণ শিক্ষার্থীরা যে লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়ে ফেললেন, তা কোনোভাবেই কাম্য নয়। অসতর্কতাবশত যে শিক্ষার্থী থুতু ফেললেন, তিনি ‘দুঃখিত’ বললে এবং যাঁর গায়ে থুতু লেগেছে, তিনি তাঁকে ক্ষমা করে দিলে তখনই ল্যাঠা চুকে যেত। কিন্তু কী এক অস্থির জাতিতে পরিণত হয়েছি আমরা! ইটপাটকেলের প্রবাদটির উদাহরণ দিতে পারলেও, ‘ক্ষমা মহৎ গুণ’, এই আদর্শ বাক্যকে চর্চা করতে পারি না; শুধু আত্মস্থ করেই মনে করি দায়িত্ব শেষ।
ক্ষমা যেমন একটি গুণ, তেমনি সদ্ব্যবহার এবং ধৈর্যও। উচ্চশিক্ষার দুটি প্রতিষ্ঠানের কোনো কোনো শিক্ষার্থী যখন অসদাচরণ এবং অধৈর্যের পরিচয় দেন, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড করেন, তখন তা দুঃখজনক। যদি কেউ কারও ওপর অন্যায়ভাবে হামলা করে, তাহলে সেটি ফৌজদারি অপরাধ। ভুক্তভোগী আইনের আশ্রয় নিতে পারে, আইন নিজের হাতে তুলে নিতে পারে না।
দুই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা যখন সামান্য থুতুকাণ্ডকে লঙ্কাকাণ্ডে পরিণত করতে পারেন, তাহলে সেই থুতু এসে আসলে কার গায়ে পড়ে?
ওই শিক্ষার্থীদের পরিবার, যেখানে আদর্শ শিক্ষা দেওয়া হয়; তাঁদের শিক্ষক, যাঁরা সুশিক্ষা দানে ব্রতী, নাকি নিজেদের ওপর?
আচ্ছা, শৈশব থেকে ‘সদাচার’বিষয়ক পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ গড়ে দেওয়া যায় না?

‘ইট মারলে পাটকেলটি খেতে হয়’ প্রবাদটির যথাযথ উদাহরণ দিয়েছেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং সিটি ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা। তাঁরা অবশ্য এক হয়ে কাউকে পাটকেল মারেননি, বরং একে অপরকে দোষারোপ করে পাটকেল ছুড়েছেন। দুই দিন ধরে সংবাদমাধ্যমের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও এই দুই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আলোচনা চলছে। ২৮ অক্টোবর আজকের পত্রিকার প্রথম পাতার এ-সংক্রান্ত খবরটি পড়লেই বিস্তারিত জানা যায়।
এরই মধ্যে অসংখ্য পাঠক জেনে গেছেন, থুতুকাণ্ডের জের ধরে সাভারের বিরুলিয়ায় অবস্থিত দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হয় ২৬ অক্টোবর, রোববার দিবাগত রাতে। রোববার রাতে খাগান এলাকায় ড্যাফোডিলের শিক্ষার্থীদের ভাড়া বাসা ‘ব্যাচেলর প্যারাডাইস হোস্টেল’-এর পাশে
বসে ছিলেন সিটির শিক্ষার্থীরা। এমন সময় সিটির এক শিক্ষার্থী অসতর্কতাবশত থুতু ফেললে তা
পাশ দিয়ে যাওয়া ড্যাফোডিলের এক শিক্ষার্থীর গায়ে লাগে। সেখানে উভয় পক্ষের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। পরে সিটি ইউনিভার্সিটির প্রায় অর্ধশত শিক্ষার্থী দেশীয় অস্ত্র ও ইটপাটকেল নিয়ে ড্যাফোডিলের শিক্ষার্থীদের ওই বাসায় হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করেন।
এই হামলার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ড্যাফোডিলের শিক্ষার্থীরা ঘটনাস্থলে জড়ো হন এবং দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া চলে। ড্যাফোডিল কর্তৃপক্ষ সিটি ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে সমাধানের চেষ্টা করার সময় সিটি ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির এক শিক্ষার্থীকে মারধর করেন। ওই খবর ছড়িয়ে পড়লে ড্যাফোডিলের শিক্ষার্থীরা সিটি ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসের ভেতরে ঢুকে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেন। সিটির শিক্ষার্থীরা ড্যাফোডিলের কিছু শিক্ষার্থীকে জিম্মি ও মারধর করেন এবং পরে ছেড়ে দেন। পুরো ঘটনায় দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের দেড় শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হন।
থুতু ফেলার তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই প্রতিবেশী প্রতিষ্ঠানের তরুণ শিক্ষার্থীরা যে লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়ে ফেললেন, তা কোনোভাবেই কাম্য নয়। অসতর্কতাবশত যে শিক্ষার্থী থুতু ফেললেন, তিনি ‘দুঃখিত’ বললে এবং যাঁর গায়ে থুতু লেগেছে, তিনি তাঁকে ক্ষমা করে দিলে তখনই ল্যাঠা চুকে যেত। কিন্তু কী এক অস্থির জাতিতে পরিণত হয়েছি আমরা! ইটপাটকেলের প্রবাদটির উদাহরণ দিতে পারলেও, ‘ক্ষমা মহৎ গুণ’, এই আদর্শ বাক্যকে চর্চা করতে পারি না; শুধু আত্মস্থ করেই মনে করি দায়িত্ব শেষ।
ক্ষমা যেমন একটি গুণ, তেমনি সদ্ব্যবহার এবং ধৈর্যও। উচ্চশিক্ষার দুটি প্রতিষ্ঠানের কোনো কোনো শিক্ষার্থী যখন অসদাচরণ এবং অধৈর্যের পরিচয় দেন, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড করেন, তখন তা দুঃখজনক। যদি কেউ কারও ওপর অন্যায়ভাবে হামলা করে, তাহলে সেটি ফৌজদারি অপরাধ। ভুক্তভোগী আইনের আশ্রয় নিতে পারে, আইন নিজের হাতে তুলে নিতে পারে না।
দুই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা যখন সামান্য থুতুকাণ্ডকে লঙ্কাকাণ্ডে পরিণত করতে পারেন, তাহলে সেই থুতু এসে আসলে কার গায়ে পড়ে?
ওই শিক্ষার্থীদের পরিবার, যেখানে আদর্শ শিক্ষা দেওয়া হয়; তাঁদের শিক্ষক, যাঁরা সুশিক্ষা দানে ব্রতী, নাকি নিজেদের ওপর?
আচ্ছা, শৈশব থেকে ‘সদাচার’বিষয়ক পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ গড়ে দেওয়া যায় না?

ড. সাজ্জাদ সিদ্দিকী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। বর্তমানে তিনি বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কারণ এবং প্রতিকার নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন...
০২ মার্চ ২০২৫
প্রায়ই ‘সংস্কৃতি’ শব্দ একটি সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। মনে করা হয় যে শিল্প-সাহিত্য-সংগীতই সংস্কৃতির সমার্থক। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সংস্কৃতি ধারণাটি পুরো জীবনধারা ও জীবনবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত, চিন্তা-চেতনা এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত। সংস্কৃতির মতো ‘গণতন্ত্র’ ধারণাকেও সীমাবদ্ধ একটি প্রেক্ষাপট থেকে দেখতে আমর
৫ ঘণ্টা আগে
ক্ষমতায় গেলে নারীদের কর্মঘণ্টা আট ঘণ্টা থেকে কমিয়ে পাঁচ ঘণ্টা করা হবে—সম্প্রতি এমন এক ঘোষণা এসেছে। কথাটা প্রথমে শুনলে অনেকের কাছে হয়তো ভালোই লাগবে। কিন্তু একটু গভীরে তাকালে বোঝা যায়, এই কথার আড়ালে লুকিয়ে আছে বিপজ্জনক এক চিন্তা—নারীকে আবার ঘরে ফেরানোর, তাঁকে কর্মক্ষেত্র থেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে দেওয়ার এক
৫ ঘণ্টা আগে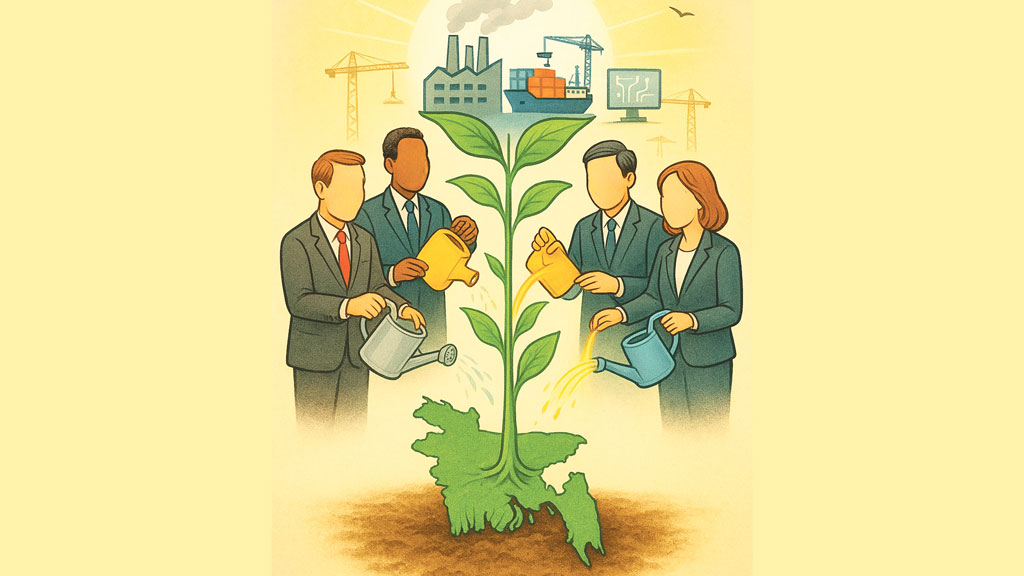
একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি হলো বিদেশি বিনিয়োগ। এই বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে যেকোনো দেশ রপ্তানির পরিমাণ বাড়িয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।
৫ ঘণ্টা আগে