মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী
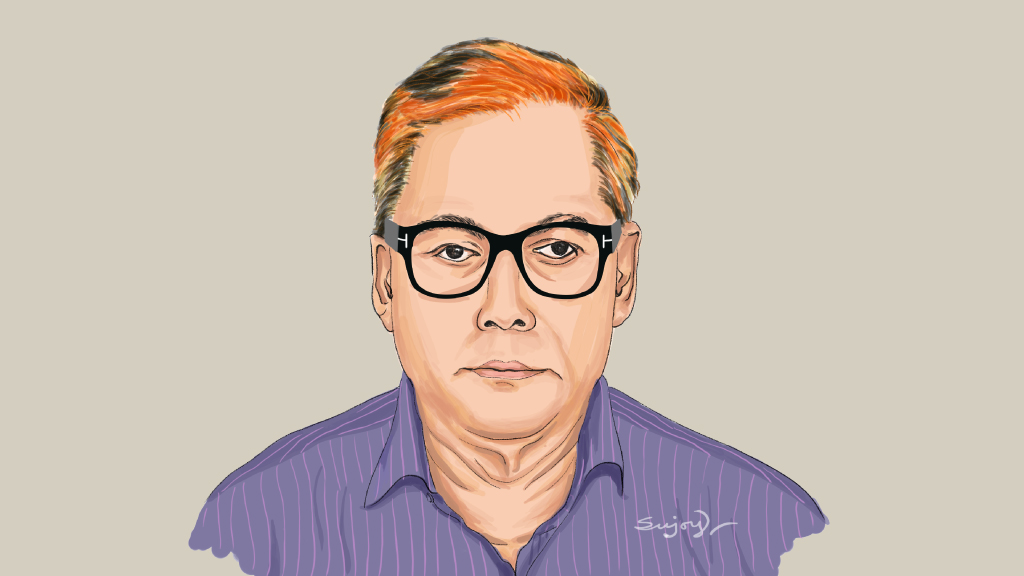
আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার আগাগোড়াই বেড়ে উঠেছে অপরিকল্পিতভাবে। কোন স্তরে কত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন, কেমন মান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে বজায় রাখতে হয়, কী ধরনের শিক্ষা জাতির জন্য অপরিহার্য, আবার কোন কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতিকে কিছুই দিতে সক্ষম নয়—এর কোনো জবাব কিংবা সঠিক ধারণা দেশে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। কিন্তু দেশে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা তথা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসার কোনো অভাব নেই। অধিকন্তু বলা চলে সব স্তরেই প্রয়োজনের চেয়ে ঢের বেশিসংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ কারণে ছাত্র ভর্তি করিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাঁচিয়ে রাখার প্রাণান্ত চেষ্টা করতে অনেকেই টিভি ও পত্রপত্রিকায় ‘ভর্তির অপূর্ব সুযোগ রয়েছে’—এমন বিজ্ঞাপন দিয়েই যাচ্ছে। গ্রামগঞ্জের নানা নামের ও ধরনের মাদ্রাসা, কেজি স্কুল, ক্যাডেট নামধারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্র ভিক্ষা করে চলছে। আসলে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগেরই কোনো অনুমোদন নেই। যে যার মতো প্রতিষ্ঠান খুলে শিক্ষক পরিচয়ে নিজের বেকারত্ব ঘোচাচ্ছেন, কিংবা আয়-উপার্জন করছেন। সত্যিকার শিক্ষা দেওয়ার কোনো স্বীকৃত প্রশিক্ষণ, শিক্ষার মানদণ্ড দেওয়ার যোগ্যতা এই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের রয়েছে কি না, তা বলা মুশকিল। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চতর মাদ্রাসা নিয়েও এমন অবস্থা বিরাজ করছে বললে আঁতকে উঠবেন না তো? একটু খবর নিলে জানতে পারবেন তাদের উচ্চশিক্ষা দিচ্ছে এমন সরকারি, বেসরকারি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসার সংখ্যা যেমন আপনাকে চমকে দেবে, একইভাবে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর হার, মান এবং ‘উচ্চশিক্ষার’ বিচিত্র রূপ দেখে আপনি যদি নিজেকে ধরে না রাখতে পারেন, তাহলে বোধ হয় এই বাস্তব অবস্থা না শোনাই আপনার জন্য মঙ্গলজনক হতে পারে! তারপরও একটু ধারণা নিয়ে ভেবে দেখুন তো দেশে উচ্চশিক্ষার নামে যা আছে বা চলছে, তাকে উচ্চশিক্ষা বলা যায় কি?
প্রথমে বলে রাখি, কলেজ, আলিম, কামিল মাদ্রাসা, সরকারি-বেসরকারি নানা ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় বা সমমানের প্রতিষ্ঠানকেই আজকের দুনিয়ায় উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। আমাদের আলোচনা এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। দেশে এখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সরকারি ও বেসরকারি কলেজের সংখ্যা ২ হাজার ২৪৯টি। এর মধ্যে ৮৫৭টি কলেজে স্নাতক, ডিগ্রি ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ৪ লাখ ২০ হাজারের অধিক শিক্ষার্থী প্রতিবছর ভর্তি হতে পারে। ঢাবির অধীনে ৭টি সরকারি কলেজে ২৬ হাজার ১৬০ আসনে প্রতিবছর ভর্তি হচ্ছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত ২ হাজার ২৪৯টি ডিগ্রি কলেজে বিএ পাস তথা স্নাতক পর্যায়ে কত শিক্ষার্থী প্রতিবছর ভর্তি হয়, তার পরিসংখ্যান খুব একটা স্পষ্ট নয়। দেশে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৮টি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ১০৬টি, সরকারি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ৫টি, সরকারি মেডিকেল কলেজ ৩৭টি, বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ৯৬টি, সরকারি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ৫টি, বেসরকারি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ৫টি, সরকারি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ৫টি, সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ৪৯টি, সরকারি স্নাতক নার্সিং ইনস্টিটিউট ৭টি এবং বেসরকারি ১৫টি, স্নাতক কওমি মাদ্রাসা ২০০টি ও স্নাতকোত্তর কওমি মাদ্রাসা ৩০০টি, ফাজিল-আলিয়া মাদ্রাসা ১ হাজার ২৭৮টি ও কামিল মাদ্রাসা ২১৫টি। এ ছাড়া বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন দূরশিক্ষণে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কয়েক লাখ শিক্ষার্থী ডিগ্রি অর্জন করছে। এর ওপর জেলায় জেলায় সাধারণ ও বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা অব্যাহত আছে। মোট কত শিক্ষার্থী এতসব ধারা-উপধারার স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কিংবা সমমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করছে, তার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়ার নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্র নেই।
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজগুলোয় স্নাতক সম্মান এবং মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জনের জন্য লাখ লাখ শিক্ষার্থী শহরে এবং গ্রামের বিভিন্ন কলেজে ভর্তি হচ্ছে। স্নাতক পাস আগে কলেজগুলোতে যতটা গুরুত্ব দিয়ে পড়ানো হতো, এখন সেগুলোতে পড়াশোনার গুরুত্ব নেই বললেই চলে। শিক্ষার্থীরা ভর্তি এবং পরীক্ষার সময় উপস্থিত হয়, এর বাইরে তাদের পঠনপাঠনের কোনো স্বাভাবিক বাধ্যবাধকতা কলেজগুলোতে পরিলক্ষিত হয় না। স্নাতক সম্মান এবং মাস্টার্স পর্যায়েও বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা বাস্তবে ক্লাস উপস্থিতি বা নিয়মিত পড়াশোনায় প্রতিফলিত হয় না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজগুলোতে স্নাতক সম্মান এবং মাস্টার্স পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদানের জন্য যেসব অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষক সংখ্যা, ল্যাব থাকা আবশ্যক, তার ন্যূনতম অনেকগুলোতেই বিদ্যমান নেই। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠদান, পঠনপাঠন বেশির ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই লক্ষ করা যাচ্ছে না।
শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার নিয়ম যতটা নিয়মিত হচ্ছে, পঠনপাঠনের বাধ্যবাধকতা এর ধারেকাছেও পরিলক্ষিত হয় না। এভাবেই স্নাতক সম্মান এবং মাস্টার্স ডিগ্রি নিয়ে অসংখ্য শিক্ষার্থী প্রতিবছর বের হয়ে আসে, যাদের শিক্ষার মান নিয়ে হাজার রকম প্রশ্ন সর্বত্র বিরাজ করছে। নবপ্রজন্মের সাধারণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সবচেয়ে বড় সংকট হচ্ছে, দক্ষ, অভিজ্ঞ শিক্ষক বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়েই নেই। গবেষণা এবং মানসম্মত পঠনপাঠনের পরিবেশও বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে ওঠেনি। বেশির ভাগ পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়ও এখন অভিজ্ঞ এবং মেধাবী শিক্ষক-সংকটে ভুগছে।
জ্ঞানবিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার, গবেষণা এবং পঠনপাঠনের চর্চা এসব বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রদর্শনে খুব একটা সফল হতে পারছে না। আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতায় তাল মিলিয়ে চলার মতো সুযোগ-সুবিধা পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই দিতে পারছে না, নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তা থেকে বেশ দূরে আছে। কলেজগুলো মানসম্মত স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পঠনপাঠন, গবেষণা দুরাশার বিষয় ছাড়া আর কিছুই নয়। আধুনিক বিশ্বে যেকোনো বিষয়ে উচ্চশিক্ষার সঙ্গে গবেষণা অপরিহার্য অংশ। কিন্তু আমাদের দেশে দু-একটা পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু কিছু বিষয় ব্যতীত কোনো পর্যায়ের উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কারিকুলামে গবেষণা মোটেও যুক্ত নয়। শিক্ষার্থীরা মৌলিক কোনো বইপুস্তকের সঙ্গেও পরিচিত নয়। বাজারে কিছু মানহীন গাইডবই এবং সাধারণ মানের কিছু বইপুস্তক ছাড়া উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীদের বইপুস্তক পড়ার কোনো আবশ্যকতাও পড়ে না। অনেক বিষয়ে শিক্ষার্থীরা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেও অধীত বিষয়ের জ্ঞানদক্ষতা অর্জন থেকে অনেক ক্ষেত্রেই পিছিয়ে আছে। বিষয়জ্ঞান ছাড়াও ভাষাজ্ঞান এবং উচ্চতর বিশ্লেষণাত্মক ধারণা অনেক বিষয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ন্যূনতম পর্যায়েও পরিলক্ষিত হয় না। সে কারণেই এদের বেশির ভাগই চাকরির বাজারে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ দেওয়ার পরীক্ষায় খুব একটা সফলতা অর্জন করতে পারে না। স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করে অনেকেই হয় বেকারত্ব কিংবা নিম্ন আয়ের কোনো উপার্জনে নিজেকে যুক্ত রাখার কর্মক্ষেত্র খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করেও সফল হতে পারছে না। অথচ বাংলাদেশে অসংখ্য শিল্পকলকারখানা, প্রতিষ্ঠান দক্ষ কর্মকর্তার অভাবে বিদেশ থেকে দক্ষ কর্মকর্তাদের উচ্চতর বেতনে নিযুক্ত করে থাকে। আমাদের উচ্চশিক্ষিত তরুণদের বেকারত্বের হার প্রতিবছর উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। এটি এখন ২৬ লাখ ছাড়িয়ে গেছে বলেও কোনো কোনো সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে। উচ্চতর সনদ ডিগ্রিধারীর সংখ্যা সীমাহীন আকারে বেড়ে যাওয়ার কারণে বিরাট অঙ্কের ঘুষ, তদবির এবং প্রভাব বিস্তার ছাড়া খুব কমসংখ্যকই একটি সাধারণ মানের চাকরি লাভে সমর্থ হয়। কেবল উচ্চতর দক্ষতায় অভিজ্ঞ মেধাবীরাই চাকরির বাজারে নিজেদের পছন্দের জায়গা খুঁজে নিতে পারছে। বেশির ভাগই শিক্ষায় দক্ষতা এবং জ্ঞানের প্রয়োজনীয় মান অর্জন না করায় আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো মানের সংকটে ভুগছে; বিশেষত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় কোনো স্তরেই শিক্ষক পদে মেধাবী ও যোগ্য প্রার্থী আশানুরূপ পাওয়া যাচ্ছে না।
তাহলে করণীয়টা কী? অবশ্যই প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার মান শুধু বৃদ্ধিই নয়, সমতা বিধানও করতে হবে। একই সঙ্গে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের ধারণা ও ভাষাজ্ঞান কাঙ্ক্ষিত মানেই উন্নীত করতে হবে। উচ্চশিক্ষার বর্তমান অপরিকল্পিত অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবেই। স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার মান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কারিকুলাম, বইপুস্তক, পঠনপাঠন, গবেষণায় এবং পরীক্ষায় আমূল পরিবর্তন আনা আবশ্যকীয়। স্নাতক সম্মান পর্যায়ের শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং সমমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, উচ্চতর গবেষণা ও উচ্চতর ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষক নিশ্চিত করা এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের সর্বশেষ আবিষ্কার ও ধারণার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একাত্ম হওয়ার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করতেই হবে। শুধু সংখ্যা ও পরিমাণগত নয়; বরং গুণগত মানে প্রাধান্য দিয়ে উচ্চশিক্ষাকে প্রতিষ্ঠানগুলোয় অর্জনের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ, আমরা এখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। এই বিপ্লবে টিকে থাকতে হলে আমাদের অবশ্যই জ্ঞানবিজ্ঞান, উচ্চতর সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অভিন্ন মানে চর্চার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। তাহলেই শিক্ষায় আর্থিক ও মানবসম্পদের অপচয় না ঘটে; বরং সমৃদ্ধিই বয়ে আনবে।
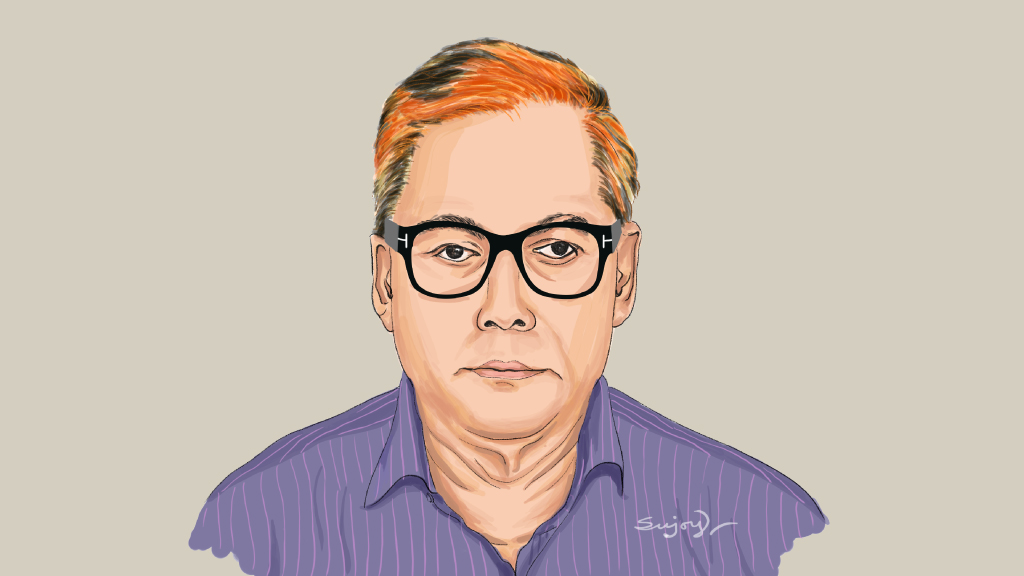
আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার আগাগোড়াই বেড়ে উঠেছে অপরিকল্পিতভাবে। কোন স্তরে কত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন, কেমন মান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে বজায় রাখতে হয়, কী ধরনের শিক্ষা জাতির জন্য অপরিহার্য, আবার কোন কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতিকে কিছুই দিতে সক্ষম নয়—এর কোনো জবাব কিংবা সঠিক ধারণা দেশে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। কিন্তু দেশে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা তথা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসার কোনো অভাব নেই। অধিকন্তু বলা চলে সব স্তরেই প্রয়োজনের চেয়ে ঢের বেশিসংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ কারণে ছাত্র ভর্তি করিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাঁচিয়ে রাখার প্রাণান্ত চেষ্টা করতে অনেকেই টিভি ও পত্রপত্রিকায় ‘ভর্তির অপূর্ব সুযোগ রয়েছে’—এমন বিজ্ঞাপন দিয়েই যাচ্ছে। গ্রামগঞ্জের নানা নামের ও ধরনের মাদ্রাসা, কেজি স্কুল, ক্যাডেট নামধারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্র ভিক্ষা করে চলছে। আসলে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগেরই কোনো অনুমোদন নেই। যে যার মতো প্রতিষ্ঠান খুলে শিক্ষক পরিচয়ে নিজের বেকারত্ব ঘোচাচ্ছেন, কিংবা আয়-উপার্জন করছেন। সত্যিকার শিক্ষা দেওয়ার কোনো স্বীকৃত প্রশিক্ষণ, শিক্ষার মানদণ্ড দেওয়ার যোগ্যতা এই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের রয়েছে কি না, তা বলা মুশকিল। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চতর মাদ্রাসা নিয়েও এমন অবস্থা বিরাজ করছে বললে আঁতকে উঠবেন না তো? একটু খবর নিলে জানতে পারবেন তাদের উচ্চশিক্ষা দিচ্ছে এমন সরকারি, বেসরকারি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসার সংখ্যা যেমন আপনাকে চমকে দেবে, একইভাবে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর হার, মান এবং ‘উচ্চশিক্ষার’ বিচিত্র রূপ দেখে আপনি যদি নিজেকে ধরে না রাখতে পারেন, তাহলে বোধ হয় এই বাস্তব অবস্থা না শোনাই আপনার জন্য মঙ্গলজনক হতে পারে! তারপরও একটু ধারণা নিয়ে ভেবে দেখুন তো দেশে উচ্চশিক্ষার নামে যা আছে বা চলছে, তাকে উচ্চশিক্ষা বলা যায় কি?
প্রথমে বলে রাখি, কলেজ, আলিম, কামিল মাদ্রাসা, সরকারি-বেসরকারি নানা ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় বা সমমানের প্রতিষ্ঠানকেই আজকের দুনিয়ায় উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। আমাদের আলোচনা এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। দেশে এখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সরকারি ও বেসরকারি কলেজের সংখ্যা ২ হাজার ২৪৯টি। এর মধ্যে ৮৫৭টি কলেজে স্নাতক, ডিগ্রি ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ৪ লাখ ২০ হাজারের অধিক শিক্ষার্থী প্রতিবছর ভর্তি হতে পারে। ঢাবির অধীনে ৭টি সরকারি কলেজে ২৬ হাজার ১৬০ আসনে প্রতিবছর ভর্তি হচ্ছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত ২ হাজার ২৪৯টি ডিগ্রি কলেজে বিএ পাস তথা স্নাতক পর্যায়ে কত শিক্ষার্থী প্রতিবছর ভর্তি হয়, তার পরিসংখ্যান খুব একটা স্পষ্ট নয়। দেশে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৮টি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ১০৬টি, সরকারি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ৫টি, সরকারি মেডিকেল কলেজ ৩৭টি, বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ৯৬টি, সরকারি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ৫টি, বেসরকারি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ৫টি, সরকারি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ৫টি, সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ৪৯টি, সরকারি স্নাতক নার্সিং ইনস্টিটিউট ৭টি এবং বেসরকারি ১৫টি, স্নাতক কওমি মাদ্রাসা ২০০টি ও স্নাতকোত্তর কওমি মাদ্রাসা ৩০০টি, ফাজিল-আলিয়া মাদ্রাসা ১ হাজার ২৭৮টি ও কামিল মাদ্রাসা ২১৫টি। এ ছাড়া বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন দূরশিক্ষণে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কয়েক লাখ শিক্ষার্থী ডিগ্রি অর্জন করছে। এর ওপর জেলায় জেলায় সাধারণ ও বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা অব্যাহত আছে। মোট কত শিক্ষার্থী এতসব ধারা-উপধারার স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কিংবা সমমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করছে, তার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়ার নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্র নেই।
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজগুলোয় স্নাতক সম্মান এবং মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জনের জন্য লাখ লাখ শিক্ষার্থী শহরে এবং গ্রামের বিভিন্ন কলেজে ভর্তি হচ্ছে। স্নাতক পাস আগে কলেজগুলোতে যতটা গুরুত্ব দিয়ে পড়ানো হতো, এখন সেগুলোতে পড়াশোনার গুরুত্ব নেই বললেই চলে। শিক্ষার্থীরা ভর্তি এবং পরীক্ষার সময় উপস্থিত হয়, এর বাইরে তাদের পঠনপাঠনের কোনো স্বাভাবিক বাধ্যবাধকতা কলেজগুলোতে পরিলক্ষিত হয় না। স্নাতক সম্মান এবং মাস্টার্স পর্যায়েও বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা বাস্তবে ক্লাস উপস্থিতি বা নিয়মিত পড়াশোনায় প্রতিফলিত হয় না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজগুলোতে স্নাতক সম্মান এবং মাস্টার্স পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদানের জন্য যেসব অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষক সংখ্যা, ল্যাব থাকা আবশ্যক, তার ন্যূনতম অনেকগুলোতেই বিদ্যমান নেই। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠদান, পঠনপাঠন বেশির ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই লক্ষ করা যাচ্ছে না।
শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার নিয়ম যতটা নিয়মিত হচ্ছে, পঠনপাঠনের বাধ্যবাধকতা এর ধারেকাছেও পরিলক্ষিত হয় না। এভাবেই স্নাতক সম্মান এবং মাস্টার্স ডিগ্রি নিয়ে অসংখ্য শিক্ষার্থী প্রতিবছর বের হয়ে আসে, যাদের শিক্ষার মান নিয়ে হাজার রকম প্রশ্ন সর্বত্র বিরাজ করছে। নবপ্রজন্মের সাধারণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সবচেয়ে বড় সংকট হচ্ছে, দক্ষ, অভিজ্ঞ শিক্ষক বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়েই নেই। গবেষণা এবং মানসম্মত পঠনপাঠনের পরিবেশও বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে ওঠেনি। বেশির ভাগ পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়ও এখন অভিজ্ঞ এবং মেধাবী শিক্ষক-সংকটে ভুগছে।
জ্ঞানবিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার, গবেষণা এবং পঠনপাঠনের চর্চা এসব বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রদর্শনে খুব একটা সফল হতে পারছে না। আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতায় তাল মিলিয়ে চলার মতো সুযোগ-সুবিধা পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই দিতে পারছে না, নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তা থেকে বেশ দূরে আছে। কলেজগুলো মানসম্মত স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পঠনপাঠন, গবেষণা দুরাশার বিষয় ছাড়া আর কিছুই নয়। আধুনিক বিশ্বে যেকোনো বিষয়ে উচ্চশিক্ষার সঙ্গে গবেষণা অপরিহার্য অংশ। কিন্তু আমাদের দেশে দু-একটা পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু কিছু বিষয় ব্যতীত কোনো পর্যায়ের উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কারিকুলামে গবেষণা মোটেও যুক্ত নয়। শিক্ষার্থীরা মৌলিক কোনো বইপুস্তকের সঙ্গেও পরিচিত নয়। বাজারে কিছু মানহীন গাইডবই এবং সাধারণ মানের কিছু বইপুস্তক ছাড়া উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীদের বইপুস্তক পড়ার কোনো আবশ্যকতাও পড়ে না। অনেক বিষয়ে শিক্ষার্থীরা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেও অধীত বিষয়ের জ্ঞানদক্ষতা অর্জন থেকে অনেক ক্ষেত্রেই পিছিয়ে আছে। বিষয়জ্ঞান ছাড়াও ভাষাজ্ঞান এবং উচ্চতর বিশ্লেষণাত্মক ধারণা অনেক বিষয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ন্যূনতম পর্যায়েও পরিলক্ষিত হয় না। সে কারণেই এদের বেশির ভাগই চাকরির বাজারে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ দেওয়ার পরীক্ষায় খুব একটা সফলতা অর্জন করতে পারে না। স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করে অনেকেই হয় বেকারত্ব কিংবা নিম্ন আয়ের কোনো উপার্জনে নিজেকে যুক্ত রাখার কর্মক্ষেত্র খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করেও সফল হতে পারছে না। অথচ বাংলাদেশে অসংখ্য শিল্পকলকারখানা, প্রতিষ্ঠান দক্ষ কর্মকর্তার অভাবে বিদেশ থেকে দক্ষ কর্মকর্তাদের উচ্চতর বেতনে নিযুক্ত করে থাকে। আমাদের উচ্চশিক্ষিত তরুণদের বেকারত্বের হার প্রতিবছর উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। এটি এখন ২৬ লাখ ছাড়িয়ে গেছে বলেও কোনো কোনো সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে। উচ্চতর সনদ ডিগ্রিধারীর সংখ্যা সীমাহীন আকারে বেড়ে যাওয়ার কারণে বিরাট অঙ্কের ঘুষ, তদবির এবং প্রভাব বিস্তার ছাড়া খুব কমসংখ্যকই একটি সাধারণ মানের চাকরি লাভে সমর্থ হয়। কেবল উচ্চতর দক্ষতায় অভিজ্ঞ মেধাবীরাই চাকরির বাজারে নিজেদের পছন্দের জায়গা খুঁজে নিতে পারছে। বেশির ভাগই শিক্ষায় দক্ষতা এবং জ্ঞানের প্রয়োজনীয় মান অর্জন না করায় আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো মানের সংকটে ভুগছে; বিশেষত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় কোনো স্তরেই শিক্ষক পদে মেধাবী ও যোগ্য প্রার্থী আশানুরূপ পাওয়া যাচ্ছে না।
তাহলে করণীয়টা কী? অবশ্যই প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার মান শুধু বৃদ্ধিই নয়, সমতা বিধানও করতে হবে। একই সঙ্গে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের ধারণা ও ভাষাজ্ঞান কাঙ্ক্ষিত মানেই উন্নীত করতে হবে। উচ্চশিক্ষার বর্তমান অপরিকল্পিত অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবেই। স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার মান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কারিকুলাম, বইপুস্তক, পঠনপাঠন, গবেষণায় এবং পরীক্ষায় আমূল পরিবর্তন আনা আবশ্যকীয়। স্নাতক সম্মান পর্যায়ের শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং সমমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, উচ্চতর গবেষণা ও উচ্চতর ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষক নিশ্চিত করা এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের সর্বশেষ আবিষ্কার ও ধারণার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একাত্ম হওয়ার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করতেই হবে। শুধু সংখ্যা ও পরিমাণগত নয়; বরং গুণগত মানে প্রাধান্য দিয়ে উচ্চশিক্ষাকে প্রতিষ্ঠানগুলোয় অর্জনের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ, আমরা এখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। এই বিপ্লবে টিকে থাকতে হলে আমাদের অবশ্যই জ্ঞানবিজ্ঞান, উচ্চতর সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অভিন্ন মানে চর্চার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। তাহলেই শিক্ষায় আর্থিক ও মানবসম্পদের অপচয় না ঘটে; বরং সমৃদ্ধিই বয়ে আনবে।

‘দুই দিন আগেই বাড়ি থেকে পাথরঘাটায় চলে এসেছি। এখন পুরোনো জাল সেলাই করছি। এক সপ্তাহের বাজারও করে এনেছি। আজ বিকেলে সাগর মোহনায় যাব, গভীর রাত থেকে জাল ফেলব।’ কথাগুলো বলছিলেন বরগুনা সদরের বাইনচটকী এলাকার জেলে হোসেন আলী। গতকাল বুধবার সকালে বরগুনার পাথরঘাটা মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে কথা হয় তাঁর...
১২ জুন ২০২৫
ভারতের স্থলবন্দর নিষেধাজ্ঞার পর সীমান্তে আটকে থাকা তৈরি পোশাক, খাদ্যসহ বিভিন্ন পণ্যের ট্রাকগুলো ফেরত আনছেন রপ্তানিকারকেরা। তবে যেসব ট্রাক বন্দরে ঢুকে গিয়েছিল, সেগুলো ভারতে প্রবেশ করানোর চেষ্টা চলছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসব ট্রাক ঢুকতে পারবে কি না, তা নিয়ে সংশয় আছে।
১৯ মে ২০২৫
আধুনিক যুগের সবচেয়ে বিস্ময়কর প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলোর একটি হচ্ছে গৌতম বুদ্ধের দেহাবশেষের সঙ্গে সম্পর্কিত ঐতিহাসিক রত্নসম্ভার। গতকাল বুধবার হংকংয়ে বিখ্যাত আর্ট নিলাম কোম্পানি সাদাবি’স-এর এক নিলামে এগুলো তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়।
০৮ মে ২০২৫
পাকিস্তানে ভারতের হামলার সমালোচনা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। চীনও এই হামলাকে ‘দুঃখজনক’ বলে অভিহিত করেছে। উদ্বেগ জানিয়েছে জাতিসংঘও। উত্তেজনা যেন আরও না বাড়ে, সে জন্য দুই পক্ষকে সংযত থাকার আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ, ফ্রান্সসহ বিভিন্ন দেশ। এদিকে ভারতের অবস্থানকে সমর্থন করেছে...
০৮ মে ২০২৫