আহমেদ শমসের, সাংবাদিক
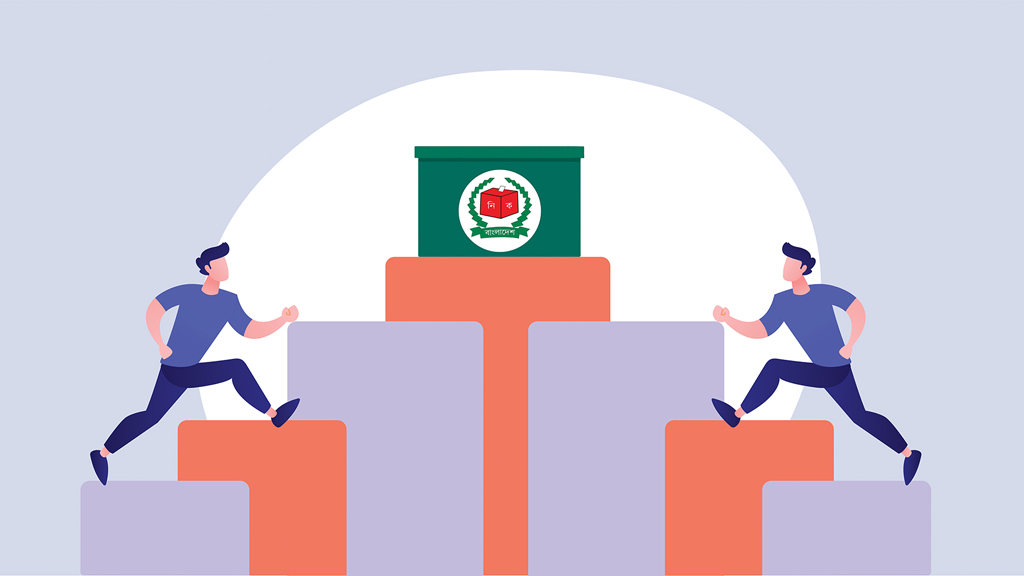
উইকিপিডিয়ায় নির্বাচনের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইভাবে: নির্বাচন হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের এমন একটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে জনগণ প্রশাসনিক কাজের জন্য একজন প্রতিনিধিকে বেছে নেয়। সপ্তদশ শতক থেকে আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে নির্বাচন একটি আবশ্যিক প্রক্রিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে আজকের দিনে নির্বাচন শব্দটি শুধু একটি দিনে ভোট দেওয়ার আনুষ্ঠানিকতার নাম নয়; এটি একটি জাতির গণতান্ত্রিক যাত্রার মৌলিক ভিত্তি। জনগণ তাদের প্রতিনিধিকে নির্বাচনের মাধ্যমে বেছে নেয়, নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও ভবিষ্যতের দায়িত্ব তুলে দেয় একদল মানুষের হাতে। তাই নির্বাচন মানেই গণতন্ত্রের প্রাণ। অবশ্য শুধু নির্বাচন হলেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় না, প্রয়োজন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন—যেখানে প্রতিটি ভোটারের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকে, প্রতিটি ভোট গণ্য হয় সমান গুরুত্বে এবং জনগণের রায়ই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আবেগ, হতাশা, অভিযোগ আর প্রত্যাশা—সবকিছু একসঙ্গে চলে আসে। কিন্তু আমাদের দেশে নির্বাচন একটি রাজনৈতিক কর্মসূচির বদলে হয়ে উঠেছে বিরোধ, সংঘাত এবং সন্দেহের কেন্দ্রবিন্দু। প্রতিটি জাতীয় নির্বাচনের আগে জনমনে প্রশ্ন জাগে, এইবার কি সত্যিই সুষ্ঠু নির্বাচন হবে?
এই প্রশ্নের উৎপত্তি ইতিহাস থেকে। ১৯৭০ সালের নির্বাচন, যা ছিল পূর্ব পাকিস্তান তথা গোটা পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম ও একমাত্র প্রায়-নিরপেক্ষ নির্বাচন, আমাদের আত্মপরিচয়ের বীজ বপন করেছিল। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও কেন্দ্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর না হওয়ায় দেখা দেয় বড় ধরনের রাজনৈতিক সংকট, শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ৯ মাসের যুদ্ধ শেষে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়।
১৯৭৩ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে। বিপুল বিজয়ে তারা ক্ষমতায় আসে, তাই বিরোধী দল বলতে তেমন কিছু ছিল না। একদলীয় শাসনের অভিপ্রায় তখনো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, কিন্তু ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক নাটকীয়তা সে পথই উন্মোচন করে দেয়।
এরপর আসে একটি অস্থির ও রক্তাক্ত সময়। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা পায়। ১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রপতি পদে জিয়াউর রহমান গণভোটের আয়োজন করেন, যার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে শুরু থেকেই প্রশ্ন ছিল। ১৯৭৮ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং ১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও ছিল সেনাবাহিনীর ছায়া, প্রশাসনের শক্ত ভূমিকা এবং ক্ষমতা ধরে রাখার কৌশল।
জিয়াউর রহমানের সময়টায় নির্বাচনী ব্যবস্থায় যে ‘নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের’ ধারা তৈরি হয়েছিল, পরবর্তীকালে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ তার চেয়েও বিস্তৃতভাবে সেটিকে ব্যবহার করেন। ১৯৮৬ সালের নির্বাচনকে ‘সামরিক শাসকের গণতান্ত্রিক মুখোশ’ হিসেবে অনেকেই আখ্যায়িত করেন। বিরোধী দলগুলোর একটি অংশ, বিশেষ করে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিলেও বিএনপি তা বর্জন করে। ভোটের দিন প্রশাসনের কঠোর নিয়ন্ত্রণ, বিরোধীদের হয়রানি এবং ফলাফল নিয়ে অনাস্থা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
এরশাদের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৮৮ সালের নির্বাচন ছিল আরও বিতর্কিত। বিএনপি ও আওয়ামী লীগ উভয়ই তাতে অংশ নেয়নি। ফলে ওই নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা দেশীয়-আন্তর্জাতিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়। ভোটার উপস্থিতি ছিল অস্বাভাবিকভাবে কম, অথচ ফলাফল দেখানো হয় বিপুল উৎসাহে। বলা হয়ে থাকে, সেই নির্বাচনই জনগণের মনে ‘ভোটহীন গণতন্ত্রের’ প্রতিচ্ছবি গেঁথে দেয়।
এই পটভূমিতেই ১৯৯০-এর গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে এরশাদের পতন ঘটে এবং আসে বহু প্রতীক্ষিত ১৯৯১ সালের নির্বাচন। এটি ছিল একটি নতুন আশার সূচনা। দেশের সব রাজনৈতিক দল অংশ নেয়, প্রশাসনে সেনাবাহিনীর সহায়তায় নির্বাচন হয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয় এ নির্বাচন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাটিও ধীরে ধীরে তখন আলোচনায় আসে, যদিও বাস্তবে রূপ নেয় ১৯৯৬ সালের আন্দোলনের পর।
১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারির নির্বাচন ছিল জটিল ও কলঙ্কিত অধ্যায়। বিএনপি সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েও নিরপেক্ষ সরকার গঠন না করায়, প্রধান বিরোধী দলগুলো ভোট বর্জন করে। সেই নির্বাচনের পর গঠিত সরকার ১২ দিনের মাথায় বিলুপ্ত হয় এবং এরশাদের আমলে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক অবিশ্বাসের ধারাটিই যেন ফের ফিরে আসে।
এরপর শুরু হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার অধীনে নির্বাচন। ১৯৯৬ (জুন), ২০০১ ও ২০০৮ সালের নির্বাচনগুলো এই ব্যবস্থার অধীনেই অনুষ্ঠিত হয় এবং তুলনামূলকভাবে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়। কিন্তু ২০১১ সালে আদালতের রায়ে এই ব্যবস্থা বাতিল হওয়ার পর আবার দেখা দেয় আস্থার সংকট।
২০১৪ সালের নির্বাচন সেই সংকটকে পূর্ণমাত্রায় উন্মোচিত করে। প্রধান বিরোধী দল বিএনপি নির্বাচন বর্জন করে, ১৫৩টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সহিংসতা, হরতাল, পেট্রলবোমা এবং মানুষের প্রাণহানি—এসব ঘটনা গণতন্ত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে।
২০১৮ সালের নির্বাচন ছিল সংখ্যার দিক থেকে অনেক বেশি ভোটার উপস্থিতি দেখানো, কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। অভিযোগ ওঠে, ভোট আগের রাতে হয়ে গেছে। বিরোধী দলের প্রার্থীরা ভোটকেন্দ্রেই ঢুকতে পারেননি, মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, পর্যবেক্ষকদের কাজ করতে বাধা দেওয়া হয়।
এই রকম নির্বাচনের পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, এমন ভোটের প্রয়োজন কী? আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারকেরা এমন একটি ভোটব্যবস্থা চালু করেন, যাতে ভোটার উপস্থিত হয়ে ভোট দেওয়াটা জরুরি নয়, জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল একতরফা ফলাফল ঘোষণা। আওয়ামী লীগের একচেটিয়া জয়। নির্বাচনের নামে এই প্রহসন অনেকের কাছেই মেনে নেওয়া কঠিন ছিল। কিন্তু সরকারের কঠোর মনোভাবের কারণে ওই নির্বাচনই বৈধ বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই অবস্থার জন্য কে দায়ী, সেটা এক লম্বা আলোচনার বিষয়। তবে এর দায় শুধু নির্বাচন কমিশনের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। নির্বাচন একটি সামষ্টিক রাষ্ট্রীয় প্রক্রিয়া, যেখানে রাজনৈতিক দল, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, প্রশাসন, নাগরিক সমাজ, মিডিয়া এবং সবচেয়ে বড় কথা—রাজনৈতিক সদিচ্ছা জরুরি। যখনই এই সদিচ্ছা হারিয়ে যায়, নির্বাচন শুধু ‘ঘোষণা’ হয়—আসলে ভোট হয় না।
গণতন্ত্র মানে কেবল একজন জনপ্রতিনিধি নির্বাচন নয়, বরং প্রত্যেক মানুষের মতপ্রকাশের অধিকার ও রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা। সেই সুযোগ তৈরি হয় সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে। অথচ আমরা নির্বাচনের কথা বললেও সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে বারবার ঘুরে দাঁড়াই সন্দেহের জগতে।
সুতরাং, আজ যদি আমরা সত্যিই গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে চাই, তবে সবার আগে দরকার আস্থা ফিরিয়ে আনা। এই আস্থা ফিরবে তখনই, যখন সরকার ও বিরোধী দল উভয়ই নিরপেক্ষ নির্বাচনে অংশগ্রহণে সম্মত হবে, প্রশাসনকে ব্যবহার করবে না, মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করবে না এবং জনগণের রায় মেনে নেওয়ার সংস্কৃতি গড়ে তুলবে।
এই বিশ্বাস ও আস্থার পরিবেশ গড়ার দায়িত্ব এককভাবে কারও নয়, তা আমাদের সবার—যারা এই রাষ্ট্রের অংশ, যারা এই রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবে। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে, আমাদের এখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে—আমরা কেমন নির্বাচন চাই?
শুধু নির্বাচন নয়, আমরা চাই এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে মানুষ ভোট দিতে গেলে ভয় পাবে না, সন্দেহ করবে না, বরং গর্ব নিয়ে বলবে—‘আমার ভোটেই গঠিত হয়েছে সরকার।’ সেই আত্মবিশ্বাসই হবে গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় বিজয়। আর এই বিজয়ের পথ তৈরি হয় শুধু তখনই, যখন নির্বাচন হয় সত্যিকার অর্থে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ।
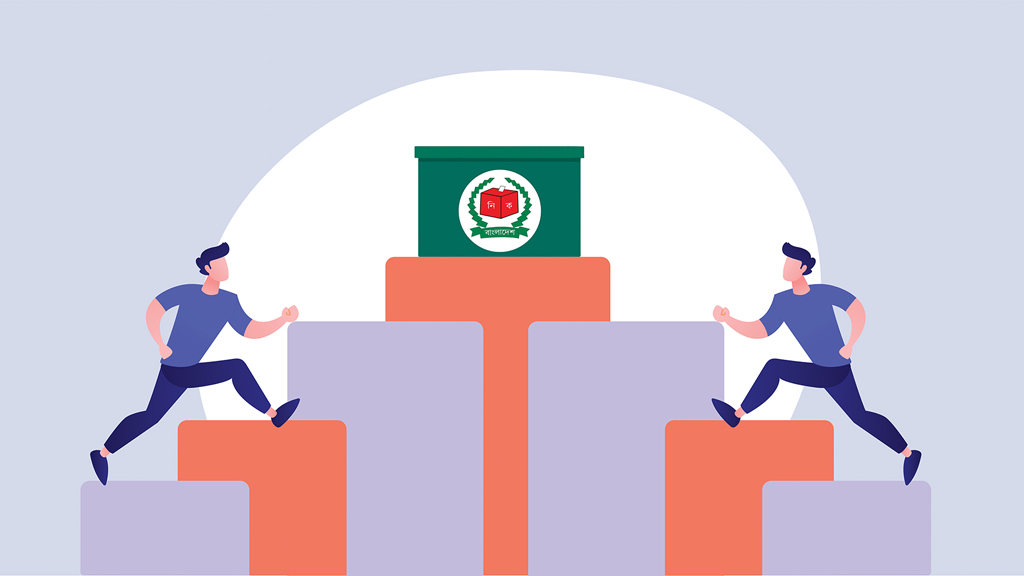
উইকিপিডিয়ায় নির্বাচনের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইভাবে: নির্বাচন হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের এমন একটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে জনগণ প্রশাসনিক কাজের জন্য একজন প্রতিনিধিকে বেছে নেয়। সপ্তদশ শতক থেকে আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে নির্বাচন একটি আবশ্যিক প্রক্রিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে আজকের দিনে নির্বাচন শব্দটি শুধু একটি দিনে ভোট দেওয়ার আনুষ্ঠানিকতার নাম নয়; এটি একটি জাতির গণতান্ত্রিক যাত্রার মৌলিক ভিত্তি। জনগণ তাদের প্রতিনিধিকে নির্বাচনের মাধ্যমে বেছে নেয়, নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও ভবিষ্যতের দায়িত্ব তুলে দেয় একদল মানুষের হাতে। তাই নির্বাচন মানেই গণতন্ত্রের প্রাণ। অবশ্য শুধু নির্বাচন হলেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় না, প্রয়োজন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন—যেখানে প্রতিটি ভোটারের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকে, প্রতিটি ভোট গণ্য হয় সমান গুরুত্বে এবং জনগণের রায়ই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আবেগ, হতাশা, অভিযোগ আর প্রত্যাশা—সবকিছু একসঙ্গে চলে আসে। কিন্তু আমাদের দেশে নির্বাচন একটি রাজনৈতিক কর্মসূচির বদলে হয়ে উঠেছে বিরোধ, সংঘাত এবং সন্দেহের কেন্দ্রবিন্দু। প্রতিটি জাতীয় নির্বাচনের আগে জনমনে প্রশ্ন জাগে, এইবার কি সত্যিই সুষ্ঠু নির্বাচন হবে?
এই প্রশ্নের উৎপত্তি ইতিহাস থেকে। ১৯৭০ সালের নির্বাচন, যা ছিল পূর্ব পাকিস্তান তথা গোটা পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম ও একমাত্র প্রায়-নিরপেক্ষ নির্বাচন, আমাদের আত্মপরিচয়ের বীজ বপন করেছিল। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও কেন্দ্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর না হওয়ায় দেখা দেয় বড় ধরনের রাজনৈতিক সংকট, শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ৯ মাসের যুদ্ধ শেষে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়।
১৯৭৩ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে। বিপুল বিজয়ে তারা ক্ষমতায় আসে, তাই বিরোধী দল বলতে তেমন কিছু ছিল না। একদলীয় শাসনের অভিপ্রায় তখনো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, কিন্তু ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক নাটকীয়তা সে পথই উন্মোচন করে দেয়।
এরপর আসে একটি অস্থির ও রক্তাক্ত সময়। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা পায়। ১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রপতি পদে জিয়াউর রহমান গণভোটের আয়োজন করেন, যার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে শুরু থেকেই প্রশ্ন ছিল। ১৯৭৮ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং ১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও ছিল সেনাবাহিনীর ছায়া, প্রশাসনের শক্ত ভূমিকা এবং ক্ষমতা ধরে রাখার কৌশল।
জিয়াউর রহমানের সময়টায় নির্বাচনী ব্যবস্থায় যে ‘নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের’ ধারা তৈরি হয়েছিল, পরবর্তীকালে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ তার চেয়েও বিস্তৃতভাবে সেটিকে ব্যবহার করেন। ১৯৮৬ সালের নির্বাচনকে ‘সামরিক শাসকের গণতান্ত্রিক মুখোশ’ হিসেবে অনেকেই আখ্যায়িত করেন। বিরোধী দলগুলোর একটি অংশ, বিশেষ করে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিলেও বিএনপি তা বর্জন করে। ভোটের দিন প্রশাসনের কঠোর নিয়ন্ত্রণ, বিরোধীদের হয়রানি এবং ফলাফল নিয়ে অনাস্থা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
এরশাদের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৮৮ সালের নির্বাচন ছিল আরও বিতর্কিত। বিএনপি ও আওয়ামী লীগ উভয়ই তাতে অংশ নেয়নি। ফলে ওই নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা দেশীয়-আন্তর্জাতিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়। ভোটার উপস্থিতি ছিল অস্বাভাবিকভাবে কম, অথচ ফলাফল দেখানো হয় বিপুল উৎসাহে। বলা হয়ে থাকে, সেই নির্বাচনই জনগণের মনে ‘ভোটহীন গণতন্ত্রের’ প্রতিচ্ছবি গেঁথে দেয়।
এই পটভূমিতেই ১৯৯০-এর গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে এরশাদের পতন ঘটে এবং আসে বহু প্রতীক্ষিত ১৯৯১ সালের নির্বাচন। এটি ছিল একটি নতুন আশার সূচনা। দেশের সব রাজনৈতিক দল অংশ নেয়, প্রশাসনে সেনাবাহিনীর সহায়তায় নির্বাচন হয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয় এ নির্বাচন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাটিও ধীরে ধীরে তখন আলোচনায় আসে, যদিও বাস্তবে রূপ নেয় ১৯৯৬ সালের আন্দোলনের পর।
১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারির নির্বাচন ছিল জটিল ও কলঙ্কিত অধ্যায়। বিএনপি সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েও নিরপেক্ষ সরকার গঠন না করায়, প্রধান বিরোধী দলগুলো ভোট বর্জন করে। সেই নির্বাচনের পর গঠিত সরকার ১২ দিনের মাথায় বিলুপ্ত হয় এবং এরশাদের আমলে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক অবিশ্বাসের ধারাটিই যেন ফের ফিরে আসে।
এরপর শুরু হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার অধীনে নির্বাচন। ১৯৯৬ (জুন), ২০০১ ও ২০০৮ সালের নির্বাচনগুলো এই ব্যবস্থার অধীনেই অনুষ্ঠিত হয় এবং তুলনামূলকভাবে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়। কিন্তু ২০১১ সালে আদালতের রায়ে এই ব্যবস্থা বাতিল হওয়ার পর আবার দেখা দেয় আস্থার সংকট।
২০১৪ সালের নির্বাচন সেই সংকটকে পূর্ণমাত্রায় উন্মোচিত করে। প্রধান বিরোধী দল বিএনপি নির্বাচন বর্জন করে, ১৫৩টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সহিংসতা, হরতাল, পেট্রলবোমা এবং মানুষের প্রাণহানি—এসব ঘটনা গণতন্ত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে।
২০১৮ সালের নির্বাচন ছিল সংখ্যার দিক থেকে অনেক বেশি ভোটার উপস্থিতি দেখানো, কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। অভিযোগ ওঠে, ভোট আগের রাতে হয়ে গেছে। বিরোধী দলের প্রার্থীরা ভোটকেন্দ্রেই ঢুকতে পারেননি, মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, পর্যবেক্ষকদের কাজ করতে বাধা দেওয়া হয়।
এই রকম নির্বাচনের পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, এমন ভোটের প্রয়োজন কী? আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারকেরা এমন একটি ভোটব্যবস্থা চালু করেন, যাতে ভোটার উপস্থিত হয়ে ভোট দেওয়াটা জরুরি নয়, জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল একতরফা ফলাফল ঘোষণা। আওয়ামী লীগের একচেটিয়া জয়। নির্বাচনের নামে এই প্রহসন অনেকের কাছেই মেনে নেওয়া কঠিন ছিল। কিন্তু সরকারের কঠোর মনোভাবের কারণে ওই নির্বাচনই বৈধ বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই অবস্থার জন্য কে দায়ী, সেটা এক লম্বা আলোচনার বিষয়। তবে এর দায় শুধু নির্বাচন কমিশনের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। নির্বাচন একটি সামষ্টিক রাষ্ট্রীয় প্রক্রিয়া, যেখানে রাজনৈতিক দল, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, প্রশাসন, নাগরিক সমাজ, মিডিয়া এবং সবচেয়ে বড় কথা—রাজনৈতিক সদিচ্ছা জরুরি। যখনই এই সদিচ্ছা হারিয়ে যায়, নির্বাচন শুধু ‘ঘোষণা’ হয়—আসলে ভোট হয় না।
গণতন্ত্র মানে কেবল একজন জনপ্রতিনিধি নির্বাচন নয়, বরং প্রত্যেক মানুষের মতপ্রকাশের অধিকার ও রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা। সেই সুযোগ তৈরি হয় সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে। অথচ আমরা নির্বাচনের কথা বললেও সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে বারবার ঘুরে দাঁড়াই সন্দেহের জগতে।
সুতরাং, আজ যদি আমরা সত্যিই গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে চাই, তবে সবার আগে দরকার আস্থা ফিরিয়ে আনা। এই আস্থা ফিরবে তখনই, যখন সরকার ও বিরোধী দল উভয়ই নিরপেক্ষ নির্বাচনে অংশগ্রহণে সম্মত হবে, প্রশাসনকে ব্যবহার করবে না, মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করবে না এবং জনগণের রায় মেনে নেওয়ার সংস্কৃতি গড়ে তুলবে।
এই বিশ্বাস ও আস্থার পরিবেশ গড়ার দায়িত্ব এককভাবে কারও নয়, তা আমাদের সবার—যারা এই রাষ্ট্রের অংশ, যারা এই রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবে। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে, আমাদের এখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে—আমরা কেমন নির্বাচন চাই?
শুধু নির্বাচন নয়, আমরা চাই এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে মানুষ ভোট দিতে গেলে ভয় পাবে না, সন্দেহ করবে না, বরং গর্ব নিয়ে বলবে—‘আমার ভোটেই গঠিত হয়েছে সরকার।’ সেই আত্মবিশ্বাসই হবে গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় বিজয়। আর এই বিজয়ের পথ তৈরি হয় শুধু তখনই, যখন নির্বাচন হয় সত্যিকার অর্থে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ।

ছোট ছিলাম যখন, তখন শোনা কথাগুলোকে অমূল্য মনে হতো। বুঝে না-বুঝে প্রচলিত কথাগুলোকেই বিশ্বাস করতাম। বয়স বাড়তে লাগল, বুঝতে পারলাম, জীবনে এমন অনেক কিছুই আছে, যা আদর্শবাদের সঙ্গে যায় না। বাস্তব একেবারে অন্য কিছু।
১৮ ঘণ্টা আগে
এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল বেশ খারাপ। বলা যায়, সন্তোষজনক নয়। যদিও পরীক্ষার ফল যে ভালো হবে, পাসের হার বেশি হবে, তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য কারণ বা উদ্যোগ কিন্তু ছিল না। বরাবরের মতো গত নয়-দশ মাসে তেমন কোনো উদ্যোগ, তৎপরতা চোখে পড়েনি।
১৮ ঘণ্টা আগে
গরিব ও দরিদ্র মানুষদের জন্য সরকারি বরাদ্দকৃত ভিজিডি কার্ড (পরিবর্তিত নাম ভিডব্লিউবি) বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। আজকের পত্রিকায় ২১ অক্টোবর সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে।
১৯ ঘণ্টা আগে
হাত-পা বেঁধে ইচ্ছেমতো পিটিয়েছে স্থানীয় লোকজন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সেই ছিনতাইকারীর। সেখানে ঘটনা থেমে থাকেনি, লোকটির শরীরে লবণ দিয়ে উল্লাস করতে থাকে জনতা। টঙ্গীর স্টেশন রোড এলাকায় প্রতিদিন গড়ে ২০টি করে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। এটা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভয়াবহ অবস্থারই ইঙ্গিত দেয়।
২ দিন আগেজাহীদ রেজা নূর

ছোট ছিলাম যখন, তখন শোনা কথাগুলোকে অমূল্য মনে হতো। বুঝে না-বুঝে প্রচলিত কথাগুলোকেই বিশ্বাস করতাম। বয়স বাড়তে লাগল, বুঝতে পারলাম, জীবনে এমন অনেক কিছুই আছে, যা আদর্শবাদের সঙ্গে যায় না। বাস্তব একেবারে অন্য কিছু।
গত শতকের গোটা সময়টায় দুনিয়াজুড়ে সাম্যবাদের দিকে ঝুঁকেছিল প্রগতিবাদী মানুষ। উপনিবেশের শৃঙ্খল ভেঙে এশিয়া-আফ্রিকায় জন্ম হচ্ছিল নতুন নতুন দেশ। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিজয় আশার আলো জাগিয়েছিল শোষিত মানুষের মনে। সারা বিশ্বে বিপ্লব ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য চে গেভারা ঘুরে বেড়িয়েছেন বিভিন্ন দেশে, উদ্বুদ্ধ করেছেন লাঞ্ছিত-বঞ্চিত মানুষকে। পৃথিবীর মেধাবী মানুষেরা সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। বিশেষ করে তরুণেরা ত্যাগ ও সংগ্রামকেই বেছে নিয়েছে জীবনের পথ হিসেবে। পুঁজিবাদ এই ভেঙে পড়ল বলে মনে হয়েছে।
কিন্তু আদৌ সে রকম কিছু ঘটেনি। নানা ধরনের অসংগতি নিয়ে পুঁজিবাদ টিকে আছে। সমাজতন্ত্রের দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেছে। চীনের শাসনব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক নাকি আধা-খ্যাঁচড়া পুঁজিবাদী কিছু—তা নিয়ে বিতর্ক এখনো চলছে। দেশে দেশে হানাহানি, নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য যেকোনো পথ অবলম্বন করা, অন্যকে নিজের আয়ত্তে রাখার চেষ্টা করেই চলেছে পুঁজিবাদ।
২. আলোচনাটা তাত্ত্বিক আলোচনায় পরিণত হওয়ার আগেই থামা দরকার। যখন সমাজতান্ত্রিক জীবনের প্রতি মোহ ও মায়ায় আকৃষ্ট হয়েছে মানুষ, তখন তারা ভেবেও দেখেনি, তত্ত্ব থাকলেই তা রাষ্ট্রীয় জীবনে সুচারুভাবে প্রয়োগ করা যায় না। মানুষের সমাজে নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতে থাকে, তার সমাধানের জন্য তত্ত্বের বাইরেও চলে যান রাষ্ট্রের কর্তারা। তাঁরা নিজের তৈরি আইনে তখন দেশ চালান।
দেশে দেশে একনায়কতন্ত্র বা স্বৈরাচার এভাবেই দাঁড়িয়ে যায়। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নেও গড়ে উঠেছিল পার্টি-আমলাতন্ত্র, যা আদর্শকে বিলীন করে দিয়ে নিজস্ব এক কঠোর ও নির্যাতনবাদী সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। কমিউনিস্ট পার্টি আর জনগণের মধ্যে যখন বিস্তর ফারাক সৃষ্টি হলো, পার্টি ক্রমেই তার গোপন গোয়েন্দা বাহিনী দিয়ে জনগণের ওপর নজরদারি শুরু করল, পার্টির মতামতের বাইরে অন্য কোনো মতকে কঠোর হাতে দমন করা শুরু করল, বিরুদ্ধমতের মানুষকে নির্বাসনে পাঠাতে লাগল, দেশত্যাগে বাধ্য করতে থাকল কিংবা শারীরিকভাবে নিশ্চিহ্ন করতে শুরু করল, তখন বোঝা গেল সমাজতন্ত্রের স্বপ্নকে সমাজতান্ত্রিক মনীষীরাই ভয়ংকরভাবে বিপথে নিয়ে যেতে পারেন। সেই সঙ্গে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ইন্ধন তো আছেই। কিন্তু ভেতরটা নষ্ট হওয়ার জন্য প্রস্তুত না থাকলে কোনো দেশকে অন্য কোনো দেশ এসে ধ্বংস করে দিতে পারে না।
সোভিয়েত ইউনিয়নে ১০ বছর ছিলাম। ৫ বছর ছিলাম গরবাচোভের পিরিস্ত্রোইকার আমলে, বাকি পাঁচ বছর ইয়েলৎসিনের গণতন্ত্রে। ইয়েলৎসিনের গণতন্ত্র ছিল এক কিম্ভূতকিমাকার ব্যবস্থা। চোখের নিমেষে বড় বড় মোড়লকে কোটিপতি হয়ে যেতে দেখেছি। এদের বেশির ভাগই একসময় সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বড় বড় চাঁই ছিল। সারা দেশে মাফিয়া ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হলে স্থানীয় মাফিয়াদের টাকা দিয়ে পালতে হতো। কিশোর গ্যাংয়ের জন্ম হতে থাকল প্রতিটি শহরেই। হঠাৎ করে নিষিদ্ধ পশ্চিমা সংস্কৃতির অবাধ প্রবেশ ঘটতে লাগল। তাতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বদহজম হতে থাকল। সে এক আজব সময় পার করেছে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নবাসী।
প্রশ্ন হলো, গত শতকের নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যে দেশগুলো বের হলো, সে দেশগুলোয় কি গণতন্ত্র আদৌ জায়গা করে নিতে পেরেছে? কেন পারেনি, তার কারণগুলোও খতিয়ে দেখা দরকার।
৩. যে আমলাতন্ত্র গড়ে উঠেছিল সোভিয়েত দেশটিতে, তাতে পার্টির নামে যথেচ্ছাচার চলত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাশিয়া সফরে গিয়ে এই প্রশ্নটিই তুলেছিলেন। ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে শুধু সমষ্টি দিয়ে কিছু গড়ে তোলা যায় কি না, অর্থাৎ সম্মিলিত নেতৃত্ব টিকতে পারে কি না, সে প্রশ্নই তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ব্যক্তি যদি বিকশিত না হয়, সমষ্টিই যদি চলার পথের অনুপ্রেরণা হয়, তাহলে ভিন্নমত, বহুমত টিকবে কী করে? আসলেই টেকেনি। কারণ, বহুমতকে প্রবলভাবে হত্যা করে একটিমাত্র মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট নেতারা। মুখে বলেছেন সম্মিলিত নেতৃত্ব, কিন্তু দাঁড় করিয়েছেন পার্টি-স্বৈরাচার। দেয়ালেরও কান আছে—এই কথায় বিশ্বাস ছিল সোভিয়েত জনগণের।
বিতর্কটি আগামী দিনের জন্য তোলা থাকল। বিশ্বের সবচেয়ে প্রগতিশীল একটি মতবাদ কী কারণে এক শ বছর পার হওয়ার আগেই মুখ থুবড়ে পড়ল, তা নিয়ে বহু তাত্ত্বিক আলোচনা আছে। সে আলোচনাগুলোর কোনো কোনোটায় সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের জন্য শুধু বাইরের শক্তির ষড়যন্ত্রকেই দেখা হয়। আমাদের দেশের মনীষীদের মধ্যেও এ রকম ঝোঁক দেখতে পাই। কিন্তু কী করে ভেতরের সংকটটা ভাঙনকে ত্বরান্বিত করেছে এবং সেটাই হয়ে উঠেছে ভাঙনের মূল কারণ—সে কথা বুঝতে হলে সে সময়ের সোভিয়েত ইউনিয়নে বসবাসকারী মানুষের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা জরুরি। সে কাজটাই ক্রমান্বয়ে করা হবে।
৪. আমাদের দেশের তরুণেরাও শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার জন্য জীবনপণ করেছিল। শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীব্যাপী প্রগতিশীল মানুষ বলতে মার্ক্স-এঙ্গেলস-লেনিন-মাও-পড়া মানুষদেরকেই বোঝাত। আক্ষরিক অর্থেই এই মানুষেরা বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিয়ে শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের অঙ্গীকার করেছিলেন। নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা ধীরে ধীরে সংকট মোকাবিলায় নিজস্ব-সৃষ্ট তত্ত্বকে প্রাধান্য দিতে থাকায় মূল আদর্শের জায়গায় যে বিচ্যুতি ঘটেছিল, প্রাথমিকভাবে তা কর্মীদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। সামনে শোষণহীন সমাজের অপার সম্ভাবনা, ফলে ছোটখাটো ভুলত্রুটিকে আমলে না নেওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছিল। এই এড়িয়ে যাওয়াটাই কাল হয়ে উঠেছিল। মানুষ প্রশ্ন করতে ভুলে গিয়েছিল এবং একসময় প্রশ্ন করাকেই ভয়াবহ অপরাধ বলে গণ্য করা শুরু হলো।
সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি শহরে যখন পড়াশোনা করছি, তখন পিরিস্ত্রোইকা আর গ্লাসনোস্ত এসে কাঁপিয়ে দিয়েছে সোভিয়েত সমাজকে। হঠাৎ করে এতটা মুক্তির আস্বাদ পাওয়া ছিল বিরল ঘটনা। মানুষ যখন মুখ খুলতে শুরু করেছে, তখন আর কিছুই ঠেকিয়ে রাখা যায়নি। সমাজে প্রচলিত সব অসংগতি নিয়ে যেমন মানুষ কথা বলেছে, তেমনি কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি যে রাগ, অভিমান ছিল, সেটাও ধীরে ধীরে প্রকাশ করেছে। পার্টির ভেতরেই ভিন্ন ভিন্ন মত জেগে উঠেছে। এই বিপুল পরিবর্তন মোকাবিলা করার মতো ক্ষমতা গরবাচোভের ছিল না। আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ তত দিনে পশ্চিমা দুনিয়ার নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে।
কিন্তু কী করে এই ভাঙনটি এল? সেটাই তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে আলোচনার চেষ্টা করব।
তৃতীয় বর্ষে পড়ার সময় রুশ সাহিত্যের ইতিহাস ক্লাসে ছিলেন এক তরুণ শিক্ষক। তিনি বললেন, বিখ্যাত সোভিয়েত সাহিত্যিক কনস্তান্তিন সিমোনভকে একবার এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন, ‘আপনি এখন কী লিখছেন?’ সিমোনভ উত্তর দিয়েছিলেন, ‘এখনো ঠিক করিনি। পার্টি যে নির্দেশ দেবে, সেটাই লিখব।’
তখন গ্লাসনোস্তের কাল। তাই শিক্ষক এই কথাটি বলতে পেরেছিলেন। একজন সৃজনশীল মানুষ কী লিখবে, সেটাও নির্ভর করছে পার্টির সিদ্ধান্তের ওপর—এই কথাটি কিসের ইঙ্গিত দেয়, তা নিয়েও কথা বলব। আজকের নাতিদীর্ঘ লেখাটি শেষ করি ওই সোভিয়েতজীবনের একটি ঘটনা দিয়েই। তখন সদ্য সে দেশে গেছি। অন্য একটি শহর থেকে আমাদেরই এক বন্ধু ছুটিতে বেড়াতে এসেছে। কথা প্রসঙ্গে ও বলছিল, এখনো প্রেমের সিদ্ধান্ত নেয়নি। এ ব্যাপারে ও নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। পার্টি যে সিদ্ধান্ত দেবে, সেটাই সে মেনে নেবে।
ঘটনাটি সত্য। পার্টির প্রতি আনুগত্য ব্যক্তিজীবনকেও ধ্বংস করে দিচ্ছিল, এ কথা তখন অনেকেই বোঝেনি। আর তখনই মনে পড়েছে মেকিয়াভেলির কথা। রাষ্ট্রের ‘নিরাপত্তা’ ও ‘স্থিতিশীলতা’ রক্ষার জন্য শাসককে যেকোনো উপায় অবলম্বন করতে হবে, তা নৈতিক বা অনৈতিক যা-ই হোক না কেন। মেকিয়াভেলি মনে করেন মানুষ স্বার্থপর, ভিতু ও অবিশ্বাসী। তাই শাসককে মানুষের এই প্রকৃতি বুঝে কাজ করতে হবে। পৃথিবীজুড়েই কি এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে না?
আমি কি সমাজতন্ত্র নিয়ে নিরাশার কথা বলছি? একেবারেই না। কেন তা নিরাশার জন্ম দিল, সে কারণগুলো খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছি মাত্র। আর তা বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যাবে, আমাদের দেশের স্বপ্নগুলোও কেন ভাঙতে থাকে, তার ইঙ্গিতও আমরা পেয়ে যাব।
লেখক: উপসম্পাদক, আজকের পত্রিকা

ছোট ছিলাম যখন, তখন শোনা কথাগুলোকে অমূল্য মনে হতো। বুঝে না-বুঝে প্রচলিত কথাগুলোকেই বিশ্বাস করতাম। বয়স বাড়তে লাগল, বুঝতে পারলাম, জীবনে এমন অনেক কিছুই আছে, যা আদর্শবাদের সঙ্গে যায় না। বাস্তব একেবারে অন্য কিছু।
গত শতকের গোটা সময়টায় দুনিয়াজুড়ে সাম্যবাদের দিকে ঝুঁকেছিল প্রগতিবাদী মানুষ। উপনিবেশের শৃঙ্খল ভেঙে এশিয়া-আফ্রিকায় জন্ম হচ্ছিল নতুন নতুন দেশ। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিজয় আশার আলো জাগিয়েছিল শোষিত মানুষের মনে। সারা বিশ্বে বিপ্লব ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য চে গেভারা ঘুরে বেড়িয়েছেন বিভিন্ন দেশে, উদ্বুদ্ধ করেছেন লাঞ্ছিত-বঞ্চিত মানুষকে। পৃথিবীর মেধাবী মানুষেরা সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। বিশেষ করে তরুণেরা ত্যাগ ও সংগ্রামকেই বেছে নিয়েছে জীবনের পথ হিসেবে। পুঁজিবাদ এই ভেঙে পড়ল বলে মনে হয়েছে।
কিন্তু আদৌ সে রকম কিছু ঘটেনি। নানা ধরনের অসংগতি নিয়ে পুঁজিবাদ টিকে আছে। সমাজতন্ত্রের দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেছে। চীনের শাসনব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক নাকি আধা-খ্যাঁচড়া পুঁজিবাদী কিছু—তা নিয়ে বিতর্ক এখনো চলছে। দেশে দেশে হানাহানি, নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য যেকোনো পথ অবলম্বন করা, অন্যকে নিজের আয়ত্তে রাখার চেষ্টা করেই চলেছে পুঁজিবাদ।
২. আলোচনাটা তাত্ত্বিক আলোচনায় পরিণত হওয়ার আগেই থামা দরকার। যখন সমাজতান্ত্রিক জীবনের প্রতি মোহ ও মায়ায় আকৃষ্ট হয়েছে মানুষ, তখন তারা ভেবেও দেখেনি, তত্ত্ব থাকলেই তা রাষ্ট্রীয় জীবনে সুচারুভাবে প্রয়োগ করা যায় না। মানুষের সমাজে নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতে থাকে, তার সমাধানের জন্য তত্ত্বের বাইরেও চলে যান রাষ্ট্রের কর্তারা। তাঁরা নিজের তৈরি আইনে তখন দেশ চালান।
দেশে দেশে একনায়কতন্ত্র বা স্বৈরাচার এভাবেই দাঁড়িয়ে যায়। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নেও গড়ে উঠেছিল পার্টি-আমলাতন্ত্র, যা আদর্শকে বিলীন করে দিয়ে নিজস্ব এক কঠোর ও নির্যাতনবাদী সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। কমিউনিস্ট পার্টি আর জনগণের মধ্যে যখন বিস্তর ফারাক সৃষ্টি হলো, পার্টি ক্রমেই তার গোপন গোয়েন্দা বাহিনী দিয়ে জনগণের ওপর নজরদারি শুরু করল, পার্টির মতামতের বাইরে অন্য কোনো মতকে কঠোর হাতে দমন করা শুরু করল, বিরুদ্ধমতের মানুষকে নির্বাসনে পাঠাতে লাগল, দেশত্যাগে বাধ্য করতে থাকল কিংবা শারীরিকভাবে নিশ্চিহ্ন করতে শুরু করল, তখন বোঝা গেল সমাজতন্ত্রের স্বপ্নকে সমাজতান্ত্রিক মনীষীরাই ভয়ংকরভাবে বিপথে নিয়ে যেতে পারেন। সেই সঙ্গে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ইন্ধন তো আছেই। কিন্তু ভেতরটা নষ্ট হওয়ার জন্য প্রস্তুত না থাকলে কোনো দেশকে অন্য কোনো দেশ এসে ধ্বংস করে দিতে পারে না।
সোভিয়েত ইউনিয়নে ১০ বছর ছিলাম। ৫ বছর ছিলাম গরবাচোভের পিরিস্ত্রোইকার আমলে, বাকি পাঁচ বছর ইয়েলৎসিনের গণতন্ত্রে। ইয়েলৎসিনের গণতন্ত্র ছিল এক কিম্ভূতকিমাকার ব্যবস্থা। চোখের নিমেষে বড় বড় মোড়লকে কোটিপতি হয়ে যেতে দেখেছি। এদের বেশির ভাগই একসময় সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বড় বড় চাঁই ছিল। সারা দেশে মাফিয়া ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হলে স্থানীয় মাফিয়াদের টাকা দিয়ে পালতে হতো। কিশোর গ্যাংয়ের জন্ম হতে থাকল প্রতিটি শহরেই। হঠাৎ করে নিষিদ্ধ পশ্চিমা সংস্কৃতির অবাধ প্রবেশ ঘটতে লাগল। তাতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বদহজম হতে থাকল। সে এক আজব সময় পার করেছে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নবাসী।
প্রশ্ন হলো, গত শতকের নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যে দেশগুলো বের হলো, সে দেশগুলোয় কি গণতন্ত্র আদৌ জায়গা করে নিতে পেরেছে? কেন পারেনি, তার কারণগুলোও খতিয়ে দেখা দরকার।
৩. যে আমলাতন্ত্র গড়ে উঠেছিল সোভিয়েত দেশটিতে, তাতে পার্টির নামে যথেচ্ছাচার চলত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাশিয়া সফরে গিয়ে এই প্রশ্নটিই তুলেছিলেন। ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে শুধু সমষ্টি দিয়ে কিছু গড়ে তোলা যায় কি না, অর্থাৎ সম্মিলিত নেতৃত্ব টিকতে পারে কি না, সে প্রশ্নই তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ব্যক্তি যদি বিকশিত না হয়, সমষ্টিই যদি চলার পথের অনুপ্রেরণা হয়, তাহলে ভিন্নমত, বহুমত টিকবে কী করে? আসলেই টেকেনি। কারণ, বহুমতকে প্রবলভাবে হত্যা করে একটিমাত্র মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট নেতারা। মুখে বলেছেন সম্মিলিত নেতৃত্ব, কিন্তু দাঁড় করিয়েছেন পার্টি-স্বৈরাচার। দেয়ালেরও কান আছে—এই কথায় বিশ্বাস ছিল সোভিয়েত জনগণের।
বিতর্কটি আগামী দিনের জন্য তোলা থাকল। বিশ্বের সবচেয়ে প্রগতিশীল একটি মতবাদ কী কারণে এক শ বছর পার হওয়ার আগেই মুখ থুবড়ে পড়ল, তা নিয়ে বহু তাত্ত্বিক আলোচনা আছে। সে আলোচনাগুলোর কোনো কোনোটায় সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের জন্য শুধু বাইরের শক্তির ষড়যন্ত্রকেই দেখা হয়। আমাদের দেশের মনীষীদের মধ্যেও এ রকম ঝোঁক দেখতে পাই। কিন্তু কী করে ভেতরের সংকটটা ভাঙনকে ত্বরান্বিত করেছে এবং সেটাই হয়ে উঠেছে ভাঙনের মূল কারণ—সে কথা বুঝতে হলে সে সময়ের সোভিয়েত ইউনিয়নে বসবাসকারী মানুষের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা জরুরি। সে কাজটাই ক্রমান্বয়ে করা হবে।
৪. আমাদের দেশের তরুণেরাও শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার জন্য জীবনপণ করেছিল। শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীব্যাপী প্রগতিশীল মানুষ বলতে মার্ক্স-এঙ্গেলস-লেনিন-মাও-পড়া মানুষদেরকেই বোঝাত। আক্ষরিক অর্থেই এই মানুষেরা বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিয়ে শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের অঙ্গীকার করেছিলেন। নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা ধীরে ধীরে সংকট মোকাবিলায় নিজস্ব-সৃষ্ট তত্ত্বকে প্রাধান্য দিতে থাকায় মূল আদর্শের জায়গায় যে বিচ্যুতি ঘটেছিল, প্রাথমিকভাবে তা কর্মীদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। সামনে শোষণহীন সমাজের অপার সম্ভাবনা, ফলে ছোটখাটো ভুলত্রুটিকে আমলে না নেওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছিল। এই এড়িয়ে যাওয়াটাই কাল হয়ে উঠেছিল। মানুষ প্রশ্ন করতে ভুলে গিয়েছিল এবং একসময় প্রশ্ন করাকেই ভয়াবহ অপরাধ বলে গণ্য করা শুরু হলো।
সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি শহরে যখন পড়াশোনা করছি, তখন পিরিস্ত্রোইকা আর গ্লাসনোস্ত এসে কাঁপিয়ে দিয়েছে সোভিয়েত সমাজকে। হঠাৎ করে এতটা মুক্তির আস্বাদ পাওয়া ছিল বিরল ঘটনা। মানুষ যখন মুখ খুলতে শুরু করেছে, তখন আর কিছুই ঠেকিয়ে রাখা যায়নি। সমাজে প্রচলিত সব অসংগতি নিয়ে যেমন মানুষ কথা বলেছে, তেমনি কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি যে রাগ, অভিমান ছিল, সেটাও ধীরে ধীরে প্রকাশ করেছে। পার্টির ভেতরেই ভিন্ন ভিন্ন মত জেগে উঠেছে। এই বিপুল পরিবর্তন মোকাবিলা করার মতো ক্ষমতা গরবাচোভের ছিল না। আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ তত দিনে পশ্চিমা দুনিয়ার নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে।
কিন্তু কী করে এই ভাঙনটি এল? সেটাই তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে আলোচনার চেষ্টা করব।
তৃতীয় বর্ষে পড়ার সময় রুশ সাহিত্যের ইতিহাস ক্লাসে ছিলেন এক তরুণ শিক্ষক। তিনি বললেন, বিখ্যাত সোভিয়েত সাহিত্যিক কনস্তান্তিন সিমোনভকে একবার এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন, ‘আপনি এখন কী লিখছেন?’ সিমোনভ উত্তর দিয়েছিলেন, ‘এখনো ঠিক করিনি। পার্টি যে নির্দেশ দেবে, সেটাই লিখব।’
তখন গ্লাসনোস্তের কাল। তাই শিক্ষক এই কথাটি বলতে পেরেছিলেন। একজন সৃজনশীল মানুষ কী লিখবে, সেটাও নির্ভর করছে পার্টির সিদ্ধান্তের ওপর—এই কথাটি কিসের ইঙ্গিত দেয়, তা নিয়েও কথা বলব। আজকের নাতিদীর্ঘ লেখাটি শেষ করি ওই সোভিয়েতজীবনের একটি ঘটনা দিয়েই। তখন সদ্য সে দেশে গেছি। অন্য একটি শহর থেকে আমাদেরই এক বন্ধু ছুটিতে বেড়াতে এসেছে। কথা প্রসঙ্গে ও বলছিল, এখনো প্রেমের সিদ্ধান্ত নেয়নি। এ ব্যাপারে ও নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। পার্টি যে সিদ্ধান্ত দেবে, সেটাই সে মেনে নেবে।
ঘটনাটি সত্য। পার্টির প্রতি আনুগত্য ব্যক্তিজীবনকেও ধ্বংস করে দিচ্ছিল, এ কথা তখন অনেকেই বোঝেনি। আর তখনই মনে পড়েছে মেকিয়াভেলির কথা। রাষ্ট্রের ‘নিরাপত্তা’ ও ‘স্থিতিশীলতা’ রক্ষার জন্য শাসককে যেকোনো উপায় অবলম্বন করতে হবে, তা নৈতিক বা অনৈতিক যা-ই হোক না কেন। মেকিয়াভেলি মনে করেন মানুষ স্বার্থপর, ভিতু ও অবিশ্বাসী। তাই শাসককে মানুষের এই প্রকৃতি বুঝে কাজ করতে হবে। পৃথিবীজুড়েই কি এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে না?
আমি কি সমাজতন্ত্র নিয়ে নিরাশার কথা বলছি? একেবারেই না। কেন তা নিরাশার জন্ম দিল, সে কারণগুলো খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছি মাত্র। আর তা বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যাবে, আমাদের দেশের স্বপ্নগুলোও কেন ভাঙতে থাকে, তার ইঙ্গিতও আমরা পেয়ে যাব।
লেখক: উপসম্পাদক, আজকের পত্রিকা
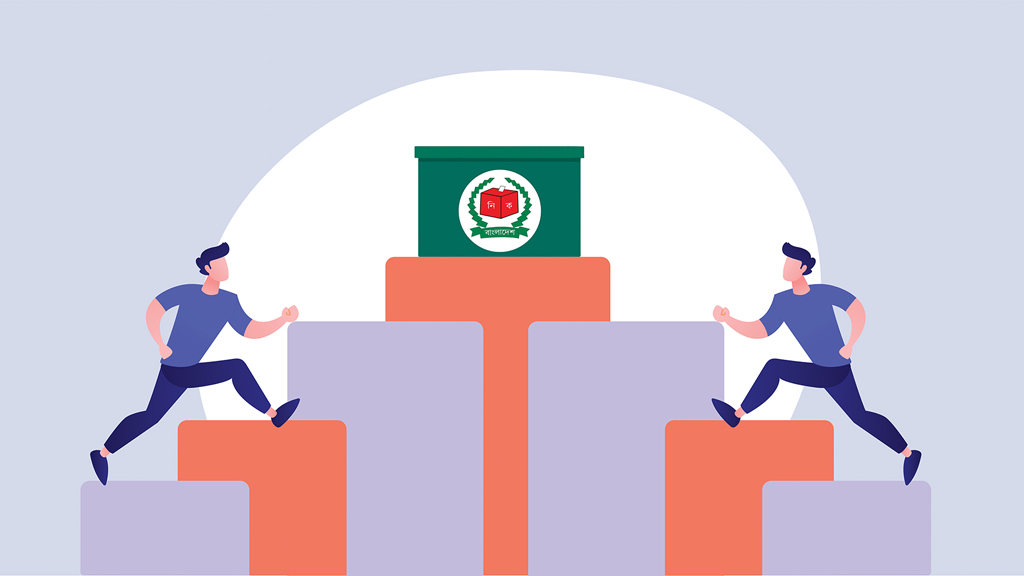
উইকিপিডিয়ায় নির্বাচনের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইভাবে: নির্বাচন হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের এমন একটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে জনগণ প্রশাসনিক কাজের জন্য একজন প্রতিনিধিকে বেছে নেয়। সপ্তদশ শতক থেকে আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে নির্বাচন একটি আবশ্যিক প্রক্রিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে।
২৬ জুলাই ২০২৫
এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল বেশ খারাপ। বলা যায়, সন্তোষজনক নয়। যদিও পরীক্ষার ফল যে ভালো হবে, পাসের হার বেশি হবে, তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য কারণ বা উদ্যোগ কিন্তু ছিল না। বরাবরের মতো গত নয়-দশ মাসে তেমন কোনো উদ্যোগ, তৎপরতা চোখে পড়েনি।
১৮ ঘণ্টা আগে
গরিব ও দরিদ্র মানুষদের জন্য সরকারি বরাদ্দকৃত ভিজিডি কার্ড (পরিবর্তিত নাম ভিডব্লিউবি) বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। আজকের পত্রিকায় ২১ অক্টোবর সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে।
১৯ ঘণ্টা আগে
হাত-পা বেঁধে ইচ্ছেমতো পিটিয়েছে স্থানীয় লোকজন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সেই ছিনতাইকারীর। সেখানে ঘটনা থেমে থাকেনি, লোকটির শরীরে লবণ দিয়ে উল্লাস করতে থাকে জনতা। টঙ্গীর স্টেশন রোড এলাকায় প্রতিদিন গড়ে ২০টি করে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। এটা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভয়াবহ অবস্থারই ইঙ্গিত দেয়।
২ দিন আগেস্বপ্না রেজা

এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল বেশ খারাপ। বলা যায়, সন্তোষজনক নয়। যদিও পরীক্ষার ফল যে ভালো হবে, পাসের হার বেশি হবে, তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য কারণ বা উদ্যোগ কিন্তু ছিল না। বরাবরের মতো গত নয়-দশ মাসে তেমন কোনো উদ্যোগ, তৎপরতা চোখে পড়েনি। রাষ্ট্র সংস্কার নিয়ে যত কথা উঠেছে, বৈষম্যের বিরুদ্ধে যত চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়েছে, অনিয়মের বিরুদ্ধে যত আওয়াজ উঠেছে, শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত মান বৃদ্ধি ও শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে তার ন্যূনতম আলাপ-আলোচনা হতে দেখা যায়নি। কারোর দৃষ্টি ও উৎসাহ এই বিষয়ে ছিল বলেও মনে হয়নি। দুঃখজনক হলেও বলতে হয় যে, রাষ্ট্র সংস্কারের চেতনায় শিক্ষাব্যবস্থাকে অচেতন অবস্থায় রাখা হয়েছে এবং সেটা বিগত সময়ের মতোই। এককথায়, আমাদের দেশে ক্ষমতাকেন্দ্রিক যাবতীয় কাজ, পরিকল্পনা, উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে উত্তম ও কার্যকর পদক্ষেপ কোনো রাজনৈতিক সরকারকেই নিতে দেখা যায়নি। যেটুকু নেওয়া হয়েছে তা অযোগ্য ও অদক্ষ ব্যক্তিদের নিয়োগ দিয়ে করা হয়েছে বলে অনেকের অভিযোগ। ফলে ভালো ফল পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব থেকেই গেছে। মেধাসম্পন্ন যোগ্য নাগরিক নয়, বরং রাজনৈতিক দল ও তার দলীয় চেতনায় দেশ গড়ার অন্যতম উপায় বলে প্রতিষ্ঠার হীন চেষ্টা চালানো হয়েছে সব সময়ই।
এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার পাসের হার ৫৮ দশমিক ৮৩ শতাংশ, যা গত ২০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ ফল বলে পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে জানা গেছে। সংবাদমাধ্যমে আরও জানা যায়, এই ফলকে শিক্ষার প্রকৃত চিত্র বলে উল্লেখ করেছেন স্বয়ং শিক্ষা উপদেষ্টা। এটা তাঁর কৃতিত্বের ঢেকুর কি না, নাকি সাধারণ জনগণের মতো হতাশার উক্তি, সেটা বলা মুশকিল। যদি কৃতিত্বের ঢেকুর এমন হয়, তাঁদের আমলে কড়াকড়ি তথা যথাযথভাবে পরীক্ষার উত্তরপত্র যাচাই করা হয়েছে, তাই পাসের হার কম হয়েছে এবং এটাই বাস্তবতা। তাহলে বলতেই হয় যে এটা নিঃসন্দেহে একটা খোঁড়া যুক্তি। যদি পাসের হার বেশি হতো তাহলে হয়তো এমন যুক্তি দেওয়া থেকে তিনি বিরত থাকতেন। উল্টো বলা হতো, যথাযথ ও উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার উত্তম ফলাফল। সব সরকারই যেভাবে কৃতিত্ব নিতে উৎসাহ বোধ করে থাকে, সে রকমই ব্যাপারটা এবারও ঘটেছে।
তবে সাধারণ জনগণ ভাবছে অন্য কথা। তারা বলছে, পরীক্ষায় পাস না করার কারণ হতে পারে উপযুক্ত শিক্ষা অর্জন ও প্রস্তুতি ছাড়াই শিক্ষার্থীরা এবার পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন। সোজাসুজি বললে দাঁড়ায়, শিক্ষার্থীরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে লেখাপড়া করেননি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাইরে থেকে গেছেন বেশ অনেক দিন। তরুণ, কিশোর, যুবকদের মধ্যে অন্য ধরনের তাড়না লক্ষ করা গেছে, যা শিক্ষাসংক্রান্ত নয়। বরং স্কুলের প্রধান শিক্ষককে লাঞ্ছিত করার ঘটনা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তিকে জুতার মালা পরিয়ে দেওয়ার মতো চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ দেখানো হয়েছে এই সময়ে। বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক ইস্যুতে শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যে ধরনের ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে, তা অনাকাঙ্ক্ষিত ও রাষ্ট্রের জন্য এক অশনিসংকেত। সরকার এই হীন কর্মকাণ্ডকে রোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে বলা যায়।
একজন প্রবীণ শিক্ষাবিদ দুঃখ করে বলছিলেন তাঁর সাম্প্রতিক সময়ের অভিজ্ঞতার কথা। যুবকদের নিয়ে আয়োজিত এক সেমিনারে তাঁকে সম্মানিত বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি যুবকদের মাঝে উপস্থিত হয়ে প্রথমেই জানতে চাইলেন, বক্তব্য দেওয়ার আগে জানতে চাই, তোমরা কয়জন নিয়মিত ক্লাসে যাচ্ছ, হাত তোলো? কিন্তু কারোর তোলা হাত তিনি দেখেননি। অবাক হন। জানতে চান, একটা হাতও না দেখার কারণ কী? তাদের কয়জন বেশ গাম্ভীর্য নিয়ে বলে, তারা এখন দেশ গড়ার কাজে ব্যস্ত। সংস্কারকাজে জড়িত। রাষ্ট্র সংস্কার হলে তারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফিরবে। প্রবীণ ভদ্রলোক ভেবে নিলেন, এই মুহূর্তে যুবকদের জ্ঞান দেওয়া বৃথা। বরং তারাই তাঁকে জ্ঞান দিতে বেশি আগ্রহী। এমন আয়োজনও নেহাত শোআপ। বর্তমানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যে অবস্থা, জাতীয় পর্যায়ে ব্যবস্থাপনার যে চিত্র, তা শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি ও প্রসারে সহায়ক নয়। যোগ্য ও দক্ষ জনশক্তির যথেষ্ট অভাব এই সেক্টরে। এই অভাব নতুন নয়, পুরোনো। বর্তমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যে সার্বিক পরিস্থিতি তার ওপর গবেষণা চালালে প্রকৃত অবস্থা বোঝা যাবে।
ফলাফলে দেখা গেছে, ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাসের হার মূলধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তুলনায় বেশি। এবার ২০২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পাসের চেহারা দেখতে পারেনি। এর কারণ অনুসন্ধান করতে না পারলে এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে শিক্ষার্থী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যকার দূরত্ব বাড়বে বৈকি, যা দেশকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে না, বরং প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে। দেশের অস্তিত্ব সংকটের একটা কারণ হবে।
অটোপাসের দাবি কর্তৃপক্ষের মেনে নেওয়ার ঘটনাটি কখনোই উন্নত শিক্ষাব্যবস্থাকে সমর্থন করে না, শিক্ষিত এক জাতির পূর্বাভাস দেয় না। বরং শিক্ষাব্যবস্থাকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের প্রচণ্ড সুযোগ দেয়। অতীতে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও তার শিক্ষার্থীদের কবজা করার প্রবণতা সব সরকারের ছিল এবং এখনো আছে। কিন্তু অটোপাস দিয়ে শিক্ষার্থীদের আশ্বস্ত করবার ঘটনা সম্ভবত এই প্রথম এবং সেটা রাজনৈতিক ইস্যুতে। যেখানে ২৪-এর আন্দোলনের শুরুটা ছিল মেধার যোগ্যতায় বিসিএসে নিয়োগের দাবিতে, যদিও সেই আন্দোলন পৌঁছে যায় শেষ অবধি বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে। সেখানে অটোপাসের বিষয়টি মেধার গুরুত্বকে কোথায় নিয়ে যায় বা যাবে, সংশ্লিষ্টরা তা বুঝতে সক্ষম হয়েছিল কি না, প্রশ্ন থেকেই যায়। প্রশ্ন থাকে, নতুন বাংলাদেশ গড়ার যে স্বপ্ন ও তার প্রত্যয়, সেখানে মেধা ও শিক্ষার বিকল্প কী? উত্তর, কোনো বিকল্প নেই। একটা শিক্ষিত জাতি একটা দেশকে যতটা নিরাপদ করে রাখতে পারে, নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে, স্থায়িত্বশীল উন্নয়নকে দৃশ্যমান করে তুলতে পারে, অন্য কোনো মন্ত্র, থিওরি কিন্তু তা পারে না।
যদি শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি মনোযোগ ও গুরুত্ব না দেওয়া হয়, তাহলে একদিন পাসের হার .০৫-এ নেমে গেলে কেউ আর আশ্চর্য হবে না। তখন এটাকে বাস্তব চিত্র বলে কৃতিত্ব নেওয়ার পথও থাকবে না। একজন ক্ষমতাসীনের চেয়ে একজন মেধাবী শিক্ষিতের প্রয়োজন এই দেশে সবচেয়ে বেশি।
স্বপ্না রেজা,কথাসাহিত্যিক ও কলাম লেখক

এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল বেশ খারাপ। বলা যায়, সন্তোষজনক নয়। যদিও পরীক্ষার ফল যে ভালো হবে, পাসের হার বেশি হবে, তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য কারণ বা উদ্যোগ কিন্তু ছিল না। বরাবরের মতো গত নয়-দশ মাসে তেমন কোনো উদ্যোগ, তৎপরতা চোখে পড়েনি। রাষ্ট্র সংস্কার নিয়ে যত কথা উঠেছে, বৈষম্যের বিরুদ্ধে যত চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়েছে, অনিয়মের বিরুদ্ধে যত আওয়াজ উঠেছে, শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত মান বৃদ্ধি ও শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে তার ন্যূনতম আলাপ-আলোচনা হতে দেখা যায়নি। কারোর দৃষ্টি ও উৎসাহ এই বিষয়ে ছিল বলেও মনে হয়নি। দুঃখজনক হলেও বলতে হয় যে, রাষ্ট্র সংস্কারের চেতনায় শিক্ষাব্যবস্থাকে অচেতন অবস্থায় রাখা হয়েছে এবং সেটা বিগত সময়ের মতোই। এককথায়, আমাদের দেশে ক্ষমতাকেন্দ্রিক যাবতীয় কাজ, পরিকল্পনা, উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে উত্তম ও কার্যকর পদক্ষেপ কোনো রাজনৈতিক সরকারকেই নিতে দেখা যায়নি। যেটুকু নেওয়া হয়েছে তা অযোগ্য ও অদক্ষ ব্যক্তিদের নিয়োগ দিয়ে করা হয়েছে বলে অনেকের অভিযোগ। ফলে ভালো ফল পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব থেকেই গেছে। মেধাসম্পন্ন যোগ্য নাগরিক নয়, বরং রাজনৈতিক দল ও তার দলীয় চেতনায় দেশ গড়ার অন্যতম উপায় বলে প্রতিষ্ঠার হীন চেষ্টা চালানো হয়েছে সব সময়ই।
এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার পাসের হার ৫৮ দশমিক ৮৩ শতাংশ, যা গত ২০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ ফল বলে পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে জানা গেছে। সংবাদমাধ্যমে আরও জানা যায়, এই ফলকে শিক্ষার প্রকৃত চিত্র বলে উল্লেখ করেছেন স্বয়ং শিক্ষা উপদেষ্টা। এটা তাঁর কৃতিত্বের ঢেকুর কি না, নাকি সাধারণ জনগণের মতো হতাশার উক্তি, সেটা বলা মুশকিল। যদি কৃতিত্বের ঢেকুর এমন হয়, তাঁদের আমলে কড়াকড়ি তথা যথাযথভাবে পরীক্ষার উত্তরপত্র যাচাই করা হয়েছে, তাই পাসের হার কম হয়েছে এবং এটাই বাস্তবতা। তাহলে বলতেই হয় যে এটা নিঃসন্দেহে একটা খোঁড়া যুক্তি। যদি পাসের হার বেশি হতো তাহলে হয়তো এমন যুক্তি দেওয়া থেকে তিনি বিরত থাকতেন। উল্টো বলা হতো, যথাযথ ও উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার উত্তম ফলাফল। সব সরকারই যেভাবে কৃতিত্ব নিতে উৎসাহ বোধ করে থাকে, সে রকমই ব্যাপারটা এবারও ঘটেছে।
তবে সাধারণ জনগণ ভাবছে অন্য কথা। তারা বলছে, পরীক্ষায় পাস না করার কারণ হতে পারে উপযুক্ত শিক্ষা অর্জন ও প্রস্তুতি ছাড়াই শিক্ষার্থীরা এবার পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন। সোজাসুজি বললে দাঁড়ায়, শিক্ষার্থীরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে লেখাপড়া করেননি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাইরে থেকে গেছেন বেশ অনেক দিন। তরুণ, কিশোর, যুবকদের মধ্যে অন্য ধরনের তাড়না লক্ষ করা গেছে, যা শিক্ষাসংক্রান্ত নয়। বরং স্কুলের প্রধান শিক্ষককে লাঞ্ছিত করার ঘটনা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তিকে জুতার মালা পরিয়ে দেওয়ার মতো চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ দেখানো হয়েছে এই সময়ে। বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক ইস্যুতে শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যে ধরনের ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে, তা অনাকাঙ্ক্ষিত ও রাষ্ট্রের জন্য এক অশনিসংকেত। সরকার এই হীন কর্মকাণ্ডকে রোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে বলা যায়।
একজন প্রবীণ শিক্ষাবিদ দুঃখ করে বলছিলেন তাঁর সাম্প্রতিক সময়ের অভিজ্ঞতার কথা। যুবকদের নিয়ে আয়োজিত এক সেমিনারে তাঁকে সম্মানিত বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি যুবকদের মাঝে উপস্থিত হয়ে প্রথমেই জানতে চাইলেন, বক্তব্য দেওয়ার আগে জানতে চাই, তোমরা কয়জন নিয়মিত ক্লাসে যাচ্ছ, হাত তোলো? কিন্তু কারোর তোলা হাত তিনি দেখেননি। অবাক হন। জানতে চান, একটা হাতও না দেখার কারণ কী? তাদের কয়জন বেশ গাম্ভীর্য নিয়ে বলে, তারা এখন দেশ গড়ার কাজে ব্যস্ত। সংস্কারকাজে জড়িত। রাষ্ট্র সংস্কার হলে তারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফিরবে। প্রবীণ ভদ্রলোক ভেবে নিলেন, এই মুহূর্তে যুবকদের জ্ঞান দেওয়া বৃথা। বরং তারাই তাঁকে জ্ঞান দিতে বেশি আগ্রহী। এমন আয়োজনও নেহাত শোআপ। বর্তমানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যে অবস্থা, জাতীয় পর্যায়ে ব্যবস্থাপনার যে চিত্র, তা শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি ও প্রসারে সহায়ক নয়। যোগ্য ও দক্ষ জনশক্তির যথেষ্ট অভাব এই সেক্টরে। এই অভাব নতুন নয়, পুরোনো। বর্তমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যে সার্বিক পরিস্থিতি তার ওপর গবেষণা চালালে প্রকৃত অবস্থা বোঝা যাবে।
ফলাফলে দেখা গেছে, ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাসের হার মূলধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তুলনায় বেশি। এবার ২০২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পাসের চেহারা দেখতে পারেনি। এর কারণ অনুসন্ধান করতে না পারলে এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে শিক্ষার্থী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যকার দূরত্ব বাড়বে বৈকি, যা দেশকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে না, বরং প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে। দেশের অস্তিত্ব সংকটের একটা কারণ হবে।
অটোপাসের দাবি কর্তৃপক্ষের মেনে নেওয়ার ঘটনাটি কখনোই উন্নত শিক্ষাব্যবস্থাকে সমর্থন করে না, শিক্ষিত এক জাতির পূর্বাভাস দেয় না। বরং শিক্ষাব্যবস্থাকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের প্রচণ্ড সুযোগ দেয়। অতীতে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও তার শিক্ষার্থীদের কবজা করার প্রবণতা সব সরকারের ছিল এবং এখনো আছে। কিন্তু অটোপাস দিয়ে শিক্ষার্থীদের আশ্বস্ত করবার ঘটনা সম্ভবত এই প্রথম এবং সেটা রাজনৈতিক ইস্যুতে। যেখানে ২৪-এর আন্দোলনের শুরুটা ছিল মেধার যোগ্যতায় বিসিএসে নিয়োগের দাবিতে, যদিও সেই আন্দোলন পৌঁছে যায় শেষ অবধি বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে। সেখানে অটোপাসের বিষয়টি মেধার গুরুত্বকে কোথায় নিয়ে যায় বা যাবে, সংশ্লিষ্টরা তা বুঝতে সক্ষম হয়েছিল কি না, প্রশ্ন থেকেই যায়। প্রশ্ন থাকে, নতুন বাংলাদেশ গড়ার যে স্বপ্ন ও তার প্রত্যয়, সেখানে মেধা ও শিক্ষার বিকল্প কী? উত্তর, কোনো বিকল্প নেই। একটা শিক্ষিত জাতি একটা দেশকে যতটা নিরাপদ করে রাখতে পারে, নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে, স্থায়িত্বশীল উন্নয়নকে দৃশ্যমান করে তুলতে পারে, অন্য কোনো মন্ত্র, থিওরি কিন্তু তা পারে না।
যদি শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি মনোযোগ ও গুরুত্ব না দেওয়া হয়, তাহলে একদিন পাসের হার .০৫-এ নেমে গেলে কেউ আর আশ্চর্য হবে না। তখন এটাকে বাস্তব চিত্র বলে কৃতিত্ব নেওয়ার পথও থাকবে না। একজন ক্ষমতাসীনের চেয়ে একজন মেধাবী শিক্ষিতের প্রয়োজন এই দেশে সবচেয়ে বেশি।
স্বপ্না রেজা,কথাসাহিত্যিক ও কলাম লেখক
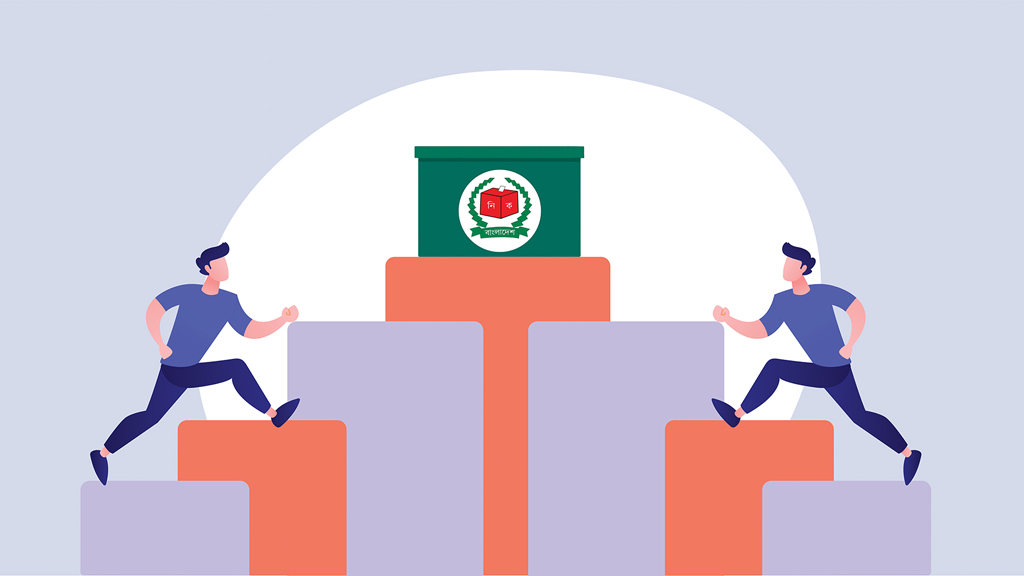
উইকিপিডিয়ায় নির্বাচনের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইভাবে: নির্বাচন হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের এমন একটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে জনগণ প্রশাসনিক কাজের জন্য একজন প্রতিনিধিকে বেছে নেয়। সপ্তদশ শতক থেকে আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে নির্বাচন একটি আবশ্যিক প্রক্রিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে।
২৬ জুলাই ২০২৫
ছোট ছিলাম যখন, তখন শোনা কথাগুলোকে অমূল্য মনে হতো। বুঝে না-বুঝে প্রচলিত কথাগুলোকেই বিশ্বাস করতাম। বয়স বাড়তে লাগল, বুঝতে পারলাম, জীবনে এমন অনেক কিছুই আছে, যা আদর্শবাদের সঙ্গে যায় না। বাস্তব একেবারে অন্য কিছু।
১৮ ঘণ্টা আগে
গরিব ও দরিদ্র মানুষদের জন্য সরকারি বরাদ্দকৃত ভিজিডি কার্ড (পরিবর্তিত নাম ভিডব্লিউবি) বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। আজকের পত্রিকায় ২১ অক্টোবর সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে।
১৯ ঘণ্টা আগে
হাত-পা বেঁধে ইচ্ছেমতো পিটিয়েছে স্থানীয় লোকজন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সেই ছিনতাইকারীর। সেখানে ঘটনা থেমে থাকেনি, লোকটির শরীরে লবণ দিয়ে উল্লাস করতে থাকে জনতা। টঙ্গীর স্টেশন রোড এলাকায় প্রতিদিন গড়ে ২০টি করে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। এটা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভয়াবহ অবস্থারই ইঙ্গিত দেয়।
২ দিন আগেসম্পাদকীয়

গরিব ও দরিদ্র মানুষদের জন্য সরকারি বরাদ্দকৃত ভিজিডি কার্ড (পরিবর্তিত নাম ভিডব্লিউবি) বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। আজকের পত্রিকায় ২১ অক্টোবর সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে।
ঘটনাটি ঘটেছে সিরাজগঞ্জের তাড়াশ উপজেলার সদর ইউনিয়নে। প্রকৃত দরিদ্র ব্যক্তিরা নয়, কার্ড পেয়েছেন ইউপি সদস্যের মেয়ে, প্রবাসীর স্ত্রী, চাকরিজীবীর পরিবার, এমনকি ১৫ বিঘা জমি ও পাকা বাড়ির মালিকেরাও। ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক, সচিব এবং একজন বিএনপিপন্থী প্রভাবশালী ইউপি সদস্যের যোগসাজশেই এই অনিয়মের কালো অধ্যায় রচিত হয়েছে। ৭ থেকে ১০ হাজার টাকা ঘুষের বিনিময়ে প্রকৃত দুস্থদের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে, সচ্ছল পরিবারগুলোকে ভিজিডি কার্ড দেওয়া হয়েছে। নীতিমালার তোয়াক্কা না করে এই তালিকা প্রণয়ন শুধু নিয়ম ভঙ্গ করাই নয়, এটি অসহায় মানুষের মৌলিক অধিকার হরণের শামিল।
শুধু দুস্থ ব্যক্তিদের কার্ডের জন্য নয়, সরকারের পক্ষ থেকে দারিদ্র্য নিরসনে বিভিন্ন প্রকল্প, বিশেষ সম্প্রদায় বা পেশার জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করাসহ নানা জনকল্যাণমূলক কাজেও এমন দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া যায়। বিধবা না হয়ে ভাতা উত্তোলন, ধনী হয়ে ভূমিহীনের জমি পাওয়া এবং প্রকৃত গৃহহীন মানুষ আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর না পাওয়াসহ নানা অভিযোগের খবর প্রতিনিয়ত পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
ঘটনাটি ঘটেছে মূলত নির্বাচিত চেয়ারম্যান না থাকায়। ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর দেশের কোনো ইউনিয়ন পরিষদে এখন আর নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও সদস্য নেই। এই ইউনিয়নে প্রশাসকের দায়িত্ব পেয়েছেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগের এক কর্মকর্তা। অনির্বাচিত ব্যক্তির সাধারণ মানুষের প্রতি দায়বোধ থাকে না। সে জন্য অপকর্মটি এই প্রশাসকের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে।
সবার প্রত্যাশা ছিল, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে এ ধরনের ঘটনা ঘটবে না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আগে যেমন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কেউ কেউ এসব করতেন, এখন সরকারের নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কেউ কেউ একই কাজ করছেন। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক হলো, তদন্ত চলাকালেই অনিয়মের মাধ্যমে কার্ড পাওয়া ব্যক্তিরা দুই মাসের চাল তুলে নিয়েছেন।
সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্যের কশাঘাত থেকে মুক্তি দেওয়া। কিন্তু যখন সেই কর্মসূচি দুর্নীতি দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ পূরণ করা সম্ভব হয় না।
যদি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কঠোর নজরদারির মাধ্যমে অনিয়মকারীদের বিচারের আওতায় আনা হতো, তাহলে এ ধরনের দুর্নীতি কিছুটা কমত।
অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধ করতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং জেলা প্রশাসকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তদন্ত প্রতিবেদন জেলা প্রশাসকের কাছে পাঠানো হয়েছে, কিন্তু এই ঘটনায় যাঁরা সরাসরি জড়িত, তাঁদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে বিভাগীয় ও ফৌজদারি ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। শুধু ইউপি সচিব ও মেম্বারকে দায়ী করে প্রশাসককে রেহাই দেওয়া হলে তা ভুল বার্তা দেবে। সব স্তরের জড়িত ব্যক্তিদের জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। একই সঙ্গে যাঁরা অনিয়ম-দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। যথাযথ তদন্ত করে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

গরিব ও দরিদ্র মানুষদের জন্য সরকারি বরাদ্দকৃত ভিজিডি কার্ড (পরিবর্তিত নাম ভিডব্লিউবি) বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। আজকের পত্রিকায় ২১ অক্টোবর সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে।
ঘটনাটি ঘটেছে সিরাজগঞ্জের তাড়াশ উপজেলার সদর ইউনিয়নে। প্রকৃত দরিদ্র ব্যক্তিরা নয়, কার্ড পেয়েছেন ইউপি সদস্যের মেয়ে, প্রবাসীর স্ত্রী, চাকরিজীবীর পরিবার, এমনকি ১৫ বিঘা জমি ও পাকা বাড়ির মালিকেরাও। ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক, সচিব এবং একজন বিএনপিপন্থী প্রভাবশালী ইউপি সদস্যের যোগসাজশেই এই অনিয়মের কালো অধ্যায় রচিত হয়েছে। ৭ থেকে ১০ হাজার টাকা ঘুষের বিনিময়ে প্রকৃত দুস্থদের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে, সচ্ছল পরিবারগুলোকে ভিজিডি কার্ড দেওয়া হয়েছে। নীতিমালার তোয়াক্কা না করে এই তালিকা প্রণয়ন শুধু নিয়ম ভঙ্গ করাই নয়, এটি অসহায় মানুষের মৌলিক অধিকার হরণের শামিল।
শুধু দুস্থ ব্যক্তিদের কার্ডের জন্য নয়, সরকারের পক্ষ থেকে দারিদ্র্য নিরসনে বিভিন্ন প্রকল্প, বিশেষ সম্প্রদায় বা পেশার জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করাসহ নানা জনকল্যাণমূলক কাজেও এমন দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া যায়। বিধবা না হয়ে ভাতা উত্তোলন, ধনী হয়ে ভূমিহীনের জমি পাওয়া এবং প্রকৃত গৃহহীন মানুষ আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর না পাওয়াসহ নানা অভিযোগের খবর প্রতিনিয়ত পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
ঘটনাটি ঘটেছে মূলত নির্বাচিত চেয়ারম্যান না থাকায়। ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর দেশের কোনো ইউনিয়ন পরিষদে এখন আর নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও সদস্য নেই। এই ইউনিয়নে প্রশাসকের দায়িত্ব পেয়েছেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগের এক কর্মকর্তা। অনির্বাচিত ব্যক্তির সাধারণ মানুষের প্রতি দায়বোধ থাকে না। সে জন্য অপকর্মটি এই প্রশাসকের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে।
সবার প্রত্যাশা ছিল, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে এ ধরনের ঘটনা ঘটবে না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আগে যেমন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কেউ কেউ এসব করতেন, এখন সরকারের নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কেউ কেউ একই কাজ করছেন। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক হলো, তদন্ত চলাকালেই অনিয়মের মাধ্যমে কার্ড পাওয়া ব্যক্তিরা দুই মাসের চাল তুলে নিয়েছেন।
সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্যের কশাঘাত থেকে মুক্তি দেওয়া। কিন্তু যখন সেই কর্মসূচি দুর্নীতি দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ পূরণ করা সম্ভব হয় না।
যদি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কঠোর নজরদারির মাধ্যমে অনিয়মকারীদের বিচারের আওতায় আনা হতো, তাহলে এ ধরনের দুর্নীতি কিছুটা কমত।
অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধ করতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং জেলা প্রশাসকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তদন্ত প্রতিবেদন জেলা প্রশাসকের কাছে পাঠানো হয়েছে, কিন্তু এই ঘটনায় যাঁরা সরাসরি জড়িত, তাঁদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে বিভাগীয় ও ফৌজদারি ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। শুধু ইউপি সচিব ও মেম্বারকে দায়ী করে প্রশাসককে রেহাই দেওয়া হলে তা ভুল বার্তা দেবে। সব স্তরের জড়িত ব্যক্তিদের জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। একই সঙ্গে যাঁরা অনিয়ম-দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। যথাযথ তদন্ত করে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
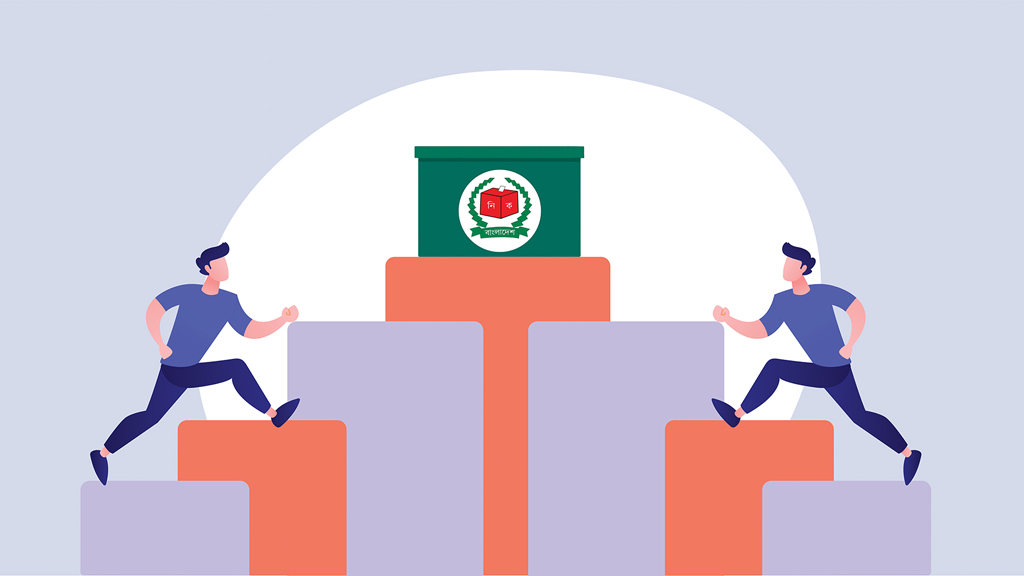
উইকিপিডিয়ায় নির্বাচনের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইভাবে: নির্বাচন হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের এমন একটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে জনগণ প্রশাসনিক কাজের জন্য একজন প্রতিনিধিকে বেছে নেয়। সপ্তদশ শতক থেকে আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে নির্বাচন একটি আবশ্যিক প্রক্রিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে।
২৬ জুলাই ২০২৫
ছোট ছিলাম যখন, তখন শোনা কথাগুলোকে অমূল্য মনে হতো। বুঝে না-বুঝে প্রচলিত কথাগুলোকেই বিশ্বাস করতাম। বয়স বাড়তে লাগল, বুঝতে পারলাম, জীবনে এমন অনেক কিছুই আছে, যা আদর্শবাদের সঙ্গে যায় না। বাস্তব একেবারে অন্য কিছু।
১৮ ঘণ্টা আগে
এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল বেশ খারাপ। বলা যায়, সন্তোষজনক নয়। যদিও পরীক্ষার ফল যে ভালো হবে, পাসের হার বেশি হবে, তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য কারণ বা উদ্যোগ কিন্তু ছিল না। বরাবরের মতো গত নয়-দশ মাসে তেমন কোনো উদ্যোগ, তৎপরতা চোখে পড়েনি।
১৮ ঘণ্টা আগে
হাত-পা বেঁধে ইচ্ছেমতো পিটিয়েছে স্থানীয় লোকজন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সেই ছিনতাইকারীর। সেখানে ঘটনা থেমে থাকেনি, লোকটির শরীরে লবণ দিয়ে উল্লাস করতে থাকে জনতা। টঙ্গীর স্টেশন রোড এলাকায় প্রতিদিন গড়ে ২০টি করে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। এটা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভয়াবহ অবস্থারই ইঙ্গিত দেয়।
২ দিন আগেসম্পাদকীয়

গাজীপুরের টঙ্গীতে এক ছিনতাইকারীকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছিল এলাকাবাসী। দুজন মিলে মোবাইল ছিনতাই করতে গিয়েছিল, তাদের একজন পালিয়ে গিয়েছিল, অন্যজনকে ধরে রশি দিয়ে হাত-পা বেঁধে ইচ্ছেমতো পিটিয়েছে স্থানীয় লোকজন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সেই ছিনতাইকারীর। সেখানে ঘটনা থেমে থাকেনি, লোকটির শরীরে লবণ দিয়ে উল্লাস করতে থাকে জনতা।
টঙ্গীর স্টেশন রোড এলাকায় প্রতিদিন গড়ে ২০টি করে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। এটা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভয়াবহ অবস্থারই ইঙ্গিত দেয়। যদি প্রতিদিন ২০টি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে থাকে, তাহলে তা প্রতিরোধ করা হয় না কেন? আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার মতো পর্যাপ্ত লোকবল কি নেই? ছিনতাইয়ের স্পটগুলো কি চিহ্নিত করা হয়েছে? এই দায় কার ওপর বর্তায়? যদি ছিনতাই রোধ করার মতো পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হতো এবং ছিনতাইকারীদের উপযুক্ত শাস্তি হতো, তাহলে এ পথ কেউ মাড়াত না। অবস্থাদৃষ্টে দেখা যাচ্ছে, সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে সংশ্লিষ্টরা। আর তাই এখনো প্রতিদিন গড়ে ২০টা করে ছিনতাই হয়ে যাচ্ছে।
ছিনতাই করার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নয়। কিন্তু উত্তেজিত জনতা সেই সাজাই দিয়েছে ছিনতাইকারীকে। জনতা ছিনতাইকারীকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করেনি, বিচার চায়নি, বরং হাত-পা রশি দিয়ে বেঁধে বেদম প্রহার করেছে। এতটাই মেরেছে যে ঘটনাস্থলেই সে নিহত হয়েছে। নিহত হওয়ার পর মৃতদেহে লবণ ছিটিয়ে উল্লাস করেছে জনতা!
আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার এই দৃষ্টান্ত মোটেই সুখকর কিছু নয়। যারা হত্যা করে, তারাই হত্যাকারী। এই হত্যার দায় কি এই উল্লসিত জনতা দেবে? প্রশ্ন জাগে, মানুষ কেন এতটা অসহিষ্ণু হয়ে উঠল? কেন একজন মানুষকে পিটিয়ে মেরে ফেলতে হবে? আইনের পথটি কি তাদের জানা নেই?
জানা আছে নিশ্চয়। কিন্তু দিনের পর দিন ছিনতাইকারীদের শাস্তি হচ্ছে না দেখে নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে কি না, সেটাও খতিয়ে দেখতে হবে। পুলিশ কিংবা নিরাপত্তারক্ষীরা যদি সতর্ক হয়ে ছিনতাইকারীদের পরিকল্পনা ভেস্তে দিতে পারত, ছিনতাইকারীরা যদি তাদের অপরাধের সাজা পেত, তাহলে হয়তো মানুষ নিজের হাতে আইন তুলে নিত না। কিন্তু এখন এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, যদি কেউ কাউকে ছিনতাইকারী বলে পেটাতে শুরু করে, তাহলে সমবেত জনতার প্রত্যেকেই খায়েশ মিটিয়ে পেটাতে থাকবে। কারও সাতে-পাঁচে নেই—এমন একজন নিরীহ মানুষও এই মবের হাতে প্রাণ হারাতে পারে।
ধরা যাক, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তৎপর হয়ে ছিনতাইকারীদের ধরতে শুরু করল, তাতে কি জনতার এই উন্মত্ততা কমে যাবে? মনে হয় না। হিংস্রতা নিবারণের জন্য পারিবারিক শিক্ষা, সচেতনতা ইত্যাদির প্রয়োজন পড়ে। সৎ গুণাবলি তৈরি করতে হলে তো সেটার চর্চা দরকার। সেই চর্চাই তো কমে গেছে। একজন মানুষের মনে যদি হিংসা, ঘৃণা, ক্ষোভ জমা হতে থাকে, কমে যেতে থাকে ভালোবাসা, মানবতা—তাহলে সে মৃত মানুষের লাশ নিয়ে উল্লাসই করবে! এ এক ভয়াবহ বাস্তবতা!

গাজীপুরের টঙ্গীতে এক ছিনতাইকারীকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছিল এলাকাবাসী। দুজন মিলে মোবাইল ছিনতাই করতে গিয়েছিল, তাদের একজন পালিয়ে গিয়েছিল, অন্যজনকে ধরে রশি দিয়ে হাত-পা বেঁধে ইচ্ছেমতো পিটিয়েছে স্থানীয় লোকজন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সেই ছিনতাইকারীর। সেখানে ঘটনা থেমে থাকেনি, লোকটির শরীরে লবণ দিয়ে উল্লাস করতে থাকে জনতা।
টঙ্গীর স্টেশন রোড এলাকায় প্রতিদিন গড়ে ২০টি করে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। এটা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভয়াবহ অবস্থারই ইঙ্গিত দেয়। যদি প্রতিদিন ২০টি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে থাকে, তাহলে তা প্রতিরোধ করা হয় না কেন? আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার মতো পর্যাপ্ত লোকবল কি নেই? ছিনতাইয়ের স্পটগুলো কি চিহ্নিত করা হয়েছে? এই দায় কার ওপর বর্তায়? যদি ছিনতাই রোধ করার মতো পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হতো এবং ছিনতাইকারীদের উপযুক্ত শাস্তি হতো, তাহলে এ পথ কেউ মাড়াত না। অবস্থাদৃষ্টে দেখা যাচ্ছে, সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে সংশ্লিষ্টরা। আর তাই এখনো প্রতিদিন গড়ে ২০টা করে ছিনতাই হয়ে যাচ্ছে।
ছিনতাই করার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নয়। কিন্তু উত্তেজিত জনতা সেই সাজাই দিয়েছে ছিনতাইকারীকে। জনতা ছিনতাইকারীকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করেনি, বিচার চায়নি, বরং হাত-পা রশি দিয়ে বেঁধে বেদম প্রহার করেছে। এতটাই মেরেছে যে ঘটনাস্থলেই সে নিহত হয়েছে। নিহত হওয়ার পর মৃতদেহে লবণ ছিটিয়ে উল্লাস করেছে জনতা!
আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার এই দৃষ্টান্ত মোটেই সুখকর কিছু নয়। যারা হত্যা করে, তারাই হত্যাকারী। এই হত্যার দায় কি এই উল্লসিত জনতা দেবে? প্রশ্ন জাগে, মানুষ কেন এতটা অসহিষ্ণু হয়ে উঠল? কেন একজন মানুষকে পিটিয়ে মেরে ফেলতে হবে? আইনের পথটি কি তাদের জানা নেই?
জানা আছে নিশ্চয়। কিন্তু দিনের পর দিন ছিনতাইকারীদের শাস্তি হচ্ছে না দেখে নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে কি না, সেটাও খতিয়ে দেখতে হবে। পুলিশ কিংবা নিরাপত্তারক্ষীরা যদি সতর্ক হয়ে ছিনতাইকারীদের পরিকল্পনা ভেস্তে দিতে পারত, ছিনতাইকারীরা যদি তাদের অপরাধের সাজা পেত, তাহলে হয়তো মানুষ নিজের হাতে আইন তুলে নিত না। কিন্তু এখন এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, যদি কেউ কাউকে ছিনতাইকারী বলে পেটাতে শুরু করে, তাহলে সমবেত জনতার প্রত্যেকেই খায়েশ মিটিয়ে পেটাতে থাকবে। কারও সাতে-পাঁচে নেই—এমন একজন নিরীহ মানুষও এই মবের হাতে প্রাণ হারাতে পারে।
ধরা যাক, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তৎপর হয়ে ছিনতাইকারীদের ধরতে শুরু করল, তাতে কি জনতার এই উন্মত্ততা কমে যাবে? মনে হয় না। হিংস্রতা নিবারণের জন্য পারিবারিক শিক্ষা, সচেতনতা ইত্যাদির প্রয়োজন পড়ে। সৎ গুণাবলি তৈরি করতে হলে তো সেটার চর্চা দরকার। সেই চর্চাই তো কমে গেছে। একজন মানুষের মনে যদি হিংসা, ঘৃণা, ক্ষোভ জমা হতে থাকে, কমে যেতে থাকে ভালোবাসা, মানবতা—তাহলে সে মৃত মানুষের লাশ নিয়ে উল্লাসই করবে! এ এক ভয়াবহ বাস্তবতা!
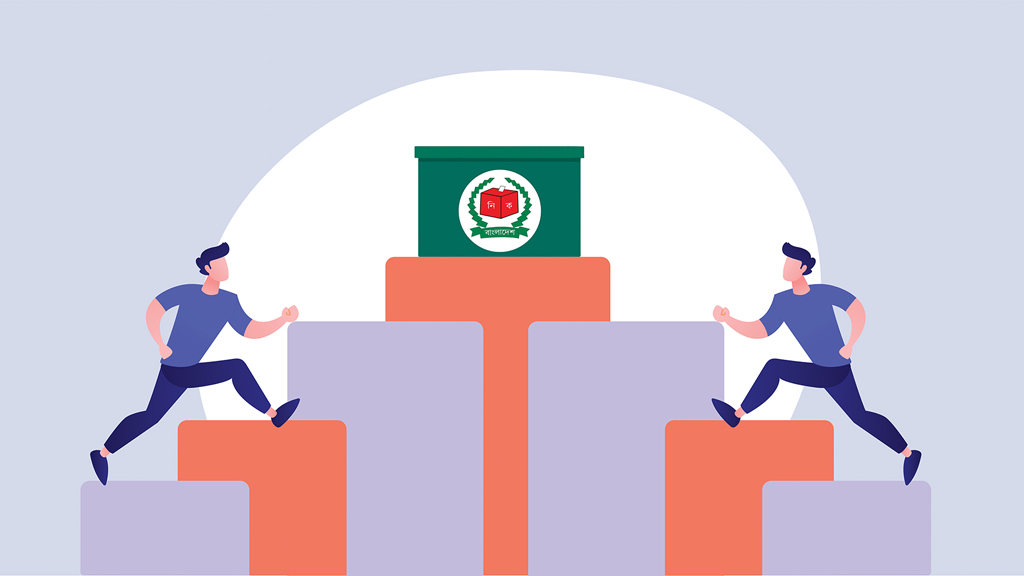
উইকিপিডিয়ায় নির্বাচনের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইভাবে: নির্বাচন হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের এমন একটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে জনগণ প্রশাসনিক কাজের জন্য একজন প্রতিনিধিকে বেছে নেয়। সপ্তদশ শতক থেকে আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে নির্বাচন একটি আবশ্যিক প্রক্রিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে।
২৬ জুলাই ২০২৫
ছোট ছিলাম যখন, তখন শোনা কথাগুলোকে অমূল্য মনে হতো। বুঝে না-বুঝে প্রচলিত কথাগুলোকেই বিশ্বাস করতাম। বয়স বাড়তে লাগল, বুঝতে পারলাম, জীবনে এমন অনেক কিছুই আছে, যা আদর্শবাদের সঙ্গে যায় না। বাস্তব একেবারে অন্য কিছু।
১৮ ঘণ্টা আগে
এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল বেশ খারাপ। বলা যায়, সন্তোষজনক নয়। যদিও পরীক্ষার ফল যে ভালো হবে, পাসের হার বেশি হবে, তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য কারণ বা উদ্যোগ কিন্তু ছিল না। বরাবরের মতো গত নয়-দশ মাসে তেমন কোনো উদ্যোগ, তৎপরতা চোখে পড়েনি।
১৮ ঘণ্টা আগে
গরিব ও দরিদ্র মানুষদের জন্য সরকারি বরাদ্দকৃত ভিজিডি কার্ড (পরিবর্তিত নাম ভিডব্লিউবি) বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। আজকের পত্রিকায় ২১ অক্টোবর সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে।
১৯ ঘণ্টা আগে