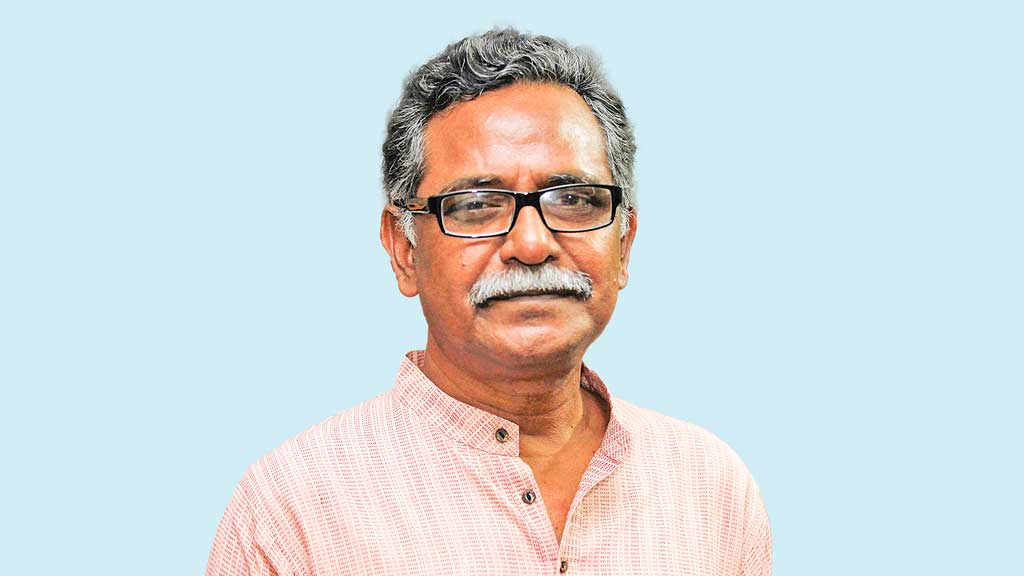
আনু মুহাম্মদ বাংলাদেশের একজন অন্যতম গণবুদ্ধিজীবী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক, একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির অন্যতম সংগঠক, তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সাবেক সদস্যসচিব। বর্তমানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের অন্যতম নেতা এবং ‘সর্বজন কথা’ পত্রিকার সম্পাদক। মার্কিন শুল্ক ও সরকারের সঙ্গে নন-ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট বা গোপনীয়তা রক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন আজকের পত্রিকার মাসুদ রানা।
মাসুদ রানা
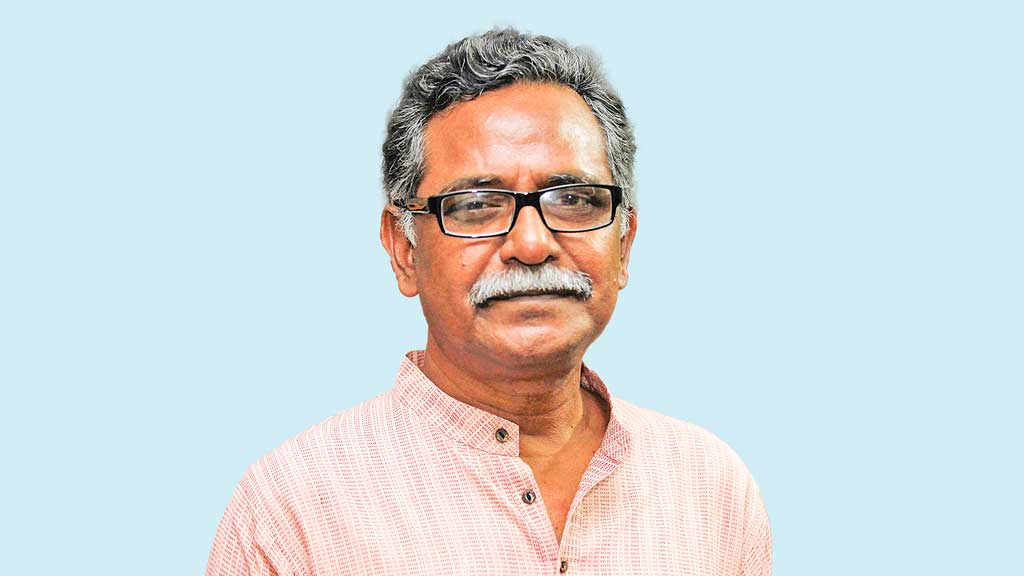
যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশি পণ্যের শুল্ক কমিয়ে ২০ শতাংশে নির্ধারণ করেছে—এটাকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?
যুক্তরাষ্ট্র তো ট্রাম্পের নেতৃত্বে সারা বিশ্বে একটা উন্মাদনা শুরু করেছে। শুল্ক বৃদ্ধির একচেটিয়া সিদ্ধান্ত যেসব যুক্তিতে দেওয়া হচ্ছে, সেগুলোর কোনোটাই গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থনীতির সাধারণ সূত্র অনুযায়ী, এসবের কোনো যুক্তি নেই। ট্রাম্পের যুক্তি হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি আছে এবং তাঁর দেশ থেকে আমাদের দেশে অনেক পণ্য আনা হয় না। এই যে আনা হয় না বা তাঁর দেশ থেকে পাঠানো হয় না, এসব তো অর্থনৈতিক কারণে হয়।
আমাদের বিশ্ববাজারে যে জায়গা থেকে আমদানি করা সুবিধাজনক, আমরা তো সেখান থেকেই আমদানি করব। অর্থনৈতিক যুক্তিতে তা-ই হওয়ার কথা। বাজার অর্থনীতির কথা হলো, যেখানে দাম কম পাওয়া যায়, সেখান থেকে আমদানি করা। আর যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করার আসলে আমাদের তেমন কিছু নেই। সে কারণে সেখানে ঘাটতি থাকে। আবার যুক্তরাষ্ট্রে চাহিদা আছে আমাদের পোশাকের। সে কারণে সেখানে আমাদের পোশাক যায়। বাজার অর্থনীতির মধ্যে তো জোরজবরদস্তির ব্যাপার থাকার কথা না।
যুক্তরাষ্ট্র বাজার অর্থনীতির কথা বলে। তারাই আবার বাজার অর্থনীতির নিয়মকানুন, বিধি-ব্যবস্থার সবকিছুকে ভেঙেচুরে তছনছ করে দিয়ে এখানে পুরো একটা দানবীয় সংঘাতসুলভ ব্যবহার করে নানা দেশে ইচ্ছেমতো শুল্ক আরোপ করছে। এটা আসলে অর্থনীতির শক্তির জোরে করছে না, সেটা করছে সামরিক শক্তির জোরে। যুক্তরাষ্ট্রের আসলে এখন আর অর্থনীতির কোনো শক্তি নেই।
এটা তারা করতে পারছে অন্যান্য দেশের অনৈক্যের কারণে। তারা এ কারণে সম্রাটসুলভ ঔদ্ধত্য দেখাতে পারছে। ট্রাম্পের মতলবটা ছিল বিভিন্ন দেশের ওপর ৩০ থেকে ৮০ বা তার বেশি শুল্ক আরোপ করা। কমানোর উদ্দেশ্য মাথায় রেখে তিনি এ রকম বড় অঙ্কের শুল্ক বসিয়েছেন। তারপর বিভিন্ন ধরনের শর্ত চাপিয়ে এখন আবার দর-কষাকষি করছেন বিভিন্ন দেশের সঙ্গে। বিভিন্ন ধরনের নীতিগত পরিবর্তনের নির্দেশ দিচ্ছেন।
বাংলাদেশে যেটা ২০ শতাংশ দাঁড়াল, সেটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। আগে আমাদের শুল্কের পরিমাণ ছিল ১৬ শতাংশ; তখন ভিয়েতনাম, পাকিস্তান, ভারত, সৌদি আরবের চেয়ে আমাদের শুল্কহার বেশি ছিল। তার ওপর এখন ২০ শতাংশ বসল। সে হিসাবে ওই সব দেশের কাছাকাছি আছে। এতে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
ট্রাম্পের এ ধরনের অপতৎপরতায় শুধু বিশ্বের নানা দেশ না, স্বয়ং যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সেখানকার ভোক্তাদের বেশি দামে জিনিস কিনতে হবে। এতে করে সব দেশ থেকে যত ধরনের জিনিস যাবে, সবকিছুর দাম বাড়বে। যুক্তরাষ্ট্রে একটা সংকট তৈরি হবে। ফলে সেখানে বেকারত্ব বাড়বে।
ট্রাম্প যত ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁর নাগরিকদের, তার কিছুই পূরণ করতে পারছেন না। তাই ট্রাম্প শুধু বিশ্বের মানুষের জন্য না, নিজ দেশের মানুষের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।
তাঁর এসব উদ্যোগের কারণে কিছু কোম্পানির লাভ হবে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকের প্রত্যেকেরই প্রকৃত আয় কমে যাবে। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির গতি এমনিতেই সংকটের মধ্যে আছে, আরও সংকটের মধ্যে পড়বে। আর সেখানে যদি মন্দা হয়, তার প্রভাব সারা বিশ্বে দেখা দেবে শুধু ট্রাম্পের কারণে।
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে সমঝোতা হয়েছে, তাতে নন-ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট বা গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এটাকে কেন গোপন করা হলো?
বাংলাদেশকে ট্রাম্পের ধমক দেওয়া এবং জোরজবরদস্তি করে শুল্ক চাপানোর সঙ্গে নানা ধরনের শর্ত দেওয়ার সম্পর্ক আছে। বাংলাদেশ আসলে ভবিষ্যতে কীভাবে চলবে, তার পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে ট্রাম্পের নির্দেশ। মানে ট্রাম্পের সঙ্গে কী কী ব্যবসা করতে হবে, তাঁর কাছ থেকে কীভাবে আমদানি বাড়াতে হবে, অন্য দেশের সঙ্গে কীভাবে আমদানি বাড়াতে হবে এবং অন্য দেশের সঙ্গে কী ধরনের সম্পর্ক রাখতে হবে—এই সবকিছু হলো ট্রাম্পের নির্দেশ। মানে, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ট্রাম্পের কথামতো হতে হবে। সেই রকম একটা নির্দেশমালা তারা বাংলাদেশকে পাঠিয়েছে। পাঠানোর পরে সেটা নিয়ে কোনো আলাপ-আলোচনা ছাড়াই সরকার কিন্তু সেটা বাস্তবায়ন শুরু করে দিয়েছে জুনের প্রথম থেকে। এটার প্রতিফলন পাওয়া যায় বাজেটে। আমি বাজেট আলোচনার সময় বলেছিলাম, এবার বাজেটে ট্রাম্প এবং আইএমএফের ছায়া আছে। ট্রাম্পের শর্ত বাস্তবায়নের কারণে শতাধিক মার্কিন পণ্যের শুল্কমুক্ত করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে বাজেটে। জাতীয় স্বার্থের কোনো আলোচনা ছাড়াই এসব শুরু হয়েছে জুন থেকেই।
কেনাকাটার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। এলএনজি আমদানি করতে হবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। যদি অন্য কোথাও কম টাকায় কেনা যায়, সেটা কেনা যাবে না। এই আমদানি চুক্তি তো কয়েক মাস আগে করা হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী বিদেশে গিয়ে সেই চুক্তি করেছেন। এরপর ২৫টি বোয়িং বিমান কেনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাজেটের মধ্যে অস্ত্র আমদানির কথা বলা হয়েছে, মাছ-মাংস ইত্যাদি শুল্কমুক্তে আমদানি করতে হবে।
এর মধ্যে শুল্ক আলোচনার সর্বশেষ পর্যায়ে যাওয়ার আগে সরকার একটা ‘নন-ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট বা গোপনীয়তা রক্ষা’ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। মানে, এই চুক্তির কোনো কিছুই প্রকাশ করা যাবে না। সরকার ১৫ শতাংশ শুল্ক কমানোর জন্য কী কী বিষয় নিয়ে চুক্তি করেছে, সেটা আমরা জানি না। কিন্তু এটা বোঝা যাচ্ছে, কয়েক মাস ধরে এই সরকারের মধ্যে বেশ কিছু ব্যক্তি আছেন, যাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের শর্তের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই সেসব বাস্তবায়নের জন্য একধাপ এগিয়ে আছেন। এতে করে তাঁরা কোনো ঝামেলার মধ্যে না পড়লেও, পুরো দেশকে একটা ফাঁদের মধ্যে ফেলে দিচ্ছেন। এই চুক্তিগুলো করার জন্য সরকারের মধ্যকার কিছু লোককে বেশি উৎসাহী দেখা যাচ্ছে। সেটাই হলো উদ্বেগের বিষয়।
গম আমরা কম দামে ইউক্রেন ও রাশিয়া থেকে কিনতে পারতাম, কিন্তু চুক্তির কারণে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আনতে হবে। চীন বা অন্য দেশ থেকে কম দামে তুলা আনা সম্ভব হলেও তা আনা যাবে না। আমাদের মাছ, মাংস যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করার দরকার না হলেও তা করতে হবে। ২৫টা বোয়িং বিমান কেনার দরকার না থাকলেও সেটা তাদের কাছ থেকেই কিনতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমস্যা ইরান ও রাশিয়ার। আমরাও এ দুই দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারব না। এতে করে বাংলাদেশের স্বাধীন কোনো অস্তিত্বই থাকবে না।
এখন সরকার ১৫ শতাংশ শুল্ক কমানোকে বিরাট সাফল্য হিসেবে দেখাতে চাইছে। কিন্তু এই ১৫ শতাংশ কমানোটা এমনিতেই সম্ভব ছিল, সেটা অন্যান্য দেশের কমানো দেখে বোঝা যাচ্ছে। এখন বাণিজ্য উপদেষ্টা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি চায়, তাহলে আমরা সেটা প্রকাশ করতে পারব। প্রকাশ করা আর না করার মধ্যে এখন আর কোনো পার্থক্য নেই। কারণ, চুক্তি তো স্বাক্ষর করা হয়ে গেছে। এতে বাংলাদেশ একটা বড় বিপদের মধ্যে পড়বে। যেসব পণ্য আমদানি করব, সেগুলো বেশি দামে কিনতে হবে। সেসবের কারণে উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাবে। এগুলো হলো আর্থিক ক্ষতির দিক।
আমাদের যে বৈশ্বিকভাবে সামরিক ব্যাপারে পোলারাইজেশনের উদ্বেগ, সেসবের ফাঁদের মধ্যে পড়ে যাব। আমাদের এ বিষয়ে পুরো নিয়ন্ত্রণটা যুক্তরাষ্ট্র নিতে চাইছে। এখানে তো চীনেরও বড় বিনিয়োগ আছে।
চীন থেকে অস্ত্র আনা যাবে না। সেখান থেকে পণ্য আমদানি কমাতে হবে। মানে, সরাসরি চীনের নাম করে তাদের অনেক ধরনের শর্ত আছে। চীনের সঙ্গে আমাদের এখনকার যে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য, সেটা বড় আকারের। কারণ, চীনের পণ্য আমদানি আমাদের জন্য সুবিধাজনক। দামের দিক থেকে, দূরত্বের দিক থেকে এবং প্রয়োজনের দিক থেকে সবচেয়ে সহজ। আর চীন থেকে আমরা কোনো অপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি করি না। শিল্পের জন্য কাঁচামাল আসে, যন্ত্রাংশ আসে। আর আসে কনজ্যুমার আইটেম। চীন থেকে আসা পণ্যগুলোর দাম সুলভ হয়।
আর যুক্তরাষ্ট্রের বাজারেও সবচেয়ে বেশি চীনের পণ্য রপ্তানি হয়। যুক্তরাষ্ট্রের এক নম্বর এবং বেশি পরিমাণে পণ্য আমদানি করা হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এখন যুক্তরাষ্ট্র অর্থনীতির রীতিনীতি এবং বাজার অর্থনীতির টেক্সটবুকের কথা তারাই বেশি করে বলে থাকে, সেটাকে তারা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে এ ধরনের শর্ত চাপিয়ে দিচ্ছে।
যুক্তরাষ্ট্রের এই নীতি কোনো বৈশ্বিক নিয়ম বা ন্যায্যতার ভিত্তিতে নয়, বরং রাজনৈতিক ও কৌশলগত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তৈরি। বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত ও দুর্বল অর্থনীতির ওপর এ ধরনের বৈষম্যমূলক শুল্ক আরোপ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ‘ন্যায্য ও সমান সুযোগভিত্তিক’ বাণিজ্যনীতির স্পষ্ট লঙ্ঘন নয় কি?
এটা আগে থেকেই হচ্ছিল। আন্তর্জাতিক অনেক প্রতিষ্ঠান এবং তাদের আইন অনেক ক্ষেত্রে অকার্যকর হয়ে গেছে। আগে থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইসরায়েল যে ফিলিস্তিনে প্রতিদিন মানুষ (শিশু ও নারী) হত্যা করছে, এর বিরুদ্ধে জাতিসংঘ, নিরাপত্তা পরিষদ এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনোটাই কার্যকর হয়নি। আন্তর্জাতিক বিধিব্যবস্থা, আইনকানুন—কোনো কিছুই কাজ করছে না।
বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে ব্যাপক উৎসাহ দেখিয়েছে। এটা বিশ্বব্যাংক বা আইএমএফের মতো না। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের সদস্য হতে হয় চাঁদার ওপর নির্ভর করে। একটি দেশের চাঁদার পরিমাণ বেশি হলে তার ভোটের সংখ্যা বেশি হয়। চাঁদার পরিমাণ কম হলে ভোটও কম হয়।
কিন্তু বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা হলো জাতিসংঘের একটি দেশের জন্য একটি ভোট। সে কারণে অন্য দেশের জন্যও একধরনের সুবিধা আছে। ফলে এই সংস্থায় যুক্তরাষ্ট্র বড় ধরনের চাপের মধ্যে পড়েছে। তার ফলে যুক্তরাষ্ট্রকে মোকাবিলা করতে ‘ব্রিকসের’ মতো সংস্থার জন্ম হয়েছে। ফলে বড় দেশের সঙ্গে ছোট দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সমঝোতা তৈরি হয়েছে। এ কারণে ব্রিকসের জন্ম যুক্তরাষ্ট্র পছন্দ করে না। এরপর একটা পর্যায়ে দেখা গেল, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সেভাবে আর কার্যকর নেই।
ট্রাম্পের এই শুল্ক চাপানোটা আন্তর্জাতিক বাজার অর্থনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে। এভাবে একটা দেশ শুল্ক আরোপ করতে পারে না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাধারণ নিয়ম হলো, কোনো দেশ শুল্ক আরোপ করলে সেখানে অন্য দেশ যেতে পারে, আবার না-ও যেতে পারে। সেটা বাস্তবায়ন করার জন্য এখন ট্রাম্প জোরজবরদস্তির আশ্রয় নিচ্ছেন। এখানে তিনি সামরিক শক্তি দেখাচ্ছেন। সমস্ত কিছু যুক্তরাষ্ট্র ঠিক করে দেবে। মানে, বাংলাদেশকে হজম করে ফেলতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। শুধু বাংলাদেশ কেন, সারা বিশ্বের ক্ষেত্রে তারা সেই চেষ্টাই করছে।
একটা অনির্বাচিত সরকার কি এ ধরনের ঝুঁকি নিতে পারে?
অন্তর্বর্তী সরকার একটা গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। তাদের দায়িত্ব আরও বেশি ছিল এগুলো প্রতিরোধ করার জন্য। তারা তো কোনো স্থায়ী সরকার না। নির্বাচিত সরকার না আসা পর্যন্ত এ ধরনের চুক্তিতে না যাওয়াই তাদের উচিত ছিল। কিন্তু দেখা গেল, তারা আগ্রহী হয়ে এ ধরনের শর্ত মেনে নিয়ে চুক্তিটা করল। যাঁরা চুক্তিটা করেছেন, তাঁদের তো একসময় খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আবার প্রবাসী, তাঁরা বাংলাদেশে থাকবেন না। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষকে দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষতির শিকার হতে হবে। সবচেয়ে বিপজ্জনক হলো, রাজনৈতিক, সামরিক ও ভূ-রাজনৈতিক পোলারাইজেশন সামনে তৈরি হবে; সেগুলোর একটা ভিকটিম হতে পারে বাংলাদেশ এ চুক্তির কারণে।
বাণিজ্য চুক্তি কাজে লাগাতে হলে নিজেদের সক্ষমতা বাড়ানোর বিকল্প নেই। আমরা কি সক্ষমতার জায়গায় আদৌ পৌঁছাতে পারব?
সক্ষমতা হলো আত্মসম্মানের ব্যাপার। একটা দেশ যদি সক্ষমতা বাড়াতে চায়, তাহলে প্রথমে আত্মসম্মান বোধের দরকার হয়। কোনো আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন সরকার এ ধরনের চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে না জনগণকে না জানিয়ে। একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যে জিনিসটা আমরা অন্য কোনো দেশ থেকে কম টাকায় পাব, সেটা আনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারস্থ হওয়াটা তো কোনো সক্ষমতার মধ্যে পড়ে না। সক্ষমতা তো বলবে, যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে আনার দরকার নেই। অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডোদের তত্ত্বই বলে, যুক্তরাষ্ট্র থেকে এ ধরনের জিনিস আমদানি করার দরকার নেই। কারণ, সেখানে দাম বেশি পড়ে। তার মানে, এই চুক্তি প্রত্যাখ্যান করাই হলো সক্ষমতা। এই চুক্তি করার মধ্য দিয়ে সক্ষমতার সব সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করা হয়েছে এবং বাংলাদেশকে বড় ধরনের বিপদের মধ্যে ফেলা হয়েছে।
সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
আজকের পত্রিকাকেও ধন্যবাদ।
যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশি পণ্যের শুল্ক কমিয়ে ২০ শতাংশে নির্ধারণ করেছে—এটাকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?
যুক্তরাষ্ট্র তো ট্রাম্পের নেতৃত্বে সারা বিশ্বে একটা উন্মাদনা শুরু করেছে। শুল্ক বৃদ্ধির একচেটিয়া সিদ্ধান্ত যেসব যুক্তিতে দেওয়া হচ্ছে, সেগুলোর কোনোটাই গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থনীতির সাধারণ সূত্র অনুযায়ী, এসবের কোনো যুক্তি নেই। ট্রাম্পের যুক্তি হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি আছে এবং তাঁর দেশ থেকে আমাদের দেশে অনেক পণ্য আনা হয় না। এই যে আনা হয় না বা তাঁর দেশ থেকে পাঠানো হয় না, এসব তো অর্থনৈতিক কারণে হয়।
আমাদের বিশ্ববাজারে যে জায়গা থেকে আমদানি করা সুবিধাজনক, আমরা তো সেখান থেকেই আমদানি করব। অর্থনৈতিক যুক্তিতে তা-ই হওয়ার কথা। বাজার অর্থনীতির কথা হলো, যেখানে দাম কম পাওয়া যায়, সেখান থেকে আমদানি করা। আর যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করার আসলে আমাদের তেমন কিছু নেই। সে কারণে সেখানে ঘাটতি থাকে। আবার যুক্তরাষ্ট্রে চাহিদা আছে আমাদের পোশাকের। সে কারণে সেখানে আমাদের পোশাক যায়। বাজার অর্থনীতির মধ্যে তো জোরজবরদস্তির ব্যাপার থাকার কথা না।
যুক্তরাষ্ট্র বাজার অর্থনীতির কথা বলে। তারাই আবার বাজার অর্থনীতির নিয়মকানুন, বিধি-ব্যবস্থার সবকিছুকে ভেঙেচুরে তছনছ করে দিয়ে এখানে পুরো একটা দানবীয় সংঘাতসুলভ ব্যবহার করে নানা দেশে ইচ্ছেমতো শুল্ক আরোপ করছে। এটা আসলে অর্থনীতির শক্তির জোরে করছে না, সেটা করছে সামরিক শক্তির জোরে। যুক্তরাষ্ট্রের আসলে এখন আর অর্থনীতির কোনো শক্তি নেই।
এটা তারা করতে পারছে অন্যান্য দেশের অনৈক্যের কারণে। তারা এ কারণে সম্রাটসুলভ ঔদ্ধত্য দেখাতে পারছে। ট্রাম্পের মতলবটা ছিল বিভিন্ন দেশের ওপর ৩০ থেকে ৮০ বা তার বেশি শুল্ক আরোপ করা। কমানোর উদ্দেশ্য মাথায় রেখে তিনি এ রকম বড় অঙ্কের শুল্ক বসিয়েছেন। তারপর বিভিন্ন ধরনের শর্ত চাপিয়ে এখন আবার দর-কষাকষি করছেন বিভিন্ন দেশের সঙ্গে। বিভিন্ন ধরনের নীতিগত পরিবর্তনের নির্দেশ দিচ্ছেন।
বাংলাদেশে যেটা ২০ শতাংশ দাঁড়াল, সেটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। আগে আমাদের শুল্কের পরিমাণ ছিল ১৬ শতাংশ; তখন ভিয়েতনাম, পাকিস্তান, ভারত, সৌদি আরবের চেয়ে আমাদের শুল্কহার বেশি ছিল। তার ওপর এখন ২০ শতাংশ বসল। সে হিসাবে ওই সব দেশের কাছাকাছি আছে। এতে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
ট্রাম্পের এ ধরনের অপতৎপরতায় শুধু বিশ্বের নানা দেশ না, স্বয়ং যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সেখানকার ভোক্তাদের বেশি দামে জিনিস কিনতে হবে। এতে করে সব দেশ থেকে যত ধরনের জিনিস যাবে, সবকিছুর দাম বাড়বে। যুক্তরাষ্ট্রে একটা সংকট তৈরি হবে। ফলে সেখানে বেকারত্ব বাড়বে।
ট্রাম্প যত ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁর নাগরিকদের, তার কিছুই পূরণ করতে পারছেন না। তাই ট্রাম্প শুধু বিশ্বের মানুষের জন্য না, নিজ দেশের মানুষের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।
তাঁর এসব উদ্যোগের কারণে কিছু কোম্পানির লাভ হবে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকের প্রত্যেকেরই প্রকৃত আয় কমে যাবে। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির গতি এমনিতেই সংকটের মধ্যে আছে, আরও সংকটের মধ্যে পড়বে। আর সেখানে যদি মন্দা হয়, তার প্রভাব সারা বিশ্বে দেখা দেবে শুধু ট্রাম্পের কারণে।
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে সমঝোতা হয়েছে, তাতে নন-ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট বা গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এটাকে কেন গোপন করা হলো?
বাংলাদেশকে ট্রাম্পের ধমক দেওয়া এবং জোরজবরদস্তি করে শুল্ক চাপানোর সঙ্গে নানা ধরনের শর্ত দেওয়ার সম্পর্ক আছে। বাংলাদেশ আসলে ভবিষ্যতে কীভাবে চলবে, তার পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে ট্রাম্পের নির্দেশ। মানে ট্রাম্পের সঙ্গে কী কী ব্যবসা করতে হবে, তাঁর কাছ থেকে কীভাবে আমদানি বাড়াতে হবে, অন্য দেশের সঙ্গে কীভাবে আমদানি বাড়াতে হবে এবং অন্য দেশের সঙ্গে কী ধরনের সম্পর্ক রাখতে হবে—এই সবকিছু হলো ট্রাম্পের নির্দেশ। মানে, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ট্রাম্পের কথামতো হতে হবে। সেই রকম একটা নির্দেশমালা তারা বাংলাদেশকে পাঠিয়েছে। পাঠানোর পরে সেটা নিয়ে কোনো আলাপ-আলোচনা ছাড়াই সরকার কিন্তু সেটা বাস্তবায়ন শুরু করে দিয়েছে জুনের প্রথম থেকে। এটার প্রতিফলন পাওয়া যায় বাজেটে। আমি বাজেট আলোচনার সময় বলেছিলাম, এবার বাজেটে ট্রাম্প এবং আইএমএফের ছায়া আছে। ট্রাম্পের শর্ত বাস্তবায়নের কারণে শতাধিক মার্কিন পণ্যের শুল্কমুক্ত করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে বাজেটে। জাতীয় স্বার্থের কোনো আলোচনা ছাড়াই এসব শুরু হয়েছে জুন থেকেই।
কেনাকাটার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। এলএনজি আমদানি করতে হবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। যদি অন্য কোথাও কম টাকায় কেনা যায়, সেটা কেনা যাবে না। এই আমদানি চুক্তি তো কয়েক মাস আগে করা হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী বিদেশে গিয়ে সেই চুক্তি করেছেন। এরপর ২৫টি বোয়িং বিমান কেনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাজেটের মধ্যে অস্ত্র আমদানির কথা বলা হয়েছে, মাছ-মাংস ইত্যাদি শুল্কমুক্তে আমদানি করতে হবে।
এর মধ্যে শুল্ক আলোচনার সর্বশেষ পর্যায়ে যাওয়ার আগে সরকার একটা ‘নন-ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট বা গোপনীয়তা রক্ষা’ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। মানে, এই চুক্তির কোনো কিছুই প্রকাশ করা যাবে না। সরকার ১৫ শতাংশ শুল্ক কমানোর জন্য কী কী বিষয় নিয়ে চুক্তি করেছে, সেটা আমরা জানি না। কিন্তু এটা বোঝা যাচ্ছে, কয়েক মাস ধরে এই সরকারের মধ্যে বেশ কিছু ব্যক্তি আছেন, যাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের শর্তের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই সেসব বাস্তবায়নের জন্য একধাপ এগিয়ে আছেন। এতে করে তাঁরা কোনো ঝামেলার মধ্যে না পড়লেও, পুরো দেশকে একটা ফাঁদের মধ্যে ফেলে দিচ্ছেন। এই চুক্তিগুলো করার জন্য সরকারের মধ্যকার কিছু লোককে বেশি উৎসাহী দেখা যাচ্ছে। সেটাই হলো উদ্বেগের বিষয়।
গম আমরা কম দামে ইউক্রেন ও রাশিয়া থেকে কিনতে পারতাম, কিন্তু চুক্তির কারণে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আনতে হবে। চীন বা অন্য দেশ থেকে কম দামে তুলা আনা সম্ভব হলেও তা আনা যাবে না। আমাদের মাছ, মাংস যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করার দরকার না হলেও তা করতে হবে। ২৫টা বোয়িং বিমান কেনার দরকার না থাকলেও সেটা তাদের কাছ থেকেই কিনতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমস্যা ইরান ও রাশিয়ার। আমরাও এ দুই দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারব না। এতে করে বাংলাদেশের স্বাধীন কোনো অস্তিত্বই থাকবে না।
এখন সরকার ১৫ শতাংশ শুল্ক কমানোকে বিরাট সাফল্য হিসেবে দেখাতে চাইছে। কিন্তু এই ১৫ শতাংশ কমানোটা এমনিতেই সম্ভব ছিল, সেটা অন্যান্য দেশের কমানো দেখে বোঝা যাচ্ছে। এখন বাণিজ্য উপদেষ্টা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি চায়, তাহলে আমরা সেটা প্রকাশ করতে পারব। প্রকাশ করা আর না করার মধ্যে এখন আর কোনো পার্থক্য নেই। কারণ, চুক্তি তো স্বাক্ষর করা হয়ে গেছে। এতে বাংলাদেশ একটা বড় বিপদের মধ্যে পড়বে। যেসব পণ্য আমদানি করব, সেগুলো বেশি দামে কিনতে হবে। সেসবের কারণে উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাবে। এগুলো হলো আর্থিক ক্ষতির দিক।
আমাদের যে বৈশ্বিকভাবে সামরিক ব্যাপারে পোলারাইজেশনের উদ্বেগ, সেসবের ফাঁদের মধ্যে পড়ে যাব। আমাদের এ বিষয়ে পুরো নিয়ন্ত্রণটা যুক্তরাষ্ট্র নিতে চাইছে। এখানে তো চীনেরও বড় বিনিয়োগ আছে।
চীন থেকে অস্ত্র আনা যাবে না। সেখান থেকে পণ্য আমদানি কমাতে হবে। মানে, সরাসরি চীনের নাম করে তাদের অনেক ধরনের শর্ত আছে। চীনের সঙ্গে আমাদের এখনকার যে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য, সেটা বড় আকারের। কারণ, চীনের পণ্য আমদানি আমাদের জন্য সুবিধাজনক। দামের দিক থেকে, দূরত্বের দিক থেকে এবং প্রয়োজনের দিক থেকে সবচেয়ে সহজ। আর চীন থেকে আমরা কোনো অপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি করি না। শিল্পের জন্য কাঁচামাল আসে, যন্ত্রাংশ আসে। আর আসে কনজ্যুমার আইটেম। চীন থেকে আসা পণ্যগুলোর দাম সুলভ হয়।
আর যুক্তরাষ্ট্রের বাজারেও সবচেয়ে বেশি চীনের পণ্য রপ্তানি হয়। যুক্তরাষ্ট্রের এক নম্বর এবং বেশি পরিমাণে পণ্য আমদানি করা হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এখন যুক্তরাষ্ট্র অর্থনীতির রীতিনীতি এবং বাজার অর্থনীতির টেক্সটবুকের কথা তারাই বেশি করে বলে থাকে, সেটাকে তারা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে এ ধরনের শর্ত চাপিয়ে দিচ্ছে।
যুক্তরাষ্ট্রের এই নীতি কোনো বৈশ্বিক নিয়ম বা ন্যায্যতার ভিত্তিতে নয়, বরং রাজনৈতিক ও কৌশলগত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তৈরি। বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত ও দুর্বল অর্থনীতির ওপর এ ধরনের বৈষম্যমূলক শুল্ক আরোপ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ‘ন্যায্য ও সমান সুযোগভিত্তিক’ বাণিজ্যনীতির স্পষ্ট লঙ্ঘন নয় কি?
এটা আগে থেকেই হচ্ছিল। আন্তর্জাতিক অনেক প্রতিষ্ঠান এবং তাদের আইন অনেক ক্ষেত্রে অকার্যকর হয়ে গেছে। আগে থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইসরায়েল যে ফিলিস্তিনে প্রতিদিন মানুষ (শিশু ও নারী) হত্যা করছে, এর বিরুদ্ধে জাতিসংঘ, নিরাপত্তা পরিষদ এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনোটাই কার্যকর হয়নি। আন্তর্জাতিক বিধিব্যবস্থা, আইনকানুন—কোনো কিছুই কাজ করছে না।
বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে ব্যাপক উৎসাহ দেখিয়েছে। এটা বিশ্বব্যাংক বা আইএমএফের মতো না। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের সদস্য হতে হয় চাঁদার ওপর নির্ভর করে। একটি দেশের চাঁদার পরিমাণ বেশি হলে তার ভোটের সংখ্যা বেশি হয়। চাঁদার পরিমাণ কম হলে ভোটও কম হয়।
কিন্তু বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা হলো জাতিসংঘের একটি দেশের জন্য একটি ভোট। সে কারণে অন্য দেশের জন্যও একধরনের সুবিধা আছে। ফলে এই সংস্থায় যুক্তরাষ্ট্র বড় ধরনের চাপের মধ্যে পড়েছে। তার ফলে যুক্তরাষ্ট্রকে মোকাবিলা করতে ‘ব্রিকসের’ মতো সংস্থার জন্ম হয়েছে। ফলে বড় দেশের সঙ্গে ছোট দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সমঝোতা তৈরি হয়েছে। এ কারণে ব্রিকসের জন্ম যুক্তরাষ্ট্র পছন্দ করে না। এরপর একটা পর্যায়ে দেখা গেল, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সেভাবে আর কার্যকর নেই।
ট্রাম্পের এই শুল্ক চাপানোটা আন্তর্জাতিক বাজার অর্থনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে। এভাবে একটা দেশ শুল্ক আরোপ করতে পারে না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাধারণ নিয়ম হলো, কোনো দেশ শুল্ক আরোপ করলে সেখানে অন্য দেশ যেতে পারে, আবার না-ও যেতে পারে। সেটা বাস্তবায়ন করার জন্য এখন ট্রাম্প জোরজবরদস্তির আশ্রয় নিচ্ছেন। এখানে তিনি সামরিক শক্তি দেখাচ্ছেন। সমস্ত কিছু যুক্তরাষ্ট্র ঠিক করে দেবে। মানে, বাংলাদেশকে হজম করে ফেলতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। শুধু বাংলাদেশ কেন, সারা বিশ্বের ক্ষেত্রে তারা সেই চেষ্টাই করছে।
একটা অনির্বাচিত সরকার কি এ ধরনের ঝুঁকি নিতে পারে?
অন্তর্বর্তী সরকার একটা গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। তাদের দায়িত্ব আরও বেশি ছিল এগুলো প্রতিরোধ করার জন্য। তারা তো কোনো স্থায়ী সরকার না। নির্বাচিত সরকার না আসা পর্যন্ত এ ধরনের চুক্তিতে না যাওয়াই তাদের উচিত ছিল। কিন্তু দেখা গেল, তারা আগ্রহী হয়ে এ ধরনের শর্ত মেনে নিয়ে চুক্তিটা করল। যাঁরা চুক্তিটা করেছেন, তাঁদের তো একসময় খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আবার প্রবাসী, তাঁরা বাংলাদেশে থাকবেন না। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষকে দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষতির শিকার হতে হবে। সবচেয়ে বিপজ্জনক হলো, রাজনৈতিক, সামরিক ও ভূ-রাজনৈতিক পোলারাইজেশন সামনে তৈরি হবে; সেগুলোর একটা ভিকটিম হতে পারে বাংলাদেশ এ চুক্তির কারণে।
বাণিজ্য চুক্তি কাজে লাগাতে হলে নিজেদের সক্ষমতা বাড়ানোর বিকল্প নেই। আমরা কি সক্ষমতার জায়গায় আদৌ পৌঁছাতে পারব?
সক্ষমতা হলো আত্মসম্মানের ব্যাপার। একটা দেশ যদি সক্ষমতা বাড়াতে চায়, তাহলে প্রথমে আত্মসম্মান বোধের দরকার হয়। কোনো আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন সরকার এ ধরনের চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে না জনগণকে না জানিয়ে। একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যে জিনিসটা আমরা অন্য কোনো দেশ থেকে কম টাকায় পাব, সেটা আনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারস্থ হওয়াটা তো কোনো সক্ষমতার মধ্যে পড়ে না। সক্ষমতা তো বলবে, যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে আনার দরকার নেই। অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডোদের তত্ত্বই বলে, যুক্তরাষ্ট্র থেকে এ ধরনের জিনিস আমদানি করার দরকার নেই। কারণ, সেখানে দাম বেশি পড়ে। তার মানে, এই চুক্তি প্রত্যাখ্যান করাই হলো সক্ষমতা। এই চুক্তি করার মধ্য দিয়ে সক্ষমতার সব সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করা হয়েছে এবং বাংলাদেশকে বড় ধরনের বিপদের মধ্যে ফেলা হয়েছে।
সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
আজকের পত্রিকাকেও ধন্যবাদ।

হাত-পা বেঁধে ইচ্ছেমতো পিটিয়েছে স্থানীয় লোকজন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সেই ছিনতাইকারীর। সেখানে ঘটনা থেমে থাকেনি, লোকটির শরীরে লবণ দিয়ে উল্লাস করতে থাকে জনতা। টঙ্গীর স্টেশন রোড এলাকায় প্রতিদিন গড়ে ২০টি করে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। এটা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভয়াবহ অবস্থারই ইঙ্গিত দেয়।
১৮ ঘণ্টা আগে
মধ্যযুগে রাজা-বাদশাহ-সম্রাটরা গায়ের জোরে দুর্বল রাজ্যগুলোকে দখলে নিতেন। রাজ্য দখলের সেসব লড়াইয়ে বেঘোরে প্রাণ হারাত হাজার হাজার সাধারণ মানুষ। সে যুগ গত হয়েছে বহু আগে। আধুনিক যুগে রাজ্য গলাধঃকরণ দুঃস্বপ্নেও কেউ কল্পনা করতে চাইবে না। কিন্তু সেই বিষয়টিই ইউক্রেনের জন্য বাস্তবতা হয়ে উঠেছে।
১৮ ঘণ্টা আগে
‘ওয়েপনাইজেশন অব এভরিথিং’ মানে ‘সবকিছুর অস্ত্রীকরণ’ করা—কথাটি এখন আর কল্পনা নয়, বৈশ্বিক রাজনীতির নির্মম বাস্তবতা। শক্তির ভারসাম্য এখন কেবল পারমাণবিক বোমা বা তেল ও গ্যাসক্ষেত্রের ওপর নির্ভর করে না। আজকে ভূ-রাজনীতির খেলার বস্তু হয়ে উঠছে বিরল মৃত্তিকা খনিজ পদার্থগুলো।
১৮ ঘণ্টা আগে
দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতি প্রাচীনকাল থেকে বহুপক্ষীয়, জটিল এবং কয়েকটি দেশের আধিপত্যবাদী স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। বিশেষ করে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমান্ত এলাকা, যা প্রাচীনকাল থেকে সামরিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অস্থিরতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচিত।
১৮ ঘণ্টা আগেসম্পাদকীয়

গাজীপুরের টঙ্গীতে এক ছিনতাইকারীকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছিল এলাকাবাসী। দুজন মিলে মোবাইল ছিনতাই করতে গিয়েছিল, তাদের একজন পালিয়ে গিয়েছিল, অন্যজনকে ধরে রশি দিয়ে হাত-পা বেঁধে ইচ্ছেমতো পিটিয়েছে স্থানীয় লোকজন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সেই ছিনতাইকারীর। সেখানে ঘটনা থেমে থাকেনি, লোকটির শরীরে লবণ দিয়ে উল্লাস করতে থাকে জনতা।
টঙ্গীর স্টেশন রোড এলাকায় প্রতিদিন গড়ে ২০টি করে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। এটা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভয়াবহ অবস্থারই ইঙ্গিত দেয়। যদি প্রতিদিন ২০টি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে থাকে, তাহলে তা প্রতিরোধ করা হয় না কেন? আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার মতো পর্যাপ্ত লোকবল কি নেই? ছিনতাইয়ের স্পটগুলো কি চিহ্নিত করা হয়েছে? এই দায় কার ওপর বর্তায়? যদি ছিনতাই রোধ করার মতো পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হতো এবং ছিনতাইকারীদের উপযুক্ত শাস্তি হতো, তাহলে এ পথ কেউ মাড়াত না। অবস্থাদৃষ্টে দেখা যাচ্ছে, সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে সংশ্লিষ্টরা। আর তাই এখনো প্রতিদিন গড়ে ২০টা করে ছিনতাই হয়ে যাচ্ছে।
ছিনতাই করার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নয়। কিন্তু উত্তেজিত জনতা সেই সাজাই দিয়েছে ছিনতাইকারীকে। জনতা ছিনতাইকারীকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করেনি, বিচার চায়নি, বরং হাত-পা রশি দিয়ে বেঁধে বেদম প্রহার করেছে। এতটাই মেরেছে যে ঘটনাস্থলেই সে নিহত হয়েছে। নিহত হওয়ার পর মৃতদেহে লবণ ছিটিয়ে উল্লাস করেছে জনতা!
আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার এই দৃষ্টান্ত মোটেই সুখকর কিছু নয়। যারা হত্যা করে, তারাই হত্যাকারী। এই হত্যার দায় কি এই উল্লসিত জনতা দেবে? প্রশ্ন জাগে, মানুষ কেন এতটা অসহিষ্ণু হয়ে উঠল? কেন একজন মানুষকে পিটিয়ে মেরে ফেলতে হবে? আইনের পথটি কি তাদের জানা নেই?
জানা আছে নিশ্চয়। কিন্তু দিনের পর দিন ছিনতাইকারীদের শাস্তি হচ্ছে না দেখে নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে কি না, সেটাও খতিয়ে দেখতে হবে। পুলিশ কিংবা নিরাপত্তারক্ষীরা যদি সতর্ক হয়ে ছিনতাইকারীদের পরিকল্পনা ভেস্তে দিতে পারত, ছিনতাইকারীরা যদি তাদের অপরাধের সাজা পেত, তাহলে হয়তো মানুষ নিজের হাতে আইন তুলে নিত না। কিন্তু এখন এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, যদি কেউ কাউকে ছিনতাইকারী বলে পেটাতে শুরু করে, তাহলে সমবেত জনতার প্রত্যেকেই খায়েশ মিটিয়ে পেটাতে থাকবে। কারও সাতে-পাঁচে নেই—এমন একজন নিরীহ মানুষও এই মবের হাতে প্রাণ হারাতে পারে।
ধরা যাক, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তৎপর হয়ে ছিনতাইকারীদের ধরতে শুরু করল, তাতে কি জনতার এই উন্মত্ততা কমে যাবে? মনে হয় না। হিংস্রতা নিবারণের জন্য পারিবারিক শিক্ষা, সচেতনতা ইত্যাদির প্রয়োজন পড়ে। সৎ গুণাবলি তৈরি করতে হলে তো সেটার চর্চা দরকার। সেই চর্চাই তো কমে গেছে। একজন মানুষের মনে যদি হিংসা, ঘৃণা, ক্ষোভ জমা হতে থাকে, কমে যেতে থাকে ভালোবাসা, মানবতা—তাহলে সে মৃত মানুষের লাশ নিয়ে উল্লাসই করবে! এ এক ভয়াবহ বাস্তবতা!

গাজীপুরের টঙ্গীতে এক ছিনতাইকারীকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছিল এলাকাবাসী। দুজন মিলে মোবাইল ছিনতাই করতে গিয়েছিল, তাদের একজন পালিয়ে গিয়েছিল, অন্যজনকে ধরে রশি দিয়ে হাত-পা বেঁধে ইচ্ছেমতো পিটিয়েছে স্থানীয় লোকজন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সেই ছিনতাইকারীর। সেখানে ঘটনা থেমে থাকেনি, লোকটির শরীরে লবণ দিয়ে উল্লাস করতে থাকে জনতা।
টঙ্গীর স্টেশন রোড এলাকায় প্রতিদিন গড়ে ২০টি করে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। এটা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভয়াবহ অবস্থারই ইঙ্গিত দেয়। যদি প্রতিদিন ২০টি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে থাকে, তাহলে তা প্রতিরোধ করা হয় না কেন? আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার মতো পর্যাপ্ত লোকবল কি নেই? ছিনতাইয়ের স্পটগুলো কি চিহ্নিত করা হয়েছে? এই দায় কার ওপর বর্তায়? যদি ছিনতাই রোধ করার মতো পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হতো এবং ছিনতাইকারীদের উপযুক্ত শাস্তি হতো, তাহলে এ পথ কেউ মাড়াত না। অবস্থাদৃষ্টে দেখা যাচ্ছে, সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে সংশ্লিষ্টরা। আর তাই এখনো প্রতিদিন গড়ে ২০টা করে ছিনতাই হয়ে যাচ্ছে।
ছিনতাই করার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নয়। কিন্তু উত্তেজিত জনতা সেই সাজাই দিয়েছে ছিনতাইকারীকে। জনতা ছিনতাইকারীকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করেনি, বিচার চায়নি, বরং হাত-পা রশি দিয়ে বেঁধে বেদম প্রহার করেছে। এতটাই মেরেছে যে ঘটনাস্থলেই সে নিহত হয়েছে। নিহত হওয়ার পর মৃতদেহে লবণ ছিটিয়ে উল্লাস করেছে জনতা!
আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার এই দৃষ্টান্ত মোটেই সুখকর কিছু নয়। যারা হত্যা করে, তারাই হত্যাকারী। এই হত্যার দায় কি এই উল্লসিত জনতা দেবে? প্রশ্ন জাগে, মানুষ কেন এতটা অসহিষ্ণু হয়ে উঠল? কেন একজন মানুষকে পিটিয়ে মেরে ফেলতে হবে? আইনের পথটি কি তাদের জানা নেই?
জানা আছে নিশ্চয়। কিন্তু দিনের পর দিন ছিনতাইকারীদের শাস্তি হচ্ছে না দেখে নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে কি না, সেটাও খতিয়ে দেখতে হবে। পুলিশ কিংবা নিরাপত্তারক্ষীরা যদি সতর্ক হয়ে ছিনতাইকারীদের পরিকল্পনা ভেস্তে দিতে পারত, ছিনতাইকারীরা যদি তাদের অপরাধের সাজা পেত, তাহলে হয়তো মানুষ নিজের হাতে আইন তুলে নিত না। কিন্তু এখন এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, যদি কেউ কাউকে ছিনতাইকারী বলে পেটাতে শুরু করে, তাহলে সমবেত জনতার প্রত্যেকেই খায়েশ মিটিয়ে পেটাতে থাকবে। কারও সাতে-পাঁচে নেই—এমন একজন নিরীহ মানুষও এই মবের হাতে প্রাণ হারাতে পারে।
ধরা যাক, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তৎপর হয়ে ছিনতাইকারীদের ধরতে শুরু করল, তাতে কি জনতার এই উন্মত্ততা কমে যাবে? মনে হয় না। হিংস্রতা নিবারণের জন্য পারিবারিক শিক্ষা, সচেতনতা ইত্যাদির প্রয়োজন পড়ে। সৎ গুণাবলি তৈরি করতে হলে তো সেটার চর্চা দরকার। সেই চর্চাই তো কমে গেছে। একজন মানুষের মনে যদি হিংসা, ঘৃণা, ক্ষোভ জমা হতে থাকে, কমে যেতে থাকে ভালোবাসা, মানবতা—তাহলে সে মৃত মানুষের লাশ নিয়ে উল্লাসই করবে! এ এক ভয়াবহ বাস্তবতা!
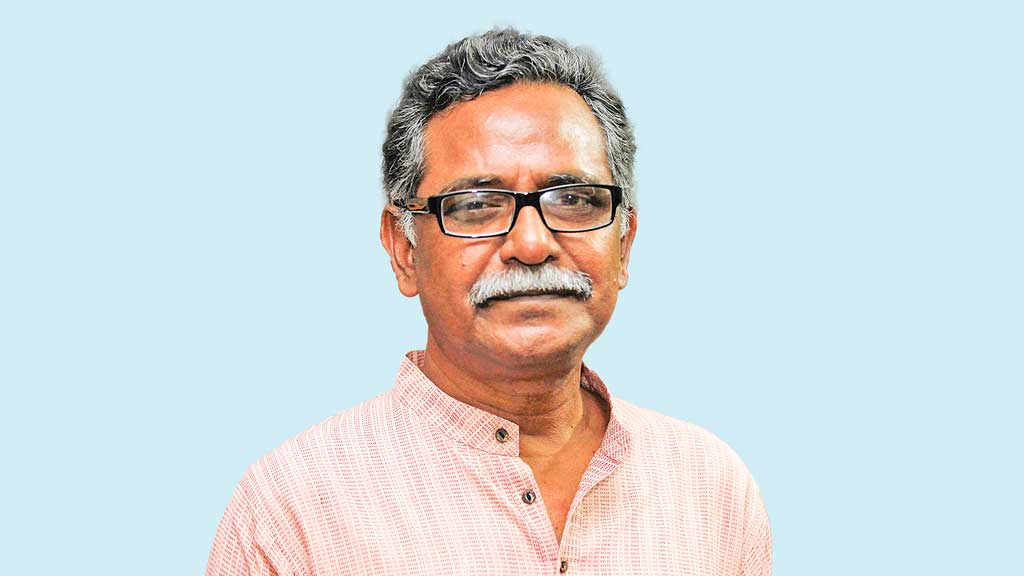
আনু মুহাম্মদ বাংলাদেশের একজন অন্যতম গণবুদ্ধিজীবী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক, একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির অন্যতম সংগঠক, তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সাবেক সদস্যসচিব।
১০ আগস্ট ২০২৫
মধ্যযুগে রাজা-বাদশাহ-সম্রাটরা গায়ের জোরে দুর্বল রাজ্যগুলোকে দখলে নিতেন। রাজ্য দখলের সেসব লড়াইয়ে বেঘোরে প্রাণ হারাত হাজার হাজার সাধারণ মানুষ। সে যুগ গত হয়েছে বহু আগে। আধুনিক যুগে রাজ্য গলাধঃকরণ দুঃস্বপ্নেও কেউ কল্পনা করতে চাইবে না। কিন্তু সেই বিষয়টিই ইউক্রেনের জন্য বাস্তবতা হয়ে উঠেছে।
১৮ ঘণ্টা আগে
‘ওয়েপনাইজেশন অব এভরিথিং’ মানে ‘সবকিছুর অস্ত্রীকরণ’ করা—কথাটি এখন আর কল্পনা নয়, বৈশ্বিক রাজনীতির নির্মম বাস্তবতা। শক্তির ভারসাম্য এখন কেবল পারমাণবিক বোমা বা তেল ও গ্যাসক্ষেত্রের ওপর নির্ভর করে না। আজকে ভূ-রাজনীতির খেলার বস্তু হয়ে উঠছে বিরল মৃত্তিকা খনিজ পদার্থগুলো।
১৮ ঘণ্টা আগে
দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতি প্রাচীনকাল থেকে বহুপক্ষীয়, জটিল এবং কয়েকটি দেশের আধিপত্যবাদী স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। বিশেষ করে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমান্ত এলাকা, যা প্রাচীনকাল থেকে সামরিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অস্থিরতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচিত।
১৮ ঘণ্টা আগেরাজিউল হাসান

মধ্যযুগে রাজা-বাদশাহ-সম্রাটরা গায়ের জোরে দুর্বল রাজ্যগুলোকে দখলে নিতেন। রাজ্য দখলের সেসব লড়াইয়ে বেঘোরে প্রাণ হারাত হাজার হাজার সাধারণ মানুষ। সে যুগ গত হয়েছে বহু আগে। আধুনিক যুগে রাজ্য গলাধঃকরণ দুঃস্বপ্নেও কেউ কল্পনা করতে চাইবে না। কিন্তু সেই বিষয়টিই ইউক্রেনের জন্য বাস্তবতা হয়ে উঠেছে। ২০১৪ সালের যুদ্ধে দেশটির ক্রিমিয়া অঞ্চল দখল করে নেয় রাশিয়া। প্রথমে সামরিক শক্তির জোরে উপদ্বীপটি দখল করা হয়েছে, তারপর গণভোট দিয়ে সেই দখলকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।
এবার ইউক্রেনের দনবাস অঞ্চল মোটামুটি দখলে চলে গেছে রাশিয়ার কাছে। এখন যুদ্ধ থামাতে এই অঞ্চলকে রাশিয়ার কাছে সমর্পণের শর্ত হাজির করা হয়েছে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির কাছে। ক্রিমিয়া দখলের সময় রাশিয়ার পাশে কেউ ছিল না। বিশ্ব মোড়ল যুক্তরাষ্ট্রও কড়া অবস্থান নিয়েছিল মস্কোর বিরুদ্ধে। তারপরও ঠেকানো যায়নি। এবার অবস্থা ভিন্ন। খোদ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এখন ইউক্রেনের বিষয়ে খানিকটা বৈরী মনোভাবাপন্ন। তাঁর তরফ থেকেই দনবাস সমর্পণের প্রস্তাব গেছে ইউক্রেনের কাছে। ফলে এবারও যে রাশিয়া দনবাস দখল করে নেবে, সে ব্যাপারে আপাতত কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু জেলেনস্কির জন্য এই যুদ্ধ যেমন বড় চাপ, একইভাবে দনবাস সমর্পণ হবে তাঁর জন্য রাজনৈতিক আত্মহত্যা।
রাশিয়া-ইউক্রেনের বর্তমান অবস্থার কারণ অনুসন্ধান করতে হলে কিছুটা পেছন ফিরে তাকাতে হবে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙার পর ইউক্রেনের স্বাধীন দেশ হিসেবে পথচলা শুরু হয়। কিন্তু ‘পৃথিবীর রুটির ঝুড়ি’খ্যাত দেশটির বড় দুর্ভাগ্য, তারা এক পরাশক্তির প্রতিবেশী। প্রতিবেশী শক্তিশালী ও ভালো হলে কিছু সুবিধা অবশ্যই পাওয়া যায়। কিন্তু প্রতিবেশী যদি বৈরী হয়, তাহলে যেকোনো দেশের জন্যই একসময় তা বড় ধরনের হুমকি হয়ে ওঠে।
রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো আবার পরাক্রমশালী হয়ে ওঠার স্বপ্ন বরাবরই প্রতিবেশীদের জন্য বড় শঙ্কা তৈরি করছে। তার ওপর ইউক্রেনের সাম্প্রতিক ইতিহাস ঘাঁটলে পরিষ্কার হয়ে যায়, দেশটির বেশির ভাগ রাজনীতিকেরই মনোযোগ রাশিয়ার মতো পরাক্রমশালী প্রতিবেশীকে নিজের পক্ষে রাখা নয়, যেকোনো মূল্যে তাকে ঠেকানো। বিশেষ করে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি দেশের প্রতিরক্ষার কথা বিবেচনা করে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট ন্যাটোয় যোগ দিতে উঠেপড়ে লেগেছিলেন। তাঁর এই প্রত্যাশা আরও চড়িয়েছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। কিন্তু রাশিয়া তো তার দোরগোড়ায় ন্যাটোর ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন মানবে না। ফলে যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। জেলেনস্কির তৎপরতার ছুতোয় ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ফের ইউক্রেনে তথাকথিত রুশ অভিযান শুরু হয়, যা এখনো চলছে।
বিবিসি, সিএনএনসহ আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলোর তথ্য বলছে, গত প্রায় চার বছরে রাশিয়া ইউক্রেনের এক-পঞ্চমাংশ এলাকা দখল করে নিয়েছে। দনবাস অঞ্চলের সিংহভাগ এখন রুশ নিয়ন্ত্রণে। ইউক্রেনের লুহানস্ক, দোনেৎস্ক এবং কৃষ্ণসাগর-তীরবর্তী মারিউপোল বন্দর নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় দনবাস ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ রাশিয়ার হাতে গেলে ক্রিমিয়ার সঙ্গে সরাসরি সড়কপথে রাশিয়ার মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টি হবে। এ কারণেই রাশিয়ার জন্য এলাকাটি গুরুত্বপূর্ণ।
কিন্তু জেলেনস্কি এই অঞ্চল সমর্পণ করতে নারাজ। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার প্রতি কিছুটা হলেও নমনীয়। যুদ্ধ থামাতে তিনি রাশিয়াকে নিষেধাজ্ঞা আরোপসহ নানা হুমকি দিয়েছেন, রুশ তেল না কিনতে ইউরোপীয় মিত্র এবং ভারত ও চীনকে বারবার সতর্ক করে যাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু এখন পর্যন্ত মস্কোর বিরুদ্ধে বড় কোনো পদক্ষেপ তিনি নেননি। বরং তিনি রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা দেশগুলোর ওপর চাপিয়েছেন বাড়তি শুল্ক। তাঁর উদ্দেশ্য রুশ তেলের বিপণন কমিয়ে দেশটির আর্থিক শক্তি কমিয়ে আনা। তবে কূটনৈতিকভাবে তিনি এখনো পুতিনের প্রতি নমনীয়। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র পেতে জেলেনস্কি হোয়াইট হাউসে গিয়েছিলেন। সেই ক্ষেপণাস্ত্র তো তিনি পানইনি, বরং এবারও ‘অপমানিত’ হয়ে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে তাঁকে। ট্রাম্প এ সময় তাঁকে উল্টো যুদ্ধ থামাতে দনবাস সমর্পণ করতে বলেছেন। এর আগেও ট্রাম্প এমন কথা বলেছেন জেলেনস্কিকে। গত ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে হোয়াইট হাউসে একবার অপমানিত হতে হয়েছে তাঁকে। সেবার প্রকাশ্যে অপমান করলেও এবার তেমনটা ঘটেনি। তবে সূত্রের বরাত দিয়ে ব্রিটিশ সংবাদপত্র ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদনের তথ্য বলছে, এবারও জেলেনস্কিকে ‘ধমক’ দিয়েছেন ট্রাম্প।
জেলেনস্কির এবারের হোয়াইট হাউস সফরের এক দিন আগেই পুতিনের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন ট্রাম্প। সেই আলোচনার পর ফের সরাসরি সাক্ষাতের ঘোষণা আসে তাঁদের তরফ থেকে। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এ সাক্ষাৎ হতে পারে বলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। তবে এবার আর যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে নয়, ট্রাম্প-পুতিন দেখা হবে হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে। কিন্তু এটিও জেলেনস্কির জন্য বড় দুঃসংবাদ। কারণ, হাঙ্গেরির প্রেসিডেন্ট ভিক্টর অরবান পুতিনের বড় সমর্থক। কাজেই এই আলোচনায়ও যে ইউক্রেনের জন্য কোনো সুসংবাদ বয়ে আনবে না, তা আগেভাগেই অনুমান করা যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও জেলেনস্কি ওই বৈঠকে থাকতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, তাঁকে যদি আমন্ত্রণ জানানো হয়, তাহলে তিনি বৈঠকে থাকতে চান।
তবে যুদ্ধ থামাতে ট্রাম্পের প্রচেষ্টা, জেলেনস্কির কূটনৈতিক তৎপরতার ফলাফল যদি দনবাস সমর্পণ হয়, তাহলে তা হবে ইউক্রেন ও তার জনগণের জন্য বড় ক্ষতি। পাশাপাশি সারা বিশ্বের জন্যও অশনিসংকেত হবে সেটি। ২০২২ সালে ইউক্রেন যুদ্ধের পর এরই মধ্যে প্রাণ বাঁচাতে লাখো ইউক্রেনীয় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমিয়েছে। ফলে জার্মানিসহ বিভিন্ন দেশের ওপর চাপ বেড়েছে। তার ওপর ইউক্রেনকে লাগাতার নানাভাবে সহায়তা দিতে গিয়ে ইউরোপের দেশগুলোকে পড়তে হয়েছে আর্থিক চাপে। এমন ক্ষতি স্বীকার করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ইউক্রেনকে যদি গুরুত্বপূর্ণ একটি অঞ্চল সমর্পণ করতে হয়, তাহলে গোটা পশ্চিমা দেশগুলোর জন্য তা হবে বড় এক পরাজয়।
এদিকে রাশিয়ার এভাবে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের ভূখণ্ড দখল করে নেওয়া যদি বৈধতা পেয়ে যায়, তখন বাকি বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোও ‘নিপীড়ক’ হয়ে উঠতে পারে বলে শঙ্কা রয়েছে। এমনিতেই শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রতিবেশী দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে নানা ঝক্কি সামলাতে হয়। তার ওপর ভূখণ্ড দখলের উদাহরণ সৃষ্টি হলে হুমকিতে পড়বে দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর জাতীয় নিরাপত্তা ও অখণ্ডতা। ফলে বিশ্বজুড়ে বাড়বে অবিশ্বাস, তৈরি হবে অস্থিরতা। তার সরাসরি প্রভাব পড়বে অর্থনীতি ও সাধারণ মানুষের ওপর। বেড়ে যাবে সংঘাত, যুদ্ধবিগ্রহ। কিন্তু আধুনিক যুগে এমনটা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

মধ্যযুগে রাজা-বাদশাহ-সম্রাটরা গায়ের জোরে দুর্বল রাজ্যগুলোকে দখলে নিতেন। রাজ্য দখলের সেসব লড়াইয়ে বেঘোরে প্রাণ হারাত হাজার হাজার সাধারণ মানুষ। সে যুগ গত হয়েছে বহু আগে। আধুনিক যুগে রাজ্য গলাধঃকরণ দুঃস্বপ্নেও কেউ কল্পনা করতে চাইবে না। কিন্তু সেই বিষয়টিই ইউক্রেনের জন্য বাস্তবতা হয়ে উঠেছে। ২০১৪ সালের যুদ্ধে দেশটির ক্রিমিয়া অঞ্চল দখল করে নেয় রাশিয়া। প্রথমে সামরিক শক্তির জোরে উপদ্বীপটি দখল করা হয়েছে, তারপর গণভোট দিয়ে সেই দখলকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।
এবার ইউক্রেনের দনবাস অঞ্চল মোটামুটি দখলে চলে গেছে রাশিয়ার কাছে। এখন যুদ্ধ থামাতে এই অঞ্চলকে রাশিয়ার কাছে সমর্পণের শর্ত হাজির করা হয়েছে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির কাছে। ক্রিমিয়া দখলের সময় রাশিয়ার পাশে কেউ ছিল না। বিশ্ব মোড়ল যুক্তরাষ্ট্রও কড়া অবস্থান নিয়েছিল মস্কোর বিরুদ্ধে। তারপরও ঠেকানো যায়নি। এবার অবস্থা ভিন্ন। খোদ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এখন ইউক্রেনের বিষয়ে খানিকটা বৈরী মনোভাবাপন্ন। তাঁর তরফ থেকেই দনবাস সমর্পণের প্রস্তাব গেছে ইউক্রেনের কাছে। ফলে এবারও যে রাশিয়া দনবাস দখল করে নেবে, সে ব্যাপারে আপাতত কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু জেলেনস্কির জন্য এই যুদ্ধ যেমন বড় চাপ, একইভাবে দনবাস সমর্পণ হবে তাঁর জন্য রাজনৈতিক আত্মহত্যা।
রাশিয়া-ইউক্রেনের বর্তমান অবস্থার কারণ অনুসন্ধান করতে হলে কিছুটা পেছন ফিরে তাকাতে হবে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙার পর ইউক্রেনের স্বাধীন দেশ হিসেবে পথচলা শুরু হয়। কিন্তু ‘পৃথিবীর রুটির ঝুড়ি’খ্যাত দেশটির বড় দুর্ভাগ্য, তারা এক পরাশক্তির প্রতিবেশী। প্রতিবেশী শক্তিশালী ও ভালো হলে কিছু সুবিধা অবশ্যই পাওয়া যায়। কিন্তু প্রতিবেশী যদি বৈরী হয়, তাহলে যেকোনো দেশের জন্যই একসময় তা বড় ধরনের হুমকি হয়ে ওঠে।
রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো আবার পরাক্রমশালী হয়ে ওঠার স্বপ্ন বরাবরই প্রতিবেশীদের জন্য বড় শঙ্কা তৈরি করছে। তার ওপর ইউক্রেনের সাম্প্রতিক ইতিহাস ঘাঁটলে পরিষ্কার হয়ে যায়, দেশটির বেশির ভাগ রাজনীতিকেরই মনোযোগ রাশিয়ার মতো পরাক্রমশালী প্রতিবেশীকে নিজের পক্ষে রাখা নয়, যেকোনো মূল্যে তাকে ঠেকানো। বিশেষ করে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি দেশের প্রতিরক্ষার কথা বিবেচনা করে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট ন্যাটোয় যোগ দিতে উঠেপড়ে লেগেছিলেন। তাঁর এই প্রত্যাশা আরও চড়িয়েছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। কিন্তু রাশিয়া তো তার দোরগোড়ায় ন্যাটোর ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন মানবে না। ফলে যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। জেলেনস্কির তৎপরতার ছুতোয় ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ফের ইউক্রেনে তথাকথিত রুশ অভিযান শুরু হয়, যা এখনো চলছে।
বিবিসি, সিএনএনসহ আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলোর তথ্য বলছে, গত প্রায় চার বছরে রাশিয়া ইউক্রেনের এক-পঞ্চমাংশ এলাকা দখল করে নিয়েছে। দনবাস অঞ্চলের সিংহভাগ এখন রুশ নিয়ন্ত্রণে। ইউক্রেনের লুহানস্ক, দোনেৎস্ক এবং কৃষ্ণসাগর-তীরবর্তী মারিউপোল বন্দর নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় দনবাস ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ রাশিয়ার হাতে গেলে ক্রিমিয়ার সঙ্গে সরাসরি সড়কপথে রাশিয়ার মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টি হবে। এ কারণেই রাশিয়ার জন্য এলাকাটি গুরুত্বপূর্ণ।
কিন্তু জেলেনস্কি এই অঞ্চল সমর্পণ করতে নারাজ। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার প্রতি কিছুটা হলেও নমনীয়। যুদ্ধ থামাতে তিনি রাশিয়াকে নিষেধাজ্ঞা আরোপসহ নানা হুমকি দিয়েছেন, রুশ তেল না কিনতে ইউরোপীয় মিত্র এবং ভারত ও চীনকে বারবার সতর্ক করে যাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু এখন পর্যন্ত মস্কোর বিরুদ্ধে বড় কোনো পদক্ষেপ তিনি নেননি। বরং তিনি রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা দেশগুলোর ওপর চাপিয়েছেন বাড়তি শুল্ক। তাঁর উদ্দেশ্য রুশ তেলের বিপণন কমিয়ে দেশটির আর্থিক শক্তি কমিয়ে আনা। তবে কূটনৈতিকভাবে তিনি এখনো পুতিনের প্রতি নমনীয়। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র পেতে জেলেনস্কি হোয়াইট হাউসে গিয়েছিলেন। সেই ক্ষেপণাস্ত্র তো তিনি পানইনি, বরং এবারও ‘অপমানিত’ হয়ে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে তাঁকে। ট্রাম্প এ সময় তাঁকে উল্টো যুদ্ধ থামাতে দনবাস সমর্পণ করতে বলেছেন। এর আগেও ট্রাম্প এমন কথা বলেছেন জেলেনস্কিকে। গত ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে হোয়াইট হাউসে একবার অপমানিত হতে হয়েছে তাঁকে। সেবার প্রকাশ্যে অপমান করলেও এবার তেমনটা ঘটেনি। তবে সূত্রের বরাত দিয়ে ব্রিটিশ সংবাদপত্র ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদনের তথ্য বলছে, এবারও জেলেনস্কিকে ‘ধমক’ দিয়েছেন ট্রাম্প।
জেলেনস্কির এবারের হোয়াইট হাউস সফরের এক দিন আগেই পুতিনের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন ট্রাম্প। সেই আলোচনার পর ফের সরাসরি সাক্ষাতের ঘোষণা আসে তাঁদের তরফ থেকে। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এ সাক্ষাৎ হতে পারে বলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। তবে এবার আর যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে নয়, ট্রাম্প-পুতিন দেখা হবে হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে। কিন্তু এটিও জেলেনস্কির জন্য বড় দুঃসংবাদ। কারণ, হাঙ্গেরির প্রেসিডেন্ট ভিক্টর অরবান পুতিনের বড় সমর্থক। কাজেই এই আলোচনায়ও যে ইউক্রেনের জন্য কোনো সুসংবাদ বয়ে আনবে না, তা আগেভাগেই অনুমান করা যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও জেলেনস্কি ওই বৈঠকে থাকতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, তাঁকে যদি আমন্ত্রণ জানানো হয়, তাহলে তিনি বৈঠকে থাকতে চান।
তবে যুদ্ধ থামাতে ট্রাম্পের প্রচেষ্টা, জেলেনস্কির কূটনৈতিক তৎপরতার ফলাফল যদি দনবাস সমর্পণ হয়, তাহলে তা হবে ইউক্রেন ও তার জনগণের জন্য বড় ক্ষতি। পাশাপাশি সারা বিশ্বের জন্যও অশনিসংকেত হবে সেটি। ২০২২ সালে ইউক্রেন যুদ্ধের পর এরই মধ্যে প্রাণ বাঁচাতে লাখো ইউক্রেনীয় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমিয়েছে। ফলে জার্মানিসহ বিভিন্ন দেশের ওপর চাপ বেড়েছে। তার ওপর ইউক্রেনকে লাগাতার নানাভাবে সহায়তা দিতে গিয়ে ইউরোপের দেশগুলোকে পড়তে হয়েছে আর্থিক চাপে। এমন ক্ষতি স্বীকার করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ইউক্রেনকে যদি গুরুত্বপূর্ণ একটি অঞ্চল সমর্পণ করতে হয়, তাহলে গোটা পশ্চিমা দেশগুলোর জন্য তা হবে বড় এক পরাজয়।
এদিকে রাশিয়ার এভাবে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের ভূখণ্ড দখল করে নেওয়া যদি বৈধতা পেয়ে যায়, তখন বাকি বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোও ‘নিপীড়ক’ হয়ে উঠতে পারে বলে শঙ্কা রয়েছে। এমনিতেই শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রতিবেশী দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে নানা ঝক্কি সামলাতে হয়। তার ওপর ভূখণ্ড দখলের উদাহরণ সৃষ্টি হলে হুমকিতে পড়বে দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর জাতীয় নিরাপত্তা ও অখণ্ডতা। ফলে বিশ্বজুড়ে বাড়বে অবিশ্বাস, তৈরি হবে অস্থিরতা। তার সরাসরি প্রভাব পড়বে অর্থনীতি ও সাধারণ মানুষের ওপর। বেড়ে যাবে সংঘাত, যুদ্ধবিগ্রহ। কিন্তু আধুনিক যুগে এমনটা কোনোভাবেই কাম্য নয়।
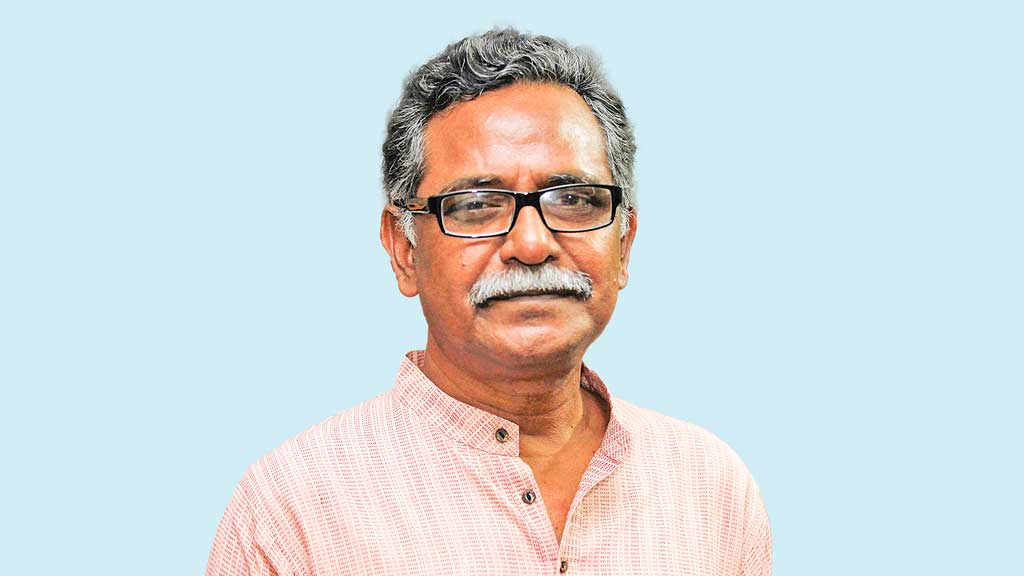
আনু মুহাম্মদ বাংলাদেশের একজন অন্যতম গণবুদ্ধিজীবী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক, একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির অন্যতম সংগঠক, তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সাবেক সদস্যসচিব।
১০ আগস্ট ২০২৫
হাত-পা বেঁধে ইচ্ছেমতো পিটিয়েছে স্থানীয় লোকজন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সেই ছিনতাইকারীর। সেখানে ঘটনা থেমে থাকেনি, লোকটির শরীরে লবণ দিয়ে উল্লাস করতে থাকে জনতা। টঙ্গীর স্টেশন রোড এলাকায় প্রতিদিন গড়ে ২০টি করে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। এটা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভয়াবহ অবস্থারই ইঙ্গিত দেয়।
১৮ ঘণ্টা আগে
‘ওয়েপনাইজেশন অব এভরিথিং’ মানে ‘সবকিছুর অস্ত্রীকরণ’ করা—কথাটি এখন আর কল্পনা নয়, বৈশ্বিক রাজনীতির নির্মম বাস্তবতা। শক্তির ভারসাম্য এখন কেবল পারমাণবিক বোমা বা তেল ও গ্যাসক্ষেত্রের ওপর নির্ভর করে না। আজকে ভূ-রাজনীতির খেলার বস্তু হয়ে উঠছে বিরল মৃত্তিকা খনিজ পদার্থগুলো।
১৮ ঘণ্টা আগে
দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতি প্রাচীনকাল থেকে বহুপক্ষীয়, জটিল এবং কয়েকটি দেশের আধিপত্যবাদী স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। বিশেষ করে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমান্ত এলাকা, যা প্রাচীনকাল থেকে সামরিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অস্থিরতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচিত।
১৮ ঘণ্টা আগেআব্দুর রহমান

‘ওয়েপনাইজেশন অব এভরিথিং’ মানে ‘সবকিছুর অস্ত্রীকরণ’ করা—কথাটি এখন আর কল্পনা নয়, বৈশ্বিক রাজনীতির নির্মম বাস্তবতা। শক্তির ভারসাম্য এখন কেবল পারমাণবিক বোমা বা তেল ও গ্যাসক্ষেত্রের ওপর নির্ভর করে না। আজকে ভূ-রাজনীতির খেলার বস্তু হয়ে উঠছে বিরল মৃত্তিকা খনিজ পদার্থগুলো। যেগুলোর নাম অধিকাংশ মানুষই শোনেনি, যা বিশ্বের প্রযুক্তি, সামরিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার কেন্দ্রে অবস্থান করছে।
রেয়ার আর্থ মিনারেলস বা বিরল মৃত্তিকা খনিজ পদার্থগুলো বলতে সাধারণত নিওডিমিয়াম, ডিসপ্রোসিয়াম, ল্যান্থানাম, সেরিয়াম, টার্বিয়ামের মতো ১৭টি ধাতব পদার্থকে বোঝায়। এগুলো রকেট, যুদ্ধবিমান, স্মার্টফোন, ইলেকট্রিক গাড়ির মোটর, উইন্ড টারবাইন, সোলার প্যানেল, স্যাটেলাইট যোগাযোগব্যবস্থা, এমনকি মিসাইল গাইডেন্স সিস্টেমসহ নানা যন্ত্র তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। একুশ শতকের শিল্প ও সামরিক শক্তির ভিত্তি হিসেবে এই খনিজগুলো পুরোপুরি নির্ভরশীল।
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে বিরল খনিজকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত আগ্রহ তীব্র হয়েছে। তিনি চীনকে প্রতিরোধের নতুন সূত্র হিসেবে এই খনিজের জোগান ও নিয়ন্ত্রণের ওপর মনোযোগ দিচ্ছেন। এরই মধ্যে চীনের মিত্র পাকিস্তান ও খনিজসমৃদ্ধ অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ওয়াশিংটন সম্পর্ক জোরদার করেছেন। মার্কিন রাষ্ট্রদূতরা মিয়ানমারের বিরল খনিজসমৃদ্ধ এলাকা ঘুরে দেখছেন, বিনিয়োগ ও সরবরাহ চুক্তির সম্ভাবনা খুঁজছেন। এমনকি দেশটির জান্তা সরকার যুক্তরাষ্ট্রের আনুকূল্য লাভের জন্য এই বিরল খনিজকে কৌশলগত হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের সম্ভাবনা দেখছে। চীনকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের এই নতুন তৎপরতা নিছক অর্থনৈতিক নয়, বরং এটি এক নতুন স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা বলে ধারণা করা যাচ্ছে।
চীনও থেমে নেই। দেশটি অনেক আগেই বুঝে গিয়েছিল ভবিষ্যতের যুদ্ধের রণক্ষেত্র হবে ভূগর্ভ। ১৯৯২ সালে তৎকালীন নেতা দেং জিয়াওপিং বলেছিলেন, ‘মধ্যপ্রাচ্যের তেল আছে, আর চীনের আছে বিরল খনিজ।’ সেই কথার অর্থ আজ পরিষ্কার হচ্ছে। চীন এখন বিশ্বের মোট উৎপাদিত বিরল খনিজের ৭০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে, আর পরিশোধনের ৯০ শতাংশ সম্পূর্ণ তাদের হাতে। এর মানে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ বা জাপান কোথাও খনিজ আবিষ্কার করলেও সেগুলো প্রক্রিয়াজাত করতে প্রায়ই চীনের ওপর নির্ভর করতে হয়। কারণ, খনিজকে বাজারযোগ্য অবস্থায় আনতে যে প্রযুক্তি, শ্রম ও পরিবেশগত অবকাঠামো দরকার, তা চীনের বাইরে তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। বৈদ্যুতিক গাড়ি থেকে যুদ্ধবিমান, রকেট থেকে ব্যাটারি, প্রতিটি উচ্চপ্রযুক্তির যন্ত্রে এই খনিজ অপরিহার্য। তাই চীন চাইলে বৈশ্বিক শিল্পপ্রবাহের শিরা বন্ধ করে দিতে পারে এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বকে প্রযুক্তিগতভাবে অচল করে দিতে পারে।
চীন প্রথমে খনিজকে অস্ত্রে পরিণত করতে না চাইলেও ট্রাম্পের বাণিজ্যযুদ্ধ চীনকে সেই পথে ঠেলে দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র চীনের রপ্তানিতে শতভাগের বেশি শুল্ক বসানোর পর বেইজিংও পাল্টা পদক্ষেপ নেয়। মার্কিন প্রযুক্তি রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি হলে চীন ঘোষণা করে, চীনা বা বিদেশি কোনো প্রতিষ্ঠান যদি চীনের বিরল খনিজ বা প্রযুক্তি ব্যবহার করে সামরিক উদ্দেশ্যে কিছু তৈরি করতে চায়, তবে বেইজিংয়ের অনুমতি লাগবে। আর এই ঘোষণার পেছনে আছে ক্ষমতার প্রশ্ন। চীন জানে, বিশ্ব এখন তাদের খনিজের ওপর নির্ভরশীল।
যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান এখন নাজুক। তাদের সামরিক প্রযুক্তি, যেমন এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান, রাডারব্যবস্থা কিংবা মিসাইল গাইডেন্স সিস্টেম বা ক্ষেপণাস্ত্র নির্দেশক প্রযুক্তি—সবই বিরল খনিজের ওপর নির্ভরশীল। একেকটি এফ-৩৫ বিমান তৈরিতে লাগে প্রায় ৪০০ কেজি বিরল মৃত্তিকা খনিজ, যার অধিকাংশই আসে চীন থেকে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সফটওয়্যার কোম্পানি গোভিনির গবেষণায় দেখা গেছে, অন্তত ১,৯০৮টি অস্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত প্রায় ৮০ হাজার উপাদান সরাসরি চীনা খনিজের ওপর নির্ভরশীল। এই পরিসংখ্যান যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষাশিল্পের ভঙ্গুর বাস্তবতাকে প্রকাশ করে।
ইউরোপও একই সংকটে আছে। জার্মানির গাড়িশিল্প, ফ্রান্সের প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন—সবই চীনের সরবরাহের কাছে বাঁধা। অথচ বিকল্প জোগান গড়ে তোলার মতো প্রযুক্তি, অর্থ বা সময় তাদের নেই। যুক্তরাষ্ট্র এখন মরিয়া হয়ে আফ্রিকার দেশগুলো যেমন অ্যাঙ্গোলা, কঙ্গো, তানজানিয়া ও মোজাম্বিকে নতুন খনিজ উৎস খুঁজছে। এমনকি লাতিন আমেরিকাতেও তাদের নজর আছে। সেখানে পশ্চিমা জোটের অর্থায়নে গড়ে তোলা হচ্ছে সড়ক, রেল ও বন্দর, যাতে ভবিষ্যতে চীনের বিকল্প সরবরাহ পথ তৈরি করা যায়।
বিরল খনিজকে কেন্দ্র করে চীনের কৌশলগত বৈশ্বিক প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টার বিপরীতে ট্রাম্প প্রশাসনও পাল্টা খেলায় নেমেছে। গ্রিনল্যান্ডের বরফাচ্ছন্ন ভূমি থেকে শুরু করে ইউক্রেনের যুদ্ধবিধ্বস্ত খনিজ অঞ্চল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র নজর দিচ্ছে নতুন খনিজ খাত দখলে। অস্ট্রেলিয়ায় বিনিয়োগ চুক্তি, পাকিস্তানের পাহাড়ি অঞ্চলে অনুসন্ধান, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কূটনৈতিক দর-কষাকষি—সবই একই ভূ-রাজনৈতিক কৌশলের অংশ।
এরই অংশ হিসেবে ‘ডিফেন্স প্রোডাকশন অ্যাক্ট’-এর আওতায় ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র রেয়ার আর্থ খাতে বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ ঘোষণা করেছে। দেশটি অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ভিয়েতনাম ও আফ্রিকার বেশ কিছু রাষ্ট্রের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে নতুন খনি প্রকল্প সন্ধানে নেমেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নও ‘ক্রিটিক্যাল র ম্যাটেরিয়ালস অ্যাক্ট’ পাস করে চীনের বিকল্প সরবরাহশৃঙ্খল তৈরির চেষ্টা করছে।
এই নতুন স্নায়ুযুদ্ধের অস্ত্র পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র নয়, বরং মাটির নিচে লুকিয়ে থাকা সামারিয়াম, গ্যাডোলিনিয়াম, ডিসপোরিয়াম আর ইট্রিয়ামের মতো ধাতু। ভবিষ্যতের প্রযুক্তি ও সামরিক শক্তি পুরোপুরি দাঁড়িয়ে থাকবে এই ধাতুগুলোর ওপর। চীন এখন বুঝে গেছে, যুদ্ধ না করেও আধিপত্য কায়েম করা সম্ভব। যুক্তরাষ্ট্রও তা বুঝে গেছে, কিন্তু তাদের হাতে সময় কম।
পৃথিবী যখন জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় ‘সবুজ জ্বালানির’ দিকে ঝুঁকছে, তখন এই খনিজগুলোর চাহিদা বহুগুণ বেড়ে গেছে। একেকটি বৈদ্যুতিক গাড়িতে প্রায় ১০ কেজি রেয়ার আর্থ মিনারেলস লাগে, একটি উইন্ড টারবাইনে প্রয়োজন ৬০০ কেজিরও বেশি। ফলে ‘সবুজবিপ্লব’ যত দ্রুত এগোচ্ছে, ততই রেয়ার আর্থের ওপর নির্ভরতা বাড়ছে।
এই নির্ভরতা নতুন উপনিবেশবাদের রূপ নিচ্ছে। আফ্রিকার কঙ্গো, জাম্বিয়া, নামিবিয়া, লাতিন আমেরিকার চিলি ও বলিভিয়া—সবখানে এখন খনিজের নামে বিদেশি বিনিয়োগের হিড়িক। যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ইউরোপ—সবাই একে অপরকে টপকে খনি, রপ্তানি অধিকার ও অবকাঠামো নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার চেষ্টা করছে। স্থানীয় জনগণ পাচ্ছে দূষণ, স্থানচ্যুতি আর ঋণচক্রের শৃঙ্খল।
ভবিষ্যতের যুদ্ধ মিসাইল দিয়ে নয়, সরবরাহ চেইনের দখল দিয়ে হবে। যে রাষ্ট্রের হাতে থাকবে রেয়ার আর্থ মিনারেলসের প্রবাহ, সেই দেশই নির্ধারণ করবে কারা প্রযুক্তিতে এগিয়ে যাবে, কারা জ্বালানি উৎপাদন করবে, এমনকি কারা যুদ্ধ করবে।
চীন এখন এই সরবরাহ-শৃঙ্খলের প্রভু। যুক্তরাষ্ট্র প্রতিরোধে মরিয়া। ইউরোপের দেশগুলো নিজেদের অবস্থান খুঁজছে—কেউ চীনের সঙ্গে সমঝোতায়, কেউ আমেরিকার সঙ্গে জোটে। কিন্তু আসল প্রশ্ন হলো—এ প্রতিযোগিতা শেষ পর্যন্ত মানবতার উপকারে আসবে, নাকি নতুন এক খনিজ সাম্রাজ্যের জন্ম দেবে? তবে সবুজ শক্তির নামে যে প্রতিযোগিতা চলছে, তা যদি পরিবেশবিধ্বংস, দারিদ্র্য আর বৈষম্যই বাড়ায়, তবে এই রেয়ার আর্থ আসলে আধুনিক সভ্যতার নতুন শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়াবে। ইতিহাস ইঙ্গিত দেয়, এই প্রতিযোগিতা দ্রুত শেষ হবে না।

‘ওয়েপনাইজেশন অব এভরিথিং’ মানে ‘সবকিছুর অস্ত্রীকরণ’ করা—কথাটি এখন আর কল্পনা নয়, বৈশ্বিক রাজনীতির নির্মম বাস্তবতা। শক্তির ভারসাম্য এখন কেবল পারমাণবিক বোমা বা তেল ও গ্যাসক্ষেত্রের ওপর নির্ভর করে না। আজকে ভূ-রাজনীতির খেলার বস্তু হয়ে উঠছে বিরল মৃত্তিকা খনিজ পদার্থগুলো। যেগুলোর নাম অধিকাংশ মানুষই শোনেনি, যা বিশ্বের প্রযুক্তি, সামরিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার কেন্দ্রে অবস্থান করছে।
রেয়ার আর্থ মিনারেলস বা বিরল মৃত্তিকা খনিজ পদার্থগুলো বলতে সাধারণত নিওডিমিয়াম, ডিসপ্রোসিয়াম, ল্যান্থানাম, সেরিয়াম, টার্বিয়ামের মতো ১৭টি ধাতব পদার্থকে বোঝায়। এগুলো রকেট, যুদ্ধবিমান, স্মার্টফোন, ইলেকট্রিক গাড়ির মোটর, উইন্ড টারবাইন, সোলার প্যানেল, স্যাটেলাইট যোগাযোগব্যবস্থা, এমনকি মিসাইল গাইডেন্স সিস্টেমসহ নানা যন্ত্র তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। একুশ শতকের শিল্প ও সামরিক শক্তির ভিত্তি হিসেবে এই খনিজগুলো পুরোপুরি নির্ভরশীল।
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে বিরল খনিজকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত আগ্রহ তীব্র হয়েছে। তিনি চীনকে প্রতিরোধের নতুন সূত্র হিসেবে এই খনিজের জোগান ও নিয়ন্ত্রণের ওপর মনোযোগ দিচ্ছেন। এরই মধ্যে চীনের মিত্র পাকিস্তান ও খনিজসমৃদ্ধ অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ওয়াশিংটন সম্পর্ক জোরদার করেছেন। মার্কিন রাষ্ট্রদূতরা মিয়ানমারের বিরল খনিজসমৃদ্ধ এলাকা ঘুরে দেখছেন, বিনিয়োগ ও সরবরাহ চুক্তির সম্ভাবনা খুঁজছেন। এমনকি দেশটির জান্তা সরকার যুক্তরাষ্ট্রের আনুকূল্য লাভের জন্য এই বিরল খনিজকে কৌশলগত হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের সম্ভাবনা দেখছে। চীনকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের এই নতুন তৎপরতা নিছক অর্থনৈতিক নয়, বরং এটি এক নতুন স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা বলে ধারণা করা যাচ্ছে।
চীনও থেমে নেই। দেশটি অনেক আগেই বুঝে গিয়েছিল ভবিষ্যতের যুদ্ধের রণক্ষেত্র হবে ভূগর্ভ। ১৯৯২ সালে তৎকালীন নেতা দেং জিয়াওপিং বলেছিলেন, ‘মধ্যপ্রাচ্যের তেল আছে, আর চীনের আছে বিরল খনিজ।’ সেই কথার অর্থ আজ পরিষ্কার হচ্ছে। চীন এখন বিশ্বের মোট উৎপাদিত বিরল খনিজের ৭০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে, আর পরিশোধনের ৯০ শতাংশ সম্পূর্ণ তাদের হাতে। এর মানে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ বা জাপান কোথাও খনিজ আবিষ্কার করলেও সেগুলো প্রক্রিয়াজাত করতে প্রায়ই চীনের ওপর নির্ভর করতে হয়। কারণ, খনিজকে বাজারযোগ্য অবস্থায় আনতে যে প্রযুক্তি, শ্রম ও পরিবেশগত অবকাঠামো দরকার, তা চীনের বাইরে তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। বৈদ্যুতিক গাড়ি থেকে যুদ্ধবিমান, রকেট থেকে ব্যাটারি, প্রতিটি উচ্চপ্রযুক্তির যন্ত্রে এই খনিজ অপরিহার্য। তাই চীন চাইলে বৈশ্বিক শিল্পপ্রবাহের শিরা বন্ধ করে দিতে পারে এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বকে প্রযুক্তিগতভাবে অচল করে দিতে পারে।
চীন প্রথমে খনিজকে অস্ত্রে পরিণত করতে না চাইলেও ট্রাম্পের বাণিজ্যযুদ্ধ চীনকে সেই পথে ঠেলে দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র চীনের রপ্তানিতে শতভাগের বেশি শুল্ক বসানোর পর বেইজিংও পাল্টা পদক্ষেপ নেয়। মার্কিন প্রযুক্তি রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি হলে চীন ঘোষণা করে, চীনা বা বিদেশি কোনো প্রতিষ্ঠান যদি চীনের বিরল খনিজ বা প্রযুক্তি ব্যবহার করে সামরিক উদ্দেশ্যে কিছু তৈরি করতে চায়, তবে বেইজিংয়ের অনুমতি লাগবে। আর এই ঘোষণার পেছনে আছে ক্ষমতার প্রশ্ন। চীন জানে, বিশ্ব এখন তাদের খনিজের ওপর নির্ভরশীল।
যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান এখন নাজুক। তাদের সামরিক প্রযুক্তি, যেমন এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান, রাডারব্যবস্থা কিংবা মিসাইল গাইডেন্স সিস্টেম বা ক্ষেপণাস্ত্র নির্দেশক প্রযুক্তি—সবই বিরল খনিজের ওপর নির্ভরশীল। একেকটি এফ-৩৫ বিমান তৈরিতে লাগে প্রায় ৪০০ কেজি বিরল মৃত্তিকা খনিজ, যার অধিকাংশই আসে চীন থেকে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সফটওয়্যার কোম্পানি গোভিনির গবেষণায় দেখা গেছে, অন্তত ১,৯০৮টি অস্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত প্রায় ৮০ হাজার উপাদান সরাসরি চীনা খনিজের ওপর নির্ভরশীল। এই পরিসংখ্যান যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষাশিল্পের ভঙ্গুর বাস্তবতাকে প্রকাশ করে।
ইউরোপও একই সংকটে আছে। জার্মানির গাড়িশিল্প, ফ্রান্সের প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন—সবই চীনের সরবরাহের কাছে বাঁধা। অথচ বিকল্প জোগান গড়ে তোলার মতো প্রযুক্তি, অর্থ বা সময় তাদের নেই। যুক্তরাষ্ট্র এখন মরিয়া হয়ে আফ্রিকার দেশগুলো যেমন অ্যাঙ্গোলা, কঙ্গো, তানজানিয়া ও মোজাম্বিকে নতুন খনিজ উৎস খুঁজছে। এমনকি লাতিন আমেরিকাতেও তাদের নজর আছে। সেখানে পশ্চিমা জোটের অর্থায়নে গড়ে তোলা হচ্ছে সড়ক, রেল ও বন্দর, যাতে ভবিষ্যতে চীনের বিকল্প সরবরাহ পথ তৈরি করা যায়।
বিরল খনিজকে কেন্দ্র করে চীনের কৌশলগত বৈশ্বিক প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টার বিপরীতে ট্রাম্প প্রশাসনও পাল্টা খেলায় নেমেছে। গ্রিনল্যান্ডের বরফাচ্ছন্ন ভূমি থেকে শুরু করে ইউক্রেনের যুদ্ধবিধ্বস্ত খনিজ অঞ্চল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র নজর দিচ্ছে নতুন খনিজ খাত দখলে। অস্ট্রেলিয়ায় বিনিয়োগ চুক্তি, পাকিস্তানের পাহাড়ি অঞ্চলে অনুসন্ধান, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কূটনৈতিক দর-কষাকষি—সবই একই ভূ-রাজনৈতিক কৌশলের অংশ।
এরই অংশ হিসেবে ‘ডিফেন্স প্রোডাকশন অ্যাক্ট’-এর আওতায় ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র রেয়ার আর্থ খাতে বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ ঘোষণা করেছে। দেশটি অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ভিয়েতনাম ও আফ্রিকার বেশ কিছু রাষ্ট্রের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে নতুন খনি প্রকল্প সন্ধানে নেমেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নও ‘ক্রিটিক্যাল র ম্যাটেরিয়ালস অ্যাক্ট’ পাস করে চীনের বিকল্প সরবরাহশৃঙ্খল তৈরির চেষ্টা করছে।
এই নতুন স্নায়ুযুদ্ধের অস্ত্র পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র নয়, বরং মাটির নিচে লুকিয়ে থাকা সামারিয়াম, গ্যাডোলিনিয়াম, ডিসপোরিয়াম আর ইট্রিয়ামের মতো ধাতু। ভবিষ্যতের প্রযুক্তি ও সামরিক শক্তি পুরোপুরি দাঁড়িয়ে থাকবে এই ধাতুগুলোর ওপর। চীন এখন বুঝে গেছে, যুদ্ধ না করেও আধিপত্য কায়েম করা সম্ভব। যুক্তরাষ্ট্রও তা বুঝে গেছে, কিন্তু তাদের হাতে সময় কম।
পৃথিবী যখন জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় ‘সবুজ জ্বালানির’ দিকে ঝুঁকছে, তখন এই খনিজগুলোর চাহিদা বহুগুণ বেড়ে গেছে। একেকটি বৈদ্যুতিক গাড়িতে প্রায় ১০ কেজি রেয়ার আর্থ মিনারেলস লাগে, একটি উইন্ড টারবাইনে প্রয়োজন ৬০০ কেজিরও বেশি। ফলে ‘সবুজবিপ্লব’ যত দ্রুত এগোচ্ছে, ততই রেয়ার আর্থের ওপর নির্ভরতা বাড়ছে।
এই নির্ভরতা নতুন উপনিবেশবাদের রূপ নিচ্ছে। আফ্রিকার কঙ্গো, জাম্বিয়া, নামিবিয়া, লাতিন আমেরিকার চিলি ও বলিভিয়া—সবখানে এখন খনিজের নামে বিদেশি বিনিয়োগের হিড়িক। যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ইউরোপ—সবাই একে অপরকে টপকে খনি, রপ্তানি অধিকার ও অবকাঠামো নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার চেষ্টা করছে। স্থানীয় জনগণ পাচ্ছে দূষণ, স্থানচ্যুতি আর ঋণচক্রের শৃঙ্খল।
ভবিষ্যতের যুদ্ধ মিসাইল দিয়ে নয়, সরবরাহ চেইনের দখল দিয়ে হবে। যে রাষ্ট্রের হাতে থাকবে রেয়ার আর্থ মিনারেলসের প্রবাহ, সেই দেশই নির্ধারণ করবে কারা প্রযুক্তিতে এগিয়ে যাবে, কারা জ্বালানি উৎপাদন করবে, এমনকি কারা যুদ্ধ করবে।
চীন এখন এই সরবরাহ-শৃঙ্খলের প্রভু। যুক্তরাষ্ট্র প্রতিরোধে মরিয়া। ইউরোপের দেশগুলো নিজেদের অবস্থান খুঁজছে—কেউ চীনের সঙ্গে সমঝোতায়, কেউ আমেরিকার সঙ্গে জোটে। কিন্তু আসল প্রশ্ন হলো—এ প্রতিযোগিতা শেষ পর্যন্ত মানবতার উপকারে আসবে, নাকি নতুন এক খনিজ সাম্রাজ্যের জন্ম দেবে? তবে সবুজ শক্তির নামে যে প্রতিযোগিতা চলছে, তা যদি পরিবেশবিধ্বংস, দারিদ্র্য আর বৈষম্যই বাড়ায়, তবে এই রেয়ার আর্থ আসলে আধুনিক সভ্যতার নতুন শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়াবে। ইতিহাস ইঙ্গিত দেয়, এই প্রতিযোগিতা দ্রুত শেষ হবে না।
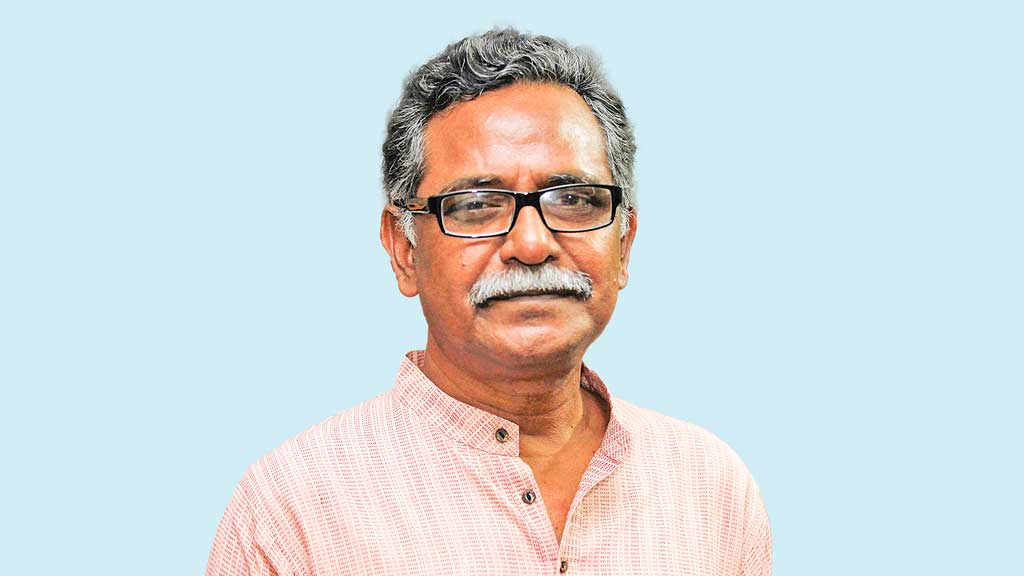
আনু মুহাম্মদ বাংলাদেশের একজন অন্যতম গণবুদ্ধিজীবী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক, একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির অন্যতম সংগঠক, তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সাবেক সদস্যসচিব।
১০ আগস্ট ২০২৫
হাত-পা বেঁধে ইচ্ছেমতো পিটিয়েছে স্থানীয় লোকজন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সেই ছিনতাইকারীর। সেখানে ঘটনা থেমে থাকেনি, লোকটির শরীরে লবণ দিয়ে উল্লাস করতে থাকে জনতা। টঙ্গীর স্টেশন রোড এলাকায় প্রতিদিন গড়ে ২০টি করে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। এটা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভয়াবহ অবস্থারই ইঙ্গিত দেয়।
১৮ ঘণ্টা আগে
মধ্যযুগে রাজা-বাদশাহ-সম্রাটরা গায়ের জোরে দুর্বল রাজ্যগুলোকে দখলে নিতেন। রাজ্য দখলের সেসব লড়াইয়ে বেঘোরে প্রাণ হারাত হাজার হাজার সাধারণ মানুষ। সে যুগ গত হয়েছে বহু আগে। আধুনিক যুগে রাজ্য গলাধঃকরণ দুঃস্বপ্নেও কেউ কল্পনা করতে চাইবে না। কিন্তু সেই বিষয়টিই ইউক্রেনের জন্য বাস্তবতা হয়ে উঠেছে।
১৮ ঘণ্টা আগে
দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতি প্রাচীনকাল থেকে বহুপক্ষীয়, জটিল এবং কয়েকটি দেশের আধিপত্যবাদী স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। বিশেষ করে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমান্ত এলাকা, যা প্রাচীনকাল থেকে সামরিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অস্থিরতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচিত।
১৮ ঘণ্টা আগেনতুন অস্থিরতা
এস এম হাসানুজ্জামান

দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতি প্রাচীনকাল থেকে বহুপক্ষীয়, জটিল এবং কয়েকটি দেশের আধিপত্যবাদী স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। বিশেষ করে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমান্ত এলাকা, যা প্রাচীনকাল থেকে সামরিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অস্থিরতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচিত। সাম্প্রতিক সংঘাতের মাধ্যমে তা আবারও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য গুরুতর হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সীমান্তের এই অস্থিরতা কেবল দুই দেশের মধ্যে সামরিক উত্তেজনায় সীমাবদ্ধ নয়; এটি দক্ষিণ এশিয়ার কূটনীতি, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা, মানবিক পরিস্থিতি এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করছে।
২০২৫ সালের ৯ অক্টোবর কাবুলের আবদুল হাক্ক স্কয়ারে দুটি বিস্ফোরণ ঘটে, যা পুরো শহরকে আতঙ্কের ছায়ায় আচ্ছন্ন করে। এই বিস্ফোরণকে পাকিস্তান সরকার তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি) প্রধান নূর ওয়ালি মেহসুদকে লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে বলে দাবি করা হয়। যদিও মেহসুদ নিজে একটি অডিও বার্তায় বেঁচে থাকার ঘোষণা দেন। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ১১ অক্টোবর রাতে আফগান বাহিনী পাকিস্তানি সীমান্তচৌকিগুলোতে পাল্টা হামলা চালায়। এই আক্রমণে পাকিস্তান তার ২৩ সেনা সদস্যকে হারায়। তবে পাল্টা হামলায় তারা দাবি করে, ২০০ তালেবান এবং তাদের সহযোগী সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। আফগান বাহিনী ঘোষণা করে, তারা সীমান্তে ২৫টি পাকিস্তানি চৌকি দখল করেছে। এর পরপরই তোরখাম, চামান এবং অন্যান্য প্রধান সীমান্তচৌকিগুলো বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বাণিজ্য, পরিবহন এবং সাধারণ জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাপনে মারাত্মকভাবে প্রভাব ফেলে।
সীমান্ত সংঘাতের পেছনে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক জটিলতা রয়েছে। পাকিস্তান দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ করে আসছে, আফগান সরকার তাদের ভূখণ্ডে টিটিপি সদস্যদের নিরাপদ আশ্রয় দিচ্ছে। আফগান প্রশাসন এই অভিযোগ অস্বীকার করলেও পাকিস্তানের অভ্যন্তরে টিটিপির হামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিস্থিতি দুই দেশের সম্পর্ককে ক্রমেই উত্তেজনাপূর্ণ করে তুলেছে। ২০২১ সালে তালেবান ক্ষমতায় আসার পর, আফগান ভূখণ্ডে টিটিপির কার্যক্রম বৃদ্ধি পায়। ইসলামাবাদ এই কার্যক্রমকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচনা করছে। আফগানিস্তানের তালেবানরা রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হচ্ছে, যা সীমান্ত অস্থিরতাকে আরও তীব্র করছে।
সীমান্ত সংঘাতের সামরিক দিকও অত্যন্ত জটিল। এ ক্ষেত্রে সংঘাত প্রায়ই গেরিলা যুদ্ধের কৌশলে পরিচালিত হয়। তালেবান বাহিনী হঠাৎ এবং অপ্রত্যাশিত আক্রমণ, দ্রুতগতি, স্থানীয় সমর্থন এবং ট্যাকটিক্যাল অপ্রচলিত কৌশল ব্যবহার করে পাকিস্তানি সীমান্তপ্রহরীদের তুলনায় অধিক কার্যকরভাবে। পাকিস্তানি বাহিনী তুলনামূলকভাবে বড়, আধুনিক ও স্থায়ী। তাদের কাছে প্রচলিত যুদ্ধের প্রযুক্তি রয়েছে—যেমন ট্যাংক, বিমান, পর্যবেক্ষণব্যবস্থা এবং আধুনিক অস্ত্র। তবু গেরিলা কৌশলের কারণে সীমান্তচৌকিগুলো হারাতে পারে। তালেবান বাহিনী স্বল্পসংখ্যক হলেও দ্রুতগতি ও চমকপ্রদ কৌশল ব্যবহার করে কার্যকর আক্রমণ চালায়।
টিটিপি, তালেবান এবং ইসলামিক স্টেট ইন খোরাসান প্রভিন্সের কর্মকাণ্ড সীমান্ত সংঘাতকে আরও জটিল করেছে। টিটিপি পাকিস্তানের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালায়, যার মধ্যে আত্মঘাতী বোমা হামলা এবং অন্যান্য সহিংস কর্মকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত। আফগান ভূখণ্ডে তারা নিরাপদ আশ্রয় পায়। আফগানিস্তান তালেবান বাহিনীর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়, কিন্তু অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সামাজিক প্রতিরোধের কারণে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।
এখনকার দুই দেশের মধ্যে সংঘাতে সীমান্তচৌকিগুলো বন্ধ থাকায় ব্যবসা-বাণিজ্য এবং পরিবহন ব্যাহত হচ্ছে। সীমান্তবর্তী সাধারণ জনগণ মানবিক সংকটের মুখোমুখি হয়েছে। খাদ্য ও স্বাস্থ্যসেবার সীমিত প্রাপ্যতা, আফগান শরণার্থীদের নিরাপদ আশ্রয় না পাওয়া এবং অর্থনৈতিক দুর্ভোগ মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি করছে। সীমান্ত অস্থিরতার কারণে স্থানীয় অর্থনীতি বিপর্যস্ত। তাই আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে মানবিক সহায়তার জন্য এই সংকট প্রশমিত করা প্রয়োজন।
এই সংঘাতে আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতিরও গুরুত্ব আছে। সম্প্রতি ভারতের সঙ্গে আফগানিস্তানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাকিস্তান সন্দেহের চোখে দেখছে। ভারতের কূটনৈতিক নীতির প্রভাব এবং পাকিস্তানের নিরাপত্তা চিন্তা—সবকিছু মিলিত হয়ে সংকটকে আরও জটিল করেছে। সৌদি আরব, কাতার, ইরান, চীন এবং রাশিয়া উভয় পক্ষকে সংযম বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছে। আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতের সফরে শান্তিপূর্ণ সমাধানের ওপর জোর দিয়েছেন। পাকিস্তানও সীমান্তে উত্তেজনা প্রশমনের জন্য কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যেন দ্বিপক্ষীয় সমঝোতার মাধ্যমে উত্তেজনা প্রশমিত করতে পারে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, সীমান্তে উত্তেজনা অব্যাহত থাকলে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও খারাপ হতে পারে। তবে উভয় পক্ষই বড় ধরনের সংঘাতে জড়াতে চায় না, কারণ তারা ইতিমধ্যেই অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও নিরাপত্তাগত সমস্যায় জর্জরিত। পাকিস্তান টিটিপির হামলা মোকাবিলায় লড়ছে এবং আফগানিস্তানও তাদের ভূখণ্ডে তালেবান বাহিনীর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। কূটনৈতিক প্রচেষ্টা এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যস্থতা ছাড়া এই সংকট সমাধান সম্ভব নয়।
পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্ত সংঘাত কেবল সামরিক উত্তেজনার বিষয় নয়। এটি আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা, আন্তর্জাতিক কূটনীতি এবং মানবিক নিরাপত্তার জন্য বহুমাত্রিক সংকট। কূটনৈতিক প্রচেষ্টা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং উভয় দেশের আন্তরিকতা ছাড়া এই সংকট সমাধান সম্ভব নয়। দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে, উভয় দেশকে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের দিকে মনোযোগী হতে হবে।

দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতি প্রাচীনকাল থেকে বহুপক্ষীয়, জটিল এবং কয়েকটি দেশের আধিপত্যবাদী স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। বিশেষ করে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমান্ত এলাকা, যা প্রাচীনকাল থেকে সামরিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অস্থিরতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচিত। সাম্প্রতিক সংঘাতের মাধ্যমে তা আবারও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য গুরুতর হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সীমান্তের এই অস্থিরতা কেবল দুই দেশের মধ্যে সামরিক উত্তেজনায় সীমাবদ্ধ নয়; এটি দক্ষিণ এশিয়ার কূটনীতি, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা, মানবিক পরিস্থিতি এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করছে।
২০২৫ সালের ৯ অক্টোবর কাবুলের আবদুল হাক্ক স্কয়ারে দুটি বিস্ফোরণ ঘটে, যা পুরো শহরকে আতঙ্কের ছায়ায় আচ্ছন্ন করে। এই বিস্ফোরণকে পাকিস্তান সরকার তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি) প্রধান নূর ওয়ালি মেহসুদকে লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে বলে দাবি করা হয়। যদিও মেহসুদ নিজে একটি অডিও বার্তায় বেঁচে থাকার ঘোষণা দেন। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ১১ অক্টোবর রাতে আফগান বাহিনী পাকিস্তানি সীমান্তচৌকিগুলোতে পাল্টা হামলা চালায়। এই আক্রমণে পাকিস্তান তার ২৩ সেনা সদস্যকে হারায়। তবে পাল্টা হামলায় তারা দাবি করে, ২০০ তালেবান এবং তাদের সহযোগী সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। আফগান বাহিনী ঘোষণা করে, তারা সীমান্তে ২৫টি পাকিস্তানি চৌকি দখল করেছে। এর পরপরই তোরখাম, চামান এবং অন্যান্য প্রধান সীমান্তচৌকিগুলো বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বাণিজ্য, পরিবহন এবং সাধারণ জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাপনে মারাত্মকভাবে প্রভাব ফেলে।
সীমান্ত সংঘাতের পেছনে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক জটিলতা রয়েছে। পাকিস্তান দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ করে আসছে, আফগান সরকার তাদের ভূখণ্ডে টিটিপি সদস্যদের নিরাপদ আশ্রয় দিচ্ছে। আফগান প্রশাসন এই অভিযোগ অস্বীকার করলেও পাকিস্তানের অভ্যন্তরে টিটিপির হামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিস্থিতি দুই দেশের সম্পর্ককে ক্রমেই উত্তেজনাপূর্ণ করে তুলেছে। ২০২১ সালে তালেবান ক্ষমতায় আসার পর, আফগান ভূখণ্ডে টিটিপির কার্যক্রম বৃদ্ধি পায়। ইসলামাবাদ এই কার্যক্রমকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচনা করছে। আফগানিস্তানের তালেবানরা রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হচ্ছে, যা সীমান্ত অস্থিরতাকে আরও তীব্র করছে।
সীমান্ত সংঘাতের সামরিক দিকও অত্যন্ত জটিল। এ ক্ষেত্রে সংঘাত প্রায়ই গেরিলা যুদ্ধের কৌশলে পরিচালিত হয়। তালেবান বাহিনী হঠাৎ এবং অপ্রত্যাশিত আক্রমণ, দ্রুতগতি, স্থানীয় সমর্থন এবং ট্যাকটিক্যাল অপ্রচলিত কৌশল ব্যবহার করে পাকিস্তানি সীমান্তপ্রহরীদের তুলনায় অধিক কার্যকরভাবে। পাকিস্তানি বাহিনী তুলনামূলকভাবে বড়, আধুনিক ও স্থায়ী। তাদের কাছে প্রচলিত যুদ্ধের প্রযুক্তি রয়েছে—যেমন ট্যাংক, বিমান, পর্যবেক্ষণব্যবস্থা এবং আধুনিক অস্ত্র। তবু গেরিলা কৌশলের কারণে সীমান্তচৌকিগুলো হারাতে পারে। তালেবান বাহিনী স্বল্পসংখ্যক হলেও দ্রুতগতি ও চমকপ্রদ কৌশল ব্যবহার করে কার্যকর আক্রমণ চালায়।
টিটিপি, তালেবান এবং ইসলামিক স্টেট ইন খোরাসান প্রভিন্সের কর্মকাণ্ড সীমান্ত সংঘাতকে আরও জটিল করেছে। টিটিপি পাকিস্তানের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালায়, যার মধ্যে আত্মঘাতী বোমা হামলা এবং অন্যান্য সহিংস কর্মকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত। আফগান ভূখণ্ডে তারা নিরাপদ আশ্রয় পায়। আফগানিস্তান তালেবান বাহিনীর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়, কিন্তু অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সামাজিক প্রতিরোধের কারণে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।
এখনকার দুই দেশের মধ্যে সংঘাতে সীমান্তচৌকিগুলো বন্ধ থাকায় ব্যবসা-বাণিজ্য এবং পরিবহন ব্যাহত হচ্ছে। সীমান্তবর্তী সাধারণ জনগণ মানবিক সংকটের মুখোমুখি হয়েছে। খাদ্য ও স্বাস্থ্যসেবার সীমিত প্রাপ্যতা, আফগান শরণার্থীদের নিরাপদ আশ্রয় না পাওয়া এবং অর্থনৈতিক দুর্ভোগ মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি করছে। সীমান্ত অস্থিরতার কারণে স্থানীয় অর্থনীতি বিপর্যস্ত। তাই আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে মানবিক সহায়তার জন্য এই সংকট প্রশমিত করা প্রয়োজন।
এই সংঘাতে আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতিরও গুরুত্ব আছে। সম্প্রতি ভারতের সঙ্গে আফগানিস্তানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাকিস্তান সন্দেহের চোখে দেখছে। ভারতের কূটনৈতিক নীতির প্রভাব এবং পাকিস্তানের নিরাপত্তা চিন্তা—সবকিছু মিলিত হয়ে সংকটকে আরও জটিল করেছে। সৌদি আরব, কাতার, ইরান, চীন এবং রাশিয়া উভয় পক্ষকে সংযম বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছে। আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতের সফরে শান্তিপূর্ণ সমাধানের ওপর জোর দিয়েছেন। পাকিস্তানও সীমান্তে উত্তেজনা প্রশমনের জন্য কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যেন দ্বিপক্ষীয় সমঝোতার মাধ্যমে উত্তেজনা প্রশমিত করতে পারে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, সীমান্তে উত্তেজনা অব্যাহত থাকলে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও খারাপ হতে পারে। তবে উভয় পক্ষই বড় ধরনের সংঘাতে জড়াতে চায় না, কারণ তারা ইতিমধ্যেই অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও নিরাপত্তাগত সমস্যায় জর্জরিত। পাকিস্তান টিটিপির হামলা মোকাবিলায় লড়ছে এবং আফগানিস্তানও তাদের ভূখণ্ডে তালেবান বাহিনীর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। কূটনৈতিক প্রচেষ্টা এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যস্থতা ছাড়া এই সংকট সমাধান সম্ভব নয়।
পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্ত সংঘাত কেবল সামরিক উত্তেজনার বিষয় নয়। এটি আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা, আন্তর্জাতিক কূটনীতি এবং মানবিক নিরাপত্তার জন্য বহুমাত্রিক সংকট। কূটনৈতিক প্রচেষ্টা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং উভয় দেশের আন্তরিকতা ছাড়া এই সংকট সমাধান সম্ভব নয়। দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে, উভয় দেশকে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের দিকে মনোযোগী হতে হবে।
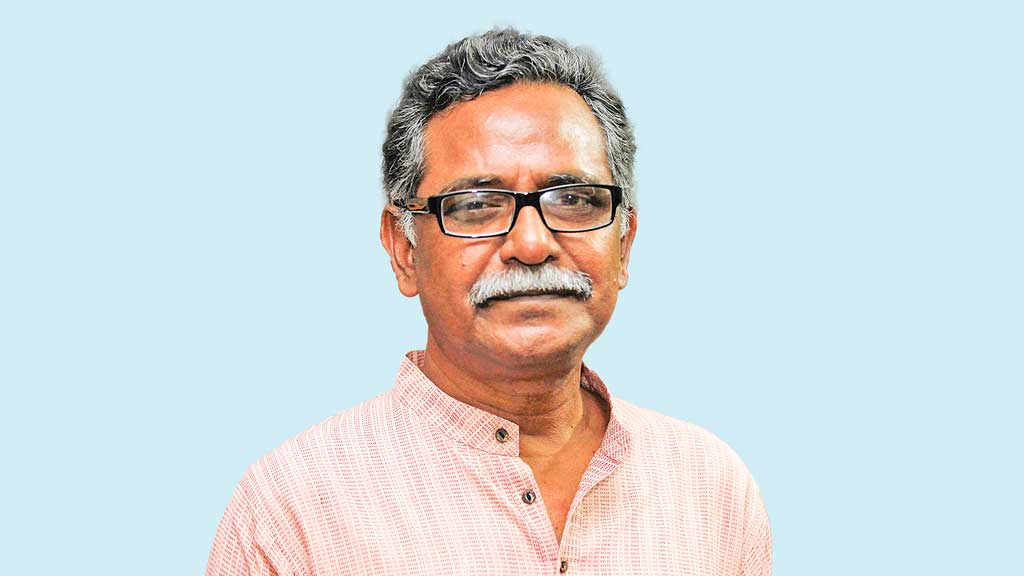
আনু মুহাম্মদ বাংলাদেশের একজন অন্যতম গণবুদ্ধিজীবী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক, একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির অন্যতম সংগঠক, তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সাবেক সদস্যসচিব।
১০ আগস্ট ২০২৫
হাত-পা বেঁধে ইচ্ছেমতো পিটিয়েছে স্থানীয় লোকজন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সেই ছিনতাইকারীর। সেখানে ঘটনা থেমে থাকেনি, লোকটির শরীরে লবণ দিয়ে উল্লাস করতে থাকে জনতা। টঙ্গীর স্টেশন রোড এলাকায় প্রতিদিন গড়ে ২০টি করে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। এটা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভয়াবহ অবস্থারই ইঙ্গিত দেয়।
১৮ ঘণ্টা আগে
মধ্যযুগে রাজা-বাদশাহ-সম্রাটরা গায়ের জোরে দুর্বল রাজ্যগুলোকে দখলে নিতেন। রাজ্য দখলের সেসব লড়াইয়ে বেঘোরে প্রাণ হারাত হাজার হাজার সাধারণ মানুষ। সে যুগ গত হয়েছে বহু আগে। আধুনিক যুগে রাজ্য গলাধঃকরণ দুঃস্বপ্নেও কেউ কল্পনা করতে চাইবে না। কিন্তু সেই বিষয়টিই ইউক্রেনের জন্য বাস্তবতা হয়ে উঠেছে।
১৮ ঘণ্টা আগে
‘ওয়েপনাইজেশন অব এভরিথিং’ মানে ‘সবকিছুর অস্ত্রীকরণ’ করা—কথাটি এখন আর কল্পনা নয়, বৈশ্বিক রাজনীতির নির্মম বাস্তবতা। শক্তির ভারসাম্য এখন কেবল পারমাণবিক বোমা বা তেল ও গ্যাসক্ষেত্রের ওপর নির্ভর করে না। আজকে ভূ-রাজনীতির খেলার বস্তু হয়ে উঠছে বিরল মৃত্তিকা খনিজ পদার্থগুলো।
১৮ ঘণ্টা আগে