আজকের পত্রিকা ডেস্ক
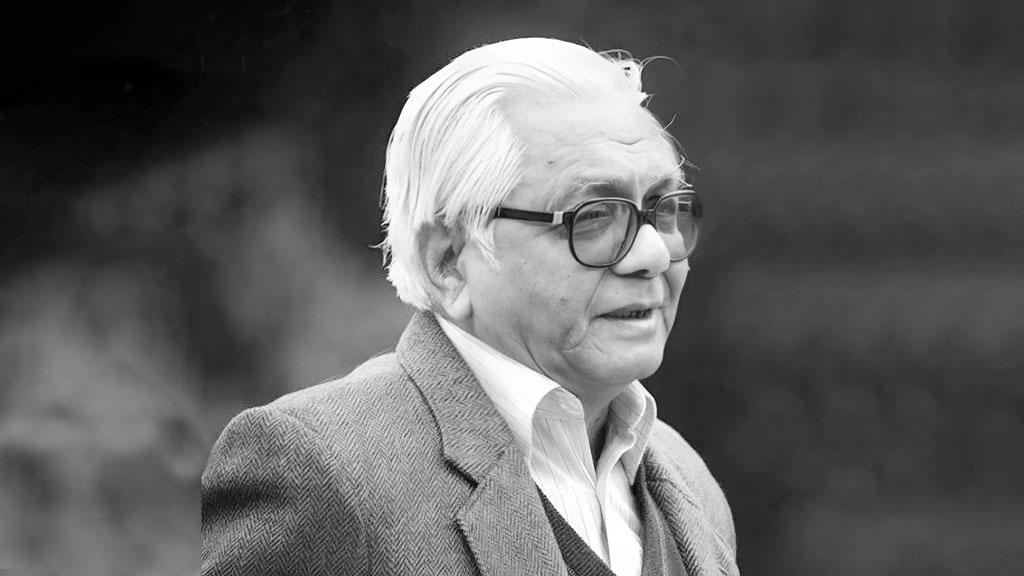
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, লেখক, গবেষক এবং বাম ধারার বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দীন উমর ৯৪ বছর বয়সে মারা গেছেন। আজ রোববার সকালে ঢাকার বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় ভুগছিলেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে দেশের প্রগতিশীল ও বুদ্ধিবৃত্তিক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
জন্ম ও শিক্ষা
বদরুদ্দীন উমর ১৯৩১ সালের ২০ ডিসেম্বর ব্রিটিশ ভারতের বর্ধমান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম আবুল হাশিম ও মাতার নাম মাহমুদা আখতার মেহেরবানু বেগম। পিতা আবুল হাশিম একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন। দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং ১৯৫০ সালে ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। উমর ১৯৪৮ সালে বর্ধমান টাউন স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৫০ সালে তিনি বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাস করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৩ সালে স্নাতক সম্মান ডিগ্রি অর্জন করেন। দর্শন বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৫৫ সালে। ১৯৬১ সালে তিনি যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন, রাজনীতি ও অর্থনীতি (পিপিই) ডিগ্রি লাভ করেন।
অক্সফোর্ডে ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে আসেন এবং ১৯৬৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। গভর্নর মোনায়েম খানের স্বৈরতান্ত্রিক আচরণের প্রতিবাদে ১৯৬৮ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ছেড়ে রাজনীতি ও লেখালেখিতে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর লেখা ‘পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি’ ভাষা আন্দোলনের ওপর প্রথম গবেষণাগ্রন্থ।
শিক্ষক থেকে বুদ্ধিজীবী
বদরুদ্দীন উমর তাঁর পেশাজীবন শুরু করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে। পরবর্তীকালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন, যা তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক অবদানের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শিক্ষকতা জীবনের পাশাপাশি তাঁর রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের বিস্তার ছিল ব্যাপক। তিনি বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের সভাপতি এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। একসময় পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতেও ছিলেন। ২০০৩ সালে তিনি জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে আমৃত্যু সেটির সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন।
ভাষা আন্দোলনের সাহিত্যিক স্থপতি
বদরুদ্দীন উমরের সর্বজনস্বীকৃত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৃতি হচ্ছে তিনটি বিশাল খণ্ডে রচিত ‘পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি’ শীর্ষক গ্রন্থটি। এই গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসকে একটি সুসংহত সাহিত্যিক রূপ দিয়েছেন। রাজনৈতিক সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে বাঙালির মননজগতে বদরুদ্দীন উমরের স্থান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং স্বীকৃত। সাহিত্যিক শংকর তাঁকে ‘ভাষা আন্দোলনের কাশীরাম দাশ’ হিসেবে অভিহিত করে তাঁর এ অবদানের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। আবুল কাসেম ফজলুল হক তাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন, বদরুদ্দীন উমর সম্ভবত সেই সৃষ্টিশীল ধারার পথিকৃৎ, যা বিগত কয়েক দশক ধরে ধীরে ধীরে দানা বাঁধছিল।
এই গ্রন্থ রচনার পটভূমি ছিল ব্যাপক ও গবেষণামূলক। ১৯৬০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ ইতিহাস রচনার জন্য তথ্য সংগ্রহ শুরু করলেও পরে তিনি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস লেখার সিদ্ধান্ত নেন। এই কাজ সম্পন্ন করতে তাঁকে প্রায় কুড়ি বছর (১৯৬৩-৮২) ব্যয় করতে হয়েছে এবং তিন সহস্রাধিক তথ্য-উৎস ব্যবহার করতে হয়েছে। প্রায় ২০০ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতা গ্রহণ করতে হয়েছিল তাঁকে। তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনাটিও ছিল ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে, যা ছিল তাঁর বাবা আবুল হাশিমের অনুরোধে লেখা ‘আমাদের ভাষার লড়াই’ শীর্ষক একটি পুস্তিকা।
গবেষণার নেপথ্যে: চ্যালেঞ্জ ও অধ্যবসায়
বদরুদ্দীন উমরের গবেষণামূলক কাজ ছিল অত্যন্ত শ্রমসাধ্য। ভাষা আন্দোলনের মতো একটি সংবেদনশীল বিষয়ে ইতিহাস লিখতে গিয়ে তিনি নানা সমস্যার সম্মুখীন হন। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল লিখিত তথ্যসূত্রের অভাব এবং স্মৃতিচারণের বিভ্রান্তি। অনেক সময় দেখা গেছে, প্রত্যক্ষদর্শীরাও দুর্বল স্মৃতি বা ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে ভুল তথ্য দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সাক্ষাৎকারের ঘটনাটি যাচাই করতে গিয়ে তিনি দেখেন, আতাউর রহমান খান নিজেকে ওই সাক্ষাৎকারে উপস্থিত বলে দাবি করলেও অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীর মাধ্যমে তা ভুল প্রমাণিত হয়। এসব সমস্যা সত্ত্বেও তিনি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজ করে গেছেন।
তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে তিনি আধুনিক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করেন। তিনি সংবাদপত্র, বিভিন্ন আন্দোলন সম্পর্কিত পুস্তক-পুস্তিকা, পার্টি দলিলপত্র, ইশতেহার এবং তৎকালীন রাজনীতিবিদ ও আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ব্যাপক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। সরকারি কোনো তথ্য উৎস থেকে খুব বেশি সাহায্য তিনি পাননি। তাঁর এই নিরলস পরিশ্রমের ফসল হিসেবেই বাংলা ভাষা আন্দোলন একটি সুসংবদ্ধ ঐতিহাসিক রূপ লাভ করে। তার গ্রন্থত্রয় সম্মিলিতভাবে একটি বিরাট জন-অঞ্চলের সামাজিক জীবনের গভীরতম দলিল, যা পূর্ব বাংলার উজ্জ্বল জীবন-নাট্যকে তুলে ধরে।
রাজনৈতিক দর্শন
বদরুদ্দীন উমর কেবল একজন ইতিহাসবিদ ছিলেন না, তাঁর রচনায় সমাজ, রাজনীতি এবং পার্টির অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর লেখালেখির মূল লক্ষ্য ছিল সমাজের সার্বিক শোষণমুক্তির উদ্দেশ্যে আন্দোলন গড়ে তোলা। বিশ্লেষক হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তীক্ষ্ণ। তাঁর প্রতিটি গ্রন্থ বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিকাশের জন্য একটি মূল্যবান দলিল।
একুশে ফেব্রুয়ারিকে তিনি কেবল ভাষার আন্দোলন হিসেবে দেখেননি, বরং এটিকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিকাশের সংগ্রাম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, ১৯৪৮ এবং ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি মৌলিক পরিবর্তন এনেছিল, যা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির গণবিরোধী চরিত্র সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলে। তাঁর মতে, ভাষা আন্দোলনই পাকিস্তানি নির্যাতনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম ব্যাপক জাতীয় প্রতিরোধ। ভাষা আন্দোলনের ফলে বুর্জোয়া রাজনীতির সাম্প্রদায়িকতা ধর্মনিরপেক্ষতা লাভ করে এবং তা সামনে উঠে আসে।
তবে তিনি ভাষা আন্দোলনের কিছু দুর্বলতার দিকও তুলে ধরেছেন। যেমন, ভাষা আন্দোলনকে সমগ্র পাকিস্তানের সমস্যা হিসেবে দেখতে না পারা এবং এর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চরিত্রের অভাব। তাঁর মতে, ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়গুলোতে এখানকার কমিউনিস্ট পার্টি এই আন্দোলনকে রাজনৈতিকভাবে উপস্থিত করতে ব্যর্থ হয়, কোনো শক্তিশালী সাহিত্যের জন্ম হয় না এবং এর ফসলকে শাসক-শোষকরাই ভোগ করে।
বদরুদ্দীন উমর তাঁর সহজ, অনাড়ম্বর এবং ধারালো গদ্যশৈলীর জন্য পরিচিত। তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন অন্যতম শক্তিশালী গদ্যশিল্পী। তাঁর লেখালেখি, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং শোষিত মানুষের মুক্তির জন্য তাঁর আপোসহীন সংগ্রাম তাঁকে চিরকাল স্মরণীয় করে রাখবে।
জীবনে কখনো পুরস্কার নেননি
বদরুদ্দীন উমরকে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তিনি কোনোটিই গ্রহণ করেননি। সর্বশেষ অন্তর্বর্তী সরকার তাঁকে স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করলেও সেটিও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন।
চলতি বছরের মার্চে স্বাধীনতা পুরস্কারের তালিকায় নাম ঘোষণা করলে এক বিবৃতিতে বদরুদ্দীন উমর বলেন, ‘১৯৭৩ সাল থেকে আমাকে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা থেকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। আমি সেগুলোর কোনোটি গ্রহণ করিনি। এখন বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার আমাকে স্বাধীনতা পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করেছে। এ জন্য তাদের ধন্যবাদ। কিন্তু তাদের দেওয়া এই পুরস্কারও আমার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।’
এর আগে ১৯৭২ সালে বদরুদ্দীন উমরকে বাংলা একাডেমি পুরস্কার দেওয়া হয়, তবে তিনি তা তাৎক্ষণিক প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি ইতিহাস পরিষদের পুরস্কার পান এবং তা প্রত্যাখ্যান করেন।
[১৯৮১ সালে সাপ্তাহিক বিচিত্রা পত্রিকার প্রচ্ছদ প্রতিবেদন অবলম্বনে]
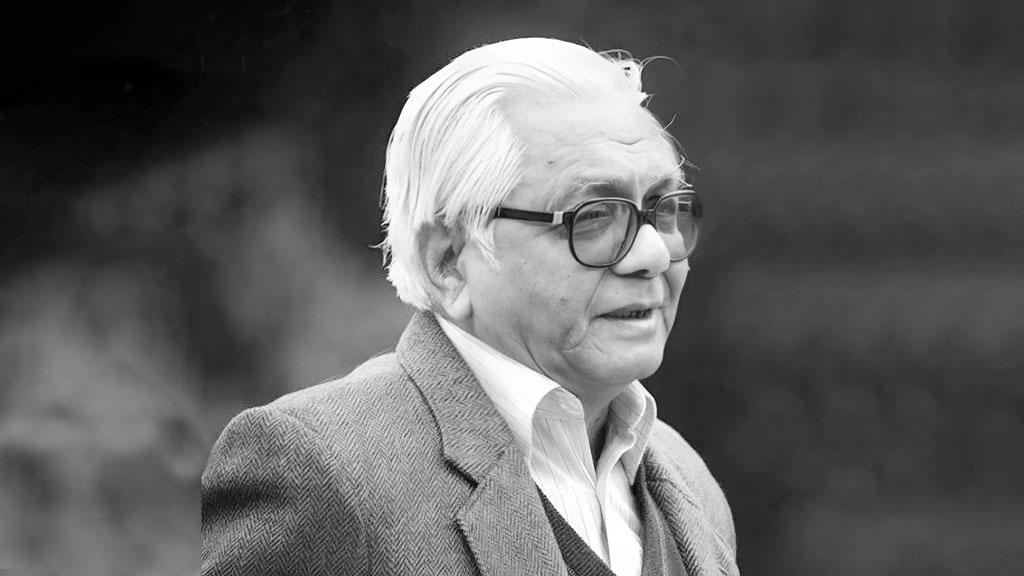
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, লেখক, গবেষক এবং বাম ধারার বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দীন উমর ৯৪ বছর বয়সে মারা গেছেন। আজ রোববার সকালে ঢাকার বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় ভুগছিলেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে দেশের প্রগতিশীল ও বুদ্ধিবৃত্তিক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
জন্ম ও শিক্ষা
বদরুদ্দীন উমর ১৯৩১ সালের ২০ ডিসেম্বর ব্রিটিশ ভারতের বর্ধমান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম আবুল হাশিম ও মাতার নাম মাহমুদা আখতার মেহেরবানু বেগম। পিতা আবুল হাশিম একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন। দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং ১৯৫০ সালে ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। উমর ১৯৪৮ সালে বর্ধমান টাউন স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৫০ সালে তিনি বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাস করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৩ সালে স্নাতক সম্মান ডিগ্রি অর্জন করেন। দর্শন বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৫৫ সালে। ১৯৬১ সালে তিনি যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন, রাজনীতি ও অর্থনীতি (পিপিই) ডিগ্রি লাভ করেন।
অক্সফোর্ডে ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে আসেন এবং ১৯৬৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। গভর্নর মোনায়েম খানের স্বৈরতান্ত্রিক আচরণের প্রতিবাদে ১৯৬৮ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ছেড়ে রাজনীতি ও লেখালেখিতে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর লেখা ‘পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি’ ভাষা আন্দোলনের ওপর প্রথম গবেষণাগ্রন্থ।
শিক্ষক থেকে বুদ্ধিজীবী
বদরুদ্দীন উমর তাঁর পেশাজীবন শুরু করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে। পরবর্তীকালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন, যা তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক অবদানের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শিক্ষকতা জীবনের পাশাপাশি তাঁর রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের বিস্তার ছিল ব্যাপক। তিনি বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের সভাপতি এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। একসময় পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতেও ছিলেন। ২০০৩ সালে তিনি জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে আমৃত্যু সেটির সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন।
ভাষা আন্দোলনের সাহিত্যিক স্থপতি
বদরুদ্দীন উমরের সর্বজনস্বীকৃত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৃতি হচ্ছে তিনটি বিশাল খণ্ডে রচিত ‘পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি’ শীর্ষক গ্রন্থটি। এই গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসকে একটি সুসংহত সাহিত্যিক রূপ দিয়েছেন। রাজনৈতিক সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে বাঙালির মননজগতে বদরুদ্দীন উমরের স্থান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং স্বীকৃত। সাহিত্যিক শংকর তাঁকে ‘ভাষা আন্দোলনের কাশীরাম দাশ’ হিসেবে অভিহিত করে তাঁর এ অবদানের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। আবুল কাসেম ফজলুল হক তাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন, বদরুদ্দীন উমর সম্ভবত সেই সৃষ্টিশীল ধারার পথিকৃৎ, যা বিগত কয়েক দশক ধরে ধীরে ধীরে দানা বাঁধছিল।
এই গ্রন্থ রচনার পটভূমি ছিল ব্যাপক ও গবেষণামূলক। ১৯৬০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ ইতিহাস রচনার জন্য তথ্য সংগ্রহ শুরু করলেও পরে তিনি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস লেখার সিদ্ধান্ত নেন। এই কাজ সম্পন্ন করতে তাঁকে প্রায় কুড়ি বছর (১৯৬৩-৮২) ব্যয় করতে হয়েছে এবং তিন সহস্রাধিক তথ্য-উৎস ব্যবহার করতে হয়েছে। প্রায় ২০০ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতা গ্রহণ করতে হয়েছিল তাঁকে। তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনাটিও ছিল ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে, যা ছিল তাঁর বাবা আবুল হাশিমের অনুরোধে লেখা ‘আমাদের ভাষার লড়াই’ শীর্ষক একটি পুস্তিকা।
গবেষণার নেপথ্যে: চ্যালেঞ্জ ও অধ্যবসায়
বদরুদ্দীন উমরের গবেষণামূলক কাজ ছিল অত্যন্ত শ্রমসাধ্য। ভাষা আন্দোলনের মতো একটি সংবেদনশীল বিষয়ে ইতিহাস লিখতে গিয়ে তিনি নানা সমস্যার সম্মুখীন হন। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল লিখিত তথ্যসূত্রের অভাব এবং স্মৃতিচারণের বিভ্রান্তি। অনেক সময় দেখা গেছে, প্রত্যক্ষদর্শীরাও দুর্বল স্মৃতি বা ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে ভুল তথ্য দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সাক্ষাৎকারের ঘটনাটি যাচাই করতে গিয়ে তিনি দেখেন, আতাউর রহমান খান নিজেকে ওই সাক্ষাৎকারে উপস্থিত বলে দাবি করলেও অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীর মাধ্যমে তা ভুল প্রমাণিত হয়। এসব সমস্যা সত্ত্বেও তিনি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজ করে গেছেন।
তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে তিনি আধুনিক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করেন। তিনি সংবাদপত্র, বিভিন্ন আন্দোলন সম্পর্কিত পুস্তক-পুস্তিকা, পার্টি দলিলপত্র, ইশতেহার এবং তৎকালীন রাজনীতিবিদ ও আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ব্যাপক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। সরকারি কোনো তথ্য উৎস থেকে খুব বেশি সাহায্য তিনি পাননি। তাঁর এই নিরলস পরিশ্রমের ফসল হিসেবেই বাংলা ভাষা আন্দোলন একটি সুসংবদ্ধ ঐতিহাসিক রূপ লাভ করে। তার গ্রন্থত্রয় সম্মিলিতভাবে একটি বিরাট জন-অঞ্চলের সামাজিক জীবনের গভীরতম দলিল, যা পূর্ব বাংলার উজ্জ্বল জীবন-নাট্যকে তুলে ধরে।
রাজনৈতিক দর্শন
বদরুদ্দীন উমর কেবল একজন ইতিহাসবিদ ছিলেন না, তাঁর রচনায় সমাজ, রাজনীতি এবং পার্টির অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর লেখালেখির মূল লক্ষ্য ছিল সমাজের সার্বিক শোষণমুক্তির উদ্দেশ্যে আন্দোলন গড়ে তোলা। বিশ্লেষক হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তীক্ষ্ণ। তাঁর প্রতিটি গ্রন্থ বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিকাশের জন্য একটি মূল্যবান দলিল।
একুশে ফেব্রুয়ারিকে তিনি কেবল ভাষার আন্দোলন হিসেবে দেখেননি, বরং এটিকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিকাশের সংগ্রাম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, ১৯৪৮ এবং ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি মৌলিক পরিবর্তন এনেছিল, যা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির গণবিরোধী চরিত্র সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলে। তাঁর মতে, ভাষা আন্দোলনই পাকিস্তানি নির্যাতনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম ব্যাপক জাতীয় প্রতিরোধ। ভাষা আন্দোলনের ফলে বুর্জোয়া রাজনীতির সাম্প্রদায়িকতা ধর্মনিরপেক্ষতা লাভ করে এবং তা সামনে উঠে আসে।
তবে তিনি ভাষা আন্দোলনের কিছু দুর্বলতার দিকও তুলে ধরেছেন। যেমন, ভাষা আন্দোলনকে সমগ্র পাকিস্তানের সমস্যা হিসেবে দেখতে না পারা এবং এর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চরিত্রের অভাব। তাঁর মতে, ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়গুলোতে এখানকার কমিউনিস্ট পার্টি এই আন্দোলনকে রাজনৈতিকভাবে উপস্থিত করতে ব্যর্থ হয়, কোনো শক্তিশালী সাহিত্যের জন্ম হয় না এবং এর ফসলকে শাসক-শোষকরাই ভোগ করে।
বদরুদ্দীন উমর তাঁর সহজ, অনাড়ম্বর এবং ধারালো গদ্যশৈলীর জন্য পরিচিত। তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন অন্যতম শক্তিশালী গদ্যশিল্পী। তাঁর লেখালেখি, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং শোষিত মানুষের মুক্তির জন্য তাঁর আপোসহীন সংগ্রাম তাঁকে চিরকাল স্মরণীয় করে রাখবে।
জীবনে কখনো পুরস্কার নেননি
বদরুদ্দীন উমরকে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তিনি কোনোটিই গ্রহণ করেননি। সর্বশেষ অন্তর্বর্তী সরকার তাঁকে স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করলেও সেটিও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন।
চলতি বছরের মার্চে স্বাধীনতা পুরস্কারের তালিকায় নাম ঘোষণা করলে এক বিবৃতিতে বদরুদ্দীন উমর বলেন, ‘১৯৭৩ সাল থেকে আমাকে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা থেকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। আমি সেগুলোর কোনোটি গ্রহণ করিনি। এখন বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার আমাকে স্বাধীনতা পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করেছে। এ জন্য তাদের ধন্যবাদ। কিন্তু তাদের দেওয়া এই পুরস্কারও আমার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।’
এর আগে ১৯৭২ সালে বদরুদ্দীন উমরকে বাংলা একাডেমি পুরস্কার দেওয়া হয়, তবে তিনি তা তাৎক্ষণিক প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি ইতিহাস পরিষদের পুরস্কার পান এবং তা প্রত্যাখ্যান করেন।
[১৯৮১ সালে সাপ্তাহিক বিচিত্রা পত্রিকার প্রচ্ছদ প্রতিবেদন অবলম্বনে]
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
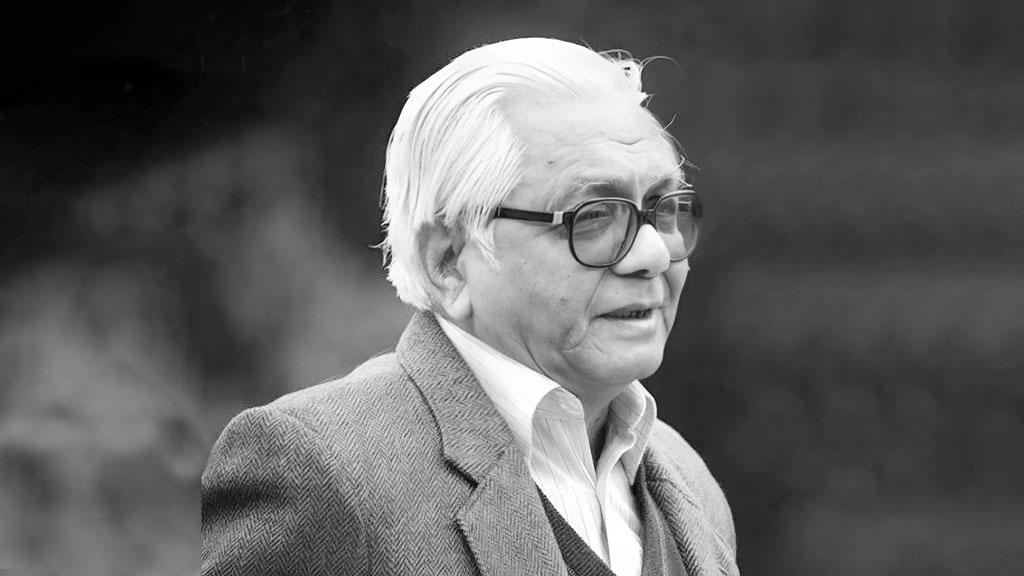
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, লেখক, গবেষক এবং বাম ধারার বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দীন উমর ৯৪ বছর বয়সে মারা গেছেন। আজ রোববার সকালে ঢাকার বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় ভুগছিলেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে দেশের প্রগতিশীল ও বুদ্ধিবৃত্তিক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
জন্ম ও শিক্ষা
বদরুদ্দীন উমর ১৯৩১ সালের ২০ ডিসেম্বর ব্রিটিশ ভারতের বর্ধমান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম আবুল হাশিম ও মাতার নাম মাহমুদা আখতার মেহেরবানু বেগম। পিতা আবুল হাশিম একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন। দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং ১৯৫০ সালে ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। উমর ১৯৪৮ সালে বর্ধমান টাউন স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৫০ সালে তিনি বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাস করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৩ সালে স্নাতক সম্মান ডিগ্রি অর্জন করেন। দর্শন বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৫৫ সালে। ১৯৬১ সালে তিনি যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন, রাজনীতি ও অর্থনীতি (পিপিই) ডিগ্রি লাভ করেন।
অক্সফোর্ডে ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে আসেন এবং ১৯৬৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। গভর্নর মোনায়েম খানের স্বৈরতান্ত্রিক আচরণের প্রতিবাদে ১৯৬৮ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ছেড়ে রাজনীতি ও লেখালেখিতে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর লেখা ‘পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি’ ভাষা আন্দোলনের ওপর প্রথম গবেষণাগ্রন্থ।
শিক্ষক থেকে বুদ্ধিজীবী
বদরুদ্দীন উমর তাঁর পেশাজীবন শুরু করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে। পরবর্তীকালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন, যা তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক অবদানের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শিক্ষকতা জীবনের পাশাপাশি তাঁর রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের বিস্তার ছিল ব্যাপক। তিনি বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের সভাপতি এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। একসময় পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতেও ছিলেন। ২০০৩ সালে তিনি জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে আমৃত্যু সেটির সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন।
ভাষা আন্দোলনের সাহিত্যিক স্থপতি
বদরুদ্দীন উমরের সর্বজনস্বীকৃত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৃতি হচ্ছে তিনটি বিশাল খণ্ডে রচিত ‘পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি’ শীর্ষক গ্রন্থটি। এই গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসকে একটি সুসংহত সাহিত্যিক রূপ দিয়েছেন। রাজনৈতিক সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে বাঙালির মননজগতে বদরুদ্দীন উমরের স্থান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং স্বীকৃত। সাহিত্যিক শংকর তাঁকে ‘ভাষা আন্দোলনের কাশীরাম দাশ’ হিসেবে অভিহিত করে তাঁর এ অবদানের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। আবুল কাসেম ফজলুল হক তাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন, বদরুদ্দীন উমর সম্ভবত সেই সৃষ্টিশীল ধারার পথিকৃৎ, যা বিগত কয়েক দশক ধরে ধীরে ধীরে দানা বাঁধছিল।
এই গ্রন্থ রচনার পটভূমি ছিল ব্যাপক ও গবেষণামূলক। ১৯৬০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ ইতিহাস রচনার জন্য তথ্য সংগ্রহ শুরু করলেও পরে তিনি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস লেখার সিদ্ধান্ত নেন। এই কাজ সম্পন্ন করতে তাঁকে প্রায় কুড়ি বছর (১৯৬৩-৮২) ব্যয় করতে হয়েছে এবং তিন সহস্রাধিক তথ্য-উৎস ব্যবহার করতে হয়েছে। প্রায় ২০০ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতা গ্রহণ করতে হয়েছিল তাঁকে। তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনাটিও ছিল ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে, যা ছিল তাঁর বাবা আবুল হাশিমের অনুরোধে লেখা ‘আমাদের ভাষার লড়াই’ শীর্ষক একটি পুস্তিকা।
গবেষণার নেপথ্যে: চ্যালেঞ্জ ও অধ্যবসায়
বদরুদ্দীন উমরের গবেষণামূলক কাজ ছিল অত্যন্ত শ্রমসাধ্য। ভাষা আন্দোলনের মতো একটি সংবেদনশীল বিষয়ে ইতিহাস লিখতে গিয়ে তিনি নানা সমস্যার সম্মুখীন হন। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল লিখিত তথ্যসূত্রের অভাব এবং স্মৃতিচারণের বিভ্রান্তি। অনেক সময় দেখা গেছে, প্রত্যক্ষদর্শীরাও দুর্বল স্মৃতি বা ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে ভুল তথ্য দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সাক্ষাৎকারের ঘটনাটি যাচাই করতে গিয়ে তিনি দেখেন, আতাউর রহমান খান নিজেকে ওই সাক্ষাৎকারে উপস্থিত বলে দাবি করলেও অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীর মাধ্যমে তা ভুল প্রমাণিত হয়। এসব সমস্যা সত্ত্বেও তিনি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজ করে গেছেন।
তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে তিনি আধুনিক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করেন। তিনি সংবাদপত্র, বিভিন্ন আন্দোলন সম্পর্কিত পুস্তক-পুস্তিকা, পার্টি দলিলপত্র, ইশতেহার এবং তৎকালীন রাজনীতিবিদ ও আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ব্যাপক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। সরকারি কোনো তথ্য উৎস থেকে খুব বেশি সাহায্য তিনি পাননি। তাঁর এই নিরলস পরিশ্রমের ফসল হিসেবেই বাংলা ভাষা আন্দোলন একটি সুসংবদ্ধ ঐতিহাসিক রূপ লাভ করে। তার গ্রন্থত্রয় সম্মিলিতভাবে একটি বিরাট জন-অঞ্চলের সামাজিক জীবনের গভীরতম দলিল, যা পূর্ব বাংলার উজ্জ্বল জীবন-নাট্যকে তুলে ধরে।
রাজনৈতিক দর্শন
বদরুদ্দীন উমর কেবল একজন ইতিহাসবিদ ছিলেন না, তাঁর রচনায় সমাজ, রাজনীতি এবং পার্টির অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর লেখালেখির মূল লক্ষ্য ছিল সমাজের সার্বিক শোষণমুক্তির উদ্দেশ্যে আন্দোলন গড়ে তোলা। বিশ্লেষক হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তীক্ষ্ণ। তাঁর প্রতিটি গ্রন্থ বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিকাশের জন্য একটি মূল্যবান দলিল।
একুশে ফেব্রুয়ারিকে তিনি কেবল ভাষার আন্দোলন হিসেবে দেখেননি, বরং এটিকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিকাশের সংগ্রাম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, ১৯৪৮ এবং ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি মৌলিক পরিবর্তন এনেছিল, যা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির গণবিরোধী চরিত্র সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলে। তাঁর মতে, ভাষা আন্দোলনই পাকিস্তানি নির্যাতনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম ব্যাপক জাতীয় প্রতিরোধ। ভাষা আন্দোলনের ফলে বুর্জোয়া রাজনীতির সাম্প্রদায়িকতা ধর্মনিরপেক্ষতা লাভ করে এবং তা সামনে উঠে আসে।
তবে তিনি ভাষা আন্দোলনের কিছু দুর্বলতার দিকও তুলে ধরেছেন। যেমন, ভাষা আন্দোলনকে সমগ্র পাকিস্তানের সমস্যা হিসেবে দেখতে না পারা এবং এর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চরিত্রের অভাব। তাঁর মতে, ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়গুলোতে এখানকার কমিউনিস্ট পার্টি এই আন্দোলনকে রাজনৈতিকভাবে উপস্থিত করতে ব্যর্থ হয়, কোনো শক্তিশালী সাহিত্যের জন্ম হয় না এবং এর ফসলকে শাসক-শোষকরাই ভোগ করে।
বদরুদ্দীন উমর তাঁর সহজ, অনাড়ম্বর এবং ধারালো গদ্যশৈলীর জন্য পরিচিত। তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন অন্যতম শক্তিশালী গদ্যশিল্পী। তাঁর লেখালেখি, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং শোষিত মানুষের মুক্তির জন্য তাঁর আপোসহীন সংগ্রাম তাঁকে চিরকাল স্মরণীয় করে রাখবে।
জীবনে কখনো পুরস্কার নেননি
বদরুদ্দীন উমরকে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তিনি কোনোটিই গ্রহণ করেননি। সর্বশেষ অন্তর্বর্তী সরকার তাঁকে স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করলেও সেটিও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন।
চলতি বছরের মার্চে স্বাধীনতা পুরস্কারের তালিকায় নাম ঘোষণা করলে এক বিবৃতিতে বদরুদ্দীন উমর বলেন, ‘১৯৭৩ সাল থেকে আমাকে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা থেকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। আমি সেগুলোর কোনোটি গ্রহণ করিনি। এখন বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার আমাকে স্বাধীনতা পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করেছে। এ জন্য তাদের ধন্যবাদ। কিন্তু তাদের দেওয়া এই পুরস্কারও আমার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।’
এর আগে ১৯৭২ সালে বদরুদ্দীন উমরকে বাংলা একাডেমি পুরস্কার দেওয়া হয়, তবে তিনি তা তাৎক্ষণিক প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি ইতিহাস পরিষদের পুরস্কার পান এবং তা প্রত্যাখ্যান করেন।
[১৯৮১ সালে সাপ্তাহিক বিচিত্রা পত্রিকার প্রচ্ছদ প্রতিবেদন অবলম্বনে]
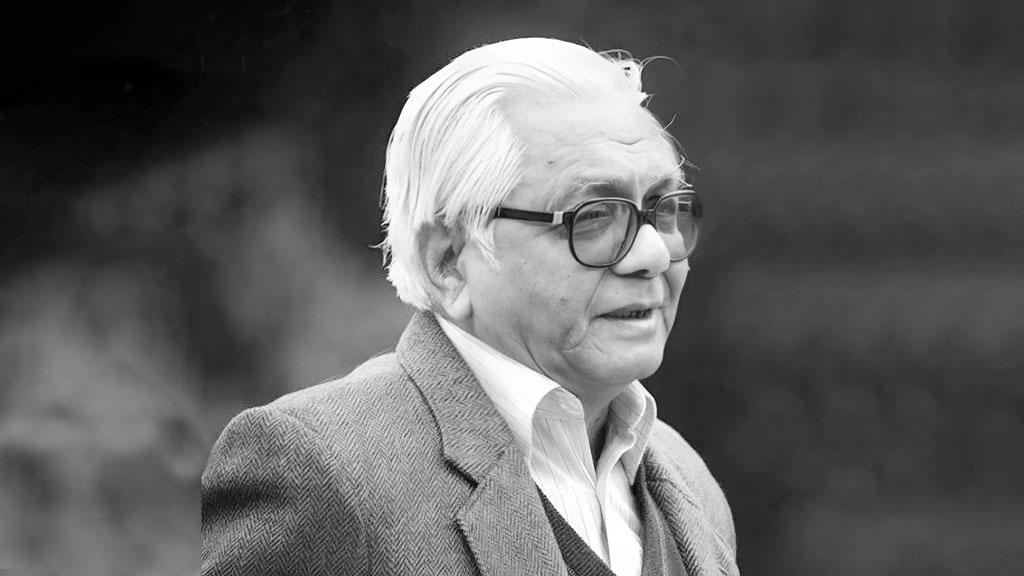
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, লেখক, গবেষক এবং বাম ধারার বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দীন উমর ৯৪ বছর বয়সে মারা গেছেন। আজ রোববার সকালে ঢাকার বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় ভুগছিলেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে দেশের প্রগতিশীল ও বুদ্ধিবৃত্তিক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
জন্ম ও শিক্ষা
বদরুদ্দীন উমর ১৯৩১ সালের ২০ ডিসেম্বর ব্রিটিশ ভারতের বর্ধমান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম আবুল হাশিম ও মাতার নাম মাহমুদা আখতার মেহেরবানু বেগম। পিতা আবুল হাশিম একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন। দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং ১৯৫০ সালে ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। উমর ১৯৪৮ সালে বর্ধমান টাউন স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৫০ সালে তিনি বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাস করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৩ সালে স্নাতক সম্মান ডিগ্রি অর্জন করেন। দর্শন বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৫৫ সালে। ১৯৬১ সালে তিনি যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন, রাজনীতি ও অর্থনীতি (পিপিই) ডিগ্রি লাভ করেন।
অক্সফোর্ডে ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে আসেন এবং ১৯৬৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। গভর্নর মোনায়েম খানের স্বৈরতান্ত্রিক আচরণের প্রতিবাদে ১৯৬৮ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ছেড়ে রাজনীতি ও লেখালেখিতে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর লেখা ‘পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি’ ভাষা আন্দোলনের ওপর প্রথম গবেষণাগ্রন্থ।
শিক্ষক থেকে বুদ্ধিজীবী
বদরুদ্দীন উমর তাঁর পেশাজীবন শুরু করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে। পরবর্তীকালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন, যা তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক অবদানের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শিক্ষকতা জীবনের পাশাপাশি তাঁর রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের বিস্তার ছিল ব্যাপক। তিনি বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের সভাপতি এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। একসময় পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতেও ছিলেন। ২০০৩ সালে তিনি জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে আমৃত্যু সেটির সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন।
ভাষা আন্দোলনের সাহিত্যিক স্থপতি
বদরুদ্দীন উমরের সর্বজনস্বীকৃত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৃতি হচ্ছে তিনটি বিশাল খণ্ডে রচিত ‘পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি’ শীর্ষক গ্রন্থটি। এই গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসকে একটি সুসংহত সাহিত্যিক রূপ দিয়েছেন। রাজনৈতিক সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে বাঙালির মননজগতে বদরুদ্দীন উমরের স্থান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং স্বীকৃত। সাহিত্যিক শংকর তাঁকে ‘ভাষা আন্দোলনের কাশীরাম দাশ’ হিসেবে অভিহিত করে তাঁর এ অবদানের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। আবুল কাসেম ফজলুল হক তাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন, বদরুদ্দীন উমর সম্ভবত সেই সৃষ্টিশীল ধারার পথিকৃৎ, যা বিগত কয়েক দশক ধরে ধীরে ধীরে দানা বাঁধছিল।
এই গ্রন্থ রচনার পটভূমি ছিল ব্যাপক ও গবেষণামূলক। ১৯৬০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ ইতিহাস রচনার জন্য তথ্য সংগ্রহ শুরু করলেও পরে তিনি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস লেখার সিদ্ধান্ত নেন। এই কাজ সম্পন্ন করতে তাঁকে প্রায় কুড়ি বছর (১৯৬৩-৮২) ব্যয় করতে হয়েছে এবং তিন সহস্রাধিক তথ্য-উৎস ব্যবহার করতে হয়েছে। প্রায় ২০০ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতা গ্রহণ করতে হয়েছিল তাঁকে। তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনাটিও ছিল ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে, যা ছিল তাঁর বাবা আবুল হাশিমের অনুরোধে লেখা ‘আমাদের ভাষার লড়াই’ শীর্ষক একটি পুস্তিকা।
গবেষণার নেপথ্যে: চ্যালেঞ্জ ও অধ্যবসায়
বদরুদ্দীন উমরের গবেষণামূলক কাজ ছিল অত্যন্ত শ্রমসাধ্য। ভাষা আন্দোলনের মতো একটি সংবেদনশীল বিষয়ে ইতিহাস লিখতে গিয়ে তিনি নানা সমস্যার সম্মুখীন হন। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল লিখিত তথ্যসূত্রের অভাব এবং স্মৃতিচারণের বিভ্রান্তি। অনেক সময় দেখা গেছে, প্রত্যক্ষদর্শীরাও দুর্বল স্মৃতি বা ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে ভুল তথ্য দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সাক্ষাৎকারের ঘটনাটি যাচাই করতে গিয়ে তিনি দেখেন, আতাউর রহমান খান নিজেকে ওই সাক্ষাৎকারে উপস্থিত বলে দাবি করলেও অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীর মাধ্যমে তা ভুল প্রমাণিত হয়। এসব সমস্যা সত্ত্বেও তিনি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজ করে গেছেন।
তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে তিনি আধুনিক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করেন। তিনি সংবাদপত্র, বিভিন্ন আন্দোলন সম্পর্কিত পুস্তক-পুস্তিকা, পার্টি দলিলপত্র, ইশতেহার এবং তৎকালীন রাজনীতিবিদ ও আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ব্যাপক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। সরকারি কোনো তথ্য উৎস থেকে খুব বেশি সাহায্য তিনি পাননি। তাঁর এই নিরলস পরিশ্রমের ফসল হিসেবেই বাংলা ভাষা আন্দোলন একটি সুসংবদ্ধ ঐতিহাসিক রূপ লাভ করে। তার গ্রন্থত্রয় সম্মিলিতভাবে একটি বিরাট জন-অঞ্চলের সামাজিক জীবনের গভীরতম দলিল, যা পূর্ব বাংলার উজ্জ্বল জীবন-নাট্যকে তুলে ধরে।
রাজনৈতিক দর্শন
বদরুদ্দীন উমর কেবল একজন ইতিহাসবিদ ছিলেন না, তাঁর রচনায় সমাজ, রাজনীতি এবং পার্টির অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর লেখালেখির মূল লক্ষ্য ছিল সমাজের সার্বিক শোষণমুক্তির উদ্দেশ্যে আন্দোলন গড়ে তোলা। বিশ্লেষক হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তীক্ষ্ণ। তাঁর প্রতিটি গ্রন্থ বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিকাশের জন্য একটি মূল্যবান দলিল।
একুশে ফেব্রুয়ারিকে তিনি কেবল ভাষার আন্দোলন হিসেবে দেখেননি, বরং এটিকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিকাশের সংগ্রাম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, ১৯৪৮ এবং ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি মৌলিক পরিবর্তন এনেছিল, যা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির গণবিরোধী চরিত্র সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলে। তাঁর মতে, ভাষা আন্দোলনই পাকিস্তানি নির্যাতনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম ব্যাপক জাতীয় প্রতিরোধ। ভাষা আন্দোলনের ফলে বুর্জোয়া রাজনীতির সাম্প্রদায়িকতা ধর্মনিরপেক্ষতা লাভ করে এবং তা সামনে উঠে আসে।
তবে তিনি ভাষা আন্দোলনের কিছু দুর্বলতার দিকও তুলে ধরেছেন। যেমন, ভাষা আন্দোলনকে সমগ্র পাকিস্তানের সমস্যা হিসেবে দেখতে না পারা এবং এর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চরিত্রের অভাব। তাঁর মতে, ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়গুলোতে এখানকার কমিউনিস্ট পার্টি এই আন্দোলনকে রাজনৈতিকভাবে উপস্থিত করতে ব্যর্থ হয়, কোনো শক্তিশালী সাহিত্যের জন্ম হয় না এবং এর ফসলকে শাসক-শোষকরাই ভোগ করে।
বদরুদ্দীন উমর তাঁর সহজ, অনাড়ম্বর এবং ধারালো গদ্যশৈলীর জন্য পরিচিত। তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন অন্যতম শক্তিশালী গদ্যশিল্পী। তাঁর লেখালেখি, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং শোষিত মানুষের মুক্তির জন্য তাঁর আপোসহীন সংগ্রাম তাঁকে চিরকাল স্মরণীয় করে রাখবে।
জীবনে কখনো পুরস্কার নেননি
বদরুদ্দীন উমরকে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তিনি কোনোটিই গ্রহণ করেননি। সর্বশেষ অন্তর্বর্তী সরকার তাঁকে স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করলেও সেটিও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন।
চলতি বছরের মার্চে স্বাধীনতা পুরস্কারের তালিকায় নাম ঘোষণা করলে এক বিবৃতিতে বদরুদ্দীন উমর বলেন, ‘১৯৭৩ সাল থেকে আমাকে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা থেকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। আমি সেগুলোর কোনোটি গ্রহণ করিনি। এখন বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার আমাকে স্বাধীনতা পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করেছে। এ জন্য তাদের ধন্যবাদ। কিন্তু তাদের দেওয়া এই পুরস্কারও আমার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।’
এর আগে ১৯৭২ সালে বদরুদ্দীন উমরকে বাংলা একাডেমি পুরস্কার দেওয়া হয়, তবে তিনি তা তাৎক্ষণিক প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি ইতিহাস পরিষদের পুরস্কার পান এবং তা প্রত্যাখ্যান করেন।
[১৯৮১ সালে সাপ্তাহিক বিচিত্রা পত্রিকার প্রচ্ছদ প্রতিবেদন অবলম্বনে]

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের (সিইসি) নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশনাররা বঙ্গভবনে পৌঁছেছেন। বঙ্গভবনের একটি সূত্র আজকের পত্রিকাকে জানিয়েছেন, আজ বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টায় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ইসির বৈঠকের শিডিউল রাখা আছে।
৩৮ মিনিট আগে
টাঙ্গাইলের শাড়ি বুনন শিল্পকে অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেসকো। গতকাল মঙ্গলবার ভারতের নয়াদিল্লিতে ইউনেসকো কনভেনশনের চলমান ২০তম আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্ষদের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
২ ঘণ্টা আগে
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে ২০২৪ সালের জুলাইয়ে ছাত্র আন্দোলনে অন্যতম সমন্বয়ক হিসেবে সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আসিফ মাহমুদ।
৩ ঘণ্টা আগে
মুক্তিবাহিনীর অগ্রাভিযানে পাকিস্তানি বাহিনীর একের পর এক অবস্থানের পতনে মুক্ত হচ্ছিল বাংলাদেশের একেকটি অঞ্চল। এগিয়ে আসছিল স্বাধীনতার মুহূর্তটি। যদিও ঠিক কখন, কীভাবে সেদিনটি আসবে, তখনো তা স্পষ্ট নয় সাধারণ মানুষের কাছে। তবে সবাই অধীর আগ্রহে ক্ষণ গুনছিল।
৩ ঘণ্টা আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের (সিইসি) নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশনাররা বঙ্গভবনে পৌঁছেছেন।
বঙ্গভবনের একটি সূত্র আজকের পত্রিকাকে জানিয়েছেন, আজ বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টায় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ইসির বৈঠকের শিডিউল রাখা আছে।
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে নির্বাচন কমিশনের সার্বিক প্রস্তুতি ও তফসিল ঘোষণা বিষয়ে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে আলোচনা করতে বঙ্গভবনে গেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন। সিইসি দুপুর ১২টা ২০ মিনিটে বঙ্গভবনে পৌঁছান।
এর আগে ১০টা ৪০ মিনিটে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন কমিশন ভবন থেকে বঙ্গভবনের উদ্দেশে রওনা হন তিনি।
প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে রয়েছেন নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ (অবসরপ্রাপ্ত), তাহমিদা বেগম, মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার ও আব্দুর রহমানেল মাছউদ এবং ইসি সচিব আখতার আহমেদ।
উল্লেখ্য, চলতি সপ্তাহেই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার কথা রয়েছে। তফসিল-সংক্রান্ত ভাষণ রেকর্ড করতে ইতিমধ্যে বিটিভি ও বাংলাদেশ বেতারকে চিঠিও দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের (সিইসি) নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশনাররা বঙ্গভবনে পৌঁছেছেন।
বঙ্গভবনের একটি সূত্র আজকের পত্রিকাকে জানিয়েছেন, আজ বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টায় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ইসির বৈঠকের শিডিউল রাখা আছে।
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে নির্বাচন কমিশনের সার্বিক প্রস্তুতি ও তফসিল ঘোষণা বিষয়ে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে আলোচনা করতে বঙ্গভবনে গেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন। সিইসি দুপুর ১২টা ২০ মিনিটে বঙ্গভবনে পৌঁছান।
এর আগে ১০টা ৪০ মিনিটে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন কমিশন ভবন থেকে বঙ্গভবনের উদ্দেশে রওনা হন তিনি।
প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে রয়েছেন নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ (অবসরপ্রাপ্ত), তাহমিদা বেগম, মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার ও আব্দুর রহমানেল মাছউদ এবং ইসি সচিব আখতার আহমেদ।
উল্লেখ্য, চলতি সপ্তাহেই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার কথা রয়েছে। তফসিল-সংক্রান্ত ভাষণ রেকর্ড করতে ইতিমধ্যে বিটিভি ও বাংলাদেশ বেতারকে চিঠিও দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।
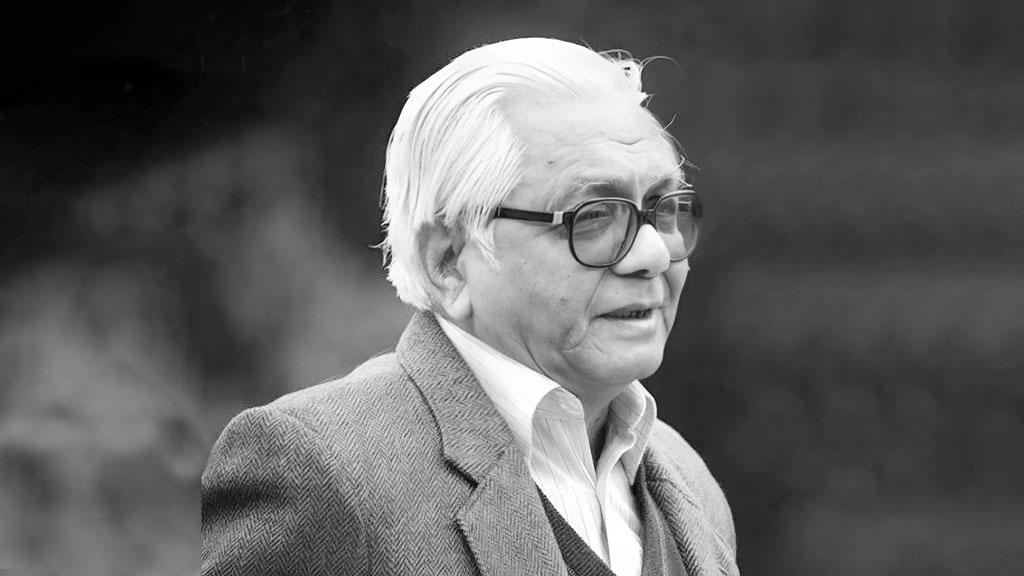
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, লেখক, গবেষক এবং বাম ধারার বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দীন উমর ৯৪ বছর বয়সে মারা গেছেন। আজ রোববার সকালে ঢাকার বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় ভুগছিলেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে...
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
টাঙ্গাইলের শাড়ি বুনন শিল্পকে অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেসকো। গতকাল মঙ্গলবার ভারতের নয়াদিল্লিতে ইউনেসকো কনভেনশনের চলমান ২০তম আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্ষদের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
২ ঘণ্টা আগে
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে ২০২৪ সালের জুলাইয়ে ছাত্র আন্দোলনে অন্যতম সমন্বয়ক হিসেবে সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আসিফ মাহমুদ।
৩ ঘণ্টা আগে
মুক্তিবাহিনীর অগ্রাভিযানে পাকিস্তানি বাহিনীর একের পর এক অবস্থানের পতনে মুক্ত হচ্ছিল বাংলাদেশের একেকটি অঞ্চল। এগিয়ে আসছিল স্বাধীনতার মুহূর্তটি। যদিও ঠিক কখন, কীভাবে সেদিনটি আসবে, তখনো তা স্পষ্ট নয় সাধারণ মানুষের কাছে। তবে সবাই অধীর আগ্রহে ক্ষণ গুনছিল।
৩ ঘণ্টা আগেবাসস, ঢাকা

টাঙ্গাইলের শাড়ি বুনন শিল্পকে অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেসকো। গতকাল মঙ্গলবার ভারতের নয়াদিল্লিতে ইউনেসকো কনভেনশনের চলমান ২০তম আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্ষদের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
এই কনভেনশনের আওতায় এটি বাংলাদেশের ষষ্ঠ একক নিবন্ধন। সভায় প্রথমবারের মতো সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর বিগত চার বছরে এটি দ্বিতীয় নিবন্ধন।
সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের প্রধান এবং ইউনেসকো সাধারণ পরিষদের সভাপতি ও বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত খন্দকার এম. তালহা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় জানান, ‘এই স্বীকৃতি বাংলাদেশের জন্য অসামান্য গৌরবের বিষয়। দীর্ঘ দুই শতকের বেশি সময় ধরে টাঙ্গাইলের তাঁতিদের অনবদ্য শিল্পকর্মের বৈশ্বিক স্বীকৃতি এটি।’
তিনি আরও বলেন, ‘টাঙ্গাইল শাড়ি বাংলাদেশের সকল নারীর নিত্য পরিধেয়, যা এই শাড়ি বুনন শিল্পের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের পেছনে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।’
এই অর্জনকে বাংলাদেশের সকল তাঁতি ও নারীদের প্রতি উৎসর্গ করেছেন রাষ্ট্রদূত খন্দকার এম. তালহা।
বাংলাদেশের অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সামগ্রিক সুরক্ষায় এই স্বীকৃতি নতুন মাত্রা যোগ করবে উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত তালহা বলেন, ঐতিহ্য হিসেবে ইউনেসকোর স্বীকৃতি অর্জনের মতো বাংলাদেশের অপরিমেয় সাংস্কৃতিক উপাদান রয়েছে।
নথি প্রস্তুত করার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কনভেনশন সংক্রান্ত অভিজ্ঞ জনবল তৈরি করার মাধ্যমে আরও অনেক ঐতিহ্যের ইউনেসকো-স্বীকৃতি অর্জনের সুযোগ রয়েছে।
এর আগে, গত ৭ ডিসেম্বর আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্ষদের চলমান ২০তম সভা উদ্বোধন করেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শংকর। অনুষ্ঠানে ইউনেসকোর নবনিযুক্ত মহাপরিচালক খালেদ এল. এনানি উপস্থিত ছিলেন।

টাঙ্গাইলের শাড়ি বুনন শিল্পকে অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেসকো। গতকাল মঙ্গলবার ভারতের নয়াদিল্লিতে ইউনেসকো কনভেনশনের চলমান ২০তম আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্ষদের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
এই কনভেনশনের আওতায় এটি বাংলাদেশের ষষ্ঠ একক নিবন্ধন। সভায় প্রথমবারের মতো সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর বিগত চার বছরে এটি দ্বিতীয় নিবন্ধন।
সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের প্রধান এবং ইউনেসকো সাধারণ পরিষদের সভাপতি ও বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত খন্দকার এম. তালহা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় জানান, ‘এই স্বীকৃতি বাংলাদেশের জন্য অসামান্য গৌরবের বিষয়। দীর্ঘ দুই শতকের বেশি সময় ধরে টাঙ্গাইলের তাঁতিদের অনবদ্য শিল্পকর্মের বৈশ্বিক স্বীকৃতি এটি।’
তিনি আরও বলেন, ‘টাঙ্গাইল শাড়ি বাংলাদেশের সকল নারীর নিত্য পরিধেয়, যা এই শাড়ি বুনন শিল্পের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের পেছনে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।’
এই অর্জনকে বাংলাদেশের সকল তাঁতি ও নারীদের প্রতি উৎসর্গ করেছেন রাষ্ট্রদূত খন্দকার এম. তালহা।
বাংলাদেশের অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সামগ্রিক সুরক্ষায় এই স্বীকৃতি নতুন মাত্রা যোগ করবে উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত তালহা বলেন, ঐতিহ্য হিসেবে ইউনেসকোর স্বীকৃতি অর্জনের মতো বাংলাদেশের অপরিমেয় সাংস্কৃতিক উপাদান রয়েছে।
নথি প্রস্তুত করার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কনভেনশন সংক্রান্ত অভিজ্ঞ জনবল তৈরি করার মাধ্যমে আরও অনেক ঐতিহ্যের ইউনেসকো-স্বীকৃতি অর্জনের সুযোগ রয়েছে।
এর আগে, গত ৭ ডিসেম্বর আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্ষদের চলমান ২০তম সভা উদ্বোধন করেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শংকর। অনুষ্ঠানে ইউনেসকোর নবনিযুক্ত মহাপরিচালক খালেদ এল. এনানি উপস্থিত ছিলেন।
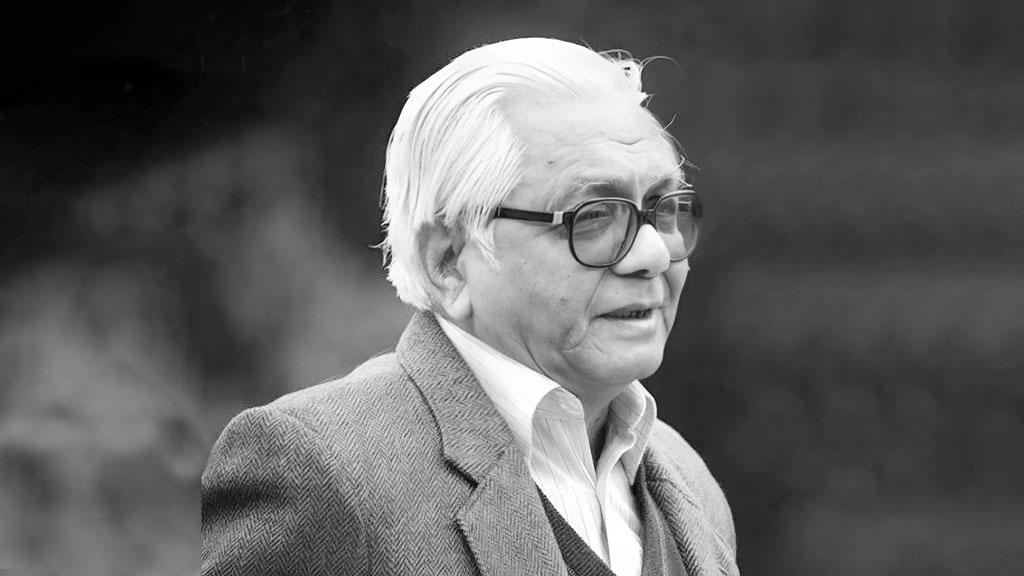
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, লেখক, গবেষক এবং বাম ধারার বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দীন উমর ৯৪ বছর বয়সে মারা গেছেন। আজ রোববার সকালে ঢাকার বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় ভুগছিলেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে...
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের (সিইসি) নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশনাররা বঙ্গভবনে পৌঁছেছেন। বঙ্গভবনের একটি সূত্র আজকের পত্রিকাকে জানিয়েছেন, আজ বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টায় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ইসির বৈঠকের শিডিউল রাখা আছে।
৩৮ মিনিট আগে
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে ২০২৪ সালের জুলাইয়ে ছাত্র আন্দোলনে অন্যতম সমন্বয়ক হিসেবে সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আসিফ মাহমুদ।
৩ ঘণ্টা আগে
মুক্তিবাহিনীর অগ্রাভিযানে পাকিস্তানি বাহিনীর একের পর এক অবস্থানের পতনে মুক্ত হচ্ছিল বাংলাদেশের একেকটি অঞ্চল। এগিয়ে আসছিল স্বাধীনতার মুহূর্তটি। যদিও ঠিক কখন, কীভাবে সেদিনটি আসবে, তখনো তা স্পষ্ট নয় সাধারণ মানুষের কাছে। তবে সবাই অধীর আগ্রহে ক্ষণ গুনছিল।
৩ ঘণ্টা আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার তোড়জোড়ের মধ্যে জরুরি সংবাদ সম্মেলনে আসছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় এবং যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।
সমসাময়িক বিষয়ে আজ বুধবার বেলা ৩টায় স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলনকক্ষে আসিফ মাহমুদের সংবাদ সম্মেলন হবে বলে মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে।
সমসাময়িক কোন বিষয়ে আসিফ মাহমুদ সংবাদ সম্মেলনে কথা বলবেন, মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণপত্রে তা উল্লেখ করা হয়নি। তবে বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আজকের সংবাদ সম্মেলন থেকে উপদেষ্টা পদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিতে পারেন তিনি।
আজ রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করার পর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার জন্য ভাষণের রেকর্ড করবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। আজ সন্ধ্যায় বা আগামীকাল বৃহস্পতিবার এই তফসিল ঘোষণা করা হবে বলে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
তথ্য মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মাহফুজ আলমও আজ পদত্যাগের ঘোষণা দিতে পারেন বলে আলোচনা রয়েছে।
উপদেষ্টার পদে থেকে নির্বাচন করতে আইনি বাধা না থাকলেও তফসিল ঘোষণার আগে সরকারে থাকা দুজন ছাত্র উপদেষ্টা পদত্যাগ করবেন বলে গুঞ্জন রয়েছে।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে ২০২৪ সালের জুলাইয়ে ছাত্র আন্দোলনে অন্যতম সমন্বয়ক হিসেবে সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আসিফ মাহমুদ। তাঁদের আন্দোলন একপর্যায়ে সরকার পতনের এক দফার আন্দোলনে রূপ নেয়। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ক্ষমতাচ্যুত হয় আওয়ামী লীগ সরকার। এরপর ওই বছরের ৮ আগস্ট ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত হয় অন্তর্বর্তী সরকার। এই সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেন আসিফ মাহমুদ।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার তোড়জোড়ের মধ্যে জরুরি সংবাদ সম্মেলনে আসছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় এবং যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।
সমসাময়িক বিষয়ে আজ বুধবার বেলা ৩টায় স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলনকক্ষে আসিফ মাহমুদের সংবাদ সম্মেলন হবে বলে মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে।
সমসাময়িক কোন বিষয়ে আসিফ মাহমুদ সংবাদ সম্মেলনে কথা বলবেন, মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণপত্রে তা উল্লেখ করা হয়নি। তবে বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আজকের সংবাদ সম্মেলন থেকে উপদেষ্টা পদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিতে পারেন তিনি।
আজ রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করার পর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার জন্য ভাষণের রেকর্ড করবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। আজ সন্ধ্যায় বা আগামীকাল বৃহস্পতিবার এই তফসিল ঘোষণা করা হবে বলে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
তথ্য মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মাহফুজ আলমও আজ পদত্যাগের ঘোষণা দিতে পারেন বলে আলোচনা রয়েছে।
উপদেষ্টার পদে থেকে নির্বাচন করতে আইনি বাধা না থাকলেও তফসিল ঘোষণার আগে সরকারে থাকা দুজন ছাত্র উপদেষ্টা পদত্যাগ করবেন বলে গুঞ্জন রয়েছে।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে ২০২৪ সালের জুলাইয়ে ছাত্র আন্দোলনে অন্যতম সমন্বয়ক হিসেবে সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আসিফ মাহমুদ। তাঁদের আন্দোলন একপর্যায়ে সরকার পতনের এক দফার আন্দোলনে রূপ নেয়। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ক্ষমতাচ্যুত হয় আওয়ামী লীগ সরকার। এরপর ওই বছরের ৮ আগস্ট ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত হয় অন্তর্বর্তী সরকার। এই সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেন আসিফ মাহমুদ।
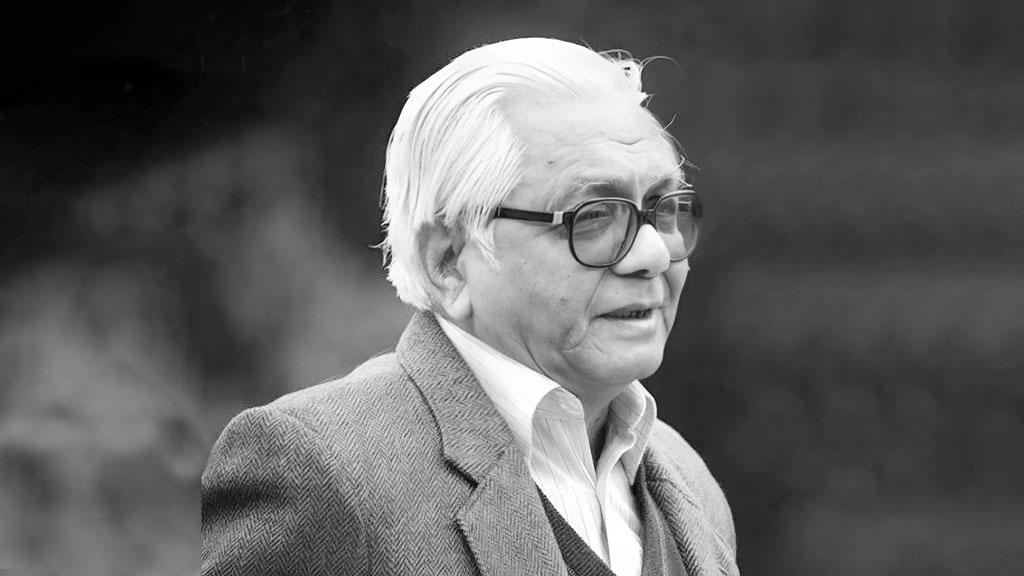
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, লেখক, গবেষক এবং বাম ধারার বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দীন উমর ৯৪ বছর বয়সে মারা গেছেন। আজ রোববার সকালে ঢাকার বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় ভুগছিলেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে...
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের (সিইসি) নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশনাররা বঙ্গভবনে পৌঁছেছেন। বঙ্গভবনের একটি সূত্র আজকের পত্রিকাকে জানিয়েছেন, আজ বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টায় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ইসির বৈঠকের শিডিউল রাখা আছে।
৩৮ মিনিট আগে
টাঙ্গাইলের শাড়ি বুনন শিল্পকে অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেসকো। গতকাল মঙ্গলবার ভারতের নয়াদিল্লিতে ইউনেসকো কনভেনশনের চলমান ২০তম আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্ষদের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
২ ঘণ্টা আগে
মুক্তিবাহিনীর অগ্রাভিযানে পাকিস্তানি বাহিনীর একের পর এক অবস্থানের পতনে মুক্ত হচ্ছিল বাংলাদেশের একেকটি অঞ্চল। এগিয়ে আসছিল স্বাধীনতার মুহূর্তটি। যদিও ঠিক কখন, কীভাবে সেদিনটি আসবে, তখনো তা স্পষ্ট নয় সাধারণ মানুষের কাছে। তবে সবাই অধীর আগ্রহে ক্ষণ গুনছিল।
৩ ঘণ্টা আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

মুক্তিবাহিনীর অগ্রাভিযানে পাকিস্তানি বাহিনীর একের পর এক অবস্থানের পতনে মুক্ত হচ্ছিল বাংলাদেশের একেকটি অঞ্চল। এগিয়ে আসছিল স্বাধীনতার মুহূর্তটি। যদিও ঠিক কখন, কীভাবে সেদিনটি আসবে, তখনো তা স্পষ্ট নয় সাধারণ মানুষের কাছে। তবে সবাই অধীর আগ্রহে ক্ষণ গুনছিল।
সেতু বিধ্বস্ত হওয়ায় ১০ ডিসেম্বর রায়পুরা অঞ্চলে ১৪টি হেলিকপ্টারের সাহায্যে ভারতীয় মিত্র বাহিনীর অগ্রবর্তী অংশ তখনকার বিশাল, প্রশস্ত মেঘনা পার হয়। স্থানীয় জনসাধারণ ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনায় শত শত নৌকার সাহায্যে অবশিষ্ট সেনা ও যুদ্ধ-সরঞ্জাম পরিবহনে সহায়তা করে।
প্রচণ্ড চাপে পড়ে আগের দিন ঢাকায় পাকিস্তানের সামরিক নেতৃত্ব ও গভর্নর মালেক সৈন্যসহ পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেদিন দাউদকান্দির পতনের পর তাঁরা বুঝে গিয়েছিলেন, ঢাকাই যৌথ বাহিনীর পরবর্তী লক্ষ্য। পাকিস্তানিদের সম্পূর্ণ পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্ত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের পূর্ণ অনুমোদন লাভ করে।
সহায়তাকারী ভারতীয় বাহিনীর রায়পুরায় অবতরণের পর প্রায় ৩ ঘণ্টা ঢাকার পাকিস্তানি সামরিক লক্ষ্যবস্তুগুলোর ওপর বিমান হামলা চলে। তখন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের সামরিক উপদেষ্টা, গণহত্যার অন্যতম সহযোগী রাও ফরমান আলী ঢাকায় অবস্থানকারী জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিব পল মার্ক হেনরিকে ‘অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির’ আয়োজন করার আবেদন জানান। বাঙালিদের ওপর ৯ মাস হত্যাযজ্ঞ চলার পর এত দিনে এসে তিনি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা এবং এই অঞ্চলে থাকা পাকিস্তানি বাহিনীকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা সম্পন্ন করার আহ্বান জানান। জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিব এ প্রস্তাব জাতিসংঘ সদর দপ্তরে পাঠিয়ে দেন।
নিরাপত্তা পরিষদে রাও ফরমান আলীর এ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার উদ্যোগ চলার সময় হঠাৎ খবর আসে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া প্রস্তাবটি নাকচ করে দিয়েছেন। ঘটনা হচ্ছে, খবরটি ওয়াশিংটনে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন সরকার ইয়াহিয়াকে জানান, পাকিস্তানি বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য সপ্তম নৌবহর ইতিমধ্যেই বঙ্গোপসাগরের দিকে রওনা হয়েছে। এ কারণেই ইয়াহিয়ার মত বদলে যায়। পাকিস্তান নিজে থেকে ‘সম্মানজনকভাবে’ সেনা প্রত্যাহারের জন্য উদ্যোগী হলেও সেই উদ্যোগকে সমর্থন না করে মার্কিন সরকার বরং তা রদ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তার ওপর ভারতকে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে সম্মত করানোর তাগিদ দিয়ে ৯ ও ১০ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট নিক্সন সোভিয়েত নেতা ব্রেজনেভকে দুই দফা বার্তা পাঠান। যুদ্ধবিরতি কার্যকর করার ব্যাপারে ভারতকে সম্মত করতে ব্রেজনেভের ওপর চাপের মাত্রা বাড়ানো হয়। তাঁকে জানানো হয়, ভারত যদি এরপরও সম্মত না হয়, তবে যুক্তরাষ্ট্র নিজে এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে।
উপমহাদেশের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র ‘শক্ত ব্যবস্থা’ গ্রহণ করতে পারে, তা সোভিয়েত ইউনিয়নের ভালো করেই জানা ছিল। সোভিয়েত সরকার তাদের নৌবাহিনীকে সতর্ক রাখে। মার্কিন সপ্তম নৌবহরের যাত্রারম্ভের আগেই সোভিয়েতরা তাদের ভারত মহাসাগরীয় নৌবহরের শক্তি বৃদ্ধি শুরু করে।
১০ ডিসেম্বর মার্কিন সপ্তম নৌবহর চীন সাগর ও ভারত মহাসাগরকে সংযোগকারী পাঁচ শ’ মাইল দীর্ঘ মালাক্কা প্রণালির ওপারে ছিল। ভারত মহাসাগরে সোভিয়েত নৌবহরের সমাবেশ তখন সম্পূর্ণ হয়নি। এই অবস্থায় জানা যায়, মার্কিন সপ্তম নৌবহরের গতিবিধি জানার জন্যই সোভিয়েত সরকার কসমস নামের নজরদারি কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে।
এদিকে চূড়ান্ত পর্বের রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের আশঙ্কায় ঢাকা ছেড়ে চলে যেতে থাকেন অনেক সাধারণ মানুষ। আগের দিন সরকার স্কুল-কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেছিল। গুজব ছড়িয়ে পড়ে, রাস্তায় রাস্তায় পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে লড়াই হবে বলে মুক্তিযোদ্ধারা লোকজনকে শহর ছেড়ে চলে যেতে বলেছেন। অনেক লোককে দেখা যায়, পরিবার-পরিজন, পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে রিকশা বা বেবিট্যাক্সিতে (সিএনজি অটোর আগের সংস্করণ) করে শহর থেকে বাইরে চলে যাচ্ছে। কেউ কেউ লটবহর মাথায় নিয়ে হেঁটেই চলেছেন। এ যেন ২৫ মার্চের গণহত্যার পর ঢাকা ছাড়ার যে ঢল নেমেছিল কিছুটা প্রতিচ্ছবি।

মুক্তিবাহিনীর অগ্রাভিযানে পাকিস্তানি বাহিনীর একের পর এক অবস্থানের পতনে মুক্ত হচ্ছিল বাংলাদেশের একেকটি অঞ্চল। এগিয়ে আসছিল স্বাধীনতার মুহূর্তটি। যদিও ঠিক কখন, কীভাবে সেদিনটি আসবে, তখনো তা স্পষ্ট নয় সাধারণ মানুষের কাছে। তবে সবাই অধীর আগ্রহে ক্ষণ গুনছিল।
সেতু বিধ্বস্ত হওয়ায় ১০ ডিসেম্বর রায়পুরা অঞ্চলে ১৪টি হেলিকপ্টারের সাহায্যে ভারতীয় মিত্র বাহিনীর অগ্রবর্তী অংশ তখনকার বিশাল, প্রশস্ত মেঘনা পার হয়। স্থানীয় জনসাধারণ ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনায় শত শত নৌকার সাহায্যে অবশিষ্ট সেনা ও যুদ্ধ-সরঞ্জাম পরিবহনে সহায়তা করে।
প্রচণ্ড চাপে পড়ে আগের দিন ঢাকায় পাকিস্তানের সামরিক নেতৃত্ব ও গভর্নর মালেক সৈন্যসহ পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেদিন দাউদকান্দির পতনের পর তাঁরা বুঝে গিয়েছিলেন, ঢাকাই যৌথ বাহিনীর পরবর্তী লক্ষ্য। পাকিস্তানিদের সম্পূর্ণ পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্ত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের পূর্ণ অনুমোদন লাভ করে।
সহায়তাকারী ভারতীয় বাহিনীর রায়পুরায় অবতরণের পর প্রায় ৩ ঘণ্টা ঢাকার পাকিস্তানি সামরিক লক্ষ্যবস্তুগুলোর ওপর বিমান হামলা চলে। তখন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের সামরিক উপদেষ্টা, গণহত্যার অন্যতম সহযোগী রাও ফরমান আলী ঢাকায় অবস্থানকারী জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিব পল মার্ক হেনরিকে ‘অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির’ আয়োজন করার আবেদন জানান। বাঙালিদের ওপর ৯ মাস হত্যাযজ্ঞ চলার পর এত দিনে এসে তিনি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা এবং এই অঞ্চলে থাকা পাকিস্তানি বাহিনীকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা সম্পন্ন করার আহ্বান জানান। জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিব এ প্রস্তাব জাতিসংঘ সদর দপ্তরে পাঠিয়ে দেন।
নিরাপত্তা পরিষদে রাও ফরমান আলীর এ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার উদ্যোগ চলার সময় হঠাৎ খবর আসে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া প্রস্তাবটি নাকচ করে দিয়েছেন। ঘটনা হচ্ছে, খবরটি ওয়াশিংটনে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন সরকার ইয়াহিয়াকে জানান, পাকিস্তানি বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য সপ্তম নৌবহর ইতিমধ্যেই বঙ্গোপসাগরের দিকে রওনা হয়েছে। এ কারণেই ইয়াহিয়ার মত বদলে যায়। পাকিস্তান নিজে থেকে ‘সম্মানজনকভাবে’ সেনা প্রত্যাহারের জন্য উদ্যোগী হলেও সেই উদ্যোগকে সমর্থন না করে মার্কিন সরকার বরং তা রদ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তার ওপর ভারতকে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে সম্মত করানোর তাগিদ দিয়ে ৯ ও ১০ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট নিক্সন সোভিয়েত নেতা ব্রেজনেভকে দুই দফা বার্তা পাঠান। যুদ্ধবিরতি কার্যকর করার ব্যাপারে ভারতকে সম্মত করতে ব্রেজনেভের ওপর চাপের মাত্রা বাড়ানো হয়। তাঁকে জানানো হয়, ভারত যদি এরপরও সম্মত না হয়, তবে যুক্তরাষ্ট্র নিজে এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে।
উপমহাদেশের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র ‘শক্ত ব্যবস্থা’ গ্রহণ করতে পারে, তা সোভিয়েত ইউনিয়নের ভালো করেই জানা ছিল। সোভিয়েত সরকার তাদের নৌবাহিনীকে সতর্ক রাখে। মার্কিন সপ্তম নৌবহরের যাত্রারম্ভের আগেই সোভিয়েতরা তাদের ভারত মহাসাগরীয় নৌবহরের শক্তি বৃদ্ধি শুরু করে।
১০ ডিসেম্বর মার্কিন সপ্তম নৌবহর চীন সাগর ও ভারত মহাসাগরকে সংযোগকারী পাঁচ শ’ মাইল দীর্ঘ মালাক্কা প্রণালির ওপারে ছিল। ভারত মহাসাগরে সোভিয়েত নৌবহরের সমাবেশ তখন সম্পূর্ণ হয়নি। এই অবস্থায় জানা যায়, মার্কিন সপ্তম নৌবহরের গতিবিধি জানার জন্যই সোভিয়েত সরকার কসমস নামের নজরদারি কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে।
এদিকে চূড়ান্ত পর্বের রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের আশঙ্কায় ঢাকা ছেড়ে চলে যেতে থাকেন অনেক সাধারণ মানুষ। আগের দিন সরকার স্কুল-কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেছিল। গুজব ছড়িয়ে পড়ে, রাস্তায় রাস্তায় পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে লড়াই হবে বলে মুক্তিযোদ্ধারা লোকজনকে শহর ছেড়ে চলে যেতে বলেছেন। অনেক লোককে দেখা যায়, পরিবার-পরিজন, পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে রিকশা বা বেবিট্যাক্সিতে (সিএনজি অটোর আগের সংস্করণ) করে শহর থেকে বাইরে চলে যাচ্ছে। কেউ কেউ লটবহর মাথায় নিয়ে হেঁটেই চলেছেন। এ যেন ২৫ মার্চের গণহত্যার পর ঢাকা ছাড়ার যে ঢল নেমেছিল কিছুটা প্রতিচ্ছবি।
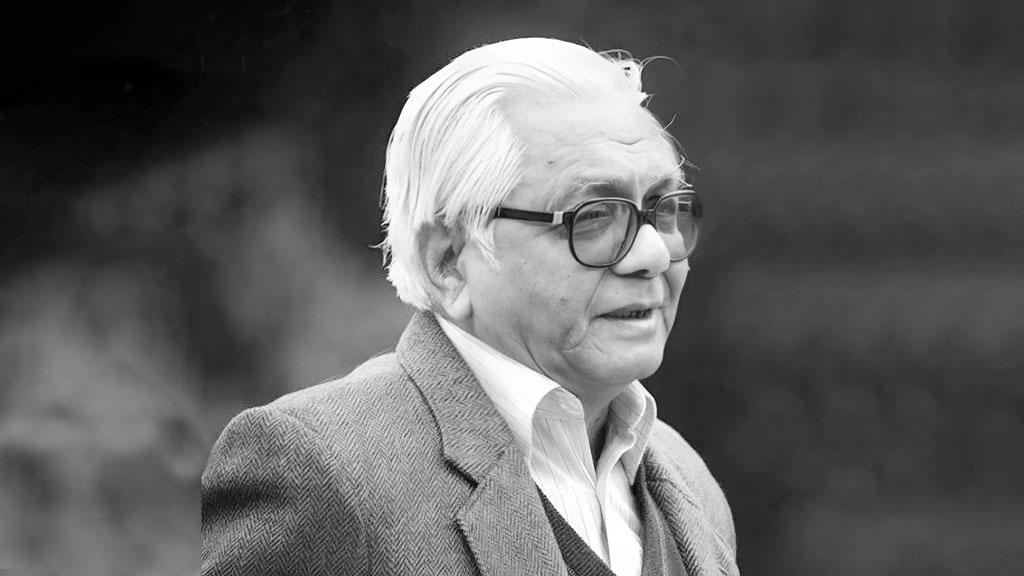
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, লেখক, গবেষক এবং বাম ধারার বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দীন উমর ৯৪ বছর বয়সে মারা গেছেন। আজ রোববার সকালে ঢাকার বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় ভুগছিলেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে...
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের (সিইসি) নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশনাররা বঙ্গভবনে পৌঁছেছেন। বঙ্গভবনের একটি সূত্র আজকের পত্রিকাকে জানিয়েছেন, আজ বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টায় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ইসির বৈঠকের শিডিউল রাখা আছে।
৩৮ মিনিট আগে
টাঙ্গাইলের শাড়ি বুনন শিল্পকে অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেসকো। গতকাল মঙ্গলবার ভারতের নয়াদিল্লিতে ইউনেসকো কনভেনশনের চলমান ২০তম আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্ষদের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
২ ঘণ্টা আগে
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে ২০২৪ সালের জুলাইয়ে ছাত্র আন্দোলনে অন্যতম সমন্বয়ক হিসেবে সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আসিফ মাহমুদ।
৩ ঘণ্টা আগে