জাহীদ রেজা নূর
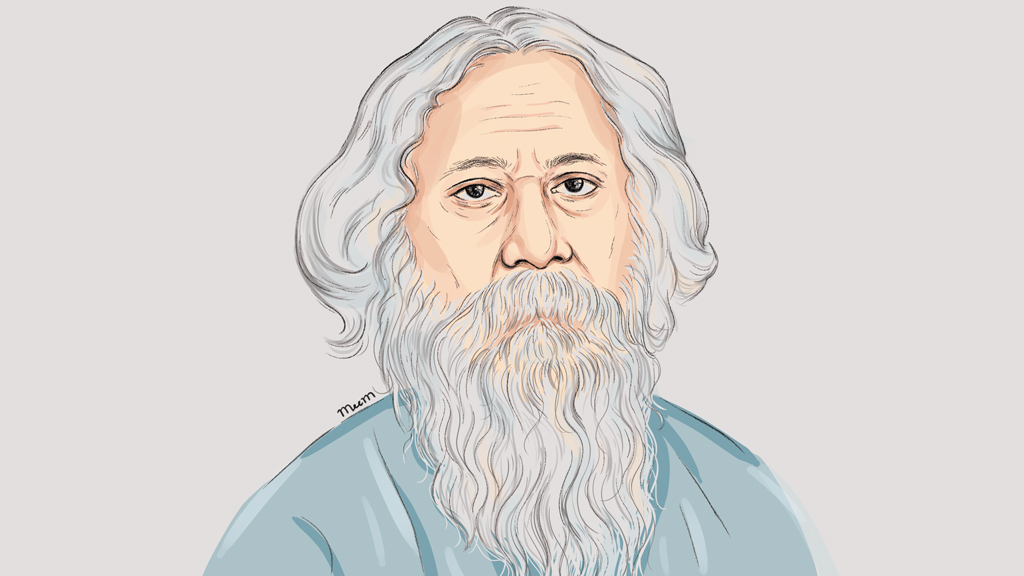
মুক্তিযুদ্ধের একপর্যায়ে যে স্বাধীনতা এল, তারই প্রশস্ত পথ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল আমাদের শৈশব। ১৯৭২ সালের বাংলাদেশকে এখনকার তরুণ চিনবে না। সেই সরু সরু রাস্তা, ছোট ছোট বাড়ি, বাড়ির সামনে লন, বড় বড় গাছ—এগুলো কি এখন আর প্রাসঙ্গিক? সে সময়ের ঢাকা শহরকে চিনতে হলে যেতে হবে মফস্বলের কোনো শহরে, কিংবা ভারতের আগরতলায়। বেশ ক’বছর আগে আগরতলায় গিয়ে মনে হয়েছিল, আরে! আমার ছেলেবেলায় দেখা ঢাকার সঙ্গে এই শহরের কত মিল!
সে সময় শহুরে তারুণ্যকে গ্রাস করেছিলেন আজম খান। তাঁর ‘রেল লাইনের ওই বস্তিতে’, ‘ওরে সালেকা ওরে মালেকা’, ‘হাইকোর্টের মাজারে’ শুনতে শুনতে মাতাল হয়ে যেত তরুণেরা। মাতাল হতো আমাদের মতো শিশুরাও। পপ সংগীত যেন আমাদের নিয়ে যেত মোক্ষধামে। বাকি সব এই ঘোরের মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল।
এরই মধ্য থেকে কখনো ঝলক দিয়ে উঠত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কোনো গান। ‘তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেবরে’, ‘সালাম সালাম হাজার সালাম’, ‘মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি।’
আর সেই গানগুলোর মধ্য থেকে ঝলক দিয়ে ওঠে, ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।’ আমাদের জাতীয় সংগীত।
বাহাত্তরে বয়স যখন ছয়, তখন আমরা চিৎকার করে জাতীয় সংগীত গাইতে থাকি। ‘মা তোর বদনখানি মলিন হলে আমি নয়নজলে ভাসি’ বলতে গিয়ে দেশের চেহারা নয়, আমার চোখে ফুটে উঠত আমার মায়ের চেহারা। রাষ্ট্রপতি আবু সায়ীদ চৌধুরী আমাদের ৫ নং চামেলিবাগের ভাড়া বাড়িতে এসে মাকে সান্ত্বনা দিয়ে চলে যাওয়ার পর যে ছবিতে আমরা আট ভাই মায়ের সঙ্গে বসে আছি, সে ছবিটাই ভেসে উঠত চোখে।
‘যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়ব না মা’, কিংবা ‘ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা’ গানটি বেসুরো কণ্ঠে গাইতে গিয়ে কখন নিজেরই অলক্ষ্যে মাটির সঙ্গে মাথার মোলাকাত হয়েছে, টেরই পাইনি।
হ্যাঁ, তখন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে গাওয়া গানগুলোর কিছু কিছু আমরা মুখস্থ করে নিয়েছিলাম। নজরুলের ‘কারার ঐ লৌহকপাট’, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ‘ধনধান্যে পুষ্পে ভরা’, অতুল প্রসাদ সেনের ‘মোদের গরব মোদের আশা’, মুকুন্দ দাসের ‘ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে’, গুরুসদয় দত্তের ‘মানুষ হ মানুষ হ আবার তোরা মানুষ হ’ গানগুলো আমাদের মোহিত করে তুলত। সলিল চৌধুরীর দুটো গান ‘মানব না এ বন্ধনে না, মানব না এ শৃঙ্খলে’, কিংবা ‘বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা’ শুনলে শরীরে অদ্ভুত শক্তি আসত। আর ছিল মোহিনী সেনের ‘মুক্তির মন্দির সোপান তলে’। এই গানটি নাচের সঙ্গে দেখতে ভালো লাগত বেশি।
এভাবেই আজম খানের প্রবল প্রমত্ত ঝড়ের মাঝে দেশের গানেরা শান্ত হয়ে মনের মাঝে বসত। কী করে সেগুলোই একসময় হয়ে উঠল তৃষ্ণার জল, সে কথাই তো বলার জন্য এই আয়োজন।
হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ
আমাদের একটা টেলিভিশন ছিল। ফিলিপস। দেশে যখন প্রথম টেলিভিশন এসেছে, তখন তার একটি এসেছিল আমাদের বাড়িতে। পাড়ার লোকেরা বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান হলে চলে আসত আমাদের বাড়িতে। তখন বারান্দায় রাখা হতো টেলিভিশন। বাড়ির সামনের লনে দাঁড়িয়ে-বসে পাড়ার মানুষেরা টিভি দেখত।
সেই টিভিতে হতো গানের অনুষ্ঠান। সম্ভবত রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠানটির নাম ছিল গীতবিতান। রাত ৮টার খবরের আগে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় বোধ হয় ছিল সে অনুষ্ঠান। সারা দিন কাজের পর আমাদের মা সে সময় একটু বসতেন টেলিভিশনের সামনে। তিনিই বলতেন সন্জীদা খাতুন, ফাহমিদা খাতুন, কলিম শরাফীর কথা। জাহেদুর রহিমের কথা। স্বীকার করে নেওয়া ভালো, সে সময় রবীন্দ্রসংগীতে মোটেই আনন্দ পেতাম না। মনে হতো, একঘেয়ে সুরে কী হচ্ছে এটা? কোথাও কোনো চমক নেই, চিৎকার নেই। একটানা কী সব কথা বলে যাওয়া হচ্ছে!
সে বয়সেই হঠাৎ করে কানে এল কয়েকটি গান। আমূল পাল্টে গেল রবীন্দ্রনাথ নিয়ে ভাবনা। গানগুলোর কয়েকটির উল্লেখ না করলে এই পাল্টে যাওয়ার ঘটনাটি বোঝা যাবে না। বলে রাখি, তখনো টেপ রেকর্ডার বা স্টেরিও সেট নেই আমাদের বাড়িতে। সম্বল এক ব্যান্ডের একটা রেডিও, আর টেলিভিশন। রেডিওটা থাকে আমাদের পঞ্চম ভ্রাতার শাসনে, ফলে সেটার কাছাকাছি হওয়া যেত শুধু সে বাড়িতে না থাকলেই।
শিশুদেরই কোনো অনুষ্ঠানে যখন শুনলাম, ‘আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে’, তখন সে গানের কথাগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে মনে হলো, আরে! এ দেখি আমার কথাই বলা হচ্ছে। আমাদের সবার কথাই বলা হচ্ছে। রাজা বলে আলাদা কেউ নেই। এ রাজা তো আমি, এ রাজা তো তুমি, এ রাজা তো সে! এ যে কী এক অনবদ্য আবিষ্কার, সেটা অনুভব না করলে বলে লাভ নেই।
তারপর ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলোরে!’ এই গান শুনতে গিয়ে একটা খটকা আসত মনে। এখানে তুমি, আর তুইয়ের ব্যবহার একই সঙ্গে করলেন কেন রবীন্দ্রনাথ, সেটা বুঝতে পারতাম না। খুদে এক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করায় সে বিজ্ঞের মতো উত্তর দিয়েছিল, ‘রবীন্দ্রনাথ তো কবি, ব্যাকরণ জানে না। বড়ুয়া স্যারের ক্লাসে গেলে রবীন্দ্রনাথ বুঝত কত ধানে কত চাল!’ উত্তরটা অবশ্য আজও পাইনি।
এবার কয়েকটি গানের কথা এক নিশ্বাসে বলে যাই, তাতে বোঝা যাবে, কেন রবীন্দ্রসংগীতকে আর প্যানপ্যানানি বলে মনে হতো না। যদিও অনেক পরে এসে বুঝতে শুরু করেছি, যাকে প্যানপ্যানানি ভেবেছি সেই ছেলেবেলায়, তা ছিল দুঃখ নামক রোগের প্রতিষেধক, নিজেকে খুঁজে পাওয়ার ওষুধ। কিন্তু সে বয়সে কে আর তা ভাবে?
‘বাঁধ ভেঙে দাও বাঁধ ভেঙে দাও।’
‘যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক।’
‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে।’
‘সংকোচের বিহ্বলতা নিজের অপমান।’
‘ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।’
‘এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে জয় মা বলে ভাসা তরী।’
অন্যরকম হলেও অনেক পরে আরেকটি গান খুব ভালো লেগেছিল, ‘বাংলার মাটি বাংলার জল’। সে কথাও বলব যথাসময়ে।
এই যে হঠাৎ করে রবীন্দ্রনাথ ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন, তা কিন্তু ‘মনে মনেই’। হারিয়ে গেছি মনে মনে। এবং হ্যাঁ, নিজের কণ্ঠে সে গান করার চেষ্টা করিনি মোটেও, নিজে বেসুরো বলে। অন্যের কণ্ঠে শুনেই প্রাণের আশ মিটিয়েছি।
কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ
স্বাধীন দেশের প্রাথমিক চলার পথে ছিল অনেক খানা-খন্দ। রাজনীতির মাঠে যে খেলা চলছিল, তাতে রেফারির বাঁশি হয়ে গিয়েছিল গৌণ। এর পর তো উদ্ভট উটের পিঠে চড়ে বসল দেশ। সে যে কোনদিকে যাচ্ছে, তা বুঝবে সাধ্য কার?
সেই অরাজকতায় ‘মানি ইজ নো প্রবলেম’ বাক্যটি হয়ে উঠল কারও কারও জন্য হীরন্ময়। রাজনীতিবিদদের জন্য রাজনীতি জটিল করে দেওয়ার খেলা শুরু হলো। মরুভূমির লু হাওয়া বইতে লাগল বাংলাদেশজুড়ে।
তখন রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলেন কী করে, সেটা একটা প্রশ্ন বটে। দেখা গেল, হারমোনিয়ামের রিডে আঙুল বুলিয়ে তুলছে রবীন্দ্রনাথের সুর। পাড়ায়-মহল্লায় সকালের দিকে তখনো শোনা যেত গলা সাধার আওয়াজ। ভোরবেলাটায় রাঙিয়ে যেত মন, ‘যাবার আগে নয়’, দিনের শুরুতেই।
সে সময় বইয়ের পাতায় আসতেন রবীন্দ্রনাথ। ‘বলাই’ কিংবা ‘ছুটি’ গল্পের মাধ্যমে তিনি ঢুকে যেতেন মনের ভিতর। গানে গানে রবীন্দ্রনাথকে পেতাম না তখন।
এর মাঝে বাড়িতে ঘটে গেল এক পরিবর্তন। মেজ ভাই মালয়েশিয়ায় গিয়েছিলেন। ফেরার পথে সেখান থেকে নিয়ে এসেছেন একটা স্টেরিও সেট। সেখানে ক্যাসেট দিলেই শোনা যাবে গান। যখন ইচ্ছে, তখন শোনা যাবে। যখন ইচ্ছে, তা বন্ধ করে অন্য একটি গান দেওয়া যাবে। গানের ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য।
সে সময় যে ক্যাসেটগুলো এল, তার একটি ছিল ‘শ্যামা’, একটি ‘চিত্রাঙ্গদা’, একটি ‘মায়ার খেলা’, একটি ‘চণ্ডালিকা’। হতে পারে দুই পিঠে দুটো গীতিনাট্য।
আলাদাভাবে এল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র সংগীতের ক্যাসেট। যে ক্যাসেট থেকে সবার আগে মুখস্থ হয়ে গেল ‘প্রাঙ্গণে মোর শিরীষ শাখায় ফাগুন মাসের কী উচ্ছ্বাসে’।
শ্যামার মধ্যেই দেখি হেমন্ত! বজ্রসেন হয়ে মঞ্চ কাঁপাচ্ছেন! এই প্রথম রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে একটু স্থিত হই। শ্যামাকে বোঝার চেষ্টা করি। বজ্রসেন আর শ্যামার মধ্যে কে বেশি আপন, তা ঠিক করে নিতে দ্বিধান্বিত হয়ে ওঠে মন। উত্তীয়কে বিপদে ফেলার পরও শ্যামাকে একমাত্র অপরাধী বলে ভাবতে ভাল্লাগে না। বজ্রসেনের জন্যই তো এত ত্যাগ, তাহলে বজ্রসেন কেন ক্ষমা করতে পারবে না শ্যামাকে! শেষে এসে বলছে ‘যাও যাও যাও, যাও ফিরে যাও।’ তারপর বলছে, ‘ক্ষম হে মম দীনতা, পাপীজন স্মরণ প্রভু।’ ‘ক্ষমিবে না আমার ক্ষমাহীনতা’—কী মারাত্মক কথা!
এইচএসসি দিলাম ১৯৮৪ সালে। এর পর ‘কণ্ঠশীলন’ নামে একটি আবৃত্তি সংগঠনে যোগ দিলাম। সেখানে কবিতার পাশাপাশি বিশ্ববীক্ষার সুযোগ হলো। রবীন্দ্রনাথের গানের পথে হাঁটার সুযোগ হলো একেবারে ভিন্ন একটি মাধ্যমে।
কণ্ঠশীলনে আবৃত্তি করতেন ফওজিয়া মান্নান। আমি তাঁকে মিলি আপা বলে ডাকি। মহড়া শেষ হলে আমরা কয়েকজন তাঁকে আর ছন্দা আপাকে তাঁদের বাড়ি পৌঁছে দিতাম। টিএসসি থেকে নীলক্ষেত হয়ে আজিমপুর কলোনিতে মিলি আপা, আর কবরস্থান ছাড়িয়ে নতুন পল্টনে ছন্দা আপাকে পৌঁছে দিতাম। ওয়াহিদুল হক সে সময় মিলি আপাদের বাড়িতে গিয়ে আটকে যেতেন। সেখানে ছিল ক্লাস নাইন পড়ুয়া তানিয়া মান্নান, মিলি আপার ছোট বোন। আমরাও কখনো কখনো বসতাম সে বাড়িতে। তানিয়া নিয়ে আসত হারমোনিয়াম। তারপর গাইত গান।
এখনো তানিয়ার রেওয়াজ করা কয়েকটি গান মনে আছে। রবীন্দ্রনাথের দিকে এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে এ গানগুলো ছিল দিশারি। একটি গান হলো, ‘আকাশ আমায় ভরল আলোয়, আকাশ আমি ভরব গানে।’ গানটা শুনি আর ভাবি, এ কি অসাধারণ কথা! বিনে পয়সার বিনিময়! আকাশ মানে সূর্য, নিশ্চয়ই আলো দিচ্ছে পৃথিবীকে, আর তাতে পৃথিবী মানে পৃথিবীর মানুষের কত আনন্দ! সে গান দিয়ে সে পুরস্কারের মূল্য দিচ্ছে!
সে সময় আরও দুটো গানের সুধা এসে মিশে যায় মনে।
‘তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি ধাই’
‘অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায়, তাহা যায়।’
গান দুটি শুনি সুবিনয় রায়ের ক্যাসেটে। রাশিয়ার দশ বছর কেটেছে এই দুই গানের ওমে। সে আরও পরের ব্যাপার।
এ ছাড়া আরও দুটি গান হলো, ‘জাগো পূরবাসী, ভগবৎ প্রেমপিয়াসি।’ অন্যটা ‘ধীরে ধীরে মোরে টেনে লহ তোমা পানে।’ পরের দুটি গান রবীন্দ্রসংগীত নয়, কিন্তু একই সঙ্গে গান তিনটি শুনতাম, এবং অবাক হয়ে খেয়াল করে দেখতাম, গান তিনটি আমাদের মুখস্থ হয়ে গেছে। আর এ সময় পেয়ে যাই এক অমোঘ বার্তা: রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে সৃষ্টিশীল সময় হলো ১৮৯১ থেকে ১৯০০ সাল। এ সময়টিতে তিনি কাটিয়েছেন পূর্ববঙ্গে!
‘আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে’
এক নতুন জগতের ঠিকানা লিখে দিল সে কালের পূর্ববঙ্গ। শাহজাদপুর, শিলাইদহ, আর পতিসর। বোটটা যেন আমি নিজের চোখে দেখি। ছিন্নপত্রগুলো ভেসে ওঠে চোখে। রবীন্দ্রনাথ নিজের চোখে মানুষ দেখছেন। তিনি সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছাচ্ছেন। এতকাল যে বদ্ধ জলাশয়ে ছিল বসবাস, সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছেন। এ যেন মহাসাগর!
গানের কথা বলছি। তাই আগে শোনা একটি গানকে এই সময়ের গায়ে লেপ্টে দিলাম:
‘আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকল খানে।’
‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলোরে’ গানটির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ওয়াহিদুল হক বলেন, ‘এ সময় বাউল সংগীতের সঙ্গে একাত্ম হচ্ছেন কবি। এই যে গানটা, সেটাও লেখা হয়েছে বাউল সুরে। একটা গান আছে, “হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে, আমার একলা নিতাই!” সেই সুরেই তো গানটা!’
গগন হরকরার ‘আমি কোথায় পাব তারে’ গানটির সুরে হলো ‘আমার সোনার বাংলা’, এখন যা আমাদের জাতীয় সংগীত। এর পর থেকে নানাভাবেই তো রবীন্দ্রনাথ এসেছেন আমার কাছে। এসেছেন তাঁর প্রবন্ধের মাধ্যমে, কবিতায়। এসেছেন অন্যদের হাত ধরে। সে রকমই কিছু কথা শোনানো জরুরি।
বিচ্ছিন্ন কিছু কথা
আমার গালে একটা চটকানা দিলেন বিষ্ণু দে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লিখলেন:
‘তুমি কি কেবল-ই স্মৃতি, শুধু এক উপলক্ষ, কবি?
হরেক উৎসবে হৈ হৈ
মঞ্চে মঞ্চে কেবল-ই কি ছবি?
তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ
আর বাইশে শ্রাবণ?’
তারপর বললেন—
‘তোমার আকাশ দাও, কবি, দাও
দীর্ঘ আশি বছরের
আমাদের ক্ষীয়মাণ মানসে ছড়াও
সূর্যোদয় সূর্যাস্তের আশি বছরের আলো,
বহুধা কীর্তিতে শত শিল্পকর্মে উন্মুক্ত উধাও
তোমার কীর্তিতে আর তোমাতে যা দিকে দিকে
একাগ্র মহৎ,
সে কঠিন ব্রতের গৌরবে,
আমাদের বিকারের গড্ডল ধুলার দিনগত অন্যায়ের কুৎসিতে
শুনি যেন সুন্দরের গান’
ওলোট পালট হয়ে গেল ভাবনার জগৎ। মেকি মনে হলো অনেক কিছুই। আসলেই কি উপলক্ষ তৈরি করে হইহই করলে রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যায়? ওই জন্ম-মৃত্যুর দুটি দিন, আর নববর্ষে ‘এসো হে বৈশাখ’ গাইলেই কর্তব্য শেষ? তাঁর গান কবিতাটিতে এসে ‘এ পরবাসে রবে কে এ পরবাসে’ পঙ্ক্তিটিতে এসে থমকে দাঁড়াই। মালতী ঘোষালকে চিনি না। কিন্তু তিনি যেন এসে গানটি শুনিয়ে যান। সে কবিতায় দেবব্রত বিশ্বাসের উদাত্ত কণ্ঠের বর্ণনা শুনে ক্যাসেটে তাঁর গান শোনার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছিলাম!
‘ব্রাত্যজনের রুদ্ধ সংগীত’ বইটি পড়ে আহত হয়েছিলাম।
শামসুর রাহমান তাঁর ঋণী কবিতায় লেখেন ফাহমিদা খাতুনের রবীন্দ্র সংগীত নিয়ে:
‘ফাহমিদা সুর ভাঁজে, এ-ও এক বৃষ্টি অপরূপ
অস্তিত্ব ডুবিয়ে নামে, গীতবিতানের কিছু নিভৃত নিশ্চুপ
পাতা ওড়ে অলৌকিক কলরবে, গাংচিলের মতো ওড়ে
ঘোরে সারা ঘরে
প্রাণের ঊর্মিল জল ছুঁয়ে যায় কত ছল ভরে।’
আরেকটা কথা বলি ফাহমিদা খাতুনকে নিয়ে। এটা অবশ্য গান। আমাদের গর্বের ইতিহাস। ‘আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে’ গানটি নিয়েই কথা।
১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবসে পাকিস্তান টেলিভিশনে গান গাইছিলেন ফাহমিদা খাতুন। স্বাধিকার আন্দোলনের সেই তুঙ্গ মুহূর্তে টেলিভিশনের বাঙালি কর্মকর্তারা চাইছিলেন না টেলিভিশনে পাকিস্তানি পতাকা দেখিয়ে অধিবেশন শেষ করতে। তাই ফাহমিদা খাতুনকে নির্দেশ দেওয়া হলো গান গেয়ে মাঝ রাত পার করে দিতে। ফাহমিদা খাতুন গাইতে থাকলেন, ‘আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি, তুমি কী অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী।’ এবং সত্যিই রাত ১২টা পেরিয়ে গেলে অধিবেশন শেষ হলো। ২৩ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান টেলিভিশনে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়নি।
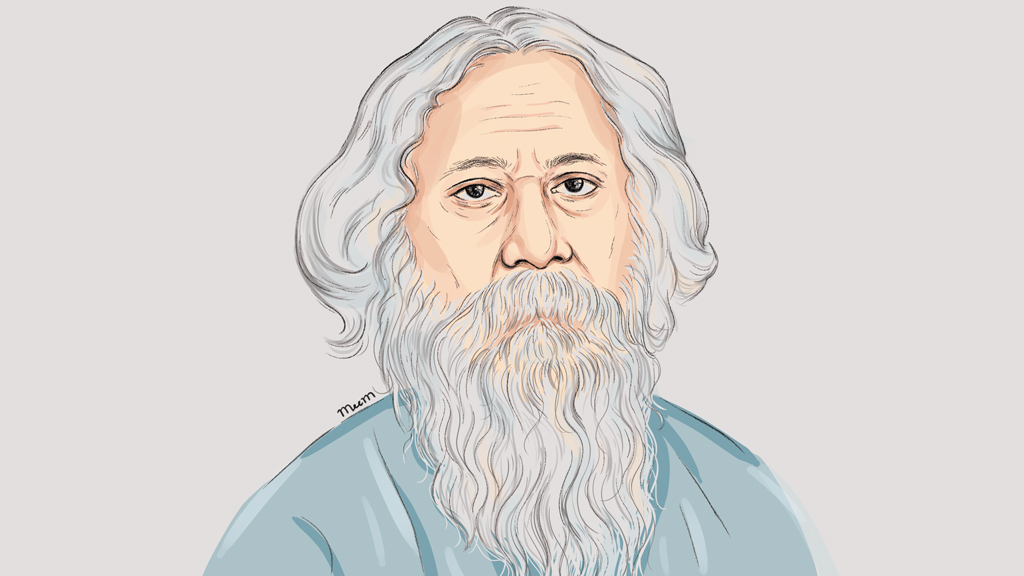
মুক্তিযুদ্ধের একপর্যায়ে যে স্বাধীনতা এল, তারই প্রশস্ত পথ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল আমাদের শৈশব। ১৯৭২ সালের বাংলাদেশকে এখনকার তরুণ চিনবে না। সেই সরু সরু রাস্তা, ছোট ছোট বাড়ি, বাড়ির সামনে লন, বড় বড় গাছ—এগুলো কি এখন আর প্রাসঙ্গিক? সে সময়ের ঢাকা শহরকে চিনতে হলে যেতে হবে মফস্বলের কোনো শহরে, কিংবা ভারতের আগরতলায়। বেশ ক’বছর আগে আগরতলায় গিয়ে মনে হয়েছিল, আরে! আমার ছেলেবেলায় দেখা ঢাকার সঙ্গে এই শহরের কত মিল!
সে সময় শহুরে তারুণ্যকে গ্রাস করেছিলেন আজম খান। তাঁর ‘রেল লাইনের ওই বস্তিতে’, ‘ওরে সালেকা ওরে মালেকা’, ‘হাইকোর্টের মাজারে’ শুনতে শুনতে মাতাল হয়ে যেত তরুণেরা। মাতাল হতো আমাদের মতো শিশুরাও। পপ সংগীত যেন আমাদের নিয়ে যেত মোক্ষধামে। বাকি সব এই ঘোরের মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল।
এরই মধ্য থেকে কখনো ঝলক দিয়ে উঠত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কোনো গান। ‘তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেবরে’, ‘সালাম সালাম হাজার সালাম’, ‘মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি।’
আর সেই গানগুলোর মধ্য থেকে ঝলক দিয়ে ওঠে, ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।’ আমাদের জাতীয় সংগীত।
বাহাত্তরে বয়স যখন ছয়, তখন আমরা চিৎকার করে জাতীয় সংগীত গাইতে থাকি। ‘মা তোর বদনখানি মলিন হলে আমি নয়নজলে ভাসি’ বলতে গিয়ে দেশের চেহারা নয়, আমার চোখে ফুটে উঠত আমার মায়ের চেহারা। রাষ্ট্রপতি আবু সায়ীদ চৌধুরী আমাদের ৫ নং চামেলিবাগের ভাড়া বাড়িতে এসে মাকে সান্ত্বনা দিয়ে চলে যাওয়ার পর যে ছবিতে আমরা আট ভাই মায়ের সঙ্গে বসে আছি, সে ছবিটাই ভেসে উঠত চোখে।
‘যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়ব না মা’, কিংবা ‘ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা’ গানটি বেসুরো কণ্ঠে গাইতে গিয়ে কখন নিজেরই অলক্ষ্যে মাটির সঙ্গে মাথার মোলাকাত হয়েছে, টেরই পাইনি।
হ্যাঁ, তখন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে গাওয়া গানগুলোর কিছু কিছু আমরা মুখস্থ করে নিয়েছিলাম। নজরুলের ‘কারার ঐ লৌহকপাট’, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ‘ধনধান্যে পুষ্পে ভরা’, অতুল প্রসাদ সেনের ‘মোদের গরব মোদের আশা’, মুকুন্দ দাসের ‘ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে’, গুরুসদয় দত্তের ‘মানুষ হ মানুষ হ আবার তোরা মানুষ হ’ গানগুলো আমাদের মোহিত করে তুলত। সলিল চৌধুরীর দুটো গান ‘মানব না এ বন্ধনে না, মানব না এ শৃঙ্খলে’, কিংবা ‘বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা’ শুনলে শরীরে অদ্ভুত শক্তি আসত। আর ছিল মোহিনী সেনের ‘মুক্তির মন্দির সোপান তলে’। এই গানটি নাচের সঙ্গে দেখতে ভালো লাগত বেশি।
এভাবেই আজম খানের প্রবল প্রমত্ত ঝড়ের মাঝে দেশের গানেরা শান্ত হয়ে মনের মাঝে বসত। কী করে সেগুলোই একসময় হয়ে উঠল তৃষ্ণার জল, সে কথাই তো বলার জন্য এই আয়োজন।
হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ
আমাদের একটা টেলিভিশন ছিল। ফিলিপস। দেশে যখন প্রথম টেলিভিশন এসেছে, তখন তার একটি এসেছিল আমাদের বাড়িতে। পাড়ার লোকেরা বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান হলে চলে আসত আমাদের বাড়িতে। তখন বারান্দায় রাখা হতো টেলিভিশন। বাড়ির সামনের লনে দাঁড়িয়ে-বসে পাড়ার মানুষেরা টিভি দেখত।
সেই টিভিতে হতো গানের অনুষ্ঠান। সম্ভবত রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠানটির নাম ছিল গীতবিতান। রাত ৮টার খবরের আগে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় বোধ হয় ছিল সে অনুষ্ঠান। সারা দিন কাজের পর আমাদের মা সে সময় একটু বসতেন টেলিভিশনের সামনে। তিনিই বলতেন সন্জীদা খাতুন, ফাহমিদা খাতুন, কলিম শরাফীর কথা। জাহেদুর রহিমের কথা। স্বীকার করে নেওয়া ভালো, সে সময় রবীন্দ্রসংগীতে মোটেই আনন্দ পেতাম না। মনে হতো, একঘেয়ে সুরে কী হচ্ছে এটা? কোথাও কোনো চমক নেই, চিৎকার নেই। একটানা কী সব কথা বলে যাওয়া হচ্ছে!
সে বয়সেই হঠাৎ করে কানে এল কয়েকটি গান। আমূল পাল্টে গেল রবীন্দ্রনাথ নিয়ে ভাবনা। গানগুলোর কয়েকটির উল্লেখ না করলে এই পাল্টে যাওয়ার ঘটনাটি বোঝা যাবে না। বলে রাখি, তখনো টেপ রেকর্ডার বা স্টেরিও সেট নেই আমাদের বাড়িতে। সম্বল এক ব্যান্ডের একটা রেডিও, আর টেলিভিশন। রেডিওটা থাকে আমাদের পঞ্চম ভ্রাতার শাসনে, ফলে সেটার কাছাকাছি হওয়া যেত শুধু সে বাড়িতে না থাকলেই।
শিশুদেরই কোনো অনুষ্ঠানে যখন শুনলাম, ‘আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে’, তখন সে গানের কথাগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে মনে হলো, আরে! এ দেখি আমার কথাই বলা হচ্ছে। আমাদের সবার কথাই বলা হচ্ছে। রাজা বলে আলাদা কেউ নেই। এ রাজা তো আমি, এ রাজা তো তুমি, এ রাজা তো সে! এ যে কী এক অনবদ্য আবিষ্কার, সেটা অনুভব না করলে বলে লাভ নেই।
তারপর ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলোরে!’ এই গান শুনতে গিয়ে একটা খটকা আসত মনে। এখানে তুমি, আর তুইয়ের ব্যবহার একই সঙ্গে করলেন কেন রবীন্দ্রনাথ, সেটা বুঝতে পারতাম না। খুদে এক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করায় সে বিজ্ঞের মতো উত্তর দিয়েছিল, ‘রবীন্দ্রনাথ তো কবি, ব্যাকরণ জানে না। বড়ুয়া স্যারের ক্লাসে গেলে রবীন্দ্রনাথ বুঝত কত ধানে কত চাল!’ উত্তরটা অবশ্য আজও পাইনি।
এবার কয়েকটি গানের কথা এক নিশ্বাসে বলে যাই, তাতে বোঝা যাবে, কেন রবীন্দ্রসংগীতকে আর প্যানপ্যানানি বলে মনে হতো না। যদিও অনেক পরে এসে বুঝতে শুরু করেছি, যাকে প্যানপ্যানানি ভেবেছি সেই ছেলেবেলায়, তা ছিল দুঃখ নামক রোগের প্রতিষেধক, নিজেকে খুঁজে পাওয়ার ওষুধ। কিন্তু সে বয়সে কে আর তা ভাবে?
‘বাঁধ ভেঙে দাও বাঁধ ভেঙে দাও।’
‘যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক।’
‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে।’
‘সংকোচের বিহ্বলতা নিজের অপমান।’
‘ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।’
‘এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে জয় মা বলে ভাসা তরী।’
অন্যরকম হলেও অনেক পরে আরেকটি গান খুব ভালো লেগেছিল, ‘বাংলার মাটি বাংলার জল’। সে কথাও বলব যথাসময়ে।
এই যে হঠাৎ করে রবীন্দ্রনাথ ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন, তা কিন্তু ‘মনে মনেই’। হারিয়ে গেছি মনে মনে। এবং হ্যাঁ, নিজের কণ্ঠে সে গান করার চেষ্টা করিনি মোটেও, নিজে বেসুরো বলে। অন্যের কণ্ঠে শুনেই প্রাণের আশ মিটিয়েছি।
কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ
স্বাধীন দেশের প্রাথমিক চলার পথে ছিল অনেক খানা-খন্দ। রাজনীতির মাঠে যে খেলা চলছিল, তাতে রেফারির বাঁশি হয়ে গিয়েছিল গৌণ। এর পর তো উদ্ভট উটের পিঠে চড়ে বসল দেশ। সে যে কোনদিকে যাচ্ছে, তা বুঝবে সাধ্য কার?
সেই অরাজকতায় ‘মানি ইজ নো প্রবলেম’ বাক্যটি হয়ে উঠল কারও কারও জন্য হীরন্ময়। রাজনীতিবিদদের জন্য রাজনীতি জটিল করে দেওয়ার খেলা শুরু হলো। মরুভূমির লু হাওয়া বইতে লাগল বাংলাদেশজুড়ে।
তখন রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলেন কী করে, সেটা একটা প্রশ্ন বটে। দেখা গেল, হারমোনিয়ামের রিডে আঙুল বুলিয়ে তুলছে রবীন্দ্রনাথের সুর। পাড়ায়-মহল্লায় সকালের দিকে তখনো শোনা যেত গলা সাধার আওয়াজ। ভোরবেলাটায় রাঙিয়ে যেত মন, ‘যাবার আগে নয়’, দিনের শুরুতেই।
সে সময় বইয়ের পাতায় আসতেন রবীন্দ্রনাথ। ‘বলাই’ কিংবা ‘ছুটি’ গল্পের মাধ্যমে তিনি ঢুকে যেতেন মনের ভিতর। গানে গানে রবীন্দ্রনাথকে পেতাম না তখন।
এর মাঝে বাড়িতে ঘটে গেল এক পরিবর্তন। মেজ ভাই মালয়েশিয়ায় গিয়েছিলেন। ফেরার পথে সেখান থেকে নিয়ে এসেছেন একটা স্টেরিও সেট। সেখানে ক্যাসেট দিলেই শোনা যাবে গান। যখন ইচ্ছে, তখন শোনা যাবে। যখন ইচ্ছে, তা বন্ধ করে অন্য একটি গান দেওয়া যাবে। গানের ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য।
সে সময় যে ক্যাসেটগুলো এল, তার একটি ছিল ‘শ্যামা’, একটি ‘চিত্রাঙ্গদা’, একটি ‘মায়ার খেলা’, একটি ‘চণ্ডালিকা’। হতে পারে দুই পিঠে দুটো গীতিনাট্য।
আলাদাভাবে এল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র সংগীতের ক্যাসেট। যে ক্যাসেট থেকে সবার আগে মুখস্থ হয়ে গেল ‘প্রাঙ্গণে মোর শিরীষ শাখায় ফাগুন মাসের কী উচ্ছ্বাসে’।
শ্যামার মধ্যেই দেখি হেমন্ত! বজ্রসেন হয়ে মঞ্চ কাঁপাচ্ছেন! এই প্রথম রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে একটু স্থিত হই। শ্যামাকে বোঝার চেষ্টা করি। বজ্রসেন আর শ্যামার মধ্যে কে বেশি আপন, তা ঠিক করে নিতে দ্বিধান্বিত হয়ে ওঠে মন। উত্তীয়কে বিপদে ফেলার পরও শ্যামাকে একমাত্র অপরাধী বলে ভাবতে ভাল্লাগে না। বজ্রসেনের জন্যই তো এত ত্যাগ, তাহলে বজ্রসেন কেন ক্ষমা করতে পারবে না শ্যামাকে! শেষে এসে বলছে ‘যাও যাও যাও, যাও ফিরে যাও।’ তারপর বলছে, ‘ক্ষম হে মম দীনতা, পাপীজন স্মরণ প্রভু।’ ‘ক্ষমিবে না আমার ক্ষমাহীনতা’—কী মারাত্মক কথা!
এইচএসসি দিলাম ১৯৮৪ সালে। এর পর ‘কণ্ঠশীলন’ নামে একটি আবৃত্তি সংগঠনে যোগ দিলাম। সেখানে কবিতার পাশাপাশি বিশ্ববীক্ষার সুযোগ হলো। রবীন্দ্রনাথের গানের পথে হাঁটার সুযোগ হলো একেবারে ভিন্ন একটি মাধ্যমে।
কণ্ঠশীলনে আবৃত্তি করতেন ফওজিয়া মান্নান। আমি তাঁকে মিলি আপা বলে ডাকি। মহড়া শেষ হলে আমরা কয়েকজন তাঁকে আর ছন্দা আপাকে তাঁদের বাড়ি পৌঁছে দিতাম। টিএসসি থেকে নীলক্ষেত হয়ে আজিমপুর কলোনিতে মিলি আপা, আর কবরস্থান ছাড়িয়ে নতুন পল্টনে ছন্দা আপাকে পৌঁছে দিতাম। ওয়াহিদুল হক সে সময় মিলি আপাদের বাড়িতে গিয়ে আটকে যেতেন। সেখানে ছিল ক্লাস নাইন পড়ুয়া তানিয়া মান্নান, মিলি আপার ছোট বোন। আমরাও কখনো কখনো বসতাম সে বাড়িতে। তানিয়া নিয়ে আসত হারমোনিয়াম। তারপর গাইত গান।
এখনো তানিয়ার রেওয়াজ করা কয়েকটি গান মনে আছে। রবীন্দ্রনাথের দিকে এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে এ গানগুলো ছিল দিশারি। একটি গান হলো, ‘আকাশ আমায় ভরল আলোয়, আকাশ আমি ভরব গানে।’ গানটা শুনি আর ভাবি, এ কি অসাধারণ কথা! বিনে পয়সার বিনিময়! আকাশ মানে সূর্য, নিশ্চয়ই আলো দিচ্ছে পৃথিবীকে, আর তাতে পৃথিবী মানে পৃথিবীর মানুষের কত আনন্দ! সে গান দিয়ে সে পুরস্কারের মূল্য দিচ্ছে!
সে সময় আরও দুটো গানের সুধা এসে মিশে যায় মনে।
‘তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি ধাই’
‘অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায়, তাহা যায়।’
গান দুটি শুনি সুবিনয় রায়ের ক্যাসেটে। রাশিয়ার দশ বছর কেটেছে এই দুই গানের ওমে। সে আরও পরের ব্যাপার।
এ ছাড়া আরও দুটি গান হলো, ‘জাগো পূরবাসী, ভগবৎ প্রেমপিয়াসি।’ অন্যটা ‘ধীরে ধীরে মোরে টেনে লহ তোমা পানে।’ পরের দুটি গান রবীন্দ্রসংগীত নয়, কিন্তু একই সঙ্গে গান তিনটি শুনতাম, এবং অবাক হয়ে খেয়াল করে দেখতাম, গান তিনটি আমাদের মুখস্থ হয়ে গেছে। আর এ সময় পেয়ে যাই এক অমোঘ বার্তা: রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে সৃষ্টিশীল সময় হলো ১৮৯১ থেকে ১৯০০ সাল। এ সময়টিতে তিনি কাটিয়েছেন পূর্ববঙ্গে!
‘আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে’
এক নতুন জগতের ঠিকানা লিখে দিল সে কালের পূর্ববঙ্গ। শাহজাদপুর, শিলাইদহ, আর পতিসর। বোটটা যেন আমি নিজের চোখে দেখি। ছিন্নপত্রগুলো ভেসে ওঠে চোখে। রবীন্দ্রনাথ নিজের চোখে মানুষ দেখছেন। তিনি সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছাচ্ছেন। এতকাল যে বদ্ধ জলাশয়ে ছিল বসবাস, সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছেন। এ যেন মহাসাগর!
গানের কথা বলছি। তাই আগে শোনা একটি গানকে এই সময়ের গায়ে লেপ্টে দিলাম:
‘আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকল খানে।’
‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলোরে’ গানটির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ওয়াহিদুল হক বলেন, ‘এ সময় বাউল সংগীতের সঙ্গে একাত্ম হচ্ছেন কবি। এই যে গানটা, সেটাও লেখা হয়েছে বাউল সুরে। একটা গান আছে, “হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে, আমার একলা নিতাই!” সেই সুরেই তো গানটা!’
গগন হরকরার ‘আমি কোথায় পাব তারে’ গানটির সুরে হলো ‘আমার সোনার বাংলা’, এখন যা আমাদের জাতীয় সংগীত। এর পর থেকে নানাভাবেই তো রবীন্দ্রনাথ এসেছেন আমার কাছে। এসেছেন তাঁর প্রবন্ধের মাধ্যমে, কবিতায়। এসেছেন অন্যদের হাত ধরে। সে রকমই কিছু কথা শোনানো জরুরি।
বিচ্ছিন্ন কিছু কথা
আমার গালে একটা চটকানা দিলেন বিষ্ণু দে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লিখলেন:
‘তুমি কি কেবল-ই স্মৃতি, শুধু এক উপলক্ষ, কবি?
হরেক উৎসবে হৈ হৈ
মঞ্চে মঞ্চে কেবল-ই কি ছবি?
তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ
আর বাইশে শ্রাবণ?’
তারপর বললেন—
‘তোমার আকাশ দাও, কবি, দাও
দীর্ঘ আশি বছরের
আমাদের ক্ষীয়মাণ মানসে ছড়াও
সূর্যোদয় সূর্যাস্তের আশি বছরের আলো,
বহুধা কীর্তিতে শত শিল্পকর্মে উন্মুক্ত উধাও
তোমার কীর্তিতে আর তোমাতে যা দিকে দিকে
একাগ্র মহৎ,
সে কঠিন ব্রতের গৌরবে,
আমাদের বিকারের গড্ডল ধুলার দিনগত অন্যায়ের কুৎসিতে
শুনি যেন সুন্দরের গান’
ওলোট পালট হয়ে গেল ভাবনার জগৎ। মেকি মনে হলো অনেক কিছুই। আসলেই কি উপলক্ষ তৈরি করে হইহই করলে রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যায়? ওই জন্ম-মৃত্যুর দুটি দিন, আর নববর্ষে ‘এসো হে বৈশাখ’ গাইলেই কর্তব্য শেষ? তাঁর গান কবিতাটিতে এসে ‘এ পরবাসে রবে কে এ পরবাসে’ পঙ্ক্তিটিতে এসে থমকে দাঁড়াই। মালতী ঘোষালকে চিনি না। কিন্তু তিনি যেন এসে গানটি শুনিয়ে যান। সে কবিতায় দেবব্রত বিশ্বাসের উদাত্ত কণ্ঠের বর্ণনা শুনে ক্যাসেটে তাঁর গান শোনার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছিলাম!
‘ব্রাত্যজনের রুদ্ধ সংগীত’ বইটি পড়ে আহত হয়েছিলাম।
শামসুর রাহমান তাঁর ঋণী কবিতায় লেখেন ফাহমিদা খাতুনের রবীন্দ্র সংগীত নিয়ে:
‘ফাহমিদা সুর ভাঁজে, এ-ও এক বৃষ্টি অপরূপ
অস্তিত্ব ডুবিয়ে নামে, গীতবিতানের কিছু নিভৃত নিশ্চুপ
পাতা ওড়ে অলৌকিক কলরবে, গাংচিলের মতো ওড়ে
ঘোরে সারা ঘরে
প্রাণের ঊর্মিল জল ছুঁয়ে যায় কত ছল ভরে।’
আরেকটা কথা বলি ফাহমিদা খাতুনকে নিয়ে। এটা অবশ্য গান। আমাদের গর্বের ইতিহাস। ‘আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে’ গানটি নিয়েই কথা।
১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবসে পাকিস্তান টেলিভিশনে গান গাইছিলেন ফাহমিদা খাতুন। স্বাধিকার আন্দোলনের সেই তুঙ্গ মুহূর্তে টেলিভিশনের বাঙালি কর্মকর্তারা চাইছিলেন না টেলিভিশনে পাকিস্তানি পতাকা দেখিয়ে অধিবেশন শেষ করতে। তাই ফাহমিদা খাতুনকে নির্দেশ দেওয়া হলো গান গেয়ে মাঝ রাত পার করে দিতে। ফাহমিদা খাতুন গাইতে থাকলেন, ‘আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি, তুমি কী অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী।’ এবং সত্যিই রাত ১২টা পেরিয়ে গেলে অধিবেশন শেষ হলো। ২৩ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান টেলিভিশনে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়নি।
জাহীদ রেজা নূর
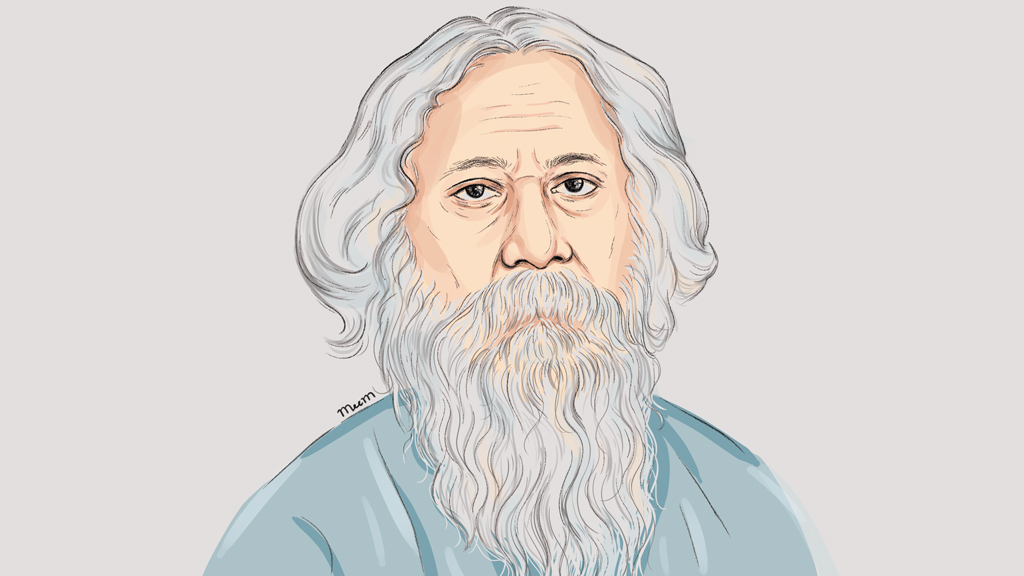
মুক্তিযুদ্ধের একপর্যায়ে যে স্বাধীনতা এল, তারই প্রশস্ত পথ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল আমাদের শৈশব। ১৯৭২ সালের বাংলাদেশকে এখনকার তরুণ চিনবে না। সেই সরু সরু রাস্তা, ছোট ছোট বাড়ি, বাড়ির সামনে লন, বড় বড় গাছ—এগুলো কি এখন আর প্রাসঙ্গিক? সে সময়ের ঢাকা শহরকে চিনতে হলে যেতে হবে মফস্বলের কোনো শহরে, কিংবা ভারতের আগরতলায়। বেশ ক’বছর আগে আগরতলায় গিয়ে মনে হয়েছিল, আরে! আমার ছেলেবেলায় দেখা ঢাকার সঙ্গে এই শহরের কত মিল!
সে সময় শহুরে তারুণ্যকে গ্রাস করেছিলেন আজম খান। তাঁর ‘রেল লাইনের ওই বস্তিতে’, ‘ওরে সালেকা ওরে মালেকা’, ‘হাইকোর্টের মাজারে’ শুনতে শুনতে মাতাল হয়ে যেত তরুণেরা। মাতাল হতো আমাদের মতো শিশুরাও। পপ সংগীত যেন আমাদের নিয়ে যেত মোক্ষধামে। বাকি সব এই ঘোরের মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল।
এরই মধ্য থেকে কখনো ঝলক দিয়ে উঠত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কোনো গান। ‘তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেবরে’, ‘সালাম সালাম হাজার সালাম’, ‘মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি।’
আর সেই গানগুলোর মধ্য থেকে ঝলক দিয়ে ওঠে, ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।’ আমাদের জাতীয় সংগীত।
বাহাত্তরে বয়স যখন ছয়, তখন আমরা চিৎকার করে জাতীয় সংগীত গাইতে থাকি। ‘মা তোর বদনখানি মলিন হলে আমি নয়নজলে ভাসি’ বলতে গিয়ে দেশের চেহারা নয়, আমার চোখে ফুটে উঠত আমার মায়ের চেহারা। রাষ্ট্রপতি আবু সায়ীদ চৌধুরী আমাদের ৫ নং চামেলিবাগের ভাড়া বাড়িতে এসে মাকে সান্ত্বনা দিয়ে চলে যাওয়ার পর যে ছবিতে আমরা আট ভাই মায়ের সঙ্গে বসে আছি, সে ছবিটাই ভেসে উঠত চোখে।
‘যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়ব না মা’, কিংবা ‘ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা’ গানটি বেসুরো কণ্ঠে গাইতে গিয়ে কখন নিজেরই অলক্ষ্যে মাটির সঙ্গে মাথার মোলাকাত হয়েছে, টেরই পাইনি।
হ্যাঁ, তখন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে গাওয়া গানগুলোর কিছু কিছু আমরা মুখস্থ করে নিয়েছিলাম। নজরুলের ‘কারার ঐ লৌহকপাট’, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ‘ধনধান্যে পুষ্পে ভরা’, অতুল প্রসাদ সেনের ‘মোদের গরব মোদের আশা’, মুকুন্দ দাসের ‘ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে’, গুরুসদয় দত্তের ‘মানুষ হ মানুষ হ আবার তোরা মানুষ হ’ গানগুলো আমাদের মোহিত করে তুলত। সলিল চৌধুরীর দুটো গান ‘মানব না এ বন্ধনে না, মানব না এ শৃঙ্খলে’, কিংবা ‘বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা’ শুনলে শরীরে অদ্ভুত শক্তি আসত। আর ছিল মোহিনী সেনের ‘মুক্তির মন্দির সোপান তলে’। এই গানটি নাচের সঙ্গে দেখতে ভালো লাগত বেশি।
এভাবেই আজম খানের প্রবল প্রমত্ত ঝড়ের মাঝে দেশের গানেরা শান্ত হয়ে মনের মাঝে বসত। কী করে সেগুলোই একসময় হয়ে উঠল তৃষ্ণার জল, সে কথাই তো বলার জন্য এই আয়োজন।
হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ
আমাদের একটা টেলিভিশন ছিল। ফিলিপস। দেশে যখন প্রথম টেলিভিশন এসেছে, তখন তার একটি এসেছিল আমাদের বাড়িতে। পাড়ার লোকেরা বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান হলে চলে আসত আমাদের বাড়িতে। তখন বারান্দায় রাখা হতো টেলিভিশন। বাড়ির সামনের লনে দাঁড়িয়ে-বসে পাড়ার মানুষেরা টিভি দেখত।
সেই টিভিতে হতো গানের অনুষ্ঠান। সম্ভবত রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠানটির নাম ছিল গীতবিতান। রাত ৮টার খবরের আগে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় বোধ হয় ছিল সে অনুষ্ঠান। সারা দিন কাজের পর আমাদের মা সে সময় একটু বসতেন টেলিভিশনের সামনে। তিনিই বলতেন সন্জীদা খাতুন, ফাহমিদা খাতুন, কলিম শরাফীর কথা। জাহেদুর রহিমের কথা। স্বীকার করে নেওয়া ভালো, সে সময় রবীন্দ্রসংগীতে মোটেই আনন্দ পেতাম না। মনে হতো, একঘেয়ে সুরে কী হচ্ছে এটা? কোথাও কোনো চমক নেই, চিৎকার নেই। একটানা কী সব কথা বলে যাওয়া হচ্ছে!
সে বয়সেই হঠাৎ করে কানে এল কয়েকটি গান। আমূল পাল্টে গেল রবীন্দ্রনাথ নিয়ে ভাবনা। গানগুলোর কয়েকটির উল্লেখ না করলে এই পাল্টে যাওয়ার ঘটনাটি বোঝা যাবে না। বলে রাখি, তখনো টেপ রেকর্ডার বা স্টেরিও সেট নেই আমাদের বাড়িতে। সম্বল এক ব্যান্ডের একটা রেডিও, আর টেলিভিশন। রেডিওটা থাকে আমাদের পঞ্চম ভ্রাতার শাসনে, ফলে সেটার কাছাকাছি হওয়া যেত শুধু সে বাড়িতে না থাকলেই।
শিশুদেরই কোনো অনুষ্ঠানে যখন শুনলাম, ‘আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে’, তখন সে গানের কথাগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে মনে হলো, আরে! এ দেখি আমার কথাই বলা হচ্ছে। আমাদের সবার কথাই বলা হচ্ছে। রাজা বলে আলাদা কেউ নেই। এ রাজা তো আমি, এ রাজা তো তুমি, এ রাজা তো সে! এ যে কী এক অনবদ্য আবিষ্কার, সেটা অনুভব না করলে বলে লাভ নেই।
তারপর ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলোরে!’ এই গান শুনতে গিয়ে একটা খটকা আসত মনে। এখানে তুমি, আর তুইয়ের ব্যবহার একই সঙ্গে করলেন কেন রবীন্দ্রনাথ, সেটা বুঝতে পারতাম না। খুদে এক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করায় সে বিজ্ঞের মতো উত্তর দিয়েছিল, ‘রবীন্দ্রনাথ তো কবি, ব্যাকরণ জানে না। বড়ুয়া স্যারের ক্লাসে গেলে রবীন্দ্রনাথ বুঝত কত ধানে কত চাল!’ উত্তরটা অবশ্য আজও পাইনি।
এবার কয়েকটি গানের কথা এক নিশ্বাসে বলে যাই, তাতে বোঝা যাবে, কেন রবীন্দ্রসংগীতকে আর প্যানপ্যানানি বলে মনে হতো না। যদিও অনেক পরে এসে বুঝতে শুরু করেছি, যাকে প্যানপ্যানানি ভেবেছি সেই ছেলেবেলায়, তা ছিল দুঃখ নামক রোগের প্রতিষেধক, নিজেকে খুঁজে পাওয়ার ওষুধ। কিন্তু সে বয়সে কে আর তা ভাবে?
‘বাঁধ ভেঙে দাও বাঁধ ভেঙে দাও।’
‘যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক।’
‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে।’
‘সংকোচের বিহ্বলতা নিজের অপমান।’
‘ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।’
‘এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে জয় মা বলে ভাসা তরী।’
অন্যরকম হলেও অনেক পরে আরেকটি গান খুব ভালো লেগেছিল, ‘বাংলার মাটি বাংলার জল’। সে কথাও বলব যথাসময়ে।
এই যে হঠাৎ করে রবীন্দ্রনাথ ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন, তা কিন্তু ‘মনে মনেই’। হারিয়ে গেছি মনে মনে। এবং হ্যাঁ, নিজের কণ্ঠে সে গান করার চেষ্টা করিনি মোটেও, নিজে বেসুরো বলে। অন্যের কণ্ঠে শুনেই প্রাণের আশ মিটিয়েছি।
কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ
স্বাধীন দেশের প্রাথমিক চলার পথে ছিল অনেক খানা-খন্দ। রাজনীতির মাঠে যে খেলা চলছিল, তাতে রেফারির বাঁশি হয়ে গিয়েছিল গৌণ। এর পর তো উদ্ভট উটের পিঠে চড়ে বসল দেশ। সে যে কোনদিকে যাচ্ছে, তা বুঝবে সাধ্য কার?
সেই অরাজকতায় ‘মানি ইজ নো প্রবলেম’ বাক্যটি হয়ে উঠল কারও কারও জন্য হীরন্ময়। রাজনীতিবিদদের জন্য রাজনীতি জটিল করে দেওয়ার খেলা শুরু হলো। মরুভূমির লু হাওয়া বইতে লাগল বাংলাদেশজুড়ে।
তখন রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলেন কী করে, সেটা একটা প্রশ্ন বটে। দেখা গেল, হারমোনিয়ামের রিডে আঙুল বুলিয়ে তুলছে রবীন্দ্রনাথের সুর। পাড়ায়-মহল্লায় সকালের দিকে তখনো শোনা যেত গলা সাধার আওয়াজ। ভোরবেলাটায় রাঙিয়ে যেত মন, ‘যাবার আগে নয়’, দিনের শুরুতেই।
সে সময় বইয়ের পাতায় আসতেন রবীন্দ্রনাথ। ‘বলাই’ কিংবা ‘ছুটি’ গল্পের মাধ্যমে তিনি ঢুকে যেতেন মনের ভিতর। গানে গানে রবীন্দ্রনাথকে পেতাম না তখন।
এর মাঝে বাড়িতে ঘটে গেল এক পরিবর্তন। মেজ ভাই মালয়েশিয়ায় গিয়েছিলেন। ফেরার পথে সেখান থেকে নিয়ে এসেছেন একটা স্টেরিও সেট। সেখানে ক্যাসেট দিলেই শোনা যাবে গান। যখন ইচ্ছে, তখন শোনা যাবে। যখন ইচ্ছে, তা বন্ধ করে অন্য একটি গান দেওয়া যাবে। গানের ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য।
সে সময় যে ক্যাসেটগুলো এল, তার একটি ছিল ‘শ্যামা’, একটি ‘চিত্রাঙ্গদা’, একটি ‘মায়ার খেলা’, একটি ‘চণ্ডালিকা’। হতে পারে দুই পিঠে দুটো গীতিনাট্য।
আলাদাভাবে এল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র সংগীতের ক্যাসেট। যে ক্যাসেট থেকে সবার আগে মুখস্থ হয়ে গেল ‘প্রাঙ্গণে মোর শিরীষ শাখায় ফাগুন মাসের কী উচ্ছ্বাসে’।
শ্যামার মধ্যেই দেখি হেমন্ত! বজ্রসেন হয়ে মঞ্চ কাঁপাচ্ছেন! এই প্রথম রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে একটু স্থিত হই। শ্যামাকে বোঝার চেষ্টা করি। বজ্রসেন আর শ্যামার মধ্যে কে বেশি আপন, তা ঠিক করে নিতে দ্বিধান্বিত হয়ে ওঠে মন। উত্তীয়কে বিপদে ফেলার পরও শ্যামাকে একমাত্র অপরাধী বলে ভাবতে ভাল্লাগে না। বজ্রসেনের জন্যই তো এত ত্যাগ, তাহলে বজ্রসেন কেন ক্ষমা করতে পারবে না শ্যামাকে! শেষে এসে বলছে ‘যাও যাও যাও, যাও ফিরে যাও।’ তারপর বলছে, ‘ক্ষম হে মম দীনতা, পাপীজন স্মরণ প্রভু।’ ‘ক্ষমিবে না আমার ক্ষমাহীনতা’—কী মারাত্মক কথা!
এইচএসসি দিলাম ১৯৮৪ সালে। এর পর ‘কণ্ঠশীলন’ নামে একটি আবৃত্তি সংগঠনে যোগ দিলাম। সেখানে কবিতার পাশাপাশি বিশ্ববীক্ষার সুযোগ হলো। রবীন্দ্রনাথের গানের পথে হাঁটার সুযোগ হলো একেবারে ভিন্ন একটি মাধ্যমে।
কণ্ঠশীলনে আবৃত্তি করতেন ফওজিয়া মান্নান। আমি তাঁকে মিলি আপা বলে ডাকি। মহড়া শেষ হলে আমরা কয়েকজন তাঁকে আর ছন্দা আপাকে তাঁদের বাড়ি পৌঁছে দিতাম। টিএসসি থেকে নীলক্ষেত হয়ে আজিমপুর কলোনিতে মিলি আপা, আর কবরস্থান ছাড়িয়ে নতুন পল্টনে ছন্দা আপাকে পৌঁছে দিতাম। ওয়াহিদুল হক সে সময় মিলি আপাদের বাড়িতে গিয়ে আটকে যেতেন। সেখানে ছিল ক্লাস নাইন পড়ুয়া তানিয়া মান্নান, মিলি আপার ছোট বোন। আমরাও কখনো কখনো বসতাম সে বাড়িতে। তানিয়া নিয়ে আসত হারমোনিয়াম। তারপর গাইত গান।
এখনো তানিয়ার রেওয়াজ করা কয়েকটি গান মনে আছে। রবীন্দ্রনাথের দিকে এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে এ গানগুলো ছিল দিশারি। একটি গান হলো, ‘আকাশ আমায় ভরল আলোয়, আকাশ আমি ভরব গানে।’ গানটা শুনি আর ভাবি, এ কি অসাধারণ কথা! বিনে পয়সার বিনিময়! আকাশ মানে সূর্য, নিশ্চয়ই আলো দিচ্ছে পৃথিবীকে, আর তাতে পৃথিবী মানে পৃথিবীর মানুষের কত আনন্দ! সে গান দিয়ে সে পুরস্কারের মূল্য দিচ্ছে!
সে সময় আরও দুটো গানের সুধা এসে মিশে যায় মনে।
‘তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি ধাই’
‘অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায়, তাহা যায়।’
গান দুটি শুনি সুবিনয় রায়ের ক্যাসেটে। রাশিয়ার দশ বছর কেটেছে এই দুই গানের ওমে। সে আরও পরের ব্যাপার।
এ ছাড়া আরও দুটি গান হলো, ‘জাগো পূরবাসী, ভগবৎ প্রেমপিয়াসি।’ অন্যটা ‘ধীরে ধীরে মোরে টেনে লহ তোমা পানে।’ পরের দুটি গান রবীন্দ্রসংগীত নয়, কিন্তু একই সঙ্গে গান তিনটি শুনতাম, এবং অবাক হয়ে খেয়াল করে দেখতাম, গান তিনটি আমাদের মুখস্থ হয়ে গেছে। আর এ সময় পেয়ে যাই এক অমোঘ বার্তা: রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে সৃষ্টিশীল সময় হলো ১৮৯১ থেকে ১৯০০ সাল। এ সময়টিতে তিনি কাটিয়েছেন পূর্ববঙ্গে!
‘আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে’
এক নতুন জগতের ঠিকানা লিখে দিল সে কালের পূর্ববঙ্গ। শাহজাদপুর, শিলাইদহ, আর পতিসর। বোটটা যেন আমি নিজের চোখে দেখি। ছিন্নপত্রগুলো ভেসে ওঠে চোখে। রবীন্দ্রনাথ নিজের চোখে মানুষ দেখছেন। তিনি সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছাচ্ছেন। এতকাল যে বদ্ধ জলাশয়ে ছিল বসবাস, সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছেন। এ যেন মহাসাগর!
গানের কথা বলছি। তাই আগে শোনা একটি গানকে এই সময়ের গায়ে লেপ্টে দিলাম:
‘আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকল খানে।’
‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলোরে’ গানটির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ওয়াহিদুল হক বলেন, ‘এ সময় বাউল সংগীতের সঙ্গে একাত্ম হচ্ছেন কবি। এই যে গানটা, সেটাও লেখা হয়েছে বাউল সুরে। একটা গান আছে, “হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে, আমার একলা নিতাই!” সেই সুরেই তো গানটা!’
গগন হরকরার ‘আমি কোথায় পাব তারে’ গানটির সুরে হলো ‘আমার সোনার বাংলা’, এখন যা আমাদের জাতীয় সংগীত। এর পর থেকে নানাভাবেই তো রবীন্দ্রনাথ এসেছেন আমার কাছে। এসেছেন তাঁর প্রবন্ধের মাধ্যমে, কবিতায়। এসেছেন অন্যদের হাত ধরে। সে রকমই কিছু কথা শোনানো জরুরি।
বিচ্ছিন্ন কিছু কথা
আমার গালে একটা চটকানা দিলেন বিষ্ণু দে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লিখলেন:
‘তুমি কি কেবল-ই স্মৃতি, শুধু এক উপলক্ষ, কবি?
হরেক উৎসবে হৈ হৈ
মঞ্চে মঞ্চে কেবল-ই কি ছবি?
তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ
আর বাইশে শ্রাবণ?’
তারপর বললেন—
‘তোমার আকাশ দাও, কবি, দাও
দীর্ঘ আশি বছরের
আমাদের ক্ষীয়মাণ মানসে ছড়াও
সূর্যোদয় সূর্যাস্তের আশি বছরের আলো,
বহুধা কীর্তিতে শত শিল্পকর্মে উন্মুক্ত উধাও
তোমার কীর্তিতে আর তোমাতে যা দিকে দিকে
একাগ্র মহৎ,
সে কঠিন ব্রতের গৌরবে,
আমাদের বিকারের গড্ডল ধুলার দিনগত অন্যায়ের কুৎসিতে
শুনি যেন সুন্দরের গান’
ওলোট পালট হয়ে গেল ভাবনার জগৎ। মেকি মনে হলো অনেক কিছুই। আসলেই কি উপলক্ষ তৈরি করে হইহই করলে রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যায়? ওই জন্ম-মৃত্যুর দুটি দিন, আর নববর্ষে ‘এসো হে বৈশাখ’ গাইলেই কর্তব্য শেষ? তাঁর গান কবিতাটিতে এসে ‘এ পরবাসে রবে কে এ পরবাসে’ পঙ্ক্তিটিতে এসে থমকে দাঁড়াই। মালতী ঘোষালকে চিনি না। কিন্তু তিনি যেন এসে গানটি শুনিয়ে যান। সে কবিতায় দেবব্রত বিশ্বাসের উদাত্ত কণ্ঠের বর্ণনা শুনে ক্যাসেটে তাঁর গান শোনার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছিলাম!
‘ব্রাত্যজনের রুদ্ধ সংগীত’ বইটি পড়ে আহত হয়েছিলাম।
শামসুর রাহমান তাঁর ঋণী কবিতায় লেখেন ফাহমিদা খাতুনের রবীন্দ্র সংগীত নিয়ে:
‘ফাহমিদা সুর ভাঁজে, এ-ও এক বৃষ্টি অপরূপ
অস্তিত্ব ডুবিয়ে নামে, গীতবিতানের কিছু নিভৃত নিশ্চুপ
পাতা ওড়ে অলৌকিক কলরবে, গাংচিলের মতো ওড়ে
ঘোরে সারা ঘরে
প্রাণের ঊর্মিল জল ছুঁয়ে যায় কত ছল ভরে।’
আরেকটা কথা বলি ফাহমিদা খাতুনকে নিয়ে। এটা অবশ্য গান। আমাদের গর্বের ইতিহাস। ‘আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে’ গানটি নিয়েই কথা।
১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবসে পাকিস্তান টেলিভিশনে গান গাইছিলেন ফাহমিদা খাতুন। স্বাধিকার আন্দোলনের সেই তুঙ্গ মুহূর্তে টেলিভিশনের বাঙালি কর্মকর্তারা চাইছিলেন না টেলিভিশনে পাকিস্তানি পতাকা দেখিয়ে অধিবেশন শেষ করতে। তাই ফাহমিদা খাতুনকে নির্দেশ দেওয়া হলো গান গেয়ে মাঝ রাত পার করে দিতে। ফাহমিদা খাতুন গাইতে থাকলেন, ‘আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি, তুমি কী অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী।’ এবং সত্যিই রাত ১২টা পেরিয়ে গেলে অধিবেশন শেষ হলো। ২৩ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান টেলিভিশনে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়নি।
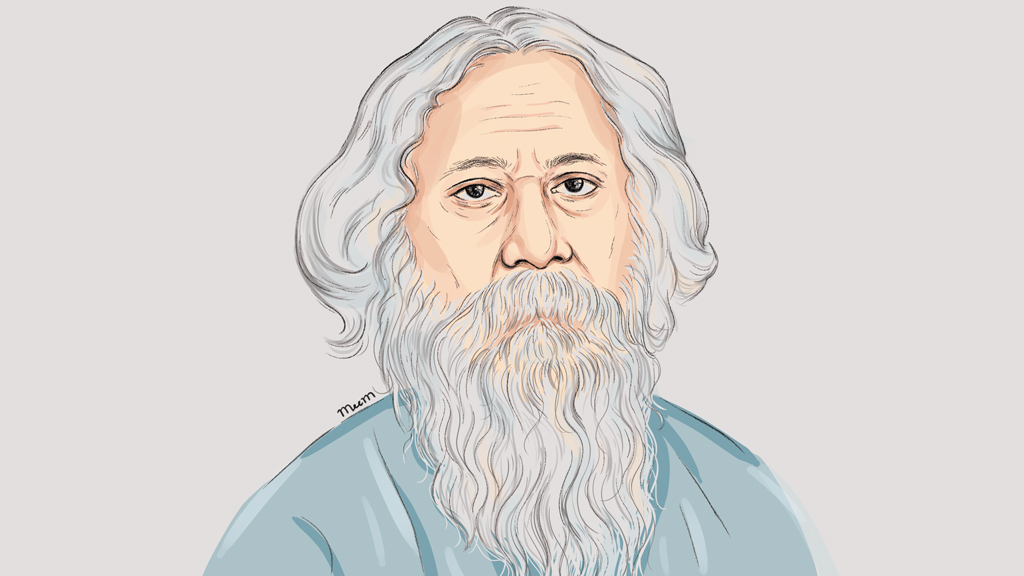
মুক্তিযুদ্ধের একপর্যায়ে যে স্বাধীনতা এল, তারই প্রশস্ত পথ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল আমাদের শৈশব। ১৯৭২ সালের বাংলাদেশকে এখনকার তরুণ চিনবে না। সেই সরু সরু রাস্তা, ছোট ছোট বাড়ি, বাড়ির সামনে লন, বড় বড় গাছ—এগুলো কি এখন আর প্রাসঙ্গিক? সে সময়ের ঢাকা শহরকে চিনতে হলে যেতে হবে মফস্বলের কোনো শহরে, কিংবা ভারতের আগরতলায়। বেশ ক’বছর আগে আগরতলায় গিয়ে মনে হয়েছিল, আরে! আমার ছেলেবেলায় দেখা ঢাকার সঙ্গে এই শহরের কত মিল!
সে সময় শহুরে তারুণ্যকে গ্রাস করেছিলেন আজম খান। তাঁর ‘রেল লাইনের ওই বস্তিতে’, ‘ওরে সালেকা ওরে মালেকা’, ‘হাইকোর্টের মাজারে’ শুনতে শুনতে মাতাল হয়ে যেত তরুণেরা। মাতাল হতো আমাদের মতো শিশুরাও। পপ সংগীত যেন আমাদের নিয়ে যেত মোক্ষধামে। বাকি সব এই ঘোরের মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল।
এরই মধ্য থেকে কখনো ঝলক দিয়ে উঠত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কোনো গান। ‘তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেবরে’, ‘সালাম সালাম হাজার সালাম’, ‘মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি।’
আর সেই গানগুলোর মধ্য থেকে ঝলক দিয়ে ওঠে, ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।’ আমাদের জাতীয় সংগীত।
বাহাত্তরে বয়স যখন ছয়, তখন আমরা চিৎকার করে জাতীয় সংগীত গাইতে থাকি। ‘মা তোর বদনখানি মলিন হলে আমি নয়নজলে ভাসি’ বলতে গিয়ে দেশের চেহারা নয়, আমার চোখে ফুটে উঠত আমার মায়ের চেহারা। রাষ্ট্রপতি আবু সায়ীদ চৌধুরী আমাদের ৫ নং চামেলিবাগের ভাড়া বাড়িতে এসে মাকে সান্ত্বনা দিয়ে চলে যাওয়ার পর যে ছবিতে আমরা আট ভাই মায়ের সঙ্গে বসে আছি, সে ছবিটাই ভেসে উঠত চোখে।
‘যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়ব না মা’, কিংবা ‘ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা’ গানটি বেসুরো কণ্ঠে গাইতে গিয়ে কখন নিজেরই অলক্ষ্যে মাটির সঙ্গে মাথার মোলাকাত হয়েছে, টেরই পাইনি।
হ্যাঁ, তখন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে গাওয়া গানগুলোর কিছু কিছু আমরা মুখস্থ করে নিয়েছিলাম। নজরুলের ‘কারার ঐ লৌহকপাট’, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ‘ধনধান্যে পুষ্পে ভরা’, অতুল প্রসাদ সেনের ‘মোদের গরব মোদের আশা’, মুকুন্দ দাসের ‘ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে’, গুরুসদয় দত্তের ‘মানুষ হ মানুষ হ আবার তোরা মানুষ হ’ গানগুলো আমাদের মোহিত করে তুলত। সলিল চৌধুরীর দুটো গান ‘মানব না এ বন্ধনে না, মানব না এ শৃঙ্খলে’, কিংবা ‘বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা’ শুনলে শরীরে অদ্ভুত শক্তি আসত। আর ছিল মোহিনী সেনের ‘মুক্তির মন্দির সোপান তলে’। এই গানটি নাচের সঙ্গে দেখতে ভালো লাগত বেশি।
এভাবেই আজম খানের প্রবল প্রমত্ত ঝড়ের মাঝে দেশের গানেরা শান্ত হয়ে মনের মাঝে বসত। কী করে সেগুলোই একসময় হয়ে উঠল তৃষ্ণার জল, সে কথাই তো বলার জন্য এই আয়োজন।
হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ
আমাদের একটা টেলিভিশন ছিল। ফিলিপস। দেশে যখন প্রথম টেলিভিশন এসেছে, তখন তার একটি এসেছিল আমাদের বাড়িতে। পাড়ার লোকেরা বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান হলে চলে আসত আমাদের বাড়িতে। তখন বারান্দায় রাখা হতো টেলিভিশন। বাড়ির সামনের লনে দাঁড়িয়ে-বসে পাড়ার মানুষেরা টিভি দেখত।
সেই টিভিতে হতো গানের অনুষ্ঠান। সম্ভবত রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠানটির নাম ছিল গীতবিতান। রাত ৮টার খবরের আগে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় বোধ হয় ছিল সে অনুষ্ঠান। সারা দিন কাজের পর আমাদের মা সে সময় একটু বসতেন টেলিভিশনের সামনে। তিনিই বলতেন সন্জীদা খাতুন, ফাহমিদা খাতুন, কলিম শরাফীর কথা। জাহেদুর রহিমের কথা। স্বীকার করে নেওয়া ভালো, সে সময় রবীন্দ্রসংগীতে মোটেই আনন্দ পেতাম না। মনে হতো, একঘেয়ে সুরে কী হচ্ছে এটা? কোথাও কোনো চমক নেই, চিৎকার নেই। একটানা কী সব কথা বলে যাওয়া হচ্ছে!
সে বয়সেই হঠাৎ করে কানে এল কয়েকটি গান। আমূল পাল্টে গেল রবীন্দ্রনাথ নিয়ে ভাবনা। গানগুলোর কয়েকটির উল্লেখ না করলে এই পাল্টে যাওয়ার ঘটনাটি বোঝা যাবে না। বলে রাখি, তখনো টেপ রেকর্ডার বা স্টেরিও সেট নেই আমাদের বাড়িতে। সম্বল এক ব্যান্ডের একটা রেডিও, আর টেলিভিশন। রেডিওটা থাকে আমাদের পঞ্চম ভ্রাতার শাসনে, ফলে সেটার কাছাকাছি হওয়া যেত শুধু সে বাড়িতে না থাকলেই।
শিশুদেরই কোনো অনুষ্ঠানে যখন শুনলাম, ‘আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে’, তখন সে গানের কথাগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে মনে হলো, আরে! এ দেখি আমার কথাই বলা হচ্ছে। আমাদের সবার কথাই বলা হচ্ছে। রাজা বলে আলাদা কেউ নেই। এ রাজা তো আমি, এ রাজা তো তুমি, এ রাজা তো সে! এ যে কী এক অনবদ্য আবিষ্কার, সেটা অনুভব না করলে বলে লাভ নেই।
তারপর ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলোরে!’ এই গান শুনতে গিয়ে একটা খটকা আসত মনে। এখানে তুমি, আর তুইয়ের ব্যবহার একই সঙ্গে করলেন কেন রবীন্দ্রনাথ, সেটা বুঝতে পারতাম না। খুদে এক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করায় সে বিজ্ঞের মতো উত্তর দিয়েছিল, ‘রবীন্দ্রনাথ তো কবি, ব্যাকরণ জানে না। বড়ুয়া স্যারের ক্লাসে গেলে রবীন্দ্রনাথ বুঝত কত ধানে কত চাল!’ উত্তরটা অবশ্য আজও পাইনি।
এবার কয়েকটি গানের কথা এক নিশ্বাসে বলে যাই, তাতে বোঝা যাবে, কেন রবীন্দ্রসংগীতকে আর প্যানপ্যানানি বলে মনে হতো না। যদিও অনেক পরে এসে বুঝতে শুরু করেছি, যাকে প্যানপ্যানানি ভেবেছি সেই ছেলেবেলায়, তা ছিল দুঃখ নামক রোগের প্রতিষেধক, নিজেকে খুঁজে পাওয়ার ওষুধ। কিন্তু সে বয়সে কে আর তা ভাবে?
‘বাঁধ ভেঙে দাও বাঁধ ভেঙে দাও।’
‘যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক।’
‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে।’
‘সংকোচের বিহ্বলতা নিজের অপমান।’
‘ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।’
‘এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে জয় মা বলে ভাসা তরী।’
অন্যরকম হলেও অনেক পরে আরেকটি গান খুব ভালো লেগেছিল, ‘বাংলার মাটি বাংলার জল’। সে কথাও বলব যথাসময়ে।
এই যে হঠাৎ করে রবীন্দ্রনাথ ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন, তা কিন্তু ‘মনে মনেই’। হারিয়ে গেছি মনে মনে। এবং হ্যাঁ, নিজের কণ্ঠে সে গান করার চেষ্টা করিনি মোটেও, নিজে বেসুরো বলে। অন্যের কণ্ঠে শুনেই প্রাণের আশ মিটিয়েছি।
কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ
স্বাধীন দেশের প্রাথমিক চলার পথে ছিল অনেক খানা-খন্দ। রাজনীতির মাঠে যে খেলা চলছিল, তাতে রেফারির বাঁশি হয়ে গিয়েছিল গৌণ। এর পর তো উদ্ভট উটের পিঠে চড়ে বসল দেশ। সে যে কোনদিকে যাচ্ছে, তা বুঝবে সাধ্য কার?
সেই অরাজকতায় ‘মানি ইজ নো প্রবলেম’ বাক্যটি হয়ে উঠল কারও কারও জন্য হীরন্ময়। রাজনীতিবিদদের জন্য রাজনীতি জটিল করে দেওয়ার খেলা শুরু হলো। মরুভূমির লু হাওয়া বইতে লাগল বাংলাদেশজুড়ে।
তখন রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলেন কী করে, সেটা একটা প্রশ্ন বটে। দেখা গেল, হারমোনিয়ামের রিডে আঙুল বুলিয়ে তুলছে রবীন্দ্রনাথের সুর। পাড়ায়-মহল্লায় সকালের দিকে তখনো শোনা যেত গলা সাধার আওয়াজ। ভোরবেলাটায় রাঙিয়ে যেত মন, ‘যাবার আগে নয়’, দিনের শুরুতেই।
সে সময় বইয়ের পাতায় আসতেন রবীন্দ্রনাথ। ‘বলাই’ কিংবা ‘ছুটি’ গল্পের মাধ্যমে তিনি ঢুকে যেতেন মনের ভিতর। গানে গানে রবীন্দ্রনাথকে পেতাম না তখন।
এর মাঝে বাড়িতে ঘটে গেল এক পরিবর্তন। মেজ ভাই মালয়েশিয়ায় গিয়েছিলেন। ফেরার পথে সেখান থেকে নিয়ে এসেছেন একটা স্টেরিও সেট। সেখানে ক্যাসেট দিলেই শোনা যাবে গান। যখন ইচ্ছে, তখন শোনা যাবে। যখন ইচ্ছে, তা বন্ধ করে অন্য একটি গান দেওয়া যাবে। গানের ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য।
সে সময় যে ক্যাসেটগুলো এল, তার একটি ছিল ‘শ্যামা’, একটি ‘চিত্রাঙ্গদা’, একটি ‘মায়ার খেলা’, একটি ‘চণ্ডালিকা’। হতে পারে দুই পিঠে দুটো গীতিনাট্য।
আলাদাভাবে এল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র সংগীতের ক্যাসেট। যে ক্যাসেট থেকে সবার আগে মুখস্থ হয়ে গেল ‘প্রাঙ্গণে মোর শিরীষ শাখায় ফাগুন মাসের কী উচ্ছ্বাসে’।
শ্যামার মধ্যেই দেখি হেমন্ত! বজ্রসেন হয়ে মঞ্চ কাঁপাচ্ছেন! এই প্রথম রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে একটু স্থিত হই। শ্যামাকে বোঝার চেষ্টা করি। বজ্রসেন আর শ্যামার মধ্যে কে বেশি আপন, তা ঠিক করে নিতে দ্বিধান্বিত হয়ে ওঠে মন। উত্তীয়কে বিপদে ফেলার পরও শ্যামাকে একমাত্র অপরাধী বলে ভাবতে ভাল্লাগে না। বজ্রসেনের জন্যই তো এত ত্যাগ, তাহলে বজ্রসেন কেন ক্ষমা করতে পারবে না শ্যামাকে! শেষে এসে বলছে ‘যাও যাও যাও, যাও ফিরে যাও।’ তারপর বলছে, ‘ক্ষম হে মম দীনতা, পাপীজন স্মরণ প্রভু।’ ‘ক্ষমিবে না আমার ক্ষমাহীনতা’—কী মারাত্মক কথা!
এইচএসসি দিলাম ১৯৮৪ সালে। এর পর ‘কণ্ঠশীলন’ নামে একটি আবৃত্তি সংগঠনে যোগ দিলাম। সেখানে কবিতার পাশাপাশি বিশ্ববীক্ষার সুযোগ হলো। রবীন্দ্রনাথের গানের পথে হাঁটার সুযোগ হলো একেবারে ভিন্ন একটি মাধ্যমে।
কণ্ঠশীলনে আবৃত্তি করতেন ফওজিয়া মান্নান। আমি তাঁকে মিলি আপা বলে ডাকি। মহড়া শেষ হলে আমরা কয়েকজন তাঁকে আর ছন্দা আপাকে তাঁদের বাড়ি পৌঁছে দিতাম। টিএসসি থেকে নীলক্ষেত হয়ে আজিমপুর কলোনিতে মিলি আপা, আর কবরস্থান ছাড়িয়ে নতুন পল্টনে ছন্দা আপাকে পৌঁছে দিতাম। ওয়াহিদুল হক সে সময় মিলি আপাদের বাড়িতে গিয়ে আটকে যেতেন। সেখানে ছিল ক্লাস নাইন পড়ুয়া তানিয়া মান্নান, মিলি আপার ছোট বোন। আমরাও কখনো কখনো বসতাম সে বাড়িতে। তানিয়া নিয়ে আসত হারমোনিয়াম। তারপর গাইত গান।
এখনো তানিয়ার রেওয়াজ করা কয়েকটি গান মনে আছে। রবীন্দ্রনাথের দিকে এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে এ গানগুলো ছিল দিশারি। একটি গান হলো, ‘আকাশ আমায় ভরল আলোয়, আকাশ আমি ভরব গানে।’ গানটা শুনি আর ভাবি, এ কি অসাধারণ কথা! বিনে পয়সার বিনিময়! আকাশ মানে সূর্য, নিশ্চয়ই আলো দিচ্ছে পৃথিবীকে, আর তাতে পৃথিবী মানে পৃথিবীর মানুষের কত আনন্দ! সে গান দিয়ে সে পুরস্কারের মূল্য দিচ্ছে!
সে সময় আরও দুটো গানের সুধা এসে মিশে যায় মনে।
‘তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি ধাই’
‘অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায়, তাহা যায়।’
গান দুটি শুনি সুবিনয় রায়ের ক্যাসেটে। রাশিয়ার দশ বছর কেটেছে এই দুই গানের ওমে। সে আরও পরের ব্যাপার।
এ ছাড়া আরও দুটি গান হলো, ‘জাগো পূরবাসী, ভগবৎ প্রেমপিয়াসি।’ অন্যটা ‘ধীরে ধীরে মোরে টেনে লহ তোমা পানে।’ পরের দুটি গান রবীন্দ্রসংগীত নয়, কিন্তু একই সঙ্গে গান তিনটি শুনতাম, এবং অবাক হয়ে খেয়াল করে দেখতাম, গান তিনটি আমাদের মুখস্থ হয়ে গেছে। আর এ সময় পেয়ে যাই এক অমোঘ বার্তা: রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে সৃষ্টিশীল সময় হলো ১৮৯১ থেকে ১৯০০ সাল। এ সময়টিতে তিনি কাটিয়েছেন পূর্ববঙ্গে!
‘আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে’
এক নতুন জগতের ঠিকানা লিখে দিল সে কালের পূর্ববঙ্গ। শাহজাদপুর, শিলাইদহ, আর পতিসর। বোটটা যেন আমি নিজের চোখে দেখি। ছিন্নপত্রগুলো ভেসে ওঠে চোখে। রবীন্দ্রনাথ নিজের চোখে মানুষ দেখছেন। তিনি সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছাচ্ছেন। এতকাল যে বদ্ধ জলাশয়ে ছিল বসবাস, সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছেন। এ যেন মহাসাগর!
গানের কথা বলছি। তাই আগে শোনা একটি গানকে এই সময়ের গায়ে লেপ্টে দিলাম:
‘আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকল খানে।’
‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলোরে’ গানটির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ওয়াহিদুল হক বলেন, ‘এ সময় বাউল সংগীতের সঙ্গে একাত্ম হচ্ছেন কবি। এই যে গানটা, সেটাও লেখা হয়েছে বাউল সুরে। একটা গান আছে, “হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে, আমার একলা নিতাই!” সেই সুরেই তো গানটা!’
গগন হরকরার ‘আমি কোথায় পাব তারে’ গানটির সুরে হলো ‘আমার সোনার বাংলা’, এখন যা আমাদের জাতীয় সংগীত। এর পর থেকে নানাভাবেই তো রবীন্দ্রনাথ এসেছেন আমার কাছে। এসেছেন তাঁর প্রবন্ধের মাধ্যমে, কবিতায়। এসেছেন অন্যদের হাত ধরে। সে রকমই কিছু কথা শোনানো জরুরি।
বিচ্ছিন্ন কিছু কথা
আমার গালে একটা চটকানা দিলেন বিষ্ণু দে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লিখলেন:
‘তুমি কি কেবল-ই স্মৃতি, শুধু এক উপলক্ষ, কবি?
হরেক উৎসবে হৈ হৈ
মঞ্চে মঞ্চে কেবল-ই কি ছবি?
তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ
আর বাইশে শ্রাবণ?’
তারপর বললেন—
‘তোমার আকাশ দাও, কবি, দাও
দীর্ঘ আশি বছরের
আমাদের ক্ষীয়মাণ মানসে ছড়াও
সূর্যোদয় সূর্যাস্তের আশি বছরের আলো,
বহুধা কীর্তিতে শত শিল্পকর্মে উন্মুক্ত উধাও
তোমার কীর্তিতে আর তোমাতে যা দিকে দিকে
একাগ্র মহৎ,
সে কঠিন ব্রতের গৌরবে,
আমাদের বিকারের গড্ডল ধুলার দিনগত অন্যায়ের কুৎসিতে
শুনি যেন সুন্দরের গান’
ওলোট পালট হয়ে গেল ভাবনার জগৎ। মেকি মনে হলো অনেক কিছুই। আসলেই কি উপলক্ষ তৈরি করে হইহই করলে রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যায়? ওই জন্ম-মৃত্যুর দুটি দিন, আর নববর্ষে ‘এসো হে বৈশাখ’ গাইলেই কর্তব্য শেষ? তাঁর গান কবিতাটিতে এসে ‘এ পরবাসে রবে কে এ পরবাসে’ পঙ্ক্তিটিতে এসে থমকে দাঁড়াই। মালতী ঘোষালকে চিনি না। কিন্তু তিনি যেন এসে গানটি শুনিয়ে যান। সে কবিতায় দেবব্রত বিশ্বাসের উদাত্ত কণ্ঠের বর্ণনা শুনে ক্যাসেটে তাঁর গান শোনার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছিলাম!
‘ব্রাত্যজনের রুদ্ধ সংগীত’ বইটি পড়ে আহত হয়েছিলাম।
শামসুর রাহমান তাঁর ঋণী কবিতায় লেখেন ফাহমিদা খাতুনের রবীন্দ্র সংগীত নিয়ে:
‘ফাহমিদা সুর ভাঁজে, এ-ও এক বৃষ্টি অপরূপ
অস্তিত্ব ডুবিয়ে নামে, গীতবিতানের কিছু নিভৃত নিশ্চুপ
পাতা ওড়ে অলৌকিক কলরবে, গাংচিলের মতো ওড়ে
ঘোরে সারা ঘরে
প্রাণের ঊর্মিল জল ছুঁয়ে যায় কত ছল ভরে।’
আরেকটা কথা বলি ফাহমিদা খাতুনকে নিয়ে। এটা অবশ্য গান। আমাদের গর্বের ইতিহাস। ‘আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে’ গানটি নিয়েই কথা।
১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবসে পাকিস্তান টেলিভিশনে গান গাইছিলেন ফাহমিদা খাতুন। স্বাধিকার আন্দোলনের সেই তুঙ্গ মুহূর্তে টেলিভিশনের বাঙালি কর্মকর্তারা চাইছিলেন না টেলিভিশনে পাকিস্তানি পতাকা দেখিয়ে অধিবেশন শেষ করতে। তাই ফাহমিদা খাতুনকে নির্দেশ দেওয়া হলো গান গেয়ে মাঝ রাত পার করে দিতে। ফাহমিদা খাতুন গাইতে থাকলেন, ‘আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি, তুমি কী অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী।’ এবং সত্যিই রাত ১২টা পেরিয়ে গেলে অধিবেশন শেষ হলো। ২৩ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান টেলিভিশনে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়নি।

ইতিহাসের সবচেয়ে কুখ্যাত মাদক সম্রাট কে? হয়তো আপনি পাবলো এস্কোবার বা এল চ্যাপোর নাম বলবেন, কিন্তু আপনি ভুল! তাঁদের জন্মের প্রায় ১০০ বছর আগে এমন একজন অবিশ্বাস্য ক্ষমতাধর নারী ছিলেন, যিনি বিশাল এক মাদক সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাঁর কাছে একালের এস্কোবার এবং এল চ্যাপোকে ছ্যাঁচড়া মাদককারবারি মনে হবে।
২ দিন আগে
শিশুসাহিত্যে চিলড্রেনস বুকার পুরস্কার চালু করেছে বুকার পুরস্কার ফাউন্ডেশন। আগামী বছর থেকে এই পুরস্কার চালু হবে এবং প্রথম বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে ২০২৭ সালের শুরুর দিকে। ৮ থেকে ১২ বছর বয়সী পাঠকদের জন্য লেখা সেরা কথাসাহিত্যের জন্য ৫০ হাজার পাউন্ড (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৮১ লাখ ৫৭ হাজার ৬৪৫ টাকা) দেওয়া
২ দিন আগে
নব্বইয়ের দশকের শুরুতে ঢাকায় খুব কম দোকানেই মিলত গ্রিল চিকেন। এ তালিকার শীর্ষে হয়তো অনেকে রাখতে পারেন সায়েন্স ল্যাবের ছায়ানীড় কনফেকশনারি অ্যান্ড ফাস্ট ফুড নামের রেস্তোরাঁটিকে। এখন তো বহু রেস্তোরাঁতেই পাওয়া যায় খাবারটি। কিন্তু ছায়ানীড়ের গ্রিল চিকেন কিংবা চিকেন শর্মার কাছে হয়তো স্বাদে হেরে যেতে...
২ দিন আগে
আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, স্বাধীনতা-সংগ্রামী, কবি-লেখক চিত্তরঞ্জন দাশ ‘দেশবন্ধু’ নামেই বিখ্যাত। তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন শচীমোহন গোপ, যিনি পঞ্চাশের দশকে রাস্তার মোড়ে বিক্রি করতেন দুধ, দই আর মাঠা। ১৯৫৮ সালে হাটখোলা রোডে ইত্তেফাক মোড়ে রেস্তোরাঁ খুলে বসেন।
৪ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

ইতিহাসের সবচেয়ে কুখ্যাত মাদক সম্রাট কে? হয়তো আপনি পাবলো এস্কোবার বা এল চ্যাপোর নাম বলবেন, কিন্তু আপনি ভুল! তাঁদের জন্মের প্রায় ১০০ বছর আগে এমন একজন অবিশ্বাস্য ক্ষমতাধর নারী ছিলেন, যিনি বিশাল এক মাদক সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাঁর কাছে একালের এস্কোবার এবং এল চ্যাপোকে ছ্যাঁচড়া মাদককারবারি মনে হবে। শুধু তা-ই নয়, তাঁকে কিন্তু কখনো গহিন অরণ্যের আস্তানায় সশস্ত্র রক্ষীবেষ্টিত হয়ে আত্মগোপনে থাকতে হয়নি। তাঁর মাদক কারবারের আয় গোটা দেশের অর্থনীতিতে বড় অবদান রাখত। আর তাঁকে কখনো জেলে যাওয়ার চিন্তা করতে হয়নি। কারণ, মাদক-সংক্রান্ত অপরাধের শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা যাঁদের ছিল, তাঁরা সবাই ছিলেন তাঁর বেতনভুক্ত কর্মচারী!
তিনি আর কেউ নন, তিনি রানি ভিক্টোরিয়া। তাঁর হাতে ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দণ্ড।
রানি ভিক্টোরিয়া শুধু সাম্রাজ্য পরিচালনাতেই মাদক ব্যবহার করেননি, ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন বিভিন্ন ধরনের ড্রাগের ভক্ত। সিংহাসনে আরোহণের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর।
ভিক্টোরিয়ার অন্যতম প্রিয় মাদক ছিল আফিম। ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটেনে আফিম সেবনের ফ্যাশনেবল উপায় ছিল—অ্যালকোহলের সঙ্গে মিশিয়ে লডেনাম আকারে পান করা। তীব্র ব্যথা বা অস্বস্তি দূর করতে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো। এমনকি দাঁত ওঠার সময় শিশুদের জন্যও এটি সুপারিশ করতেন চিকিৎসকেরা। রানি ভিক্টোরিয়াও প্রতিদিন সকালে এক ঢোক লডেনাম পান করে দিন শুরু করতেন।
এ ছাড়া তিনি সেবন করতেন কোকেন। এটি তখন ছিল সম্পূর্ণ নতুন এবং বৈধ। দাঁতের ব্যথা উপশম এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য রানি কোকেন মিশ্রিত চুইংগাম ও ওয়াইন পছন্দ করতেন। প্রসবের সময় অসহনীয় যন্ত্রণা কমাতে তিনি সানন্দে ক্লোরোফর্ম গ্রহণ করেন এবং এই অভিজ্ঞতাটিকে ‘স্বর্গীয়’ বলে বর্ণনা করেছেন।
১৮৩৭ সালে যখন ভিক্টোরিয়া সিংহাসনে বসেন, উত্তরাধিকারসূত্রে একটি বড় সংকটের বোঝা তাঁর ঘাড়ে চাপে—ব্রিটিশরা চীন থেকে বিপুল পরিমাণ চা আমদানি করত। এর ফলে ব্রিটেনের সব অর্থ চীনে চলে যাচ্ছিল। আর ওই সময় ব্রিটিশদের হাতে চীনে রপ্তানি করার মতো কিছু ছিল না। ব্রিটেন মরিয়া হয়ে এমন একটি পণ্যের সন্ধান করছিল, যা চীনের লোকেরা চাইবে।
এ সমস্যার সমাধান ছিল আফিম। ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত ভারতে প্রচুর আফিম উৎপাদিত হতো। এটি ছিল অত্যন্ত কার্যকর ব্যথানাশক এবং মারাত্মকভাবে আসক্তি সৃষ্টিকারী। ফলে চীনের লোকেরা এর জন্য প্রচুর দাম দিতে প্রস্তুত ছিল। রানি ভিক্টোরিয়ার শাসন শুরু হওয়ার পর, চীনে আফিমের চালান দ্রুত বাড়তে থাকে। আফিমের কল্যাণে রাতারাতি বাণিজ্য ভারসাম্য বদলে যায়। চীনই ব্রিটিশদের কাছে ঋণী হতে শুরু করে। মাদক কারবার থেকে আসা অর্থ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মোট বার্ষিক আয়ের ১৫ থেকে ২০ শতাংশে দাঁড়ায়।
চীন সরকার মরিয়া হয়ে আফিমের প্রবাহ বন্ধ করার চেষ্টা করে। চীনের সম্রাট এই কাজের জন্য প্রশাসক লিন জেক্সুকে নিয়োগ করেন। জেক্সু রানি ভিক্টোরিয়ার কাছে একটি চিঠি লিখে ব্রিটিশদের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন—চীন যেখানে চা, রেশম ও মৃৎপাত্রের মতো উপকারী পণ্য পাঠাচ্ছে, সেখানে ব্রিটেন কেন তার বিনিময়ে কোটি কোটি মানুষকে ক্ষতিকর মাদক পাঠাচ্ছে?
রানি সেই চিঠি পড়ারও প্রয়োজন বোধ করেননি। ফলে ১৮৩৯ সালের বসন্তে লিন জেক্সু ব্রিটিশ জাহাজ বহর আটক করেন এবং প্রায় আড়াই মিলিয়ন পাউন্ড আফিম দক্ষিণ চীন সাগরে ফেলে দেন।
মাত্র ২০ বছর বয়সী রানি ভিক্টোরিয়া এই ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। যেকোনো ক্ষমতাধর সাম্রাজ্যবাদী কিশোরীর মতো তাঁর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল প্রত্যাশিতই—তিনি চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এটিই ইতিহাসে প্রথম ‘আফিম যুদ্ধ’ নামে পরিচিত।
ব্রিটিশ বাহিনী চীনা সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে এবং হাজার হাজার চীনা নাগরিককে হত্যা করে। সম্রাট বাধ্য হয়ে একটি অসম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির ফলে হংকংকে ব্রিটিশদের হাতে তুলে দিতে হয়। চীনে আফিম ঢোকার জন্য আরও বন্দর খুলে দেওয়া হয় এবং চীনে বসবাসকারী ব্রিটিশ নাগরিকেরা আইনি সুরক্ষা পান।
এ ঘটনা বিশ্বজুড়ে চীন সাম্রাজ্যের অজেয় ভাবমূর্তি ভেঙে দেয়। এভাবেই একজন একগুঁয়ে কিশোরী রানি একটি প্রাচীন, মর্যাদাপূর্ণ সভ্যতাকে তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করেন। এই নির্মম, নির্লজ্জ আত্মস্বার্থই রানি ভিক্টোরিয়াকে ইতিহাসের সবচেয়ে সফল মাদক সম্রাট বানিয়ে তোলে!
তথ্যসূত্র: টাইম

ইতিহাসের সবচেয়ে কুখ্যাত মাদক সম্রাট কে? হয়তো আপনি পাবলো এস্কোবার বা এল চ্যাপোর নাম বলবেন, কিন্তু আপনি ভুল! তাঁদের জন্মের প্রায় ১০০ বছর আগে এমন একজন অবিশ্বাস্য ক্ষমতাধর নারী ছিলেন, যিনি বিশাল এক মাদক সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাঁর কাছে একালের এস্কোবার এবং এল চ্যাপোকে ছ্যাঁচড়া মাদককারবারি মনে হবে। শুধু তা-ই নয়, তাঁকে কিন্তু কখনো গহিন অরণ্যের আস্তানায় সশস্ত্র রক্ষীবেষ্টিত হয়ে আত্মগোপনে থাকতে হয়নি। তাঁর মাদক কারবারের আয় গোটা দেশের অর্থনীতিতে বড় অবদান রাখত। আর তাঁকে কখনো জেলে যাওয়ার চিন্তা করতে হয়নি। কারণ, মাদক-সংক্রান্ত অপরাধের শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা যাঁদের ছিল, তাঁরা সবাই ছিলেন তাঁর বেতনভুক্ত কর্মচারী!
তিনি আর কেউ নন, তিনি রানি ভিক্টোরিয়া। তাঁর হাতে ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দণ্ড।
রানি ভিক্টোরিয়া শুধু সাম্রাজ্য পরিচালনাতেই মাদক ব্যবহার করেননি, ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন বিভিন্ন ধরনের ড্রাগের ভক্ত। সিংহাসনে আরোহণের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর।
ভিক্টোরিয়ার অন্যতম প্রিয় মাদক ছিল আফিম। ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটেনে আফিম সেবনের ফ্যাশনেবল উপায় ছিল—অ্যালকোহলের সঙ্গে মিশিয়ে লডেনাম আকারে পান করা। তীব্র ব্যথা বা অস্বস্তি দূর করতে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো। এমনকি দাঁত ওঠার সময় শিশুদের জন্যও এটি সুপারিশ করতেন চিকিৎসকেরা। রানি ভিক্টোরিয়াও প্রতিদিন সকালে এক ঢোক লডেনাম পান করে দিন শুরু করতেন।
এ ছাড়া তিনি সেবন করতেন কোকেন। এটি তখন ছিল সম্পূর্ণ নতুন এবং বৈধ। দাঁতের ব্যথা উপশম এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য রানি কোকেন মিশ্রিত চুইংগাম ও ওয়াইন পছন্দ করতেন। প্রসবের সময় অসহনীয় যন্ত্রণা কমাতে তিনি সানন্দে ক্লোরোফর্ম গ্রহণ করেন এবং এই অভিজ্ঞতাটিকে ‘স্বর্গীয়’ বলে বর্ণনা করেছেন।
১৮৩৭ সালে যখন ভিক্টোরিয়া সিংহাসনে বসেন, উত্তরাধিকারসূত্রে একটি বড় সংকটের বোঝা তাঁর ঘাড়ে চাপে—ব্রিটিশরা চীন থেকে বিপুল পরিমাণ চা আমদানি করত। এর ফলে ব্রিটেনের সব অর্থ চীনে চলে যাচ্ছিল। আর ওই সময় ব্রিটিশদের হাতে চীনে রপ্তানি করার মতো কিছু ছিল না। ব্রিটেন মরিয়া হয়ে এমন একটি পণ্যের সন্ধান করছিল, যা চীনের লোকেরা চাইবে।
এ সমস্যার সমাধান ছিল আফিম। ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত ভারতে প্রচুর আফিম উৎপাদিত হতো। এটি ছিল অত্যন্ত কার্যকর ব্যথানাশক এবং মারাত্মকভাবে আসক্তি সৃষ্টিকারী। ফলে চীনের লোকেরা এর জন্য প্রচুর দাম দিতে প্রস্তুত ছিল। রানি ভিক্টোরিয়ার শাসন শুরু হওয়ার পর, চীনে আফিমের চালান দ্রুত বাড়তে থাকে। আফিমের কল্যাণে রাতারাতি বাণিজ্য ভারসাম্য বদলে যায়। চীনই ব্রিটিশদের কাছে ঋণী হতে শুরু করে। মাদক কারবার থেকে আসা অর্থ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মোট বার্ষিক আয়ের ১৫ থেকে ২০ শতাংশে দাঁড়ায়।
চীন সরকার মরিয়া হয়ে আফিমের প্রবাহ বন্ধ করার চেষ্টা করে। চীনের সম্রাট এই কাজের জন্য প্রশাসক লিন জেক্সুকে নিয়োগ করেন। জেক্সু রানি ভিক্টোরিয়ার কাছে একটি চিঠি লিখে ব্রিটিশদের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন—চীন যেখানে চা, রেশম ও মৃৎপাত্রের মতো উপকারী পণ্য পাঠাচ্ছে, সেখানে ব্রিটেন কেন তার বিনিময়ে কোটি কোটি মানুষকে ক্ষতিকর মাদক পাঠাচ্ছে?
রানি সেই চিঠি পড়ারও প্রয়োজন বোধ করেননি। ফলে ১৮৩৯ সালের বসন্তে লিন জেক্সু ব্রিটিশ জাহাজ বহর আটক করেন এবং প্রায় আড়াই মিলিয়ন পাউন্ড আফিম দক্ষিণ চীন সাগরে ফেলে দেন।
মাত্র ২০ বছর বয়সী রানি ভিক্টোরিয়া এই ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। যেকোনো ক্ষমতাধর সাম্রাজ্যবাদী কিশোরীর মতো তাঁর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল প্রত্যাশিতই—তিনি চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এটিই ইতিহাসে প্রথম ‘আফিম যুদ্ধ’ নামে পরিচিত।
ব্রিটিশ বাহিনী চীনা সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে এবং হাজার হাজার চীনা নাগরিককে হত্যা করে। সম্রাট বাধ্য হয়ে একটি অসম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির ফলে হংকংকে ব্রিটিশদের হাতে তুলে দিতে হয়। চীনে আফিম ঢোকার জন্য আরও বন্দর খুলে দেওয়া হয় এবং চীনে বসবাসকারী ব্রিটিশ নাগরিকেরা আইনি সুরক্ষা পান।
এ ঘটনা বিশ্বজুড়ে চীন সাম্রাজ্যের অজেয় ভাবমূর্তি ভেঙে দেয়। এভাবেই একজন একগুঁয়ে কিশোরী রানি একটি প্রাচীন, মর্যাদাপূর্ণ সভ্যতাকে তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করেন। এই নির্মম, নির্লজ্জ আত্মস্বার্থই রানি ভিক্টোরিয়াকে ইতিহাসের সবচেয়ে সফল মাদক সম্রাট বানিয়ে তোলে!
তথ্যসূত্র: টাইম
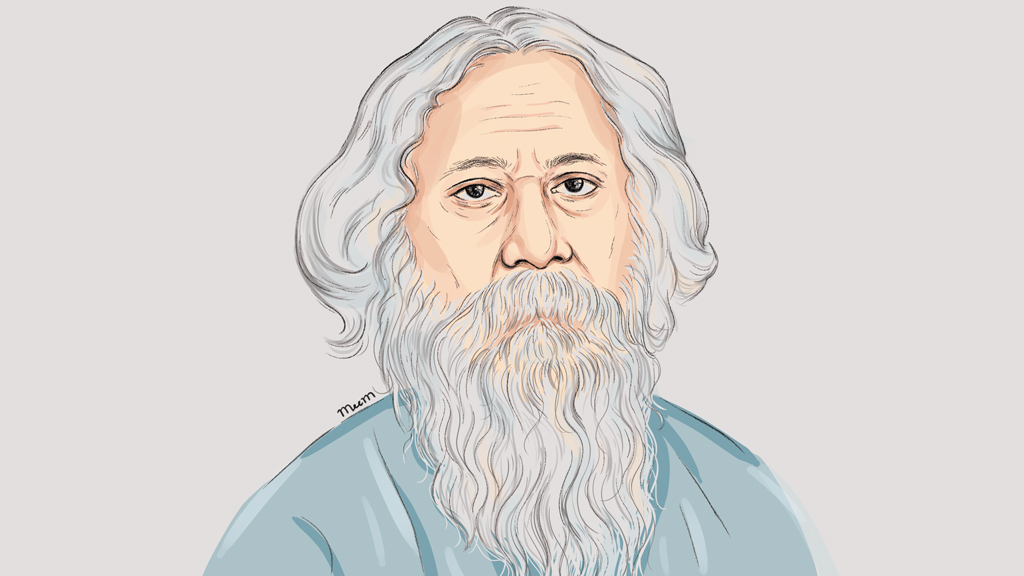
সম্ভবত রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠানটির নাম ছিল গীতবিতান। রাত ৮টার খবরের আগে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় বোধ হয় ছিল সে অনুষ্ঠান। সারা দিন কাজের পর আমাদের মা সে সময় একটু বসতেন টেলিভিশনের সামনে। তিনিই বলতেন সন্জীদা খাতুন, ফাহমিদা খাতুন, কলিম শরাফীর কথা। জাহেদুর রহিমের কথা। স্বীকার করে নেওয়া ভালো, সে সময় রবীন্দ্রসংগ
০৮ মে ২০২২
শিশুসাহিত্যে চিলড্রেনস বুকার পুরস্কার চালু করেছে বুকার পুরস্কার ফাউন্ডেশন। আগামী বছর থেকে এই পুরস্কার চালু হবে এবং প্রথম বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে ২০২৭ সালের শুরুর দিকে। ৮ থেকে ১২ বছর বয়সী পাঠকদের জন্য লেখা সেরা কথাসাহিত্যের জন্য ৫০ হাজার পাউন্ড (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৮১ লাখ ৫৭ হাজার ৬৪৫ টাকা) দেওয়া
২ দিন আগে
নব্বইয়ের দশকের শুরুতে ঢাকায় খুব কম দোকানেই মিলত গ্রিল চিকেন। এ তালিকার শীর্ষে হয়তো অনেকে রাখতে পারেন সায়েন্স ল্যাবের ছায়ানীড় কনফেকশনারি অ্যান্ড ফাস্ট ফুড নামের রেস্তোরাঁটিকে। এখন তো বহু রেস্তোরাঁতেই পাওয়া যায় খাবারটি। কিন্তু ছায়ানীড়ের গ্রিল চিকেন কিংবা চিকেন শর্মার কাছে হয়তো স্বাদে হেরে যেতে...
২ দিন আগে
আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, স্বাধীনতা-সংগ্রামী, কবি-লেখক চিত্তরঞ্জন দাশ ‘দেশবন্ধু’ নামেই বিখ্যাত। তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন শচীমোহন গোপ, যিনি পঞ্চাশের দশকে রাস্তার মোড়ে বিক্রি করতেন দুধ, দই আর মাঠা। ১৯৫৮ সালে হাটখোলা রোডে ইত্তেফাক মোড়ে রেস্তোরাঁ খুলে বসেন।
৪ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

শিশুসাহিত্যে চিলড্রেনস বুকার পুরস্কার চালু করেছে বুকার পুরস্কার ফাউন্ডেশন। আগামী বছর থেকে এই পুরস্কার চালু হবে এবং প্রথম বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে ২০২৭ সালের শুরুর দিকে। ৮ থেকে ১২ বছর বয়সী পাঠকদের জন্য লেখা সেরা কথাসাহিত্যের জন্য ৫০ হাজার পাউন্ড (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৮১ লাখ ৫৭ হাজার ৬৪৫ টাকা) দেওয়া হবে।
বুকার পুরস্কারের ইতিহাসে এই প্রথমবার বিচারক প্যানেলে থাকবে শিশুরাও। বর্তমান চিলড্রেনস লরিয়েট শিশুসাহিত্যিক ফ্রাঙ্ক কটরেল-বয়েস বিচারকদের উদ্বোধনী প্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁর সঙ্গে আরও দুজন প্রাপ্তবয়স্ক বিচারক থাকবেন, যাঁরা প্রথমে আটটি বইয়ের একটি শর্টলিস্ট তৈরি করবেন। এরপর বিজয়ী নির্ধারণে সহায়তা করার জন্য তিনজন শিশু বিচারক নির্বাচিত হবেন।
বুকার প্রাইজ ফাউন্ডেশন জানিয়েছে, প্রতিবছর চিলড্রেনস বুকার প্রাইজের জন্য শর্টলিস্টেড হওয়া এবং বিজয়ী বইগুলোর ৩০ হাজার কপি শিশুদের উপহার দেওয়া হবে। ন্যাশনাল লিটারেসি ট্রাস্ট, দ্য রিডিং এজেন্সি, বুকব্যাংকস এবং চিলড্রেনস বুক প্রজেক্টসহ বিভিন্ন সহযোগী সংস্থাদের মাধ্যমে এ বইগুলো দেওয়া হবে। গত ২০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে শিশুদের ‘আনন্দ নিয়ে পড়া’র প্রবণতা। এমন সময় বুকার প্রাইজ ফাউন্ডেশন এ উদ্যোগটি নিল।
কটরেল-বয়েস বলেন, এই পুরস্কার শিশুদের উপভোগ করার মতো বই খুঁজে বের করা সহজ করে তুলবে। তিনি আরও বলেন, ‘প্রতিটি শিশুরই বইয়ের জগতে ডুব দেওয়ার যে আনন্দ, তা উপভোগ করার সুযোগ পাওয়া উচিত। বিচারক প্যানেলে তাদের আমন্ত্রণ জানানোর মাধ্যমে এবং মনোনীত বইগুলো উপহার দেওয়ার মাধ্যমে হাজার হাজার শিশুকে বই পড়ার চমৎকার দুনিয়ায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে।’
তিনি আরও যোগ করেন, ‘এটা বেশ দারুণ আয়োজন হতে যাচ্ছে।’ তিনি মজা করে বলেন, ‘চলুন, হইচই শুরু করা যাক!’
শিশুসাহিত্য জগতের শীর্ষ লেখকদের ব্যাপক সমর্থন পেয়েছে এ ঘোষণা। সাবেক শিশুসাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত মালরি ব্ল্যাকম্যান, জ্যাকলিন উইলসন, মাইকেল মরপুরগো, ক্রেসিডা কাউয়েল, অ্যান ফাইন এবং জোসেফ কোয়েলোরা—সবাই নতুন এই পুরস্কারকে স্বাগত জানিয়েছেন।
ইংরেজিতে লেখা বা ইংরেজিতে অনূদিত এবং যুক্তরাজ্য বা আয়ারল্যান্ডে প্রকাশিত সমসাময়িক শিশুসাহিত্যগুলোতে এ পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রাপ্তবয়স্কদের বুকার এবং আন্তর্জাতিক বুকার পুরস্কারের মতোই বিজয়ী লেখক ৫০ হাজার পাউন্ড এবং শর্টলিস্টেড লেখকেরা প্রত্যেকে ২ হাজার ৫০০ পাউন্ড পাবেন।
প্রথম চিলড্রেনস বুকার পুরস্কারের জন্য আবেদন গ্রহণ শুরু হবে ২০২৬ সালের বসন্তে। বিচারক হতে শিশুদের আবেদন প্রক্রিয়াও এই সময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে। সেই বছরের নভেম্বরে ঘোষণা করা হবে শর্টলিস্ট এবং শিশু বিচারকদের নাম। বিজয়ীর নাম প্রকাশ করা হবে ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে তরুণ পাঠকদের জন্য আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে। ২০২৭ সালের পুরস্কারের জন্য ২০২৫ সালের ১ নভেম্বর থেকে ২০২৬ সালের ৩১ অক্টোবরের মধ্যে প্রকাশিত বই হতে হবে।
শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিল্পকলায় সমর্থন এবং জলবায়ু-সংকট মোকাবিলায় কাজ করা দাতব্য সংস্থা একেও ফাউন্ডেশনের (AKO Foundation) সহযোগিতায় এ পুরস্কার পরিচালিত হবে।
বুকার প্রাইজ ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী (সিইও) গ্যাবি উড বলেন, ‘২০০৫ সালে আন্তর্জাতিক বুকার প্রাইজ চালুর পর গত ২০ বছরে আমাদের সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী উদ্যোগ চিলড্রেনস বুকার। এর একাধিক লক্ষ্য রয়েছে। একদিকে এটি শিশুদের জন্য লেখা ভবিষ্যৎ ক্লাসিক সাহিত্যকে সম্মান জানাবে, অন্যদিকে এটি এমন একটি সামাজিক উদ্যোগ, যা তরুণদের আরও বেশি করে পড়াশোনায় অনুপ্রাণিত করবে। এর মাধ্যমেই আমরা এমন এক বীজ রোপণ করতে চাই, যেখান থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আজীবন পাঠকেরা বিকশিত হবে। আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি, শিশুদের বিশেষ করে শিশুসাহিত্যের আসল বিচারকদের মতামত শোনার জন্য।
একেও ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী ফিলিপ ল-ফোর্ড বলেন, ‘এই অংশীদারত্ব ফাউন্ডেশনের সাক্ষরতা বৃদ্ধি ও সামাজিক গতিশীলতা উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। আমরা গর্বিত যে এমন একটি প্রকল্পে অবদান রাখতে পারছি, যা তরুণ পাঠকদের অনুপ্রাণিত ও ক্ষমতায়িত করবে।’
বিনো ব্রেইন নামের একটি যুব গবেষণা সংস্থা ও ন্যাশনাল লিটারেসি ট্রাস্টের সহযোগিতায় নিয়মিত পরামর্শ সেশনের মাধ্যমে শিশুরা এই পুরস্কারের গঠন প্রক্রিয়ায় অংশ নেবে। ন্যাশনাল লিটারেসি ট্রাস্ট শিশুদের পড়ার অভ্যাসের দীর্ঘমেয়াদি প্রবণতা মূল্যায়নে সহায়তা করবে।
বুকার ফাউন্ডেশনের মতে, এই নতুন পুরস্কারটি শিশুসাহিত্যকে ‘সংস্কৃতির কেন্দ্রে স্থাপন’ করার একটি প্রচেষ্টা। সিইও গ্যাবি উড বলেন, ‘এই উদ্যোগের লক্ষ্য শুধু শিশুসাহিত্যে উৎকর্ষকে স্বীকৃতি দেওয়া নয়, বরং আরও বেশি তরুণকে এমন গল্প ও চরিত্র আবিষ্কারে সহায়তা করা ‘যারা তাদের সারা জীবনের সঙ্গী হয়ে থাকবে।’
বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী সাহিত্য পুরস্কার বুকার প্রাইজ প্রথম প্রদান করা হয়েছিল ১৯৬৯ সালে। যুক্তরাজ্য বা আয়ারল্যান্ডে প্রকাশিত ইংরেজিতে রচিত অসাধারণ কথাসাহিত্যকে সম্মান জানাতে এই পুরস্কার প্রবর্তিত হয়।

শিশুসাহিত্যে চিলড্রেনস বুকার পুরস্কার চালু করেছে বুকার পুরস্কার ফাউন্ডেশন। আগামী বছর থেকে এই পুরস্কার চালু হবে এবং প্রথম বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে ২০২৭ সালের শুরুর দিকে। ৮ থেকে ১২ বছর বয়সী পাঠকদের জন্য লেখা সেরা কথাসাহিত্যের জন্য ৫০ হাজার পাউন্ড (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৮১ লাখ ৫৭ হাজার ৬৪৫ টাকা) দেওয়া হবে।
বুকার পুরস্কারের ইতিহাসে এই প্রথমবার বিচারক প্যানেলে থাকবে শিশুরাও। বর্তমান চিলড্রেনস লরিয়েট শিশুসাহিত্যিক ফ্রাঙ্ক কটরেল-বয়েস বিচারকদের উদ্বোধনী প্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁর সঙ্গে আরও দুজন প্রাপ্তবয়স্ক বিচারক থাকবেন, যাঁরা প্রথমে আটটি বইয়ের একটি শর্টলিস্ট তৈরি করবেন। এরপর বিজয়ী নির্ধারণে সহায়তা করার জন্য তিনজন শিশু বিচারক নির্বাচিত হবেন।
বুকার প্রাইজ ফাউন্ডেশন জানিয়েছে, প্রতিবছর চিলড্রেনস বুকার প্রাইজের জন্য শর্টলিস্টেড হওয়া এবং বিজয়ী বইগুলোর ৩০ হাজার কপি শিশুদের উপহার দেওয়া হবে। ন্যাশনাল লিটারেসি ট্রাস্ট, দ্য রিডিং এজেন্সি, বুকব্যাংকস এবং চিলড্রেনস বুক প্রজেক্টসহ বিভিন্ন সহযোগী সংস্থাদের মাধ্যমে এ বইগুলো দেওয়া হবে। গত ২০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে শিশুদের ‘আনন্দ নিয়ে পড়া’র প্রবণতা। এমন সময় বুকার প্রাইজ ফাউন্ডেশন এ উদ্যোগটি নিল।
কটরেল-বয়েস বলেন, এই পুরস্কার শিশুদের উপভোগ করার মতো বই খুঁজে বের করা সহজ করে তুলবে। তিনি আরও বলেন, ‘প্রতিটি শিশুরই বইয়ের জগতে ডুব দেওয়ার যে আনন্দ, তা উপভোগ করার সুযোগ পাওয়া উচিত। বিচারক প্যানেলে তাদের আমন্ত্রণ জানানোর মাধ্যমে এবং মনোনীত বইগুলো উপহার দেওয়ার মাধ্যমে হাজার হাজার শিশুকে বই পড়ার চমৎকার দুনিয়ায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে।’
তিনি আরও যোগ করেন, ‘এটা বেশ দারুণ আয়োজন হতে যাচ্ছে।’ তিনি মজা করে বলেন, ‘চলুন, হইচই শুরু করা যাক!’
শিশুসাহিত্য জগতের শীর্ষ লেখকদের ব্যাপক সমর্থন পেয়েছে এ ঘোষণা। সাবেক শিশুসাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত মালরি ব্ল্যাকম্যান, জ্যাকলিন উইলসন, মাইকেল মরপুরগো, ক্রেসিডা কাউয়েল, অ্যান ফাইন এবং জোসেফ কোয়েলোরা—সবাই নতুন এই পুরস্কারকে স্বাগত জানিয়েছেন।
ইংরেজিতে লেখা বা ইংরেজিতে অনূদিত এবং যুক্তরাজ্য বা আয়ারল্যান্ডে প্রকাশিত সমসাময়িক শিশুসাহিত্যগুলোতে এ পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রাপ্তবয়স্কদের বুকার এবং আন্তর্জাতিক বুকার পুরস্কারের মতোই বিজয়ী লেখক ৫০ হাজার পাউন্ড এবং শর্টলিস্টেড লেখকেরা প্রত্যেকে ২ হাজার ৫০০ পাউন্ড পাবেন।
প্রথম চিলড্রেনস বুকার পুরস্কারের জন্য আবেদন গ্রহণ শুরু হবে ২০২৬ সালের বসন্তে। বিচারক হতে শিশুদের আবেদন প্রক্রিয়াও এই সময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে। সেই বছরের নভেম্বরে ঘোষণা করা হবে শর্টলিস্ট এবং শিশু বিচারকদের নাম। বিজয়ীর নাম প্রকাশ করা হবে ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে তরুণ পাঠকদের জন্য আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে। ২০২৭ সালের পুরস্কারের জন্য ২০২৫ সালের ১ নভেম্বর থেকে ২০২৬ সালের ৩১ অক্টোবরের মধ্যে প্রকাশিত বই হতে হবে।
শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিল্পকলায় সমর্থন এবং জলবায়ু-সংকট মোকাবিলায় কাজ করা দাতব্য সংস্থা একেও ফাউন্ডেশনের (AKO Foundation) সহযোগিতায় এ পুরস্কার পরিচালিত হবে।
বুকার প্রাইজ ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী (সিইও) গ্যাবি উড বলেন, ‘২০০৫ সালে আন্তর্জাতিক বুকার প্রাইজ চালুর পর গত ২০ বছরে আমাদের সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী উদ্যোগ চিলড্রেনস বুকার। এর একাধিক লক্ষ্য রয়েছে। একদিকে এটি শিশুদের জন্য লেখা ভবিষ্যৎ ক্লাসিক সাহিত্যকে সম্মান জানাবে, অন্যদিকে এটি এমন একটি সামাজিক উদ্যোগ, যা তরুণদের আরও বেশি করে পড়াশোনায় অনুপ্রাণিত করবে। এর মাধ্যমেই আমরা এমন এক বীজ রোপণ করতে চাই, যেখান থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আজীবন পাঠকেরা বিকশিত হবে। আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি, শিশুদের বিশেষ করে শিশুসাহিত্যের আসল বিচারকদের মতামত শোনার জন্য।
একেও ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী ফিলিপ ল-ফোর্ড বলেন, ‘এই অংশীদারত্ব ফাউন্ডেশনের সাক্ষরতা বৃদ্ধি ও সামাজিক গতিশীলতা উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। আমরা গর্বিত যে এমন একটি প্রকল্পে অবদান রাখতে পারছি, যা তরুণ পাঠকদের অনুপ্রাণিত ও ক্ষমতায়িত করবে।’
বিনো ব্রেইন নামের একটি যুব গবেষণা সংস্থা ও ন্যাশনাল লিটারেসি ট্রাস্টের সহযোগিতায় নিয়মিত পরামর্শ সেশনের মাধ্যমে শিশুরা এই পুরস্কারের গঠন প্রক্রিয়ায় অংশ নেবে। ন্যাশনাল লিটারেসি ট্রাস্ট শিশুদের পড়ার অভ্যাসের দীর্ঘমেয়াদি প্রবণতা মূল্যায়নে সহায়তা করবে।
বুকার ফাউন্ডেশনের মতে, এই নতুন পুরস্কারটি শিশুসাহিত্যকে ‘সংস্কৃতির কেন্দ্রে স্থাপন’ করার একটি প্রচেষ্টা। সিইও গ্যাবি উড বলেন, ‘এই উদ্যোগের লক্ষ্য শুধু শিশুসাহিত্যে উৎকর্ষকে স্বীকৃতি দেওয়া নয়, বরং আরও বেশি তরুণকে এমন গল্প ও চরিত্র আবিষ্কারে সহায়তা করা ‘যারা তাদের সারা জীবনের সঙ্গী হয়ে থাকবে।’
বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী সাহিত্য পুরস্কার বুকার প্রাইজ প্রথম প্রদান করা হয়েছিল ১৯৬৯ সালে। যুক্তরাজ্য বা আয়ারল্যান্ডে প্রকাশিত ইংরেজিতে রচিত অসাধারণ কথাসাহিত্যকে সম্মান জানাতে এই পুরস্কার প্রবর্তিত হয়।
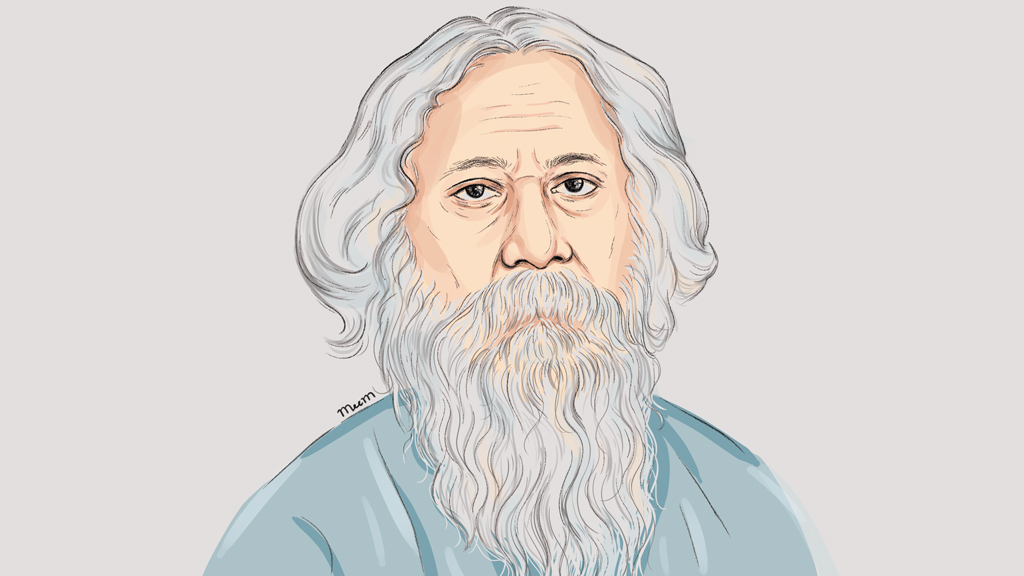
সম্ভবত রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠানটির নাম ছিল গীতবিতান। রাত ৮টার খবরের আগে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় বোধ হয় ছিল সে অনুষ্ঠান। সারা দিন কাজের পর আমাদের মা সে সময় একটু বসতেন টেলিভিশনের সামনে। তিনিই বলতেন সন্জীদা খাতুন, ফাহমিদা খাতুন, কলিম শরাফীর কথা। জাহেদুর রহিমের কথা। স্বীকার করে নেওয়া ভালো, সে সময় রবীন্দ্রসংগ
০৮ মে ২০২২
ইতিহাসের সবচেয়ে কুখ্যাত মাদক সম্রাট কে? হয়তো আপনি পাবলো এস্কোবার বা এল চ্যাপোর নাম বলবেন, কিন্তু আপনি ভুল! তাঁদের জন্মের প্রায় ১০০ বছর আগে এমন একজন অবিশ্বাস্য ক্ষমতাধর নারী ছিলেন, যিনি বিশাল এক মাদক সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাঁর কাছে একালের এস্কোবার এবং এল চ্যাপোকে ছ্যাঁচড়া মাদককারবারি মনে হবে।
২ দিন আগে
নব্বইয়ের দশকের শুরুতে ঢাকায় খুব কম দোকানেই মিলত গ্রিল চিকেন। এ তালিকার শীর্ষে হয়তো অনেকে রাখতে পারেন সায়েন্স ল্যাবের ছায়ানীড় কনফেকশনারি অ্যান্ড ফাস্ট ফুড নামের রেস্তোরাঁটিকে। এখন তো বহু রেস্তোরাঁতেই পাওয়া যায় খাবারটি। কিন্তু ছায়ানীড়ের গ্রিল চিকেন কিংবা চিকেন শর্মার কাছে হয়তো স্বাদে হেরে যেতে...
২ দিন আগে
আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, স্বাধীনতা-সংগ্রামী, কবি-লেখক চিত্তরঞ্জন দাশ ‘দেশবন্ধু’ নামেই বিখ্যাত। তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন শচীমোহন গোপ, যিনি পঞ্চাশের দশকে রাস্তার মোড়ে বিক্রি করতেন দুধ, দই আর মাঠা। ১৯৫৮ সালে হাটখোলা রোডে ইত্তেফাক মোড়ে রেস্তোরাঁ খুলে বসেন।
৪ দিন আগেসম্পাদকীয়

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে ঢাকায় খুব কম দোকানেই মিলত গ্রিল চিকেন। এ তালিকার শীর্ষে হয়তো অনেকে রাখতে পারেন সায়েন্স ল্যাবের ছায়ানীড় কনফেকশনারি অ্যান্ড ফাস্ট ফুড নামের রেস্তোরাঁটিকে। এখন তো বহু রেস্তোরাঁতেই পাওয়া যায় খাবারটি। কিন্তু ছায়ানীড়ের গ্রিল চিকেন কিংবা চিকেন শর্মার কাছে হয়তো স্বাদে হেরে যেতে পারে অন্য জায়গার এসব খাবার। অন্তত ছায়ানীড়ের নিয়মিত ভক্ত-গ্রাহকেরা এমন দাবি করতেই পারেন। তাতে দোষের কিছু নেই।
তাই হয়তো এখনো রেস্তোরাঁটির সামনে ভিড় লেগে থাকে। ব্যস্ত সড়কের পাশ থেকে যখন মুরগি পোড়ার সুঘ্রাণ পাওয়া যায়, তখন পথে যেতে অনেকেই হয়তো বিরতি নিয়ে কিনে নেন ছায়ানীড়ের শর্মা বা গ্রিল চিকেন। ভেতরে বসে খেতে হলে লম্বা লাইনে যেমন দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, আবার পার্সেল নিতে গেলেও অপেক্ষা করতে হয়। প্রাত্যহিক এ দৃশ্য ছায়ানীড়ের জনপ্রিয়তার প্রমাণ। বিরিয়ানি ও অন্যান্য ফাস্ট ফুড খাবারও পাওয়া যায় এখানে।
ছবি: ওমর ফারুক

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে ঢাকায় খুব কম দোকানেই মিলত গ্রিল চিকেন। এ তালিকার শীর্ষে হয়তো অনেকে রাখতে পারেন সায়েন্স ল্যাবের ছায়ানীড় কনফেকশনারি অ্যান্ড ফাস্ট ফুড নামের রেস্তোরাঁটিকে। এখন তো বহু রেস্তোরাঁতেই পাওয়া যায় খাবারটি। কিন্তু ছায়ানীড়ের গ্রিল চিকেন কিংবা চিকেন শর্মার কাছে হয়তো স্বাদে হেরে যেতে পারে অন্য জায়গার এসব খাবার। অন্তত ছায়ানীড়ের নিয়মিত ভক্ত-গ্রাহকেরা এমন দাবি করতেই পারেন। তাতে দোষের কিছু নেই।
তাই হয়তো এখনো রেস্তোরাঁটির সামনে ভিড় লেগে থাকে। ব্যস্ত সড়কের পাশ থেকে যখন মুরগি পোড়ার সুঘ্রাণ পাওয়া যায়, তখন পথে যেতে অনেকেই হয়তো বিরতি নিয়ে কিনে নেন ছায়ানীড়ের শর্মা বা গ্রিল চিকেন। ভেতরে বসে খেতে হলে লম্বা লাইনে যেমন দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, আবার পার্সেল নিতে গেলেও অপেক্ষা করতে হয়। প্রাত্যহিক এ দৃশ্য ছায়ানীড়ের জনপ্রিয়তার প্রমাণ। বিরিয়ানি ও অন্যান্য ফাস্ট ফুড খাবারও পাওয়া যায় এখানে।
ছবি: ওমর ফারুক
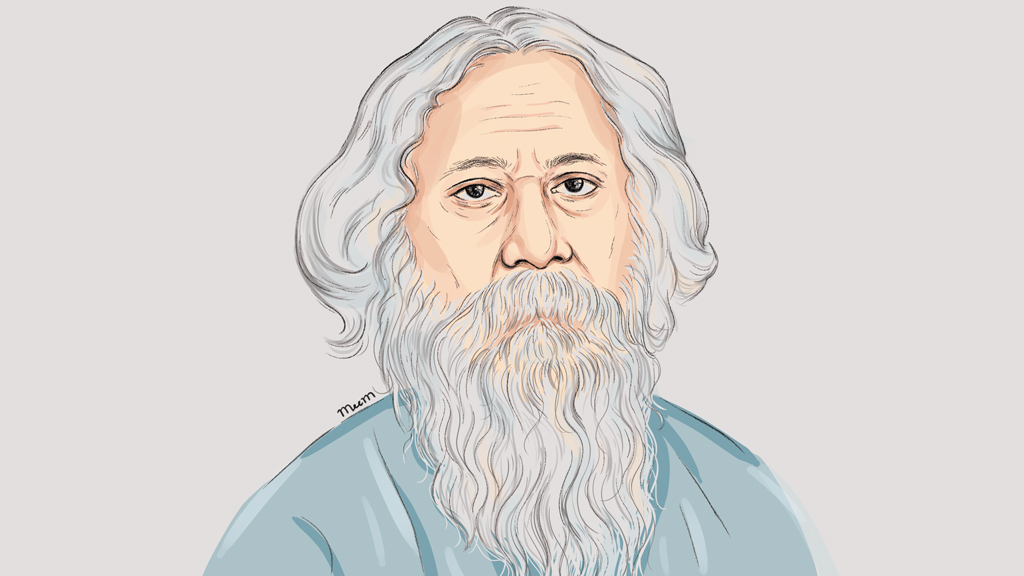
সম্ভবত রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠানটির নাম ছিল গীতবিতান। রাত ৮টার খবরের আগে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় বোধ হয় ছিল সে অনুষ্ঠান। সারা দিন কাজের পর আমাদের মা সে সময় একটু বসতেন টেলিভিশনের সামনে। তিনিই বলতেন সন্জীদা খাতুন, ফাহমিদা খাতুন, কলিম শরাফীর কথা। জাহেদুর রহিমের কথা। স্বীকার করে নেওয়া ভালো, সে সময় রবীন্দ্রসংগ
০৮ মে ২০২২
ইতিহাসের সবচেয়ে কুখ্যাত মাদক সম্রাট কে? হয়তো আপনি পাবলো এস্কোবার বা এল চ্যাপোর নাম বলবেন, কিন্তু আপনি ভুল! তাঁদের জন্মের প্রায় ১০০ বছর আগে এমন একজন অবিশ্বাস্য ক্ষমতাধর নারী ছিলেন, যিনি বিশাল এক মাদক সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাঁর কাছে একালের এস্কোবার এবং এল চ্যাপোকে ছ্যাঁচড়া মাদককারবারি মনে হবে।
২ দিন আগে
শিশুসাহিত্যে চিলড্রেনস বুকার পুরস্কার চালু করেছে বুকার পুরস্কার ফাউন্ডেশন। আগামী বছর থেকে এই পুরস্কার চালু হবে এবং প্রথম বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে ২০২৭ সালের শুরুর দিকে। ৮ থেকে ১২ বছর বয়সী পাঠকদের জন্য লেখা সেরা কথাসাহিত্যের জন্য ৫০ হাজার পাউন্ড (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৮১ লাখ ৫৭ হাজার ৬৪৫ টাকা) দেওয়া
২ দিন আগে
আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, স্বাধীনতা-সংগ্রামী, কবি-লেখক চিত্তরঞ্জন দাশ ‘দেশবন্ধু’ নামেই বিখ্যাত। তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন শচীমোহন গোপ, যিনি পঞ্চাশের দশকে রাস্তার মোড়ে বিক্রি করতেন দুধ, দই আর মাঠা। ১৯৫৮ সালে হাটখোলা রোডে ইত্তেফাক মোড়ে রেস্তোরাঁ খুলে বসেন।
৪ দিন আগেসম্পাদকীয়

আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, স্বাধীনতা-সংগ্রামী, কবি-লেখক চিত্তরঞ্জন দাশ ‘দেশবন্ধু’ নামেই বিখ্যাত। তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন শচীমোহন গোপ, যিনি পঞ্চাশের দশকে রাস্তার মোড়ে বিক্রি করতেন দুধ, দই আর মাঠা। ১৯৫৮ সালে হাটখোলা রোডে ইত্তেফাক মোড়ে রেস্তোরাঁ খুলে বসেন। বলা হয়, চিত্তরঞ্জন দাশের জীবনদর্শনে প্রভাবিত হয়েই শচীমোহন রেস্তোরাঁটির নাম দেন ‘দেশবন্ধু সুইটমিট অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট’। এর উল্টো দিকে তখন ছিল ইত্তেফাক পত্রিকার অফিস।
সেখানকার সাংবাদিকেরা দেশবন্ধুর পরোটা-লুচি-ভাজি-হালুয়া খেতে যেতেন নিয়মিত। কবি-সাহিত্যিক-অভিনয়শিল্পীরাও পছন্দ করতেন এই রেস্তোরাঁর খাবার। এমনকি এফডিসিতে ফরমাশ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো দেশবন্ধুর নাশতা। এখন হয়তো মানিক মিয়া, রাজ্জাক, কবরী কিংবা শাবানাদের মতো বিখ্যাতরা সেখানে যান না কিন্তু তাতে দেশবন্ধুর জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েনি একটুও। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এখনো ঢাকাবাসীর ভিড় দেখা যায় এই রেস্তোরাঁয়। ভাবা যায়, সারা দিনই এখানকার পরোটা-ভাজি বিক্রি হতে থাকে! দুপুরে অবশ্য খাবারের তালিকায় ভাত-মাছ-মাংসও আছে। ছবি: মেহেদী হাসান

আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, স্বাধীনতা-সংগ্রামী, কবি-লেখক চিত্তরঞ্জন দাশ ‘দেশবন্ধু’ নামেই বিখ্যাত। তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন শচীমোহন গোপ, যিনি পঞ্চাশের দশকে রাস্তার মোড়ে বিক্রি করতেন দুধ, দই আর মাঠা। ১৯৫৮ সালে হাটখোলা রোডে ইত্তেফাক মোড়ে রেস্তোরাঁ খুলে বসেন। বলা হয়, চিত্তরঞ্জন দাশের জীবনদর্শনে প্রভাবিত হয়েই শচীমোহন রেস্তোরাঁটির নাম দেন ‘দেশবন্ধু সুইটমিট অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট’। এর উল্টো দিকে তখন ছিল ইত্তেফাক পত্রিকার অফিস।
সেখানকার সাংবাদিকেরা দেশবন্ধুর পরোটা-লুচি-ভাজি-হালুয়া খেতে যেতেন নিয়মিত। কবি-সাহিত্যিক-অভিনয়শিল্পীরাও পছন্দ করতেন এই রেস্তোরাঁর খাবার। এমনকি এফডিসিতে ফরমাশ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো দেশবন্ধুর নাশতা। এখন হয়তো মানিক মিয়া, রাজ্জাক, কবরী কিংবা শাবানাদের মতো বিখ্যাতরা সেখানে যান না কিন্তু তাতে দেশবন্ধুর জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েনি একটুও। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এখনো ঢাকাবাসীর ভিড় দেখা যায় এই রেস্তোরাঁয়। ভাবা যায়, সারা দিনই এখানকার পরোটা-ভাজি বিক্রি হতে থাকে! দুপুরে অবশ্য খাবারের তালিকায় ভাত-মাছ-মাংসও আছে। ছবি: মেহেদী হাসান
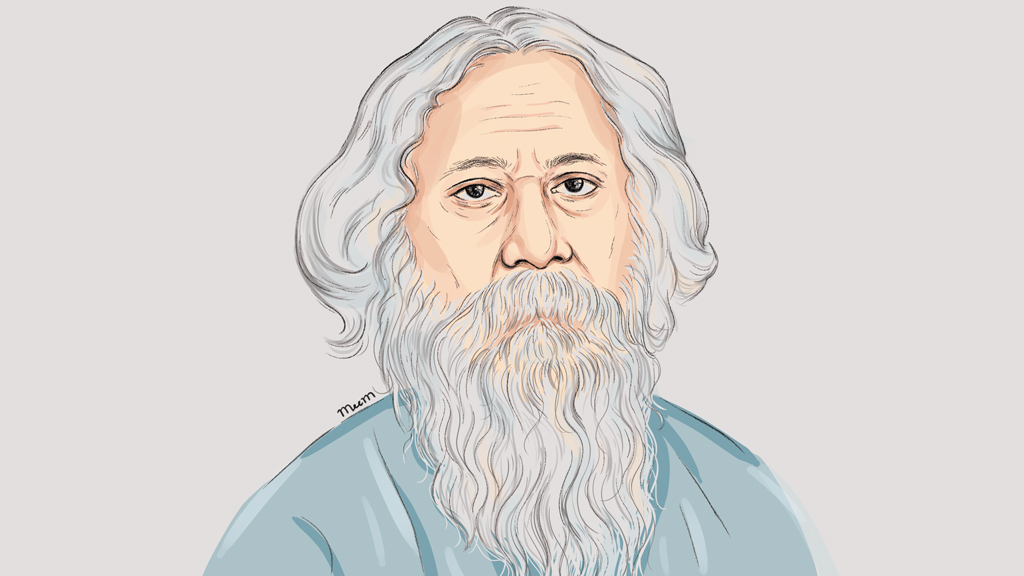
সম্ভবত রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠানটির নাম ছিল গীতবিতান। রাত ৮টার খবরের আগে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় বোধ হয় ছিল সে অনুষ্ঠান। সারা দিন কাজের পর আমাদের মা সে সময় একটু বসতেন টেলিভিশনের সামনে। তিনিই বলতেন সন্জীদা খাতুন, ফাহমিদা খাতুন, কলিম শরাফীর কথা। জাহেদুর রহিমের কথা। স্বীকার করে নেওয়া ভালো, সে সময় রবীন্দ্রসংগ
০৮ মে ২০২২
ইতিহাসের সবচেয়ে কুখ্যাত মাদক সম্রাট কে? হয়তো আপনি পাবলো এস্কোবার বা এল চ্যাপোর নাম বলবেন, কিন্তু আপনি ভুল! তাঁদের জন্মের প্রায় ১০০ বছর আগে এমন একজন অবিশ্বাস্য ক্ষমতাধর নারী ছিলেন, যিনি বিশাল এক মাদক সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাঁর কাছে একালের এস্কোবার এবং এল চ্যাপোকে ছ্যাঁচড়া মাদককারবারি মনে হবে।
২ দিন আগে
শিশুসাহিত্যে চিলড্রেনস বুকার পুরস্কার চালু করেছে বুকার পুরস্কার ফাউন্ডেশন। আগামী বছর থেকে এই পুরস্কার চালু হবে এবং প্রথম বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে ২০২৭ সালের শুরুর দিকে। ৮ থেকে ১২ বছর বয়সী পাঠকদের জন্য লেখা সেরা কথাসাহিত্যের জন্য ৫০ হাজার পাউন্ড (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৮১ লাখ ৫৭ হাজার ৬৪৫ টাকা) দেওয়া
২ দিন আগে
নব্বইয়ের দশকের শুরুতে ঢাকায় খুব কম দোকানেই মিলত গ্রিল চিকেন। এ তালিকার শীর্ষে হয়তো অনেকে রাখতে পারেন সায়েন্স ল্যাবের ছায়ানীড় কনফেকশনারি অ্যান্ড ফাস্ট ফুড নামের রেস্তোরাঁটিকে। এখন তো বহু রেস্তোরাঁতেই পাওয়া যায় খাবারটি। কিন্তু ছায়ানীড়ের গ্রিল চিকেন কিংবা চিকেন শর্মার কাছে হয়তো স্বাদে হেরে যেতে...
২ দিন আগে