মামুনুর রশীদ

গত সংখ্যায় লিখেছিলাম, এখন আর ছাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না, চারদিকে পরীক্ষার্থী। কিন্তু দ্রুতই দেখা যাচ্ছে, ছাত্র এবং পরীক্ষার্থী কাউকেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ছাত্রদের একটা বৃহদাংশ রাজনীতিবিদে পরিণত হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, তাদের অঙ্গুলি হেলনে বড় বড় রাজনৈতিক সিদ্ধান্তও হয়ে যাচ্ছে। ভেবেছিলাম প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে, ‘সেন্টার অব এক্সিলেন্স’ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। সেই আলোচনার প্রশ্ন খুব দ্রুতই শেষ হয়ে গেল। সে সময় ভবিষ্যতেও আর আসবে বলে মনে হয় না। এর একটা তাৎক্ষণিক জবাব আমার ‘জয়-জয়ন্তী’ নাটকে আছে। একটি দৃশ্যে একটি নাট্যদলের প্রধান ব্যক্তি বলছেন, ‘রাষ্ট্রে উত্থান-পতন চলছে আর সেই উত্থান-পতনের মধ্যে আমাদের আসর কেউ করছে না। রাজনীতির সঙ্গে আমাদের এই শিল্পের যে বড় বিরোধ। দ্রুতলয়ে যখন চলে সমাজ, তখন আমাদের এই শিল্প মানুষকে প্লাবিত করে না।’
মানুষ এমন এক ঘোরের মধ্যে প্রবেশ করে যখন সুদূরপ্রসারী কোনো চিন্তা মানুষকে ভাবায় না। সেই রকম এক অস্থির সময়ে আমরা আছি, যখন শুধুই এক অনিশ্চয়তার জন্ম হচ্ছে। দেশভাগের পর রাজনীতির দুটি ধারাই প্রবল হয়ে উঠেছিল। একটি জাতীয়তাবাদী এবং অসাম্প্রদায়িক ধারা। অন্যটি সমাজতান্ত্রিক ধারা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। সে সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন পুরো বিশ্বের প্রেরণার উৎস। শ্রেণিহীন সমাজ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ন্যায়সংগত হিসেবেই বিবেচিত হয়েছে। ষাটের দশকে সামরিক শাসন, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়ন সত্ত্বেও এই ধারাগুলো প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল।
ছাত্রদের আন্দোলন একটা মুখ্য শক্তি হিসেবে সামনের দিকে চলে আসে। ফলাফলে, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান এবং পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধও সংঘটিত হয়। দুটিই বাঙালি জাতিকে বিজয়ী জাতি হিসেবে মহিমান্বিত করে। পরবর্তীকালে সুদীর্ঘ সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেও একটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সফল সমাপ্তি ঘটে, যার সূচনায় ছাত্ররা না থাকলেও রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও দলগুলো রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। ছাত্ররাজনীতি তার আপন গতিতে এগিয়ে চলে।
পরবর্তীকালে নানা সংকটের উদ্ভব হলেও রাজনৈতিক নেতৃত্ব একধরনের আপসরফা করে দিন কাটালেও শেষরক্ষা হয়নি। পাকিস্তান একসময় রাজনৈতিক নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। কিন্তু যে শক্তি এ সময় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, সে-ও রাজনীতির বাইরের শক্তি, কোনো রাজনৈতিক আদর্শভিত্তিক শক্তি নয়। কোনো সুদূরপ্রসারী জনকল্যাণের কর্মসূচি নেই, বরং একেবারেই রাজনীতির বাইরের কিছু দাতা সংস্থা ও বিদেশি সাহায্যপুষ্ট কিছু ব্যক্তি এ সময় ক্ষমতায় চলে আসে।
গত আগস্টে মনে হয়েছিল এই অভ্যুত্থানে সেনাবাহিনীর একটা কার্যকর ভূমিকা আছে। দৃশ্যত পথেঘাটে সর্বত্র সেনাবাহিনীকে জনগণ আহ্বানও করেছিল। কিন্তু সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে গিয়ে সেখানে মবতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। এই মবতন্ত্রের আবির্ভাব ভয়াবহ হয়ে ওঠে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিশেষ করে পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে লড়াইরত জনতার সংঘর্ষে বিপুল হতাহতের ঘটনায় পুলিশ বাহিনীর একাংশও নিহত হয়। কার্যত এ সময় পথঘাট, পাড়া-মহল্লা সর্বত্র আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীশূন্য হয়ে পড়ে। এ সময় সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে কিছু কিছু এলাকা পাহারা দেওয়া সম্ভব হলেও এ ধরনের কাজে তারা মোটেও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। বিভিন্ন স্থানে চুরি, ডাকাতি ও রাহাজানি শুরু হয়। পুলিশ বাহিনী মোতায়েনের জন্য তাগিদ দিতে থাকে জনগণ। ক্ষমতাচ্যুত রাজনৈতিক দল মাঠ থেকে সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত হয়ে পড়ে। কিন্তু অন্য রাজনৈতিক দলগুলো এ সময় পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হয়। দলের প্রধানের নির্দেশনা উপেক্ষা করে একধরনের অন্যায় পথে তারা অগ্রসর হয়।
এই সময়টি ছিল বৃহৎ ও অবৃহৎ রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব পালনের সঠিক সময়। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার একের পর এক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপ করলেও কোনো রাজনৈতিক মীমাংসায় পৌঁছায় না। এদিকে রাজনীতিতে নতুন এক উপাদান আসে, যা হলো সংস্কার। ‘সংস্কার’ এবং ‘ঐকমত্য’ শব্দ দুটির প্রচলন হয়। অরাজনৈতিক লোকদের হাতে যদি এসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া হয়, তাহলে অভিজ্ঞতা ও সদিচ্ছার অভাবে তা ক্রমেই বিলম্বিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। সমাজে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা একটি বড় ধরনের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, যার সঙ্গে যুক্ত হয় ঐক্যের সংস্কৃতি। আদর্শগত কোনো বিষয় না থাকলে শতবর্ষ চেষ্টা করেও তা সম্ভব নয়।
অতীতে এ দেশের মানুষ এত বেশি রাজনৈতিক আলোচনা, গুজব, অনৈক্য, যার যার মতো ভবিষ্যদ্বাণী বা চর্চা করেনি। প্রতিদিন সভা, সমাবেশ, অবস্থান ধর্মঘট, দাবি আদায়ের নানা উপায়—এসব নিয়ে জনগণের ভোগান্তির শেষ নেই। কিন্তু বৃহৎ দলগুলোর নির্বাচন আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে। এ কথা ঠিক, বৃহৎ দল যারা আগেও ক্ষমতায় এসেছে, তারা একটি দ্রুত মীমাংসা চাইছে এবং যথার্থই ধৈর্যের পরিচয় দিচ্ছে। ইতিমধ্যে নানা ধরনের মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে অনেক নিরীহ মানুষ একধরনের হয়রানির শিকার হচ্ছে।
রাজনীতি কোনো পাণ্ডিত্য, বুদ্ধিমত্তা বা কৌশলের অস্ত্র প্রয়োগ নয়, এটি একটি সংস্কৃতি। এই রাজনৈতিক সংস্কৃতিটি কেউ কেউ ছোটবেলা থেকেই অনুশীলন করেন, জেল খাটেন, নিপীড়ন সহ্য করেন এবং জনগণের মনের কথাটি তাঁরা বুঝতে পারেন। তাঁরা প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করেন, আবার আপসও করেন। এই অনুশীলনের ফলাফলে গণতান্ত্রিক চর্চা গড়ে ওঠে, যার চূড়ান্ত ফলাফলটি ঘটে নির্বাচনে। এইখানেই বড় সমস্যা। অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার পরও রাজনীতিবিদেরা স্বভাবে ক্ষত্রিয় হয়ে পড়েন। লড়াইয়ের ময়দান কেউ ছাড়তে চান না এবং বুদ্ধির চেয়ে পেশিশক্তির ব্যবহার করেন সর্বত্র। সবকিছুর মধ্যেই প্রাধান্য পায় ক্ষমতা। এই ক্ষমতা নামক বিষয়টি সবকিছুকেই ম্লান করে দেয়।
ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অর্থ। যেন ক্ষমতার আরেক নামই অর্থ। অর্থ মানুষকে কতটা সুখ দিতে পারে? রাজনীতি করতে এসেই সবাই অর্থের খোঁজ করে। বিপুল পরিমাণ অর্থ তাদের চাই। এই অর্থ উপার্জন একটা পর্যায়ে লুটের অপর নাম হয়ে দাঁড়ায়। লুট করা অর্থের স্থান স্বদেশে হয় না, বিদেশে আশ্রয় খোঁজে তারা। সমৃদ্ধ দেশটি দরিদ্র হয়ে যায়। ক্ষমতা শুধু রাজনীতিকেরা ভোগ করেন না। চারপাশের ছোট-বড় আমলা, ব্যবসায়ী সবাই লুণ্ঠনে অংশ নিয়ে থাকেন।
এই অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে যে বিষয়টি সবচেয়ে প্রাধান্য পাওয়া উচিত ছিল, তা হলো দুর্নীতি; দুর্নীতিপরায়ণ সমাজটাকে কীভাবে দুর্নীতিমুক্ত করা সম্ভব। প্রয়োজনীয় একটা শিক্ষাব্যবস্থা উদ্বোধন করাও দরকার ছিল। দেখা যাচ্ছে এই রাজনৈতিক শূন্যতার মধ্য থেকে একশ্রেণির লোক দুর্নীতির নতুন নতুন পথ উদ্ভাবন করছে। সেদিকে তেমনভাবে নজর দেওয়ার সময়ও তারা পেল না। সময় দ্রুতই বয়ে যাচ্ছে। ১৮ কোটি মানুষের জীবন থেকে একটি দিনও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ কথা ঠিক, দেশ পরিচালনা করবেন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। এই প্রতিনিধিত্বকে কতটা জবাবদিহির মধ্যে নিয়ে আসা যায়, সেটাই হওয়া উচিত প্রধান বিবেচনা। সেদিকে না গিয়ে গন্ডায় গন্ডায় বৈঠক করে কালক্ষেপণই হবে।
প্রতিদিনই নানা রকমের গুজবে বিপর্যস্ত জনমানুষ, বিশেষ করে অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে সেনাবাহিনীর সম্পর্ক নিয়ে। সেনাবাহিনী জননিরাপত্তার একটি প্রধান শক্তি। সেখানে যদি নানা ধরনের প্রশ্ন পল্লবিত হতে থাকে, তাহলে তা জনগণের মধ্যেও একটা সময় সৃষ্টি হতে থাকে। প্রতিদিনই মৌলিক কিছু বিষয় নিয়ে নিষ্ফল আলোচনা হচ্ছে। মীমাংসিত বিষয় নিয়ে বারবার আলোচনার সূচনা হলে তা স্বাস্থ্যকর তো নয়ই, পথে-ঘাটে নানা ধরনের হুংকার শুনেও মানুষ ভয়ে চুপসে যাবে; রাষ্ট্র, রাজনীতি নিয়ে আতঙ্কিত হবে।
এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান। অন্য সম্প্রদায়েরও মানুষ আছে। এ দেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ এবং ধর্মভীরু। ধর্মকে নিয়ে বা ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার মানুষের বিশ্বাসকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। অন্তর্বর্তী সরকার এ ব্যাপারে তার দায়িত্বের ডালপালা না বাড়িয়ে দ্রুত জনপ্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরই শ্রেয় পথ বলে বিবেচনা করি।

গত সংখ্যায় লিখেছিলাম, এখন আর ছাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না, চারদিকে পরীক্ষার্থী। কিন্তু দ্রুতই দেখা যাচ্ছে, ছাত্র এবং পরীক্ষার্থী কাউকেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ছাত্রদের একটা বৃহদাংশ রাজনীতিবিদে পরিণত হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, তাদের অঙ্গুলি হেলনে বড় বড় রাজনৈতিক সিদ্ধান্তও হয়ে যাচ্ছে। ভেবেছিলাম প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে, ‘সেন্টার অব এক্সিলেন্স’ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। সেই আলোচনার প্রশ্ন খুব দ্রুতই শেষ হয়ে গেল। সে সময় ভবিষ্যতেও আর আসবে বলে মনে হয় না। এর একটা তাৎক্ষণিক জবাব আমার ‘জয়-জয়ন্তী’ নাটকে আছে। একটি দৃশ্যে একটি নাট্যদলের প্রধান ব্যক্তি বলছেন, ‘রাষ্ট্রে উত্থান-পতন চলছে আর সেই উত্থান-পতনের মধ্যে আমাদের আসর কেউ করছে না। রাজনীতির সঙ্গে আমাদের এই শিল্পের যে বড় বিরোধ। দ্রুতলয়ে যখন চলে সমাজ, তখন আমাদের এই শিল্প মানুষকে প্লাবিত করে না।’
মানুষ এমন এক ঘোরের মধ্যে প্রবেশ করে যখন সুদূরপ্রসারী কোনো চিন্তা মানুষকে ভাবায় না। সেই রকম এক অস্থির সময়ে আমরা আছি, যখন শুধুই এক অনিশ্চয়তার জন্ম হচ্ছে। দেশভাগের পর রাজনীতির দুটি ধারাই প্রবল হয়ে উঠেছিল। একটি জাতীয়তাবাদী এবং অসাম্প্রদায়িক ধারা। অন্যটি সমাজতান্ত্রিক ধারা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। সে সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন পুরো বিশ্বের প্রেরণার উৎস। শ্রেণিহীন সমাজ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ন্যায়সংগত হিসেবেই বিবেচিত হয়েছে। ষাটের দশকে সামরিক শাসন, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়ন সত্ত্বেও এই ধারাগুলো প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল।
ছাত্রদের আন্দোলন একটা মুখ্য শক্তি হিসেবে সামনের দিকে চলে আসে। ফলাফলে, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান এবং পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধও সংঘটিত হয়। দুটিই বাঙালি জাতিকে বিজয়ী জাতি হিসেবে মহিমান্বিত করে। পরবর্তীকালে সুদীর্ঘ সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেও একটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সফল সমাপ্তি ঘটে, যার সূচনায় ছাত্ররা না থাকলেও রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও দলগুলো রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। ছাত্ররাজনীতি তার আপন গতিতে এগিয়ে চলে।
পরবর্তীকালে নানা সংকটের উদ্ভব হলেও রাজনৈতিক নেতৃত্ব একধরনের আপসরফা করে দিন কাটালেও শেষরক্ষা হয়নি। পাকিস্তান একসময় রাজনৈতিক নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। কিন্তু যে শক্তি এ সময় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, সে-ও রাজনীতির বাইরের শক্তি, কোনো রাজনৈতিক আদর্শভিত্তিক শক্তি নয়। কোনো সুদূরপ্রসারী জনকল্যাণের কর্মসূচি নেই, বরং একেবারেই রাজনীতির বাইরের কিছু দাতা সংস্থা ও বিদেশি সাহায্যপুষ্ট কিছু ব্যক্তি এ সময় ক্ষমতায় চলে আসে।
গত আগস্টে মনে হয়েছিল এই অভ্যুত্থানে সেনাবাহিনীর একটা কার্যকর ভূমিকা আছে। দৃশ্যত পথেঘাটে সর্বত্র সেনাবাহিনীকে জনগণ আহ্বানও করেছিল। কিন্তু সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে গিয়ে সেখানে মবতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। এই মবতন্ত্রের আবির্ভাব ভয়াবহ হয়ে ওঠে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিশেষ করে পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে লড়াইরত জনতার সংঘর্ষে বিপুল হতাহতের ঘটনায় পুলিশ বাহিনীর একাংশও নিহত হয়। কার্যত এ সময় পথঘাট, পাড়া-মহল্লা সর্বত্র আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীশূন্য হয়ে পড়ে। এ সময় সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে কিছু কিছু এলাকা পাহারা দেওয়া সম্ভব হলেও এ ধরনের কাজে তারা মোটেও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। বিভিন্ন স্থানে চুরি, ডাকাতি ও রাহাজানি শুরু হয়। পুলিশ বাহিনী মোতায়েনের জন্য তাগিদ দিতে থাকে জনগণ। ক্ষমতাচ্যুত রাজনৈতিক দল মাঠ থেকে সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত হয়ে পড়ে। কিন্তু অন্য রাজনৈতিক দলগুলো এ সময় পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হয়। দলের প্রধানের নির্দেশনা উপেক্ষা করে একধরনের অন্যায় পথে তারা অগ্রসর হয়।
এই সময়টি ছিল বৃহৎ ও অবৃহৎ রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব পালনের সঠিক সময়। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার একের পর এক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপ করলেও কোনো রাজনৈতিক মীমাংসায় পৌঁছায় না। এদিকে রাজনীতিতে নতুন এক উপাদান আসে, যা হলো সংস্কার। ‘সংস্কার’ এবং ‘ঐকমত্য’ শব্দ দুটির প্রচলন হয়। অরাজনৈতিক লোকদের হাতে যদি এসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া হয়, তাহলে অভিজ্ঞতা ও সদিচ্ছার অভাবে তা ক্রমেই বিলম্বিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। সমাজে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা একটি বড় ধরনের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, যার সঙ্গে যুক্ত হয় ঐক্যের সংস্কৃতি। আদর্শগত কোনো বিষয় না থাকলে শতবর্ষ চেষ্টা করেও তা সম্ভব নয়।
অতীতে এ দেশের মানুষ এত বেশি রাজনৈতিক আলোচনা, গুজব, অনৈক্য, যার যার মতো ভবিষ্যদ্বাণী বা চর্চা করেনি। প্রতিদিন সভা, সমাবেশ, অবস্থান ধর্মঘট, দাবি আদায়ের নানা উপায়—এসব নিয়ে জনগণের ভোগান্তির শেষ নেই। কিন্তু বৃহৎ দলগুলোর নির্বাচন আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে। এ কথা ঠিক, বৃহৎ দল যারা আগেও ক্ষমতায় এসেছে, তারা একটি দ্রুত মীমাংসা চাইছে এবং যথার্থই ধৈর্যের পরিচয় দিচ্ছে। ইতিমধ্যে নানা ধরনের মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে অনেক নিরীহ মানুষ একধরনের হয়রানির শিকার হচ্ছে।
রাজনীতি কোনো পাণ্ডিত্য, বুদ্ধিমত্তা বা কৌশলের অস্ত্র প্রয়োগ নয়, এটি একটি সংস্কৃতি। এই রাজনৈতিক সংস্কৃতিটি কেউ কেউ ছোটবেলা থেকেই অনুশীলন করেন, জেল খাটেন, নিপীড়ন সহ্য করেন এবং জনগণের মনের কথাটি তাঁরা বুঝতে পারেন। তাঁরা প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করেন, আবার আপসও করেন। এই অনুশীলনের ফলাফলে গণতান্ত্রিক চর্চা গড়ে ওঠে, যার চূড়ান্ত ফলাফলটি ঘটে নির্বাচনে। এইখানেই বড় সমস্যা। অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার পরও রাজনীতিবিদেরা স্বভাবে ক্ষত্রিয় হয়ে পড়েন। লড়াইয়ের ময়দান কেউ ছাড়তে চান না এবং বুদ্ধির চেয়ে পেশিশক্তির ব্যবহার করেন সর্বত্র। সবকিছুর মধ্যেই প্রাধান্য পায় ক্ষমতা। এই ক্ষমতা নামক বিষয়টি সবকিছুকেই ম্লান করে দেয়।
ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অর্থ। যেন ক্ষমতার আরেক নামই অর্থ। অর্থ মানুষকে কতটা সুখ দিতে পারে? রাজনীতি করতে এসেই সবাই অর্থের খোঁজ করে। বিপুল পরিমাণ অর্থ তাদের চাই। এই অর্থ উপার্জন একটা পর্যায়ে লুটের অপর নাম হয়ে দাঁড়ায়। লুট করা অর্থের স্থান স্বদেশে হয় না, বিদেশে আশ্রয় খোঁজে তারা। সমৃদ্ধ দেশটি দরিদ্র হয়ে যায়। ক্ষমতা শুধু রাজনীতিকেরা ভোগ করেন না। চারপাশের ছোট-বড় আমলা, ব্যবসায়ী সবাই লুণ্ঠনে অংশ নিয়ে থাকেন।
এই অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে যে বিষয়টি সবচেয়ে প্রাধান্য পাওয়া উচিত ছিল, তা হলো দুর্নীতি; দুর্নীতিপরায়ণ সমাজটাকে কীভাবে দুর্নীতিমুক্ত করা সম্ভব। প্রয়োজনীয় একটা শিক্ষাব্যবস্থা উদ্বোধন করাও দরকার ছিল। দেখা যাচ্ছে এই রাজনৈতিক শূন্যতার মধ্য থেকে একশ্রেণির লোক দুর্নীতির নতুন নতুন পথ উদ্ভাবন করছে। সেদিকে তেমনভাবে নজর দেওয়ার সময়ও তারা পেল না। সময় দ্রুতই বয়ে যাচ্ছে। ১৮ কোটি মানুষের জীবন থেকে একটি দিনও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ কথা ঠিক, দেশ পরিচালনা করবেন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। এই প্রতিনিধিত্বকে কতটা জবাবদিহির মধ্যে নিয়ে আসা যায়, সেটাই হওয়া উচিত প্রধান বিবেচনা। সেদিকে না গিয়ে গন্ডায় গন্ডায় বৈঠক করে কালক্ষেপণই হবে।
প্রতিদিনই নানা রকমের গুজবে বিপর্যস্ত জনমানুষ, বিশেষ করে অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে সেনাবাহিনীর সম্পর্ক নিয়ে। সেনাবাহিনী জননিরাপত্তার একটি প্রধান শক্তি। সেখানে যদি নানা ধরনের প্রশ্ন পল্লবিত হতে থাকে, তাহলে তা জনগণের মধ্যেও একটা সময় সৃষ্টি হতে থাকে। প্রতিদিনই মৌলিক কিছু বিষয় নিয়ে নিষ্ফল আলোচনা হচ্ছে। মীমাংসিত বিষয় নিয়ে বারবার আলোচনার সূচনা হলে তা স্বাস্থ্যকর তো নয়ই, পথে-ঘাটে নানা ধরনের হুংকার শুনেও মানুষ ভয়ে চুপসে যাবে; রাষ্ট্র, রাজনীতি নিয়ে আতঙ্কিত হবে।
এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান। অন্য সম্প্রদায়েরও মানুষ আছে। এ দেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ এবং ধর্মভীরু। ধর্মকে নিয়ে বা ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার মানুষের বিশ্বাসকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। অন্তর্বর্তী সরকার এ ব্যাপারে তার দায়িত্বের ডালপালা না বাড়িয়ে দ্রুত জনপ্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরই শ্রেয় পথ বলে বিবেচনা করি।

ঢাকা শহরের যানজটের সমস্যা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি দিয়েছে মেট্রোরেল। তবে এটা চালুর প্রায় দেড় বছরে এই আধুনিক গণপরিবহনব্যবস্থা মাঝে মাঝে বন্ধ হয়েছে। সেটা একটা ভাবনার বিষয়। মূলত এই সময়ের মধ্যে অন্তত ১০ বার মেট্রোরেল চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়েছে, যার বেশির ভাগই জনগণের গাফিলতির কারণে হয়েছে।
১ দিন আগে
আমরা এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখি, যেখানে নানা ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গের মানুষ পরস্পরের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করবে। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় জারিত হয়ে সমাজের বৈচিত্র্যকে উদ্যাপন করবে। আমরা এমন এক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখি, যে রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের মানবিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখবে।
১ দিন আগে
পথকুকুর বা বিড়াল হত্যা গুরুতর অপরাধ এবং এটি জনস্বাস্থ্য ও পশু সুরক্ষার দিক থেকে একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী, এই ধরনের পশু হত্যা নিষ্ঠুরতা এবং মানবিক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
১ দিন আগে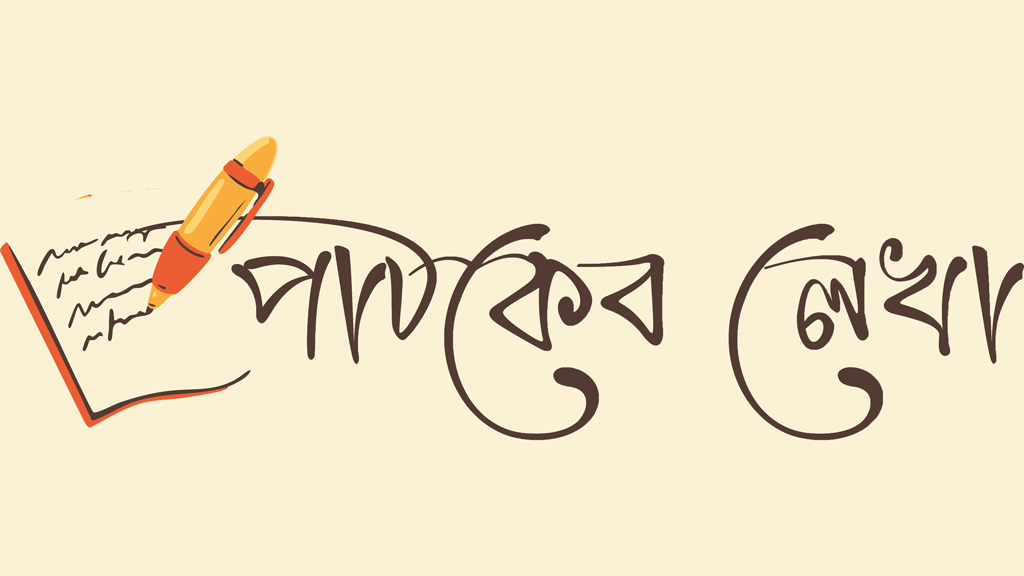
মানুষের জীবন শুধু বেঁচে থাকার নাম নয়; জীবন মানে হচ্ছে পূর্ণতার সন্ধান, মানসিক শান্তি ও শারীরিক সুস্থতার সুষম সমন্বয়। এই সমন্বয় সাধনের দুটি প্রধান উপাদান হলো সংগীত ও শরীরচর্চা। সংগীত আত্মাকে প্রশান্ত করে, মনকে উজ্জীবিত করে; আর শরীরচর্চা দেহকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখে।
১ দিন আগেসম্পাদকীয়

ঢাকা শহরের যানজটের সমস্যা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি দিয়েছে মেট্রোরেল। তবে এটা চালুর প্রায় দেড় বছরে এই আধুনিক গণপরিবহনব্যবস্থা মাঝে মাঝে বন্ধ হয়েছে। সেটা একটা ভাবনার বিষয়। মূলত এই সময়ের মধ্যে অন্তত ১০ বার মেট্রোরেল চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়েছে, যার বেশির ভাগই জনগণের গাফিলতির কারণে হয়েছে।
এই দেড় বছরে মেট্রোরেল লাইনে কাপড়, ব্যাগ, ড্রোন, তার নিক্ষেপের কারণে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে। এখনই যদি এসব সমস্যা সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ না করা যায়, তাহলে ভবিষ্যতে আরও বড় দুর্ঘটনার ঝুঁকি তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। একটা ভালো ব্যাপার যে, মেট্রোরেলের নিরাপত্তাব্যবস্থা এমন যে রেললাইনে সামান্যতম বাধা সৃষ্টি হলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেন থেমে যায়। এটি দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য ভালো দিক হলেও, মানবসৃষ্ট কারণে ঘন ঘন এই থমকে যাওয়া আধুনিক এই ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে কর্তৃপক্ষকে সেসব সমস্যা সমাধানের দিকে দৃষ্টি দেওয়া জরুরি।
জনগণ দ্বারা সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে করণীয় নিয়ে এখনই ভাবতে হবে কর্তৃপক্ষকে। তবে প্রযুক্তিগত সমস্যাও যে আছে, তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। কিছুদিন আগে ফার্মগেট এলাকায় বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ে একজনের নিহত হওয়ার ঘটনাটি এই আধুনিক পরিবহনব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা তৈরি করেছে। বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ার ঘটনায় ১১ ঘণ্টা পর্যন্ত ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। যান্ত্রিক ত্রুটি হতেই পারে, তবে গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা সরঞ্জাম বারবার বিকল হওয়া বা খুলে পড়ার ঘটনাটি মেট্রোরেলের কারিগরি তদারকি ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করেছে। এ ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত নজরদারি ও রক্ষণাবেক্ষণে আরও গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক। এক সূত্র থেকে জানা যায়, এই নিহতের ঘটনা এবং অন্যান্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মেট্রোরেলে আগের তুলনায় ১০ শতাংশ যাত্রী কমে গেছে।
যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা মেট্রোরেল চলাচল স্বাভাবিক রাখতে কিছু কার্যকর পদক্ষেপের পরামর্শ দিয়েছেন। যেমন মেট্রোরেলের লাইনে বস্তু শনাক্ত করতে ‘অবজেক্ট ডিটেকশন সেন্সর’ ও ‘এআই-চালিত সিসিটিভি’ স্থাপন করা, ড্রোন পড়া প্রতিরোধে ‘ড্রোন ডিটেকশন রাডার’ ও ‘জিওফেন্সিং সিস্টেম’ ব্যবহার করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া। এ ছাড়া বৈদ্যুতিক লাইনে সুরক্ষা নেট বসালে বাইরে থেকে তার বা বস্তু নিক্ষেপ ঠেকানো সম্ভব।
মেট্রোরেল দেশের সম্পদ। জনগণের মধ্যে সে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এর সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব। ডিএমটিসিএলকে প্রযুক্তিগত ত্রুটিগুলো দ্রুত সমাধান এবং রক্ষণাবেক্ষণে সর্বোচ্চ মান বজায় রাখতে হবে। একই সঙ্গে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে, যাতে মানুষ বুঝতে পারে তাদের সামান্য ভুল বা অসচেতনতা হাজার হাজার যাত্রীর ভোগান্তি এবং মারাত্মক দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। সচেতনতা ও প্রযুক্তিগত সুরক্ষা—এই দুইয়ের সমন্বয়েই কেবল মেট্রোরেলের মসৃণ ও নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করা সম্ভব। এই আধুনিক পরিষেবা যেন মাঝে মাঝে থমকে যাওয়ার দুর্নাম থেকে মুক্তি পায়, সেই প্রত্যাশা আমাদের।

ঢাকা শহরের যানজটের সমস্যা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি দিয়েছে মেট্রোরেল। তবে এটা চালুর প্রায় দেড় বছরে এই আধুনিক গণপরিবহনব্যবস্থা মাঝে মাঝে বন্ধ হয়েছে। সেটা একটা ভাবনার বিষয়। মূলত এই সময়ের মধ্যে অন্তত ১০ বার মেট্রোরেল চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়েছে, যার বেশির ভাগই জনগণের গাফিলতির কারণে হয়েছে।
এই দেড় বছরে মেট্রোরেল লাইনে কাপড়, ব্যাগ, ড্রোন, তার নিক্ষেপের কারণে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে। এখনই যদি এসব সমস্যা সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ না করা যায়, তাহলে ভবিষ্যতে আরও বড় দুর্ঘটনার ঝুঁকি তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। একটা ভালো ব্যাপার যে, মেট্রোরেলের নিরাপত্তাব্যবস্থা এমন যে রেললাইনে সামান্যতম বাধা সৃষ্টি হলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেন থেমে যায়। এটি দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য ভালো দিক হলেও, মানবসৃষ্ট কারণে ঘন ঘন এই থমকে যাওয়া আধুনিক এই ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে কর্তৃপক্ষকে সেসব সমস্যা সমাধানের দিকে দৃষ্টি দেওয়া জরুরি।
জনগণ দ্বারা সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে করণীয় নিয়ে এখনই ভাবতে হবে কর্তৃপক্ষকে। তবে প্রযুক্তিগত সমস্যাও যে আছে, তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। কিছুদিন আগে ফার্মগেট এলাকায় বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ে একজনের নিহত হওয়ার ঘটনাটি এই আধুনিক পরিবহনব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা তৈরি করেছে। বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ার ঘটনায় ১১ ঘণ্টা পর্যন্ত ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। যান্ত্রিক ত্রুটি হতেই পারে, তবে গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা সরঞ্জাম বারবার বিকল হওয়া বা খুলে পড়ার ঘটনাটি মেট্রোরেলের কারিগরি তদারকি ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করেছে। এ ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত নজরদারি ও রক্ষণাবেক্ষণে আরও গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক। এক সূত্র থেকে জানা যায়, এই নিহতের ঘটনা এবং অন্যান্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মেট্রোরেলে আগের তুলনায় ১০ শতাংশ যাত্রী কমে গেছে।
যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা মেট্রোরেল চলাচল স্বাভাবিক রাখতে কিছু কার্যকর পদক্ষেপের পরামর্শ দিয়েছেন। যেমন মেট্রোরেলের লাইনে বস্তু শনাক্ত করতে ‘অবজেক্ট ডিটেকশন সেন্সর’ ও ‘এআই-চালিত সিসিটিভি’ স্থাপন করা, ড্রোন পড়া প্রতিরোধে ‘ড্রোন ডিটেকশন রাডার’ ও ‘জিওফেন্সিং সিস্টেম’ ব্যবহার করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া। এ ছাড়া বৈদ্যুতিক লাইনে সুরক্ষা নেট বসালে বাইরে থেকে তার বা বস্তু নিক্ষেপ ঠেকানো সম্ভব।
মেট্রোরেল দেশের সম্পদ। জনগণের মধ্যে সে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এর সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব। ডিএমটিসিএলকে প্রযুক্তিগত ত্রুটিগুলো দ্রুত সমাধান এবং রক্ষণাবেক্ষণে সর্বোচ্চ মান বজায় রাখতে হবে। একই সঙ্গে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে, যাতে মানুষ বুঝতে পারে তাদের সামান্য ভুল বা অসচেতনতা হাজার হাজার যাত্রীর ভোগান্তি এবং মারাত্মক দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। সচেতনতা ও প্রযুক্তিগত সুরক্ষা—এই দুইয়ের সমন্বয়েই কেবল মেট্রোরেলের মসৃণ ও নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করা সম্ভব। এই আধুনিক পরিষেবা যেন মাঝে মাঝে থমকে যাওয়ার দুর্নাম থেকে মুক্তি পায়, সেই প্রত্যাশা আমাদের।

গত সংখ্যায় লিখেছিলাম, এখন আর ছাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না, চারদিকে পরীক্ষার্থী। কিন্তু দ্রুতই দেখা যাচ্ছে, ছাত্র এবং পরীক্ষার্থী কাউকেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ছাত্রদের একটা বৃহদাংশ রাজনীতিবিদে পরিণত হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, তাদের অঙ্গুলি হেলনে বড় বড় রাজনৈতিক সিদ্ধান্তও হয়ে যাচ্ছে। ভেবেছিলাম প্রাথমিক শিক্ষা
১৫ মে ২০২৫
আমরা এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখি, যেখানে নানা ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গের মানুষ পরস্পরের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করবে। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় জারিত হয়ে সমাজের বৈচিত্র্যকে উদ্যাপন করবে। আমরা এমন এক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখি, যে রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের মানবিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখবে।
১ দিন আগে
পথকুকুর বা বিড়াল হত্যা গুরুতর অপরাধ এবং এটি জনস্বাস্থ্য ও পশু সুরক্ষার দিক থেকে একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী, এই ধরনের পশু হত্যা নিষ্ঠুরতা এবং মানবিক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
১ দিন আগে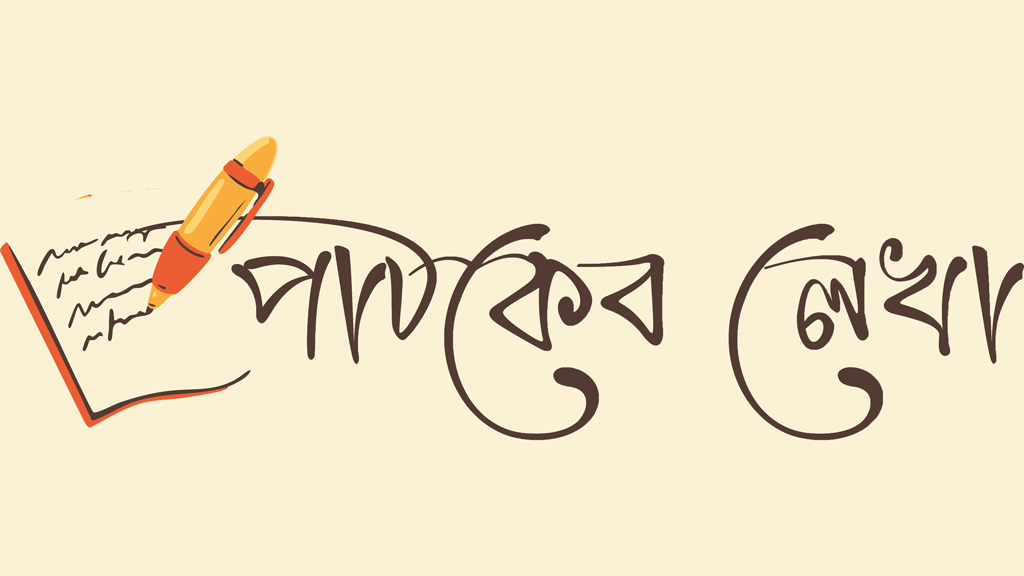
মানুষের জীবন শুধু বেঁচে থাকার নাম নয়; জীবন মানে হচ্ছে পূর্ণতার সন্ধান, মানসিক শান্তি ও শারীরিক সুস্থতার সুষম সমন্বয়। এই সমন্বয় সাধনের দুটি প্রধান উপাদান হলো সংগীত ও শরীরচর্চা। সংগীত আত্মাকে প্রশান্ত করে, মনকে উজ্জীবিত করে; আর শরীরচর্চা দেহকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখে।
১ দিন আগেবিধান রিবেরু

আমরা এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখি, যেখানে নানা ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গের মানুষ পরস্পরের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করবে। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় জারিত হয়ে সমাজের বৈচিত্র্যকে উদ্যাপন করবে। আমরা এমন এক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখি, যে রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের মানবিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখবে। বৈষম্য ও দারিদ্র্যকে মুখে মুখে নয়, প্রকৃত অর্থেই জাদুঘরে পাঠাবে। এমন সমাজ ও রাষ্ট্র পাওয়ার স্বপ্ন আমরা মূর্ত করে তুলেছিলাম ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। কিন্তু গন্ডগোলটা বাধল যখন একটি গোষ্ঠী বা ব্যক্তি নিজের মত ও বিশ্বাসকে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতে শুরু করল এবং চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। এতে করে সমাজে দেখা দিল সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ, রাষ্ট্রে প্রতিভাত হলো স্বৈরতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদ।
একটি সমাজে নানা মত ও পথের মানুষ থাকবে। বিশ্বাসী থাকবে। অবিশ্বাসী থাকবে। সবাইকে নিয়েই সমাজ ও রাষ্ট্র। ভিন্ন ভিন্ন দল ও মতের হয়েও তাহলে কেমন করে মানুষ এক সূত্রে গাঁথা থাকবে? কেমন করে একটি মানচিত্রের ভেতর চিহ্নিত হবে অভিন্নতা? জাতি থেকে জাতীয়তাবোধ, সেখান থেকে আমরা পেলাম জাতিরাষ্ট্র। সাতচল্লিশের আগে ভারতবর্ষে ধর্মকে জাতি ঠাওরে বা সুবিধার জন্য মনে মনে ধরে নিয়ে, দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগ করা হলো। কিন্তু ধর্মভিত্তিক জাতি যে সোনার পাথরবাটি, তা ১৯৭১ সালেই আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি। জাতি গঠনে গণমানুষের সম্মিলিত কল্পনাশক্তির একটা ভূমিকা আছে সত্যি, কিন্তু সেটার সুবিধা নিয়ে কেউ যদি জাতি গঠনের জন্য ধর্মকে ভিত্তি বানায়, তাহলে বলতে হয় কেউ চোরাবালির ওপর প্রাসাদ নির্মাণের স্বপ্ন দেখছে। দুই যুগ পূরণ হওয়ার আগেই তাই স্বপ্নভঙ্গের ঘটনাও ঘটেছে। বাস্তবে আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছি। তখন ভেবেছি এবার অসাম্প্রদায়িক ও সমতার সমাজ গঠন করা সহজ হবে। কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হলো কি?
কেউ বলেন জাতি হলো এক কল্পিত জনগোষ্ঠী। কেউবা বলেন এটি রাষ্ট্র গঠনের জন্য এক সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তি। আমাদের ভেতর একটি সামাজিক অনুভূতি কাজ করে যে, আমরা সবাই একই দেশের নাগরিক। এখানে যদি ফাটল থাকে, তাহলে সে দেশের ললাট থেকে শনির দশা কাটে না। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যতই প্রচার করা হোক না কেন বাঙালি জাতীয়তাবাদ কিংবা বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, কোথায় গিয়ে যেন তৃতীয় আরেকটি মতবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং তারা ১৯৪৭-এর দিকে তাকিয়ে ১৯৭১ সালকে গৌণ করে দিতে চায়। সাতচল্লিশে ধর্মকে জাতি জ্ঞান করে যে বিভাজন হয়েছিল, ১৯৭১ সালে কিন্তু সেই ভ্রম কেটে যায় এবং স্পষ্টতই মানুষ অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ধারণ করে জালিমের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। কিন্তু আজ সেই তৃতীয় পক্ষ ১৯৭১ সালকে অস্বীকার করতে চায়, ১৬ ডিসেম্বরকে বিজয় দিবস হিসেবেও তারা মানতে নারাজ। এমনকি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্য এসব গুরুত্বপূর্ণ তারিখ নিয়েও কেউ কেউ অত্যন্ত আপত্তিজনক মন্তব্য করে ফেলছেন। যেটি রাষ্ট্রদ্রোহের শামিল। তবে কি জাতি হিসেবে নিজেদের ভাবার ক্ষেত্রে পাটাতনে আবার সেই ধর্মভিত্তিক চিন্তাই মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে? নয় তো কেন হঠাৎ আবার এত ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের উত্থান ঘটল? কেনইবা সমাজে ধর্মের প্রতি, ধর্মভিত্তিক রাজনীতির প্রতি এই পক্ষপাত লক্ষ করা যাচ্ছে? বাংলাদেশের সমাজে ইদানীং মানুষ নিজেদের মানব, বিশ্বনাগরিক বা একটি জাতিগোষ্ঠীর পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার বদলে ধর্মপরিচয়কে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে, সর্বাগ্রে স্থান দিচ্ছে। এই পরিবর্তন কেন ঘটল, কেমন করে ঘটল, তার হদিস সমাজবিজ্ঞানীরা ভালো করতে পারবেন। তবে এই পরিবর্তনের দায় কোনোভাবেই রাজনীতিবিদ ও শাসকশ্রেণি এড়াতে পারবে না।
যে মুক্তিযুদ্ধ আমাদের গৌরব করার মতো আত্মপরিচয় দিয়েছে, যে মুক্তিযুদ্ধ আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যে মুক্তিযুদ্ধ প্রমাণ করেছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষ এক সাগর রক্ত ঢালতে পারে অনায়াসে, সেই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আজ অত্যন্ত আপত্তিকর কথা উঠছে। তারা ফিরে যেতে চাইছে সাতচল্লিশে। কী উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ! একটি গোষ্ঠী ও কিছু তথাকথিক কনটেন্ট ক্রিয়েটর নিজেদের বিপুল অনুসারী সহযোগে মুক্তিযুদ্ধসংক্রান্ত যে ভয়ংকর মিথ্যা তথ্য প্রচার এবং চরম অপমানজনক বাক্য ব্যবহার করছে, তাতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় না হয়ে উপায় নেই। যেকোনো সুস্থ মানুষ, যাঁরা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকে সব দল-মত ও পথের ঊর্ধ্বে রেখে, যুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান, ৩০ লাখ শহীদ ও ২ লাখ নারীর সম্ভ্রমের কথা মাথায় রেখে, বাংলাদেশকে নিজেদের অস্তিত্বের অংশ মনে করেন, তাঁদের প্রত্যেকেই আজ বিমর্ষবোধ করছেন। মুক্তিযুদ্ধ যে শোষণহীন ও বৈষম্যমুক্ত সমাজের আকাঙ্ক্ষা থেকে উৎসারিত পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক ও জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে জনযুদ্ধ ছিল, সেটিকে যেন ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। দেখা যাচ্ছে, অনেকে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ও নির্যাতিতদের সংখ্যা নিয়ে কুতর্কের দোকান খুলে বসেছে। ৭ মার্চের ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান ‘জয় বাংলা’র পর ‘জয় পাকিস্তান’ বলেছিলেন কি না, সেটি আবিষ্কার করতে অস্থির হয়ে যাচ্ছে। যেন শেখ মুজিবুর রহমান ‘জয় পাকিস্তান’ বললেই গোটা ৭ মার্চের উত্তাল ভাষণ ও ভাষণ শুনতে আসা লাখো মানুষের মনের ভেতর থাকা স্বাধীনতার জন্য সমুদ্রসমান কল্লোল মিথ্যা হয়ে যায়। যদিও তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে সেদিনের বিশাল জনসভায় সশরীরের উপস্থিত থাকা অনেক বিশিষ্ট মানুষই শোনেননি ‘জয় পাকিস্তান’ বলা হচ্ছে। তাহলে এখন কেন এসব ছোটখাটো কথা নিয়ে এত সময়ক্ষেপণ? এসব করলেই কি এই জনপদের মানুষ যে পাকিস্তানি শাসকদের, বলতে গেলে খালি হাতে যুদ্ধ করে পরাজিত করেছিল, তা লুকিয়ে ফেলা যাবে? কারা এই অপচেষ্টা করছে আজকে? যেহেতু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের কাছে গৌরব ও অর্জনের ইতিহাস, তাই একে প্রশ্নবিদ্ধ করে তর্ক জুড়ে দিলে, মনে করা হচ্ছে মানুষ ওটা নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। আর এই ফাঁকে স্বার্থ উদ্ধার করে নেবে সুযোগসন্ধানীরা।
আরেকটি বিষয় নিয়ে কথা না বললেই নয়, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক কারণেই ভারত ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে গিয়েছিল। এটা ঠিক, তাদের জনতুষ্টিমূলক সংস্কৃতিতে, বিশেষ করে চলচ্চিত্রে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হিসেবে দেখানো হয়, এটা নিয়ে আপত্তি বজায় রেখেই বলতে চাই, সে সময় ভারত পূর্ববঙ্গের লাখ লাখ শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা দিয়ে যে নজির স্থাপন করেছিল, সেটি অস্বীকার করার জো নেই। তাদের আচরণ অনেক সময় বড়ভাইসুলভ ও কিছুটা আপত্তিজনক হলেও, মুক্তিযুদ্ধে তাদের যে সেনাসদস্য মারা গেছেন তা তো আর মিথ্যা নয়। কাজেই যার যেটা প্রাপ্য তাকে সেটা দিতে হয়। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা।
ইদানীং যে প্রবণতা প্রবল আকারে দেখা যাচ্ছে, সেটিকে আমি বলব, মাছির লক্ষণাক্রান্ত। ধরুন শেখ মুজিবুর রহমানের যে ভূমিকা রয়েছে মুক্তিযুদ্ধে, সেটি যেকোনো বিচারেই বাংলাদেশ গঠনের পর বাকশাল গঠনের চেয়ে অনেক বড় ব্যাপার। কিন্তু আজকাল দেখি তাঁর ওই অবদানের কথা উল্লেখ না করে কেবল বাকশাল নিয়ে আলাপ করা হয়। বাকশাল নিয়ে অবশ্যই আলাপ করা জরুরি, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর অবদানকে ছাপিয়ে সেটিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার ভেতর যে ভাষাবলয় পরিলক্ষিত হয়, যে বয়ান প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চোখে পড়ে, সেটি হুবহু বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী, তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক ও তাদের দোসরদের বয়ানের সঙ্গে মিলে যায়। স্বাধীনতালাভের অর্ধশতাব্দী পর এসেও বাংলাদেশ-বিরোধিতা এমনভাবে ফিরে আসার জন্য আমি মনে করি বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে যাঁরা ব্যবসা করেছেন তাঁরাই মূলত দায়ী। তাঁরাই আসলে খাল কেটে কুমির এনেছেন। এখন খাল খননকারীরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পলাতক, কিন্তু জনপদের মানুষ কুমিরের ভয়ে অনিশ্চিত জীবন কাটাচ্ছে।
শুধু এটুকু বলে শেষ করি, গণতন্ত্র মানে শুধু ভোট দেওয়া নয়। ভোট দেওয়ার ভেতর দিয়ে মানুষকে গণিতে পরিণত করা হয়। মাথা গোনার আরেক নাম ভোট। গণতন্ত্র তার চেয়েও বেশি কিছু। ভোট প্রদান জরুরি, কিন্তু তার চেয়েও অধিক জরুরি এই জনপদের মানুষের কাছে গণতন্ত্রের ধারণাকে স্পষ্ট করে তোলা। এটা যত দিন না হচ্ছে, তত দিন আসলে এই খাল কাটা ও কুমিরের খেলা চলতে থাকবে। কারণ, এতে খননকারী ও কুমির উভয়েরই লাভ রয়েছে।

আমরা এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখি, যেখানে নানা ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গের মানুষ পরস্পরের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করবে। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় জারিত হয়ে সমাজের বৈচিত্র্যকে উদ্যাপন করবে। আমরা এমন এক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখি, যে রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের মানবিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখবে। বৈষম্য ও দারিদ্র্যকে মুখে মুখে নয়, প্রকৃত অর্থেই জাদুঘরে পাঠাবে। এমন সমাজ ও রাষ্ট্র পাওয়ার স্বপ্ন আমরা মূর্ত করে তুলেছিলাম ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। কিন্তু গন্ডগোলটা বাধল যখন একটি গোষ্ঠী বা ব্যক্তি নিজের মত ও বিশ্বাসকে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতে শুরু করল এবং চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। এতে করে সমাজে দেখা দিল সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ, রাষ্ট্রে প্রতিভাত হলো স্বৈরতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদ।
একটি সমাজে নানা মত ও পথের মানুষ থাকবে। বিশ্বাসী থাকবে। অবিশ্বাসী থাকবে। সবাইকে নিয়েই সমাজ ও রাষ্ট্র। ভিন্ন ভিন্ন দল ও মতের হয়েও তাহলে কেমন করে মানুষ এক সূত্রে গাঁথা থাকবে? কেমন করে একটি মানচিত্রের ভেতর চিহ্নিত হবে অভিন্নতা? জাতি থেকে জাতীয়তাবোধ, সেখান থেকে আমরা পেলাম জাতিরাষ্ট্র। সাতচল্লিশের আগে ভারতবর্ষে ধর্মকে জাতি ঠাওরে বা সুবিধার জন্য মনে মনে ধরে নিয়ে, দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগ করা হলো। কিন্তু ধর্মভিত্তিক জাতি যে সোনার পাথরবাটি, তা ১৯৭১ সালেই আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি। জাতি গঠনে গণমানুষের সম্মিলিত কল্পনাশক্তির একটা ভূমিকা আছে সত্যি, কিন্তু সেটার সুবিধা নিয়ে কেউ যদি জাতি গঠনের জন্য ধর্মকে ভিত্তি বানায়, তাহলে বলতে হয় কেউ চোরাবালির ওপর প্রাসাদ নির্মাণের স্বপ্ন দেখছে। দুই যুগ পূরণ হওয়ার আগেই তাই স্বপ্নভঙ্গের ঘটনাও ঘটেছে। বাস্তবে আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছি। তখন ভেবেছি এবার অসাম্প্রদায়িক ও সমতার সমাজ গঠন করা সহজ হবে। কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হলো কি?
কেউ বলেন জাতি হলো এক কল্পিত জনগোষ্ঠী। কেউবা বলেন এটি রাষ্ট্র গঠনের জন্য এক সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তি। আমাদের ভেতর একটি সামাজিক অনুভূতি কাজ করে যে, আমরা সবাই একই দেশের নাগরিক। এখানে যদি ফাটল থাকে, তাহলে সে দেশের ললাট থেকে শনির দশা কাটে না। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যতই প্রচার করা হোক না কেন বাঙালি জাতীয়তাবাদ কিংবা বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, কোথায় গিয়ে যেন তৃতীয় আরেকটি মতবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং তারা ১৯৪৭-এর দিকে তাকিয়ে ১৯৭১ সালকে গৌণ করে দিতে চায়। সাতচল্লিশে ধর্মকে জাতি জ্ঞান করে যে বিভাজন হয়েছিল, ১৯৭১ সালে কিন্তু সেই ভ্রম কেটে যায় এবং স্পষ্টতই মানুষ অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ধারণ করে জালিমের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। কিন্তু আজ সেই তৃতীয় পক্ষ ১৯৭১ সালকে অস্বীকার করতে চায়, ১৬ ডিসেম্বরকে বিজয় দিবস হিসেবেও তারা মানতে নারাজ। এমনকি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্য এসব গুরুত্বপূর্ণ তারিখ নিয়েও কেউ কেউ অত্যন্ত আপত্তিজনক মন্তব্য করে ফেলছেন। যেটি রাষ্ট্রদ্রোহের শামিল। তবে কি জাতি হিসেবে নিজেদের ভাবার ক্ষেত্রে পাটাতনে আবার সেই ধর্মভিত্তিক চিন্তাই মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে? নয় তো কেন হঠাৎ আবার এত ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের উত্থান ঘটল? কেনইবা সমাজে ধর্মের প্রতি, ধর্মভিত্তিক রাজনীতির প্রতি এই পক্ষপাত লক্ষ করা যাচ্ছে? বাংলাদেশের সমাজে ইদানীং মানুষ নিজেদের মানব, বিশ্বনাগরিক বা একটি জাতিগোষ্ঠীর পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার বদলে ধর্মপরিচয়কে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে, সর্বাগ্রে স্থান দিচ্ছে। এই পরিবর্তন কেন ঘটল, কেমন করে ঘটল, তার হদিস সমাজবিজ্ঞানীরা ভালো করতে পারবেন। তবে এই পরিবর্তনের দায় কোনোভাবেই রাজনীতিবিদ ও শাসকশ্রেণি এড়াতে পারবে না।
যে মুক্তিযুদ্ধ আমাদের গৌরব করার মতো আত্মপরিচয় দিয়েছে, যে মুক্তিযুদ্ধ আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যে মুক্তিযুদ্ধ প্রমাণ করেছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষ এক সাগর রক্ত ঢালতে পারে অনায়াসে, সেই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আজ অত্যন্ত আপত্তিকর কথা উঠছে। তারা ফিরে যেতে চাইছে সাতচল্লিশে। কী উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ! একটি গোষ্ঠী ও কিছু তথাকথিক কনটেন্ট ক্রিয়েটর নিজেদের বিপুল অনুসারী সহযোগে মুক্তিযুদ্ধসংক্রান্ত যে ভয়ংকর মিথ্যা তথ্য প্রচার এবং চরম অপমানজনক বাক্য ব্যবহার করছে, তাতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় না হয়ে উপায় নেই। যেকোনো সুস্থ মানুষ, যাঁরা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকে সব দল-মত ও পথের ঊর্ধ্বে রেখে, যুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান, ৩০ লাখ শহীদ ও ২ লাখ নারীর সম্ভ্রমের কথা মাথায় রেখে, বাংলাদেশকে নিজেদের অস্তিত্বের অংশ মনে করেন, তাঁদের প্রত্যেকেই আজ বিমর্ষবোধ করছেন। মুক্তিযুদ্ধ যে শোষণহীন ও বৈষম্যমুক্ত সমাজের আকাঙ্ক্ষা থেকে উৎসারিত পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক ও জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে জনযুদ্ধ ছিল, সেটিকে যেন ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। দেখা যাচ্ছে, অনেকে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ও নির্যাতিতদের সংখ্যা নিয়ে কুতর্কের দোকান খুলে বসেছে। ৭ মার্চের ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান ‘জয় বাংলা’র পর ‘জয় পাকিস্তান’ বলেছিলেন কি না, সেটি আবিষ্কার করতে অস্থির হয়ে যাচ্ছে। যেন শেখ মুজিবুর রহমান ‘জয় পাকিস্তান’ বললেই গোটা ৭ মার্চের উত্তাল ভাষণ ও ভাষণ শুনতে আসা লাখো মানুষের মনের ভেতর থাকা স্বাধীনতার জন্য সমুদ্রসমান কল্লোল মিথ্যা হয়ে যায়। যদিও তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে সেদিনের বিশাল জনসভায় সশরীরের উপস্থিত থাকা অনেক বিশিষ্ট মানুষই শোনেননি ‘জয় পাকিস্তান’ বলা হচ্ছে। তাহলে এখন কেন এসব ছোটখাটো কথা নিয়ে এত সময়ক্ষেপণ? এসব করলেই কি এই জনপদের মানুষ যে পাকিস্তানি শাসকদের, বলতে গেলে খালি হাতে যুদ্ধ করে পরাজিত করেছিল, তা লুকিয়ে ফেলা যাবে? কারা এই অপচেষ্টা করছে আজকে? যেহেতু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের কাছে গৌরব ও অর্জনের ইতিহাস, তাই একে প্রশ্নবিদ্ধ করে তর্ক জুড়ে দিলে, মনে করা হচ্ছে মানুষ ওটা নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। আর এই ফাঁকে স্বার্থ উদ্ধার করে নেবে সুযোগসন্ধানীরা।
আরেকটি বিষয় নিয়ে কথা না বললেই নয়, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক কারণেই ভারত ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে গিয়েছিল। এটা ঠিক, তাদের জনতুষ্টিমূলক সংস্কৃতিতে, বিশেষ করে চলচ্চিত্রে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হিসেবে দেখানো হয়, এটা নিয়ে আপত্তি বজায় রেখেই বলতে চাই, সে সময় ভারত পূর্ববঙ্গের লাখ লাখ শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা দিয়ে যে নজির স্থাপন করেছিল, সেটি অস্বীকার করার জো নেই। তাদের আচরণ অনেক সময় বড়ভাইসুলভ ও কিছুটা আপত্তিজনক হলেও, মুক্তিযুদ্ধে তাদের যে সেনাসদস্য মারা গেছেন তা তো আর মিথ্যা নয়। কাজেই যার যেটা প্রাপ্য তাকে সেটা দিতে হয়। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা।
ইদানীং যে প্রবণতা প্রবল আকারে দেখা যাচ্ছে, সেটিকে আমি বলব, মাছির লক্ষণাক্রান্ত। ধরুন শেখ মুজিবুর রহমানের যে ভূমিকা রয়েছে মুক্তিযুদ্ধে, সেটি যেকোনো বিচারেই বাংলাদেশ গঠনের পর বাকশাল গঠনের চেয়ে অনেক বড় ব্যাপার। কিন্তু আজকাল দেখি তাঁর ওই অবদানের কথা উল্লেখ না করে কেবল বাকশাল নিয়ে আলাপ করা হয়। বাকশাল নিয়ে অবশ্যই আলাপ করা জরুরি, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর অবদানকে ছাপিয়ে সেটিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার ভেতর যে ভাষাবলয় পরিলক্ষিত হয়, যে বয়ান প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চোখে পড়ে, সেটি হুবহু বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী, তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক ও তাদের দোসরদের বয়ানের সঙ্গে মিলে যায়। স্বাধীনতালাভের অর্ধশতাব্দী পর এসেও বাংলাদেশ-বিরোধিতা এমনভাবে ফিরে আসার জন্য আমি মনে করি বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে যাঁরা ব্যবসা করেছেন তাঁরাই মূলত দায়ী। তাঁরাই আসলে খাল কেটে কুমির এনেছেন। এখন খাল খননকারীরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পলাতক, কিন্তু জনপদের মানুষ কুমিরের ভয়ে অনিশ্চিত জীবন কাটাচ্ছে।
শুধু এটুকু বলে শেষ করি, গণতন্ত্র মানে শুধু ভোট দেওয়া নয়। ভোট দেওয়ার ভেতর দিয়ে মানুষকে গণিতে পরিণত করা হয়। মাথা গোনার আরেক নাম ভোট। গণতন্ত্র তার চেয়েও বেশি কিছু। ভোট প্রদান জরুরি, কিন্তু তার চেয়েও অধিক জরুরি এই জনপদের মানুষের কাছে গণতন্ত্রের ধারণাকে স্পষ্ট করে তোলা। এটা যত দিন না হচ্ছে, তত দিন আসলে এই খাল কাটা ও কুমিরের খেলা চলতে থাকবে। কারণ, এতে খননকারী ও কুমির উভয়েরই লাভ রয়েছে।

গত সংখ্যায় লিখেছিলাম, এখন আর ছাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না, চারদিকে পরীক্ষার্থী। কিন্তু দ্রুতই দেখা যাচ্ছে, ছাত্র এবং পরীক্ষার্থী কাউকেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ছাত্রদের একটা বৃহদাংশ রাজনীতিবিদে পরিণত হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, তাদের অঙ্গুলি হেলনে বড় বড় রাজনৈতিক সিদ্ধান্তও হয়ে যাচ্ছে। ভেবেছিলাম প্রাথমিক শিক্ষা
১৫ মে ২০২৫
ঢাকা শহরের যানজটের সমস্যা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি দিয়েছে মেট্রোরেল। তবে এটা চালুর প্রায় দেড় বছরে এই আধুনিক গণপরিবহনব্যবস্থা মাঝে মাঝে বন্ধ হয়েছে। সেটা একটা ভাবনার বিষয়। মূলত এই সময়ের মধ্যে অন্তত ১০ বার মেট্রোরেল চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়েছে, যার বেশির ভাগই জনগণের গাফিলতির কারণে হয়েছে।
১ দিন আগে
পথকুকুর বা বিড়াল হত্যা গুরুতর অপরাধ এবং এটি জনস্বাস্থ্য ও পশু সুরক্ষার দিক থেকে একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী, এই ধরনের পশু হত্যা নিষ্ঠুরতা এবং মানবিক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
১ দিন আগে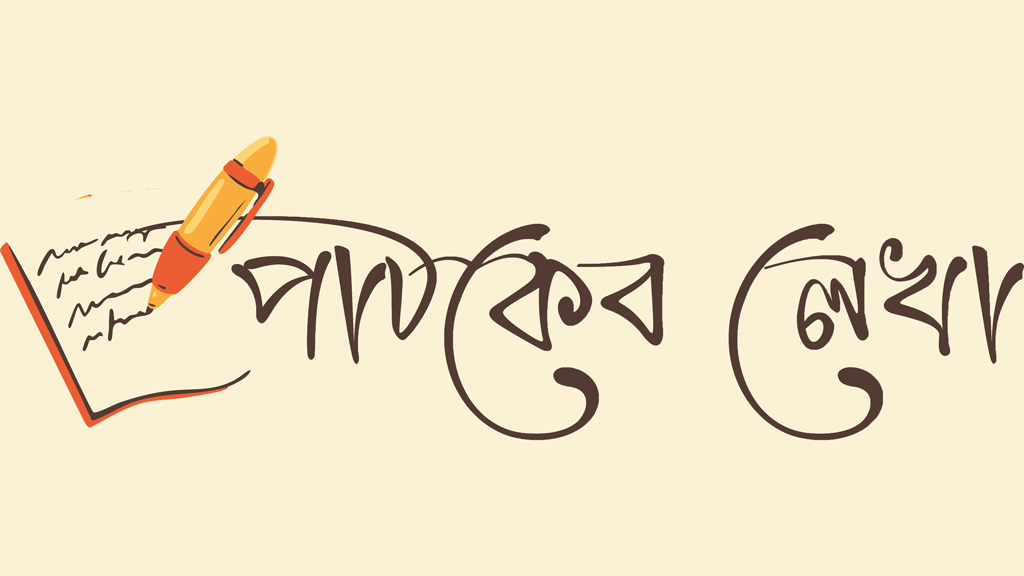
মানুষের জীবন শুধু বেঁচে থাকার নাম নয়; জীবন মানে হচ্ছে পূর্ণতার সন্ধান, মানসিক শান্তি ও শারীরিক সুস্থতার সুষম সমন্বয়। এই সমন্বয় সাধনের দুটি প্রধান উপাদান হলো সংগীত ও শরীরচর্চা। সংগীত আত্মাকে প্রশান্ত করে, মনকে উজ্জীবিত করে; আর শরীরচর্চা দেহকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখে।
১ দিন আগেঅ্যাডভোকেট সাহিদা আক্তার

পথকুকুর বা বিড়াল হত্যা গুরুতর অপরাধ এবং এটি জনস্বাস্থ্য ও পশু সুরক্ষার দিক থেকে একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী, এই ধরনের পশু হত্যা নিষ্ঠুরতা এবং মানবিক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
বাংলাদেশের আইনে পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা বা অমানবিক আচরণ রোধ করার জন্য বিশেষ বিধান রয়েছে। ১৯২০ সালে প্রণীত ‘পশু সুরক্ষা আইন’-এর মাধ্যমে পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা বা অমানবিক আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই আইনে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি জেনেবুঝে বা অবহেলায় কোনো প্রাণীকে আঘাত করে বা হত্যা করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে মামলা হতে পারে এবং শাস্তি হতে পারে।
২০১০ সালে বাংলাদেশ সরকার ‘পশু সুরক্ষা আইন সংশোধনী ২০১০’ প্রণয়ন করে, যাতে পশু হত্যা বা তাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের জন্য আরও কঠোর শাস্তি নির্ধারণ করা হয়।
পথকুকুর বা বিড়াল হত্যা হলে সাধারণত অভিযোগ দায়েরের দায়িত্ব স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন বা স্থানীয় পরিষদের ওপর পড়ে। তবে, এটি শুধু পুলিশের কাজ নয়; যেকোনো নাগরিক, পশু অধিকার রক্ষা সংস্থা বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনও এই ধরনের ঘটনার বিষয়ে মামলা করতে পারে।
যেকোনো হত্যা বা পশু নির্যাতনের ঘটনা প্রমাণ করতে হলে, পুলিশ বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রাথমিক তদন্ত করতে হবে।
স্থানীয় মানুষ বা প্রত্যক্ষদর্শীরা যদি এই হত্যার সাক্ষী হন, তাঁরা এই বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। এ ছাড়া প্রাণী অধিকার রক্ষা সংগঠনগুলোরও সক্রিয় ভূমিকা থাকে এবং তারা এগুলোর বিরুদ্ধে মামলা করতে সাহায্য করে।
পথকুকুর বা বিড়াল হত্যা করার শাস্তি বাংলাদেশে নির্দিষ্ট। ‘পশু সুরক্ষা আইন’ অনুযায়ী, যদি কোনো ব্যক্তি জেনেবুঝে বা অমানবিকভাবে কোনো প্রাণীকে আঘাত করে বা হত্যা করে, তাহলে তাকে শাস্তি প্রদান করা হয়।
জরিমানা: পশু হত্যার অপরাধে একজন ব্যক্তির ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। তবে, এটি সাধারণত প্রাথমিক শাস্তি হিসেবে নির্ধারিত হয়।
কারাদণ্ড: কিছু ক্ষেত্রে, বিশেষত যদি হত্যাটি অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে সংঘটিত হয়, তাহলে শাস্তি হিসেবে এক মাসের কারাদণ্ড হতে পারে। এই শাস্তি সংশ্লিষ্ট আদালত নির্ধারণ করবেন।
অবহেলাজনিত হত্যা: যদি কেউ অবহেলাজনিত কোনো প্রাণীকে হত্যা করে, যেমন সড়ক দুর্ঘটনার কারণে বা কোনো অজ্ঞাত কারণে, তখনো শাস্তি আরোপ করা হতে পারে। তবে, যদি হত্যা প্রমাণিত না হয়, শাস্তি কিছুটা কম হতে পারে।
বিষ প্রয়োগ: যদি কেউ প্রাণীকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করে, তাহলে শাস্তি আরও কঠোর হতে পারে। বিষ প্রয়োগ বা নিষিদ্ধ কোনো উপাদান দিয়ে প্রাণী হত্যার জন্য তিন বছরের কারাদণ্ডও হতে পারে এবং জরিমানাও আদায় করা হতে পারে।
বাংলাদেশে যদিও আইন রয়েছে, তবে পথকুকুর বা বিড়াল হত্যা সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা থাকে।
প্রমাণের অভাব: অনেক সময় পথকুকুর বা বিড়াল হত্যা প্রমাণ করা কঠিন হয়, কারণ এই ধরনের ঘটনা সাধারণত অপরিচিত জায়গায় ঘটে এবং প্রমাণ সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।
আবেগগত দ্বন্দ্ব: অনেক মানুষের কাছে পথকুকুর বা বিড়াল হত্যার গুরুত্ব তেমন অনুভূত হয় না, কারণ তারা মনে করে এসব প্রাণী কেবল ‘যাযাবর’ এবং তাদের কোনো বিশেষ মূল্য নেই। কিন্তু, এটি একটি ভুল ধারণা এবং এ ধরনের চিন্তা সমাজে পশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতার পথ প্রশস্ত করে।
আইন প্রয়োগের দুর্বলতা: অনেক সময় পুলিশের মনোযোগ এবং কার্যকর তদন্তের অভাবের কারণে এই ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয় না। পথকুকুর বা বিড়াল হত্যা বন্ধ করতে এবং তাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা কমাতে কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন:
সচেতনতা বৃদ্ধি: মানুষের মধ্যে পশুর প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা তৈরি করতে হবে। জনগণকে জানাতে হবে যে পশু হত্যা শুধু একটি অপরাধ নয়, বরং এটি মানবিকতারও প্রশ্ন।
আইনের প্রয়োগ আরও কঠোর করা: আইন প্রয়োগে গাফিলতি দূর করতে পুলিশের প্রশিক্ষণ এবং মনোযোগ বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে এই ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া যায়।
প্রাণী অধিকার রক্ষা সংগঠনের সহায়তা: প্রাণী অধিকার রক্ষা সংস্থাগুলোর তদারকি এবং কাজকে আরও সক্রিয় ও জনপ্রিয় করতে হবে।
সাহিদা আক্তার, আইনজীবী, জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ঢাকা

পথকুকুর বা বিড়াল হত্যা গুরুতর অপরাধ এবং এটি জনস্বাস্থ্য ও পশু সুরক্ষার দিক থেকে একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী, এই ধরনের পশু হত্যা নিষ্ঠুরতা এবং মানবিক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
বাংলাদেশের আইনে পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা বা অমানবিক আচরণ রোধ করার জন্য বিশেষ বিধান রয়েছে। ১৯২০ সালে প্রণীত ‘পশু সুরক্ষা আইন’-এর মাধ্যমে পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা বা অমানবিক আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই আইনে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি জেনেবুঝে বা অবহেলায় কোনো প্রাণীকে আঘাত করে বা হত্যা করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে মামলা হতে পারে এবং শাস্তি হতে পারে।
২০১০ সালে বাংলাদেশ সরকার ‘পশু সুরক্ষা আইন সংশোধনী ২০১০’ প্রণয়ন করে, যাতে পশু হত্যা বা তাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের জন্য আরও কঠোর শাস্তি নির্ধারণ করা হয়।
পথকুকুর বা বিড়াল হত্যা হলে সাধারণত অভিযোগ দায়েরের দায়িত্ব স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন বা স্থানীয় পরিষদের ওপর পড়ে। তবে, এটি শুধু পুলিশের কাজ নয়; যেকোনো নাগরিক, পশু অধিকার রক্ষা সংস্থা বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনও এই ধরনের ঘটনার বিষয়ে মামলা করতে পারে।
যেকোনো হত্যা বা পশু নির্যাতনের ঘটনা প্রমাণ করতে হলে, পুলিশ বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রাথমিক তদন্ত করতে হবে।
স্থানীয় মানুষ বা প্রত্যক্ষদর্শীরা যদি এই হত্যার সাক্ষী হন, তাঁরা এই বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। এ ছাড়া প্রাণী অধিকার রক্ষা সংগঠনগুলোরও সক্রিয় ভূমিকা থাকে এবং তারা এগুলোর বিরুদ্ধে মামলা করতে সাহায্য করে।
পথকুকুর বা বিড়াল হত্যা করার শাস্তি বাংলাদেশে নির্দিষ্ট। ‘পশু সুরক্ষা আইন’ অনুযায়ী, যদি কোনো ব্যক্তি জেনেবুঝে বা অমানবিকভাবে কোনো প্রাণীকে আঘাত করে বা হত্যা করে, তাহলে তাকে শাস্তি প্রদান করা হয়।
জরিমানা: পশু হত্যার অপরাধে একজন ব্যক্তির ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। তবে, এটি সাধারণত প্রাথমিক শাস্তি হিসেবে নির্ধারিত হয়।
কারাদণ্ড: কিছু ক্ষেত্রে, বিশেষত যদি হত্যাটি অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে সংঘটিত হয়, তাহলে শাস্তি হিসেবে এক মাসের কারাদণ্ড হতে পারে। এই শাস্তি সংশ্লিষ্ট আদালত নির্ধারণ করবেন।
অবহেলাজনিত হত্যা: যদি কেউ অবহেলাজনিত কোনো প্রাণীকে হত্যা করে, যেমন সড়ক দুর্ঘটনার কারণে বা কোনো অজ্ঞাত কারণে, তখনো শাস্তি আরোপ করা হতে পারে। তবে, যদি হত্যা প্রমাণিত না হয়, শাস্তি কিছুটা কম হতে পারে।
বিষ প্রয়োগ: যদি কেউ প্রাণীকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করে, তাহলে শাস্তি আরও কঠোর হতে পারে। বিষ প্রয়োগ বা নিষিদ্ধ কোনো উপাদান দিয়ে প্রাণী হত্যার জন্য তিন বছরের কারাদণ্ডও হতে পারে এবং জরিমানাও আদায় করা হতে পারে।
বাংলাদেশে যদিও আইন রয়েছে, তবে পথকুকুর বা বিড়াল হত্যা সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা থাকে।
প্রমাণের অভাব: অনেক সময় পথকুকুর বা বিড়াল হত্যা প্রমাণ করা কঠিন হয়, কারণ এই ধরনের ঘটনা সাধারণত অপরিচিত জায়গায় ঘটে এবং প্রমাণ সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।
আবেগগত দ্বন্দ্ব: অনেক মানুষের কাছে পথকুকুর বা বিড়াল হত্যার গুরুত্ব তেমন অনুভূত হয় না, কারণ তারা মনে করে এসব প্রাণী কেবল ‘যাযাবর’ এবং তাদের কোনো বিশেষ মূল্য নেই। কিন্তু, এটি একটি ভুল ধারণা এবং এ ধরনের চিন্তা সমাজে পশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতার পথ প্রশস্ত করে।
আইন প্রয়োগের দুর্বলতা: অনেক সময় পুলিশের মনোযোগ এবং কার্যকর তদন্তের অভাবের কারণে এই ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয় না। পথকুকুর বা বিড়াল হত্যা বন্ধ করতে এবং তাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা কমাতে কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন:
সচেতনতা বৃদ্ধি: মানুষের মধ্যে পশুর প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা তৈরি করতে হবে। জনগণকে জানাতে হবে যে পশু হত্যা শুধু একটি অপরাধ নয়, বরং এটি মানবিকতারও প্রশ্ন।
আইনের প্রয়োগ আরও কঠোর করা: আইন প্রয়োগে গাফিলতি দূর করতে পুলিশের প্রশিক্ষণ এবং মনোযোগ বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে এই ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া যায়।
প্রাণী অধিকার রক্ষা সংগঠনের সহায়তা: প্রাণী অধিকার রক্ষা সংস্থাগুলোর তদারকি এবং কাজকে আরও সক্রিয় ও জনপ্রিয় করতে হবে।
সাহিদা আক্তার, আইনজীবী, জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ঢাকা

গত সংখ্যায় লিখেছিলাম, এখন আর ছাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না, চারদিকে পরীক্ষার্থী। কিন্তু দ্রুতই দেখা যাচ্ছে, ছাত্র এবং পরীক্ষার্থী কাউকেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ছাত্রদের একটা বৃহদাংশ রাজনীতিবিদে পরিণত হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, তাদের অঙ্গুলি হেলনে বড় বড় রাজনৈতিক সিদ্ধান্তও হয়ে যাচ্ছে। ভেবেছিলাম প্রাথমিক শিক্ষা
১৫ মে ২০২৫
ঢাকা শহরের যানজটের সমস্যা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি দিয়েছে মেট্রোরেল। তবে এটা চালুর প্রায় দেড় বছরে এই আধুনিক গণপরিবহনব্যবস্থা মাঝে মাঝে বন্ধ হয়েছে। সেটা একটা ভাবনার বিষয়। মূলত এই সময়ের মধ্যে অন্তত ১০ বার মেট্রোরেল চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়েছে, যার বেশির ভাগই জনগণের গাফিলতির কারণে হয়েছে।
১ দিন আগে
আমরা এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখি, যেখানে নানা ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গের মানুষ পরস্পরের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করবে। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় জারিত হয়ে সমাজের বৈচিত্র্যকে উদ্যাপন করবে। আমরা এমন এক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখি, যে রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের মানবিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখবে।
১ দিন আগে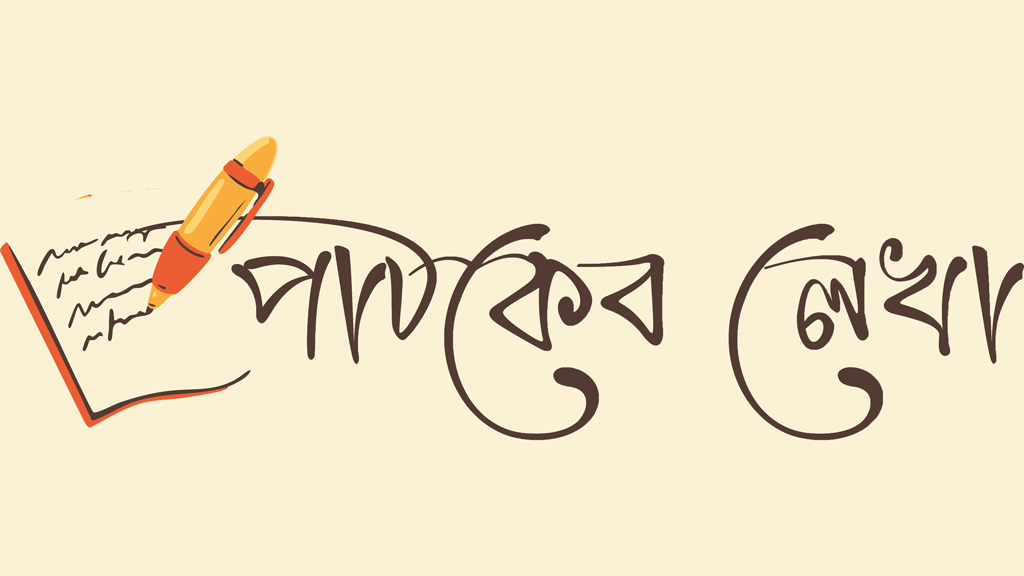
মানুষের জীবন শুধু বেঁচে থাকার নাম নয়; জীবন মানে হচ্ছে পূর্ণতার সন্ধান, মানসিক শান্তি ও শারীরিক সুস্থতার সুষম সমন্বয়। এই সমন্বয় সাধনের দুটি প্রধান উপাদান হলো সংগীত ও শরীরচর্চা। সংগীত আত্মাকে প্রশান্ত করে, মনকে উজ্জীবিত করে; আর শরীরচর্চা দেহকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখে।
১ দিন আগেসুধীর বরণ মাঝি
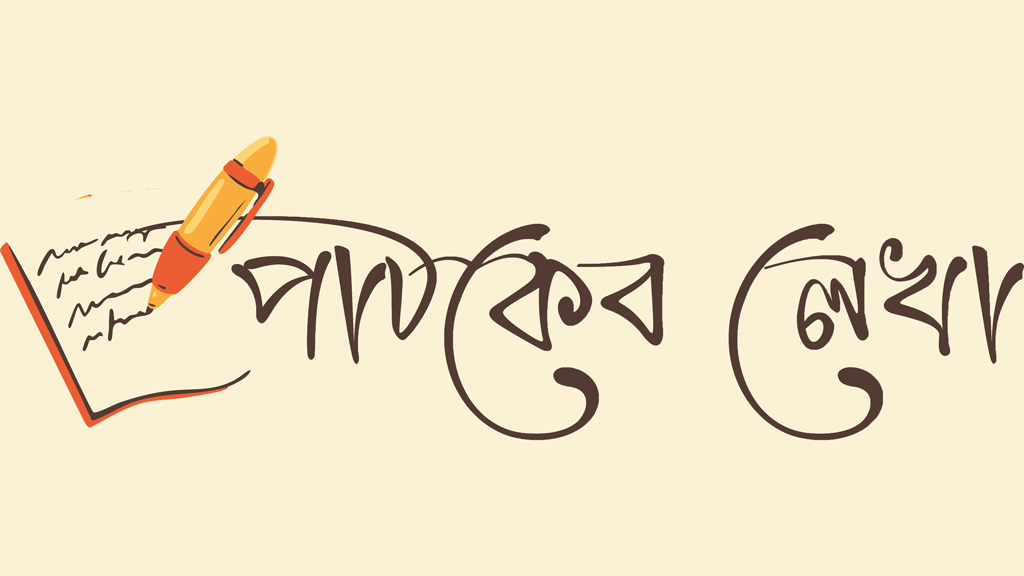
মানুষের জীবন শুধু বেঁচে থাকার নাম নয়; জীবন মানে হচ্ছে পূর্ণতার সন্ধান, মানসিক শান্তি ও শারীরিক সুস্থতার সুষম সমন্বয়। এই সমন্বয় সাধনের দুটি প্রধান উপাদান হলো সংগীত ও শরীরচর্চা। সংগীত আত্মাকে প্রশান্ত করে, মনকে উজ্জীবিত করে; আর শরীরচর্চা দেহকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখে। এই দুইয়ের মিলিত প্রভাবেই গড়ে ওঠে এক পরিপূর্ণ, ভারসাম্যপূর্ণ ও অর্থবহ জীবন। যে সমাজে মানুষ সংগীতের মাধুর্য ও শরীরচর্চার শৃঙ্খলাকে গ্রহণ করে, সে সমাজ হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত, সৃজনশীল ও মানবিক গুণে পরিপূর্ণ।
সংগীত মানুষের হৃদয়ের ভাষা। ভাষা যখন থেমে যায়, তখন সুরই হয়ে ওঠে প্রকাশের মাধ্যম। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ তার অনুভূতি, আনন্দ, দুঃখ, প্রেম, প্রার্থনা কিংবা প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে সংগীতকে বেছে নিয়েছে। প্রকৃতির শব্দের ভেতরেও সংগীতের ছোঁয়া—বৃষ্টির ঝরঝর শব্দ, পাখির কলতান, ঢেউয়ের মৃদু গর্জন—সবই জীবনের ছন্দের বহিঃপ্রকাশ। এই ছন্দ থেকেই মানুষ খুঁজে পেয়েছে সংগীতের রূপ, যা তাকে দিয়েছে মানসিক মুক্তি, সৃষ্টিশীলতার প্রেরণা ও আত্মার প্রশান্তি। আজও যখন কোনো মানুষ ক্লান্ত, উদ্বিগ্ন বা নিঃসঙ্গ হয়, তখন সংগীতই তার একমাত্র সান্ত্বনা হয়ে ওঠে।
মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখা যায়, সংগীত মানুষের মানসিক ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সংগীত থেরাপি আজ বিশ্বজুড়ে একটি স্বীকৃত চিকিৎসা পদ্ধতি। মানসিক অবসাদ, হতাশা বা উদ্বেগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা যখন সংগীতের ছন্দে নিজেকে মেলে ধরতে পারে, তখন তাদের মস্তিষ্কে ডোপামিন ও সেরোটোনিনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, যা মানসিক প্রশান্তি এনে দেয়। তাই সংগীত শুধু বিনোদন নয়, এটি এক গভীর মানসিক ও আত্মিক চিকিৎসা। শিশুরা যখন ছোটবেলা থেকেই সংগীতচর্চায় যুক্ত হয়, তখন তাদের মনোযোগ, স্মৃতিশক্তি, শৃঙ্খলা ও আবেগময় সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ সংগীত শুধু মনোরঞ্জন নয়, এটি চরিত্র গঠনেরও সহায়কশক্তি।
অন্যদিকে, শরীরচর্চা মানুষের শারীরিক ও মানসিক উভয় বিকাশের অন্যতম প্রধান অনুঘটক। একটি লাতিন প্রবাদ হলো, ‘সুস্থ দেহে সুস্থ মন’। শারীরিক সুস্থতা ছাড়া মানসিক উৎকর্ষ সম্ভব নয়। নিয়মিত শরীরচর্চা হৃদ্যন্ত্রকে শক্তিশালী করে, রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়, শরীরে অক্সিজেনের প্রবাহ উন্নত করে এবং বিভিন্ন রোগপ্রতিরোধে সহায়তা করে। কিন্তু এর থেকেও বড় কথা হলো, শরীরচর্চা মানুষকে দেয় আত্মনিয়ন্ত্রণ, অধ্যবসায়, সাহস ও ইতিবাচক মনোভাব। প্রতিদিনের শরীরচর্চা যেন জীবনের এক ধ্রুব অনুশাসন, যা আমাদের শেখায় পরিশ্রম, ধৈর্য ও শৃঙ্খলার মূল্য।
আজকের যুগে যখন প্রযুক্তিনির্ভর জীবন মানুষকে ক্রমেই নিস্তেজ ও স্থবির করে তুলছে, তখন শরীরচর্চা আমাদের জাগ্রত রাখে। অফিস, স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়—সব জায়গায় এখন বসে থাকার প্রবণতা বেড়েছে। ফলে স্থূলতা, ডায়াবেটিস, হৃদ্রোগ, বিষণ্নতা ইত্যাদি নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠছে। নিয়মিত ব্যায়াম, হাঁটা, দৌড়ানো, সাঁতার বা যোগব্যায়াম কেবল শরীরকে সুস্থ রাখে না, মানসিক চাপও কমায়।
সংগীত ও শরীরচর্চার মধ্যে এক গভীর সম্পর্কও রয়েছে। যেমন যোগব্যায়াম বা ধ্যানের সময় সুমধুর সংগীত মনকে কেন্দ্রীভূত করতে সাহায্য করে। আবার অনেক ব্যায়াম বা ক্রীড়া কার্যক্রমে ছন্দময় সংগীত শরীরকে উদ্দীপিত করে তোলে। জিমে ব্যায়াম করার সময় বা দৌড়ানোর সময় অনুপ্রেরণাদায়ক গান শুনলে শরীরে নতুন শক্তির সঞ্চার হয়।
শিক্ষার ক্ষেত্রেও সংগীত ও শরীরচর্চার ভূমিকা অপরিসীম। আধুনিক শিক্ষা শুধু বইয়ের জ্ঞান নয়; এটি দেহ, মন ও বুদ্ধির সমন্বিত বিকাশ চায়। তাই বিদ্যালয়ে সংগীত শিক্ষা ও শারীরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। সংগীত শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তি ও নান্দনিক বোধকে জাগিয়ে তোলে, আর শরীরচর্চা তাকে করে তোলে সুস্থ, পরিশ্রমী ও আত্মনিয়ন্ত্রিত। আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতিতেও এই দুই বিষয়কে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কারণ এ দুটি ছাড়া পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব গঠন অসম্ভব।
সংগীত ও শরীরচর্চা জীবনের দুটি অনিবার্য স্তম্ভ। একদিকে সংগীত আত্মাকে দেয় শান্তি, অন্যদিকে শরীরচর্চা দেহে আনে শক্তি। এই দুইয়ের সমন্বয়ই আমাদের দেয় জীবনকে উপভোগ করার সক্ষমতা। যে ব্যক্তি সংগীতের সৌন্দর্য বোঝে ও নিয়মিত শরীরচর্চা করে, সে শুধু দীর্ঘজীবীই নয়, প্রকৃত অর্থে সুখী মানুষ। জীবন তখন আর নিছক বেঁচে থাকা নয়; বরং এক সুরেলা, উদ্দীপনাময়, অর্থবহ যাত্রা। তাই বলা যায়, সংগীত ও শরীরচর্চা ছাড়া জীবন বোধহীন, প্রাণহীন এক জড় অস্তিত্বমাত্র।
শিক্ষক, হাইমচর সরকারি মহাবিদ্যালয়, চাঁদপুর
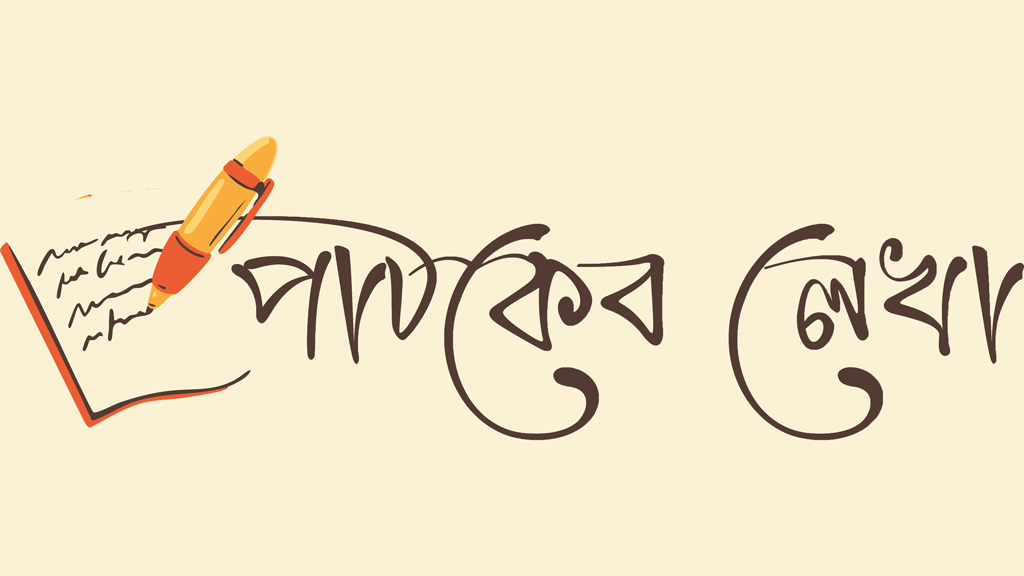
মানুষের জীবন শুধু বেঁচে থাকার নাম নয়; জীবন মানে হচ্ছে পূর্ণতার সন্ধান, মানসিক শান্তি ও শারীরিক সুস্থতার সুষম সমন্বয়। এই সমন্বয় সাধনের দুটি প্রধান উপাদান হলো সংগীত ও শরীরচর্চা। সংগীত আত্মাকে প্রশান্ত করে, মনকে উজ্জীবিত করে; আর শরীরচর্চা দেহকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখে। এই দুইয়ের মিলিত প্রভাবেই গড়ে ওঠে এক পরিপূর্ণ, ভারসাম্যপূর্ণ ও অর্থবহ জীবন। যে সমাজে মানুষ সংগীতের মাধুর্য ও শরীরচর্চার শৃঙ্খলাকে গ্রহণ করে, সে সমাজ হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত, সৃজনশীল ও মানবিক গুণে পরিপূর্ণ।
সংগীত মানুষের হৃদয়ের ভাষা। ভাষা যখন থেমে যায়, তখন সুরই হয়ে ওঠে প্রকাশের মাধ্যম। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ তার অনুভূতি, আনন্দ, দুঃখ, প্রেম, প্রার্থনা কিংবা প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে সংগীতকে বেছে নিয়েছে। প্রকৃতির শব্দের ভেতরেও সংগীতের ছোঁয়া—বৃষ্টির ঝরঝর শব্দ, পাখির কলতান, ঢেউয়ের মৃদু গর্জন—সবই জীবনের ছন্দের বহিঃপ্রকাশ। এই ছন্দ থেকেই মানুষ খুঁজে পেয়েছে সংগীতের রূপ, যা তাকে দিয়েছে মানসিক মুক্তি, সৃষ্টিশীলতার প্রেরণা ও আত্মার প্রশান্তি। আজও যখন কোনো মানুষ ক্লান্ত, উদ্বিগ্ন বা নিঃসঙ্গ হয়, তখন সংগীতই তার একমাত্র সান্ত্বনা হয়ে ওঠে।
মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখা যায়, সংগীত মানুষের মানসিক ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সংগীত থেরাপি আজ বিশ্বজুড়ে একটি স্বীকৃত চিকিৎসা পদ্ধতি। মানসিক অবসাদ, হতাশা বা উদ্বেগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা যখন সংগীতের ছন্দে নিজেকে মেলে ধরতে পারে, তখন তাদের মস্তিষ্কে ডোপামিন ও সেরোটোনিনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, যা মানসিক প্রশান্তি এনে দেয়। তাই সংগীত শুধু বিনোদন নয়, এটি এক গভীর মানসিক ও আত্মিক চিকিৎসা। শিশুরা যখন ছোটবেলা থেকেই সংগীতচর্চায় যুক্ত হয়, তখন তাদের মনোযোগ, স্মৃতিশক্তি, শৃঙ্খলা ও আবেগময় সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ সংগীত শুধু মনোরঞ্জন নয়, এটি চরিত্র গঠনেরও সহায়কশক্তি।
অন্যদিকে, শরীরচর্চা মানুষের শারীরিক ও মানসিক উভয় বিকাশের অন্যতম প্রধান অনুঘটক। একটি লাতিন প্রবাদ হলো, ‘সুস্থ দেহে সুস্থ মন’। শারীরিক সুস্থতা ছাড়া মানসিক উৎকর্ষ সম্ভব নয়। নিয়মিত শরীরচর্চা হৃদ্যন্ত্রকে শক্তিশালী করে, রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়, শরীরে অক্সিজেনের প্রবাহ উন্নত করে এবং বিভিন্ন রোগপ্রতিরোধে সহায়তা করে। কিন্তু এর থেকেও বড় কথা হলো, শরীরচর্চা মানুষকে দেয় আত্মনিয়ন্ত্রণ, অধ্যবসায়, সাহস ও ইতিবাচক মনোভাব। প্রতিদিনের শরীরচর্চা যেন জীবনের এক ধ্রুব অনুশাসন, যা আমাদের শেখায় পরিশ্রম, ধৈর্য ও শৃঙ্খলার মূল্য।
আজকের যুগে যখন প্রযুক্তিনির্ভর জীবন মানুষকে ক্রমেই নিস্তেজ ও স্থবির করে তুলছে, তখন শরীরচর্চা আমাদের জাগ্রত রাখে। অফিস, স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়—সব জায়গায় এখন বসে থাকার প্রবণতা বেড়েছে। ফলে স্থূলতা, ডায়াবেটিস, হৃদ্রোগ, বিষণ্নতা ইত্যাদি নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠছে। নিয়মিত ব্যায়াম, হাঁটা, দৌড়ানো, সাঁতার বা যোগব্যায়াম কেবল শরীরকে সুস্থ রাখে না, মানসিক চাপও কমায়।
সংগীত ও শরীরচর্চার মধ্যে এক গভীর সম্পর্কও রয়েছে। যেমন যোগব্যায়াম বা ধ্যানের সময় সুমধুর সংগীত মনকে কেন্দ্রীভূত করতে সাহায্য করে। আবার অনেক ব্যায়াম বা ক্রীড়া কার্যক্রমে ছন্দময় সংগীত শরীরকে উদ্দীপিত করে তোলে। জিমে ব্যায়াম করার সময় বা দৌড়ানোর সময় অনুপ্রেরণাদায়ক গান শুনলে শরীরে নতুন শক্তির সঞ্চার হয়।
শিক্ষার ক্ষেত্রেও সংগীত ও শরীরচর্চার ভূমিকা অপরিসীম। আধুনিক শিক্ষা শুধু বইয়ের জ্ঞান নয়; এটি দেহ, মন ও বুদ্ধির সমন্বিত বিকাশ চায়। তাই বিদ্যালয়ে সংগীত শিক্ষা ও শারীরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। সংগীত শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তি ও নান্দনিক বোধকে জাগিয়ে তোলে, আর শরীরচর্চা তাকে করে তোলে সুস্থ, পরিশ্রমী ও আত্মনিয়ন্ত্রিত। আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতিতেও এই দুই বিষয়কে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কারণ এ দুটি ছাড়া পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব গঠন অসম্ভব।
সংগীত ও শরীরচর্চা জীবনের দুটি অনিবার্য স্তম্ভ। একদিকে সংগীত আত্মাকে দেয় শান্তি, অন্যদিকে শরীরচর্চা দেহে আনে শক্তি। এই দুইয়ের সমন্বয়ই আমাদের দেয় জীবনকে উপভোগ করার সক্ষমতা। যে ব্যক্তি সংগীতের সৌন্দর্য বোঝে ও নিয়মিত শরীরচর্চা করে, সে শুধু দীর্ঘজীবীই নয়, প্রকৃত অর্থে সুখী মানুষ। জীবন তখন আর নিছক বেঁচে থাকা নয়; বরং এক সুরেলা, উদ্দীপনাময়, অর্থবহ যাত্রা। তাই বলা যায়, সংগীত ও শরীরচর্চা ছাড়া জীবন বোধহীন, প্রাণহীন এক জড় অস্তিত্বমাত্র।
শিক্ষক, হাইমচর সরকারি মহাবিদ্যালয়, চাঁদপুর

গত সংখ্যায় লিখেছিলাম, এখন আর ছাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না, চারদিকে পরীক্ষার্থী। কিন্তু দ্রুতই দেখা যাচ্ছে, ছাত্র এবং পরীক্ষার্থী কাউকেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ছাত্রদের একটা বৃহদাংশ রাজনীতিবিদে পরিণত হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, তাদের অঙ্গুলি হেলনে বড় বড় রাজনৈতিক সিদ্ধান্তও হয়ে যাচ্ছে। ভেবেছিলাম প্রাথমিক শিক্ষা
১৫ মে ২০২৫
ঢাকা শহরের যানজটের সমস্যা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি দিয়েছে মেট্রোরেল। তবে এটা চালুর প্রায় দেড় বছরে এই আধুনিক গণপরিবহনব্যবস্থা মাঝে মাঝে বন্ধ হয়েছে। সেটা একটা ভাবনার বিষয়। মূলত এই সময়ের মধ্যে অন্তত ১০ বার মেট্রোরেল চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়েছে, যার বেশির ভাগই জনগণের গাফিলতির কারণে হয়েছে।
১ দিন আগে
আমরা এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখি, যেখানে নানা ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গের মানুষ পরস্পরের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করবে। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় জারিত হয়ে সমাজের বৈচিত্র্যকে উদ্যাপন করবে। আমরা এমন এক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখি, যে রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের মানবিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখবে।
১ দিন আগে
পথকুকুর বা বিড়াল হত্যা গুরুতর অপরাধ এবং এটি জনস্বাস্থ্য ও পশু সুরক্ষার দিক থেকে একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী, এই ধরনের পশু হত্যা নিষ্ঠুরতা এবং মানবিক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
১ দিন আগে