জাহীদ রেজা নূর
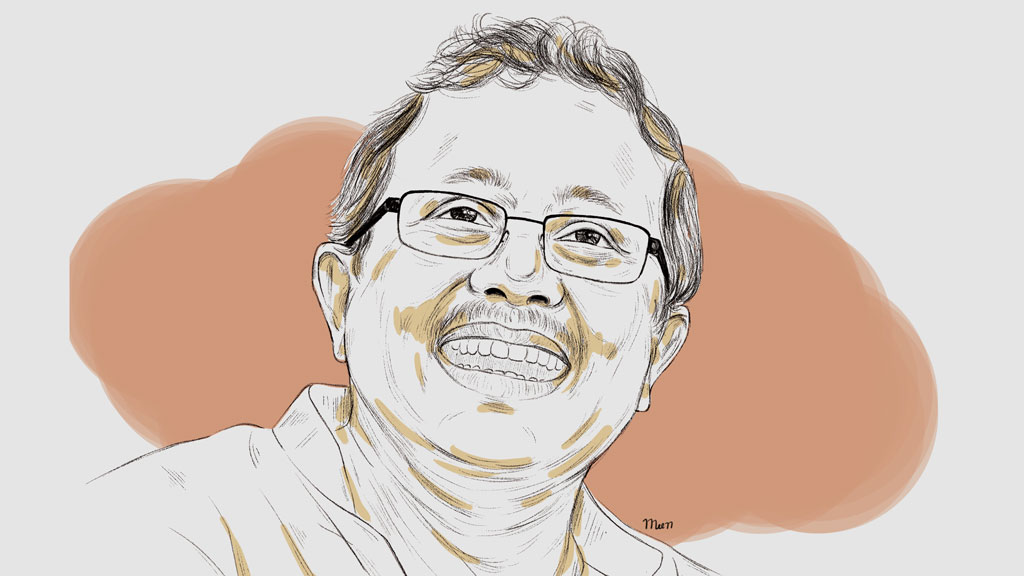
সোভিয়েত ইউনিয়নে যখন গিয়েছিলাম, তখন প্রথম বর্ষে আমাদের শহরে পড়তে এল রাজন, সেটা ১৯৮৭ সাল। রোস্তভ নামে একটি শহরে প্রস্তুতিপর্বের পড়াশোনা শেষ করে ক্রাসনাদারে এসেছে। মেডিকেলে পড়বে। আমি সদ্য কুবান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব বিভাগে ক্লাস শুরু করেছি। আমাদের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের সুবিধা ছিল, ক্যাম্পাসেই ক্লাস হতো। সারা শহর ছুটোছুটি করতে হতো না। রাজনদের ক্লাস হতো সারা শহরে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন ভবনে। ফলে ওদের কষ্টটা ছিল বেশি। ট্রাম, ট্রলিবাস, বাস ব্যবহার করে ক্লাস করত ওরা।
একটু অবসর পেলেই রাজন চলে আসত আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে। সেখানে অনেক রাত পর্যন্ত আমরা নানা ধরনের আলোচনা করতাম। সে আলোচনায় থাকত সমাজ বদলের কথা, খোঁজা হতো সাংস্কৃতিক মুক্তির উপায়। তখন আর আমাদের বয়স কত? কুড়ির এপাশ–ওপাশ। কিন্তু ভাবনাগুলো ছিল প্রখর ভালোবাসায় ঘেরা।
রাজনকে কখনোই আমার মনে হয়নি, ও হিন্দু, কিংবা আমাকেও কখনো মুসলমান ভেবে রাজন কথা বলেনি। এখন ভাবি, সে সময়টায় কী করে আমরা ধর্মীয় গণ্ডি অতিক্রম করে সম্পর্কগুলো গড়ে নিতাম? বলতেই হয়, আমাদের ক্রাসনাদার শহরে জহরদা, শ্যামলদা, বিবেকদা, প্রবীরদা, প্রশান্তদা, সমিত ছিল। কিন্তু এদের কাউকেই কখনো হিন্দু মনে করিনি। জহরদা পরপর দুবার আমাদের শহরের বাঙালি ছাত্র সংগঠনের সভাপতি ছিলেন। সমিত ছিল একবার।
তার মানে কি সে সময়টায় স্বাধীনতার অঙ্গীকারের একটা রেশ ছিল মানুষের মনে? আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে পুরো বাঙালি এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃ–গোষ্ঠীর মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশ নিয়েছিল। তারই রেশ রয়ে গিয়েছিল? সেটাই কি এই বন্ধুতার কারণ?
দুই.
পরে ভেবে দেখেছি, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আবহ মানস গঠনে সাহায্য করেছে ঠিকই, কিন্তু তার চেয়ে বড় ছিল পারিবারিক শিক্ষা। সোভিয়েত ইউনিয়নে যে ছেলেমেয়েরা পড়তে যেত, তাদের বেশির ভাগই পারিবারিকভাবে ছিল অগ্রসর মানুষ। তাদের কাছে আন্তর্জাতিকতাবাদ, দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা কোনো কৃত্রিম বিষয় ছিল না। হয়তো সেটাই ছিল এই বন্ধনের একটা বড় কারণ। এখনো তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। এখনো মনে হয় না, তারা অনেক দূরের মানুষ।
এ বছর দুর্গা পূজায় রাজন চেয়েছিল বড় করে উৎসব করবে। কিন্তু পূজামণ্ডপে হামলা, প্রতিমা ভাঙচুর, মানুষ হত্যা ইত্যাদির কারণে ওর পূজার আনন্দ মাটি হয়ে গিয়েছিল।
বিজয়া দশমীর দিন তাই ওর বাড়িতে রাতে শুধু আমার পরিবারই ছিল আমন্ত্রিত। আর কেউ নয়। আমরা সহিংসতার আবহে নিজেদের মতো থাকতে চেষ্টা করেছি। ভাবতে চেষ্টা করেছি, সবকিছুর পরও একটা উজ্জ্বল আলো হয়তো দেখা যাবে। কিন্তু সে ভাবনা যে ধীরে ধীরে একেবারেই অবাস্তব হয়ে উঠছে, সেটা ভেবেও মনে কাঁটা দিয়েছে।
তিন.
বাঙালি হিন্দু–মুসলিম সম্পর্কের শুরুটা নিয়ে ভাবলে অনেক কিছু পরিষ্কার হবে। অন্ধতা যাদের গ্রাস করেছে, তাদের ভাবনায় আলো ফেলার জন্যই তা বলতে হবে।
বাঙালি মুসলমানের অধিকাংশই দেশজ মুসলমান, অর্থাৎ ধর্মান্তরিত মুসলমান। নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে সুফি দরবেশরাই বাংলায় এসেছিলেন ধর্মপ্রচারের জন্য। বখতিয়ার খিলজির বাংলা জয়ের অনেক আগে থেকেই ধর্মান্তরকরণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। তার মানে, একহাতে কোরআন, অন্য হাতে কৃপাণ নিয়ে মুসলমানরা বলপূর্বক অন্য ধর্মের মানুষকে ধর্মান্তরিত করছিল, এটা আসরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচারের ফল। এ দেশের মানুষ ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হওয়ার একটা বড় কারণ ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার আকুতি। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিল সেন–বর্মণ ও দেব শাসকেরা। খেয়াল করলেই দেখা যাবে, বাংলার উত্তর ও পূর্ব অংশে বৌদ্ধদের সংখ্যা ছিল বেশি। পাল যুগে বৌদ্ধ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব থাকলেও কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি আলাদা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। পাল শাসনের সমাপ্তিতে যে সেন শাসন শুরু হলো, তা ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসন। অত্যাচারের মাত্রা ভয়াবহরকম হয়ে উঠেছিল। তখন বৌদ্ধরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করেছিল।
 বাংলায় মুসলমান শাসন শুরু হওয়ার পর সুফিদের আগমন আরও বেড়ে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের তুলনায় ইসলাম ছিল উদার। ইসলাম ধর্ম অন্তত তত্ত্বগতভাবে মানুষে মানুষে সমানাধিকার দেয়। তার ছোঁয়া লাগলে এই ধর্মের কারও জাত যায় না। কোরআন পড়তে তার কোনো বাধা নেই। ফলে নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও সুফিদের আমন্ত্রণে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছিল। কখনোই যে ধর্মান্তরিত করার জন্য মুসলমানেরা চাপ দেয়নি, সে কথা বলা যাবে না, তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রবল শোষণে জর্জরিত হয়েই মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে।
বাংলায় মুসলমান শাসন শুরু হওয়ার পর সুফিদের আগমন আরও বেড়ে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের তুলনায় ইসলাম ছিল উদার। ইসলাম ধর্ম অন্তত তত্ত্বগতভাবে মানুষে মানুষে সমানাধিকার দেয়। তার ছোঁয়া লাগলে এই ধর্মের কারও জাত যায় না। কোরআন পড়তে তার কোনো বাধা নেই। ফলে নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও সুফিদের আমন্ত্রণে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছিল। কখনোই যে ধর্মান্তরিত করার জন্য মুসলমানেরা চাপ দেয়নি, সে কথা বলা যাবে না, তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রবল শোষণে জর্জরিত হয়েই মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে।
এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলা দরকার। সুফিদের সাধনায় বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে ভারতীয় যোগের প্রভাব পড়েছিল। তারও আগে ভারতে তান্ত্রিক ধর্মকর্মের ওপর বিশ্বাস ছিল। তান্ত্রিক গুরুরা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করা হতো। সুফি দরবেশদের সাধনাও অনেকটা তান্ত্রিক সাধনা বলে মনে করা হতো। সুফিরা ইসলামের শরিয়তি বিধান মেনে চলতেন না। ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না তাদের। ফলে খুব সহজেই সাধারণ মানুষ তাদের দিকে আকৃষ্ট হয়।
এ তো গেল নিম্নবিত্ত মানুষের ইসলাম গ্রহণের কথা। হিন্দু উচ্চবিত্ত মানুষের ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলিম হওয়ার কারণগুলোর মধ্যে ছিল, মুসলমান হলে জিজিয়া কর দিতে হতো না, উচ্চ রাজপদ লাভ করার সুযোগ আসত। এ ছাড়াও আরেকটা অদ্ভুত কারণে ধর্ম পরিবর্তন করতেন তারা। হিন্দু ধর্মের ভয়াবহ ছুৎমার্গ, অর্থাৎ স্পর্শদোষ, খাদ্যদোষ, দৃষ্টিদোষ ইত্যাদির কারণে অনেক হিন্দু ধর্মাবলম্বীকেই সমাজে পতিত করে রাখা হতো। গোষ্ঠীসমেত তাদের সমাজচ্যুত করা হতো। তখন উপায়ন্তর না দেখে তারা ধর্ম পরিবর্তন করতেন।
বাংলার শাসনকর্তাদের অধিকাংশই ছিলেন বহিরাগত মুসলমান। তবে নবাবি আমলে যারা মোগল সাম্রাজ্যকে অগ্রাহ্য করে বাংলা শাসন করেছেন, তারা এই দেশের মানুষের মতোই দিনযাপন করতেন। তারা লুণ্ঠন প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু মোগল শাসকেরা যাদের শাসন করতে পাঠাতেন, তারা চলে যাওয়ার সময় এ দেশের সম্পদও নিয়ে যেতেন।
এত কথা এখানে বলার উদ্দেশ্য হলো:
ক. বাংলার বৌদ্ধ ও হিন্দুরা ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন মূলত ব্রাহ্মণ্যবাদী শোষণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। অধিকাংশ ধর্মান্তর ঘটে সুফিবাদের প্রভাবে।
খ. সুফিবাদ শরিয়তি বিধান মেনে চলত না। সুফিবাদী ধারার ইসলাম এবং লোকজ সংস্কৃতির মিশ্রণেই গড়ে উঠেছিল এ দেশের ইসলাম।
গ. এ দেশে যারা মুসলিম হিসেবে বসবাস করছেন, তাদের প্রায় সবাই ধর্মান্তরিত মুসলমান। বৌদ্ধ ও হিন্দুদের থেকেই ধর্মান্তরিত হয়েছেন। তাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এ দেশের মাটিতেই প্রথিত। আরবদেশের সংস্কৃতি থেকে তা বেড়ে ওঠেনি।
ঘ. খুব অল্পসংখ্যক বিদেশি শাসক এ দেশ শাসন করেছে। তাদের উত্তরাধিকার এত অধিক সংখ্যক নয়, যে নিজেদের আরব–বংশোদ্ভূত বলে দাবি করা যায়।
চার.
সম্প্রদায়–প্রশ্নে আমরা হেরে গেলাম কখন?
মনে করার কোনো কারণ নেই, এ দেশে হিন্দু–মুসলমান সম্পর্ক আগে সোনায় সোহাগা ছিল। জাত–পাতের প্রশ্নে হিন্দুবাড়ি ছিল (মূলত ব্রাহ্মণ) ভীষণরকম রক্ষণশীল। সেখানে মুসলমান ছেলেমেয়েদের খাওয়া–দাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কয়েকটি আত্মজীবনী পড়ে মনে হয়েছে, এ ব্যাপারে কট্টর মৌলবাদ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল। ইংরেজ আমলে হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি অংশের মধ্যে নতুন আলো এসে পড়ায় (যাকে অনেকেই বাংলার রেনেসাঁ নামে আখ্যায়িত করেন) অনেক ধরনের রক্ষণশীলতা থেকে তারা বেরিয়ে আসতে শুরু করেন। মূলত ইউরোপীয় মূল্যবোধের কারণে তারা অনেক বেশি উদারপন্থী হয়ে ওঠেন। কিন্তু অনগ্রসর গোটা ভারতের রক্ষণশীল মানসিকতা যেমন তার বিকাশের অন্তরায় ছিল, তেমনি দেশজ সংস্কৃতিকে একেবারে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল বলে এই মূল্যবোধ খুব বেশি দূর এগিয়ে যেতে পারেনি। ফলে বাংলার রেনেসাঁ বেশ কিছু ভালো স্বপ্ন দেখিয়েছে বটে, কিন্তু স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মেলানো হয়নি বলে সারা দেশের মানুষকে উদ্বেলিত করতে পারেনি।
বাঙালি মুসলমান তার মুক্তির পথ খুঁজেছে আরও পরে। এবং তা ইংরেজদের হাত ধরেই। সে সব ইতিহাস এখানে না বলে শুধু এ কথা বলাই যথেষ্ট যে, মুক্তবুদ্ধির চর্চা করার সময় যে প্রসঙ্গটিকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, তা হলো হাজার বছর ধরে আচরিত ধর্মবোধের সঙ্গে নতুন চিন্তাধারার সাংঘর্ষিক জায়গাগুলোকে আলোচনায় আনা। এবং প্রমাণ করে দেখিয়ে দেওয়া দরকার ছিল, কীভাবে মানুষকে মানবিক হতে হবে।
 পাঁচ.
পাঁচ.
মুক্তবুদ্ধির চর্চাটা রয়ে গেল কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া তথাকথিত ‘শিক্ষিত’ মানুষের মধ্যে। এই ‘শিক্ষিত’ মানুষের বাইরে যে গোটা দেশটা ছিল, সেটা কিন্তু এই আলোয় উদ্ভাসিত হলো না। রাজনীতি থেকে একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টা খানিক স্পষ্ট হবে। এ দেশে সর্বস্ব ত্যাগ করে যারা রাজনীতি করল, তাদের সিংহভাগই ছিলেন সাম্যবাদী। কিন্তু তাদের এই আত্মত্যাগ, সাম্যবাদী চেতনা কেন সাধারণ মানুষ গ্রহণ করল না? কমিউনিস্ট আন্দোলন মধ্যবিত্ত শ্রেণির আন্দোলন হিসেবেই বিকশিত হলো, নিম্নবিত্ত মানুষকে বাঁচানোর এই লড়াইয়ে নিম্নবিত্ত মানুষ কেন আকৃষ্ট হলো না? কেন মানুষ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যেই খুঁজল মুক্তির পথ?
এখন মনে হয়, এর বড় কারণটিই হলো, দেশের সংস্কৃতির শিকড়ের ওপর দাঁড়িয়ে যখন দেশের লাঞ্ছনা, বঞ্চনার কথা বলেছে কোনো জাতীয়তাবাদী নেতা, তখন তা সহজেই বুঝতে পেরেছে মানুষ। কমিউনিস্ট কিংবা ইসলামি চিন্তাধারাকে অগ্রাহ্য করেই বাঙালি জাতীয়তাবাদে দীক্ষিত হয়েছে এই অঞ্চলের মানুষ। কমিউনিস্টরা বলেছে আন্তর্জাতিকতাবাদের কথা। নিজ দেশকে তারা সেই আন্তর্জাতিকতাবাদের অংশ বলে প্রচার করেছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ থাকে তার নিজের অভাব, সমস্যা, সংকট নিয়ে। অন্য দেশের নির্যাতিত মানুষদের জন্য তার মর্মযাতনা থাকতে পারে, কিন্তু কোনোভাবেই তা নিজের কষ্ট, সংগ্রামের চেয়ে বড় নয়। ফলে, আন্তর্জাতিকতাবাদ এখানে বেড়ে উঠতে পারেনি। এবং এক সময় দেখা গেছে বিপ্লব প্রচারের জন্য সমাজতন্ত্রী টাকার আমদানি বন্ধ হয়ে যেতেই এই আন্দোলনে মরিচা ধরেছে।
অন্যদিকে, আরব–উদ্ভূত ধর্মীয় রাজনীতিও এই দেশের হালে পানি পায়নি একই কারণে। মানুষ নিজেকে দেশের অংশ বলে ভাবতে শুরু করেছে। আরবের খেজুর সংস্কৃতি দিয়ে এ দেশের ডাল–ভাতের চাহিদা মিটবে না, সেটা বুঝতে সময় নেয়নি আইয়ুবী স্বৈরশাসনের আমলে।
অথচ সেই আরব সংস্কৃতির রমরমায় বাঙালি তথা এই দেশের মানুষ আজ নতুন করে আবার আত্মপরিচয়ের সংকটে ভুগছে। সুফিবাদকে একেবারে অগ্রাহ্য করে কট্টর সালাফিবাদের দিকে রওনা দিল বাঙালি মুসলমান।
কেন এমন হলো?
ছয়.
সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে এগোলে এই জেহাদি জোশের একটা প্যাটার্ন হয়তো বোঝা সম্ভব হবে।
যে কোনো জাতীয়তাবাদের মতো বাঙালি জাতীয়তাবাদও বাঙালির মনে অনেক স্বপ্নের জন্ম দিয়েছিল। বুঝিয়েছিল, অসাম্প্রদায়িকতাই মুক্তির পথ দেখাবে। সমাজের সকল ক্ষেত্রে নিজেদের দক্ষতা ও পরিশ্রম দিয়ে গড়ে তুলতে হবে দেশ। দক্ষতা ও পরিশ্রম দিয়ে দেশ গড়ার কাজটি যখনই হোঁচট খেয়েছে, তখন জাতীয়তাবাদও হোঁচট খেয়েছে। আর সেই শূন্যস্থান পূরণ করার দিকে এগিয়েছে ইসলামি জাতীয়তাবাদ। ইসলাম যদি সকল মুসলমানকে এক করতে পারত, তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে মুসলমানদের একটাই দেশ থাকত, কিন্তু সেখানে এতগুলো আলাদা দেশ কেন?
বাঙালি জাতীয়তাবাদ যখন স্বপ্নগুলো পূরণ করতে পারল না, এবং বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর সুপরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশকে মিনি পাকিস্তানে পরিণত করা হলো, তারপর থেকে আমাদের দেশের রাজনৈতিক–সামাজিক–সাংস্কৃতিক জীবনটা পর্যালোচনা করলেই বোঝা যাবে, বেহুলার বাসরঘরে কী করে সাম্প্রদায়িকতার সাপ ঢুকে পড়ল।
সাত.
বাঙালি মুসলমান টেরও পেল না, কীভাবে তারা রাজনীতির শিকার হয়েছে। একই কথা বাঙালি হিন্দুর ক্ষেত্রেও বলা চলে। ১৯০৫ সালে বাঙালি হিন্দু যখন বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল, তখন বাঙালি সত্তাই ছিল প্রধান পরিচয়। কিন্তু এরপর থেকেই ধীরে ধীরে বাঙালি হিন্দু প্রভাবিত হলো নিখিল ভারতীয় রাজনীতি দিয়ে, এবং কংগ্রেস নেতৃত্বেও গোঁড়াদের অবস্থান দৃঢ় হয়ে গেল। বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা তখন হয়ে গেল ভারতীয় জাতীয়তাবাদী। ফলে সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, শরৎ বসু, কিরণ শঙ্কর রায় যখন দেশভাগের সময় বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করছেন, তখন বাংলার হিন্দুরা তাদের ধর্মীয় পরিচয়টাকে জাতীয় পরিচয়ের চেয়ে বড় করে দেখেছিল। পূর্ব বাংলার মুসলিমরাও কিছুদিন অবিভক্ত বঙ্গের পক্ষে লড়াই করে একসময় খণ্ডিত বাংলাকে মেনে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারে কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় চলে এসেছিল। সেই অস্থির সময়টি নিয়ে যে যার মতো ব্যাখ্যা দেয়, কিন্তু সে সময় জাতিগত পরিচয়ে বলীয়ান হতে না পারাই যে পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িকতার আগুনকে উসকে দিয়েছে, সে কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।
আট.
তাই ভাবতে হবে—ধর্মচর্চার ভার কাদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে? এখন তো বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে মসজিদ অনেক বেশি যোগাযোগের মাধ্যম হয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জ্ঞানচর্চা মোটেই অনুপ্রেরণাদায়ক অবস্থানে নেই। শিক্ষক–শিক্ষার্থীদের মধ্যেও চর্চাহীন, প্রজ্ঞাহীন মুফতে টাকা বানানোর প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ফলে, নৈতিকভাবে দৃঢ় অবস্থান ধরে রেখে কোনো বিষয়ে কথা বলার মতো মানুষ ক্রমেই কমে যাচ্ছে। শুক্রবার দিন জুম্মার নামাজ আদায় করতে মসজিদে ভিড় করেন মানুষ। সে সময় মসজিদ এলাকায় যে আলোচনা হয়, যে খুতবা শুনে বাড়ি ফেরেন ধর্মভীরু মুসলমান, তাতে ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর মতো বহু উপাদান থাকে। ধর্মের অপব্যাখ্যার বিরুদ্ধেও কেউ কথা বলতে সাহস পায় না। কারণ মসজিদ এলাকায় এই ধরনের ধর্মের লেবাসধারী মানুষেরই আধিক্য। এরা যুক্তি মানে না।
একজন মুসলমানের কাছে যেমন মসজিদ, একজন হিন্দুর কাছে তেমন মন্দির, খ্রিষ্টানের কাছে চার্চ, বৌদ্ধের কাছে প্যাগোডা ঠিক তেমন। যার যার ধর্ম তার তার। যিনি যে ধর্ম পালন করছেন, তিনি তার ধর্মের অনুশাসন মেনে চলবেন। কিন্তু ধর্মটাকে অর্ধশিক্ষিত মানুষের হাতে ছেড়ে দেওয়ার ফলেই এই গোল বেঁধেছে। প্রচলিত ধারণা মতে, উচ্চশিক্ষা লাভকারী মানুষই শিক্ষিত। কথাটা অসার। বহুযুগের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারায় মানুষ যে বিদ্যা করায়ত্ত করেছে, তার যে শক্তি আছে, তা অমূল্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ না নিয়েই সেই অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে কৃষক ফসল ফলায়। কোন জমিতে কতটুকু সার দিতে হবে, কোন সময়টা ফসল রোপণের জন্য উৎকৃষ্ট সময়, কখন ফসল কাটতে হবে এগুলো বছরের পর বছরের অভিজ্ঞতা থেকেই কৃষক করে যায়। বিজ্ঞান হয়তো সেই শিক্ষার সঙ্গে সংগতিপূর্ণভাবে আরও কিছু কাজ করে, যা এই প্রক্রিয়াকে সহজ করে তোলে।
তাই তথাকথিত শিক্ষিত মানুষের চেয়ে জীবনের শিক্ষালাভ করেছেন যিনি প্রকৃতি থেকে, তিনি নিশ্চয়ই পিছিয়ে পড়া মানুষ নন। গোল বাধে অর্ধশিক্ষিত মানুষ নিয়ে। এরা না বুঝে বা নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নিজের মতো কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে নেয়। যেহেতু তাদের কেউ চ্যালেঞ্জ করছে না, সেহেতু এরা কল্পিত ভাবনাকেই সত্য বলে চালিয়ে দিতে চায় এবং ধর্ম নিয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করার রীতি নেই বলে সবাই চুপ করে থাকে। সাধারণ মানুষ ভুলেই যায় যে, প্রশ্নটি ধর্ম নিয়ে নয়, ধর্মের অপব্যাখ্যা নিয়ে। ফলে ওয়াজ, মসজিদের ভুল বয়ানগুলোই ছড়িয়ে যায় সমাজে, সমাজ তার যৌক্তিক অবস্থান হারায় এবং ধীরে ধীরে অন্ধবিশ্বাসের দিকে অগ্রসর হয়।
এখন একটি বিষয় আলোচনায় আসা দরকার। দেশের একটা বড় অংশের শিক্ষাব্যবস্থায় দেশ নেই, দেশের মানুষ নেই, দেশের ইতিহাস নেই, ধর্মীয় পরিচয়টাই সেখানে তার একমাত্র পরিচয়—এ রকম একটা জেলখানা যারা বানিয়েছে, তাদের কাছ থেকে সুস্থ চিন্তা আশা করা যায় না। দেশের উৎপাদনের সঙ্গে এদের যোগাযোগের ব্যবস্থা কে করে দেবে। মসজিদ, মাদ্রাসা ছাড়া তো এদের চাকরির সুযোগ কম। তার মানে, ওই আবহ ছাড়া আর কোনো আবহের মধ্যেই তাদের যাওয়ার সুযোগ নেই। এ রকম জীবনে হতাশা আসাটা স্বাভাবিক। ঢলে তারা কীভাবে অন্যের দুঃখ, কষ্ট অনুভব করবে?
 নয়.
নয়.
ধর্ম, আরববিশ্ব, মুসলমান পরিচয় ইত্যাদি আসলে কোনো ব্যাপারই নয়। ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে নিজের অপরাধকে ঢেকে ফেলার এক অদ্ভুত খেলায় নিয়োজিত হয়েছে বাংলাদেশের ধর্ম ব্যবসায়ীরা। আর সেটাকেই ধর্মীয় বিধান বলে চালানোর চেষ্টা করছে।
দশ.
আমাদের স্কুলের নাম ছিল সিদ্ধেশ্বরী বালক উচ্চ বিদ্যালয়। আমার কাছের বন্ধুদের একজন ছিল জয়ন্ত কুমার ভৌমিক। গত শতাব্দীর সাত ও আটের দশকে স্কুলের নামটি হিন্দু নাম কিনা, জয়ন্ত হিন্দু হয়েও আমার কাছের বন্ধুদের একজন কেন, সে প্রশ্ন ওঠেনি কখনো। অমরজ্যোতি ক্লাবে খেলার সময় আমাদের ওয়ানডাউন ব্যাটসম্যান সৌমিত্র বা টুটুলকে কখনোই ধর্ম পরিচয় দিয়ে বিচার করিনি আমরা। আমার আর সৌমিত্রের জুটি একসঙ্গে অনেকটা সময় ক্রিজে কাটিয়েছি। তখন আমাদের একটাই পরিচয়, রান করে দলকে ভালো জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে। এখন কেন ধর্ম পরিচয়টা বড় হয়ে উঠছে?
বড় হয়ে উঠছে এ কারণে যে, পরিবারে ধর্ম–সহিষ্ণুতার শিক্ষা দেওয়া হয় না। ফেসবুকে স্ট্যাটাস কিংবা স্ট্যাটাসের মন্তব্যগুলো পড়লেই বুঝতে পারবেন, আমরা কোথায় আছি। নারী সম্পর্কে অধিকাংশ পুরুষের অবস্থানও টের পাবেন।
এগারো.
যারা এই অপঘাত থেকে বাঁচাতে পারত, তারা সময়মতো নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়ায়নি। অনেকেই ফেসবুকে, পত্রিকার লেখালেখিতে এই ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন, অথচ যে সংকটকালে মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হয়, সে কাজটি প্রতিবেশীরা করেননি। ধর্মীয় সহনশীলতা থাকলে তো স্থানীয় মুসলমানেরাই হিন্দু সম্প্রদায়ের অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। কোথাও কোথাও যে সে রকম ঘটনা ঘটেনি, তা–ও নয়। কিন্তু মতলববাজরা তাদের স্বার্থসিদ্ধি করে নিয়েছিল আগেই।
আমাদের যে পোক্ত সমাজ ছিল, তার বন্ধন শিথিল হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ভারতের কথা টেনে আনার কোনো দরকার নেই। ভারতে উগ্র হিন্দুত্ববাদ যদি বিজেপির মাধ্যমে প্রসারিত হয়, তাহলে সেটাও ভারতের জনজীবনের জন্য খুবই অস্বাস্থ্যকর অবস্থা। তার নিন্দা জানাব। কিন্তু আমাদের দেশের কিছু মুসলমানের অন্যায়কে জায়েজ করার জন্য ভারতের হিন্দুকে টেনে আনার কোনো অর্থ নেই। সেটাও মতলববাজির চূড়ান্ত।
বারো.
সমাজটা হারিয়ে গেছে। সমাজের বন্ধন শিথিল হয়েছে। ধর্মবিদ্বেষ বেড়েছে।
সমাজ হারিয়ে যাওয়ার পেছনে যে কারণগুলো আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো সাংস্কৃতিক বন্ধন ছিন্ন হওয়া। দেশের মানুষ সাংস্কৃতিক জীবনযাপনে অংশ নিচ্ছে কম। সংস্কৃতিই তো মানুষে মানুষে মিলন আনে। সিনেমা, নাটক, যাত্রার অভিনয় দেখে, সংলাপ শুনে মানুষের মনে বোধ জন্মায়, গানের সুরে সে বুঝতে পারে, হৃদয়ে ভালোবাসা, দেশপ্রেমের চাষবাস করার প্রয়োজনীয়তা। বৈশাখী মেলা, নবান্ন, পিঠা উৎসব ইত্যাদি পোক্ত করে সামাজিক বন্ধন।
সে সব মুছে গিয়ে মানুষ যান্ত্রিকতায় বিশ্বাসী হয়ে পড়ছে। ছুটছে টাকার পেছনে। আরা ছুটছে ধর্মান্ধতার পেছনে। তাই এই আলগা হয়ে যাওয়া বাঁধনকে পোক্ত করা খুব দরকার। কিন্তু তার আলামত পাচ্ছি না।
আর রাজনীতি? এ ধরনের নিন্দনীয় ঘটনা ঘটার সময় জনপ্রতিনিধিরা কোথায় থাকেন? তারা কেন মানুষকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন না? তাঁরা চাইলেই নিজ সংগঠনের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে এই সংকটের মোকাবিলা করতে পারেন।
পাশের বাড়ির মানুষটাও তো পাশে এসে দাঁড়াতে পারেন? কেন দাঁড়ান না?
ওই যে বললাম, আলগা হয়েছে বাঁধনের জোর। এটা রবীন্দ্রনাথের কথা। ‘রথের রশি’তে লিখেছিলেন তিনি। সেই বাঁধন পোক্ত হবে কিনা, তা নির্ভর করছে আমাদের কাণ্ডজ্ঞানের ওপর। সেটা আপাতত খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে।
লেখক: উপসম্পাদক, আজকের পত্রিকা।
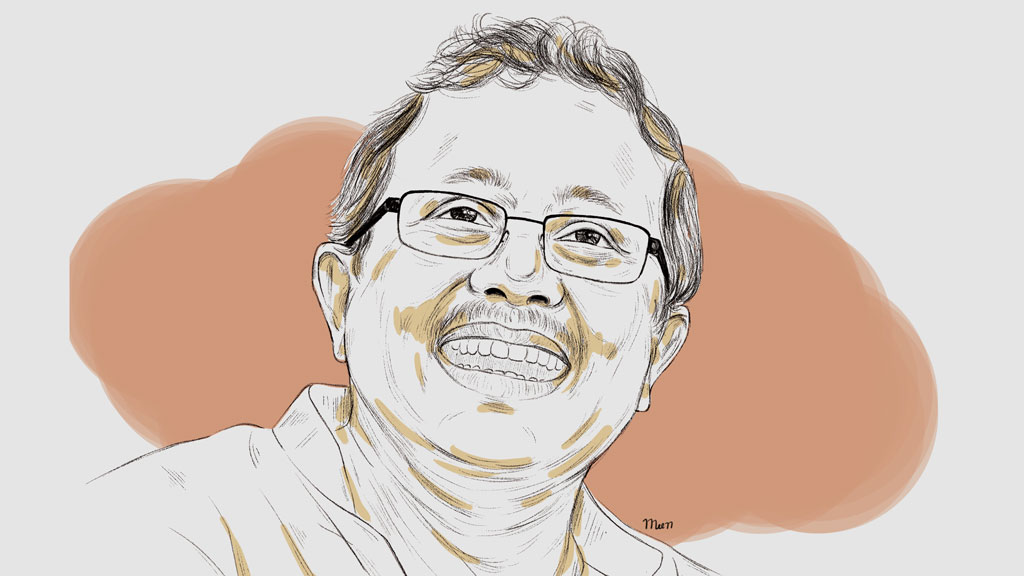
সোভিয়েত ইউনিয়নে যখন গিয়েছিলাম, তখন প্রথম বর্ষে আমাদের শহরে পড়তে এল রাজন, সেটা ১৯৮৭ সাল। রোস্তভ নামে একটি শহরে প্রস্তুতিপর্বের পড়াশোনা শেষ করে ক্রাসনাদারে এসেছে। মেডিকেলে পড়বে। আমি সদ্য কুবান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব বিভাগে ক্লাস শুরু করেছি। আমাদের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের সুবিধা ছিল, ক্যাম্পাসেই ক্লাস হতো। সারা শহর ছুটোছুটি করতে হতো না। রাজনদের ক্লাস হতো সারা শহরে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন ভবনে। ফলে ওদের কষ্টটা ছিল বেশি। ট্রাম, ট্রলিবাস, বাস ব্যবহার করে ক্লাস করত ওরা।
একটু অবসর পেলেই রাজন চলে আসত আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে। সেখানে অনেক রাত পর্যন্ত আমরা নানা ধরনের আলোচনা করতাম। সে আলোচনায় থাকত সমাজ বদলের কথা, খোঁজা হতো সাংস্কৃতিক মুক্তির উপায়। তখন আর আমাদের বয়স কত? কুড়ির এপাশ–ওপাশ। কিন্তু ভাবনাগুলো ছিল প্রখর ভালোবাসায় ঘেরা।
রাজনকে কখনোই আমার মনে হয়নি, ও হিন্দু, কিংবা আমাকেও কখনো মুসলমান ভেবে রাজন কথা বলেনি। এখন ভাবি, সে সময়টায় কী করে আমরা ধর্মীয় গণ্ডি অতিক্রম করে সম্পর্কগুলো গড়ে নিতাম? বলতেই হয়, আমাদের ক্রাসনাদার শহরে জহরদা, শ্যামলদা, বিবেকদা, প্রবীরদা, প্রশান্তদা, সমিত ছিল। কিন্তু এদের কাউকেই কখনো হিন্দু মনে করিনি। জহরদা পরপর দুবার আমাদের শহরের বাঙালি ছাত্র সংগঠনের সভাপতি ছিলেন। সমিত ছিল একবার।
তার মানে কি সে সময়টায় স্বাধীনতার অঙ্গীকারের একটা রেশ ছিল মানুষের মনে? আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে পুরো বাঙালি এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃ–গোষ্ঠীর মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশ নিয়েছিল। তারই রেশ রয়ে গিয়েছিল? সেটাই কি এই বন্ধুতার কারণ?
দুই.
পরে ভেবে দেখেছি, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আবহ মানস গঠনে সাহায্য করেছে ঠিকই, কিন্তু তার চেয়ে বড় ছিল পারিবারিক শিক্ষা। সোভিয়েত ইউনিয়নে যে ছেলেমেয়েরা পড়তে যেত, তাদের বেশির ভাগই পারিবারিকভাবে ছিল অগ্রসর মানুষ। তাদের কাছে আন্তর্জাতিকতাবাদ, দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা কোনো কৃত্রিম বিষয় ছিল না। হয়তো সেটাই ছিল এই বন্ধনের একটা বড় কারণ। এখনো তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। এখনো মনে হয় না, তারা অনেক দূরের মানুষ।
এ বছর দুর্গা পূজায় রাজন চেয়েছিল বড় করে উৎসব করবে। কিন্তু পূজামণ্ডপে হামলা, প্রতিমা ভাঙচুর, মানুষ হত্যা ইত্যাদির কারণে ওর পূজার আনন্দ মাটি হয়ে গিয়েছিল।
বিজয়া দশমীর দিন তাই ওর বাড়িতে রাতে শুধু আমার পরিবারই ছিল আমন্ত্রিত। আর কেউ নয়। আমরা সহিংসতার আবহে নিজেদের মতো থাকতে চেষ্টা করেছি। ভাবতে চেষ্টা করেছি, সবকিছুর পরও একটা উজ্জ্বল আলো হয়তো দেখা যাবে। কিন্তু সে ভাবনা যে ধীরে ধীরে একেবারেই অবাস্তব হয়ে উঠছে, সেটা ভেবেও মনে কাঁটা দিয়েছে।
তিন.
বাঙালি হিন্দু–মুসলিম সম্পর্কের শুরুটা নিয়ে ভাবলে অনেক কিছু পরিষ্কার হবে। অন্ধতা যাদের গ্রাস করেছে, তাদের ভাবনায় আলো ফেলার জন্যই তা বলতে হবে।
বাঙালি মুসলমানের অধিকাংশই দেশজ মুসলমান, অর্থাৎ ধর্মান্তরিত মুসলমান। নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে সুফি দরবেশরাই বাংলায় এসেছিলেন ধর্মপ্রচারের জন্য। বখতিয়ার খিলজির বাংলা জয়ের অনেক আগে থেকেই ধর্মান্তরকরণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। তার মানে, একহাতে কোরআন, অন্য হাতে কৃপাণ নিয়ে মুসলমানরা বলপূর্বক অন্য ধর্মের মানুষকে ধর্মান্তরিত করছিল, এটা আসরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচারের ফল। এ দেশের মানুষ ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হওয়ার একটা বড় কারণ ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার আকুতি। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিল সেন–বর্মণ ও দেব শাসকেরা। খেয়াল করলেই দেখা যাবে, বাংলার উত্তর ও পূর্ব অংশে বৌদ্ধদের সংখ্যা ছিল বেশি। পাল যুগে বৌদ্ধ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব থাকলেও কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি আলাদা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। পাল শাসনের সমাপ্তিতে যে সেন শাসন শুরু হলো, তা ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসন। অত্যাচারের মাত্রা ভয়াবহরকম হয়ে উঠেছিল। তখন বৌদ্ধরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করেছিল।
 বাংলায় মুসলমান শাসন শুরু হওয়ার পর সুফিদের আগমন আরও বেড়ে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের তুলনায় ইসলাম ছিল উদার। ইসলাম ধর্ম অন্তত তত্ত্বগতভাবে মানুষে মানুষে সমানাধিকার দেয়। তার ছোঁয়া লাগলে এই ধর্মের কারও জাত যায় না। কোরআন পড়তে তার কোনো বাধা নেই। ফলে নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও সুফিদের আমন্ত্রণে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছিল। কখনোই যে ধর্মান্তরিত করার জন্য মুসলমানেরা চাপ দেয়নি, সে কথা বলা যাবে না, তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রবল শোষণে জর্জরিত হয়েই মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে।
বাংলায় মুসলমান শাসন শুরু হওয়ার পর সুফিদের আগমন আরও বেড়ে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের তুলনায় ইসলাম ছিল উদার। ইসলাম ধর্ম অন্তত তত্ত্বগতভাবে মানুষে মানুষে সমানাধিকার দেয়। তার ছোঁয়া লাগলে এই ধর্মের কারও জাত যায় না। কোরআন পড়তে তার কোনো বাধা নেই। ফলে নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও সুফিদের আমন্ত্রণে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছিল। কখনোই যে ধর্মান্তরিত করার জন্য মুসলমানেরা চাপ দেয়নি, সে কথা বলা যাবে না, তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রবল শোষণে জর্জরিত হয়েই মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে।
এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলা দরকার। সুফিদের সাধনায় বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে ভারতীয় যোগের প্রভাব পড়েছিল। তারও আগে ভারতে তান্ত্রিক ধর্মকর্মের ওপর বিশ্বাস ছিল। তান্ত্রিক গুরুরা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করা হতো। সুফি দরবেশদের সাধনাও অনেকটা তান্ত্রিক সাধনা বলে মনে করা হতো। সুফিরা ইসলামের শরিয়তি বিধান মেনে চলতেন না। ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না তাদের। ফলে খুব সহজেই সাধারণ মানুষ তাদের দিকে আকৃষ্ট হয়।
এ তো গেল নিম্নবিত্ত মানুষের ইসলাম গ্রহণের কথা। হিন্দু উচ্চবিত্ত মানুষের ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলিম হওয়ার কারণগুলোর মধ্যে ছিল, মুসলমান হলে জিজিয়া কর দিতে হতো না, উচ্চ রাজপদ লাভ করার সুযোগ আসত। এ ছাড়াও আরেকটা অদ্ভুত কারণে ধর্ম পরিবর্তন করতেন তারা। হিন্দু ধর্মের ভয়াবহ ছুৎমার্গ, অর্থাৎ স্পর্শদোষ, খাদ্যদোষ, দৃষ্টিদোষ ইত্যাদির কারণে অনেক হিন্দু ধর্মাবলম্বীকেই সমাজে পতিত করে রাখা হতো। গোষ্ঠীসমেত তাদের সমাজচ্যুত করা হতো। তখন উপায়ন্তর না দেখে তারা ধর্ম পরিবর্তন করতেন।
বাংলার শাসনকর্তাদের অধিকাংশই ছিলেন বহিরাগত মুসলমান। তবে নবাবি আমলে যারা মোগল সাম্রাজ্যকে অগ্রাহ্য করে বাংলা শাসন করেছেন, তারা এই দেশের মানুষের মতোই দিনযাপন করতেন। তারা লুণ্ঠন প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু মোগল শাসকেরা যাদের শাসন করতে পাঠাতেন, তারা চলে যাওয়ার সময় এ দেশের সম্পদও নিয়ে যেতেন।
এত কথা এখানে বলার উদ্দেশ্য হলো:
ক. বাংলার বৌদ্ধ ও হিন্দুরা ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন মূলত ব্রাহ্মণ্যবাদী শোষণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। অধিকাংশ ধর্মান্তর ঘটে সুফিবাদের প্রভাবে।
খ. সুফিবাদ শরিয়তি বিধান মেনে চলত না। সুফিবাদী ধারার ইসলাম এবং লোকজ সংস্কৃতির মিশ্রণেই গড়ে উঠেছিল এ দেশের ইসলাম।
গ. এ দেশে যারা মুসলিম হিসেবে বসবাস করছেন, তাদের প্রায় সবাই ধর্মান্তরিত মুসলমান। বৌদ্ধ ও হিন্দুদের থেকেই ধর্মান্তরিত হয়েছেন। তাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এ দেশের মাটিতেই প্রথিত। আরবদেশের সংস্কৃতি থেকে তা বেড়ে ওঠেনি।
ঘ. খুব অল্পসংখ্যক বিদেশি শাসক এ দেশ শাসন করেছে। তাদের উত্তরাধিকার এত অধিক সংখ্যক নয়, যে নিজেদের আরব–বংশোদ্ভূত বলে দাবি করা যায়।
চার.
সম্প্রদায়–প্রশ্নে আমরা হেরে গেলাম কখন?
মনে করার কোনো কারণ নেই, এ দেশে হিন্দু–মুসলমান সম্পর্ক আগে সোনায় সোহাগা ছিল। জাত–পাতের প্রশ্নে হিন্দুবাড়ি ছিল (মূলত ব্রাহ্মণ) ভীষণরকম রক্ষণশীল। সেখানে মুসলমান ছেলেমেয়েদের খাওয়া–দাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কয়েকটি আত্মজীবনী পড়ে মনে হয়েছে, এ ব্যাপারে কট্টর মৌলবাদ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল। ইংরেজ আমলে হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি অংশের মধ্যে নতুন আলো এসে পড়ায় (যাকে অনেকেই বাংলার রেনেসাঁ নামে আখ্যায়িত করেন) অনেক ধরনের রক্ষণশীলতা থেকে তারা বেরিয়ে আসতে শুরু করেন। মূলত ইউরোপীয় মূল্যবোধের কারণে তারা অনেক বেশি উদারপন্থী হয়ে ওঠেন। কিন্তু অনগ্রসর গোটা ভারতের রক্ষণশীল মানসিকতা যেমন তার বিকাশের অন্তরায় ছিল, তেমনি দেশজ সংস্কৃতিকে একেবারে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল বলে এই মূল্যবোধ খুব বেশি দূর এগিয়ে যেতে পারেনি। ফলে বাংলার রেনেসাঁ বেশ কিছু ভালো স্বপ্ন দেখিয়েছে বটে, কিন্তু স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মেলানো হয়নি বলে সারা দেশের মানুষকে উদ্বেলিত করতে পারেনি।
বাঙালি মুসলমান তার মুক্তির পথ খুঁজেছে আরও পরে। এবং তা ইংরেজদের হাত ধরেই। সে সব ইতিহাস এখানে না বলে শুধু এ কথা বলাই যথেষ্ট যে, মুক্তবুদ্ধির চর্চা করার সময় যে প্রসঙ্গটিকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, তা হলো হাজার বছর ধরে আচরিত ধর্মবোধের সঙ্গে নতুন চিন্তাধারার সাংঘর্ষিক জায়গাগুলোকে আলোচনায় আনা। এবং প্রমাণ করে দেখিয়ে দেওয়া দরকার ছিল, কীভাবে মানুষকে মানবিক হতে হবে।
 পাঁচ.
পাঁচ.
মুক্তবুদ্ধির চর্চাটা রয়ে গেল কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া তথাকথিত ‘শিক্ষিত’ মানুষের মধ্যে। এই ‘শিক্ষিত’ মানুষের বাইরে যে গোটা দেশটা ছিল, সেটা কিন্তু এই আলোয় উদ্ভাসিত হলো না। রাজনীতি থেকে একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টা খানিক স্পষ্ট হবে। এ দেশে সর্বস্ব ত্যাগ করে যারা রাজনীতি করল, তাদের সিংহভাগই ছিলেন সাম্যবাদী। কিন্তু তাদের এই আত্মত্যাগ, সাম্যবাদী চেতনা কেন সাধারণ মানুষ গ্রহণ করল না? কমিউনিস্ট আন্দোলন মধ্যবিত্ত শ্রেণির আন্দোলন হিসেবেই বিকশিত হলো, নিম্নবিত্ত মানুষকে বাঁচানোর এই লড়াইয়ে নিম্নবিত্ত মানুষ কেন আকৃষ্ট হলো না? কেন মানুষ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যেই খুঁজল মুক্তির পথ?
এখন মনে হয়, এর বড় কারণটিই হলো, দেশের সংস্কৃতির শিকড়ের ওপর দাঁড়িয়ে যখন দেশের লাঞ্ছনা, বঞ্চনার কথা বলেছে কোনো জাতীয়তাবাদী নেতা, তখন তা সহজেই বুঝতে পেরেছে মানুষ। কমিউনিস্ট কিংবা ইসলামি চিন্তাধারাকে অগ্রাহ্য করেই বাঙালি জাতীয়তাবাদে দীক্ষিত হয়েছে এই অঞ্চলের মানুষ। কমিউনিস্টরা বলেছে আন্তর্জাতিকতাবাদের কথা। নিজ দেশকে তারা সেই আন্তর্জাতিকতাবাদের অংশ বলে প্রচার করেছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ থাকে তার নিজের অভাব, সমস্যা, সংকট নিয়ে। অন্য দেশের নির্যাতিত মানুষদের জন্য তার মর্মযাতনা থাকতে পারে, কিন্তু কোনোভাবেই তা নিজের কষ্ট, সংগ্রামের চেয়ে বড় নয়। ফলে, আন্তর্জাতিকতাবাদ এখানে বেড়ে উঠতে পারেনি। এবং এক সময় দেখা গেছে বিপ্লব প্রচারের জন্য সমাজতন্ত্রী টাকার আমদানি বন্ধ হয়ে যেতেই এই আন্দোলনে মরিচা ধরেছে।
অন্যদিকে, আরব–উদ্ভূত ধর্মীয় রাজনীতিও এই দেশের হালে পানি পায়নি একই কারণে। মানুষ নিজেকে দেশের অংশ বলে ভাবতে শুরু করেছে। আরবের খেজুর সংস্কৃতি দিয়ে এ দেশের ডাল–ভাতের চাহিদা মিটবে না, সেটা বুঝতে সময় নেয়নি আইয়ুবী স্বৈরশাসনের আমলে।
অথচ সেই আরব সংস্কৃতির রমরমায় বাঙালি তথা এই দেশের মানুষ আজ নতুন করে আবার আত্মপরিচয়ের সংকটে ভুগছে। সুফিবাদকে একেবারে অগ্রাহ্য করে কট্টর সালাফিবাদের দিকে রওনা দিল বাঙালি মুসলমান।
কেন এমন হলো?
ছয়.
সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে এগোলে এই জেহাদি জোশের একটা প্যাটার্ন হয়তো বোঝা সম্ভব হবে।
যে কোনো জাতীয়তাবাদের মতো বাঙালি জাতীয়তাবাদও বাঙালির মনে অনেক স্বপ্নের জন্ম দিয়েছিল। বুঝিয়েছিল, অসাম্প্রদায়িকতাই মুক্তির পথ দেখাবে। সমাজের সকল ক্ষেত্রে নিজেদের দক্ষতা ও পরিশ্রম দিয়ে গড়ে তুলতে হবে দেশ। দক্ষতা ও পরিশ্রম দিয়ে দেশ গড়ার কাজটি যখনই হোঁচট খেয়েছে, তখন জাতীয়তাবাদও হোঁচট খেয়েছে। আর সেই শূন্যস্থান পূরণ করার দিকে এগিয়েছে ইসলামি জাতীয়তাবাদ। ইসলাম যদি সকল মুসলমানকে এক করতে পারত, তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে মুসলমানদের একটাই দেশ থাকত, কিন্তু সেখানে এতগুলো আলাদা দেশ কেন?
বাঙালি জাতীয়তাবাদ যখন স্বপ্নগুলো পূরণ করতে পারল না, এবং বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর সুপরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশকে মিনি পাকিস্তানে পরিণত করা হলো, তারপর থেকে আমাদের দেশের রাজনৈতিক–সামাজিক–সাংস্কৃতিক জীবনটা পর্যালোচনা করলেই বোঝা যাবে, বেহুলার বাসরঘরে কী করে সাম্প্রদায়িকতার সাপ ঢুকে পড়ল।
সাত.
বাঙালি মুসলমান টেরও পেল না, কীভাবে তারা রাজনীতির শিকার হয়েছে। একই কথা বাঙালি হিন্দুর ক্ষেত্রেও বলা চলে। ১৯০৫ সালে বাঙালি হিন্দু যখন বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল, তখন বাঙালি সত্তাই ছিল প্রধান পরিচয়। কিন্তু এরপর থেকেই ধীরে ধীরে বাঙালি হিন্দু প্রভাবিত হলো নিখিল ভারতীয় রাজনীতি দিয়ে, এবং কংগ্রেস নেতৃত্বেও গোঁড়াদের অবস্থান দৃঢ় হয়ে গেল। বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা তখন হয়ে গেল ভারতীয় জাতীয়তাবাদী। ফলে সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, শরৎ বসু, কিরণ শঙ্কর রায় যখন দেশভাগের সময় বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করছেন, তখন বাংলার হিন্দুরা তাদের ধর্মীয় পরিচয়টাকে জাতীয় পরিচয়ের চেয়ে বড় করে দেখেছিল। পূর্ব বাংলার মুসলিমরাও কিছুদিন অবিভক্ত বঙ্গের পক্ষে লড়াই করে একসময় খণ্ডিত বাংলাকে মেনে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারে কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় চলে এসেছিল। সেই অস্থির সময়টি নিয়ে যে যার মতো ব্যাখ্যা দেয়, কিন্তু সে সময় জাতিগত পরিচয়ে বলীয়ান হতে না পারাই যে পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িকতার আগুনকে উসকে দিয়েছে, সে কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।
আট.
তাই ভাবতে হবে—ধর্মচর্চার ভার কাদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে? এখন তো বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে মসজিদ অনেক বেশি যোগাযোগের মাধ্যম হয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জ্ঞানচর্চা মোটেই অনুপ্রেরণাদায়ক অবস্থানে নেই। শিক্ষক–শিক্ষার্থীদের মধ্যেও চর্চাহীন, প্রজ্ঞাহীন মুফতে টাকা বানানোর প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ফলে, নৈতিকভাবে দৃঢ় অবস্থান ধরে রেখে কোনো বিষয়ে কথা বলার মতো মানুষ ক্রমেই কমে যাচ্ছে। শুক্রবার দিন জুম্মার নামাজ আদায় করতে মসজিদে ভিড় করেন মানুষ। সে সময় মসজিদ এলাকায় যে আলোচনা হয়, যে খুতবা শুনে বাড়ি ফেরেন ধর্মভীরু মুসলমান, তাতে ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর মতো বহু উপাদান থাকে। ধর্মের অপব্যাখ্যার বিরুদ্ধেও কেউ কথা বলতে সাহস পায় না। কারণ মসজিদ এলাকায় এই ধরনের ধর্মের লেবাসধারী মানুষেরই আধিক্য। এরা যুক্তি মানে না।
একজন মুসলমানের কাছে যেমন মসজিদ, একজন হিন্দুর কাছে তেমন মন্দির, খ্রিষ্টানের কাছে চার্চ, বৌদ্ধের কাছে প্যাগোডা ঠিক তেমন। যার যার ধর্ম তার তার। যিনি যে ধর্ম পালন করছেন, তিনি তার ধর্মের অনুশাসন মেনে চলবেন। কিন্তু ধর্মটাকে অর্ধশিক্ষিত মানুষের হাতে ছেড়ে দেওয়ার ফলেই এই গোল বেঁধেছে। প্রচলিত ধারণা মতে, উচ্চশিক্ষা লাভকারী মানুষই শিক্ষিত। কথাটা অসার। বহুযুগের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারায় মানুষ যে বিদ্যা করায়ত্ত করেছে, তার যে শক্তি আছে, তা অমূল্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ না নিয়েই সেই অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে কৃষক ফসল ফলায়। কোন জমিতে কতটুকু সার দিতে হবে, কোন সময়টা ফসল রোপণের জন্য উৎকৃষ্ট সময়, কখন ফসল কাটতে হবে এগুলো বছরের পর বছরের অভিজ্ঞতা থেকেই কৃষক করে যায়। বিজ্ঞান হয়তো সেই শিক্ষার সঙ্গে সংগতিপূর্ণভাবে আরও কিছু কাজ করে, যা এই প্রক্রিয়াকে সহজ করে তোলে।
তাই তথাকথিত শিক্ষিত মানুষের চেয়ে জীবনের শিক্ষালাভ করেছেন যিনি প্রকৃতি থেকে, তিনি নিশ্চয়ই পিছিয়ে পড়া মানুষ নন। গোল বাধে অর্ধশিক্ষিত মানুষ নিয়ে। এরা না বুঝে বা নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নিজের মতো কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে নেয়। যেহেতু তাদের কেউ চ্যালেঞ্জ করছে না, সেহেতু এরা কল্পিত ভাবনাকেই সত্য বলে চালিয়ে দিতে চায় এবং ধর্ম নিয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করার রীতি নেই বলে সবাই চুপ করে থাকে। সাধারণ মানুষ ভুলেই যায় যে, প্রশ্নটি ধর্ম নিয়ে নয়, ধর্মের অপব্যাখ্যা নিয়ে। ফলে ওয়াজ, মসজিদের ভুল বয়ানগুলোই ছড়িয়ে যায় সমাজে, সমাজ তার যৌক্তিক অবস্থান হারায় এবং ধীরে ধীরে অন্ধবিশ্বাসের দিকে অগ্রসর হয়।
এখন একটি বিষয় আলোচনায় আসা দরকার। দেশের একটা বড় অংশের শিক্ষাব্যবস্থায় দেশ নেই, দেশের মানুষ নেই, দেশের ইতিহাস নেই, ধর্মীয় পরিচয়টাই সেখানে তার একমাত্র পরিচয়—এ রকম একটা জেলখানা যারা বানিয়েছে, তাদের কাছ থেকে সুস্থ চিন্তা আশা করা যায় না। দেশের উৎপাদনের সঙ্গে এদের যোগাযোগের ব্যবস্থা কে করে দেবে। মসজিদ, মাদ্রাসা ছাড়া তো এদের চাকরির সুযোগ কম। তার মানে, ওই আবহ ছাড়া আর কোনো আবহের মধ্যেই তাদের যাওয়ার সুযোগ নেই। এ রকম জীবনে হতাশা আসাটা স্বাভাবিক। ঢলে তারা কীভাবে অন্যের দুঃখ, কষ্ট অনুভব করবে?
 নয়.
নয়.
ধর্ম, আরববিশ্ব, মুসলমান পরিচয় ইত্যাদি আসলে কোনো ব্যাপারই নয়। ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে নিজের অপরাধকে ঢেকে ফেলার এক অদ্ভুত খেলায় নিয়োজিত হয়েছে বাংলাদেশের ধর্ম ব্যবসায়ীরা। আর সেটাকেই ধর্মীয় বিধান বলে চালানোর চেষ্টা করছে।
দশ.
আমাদের স্কুলের নাম ছিল সিদ্ধেশ্বরী বালক উচ্চ বিদ্যালয়। আমার কাছের বন্ধুদের একজন ছিল জয়ন্ত কুমার ভৌমিক। গত শতাব্দীর সাত ও আটের দশকে স্কুলের নামটি হিন্দু নাম কিনা, জয়ন্ত হিন্দু হয়েও আমার কাছের বন্ধুদের একজন কেন, সে প্রশ্ন ওঠেনি কখনো। অমরজ্যোতি ক্লাবে খেলার সময় আমাদের ওয়ানডাউন ব্যাটসম্যান সৌমিত্র বা টুটুলকে কখনোই ধর্ম পরিচয় দিয়ে বিচার করিনি আমরা। আমার আর সৌমিত্রের জুটি একসঙ্গে অনেকটা সময় ক্রিজে কাটিয়েছি। তখন আমাদের একটাই পরিচয়, রান করে দলকে ভালো জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে। এখন কেন ধর্ম পরিচয়টা বড় হয়ে উঠছে?
বড় হয়ে উঠছে এ কারণে যে, পরিবারে ধর্ম–সহিষ্ণুতার শিক্ষা দেওয়া হয় না। ফেসবুকে স্ট্যাটাস কিংবা স্ট্যাটাসের মন্তব্যগুলো পড়লেই বুঝতে পারবেন, আমরা কোথায় আছি। নারী সম্পর্কে অধিকাংশ পুরুষের অবস্থানও টের পাবেন।
এগারো.
যারা এই অপঘাত থেকে বাঁচাতে পারত, তারা সময়মতো নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়ায়নি। অনেকেই ফেসবুকে, পত্রিকার লেখালেখিতে এই ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন, অথচ যে সংকটকালে মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হয়, সে কাজটি প্রতিবেশীরা করেননি। ধর্মীয় সহনশীলতা থাকলে তো স্থানীয় মুসলমানেরাই হিন্দু সম্প্রদায়ের অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। কোথাও কোথাও যে সে রকম ঘটনা ঘটেনি, তা–ও নয়। কিন্তু মতলববাজরা তাদের স্বার্থসিদ্ধি করে নিয়েছিল আগেই।
আমাদের যে পোক্ত সমাজ ছিল, তার বন্ধন শিথিল হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ভারতের কথা টেনে আনার কোনো দরকার নেই। ভারতে উগ্র হিন্দুত্ববাদ যদি বিজেপির মাধ্যমে প্রসারিত হয়, তাহলে সেটাও ভারতের জনজীবনের জন্য খুবই অস্বাস্থ্যকর অবস্থা। তার নিন্দা জানাব। কিন্তু আমাদের দেশের কিছু মুসলমানের অন্যায়কে জায়েজ করার জন্য ভারতের হিন্দুকে টেনে আনার কোনো অর্থ নেই। সেটাও মতলববাজির চূড়ান্ত।
বারো.
সমাজটা হারিয়ে গেছে। সমাজের বন্ধন শিথিল হয়েছে। ধর্মবিদ্বেষ বেড়েছে।
সমাজ হারিয়ে যাওয়ার পেছনে যে কারণগুলো আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো সাংস্কৃতিক বন্ধন ছিন্ন হওয়া। দেশের মানুষ সাংস্কৃতিক জীবনযাপনে অংশ নিচ্ছে কম। সংস্কৃতিই তো মানুষে মানুষে মিলন আনে। সিনেমা, নাটক, যাত্রার অভিনয় দেখে, সংলাপ শুনে মানুষের মনে বোধ জন্মায়, গানের সুরে সে বুঝতে পারে, হৃদয়ে ভালোবাসা, দেশপ্রেমের চাষবাস করার প্রয়োজনীয়তা। বৈশাখী মেলা, নবান্ন, পিঠা উৎসব ইত্যাদি পোক্ত করে সামাজিক বন্ধন।
সে সব মুছে গিয়ে মানুষ যান্ত্রিকতায় বিশ্বাসী হয়ে পড়ছে। ছুটছে টাকার পেছনে। আরা ছুটছে ধর্মান্ধতার পেছনে। তাই এই আলগা হয়ে যাওয়া বাঁধনকে পোক্ত করা খুব দরকার। কিন্তু তার আলামত পাচ্ছি না।
আর রাজনীতি? এ ধরনের নিন্দনীয় ঘটনা ঘটার সময় জনপ্রতিনিধিরা কোথায় থাকেন? তারা কেন মানুষকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন না? তাঁরা চাইলেই নিজ সংগঠনের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে এই সংকটের মোকাবিলা করতে পারেন।
পাশের বাড়ির মানুষটাও তো পাশে এসে দাঁড়াতে পারেন? কেন দাঁড়ান না?
ওই যে বললাম, আলগা হয়েছে বাঁধনের জোর। এটা রবীন্দ্রনাথের কথা। ‘রথের রশি’তে লিখেছিলেন তিনি। সেই বাঁধন পোক্ত হবে কিনা, তা নির্ভর করছে আমাদের কাণ্ডজ্ঞানের ওপর। সেটা আপাতত খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে।
লেখক: উপসম্পাদক, আজকের পত্রিকা।

ঢাকা শহরের যানজটের সমস্যা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি দিয়েছে মেট্রোরেল। তবে এটা চালুর প্রায় দেড় বছরে এই আধুনিক গণপরিবহনব্যবস্থা মাঝে মাঝে বন্ধ হয়েছে। সেটা একটা ভাবনার বিষয়। মূলত এই সময়ের মধ্যে অন্তত ১০ বার মেট্রোরেল চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়েছে, যার বেশির ভাগই জনগণের গাফিলতির কারণে হয়েছে।
১ দিন আগে
আমরা এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখি, যেখানে নানা ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গের মানুষ পরস্পরের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করবে। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় জারিত হয়ে সমাজের বৈচিত্র্যকে উদ্যাপন করবে। আমরা এমন এক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখি, যে রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের মানবিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখবে।
১ দিন আগে
পথকুকুর বা বিড়াল হত্যা গুরুতর অপরাধ এবং এটি জনস্বাস্থ্য ও পশু সুরক্ষার দিক থেকে একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী, এই ধরনের পশু হত্যা নিষ্ঠুরতা এবং মানবিক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
১ দিন আগে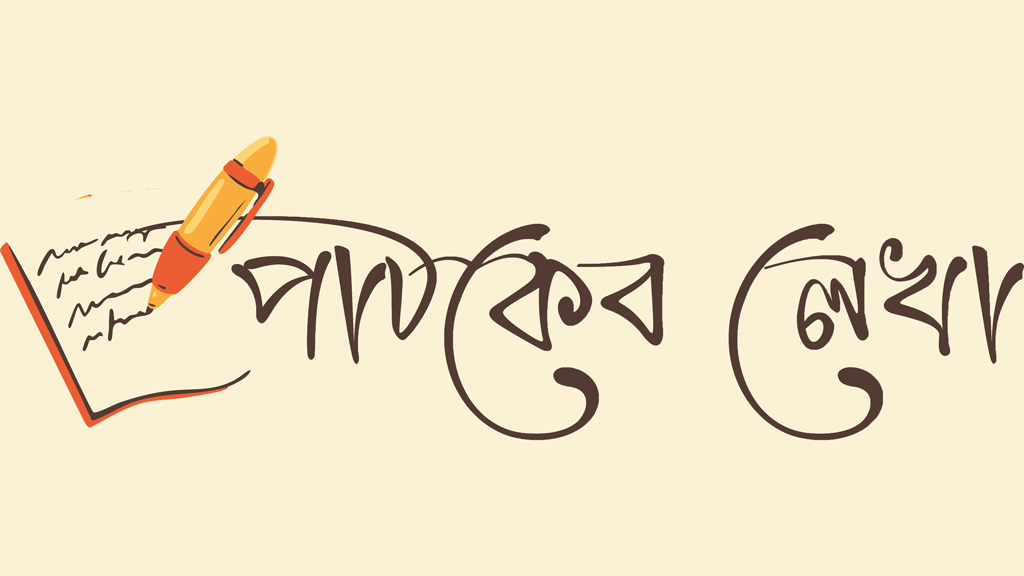
মানুষের জীবন শুধু বেঁচে থাকার নাম নয়; জীবন মানে হচ্ছে পূর্ণতার সন্ধান, মানসিক শান্তি ও শারীরিক সুস্থতার সুষম সমন্বয়। এই সমন্বয় সাধনের দুটি প্রধান উপাদান হলো সংগীত ও শরীরচর্চা। সংগীত আত্মাকে প্রশান্ত করে, মনকে উজ্জীবিত করে; আর শরীরচর্চা দেহকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখে।
১ দিন আগেসম্পাদকীয়

ঢাকা শহরের যানজটের সমস্যা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি দিয়েছে মেট্রোরেল। তবে এটা চালুর প্রায় দেড় বছরে এই আধুনিক গণপরিবহনব্যবস্থা মাঝে মাঝে বন্ধ হয়েছে। সেটা একটা ভাবনার বিষয়। মূলত এই সময়ের মধ্যে অন্তত ১০ বার মেট্রোরেল চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়েছে, যার বেশির ভাগই জনগণের গাফিলতির কারণে হয়েছে।
এই দেড় বছরে মেট্রোরেল লাইনে কাপড়, ব্যাগ, ড্রোন, তার নিক্ষেপের কারণে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে। এখনই যদি এসব সমস্যা সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ না করা যায়, তাহলে ভবিষ্যতে আরও বড় দুর্ঘটনার ঝুঁকি তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। একটা ভালো ব্যাপার যে, মেট্রোরেলের নিরাপত্তাব্যবস্থা এমন যে রেললাইনে সামান্যতম বাধা সৃষ্টি হলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেন থেমে যায়। এটি দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য ভালো দিক হলেও, মানবসৃষ্ট কারণে ঘন ঘন এই থমকে যাওয়া আধুনিক এই ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে কর্তৃপক্ষকে সেসব সমস্যা সমাধানের দিকে দৃষ্টি দেওয়া জরুরি।
জনগণ দ্বারা সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে করণীয় নিয়ে এখনই ভাবতে হবে কর্তৃপক্ষকে। তবে প্রযুক্তিগত সমস্যাও যে আছে, তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। কিছুদিন আগে ফার্মগেট এলাকায় বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ে একজনের নিহত হওয়ার ঘটনাটি এই আধুনিক পরিবহনব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা তৈরি করেছে। বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ার ঘটনায় ১১ ঘণ্টা পর্যন্ত ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। যান্ত্রিক ত্রুটি হতেই পারে, তবে গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা সরঞ্জাম বারবার বিকল হওয়া বা খুলে পড়ার ঘটনাটি মেট্রোরেলের কারিগরি তদারকি ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করেছে। এ ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত নজরদারি ও রক্ষণাবেক্ষণে আরও গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক। এক সূত্র থেকে জানা যায়, এই নিহতের ঘটনা এবং অন্যান্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মেট্রোরেলে আগের তুলনায় ১০ শতাংশ যাত্রী কমে গেছে।
যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা মেট্রোরেল চলাচল স্বাভাবিক রাখতে কিছু কার্যকর পদক্ষেপের পরামর্শ দিয়েছেন। যেমন মেট্রোরেলের লাইনে বস্তু শনাক্ত করতে ‘অবজেক্ট ডিটেকশন সেন্সর’ ও ‘এআই-চালিত সিসিটিভি’ স্থাপন করা, ড্রোন পড়া প্রতিরোধে ‘ড্রোন ডিটেকশন রাডার’ ও ‘জিওফেন্সিং সিস্টেম’ ব্যবহার করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া। এ ছাড়া বৈদ্যুতিক লাইনে সুরক্ষা নেট বসালে বাইরে থেকে তার বা বস্তু নিক্ষেপ ঠেকানো সম্ভব।
মেট্রোরেল দেশের সম্পদ। জনগণের মধ্যে সে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এর সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব। ডিএমটিসিএলকে প্রযুক্তিগত ত্রুটিগুলো দ্রুত সমাধান এবং রক্ষণাবেক্ষণে সর্বোচ্চ মান বজায় রাখতে হবে। একই সঙ্গে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে, যাতে মানুষ বুঝতে পারে তাদের সামান্য ভুল বা অসচেতনতা হাজার হাজার যাত্রীর ভোগান্তি এবং মারাত্মক দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। সচেতনতা ও প্রযুক্তিগত সুরক্ষা—এই দুইয়ের সমন্বয়েই কেবল মেট্রোরেলের মসৃণ ও নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করা সম্ভব। এই আধুনিক পরিষেবা যেন মাঝে মাঝে থমকে যাওয়ার দুর্নাম থেকে মুক্তি পায়, সেই প্রত্যাশা আমাদের।

ঢাকা শহরের যানজটের সমস্যা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি দিয়েছে মেট্রোরেল। তবে এটা চালুর প্রায় দেড় বছরে এই আধুনিক গণপরিবহনব্যবস্থা মাঝে মাঝে বন্ধ হয়েছে। সেটা একটা ভাবনার বিষয়। মূলত এই সময়ের মধ্যে অন্তত ১০ বার মেট্রোরেল চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়েছে, যার বেশির ভাগই জনগণের গাফিলতির কারণে হয়েছে।
এই দেড় বছরে মেট্রোরেল লাইনে কাপড়, ব্যাগ, ড্রোন, তার নিক্ষেপের কারণে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে। এখনই যদি এসব সমস্যা সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ না করা যায়, তাহলে ভবিষ্যতে আরও বড় দুর্ঘটনার ঝুঁকি তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। একটা ভালো ব্যাপার যে, মেট্রোরেলের নিরাপত্তাব্যবস্থা এমন যে রেললাইনে সামান্যতম বাধা সৃষ্টি হলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেন থেমে যায়। এটি দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য ভালো দিক হলেও, মানবসৃষ্ট কারণে ঘন ঘন এই থমকে যাওয়া আধুনিক এই ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে কর্তৃপক্ষকে সেসব সমস্যা সমাধানের দিকে দৃষ্টি দেওয়া জরুরি।
জনগণ দ্বারা সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে করণীয় নিয়ে এখনই ভাবতে হবে কর্তৃপক্ষকে। তবে প্রযুক্তিগত সমস্যাও যে আছে, তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। কিছুদিন আগে ফার্মগেট এলাকায় বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ে একজনের নিহত হওয়ার ঘটনাটি এই আধুনিক পরিবহনব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা তৈরি করেছে। বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ার ঘটনায় ১১ ঘণ্টা পর্যন্ত ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। যান্ত্রিক ত্রুটি হতেই পারে, তবে গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা সরঞ্জাম বারবার বিকল হওয়া বা খুলে পড়ার ঘটনাটি মেট্রোরেলের কারিগরি তদারকি ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করেছে। এ ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত নজরদারি ও রক্ষণাবেক্ষণে আরও গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক। এক সূত্র থেকে জানা যায়, এই নিহতের ঘটনা এবং অন্যান্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মেট্রোরেলে আগের তুলনায় ১০ শতাংশ যাত্রী কমে গেছে।
যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা মেট্রোরেল চলাচল স্বাভাবিক রাখতে কিছু কার্যকর পদক্ষেপের পরামর্শ দিয়েছেন। যেমন মেট্রোরেলের লাইনে বস্তু শনাক্ত করতে ‘অবজেক্ট ডিটেকশন সেন্সর’ ও ‘এআই-চালিত সিসিটিভি’ স্থাপন করা, ড্রোন পড়া প্রতিরোধে ‘ড্রোন ডিটেকশন রাডার’ ও ‘জিওফেন্সিং সিস্টেম’ ব্যবহার করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া। এ ছাড়া বৈদ্যুতিক লাইনে সুরক্ষা নেট বসালে বাইরে থেকে তার বা বস্তু নিক্ষেপ ঠেকানো সম্ভব।
মেট্রোরেল দেশের সম্পদ। জনগণের মধ্যে সে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এর সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব। ডিএমটিসিএলকে প্রযুক্তিগত ত্রুটিগুলো দ্রুত সমাধান এবং রক্ষণাবেক্ষণে সর্বোচ্চ মান বজায় রাখতে হবে। একই সঙ্গে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে, যাতে মানুষ বুঝতে পারে তাদের সামান্য ভুল বা অসচেতনতা হাজার হাজার যাত্রীর ভোগান্তি এবং মারাত্মক দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। সচেতনতা ও প্রযুক্তিগত সুরক্ষা—এই দুইয়ের সমন্বয়েই কেবল মেট্রোরেলের মসৃণ ও নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করা সম্ভব। এই আধুনিক পরিষেবা যেন মাঝে মাঝে থমকে যাওয়ার দুর্নাম থেকে মুক্তি পায়, সেই প্রত্যাশা আমাদের।
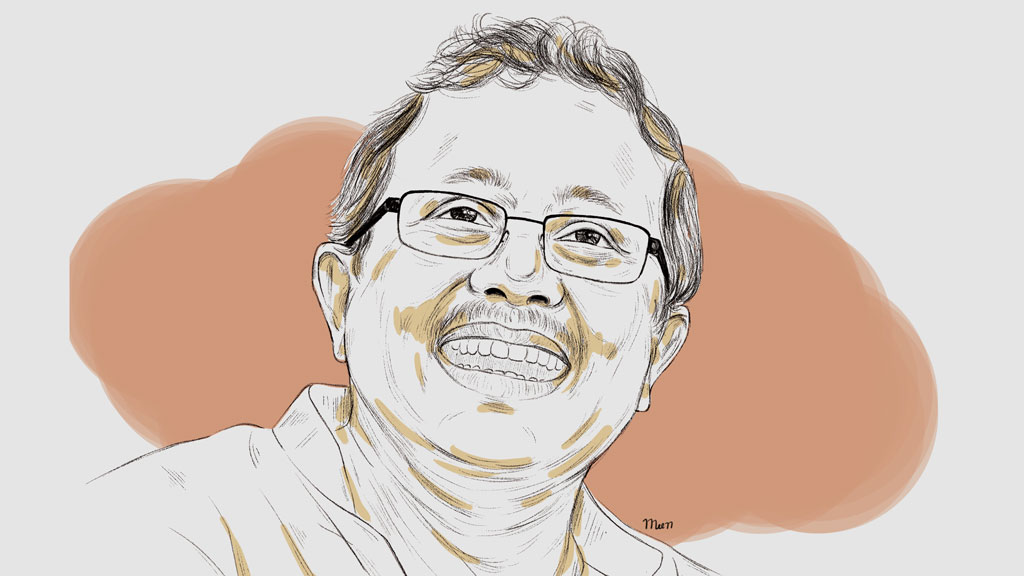
মুক্তবুদ্ধির চর্চাটা রয়ে গেল কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া তথাকথিত ‘শিক্ষিত’ মানুষের মধ্যে। এই ‘শিক্ষিত’ মানুষের বাইরে যে গোটা দেশটা ছিল, সেটা কিন্তু এই আলোয় উদ্ভাসিত হলো না। রাজনীতি থেকে একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টা খানিক স্পষ্ট হবে। এ দেশে সর্বস্ব ত্যাগ করে যারা রাজনীতি করল, তাদের সিংহভাগই ছিলেন সাম্যবাদী।
২২ অক্টোবর ২০২১
আমরা এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখি, যেখানে নানা ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গের মানুষ পরস্পরের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করবে। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় জারিত হয়ে সমাজের বৈচিত্র্যকে উদ্যাপন করবে। আমরা এমন এক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখি, যে রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের মানবিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখবে।
১ দিন আগে
পথকুকুর বা বিড়াল হত্যা গুরুতর অপরাধ এবং এটি জনস্বাস্থ্য ও পশু সুরক্ষার দিক থেকে একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী, এই ধরনের পশু হত্যা নিষ্ঠুরতা এবং মানবিক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
১ দিন আগে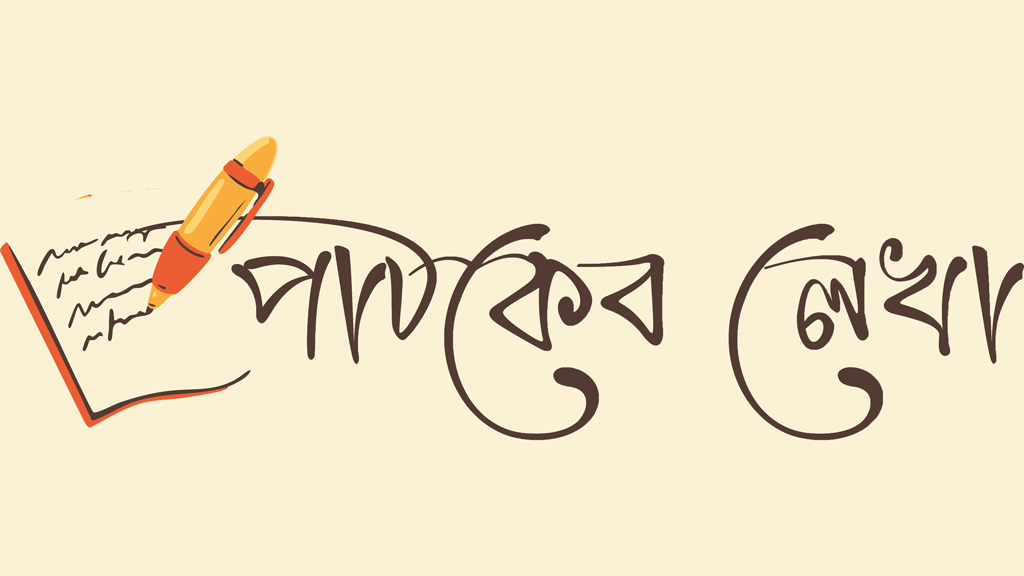
মানুষের জীবন শুধু বেঁচে থাকার নাম নয়; জীবন মানে হচ্ছে পূর্ণতার সন্ধান, মানসিক শান্তি ও শারীরিক সুস্থতার সুষম সমন্বয়। এই সমন্বয় সাধনের দুটি প্রধান উপাদান হলো সংগীত ও শরীরচর্চা। সংগীত আত্মাকে প্রশান্ত করে, মনকে উজ্জীবিত করে; আর শরীরচর্চা দেহকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখে।
১ দিন আগেবিধান রিবেরু

আমরা এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখি, যেখানে নানা ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গের মানুষ পরস্পরের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করবে। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় জারিত হয়ে সমাজের বৈচিত্র্যকে উদ্যাপন করবে। আমরা এমন এক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখি, যে রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের মানবিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখবে। বৈষম্য ও দারিদ্র্যকে মুখে মুখে নয়, প্রকৃত অর্থেই জাদুঘরে পাঠাবে। এমন সমাজ ও রাষ্ট্র পাওয়ার স্বপ্ন আমরা মূর্ত করে তুলেছিলাম ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। কিন্তু গন্ডগোলটা বাধল যখন একটি গোষ্ঠী বা ব্যক্তি নিজের মত ও বিশ্বাসকে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতে শুরু করল এবং চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। এতে করে সমাজে দেখা দিল সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ, রাষ্ট্রে প্রতিভাত হলো স্বৈরতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদ।
একটি সমাজে নানা মত ও পথের মানুষ থাকবে। বিশ্বাসী থাকবে। অবিশ্বাসী থাকবে। সবাইকে নিয়েই সমাজ ও রাষ্ট্র। ভিন্ন ভিন্ন দল ও মতের হয়েও তাহলে কেমন করে মানুষ এক সূত্রে গাঁথা থাকবে? কেমন করে একটি মানচিত্রের ভেতর চিহ্নিত হবে অভিন্নতা? জাতি থেকে জাতীয়তাবোধ, সেখান থেকে আমরা পেলাম জাতিরাষ্ট্র। সাতচল্লিশের আগে ভারতবর্ষে ধর্মকে জাতি ঠাওরে বা সুবিধার জন্য মনে মনে ধরে নিয়ে, দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগ করা হলো। কিন্তু ধর্মভিত্তিক জাতি যে সোনার পাথরবাটি, তা ১৯৭১ সালেই আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি। জাতি গঠনে গণমানুষের সম্মিলিত কল্পনাশক্তির একটা ভূমিকা আছে সত্যি, কিন্তু সেটার সুবিধা নিয়ে কেউ যদি জাতি গঠনের জন্য ধর্মকে ভিত্তি বানায়, তাহলে বলতে হয় কেউ চোরাবালির ওপর প্রাসাদ নির্মাণের স্বপ্ন দেখছে। দুই যুগ পূরণ হওয়ার আগেই তাই স্বপ্নভঙ্গের ঘটনাও ঘটেছে। বাস্তবে আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছি। তখন ভেবেছি এবার অসাম্প্রদায়িক ও সমতার সমাজ গঠন করা সহজ হবে। কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হলো কি?
কেউ বলেন জাতি হলো এক কল্পিত জনগোষ্ঠী। কেউবা বলেন এটি রাষ্ট্র গঠনের জন্য এক সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তি। আমাদের ভেতর একটি সামাজিক অনুভূতি কাজ করে যে, আমরা সবাই একই দেশের নাগরিক। এখানে যদি ফাটল থাকে, তাহলে সে দেশের ললাট থেকে শনির দশা কাটে না। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যতই প্রচার করা হোক না কেন বাঙালি জাতীয়তাবাদ কিংবা বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, কোথায় গিয়ে যেন তৃতীয় আরেকটি মতবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং তারা ১৯৪৭-এর দিকে তাকিয়ে ১৯৭১ সালকে গৌণ করে দিতে চায়। সাতচল্লিশে ধর্মকে জাতি জ্ঞান করে যে বিভাজন হয়েছিল, ১৯৭১ সালে কিন্তু সেই ভ্রম কেটে যায় এবং স্পষ্টতই মানুষ অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ধারণ করে জালিমের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। কিন্তু আজ সেই তৃতীয় পক্ষ ১৯৭১ সালকে অস্বীকার করতে চায়, ১৬ ডিসেম্বরকে বিজয় দিবস হিসেবেও তারা মানতে নারাজ। এমনকি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্য এসব গুরুত্বপূর্ণ তারিখ নিয়েও কেউ কেউ অত্যন্ত আপত্তিজনক মন্তব্য করে ফেলছেন। যেটি রাষ্ট্রদ্রোহের শামিল। তবে কি জাতি হিসেবে নিজেদের ভাবার ক্ষেত্রে পাটাতনে আবার সেই ধর্মভিত্তিক চিন্তাই মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে? নয় তো কেন হঠাৎ আবার এত ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের উত্থান ঘটল? কেনইবা সমাজে ধর্মের প্রতি, ধর্মভিত্তিক রাজনীতির প্রতি এই পক্ষপাত লক্ষ করা যাচ্ছে? বাংলাদেশের সমাজে ইদানীং মানুষ নিজেদের মানব, বিশ্বনাগরিক বা একটি জাতিগোষ্ঠীর পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার বদলে ধর্মপরিচয়কে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে, সর্বাগ্রে স্থান দিচ্ছে। এই পরিবর্তন কেন ঘটল, কেমন করে ঘটল, তার হদিস সমাজবিজ্ঞানীরা ভালো করতে পারবেন। তবে এই পরিবর্তনের দায় কোনোভাবেই রাজনীতিবিদ ও শাসকশ্রেণি এড়াতে পারবে না।
যে মুক্তিযুদ্ধ আমাদের গৌরব করার মতো আত্মপরিচয় দিয়েছে, যে মুক্তিযুদ্ধ আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যে মুক্তিযুদ্ধ প্রমাণ করেছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষ এক সাগর রক্ত ঢালতে পারে অনায়াসে, সেই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আজ অত্যন্ত আপত্তিকর কথা উঠছে। তারা ফিরে যেতে চাইছে সাতচল্লিশে। কী উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ! একটি গোষ্ঠী ও কিছু তথাকথিক কনটেন্ট ক্রিয়েটর নিজেদের বিপুল অনুসারী সহযোগে মুক্তিযুদ্ধসংক্রান্ত যে ভয়ংকর মিথ্যা তথ্য প্রচার এবং চরম অপমানজনক বাক্য ব্যবহার করছে, তাতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় না হয়ে উপায় নেই। যেকোনো সুস্থ মানুষ, যাঁরা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকে সব দল-মত ও পথের ঊর্ধ্বে রেখে, যুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান, ৩০ লাখ শহীদ ও ২ লাখ নারীর সম্ভ্রমের কথা মাথায় রেখে, বাংলাদেশকে নিজেদের অস্তিত্বের অংশ মনে করেন, তাঁদের প্রত্যেকেই আজ বিমর্ষবোধ করছেন। মুক্তিযুদ্ধ যে শোষণহীন ও বৈষম্যমুক্ত সমাজের আকাঙ্ক্ষা থেকে উৎসারিত পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক ও জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে জনযুদ্ধ ছিল, সেটিকে যেন ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। দেখা যাচ্ছে, অনেকে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ও নির্যাতিতদের সংখ্যা নিয়ে কুতর্কের দোকান খুলে বসেছে। ৭ মার্চের ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান ‘জয় বাংলা’র পর ‘জয় পাকিস্তান’ বলেছিলেন কি না, সেটি আবিষ্কার করতে অস্থির হয়ে যাচ্ছে। যেন শেখ মুজিবুর রহমান ‘জয় পাকিস্তান’ বললেই গোটা ৭ মার্চের উত্তাল ভাষণ ও ভাষণ শুনতে আসা লাখো মানুষের মনের ভেতর থাকা স্বাধীনতার জন্য সমুদ্রসমান কল্লোল মিথ্যা হয়ে যায়। যদিও তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে সেদিনের বিশাল জনসভায় সশরীরের উপস্থিত থাকা অনেক বিশিষ্ট মানুষই শোনেননি ‘জয় পাকিস্তান’ বলা হচ্ছে। তাহলে এখন কেন এসব ছোটখাটো কথা নিয়ে এত সময়ক্ষেপণ? এসব করলেই কি এই জনপদের মানুষ যে পাকিস্তানি শাসকদের, বলতে গেলে খালি হাতে যুদ্ধ করে পরাজিত করেছিল, তা লুকিয়ে ফেলা যাবে? কারা এই অপচেষ্টা করছে আজকে? যেহেতু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের কাছে গৌরব ও অর্জনের ইতিহাস, তাই একে প্রশ্নবিদ্ধ করে তর্ক জুড়ে দিলে, মনে করা হচ্ছে মানুষ ওটা নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। আর এই ফাঁকে স্বার্থ উদ্ধার করে নেবে সুযোগসন্ধানীরা।
আরেকটি বিষয় নিয়ে কথা না বললেই নয়, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক কারণেই ভারত ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে গিয়েছিল। এটা ঠিক, তাদের জনতুষ্টিমূলক সংস্কৃতিতে, বিশেষ করে চলচ্চিত্রে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হিসেবে দেখানো হয়, এটা নিয়ে আপত্তি বজায় রেখেই বলতে চাই, সে সময় ভারত পূর্ববঙ্গের লাখ লাখ শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা দিয়ে যে নজির স্থাপন করেছিল, সেটি অস্বীকার করার জো নেই। তাদের আচরণ অনেক সময় বড়ভাইসুলভ ও কিছুটা আপত্তিজনক হলেও, মুক্তিযুদ্ধে তাদের যে সেনাসদস্য মারা গেছেন তা তো আর মিথ্যা নয়। কাজেই যার যেটা প্রাপ্য তাকে সেটা দিতে হয়। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা।
ইদানীং যে প্রবণতা প্রবল আকারে দেখা যাচ্ছে, সেটিকে আমি বলব, মাছির লক্ষণাক্রান্ত। ধরুন শেখ মুজিবুর রহমানের যে ভূমিকা রয়েছে মুক্তিযুদ্ধে, সেটি যেকোনো বিচারেই বাংলাদেশ গঠনের পর বাকশাল গঠনের চেয়ে অনেক বড় ব্যাপার। কিন্তু আজকাল দেখি তাঁর ওই অবদানের কথা উল্লেখ না করে কেবল বাকশাল নিয়ে আলাপ করা হয়। বাকশাল নিয়ে অবশ্যই আলাপ করা জরুরি, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর অবদানকে ছাপিয়ে সেটিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার ভেতর যে ভাষাবলয় পরিলক্ষিত হয়, যে বয়ান প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চোখে পড়ে, সেটি হুবহু বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী, তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক ও তাদের দোসরদের বয়ানের সঙ্গে মিলে যায়। স্বাধীনতালাভের অর্ধশতাব্দী পর এসেও বাংলাদেশ-বিরোধিতা এমনভাবে ফিরে আসার জন্য আমি মনে করি বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে যাঁরা ব্যবসা করেছেন তাঁরাই মূলত দায়ী। তাঁরাই আসলে খাল কেটে কুমির এনেছেন। এখন খাল খননকারীরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পলাতক, কিন্তু জনপদের মানুষ কুমিরের ভয়ে অনিশ্চিত জীবন কাটাচ্ছে।
শুধু এটুকু বলে শেষ করি, গণতন্ত্র মানে শুধু ভোট দেওয়া নয়। ভোট দেওয়ার ভেতর দিয়ে মানুষকে গণিতে পরিণত করা হয়। মাথা গোনার আরেক নাম ভোট। গণতন্ত্র তার চেয়েও বেশি কিছু। ভোট প্রদান জরুরি, কিন্তু তার চেয়েও অধিক জরুরি এই জনপদের মানুষের কাছে গণতন্ত্রের ধারণাকে স্পষ্ট করে তোলা। এটা যত দিন না হচ্ছে, তত দিন আসলে এই খাল কাটা ও কুমিরের খেলা চলতে থাকবে। কারণ, এতে খননকারী ও কুমির উভয়েরই লাভ রয়েছে।

আমরা এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখি, যেখানে নানা ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গের মানুষ পরস্পরের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করবে। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় জারিত হয়ে সমাজের বৈচিত্র্যকে উদ্যাপন করবে। আমরা এমন এক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখি, যে রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের মানবিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখবে। বৈষম্য ও দারিদ্র্যকে মুখে মুখে নয়, প্রকৃত অর্থেই জাদুঘরে পাঠাবে। এমন সমাজ ও রাষ্ট্র পাওয়ার স্বপ্ন আমরা মূর্ত করে তুলেছিলাম ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। কিন্তু গন্ডগোলটা বাধল যখন একটি গোষ্ঠী বা ব্যক্তি নিজের মত ও বিশ্বাসকে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতে শুরু করল এবং চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। এতে করে সমাজে দেখা দিল সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ, রাষ্ট্রে প্রতিভাত হলো স্বৈরতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদ।
একটি সমাজে নানা মত ও পথের মানুষ থাকবে। বিশ্বাসী থাকবে। অবিশ্বাসী থাকবে। সবাইকে নিয়েই সমাজ ও রাষ্ট্র। ভিন্ন ভিন্ন দল ও মতের হয়েও তাহলে কেমন করে মানুষ এক সূত্রে গাঁথা থাকবে? কেমন করে একটি মানচিত্রের ভেতর চিহ্নিত হবে অভিন্নতা? জাতি থেকে জাতীয়তাবোধ, সেখান থেকে আমরা পেলাম জাতিরাষ্ট্র। সাতচল্লিশের আগে ভারতবর্ষে ধর্মকে জাতি ঠাওরে বা সুবিধার জন্য মনে মনে ধরে নিয়ে, দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগ করা হলো। কিন্তু ধর্মভিত্তিক জাতি যে সোনার পাথরবাটি, তা ১৯৭১ সালেই আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি। জাতি গঠনে গণমানুষের সম্মিলিত কল্পনাশক্তির একটা ভূমিকা আছে সত্যি, কিন্তু সেটার সুবিধা নিয়ে কেউ যদি জাতি গঠনের জন্য ধর্মকে ভিত্তি বানায়, তাহলে বলতে হয় কেউ চোরাবালির ওপর প্রাসাদ নির্মাণের স্বপ্ন দেখছে। দুই যুগ পূরণ হওয়ার আগেই তাই স্বপ্নভঙ্গের ঘটনাও ঘটেছে। বাস্তবে আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছি। তখন ভেবেছি এবার অসাম্প্রদায়িক ও সমতার সমাজ গঠন করা সহজ হবে। কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হলো কি?
কেউ বলেন জাতি হলো এক কল্পিত জনগোষ্ঠী। কেউবা বলেন এটি রাষ্ট্র গঠনের জন্য এক সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তি। আমাদের ভেতর একটি সামাজিক অনুভূতি কাজ করে যে, আমরা সবাই একই দেশের নাগরিক। এখানে যদি ফাটল থাকে, তাহলে সে দেশের ললাট থেকে শনির দশা কাটে না। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যতই প্রচার করা হোক না কেন বাঙালি জাতীয়তাবাদ কিংবা বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, কোথায় গিয়ে যেন তৃতীয় আরেকটি মতবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং তারা ১৯৪৭-এর দিকে তাকিয়ে ১৯৭১ সালকে গৌণ করে দিতে চায়। সাতচল্লিশে ধর্মকে জাতি জ্ঞান করে যে বিভাজন হয়েছিল, ১৯৭১ সালে কিন্তু সেই ভ্রম কেটে যায় এবং স্পষ্টতই মানুষ অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ধারণ করে জালিমের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। কিন্তু আজ সেই তৃতীয় পক্ষ ১৯৭১ সালকে অস্বীকার করতে চায়, ১৬ ডিসেম্বরকে বিজয় দিবস হিসেবেও তারা মানতে নারাজ। এমনকি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্য এসব গুরুত্বপূর্ণ তারিখ নিয়েও কেউ কেউ অত্যন্ত আপত্তিজনক মন্তব্য করে ফেলছেন। যেটি রাষ্ট্রদ্রোহের শামিল। তবে কি জাতি হিসেবে নিজেদের ভাবার ক্ষেত্রে পাটাতনে আবার সেই ধর্মভিত্তিক চিন্তাই মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে? নয় তো কেন হঠাৎ আবার এত ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের উত্থান ঘটল? কেনইবা সমাজে ধর্মের প্রতি, ধর্মভিত্তিক রাজনীতির প্রতি এই পক্ষপাত লক্ষ করা যাচ্ছে? বাংলাদেশের সমাজে ইদানীং মানুষ নিজেদের মানব, বিশ্বনাগরিক বা একটি জাতিগোষ্ঠীর পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার বদলে ধর্মপরিচয়কে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে, সর্বাগ্রে স্থান দিচ্ছে। এই পরিবর্তন কেন ঘটল, কেমন করে ঘটল, তার হদিস সমাজবিজ্ঞানীরা ভালো করতে পারবেন। তবে এই পরিবর্তনের দায় কোনোভাবেই রাজনীতিবিদ ও শাসকশ্রেণি এড়াতে পারবে না।
যে মুক্তিযুদ্ধ আমাদের গৌরব করার মতো আত্মপরিচয় দিয়েছে, যে মুক্তিযুদ্ধ আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যে মুক্তিযুদ্ধ প্রমাণ করেছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষ এক সাগর রক্ত ঢালতে পারে অনায়াসে, সেই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আজ অত্যন্ত আপত্তিকর কথা উঠছে। তারা ফিরে যেতে চাইছে সাতচল্লিশে। কী উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ! একটি গোষ্ঠী ও কিছু তথাকথিক কনটেন্ট ক্রিয়েটর নিজেদের বিপুল অনুসারী সহযোগে মুক্তিযুদ্ধসংক্রান্ত যে ভয়ংকর মিথ্যা তথ্য প্রচার এবং চরম অপমানজনক বাক্য ব্যবহার করছে, তাতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় না হয়ে উপায় নেই। যেকোনো সুস্থ মানুষ, যাঁরা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকে সব দল-মত ও পথের ঊর্ধ্বে রেখে, যুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান, ৩০ লাখ শহীদ ও ২ লাখ নারীর সম্ভ্রমের কথা মাথায় রেখে, বাংলাদেশকে নিজেদের অস্তিত্বের অংশ মনে করেন, তাঁদের প্রত্যেকেই আজ বিমর্ষবোধ করছেন। মুক্তিযুদ্ধ যে শোষণহীন ও বৈষম্যমুক্ত সমাজের আকাঙ্ক্ষা থেকে উৎসারিত পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক ও জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে জনযুদ্ধ ছিল, সেটিকে যেন ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। দেখা যাচ্ছে, অনেকে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ও নির্যাতিতদের সংখ্যা নিয়ে কুতর্কের দোকান খুলে বসেছে। ৭ মার্চের ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান ‘জয় বাংলা’র পর ‘জয় পাকিস্তান’ বলেছিলেন কি না, সেটি আবিষ্কার করতে অস্থির হয়ে যাচ্ছে। যেন শেখ মুজিবুর রহমান ‘জয় পাকিস্তান’ বললেই গোটা ৭ মার্চের উত্তাল ভাষণ ও ভাষণ শুনতে আসা লাখো মানুষের মনের ভেতর থাকা স্বাধীনতার জন্য সমুদ্রসমান কল্লোল মিথ্যা হয়ে যায়। যদিও তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে সেদিনের বিশাল জনসভায় সশরীরের উপস্থিত থাকা অনেক বিশিষ্ট মানুষই শোনেননি ‘জয় পাকিস্তান’ বলা হচ্ছে। তাহলে এখন কেন এসব ছোটখাটো কথা নিয়ে এত সময়ক্ষেপণ? এসব করলেই কি এই জনপদের মানুষ যে পাকিস্তানি শাসকদের, বলতে গেলে খালি হাতে যুদ্ধ করে পরাজিত করেছিল, তা লুকিয়ে ফেলা যাবে? কারা এই অপচেষ্টা করছে আজকে? যেহেতু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের কাছে গৌরব ও অর্জনের ইতিহাস, তাই একে প্রশ্নবিদ্ধ করে তর্ক জুড়ে দিলে, মনে করা হচ্ছে মানুষ ওটা নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। আর এই ফাঁকে স্বার্থ উদ্ধার করে নেবে সুযোগসন্ধানীরা।
আরেকটি বিষয় নিয়ে কথা না বললেই নয়, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক কারণেই ভারত ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে গিয়েছিল। এটা ঠিক, তাদের জনতুষ্টিমূলক সংস্কৃতিতে, বিশেষ করে চলচ্চিত্রে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হিসেবে দেখানো হয়, এটা নিয়ে আপত্তি বজায় রেখেই বলতে চাই, সে সময় ভারত পূর্ববঙ্গের লাখ লাখ শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা দিয়ে যে নজির স্থাপন করেছিল, সেটি অস্বীকার করার জো নেই। তাদের আচরণ অনেক সময় বড়ভাইসুলভ ও কিছুটা আপত্তিজনক হলেও, মুক্তিযুদ্ধে তাদের যে সেনাসদস্য মারা গেছেন তা তো আর মিথ্যা নয়। কাজেই যার যেটা প্রাপ্য তাকে সেটা দিতে হয়। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা।
ইদানীং যে প্রবণতা প্রবল আকারে দেখা যাচ্ছে, সেটিকে আমি বলব, মাছির লক্ষণাক্রান্ত। ধরুন শেখ মুজিবুর রহমানের যে ভূমিকা রয়েছে মুক্তিযুদ্ধে, সেটি যেকোনো বিচারেই বাংলাদেশ গঠনের পর বাকশাল গঠনের চেয়ে অনেক বড় ব্যাপার। কিন্তু আজকাল দেখি তাঁর ওই অবদানের কথা উল্লেখ না করে কেবল বাকশাল নিয়ে আলাপ করা হয়। বাকশাল নিয়ে অবশ্যই আলাপ করা জরুরি, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর অবদানকে ছাপিয়ে সেটিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার ভেতর যে ভাষাবলয় পরিলক্ষিত হয়, যে বয়ান প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চোখে পড়ে, সেটি হুবহু বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী, তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক ও তাদের দোসরদের বয়ানের সঙ্গে মিলে যায়। স্বাধীনতালাভের অর্ধশতাব্দী পর এসেও বাংলাদেশ-বিরোধিতা এমনভাবে ফিরে আসার জন্য আমি মনে করি বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে যাঁরা ব্যবসা করেছেন তাঁরাই মূলত দায়ী। তাঁরাই আসলে খাল কেটে কুমির এনেছেন। এখন খাল খননকারীরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পলাতক, কিন্তু জনপদের মানুষ কুমিরের ভয়ে অনিশ্চিত জীবন কাটাচ্ছে।
শুধু এটুকু বলে শেষ করি, গণতন্ত্র মানে শুধু ভোট দেওয়া নয়। ভোট দেওয়ার ভেতর দিয়ে মানুষকে গণিতে পরিণত করা হয়। মাথা গোনার আরেক নাম ভোট। গণতন্ত্র তার চেয়েও বেশি কিছু। ভোট প্রদান জরুরি, কিন্তু তার চেয়েও অধিক জরুরি এই জনপদের মানুষের কাছে গণতন্ত্রের ধারণাকে স্পষ্ট করে তোলা। এটা যত দিন না হচ্ছে, তত দিন আসলে এই খাল কাটা ও কুমিরের খেলা চলতে থাকবে। কারণ, এতে খননকারী ও কুমির উভয়েরই লাভ রয়েছে।
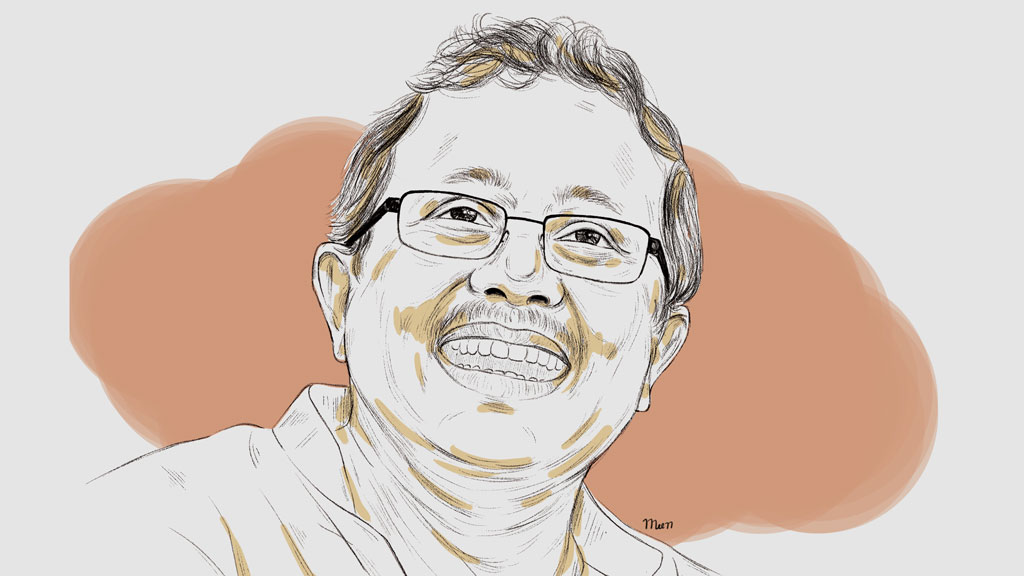
মুক্তবুদ্ধির চর্চাটা রয়ে গেল কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া তথাকথিত ‘শিক্ষিত’ মানুষের মধ্যে। এই ‘শিক্ষিত’ মানুষের বাইরে যে গোটা দেশটা ছিল, সেটা কিন্তু এই আলোয় উদ্ভাসিত হলো না। রাজনীতি থেকে একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টা খানিক স্পষ্ট হবে। এ দেশে সর্বস্ব ত্যাগ করে যারা রাজনীতি করল, তাদের সিংহভাগই ছিলেন সাম্যবাদী।
২২ অক্টোবর ২০২১
ঢাকা শহরের যানজটের সমস্যা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি দিয়েছে মেট্রোরেল। তবে এটা চালুর প্রায় দেড় বছরে এই আধুনিক গণপরিবহনব্যবস্থা মাঝে মাঝে বন্ধ হয়েছে। সেটা একটা ভাবনার বিষয়। মূলত এই সময়ের মধ্যে অন্তত ১০ বার মেট্রোরেল চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়েছে, যার বেশির ভাগই জনগণের গাফিলতির কারণে হয়েছে।
১ দিন আগে
পথকুকুর বা বিড়াল হত্যা গুরুতর অপরাধ এবং এটি জনস্বাস্থ্য ও পশু সুরক্ষার দিক থেকে একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী, এই ধরনের পশু হত্যা নিষ্ঠুরতা এবং মানবিক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
১ দিন আগে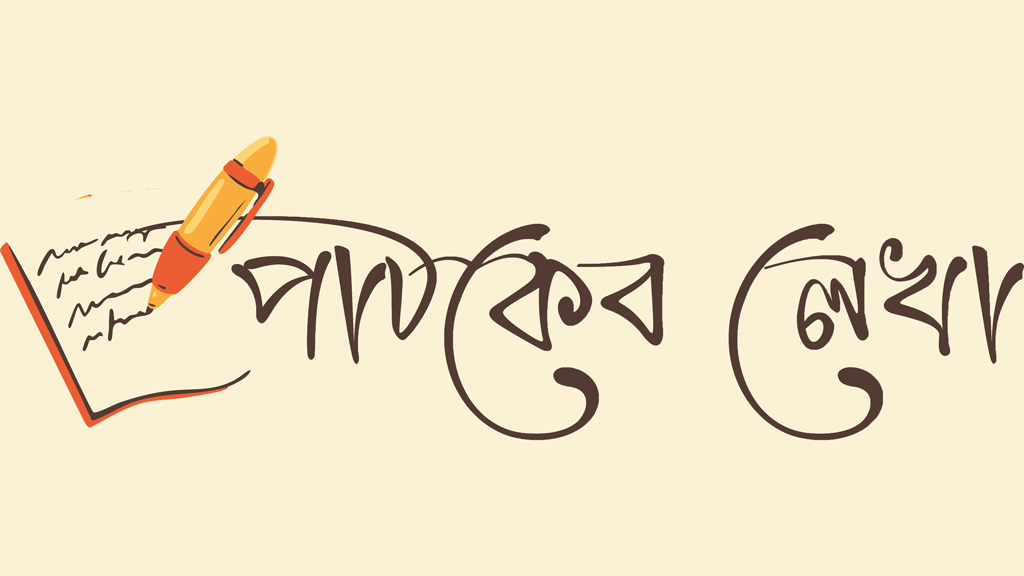
মানুষের জীবন শুধু বেঁচে থাকার নাম নয়; জীবন মানে হচ্ছে পূর্ণতার সন্ধান, মানসিক শান্তি ও শারীরিক সুস্থতার সুষম সমন্বয়। এই সমন্বয় সাধনের দুটি প্রধান উপাদান হলো সংগীত ও শরীরচর্চা। সংগীত আত্মাকে প্রশান্ত করে, মনকে উজ্জীবিত করে; আর শরীরচর্চা দেহকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখে।
১ দিন আগেঅ্যাডভোকেট সাহিদা আক্তার

পথকুকুর বা বিড়াল হত্যা গুরুতর অপরাধ এবং এটি জনস্বাস্থ্য ও পশু সুরক্ষার দিক থেকে একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী, এই ধরনের পশু হত্যা নিষ্ঠুরতা এবং মানবিক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
বাংলাদেশের আইনে পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা বা অমানবিক আচরণ রোধ করার জন্য বিশেষ বিধান রয়েছে। ১৯২০ সালে প্রণীত ‘পশু সুরক্ষা আইন’-এর মাধ্যমে পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা বা অমানবিক আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই আইনে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি জেনেবুঝে বা অবহেলায় কোনো প্রাণীকে আঘাত করে বা হত্যা করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে মামলা হতে পারে এবং শাস্তি হতে পারে।
২০১০ সালে বাংলাদেশ সরকার ‘পশু সুরক্ষা আইন সংশোধনী ২০১০’ প্রণয়ন করে, যাতে পশু হত্যা বা তাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের জন্য আরও কঠোর শাস্তি নির্ধারণ করা হয়।
পথকুকুর বা বিড়াল হত্যা হলে সাধারণত অভিযোগ দায়েরের দায়িত্ব স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন বা স্থানীয় পরিষদের ওপর পড়ে। তবে, এটি শুধু পুলিশের কাজ নয়; যেকোনো নাগরিক, পশু অধিকার রক্ষা সংস্থা বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনও এই ধরনের ঘটনার বিষয়ে মামলা করতে পারে।
যেকোনো হত্যা বা পশু নির্যাতনের ঘটনা প্রমাণ করতে হলে, পুলিশ বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রাথমিক তদন্ত করতে হবে।
স্থানীয় মানুষ বা প্রত্যক্ষদর্শীরা যদি এই হত্যার সাক্ষী হন, তাঁরা এই বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। এ ছাড়া প্রাণী অধিকার রক্ষা সংগঠনগুলোরও সক্রিয় ভূমিকা থাকে এবং তারা এগুলোর বিরুদ্ধে মামলা করতে সাহায্য করে।
পথকুকুর বা বিড়াল হত্যা করার শাস্তি বাংলাদেশে নির্দিষ্ট। ‘পশু সুরক্ষা আইন’ অনুযায়ী, যদি কোনো ব্যক্তি জেনেবুঝে বা অমানবিকভাবে কোনো প্রাণীকে আঘাত করে বা হত্যা করে, তাহলে তাকে শাস্তি প্রদান করা হয়।
জরিমানা: পশু হত্যার অপরাধে একজন ব্যক্তির ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। তবে, এটি সাধারণত প্রাথমিক শাস্তি হিসেবে নির্ধারিত হয়।
কারাদণ্ড: কিছু ক্ষেত্রে, বিশেষত যদি হত্যাটি অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে সংঘটিত হয়, তাহলে শাস্তি হিসেবে এক মাসের কারাদণ্ড হতে পারে। এই শাস্তি সংশ্লিষ্ট আদালত নির্ধারণ করবেন।
অবহেলাজনিত হত্যা: যদি কেউ অবহেলাজনিত কোনো প্রাণীকে হত্যা করে, যেমন সড়ক দুর্ঘটনার কারণে বা কোনো অজ্ঞাত কারণে, তখনো শাস্তি আরোপ করা হতে পারে। তবে, যদি হত্যা প্রমাণিত না হয়, শাস্তি কিছুটা কম হতে পারে।
বিষ প্রয়োগ: যদি কেউ প্রাণীকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করে, তাহলে শাস্তি আরও কঠোর হতে পারে। বিষ প্রয়োগ বা নিষিদ্ধ কোনো উপাদান দিয়ে প্রাণী হত্যার জন্য তিন বছরের কারাদণ্ডও হতে পারে এবং জরিমানাও আদায় করা হতে পারে।
বাংলাদেশে যদিও আইন রয়েছে, তবে পথকুকুর বা বিড়াল হত্যা সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা থাকে।
প্রমাণের অভাব: অনেক সময় পথকুকুর বা বিড়াল হত্যা প্রমাণ করা কঠিন হয়, কারণ এই ধরনের ঘটনা সাধারণত অপরিচিত জায়গায় ঘটে এবং প্রমাণ সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।
আবেগগত দ্বন্দ্ব: অনেক মানুষের কাছে পথকুকুর বা বিড়াল হত্যার গুরুত্ব তেমন অনুভূত হয় না, কারণ তারা মনে করে এসব প্রাণী কেবল ‘যাযাবর’ এবং তাদের কোনো বিশেষ মূল্য নেই। কিন্তু, এটি একটি ভুল ধারণা এবং এ ধরনের চিন্তা সমাজে পশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতার পথ প্রশস্ত করে।
আইন প্রয়োগের দুর্বলতা: অনেক সময় পুলিশের মনোযোগ এবং কার্যকর তদন্তের অভাবের কারণে এই ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয় না। পথকুকুর বা বিড়াল হত্যা বন্ধ করতে এবং তাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা কমাতে কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন:
সচেতনতা বৃদ্ধি: মানুষের মধ্যে পশুর প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা তৈরি করতে হবে। জনগণকে জানাতে হবে যে পশু হত্যা শুধু একটি অপরাধ নয়, বরং এটি মানবিকতারও প্রশ্ন।
আইনের প্রয়োগ আরও কঠোর করা: আইন প্রয়োগে গাফিলতি দূর করতে পুলিশের প্রশিক্ষণ এবং মনোযোগ বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে এই ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া যায়।
প্রাণী অধিকার রক্ষা সংগঠনের সহায়তা: প্রাণী অধিকার রক্ষা সংস্থাগুলোর তদারকি এবং কাজকে আরও সক্রিয় ও জনপ্রিয় করতে হবে।
সাহিদা আক্তার, আইনজীবী, জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ঢাকা

পথকুকুর বা বিড়াল হত্যা গুরুতর অপরাধ এবং এটি জনস্বাস্থ্য ও পশু সুরক্ষার দিক থেকে একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী, এই ধরনের পশু হত্যা নিষ্ঠুরতা এবং মানবিক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
বাংলাদেশের আইনে পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা বা অমানবিক আচরণ রোধ করার জন্য বিশেষ বিধান রয়েছে। ১৯২০ সালে প্রণীত ‘পশু সুরক্ষা আইন’-এর মাধ্যমে পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা বা অমানবিক আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই আইনে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি জেনেবুঝে বা অবহেলায় কোনো প্রাণীকে আঘাত করে বা হত্যা করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে মামলা হতে পারে এবং শাস্তি হতে পারে।
২০১০ সালে বাংলাদেশ সরকার ‘পশু সুরক্ষা আইন সংশোধনী ২০১০’ প্রণয়ন করে, যাতে পশু হত্যা বা তাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের জন্য আরও কঠোর শাস্তি নির্ধারণ করা হয়।
পথকুকুর বা বিড়াল হত্যা হলে সাধারণত অভিযোগ দায়েরের দায়িত্ব স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন বা স্থানীয় পরিষদের ওপর পড়ে। তবে, এটি শুধু পুলিশের কাজ নয়; যেকোনো নাগরিক, পশু অধিকার রক্ষা সংস্থা বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনও এই ধরনের ঘটনার বিষয়ে মামলা করতে পারে।
যেকোনো হত্যা বা পশু নির্যাতনের ঘটনা প্রমাণ করতে হলে, পুলিশ বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রাথমিক তদন্ত করতে হবে।
স্থানীয় মানুষ বা প্রত্যক্ষদর্শীরা যদি এই হত্যার সাক্ষী হন, তাঁরা এই বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। এ ছাড়া প্রাণী অধিকার রক্ষা সংগঠনগুলোরও সক্রিয় ভূমিকা থাকে এবং তারা এগুলোর বিরুদ্ধে মামলা করতে সাহায্য করে।
পথকুকুর বা বিড়াল হত্যা করার শাস্তি বাংলাদেশে নির্দিষ্ট। ‘পশু সুরক্ষা আইন’ অনুযায়ী, যদি কোনো ব্যক্তি জেনেবুঝে বা অমানবিকভাবে কোনো প্রাণীকে আঘাত করে বা হত্যা করে, তাহলে তাকে শাস্তি প্রদান করা হয়।
জরিমানা: পশু হত্যার অপরাধে একজন ব্যক্তির ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। তবে, এটি সাধারণত প্রাথমিক শাস্তি হিসেবে নির্ধারিত হয়।
কারাদণ্ড: কিছু ক্ষেত্রে, বিশেষত যদি হত্যাটি অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে সংঘটিত হয়, তাহলে শাস্তি হিসেবে এক মাসের কারাদণ্ড হতে পারে। এই শাস্তি সংশ্লিষ্ট আদালত নির্ধারণ করবেন।
অবহেলাজনিত হত্যা: যদি কেউ অবহেলাজনিত কোনো প্রাণীকে হত্যা করে, যেমন সড়ক দুর্ঘটনার কারণে বা কোনো অজ্ঞাত কারণে, তখনো শাস্তি আরোপ করা হতে পারে। তবে, যদি হত্যা প্রমাণিত না হয়, শাস্তি কিছুটা কম হতে পারে।
বিষ প্রয়োগ: যদি কেউ প্রাণীকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করে, তাহলে শাস্তি আরও কঠোর হতে পারে। বিষ প্রয়োগ বা নিষিদ্ধ কোনো উপাদান দিয়ে প্রাণী হত্যার জন্য তিন বছরের কারাদণ্ডও হতে পারে এবং জরিমানাও আদায় করা হতে পারে।
বাংলাদেশে যদিও আইন রয়েছে, তবে পথকুকুর বা বিড়াল হত্যা সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা থাকে।
প্রমাণের অভাব: অনেক সময় পথকুকুর বা বিড়াল হত্যা প্রমাণ করা কঠিন হয়, কারণ এই ধরনের ঘটনা সাধারণত অপরিচিত জায়গায় ঘটে এবং প্রমাণ সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।
আবেগগত দ্বন্দ্ব: অনেক মানুষের কাছে পথকুকুর বা বিড়াল হত্যার গুরুত্ব তেমন অনুভূত হয় না, কারণ তারা মনে করে এসব প্রাণী কেবল ‘যাযাবর’ এবং তাদের কোনো বিশেষ মূল্য নেই। কিন্তু, এটি একটি ভুল ধারণা এবং এ ধরনের চিন্তা সমাজে পশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতার পথ প্রশস্ত করে।
আইন প্রয়োগের দুর্বলতা: অনেক সময় পুলিশের মনোযোগ এবং কার্যকর তদন্তের অভাবের কারণে এই ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয় না। পথকুকুর বা বিড়াল হত্যা বন্ধ করতে এবং তাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা কমাতে কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন:
সচেতনতা বৃদ্ধি: মানুষের মধ্যে পশুর প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা তৈরি করতে হবে। জনগণকে জানাতে হবে যে পশু হত্যা শুধু একটি অপরাধ নয়, বরং এটি মানবিকতারও প্রশ্ন।
আইনের প্রয়োগ আরও কঠোর করা: আইন প্রয়োগে গাফিলতি দূর করতে পুলিশের প্রশিক্ষণ এবং মনোযোগ বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে এই ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া যায়।
প্রাণী অধিকার রক্ষা সংগঠনের সহায়তা: প্রাণী অধিকার রক্ষা সংস্থাগুলোর তদারকি এবং কাজকে আরও সক্রিয় ও জনপ্রিয় করতে হবে।
সাহিদা আক্তার, আইনজীবী, জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ঢাকা
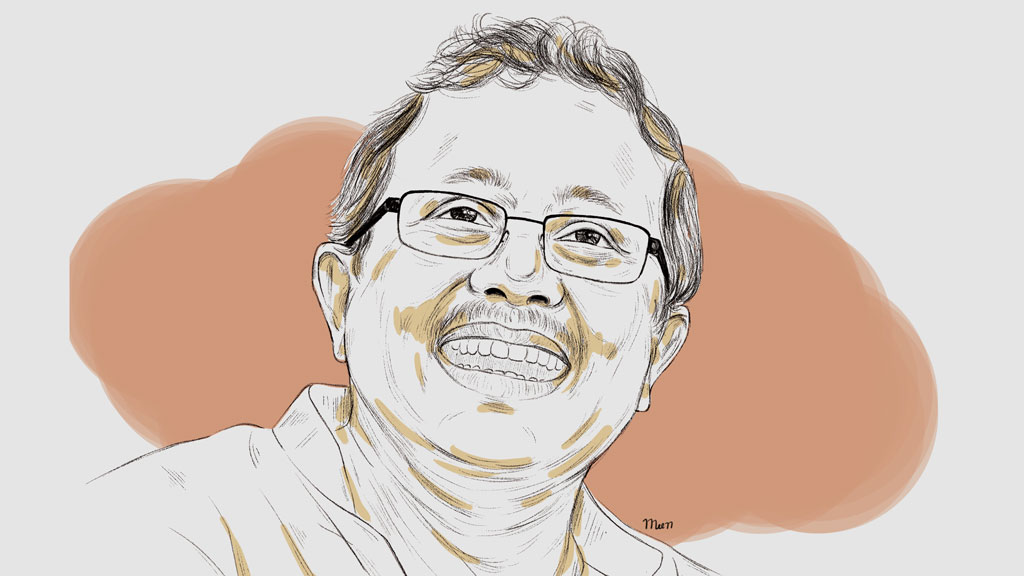
মুক্তবুদ্ধির চর্চাটা রয়ে গেল কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া তথাকথিত ‘শিক্ষিত’ মানুষের মধ্যে। এই ‘শিক্ষিত’ মানুষের বাইরে যে গোটা দেশটা ছিল, সেটা কিন্তু এই আলোয় উদ্ভাসিত হলো না। রাজনীতি থেকে একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টা খানিক স্পষ্ট হবে। এ দেশে সর্বস্ব ত্যাগ করে যারা রাজনীতি করল, তাদের সিংহভাগই ছিলেন সাম্যবাদী।
২২ অক্টোবর ২০২১
ঢাকা শহরের যানজটের সমস্যা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি দিয়েছে মেট্রোরেল। তবে এটা চালুর প্রায় দেড় বছরে এই আধুনিক গণপরিবহনব্যবস্থা মাঝে মাঝে বন্ধ হয়েছে। সেটা একটা ভাবনার বিষয়। মূলত এই সময়ের মধ্যে অন্তত ১০ বার মেট্রোরেল চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়েছে, যার বেশির ভাগই জনগণের গাফিলতির কারণে হয়েছে।
১ দিন আগে
আমরা এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখি, যেখানে নানা ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গের মানুষ পরস্পরের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করবে। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় জারিত হয়ে সমাজের বৈচিত্র্যকে উদ্যাপন করবে। আমরা এমন এক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখি, যে রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের মানবিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখবে।
১ দিন আগে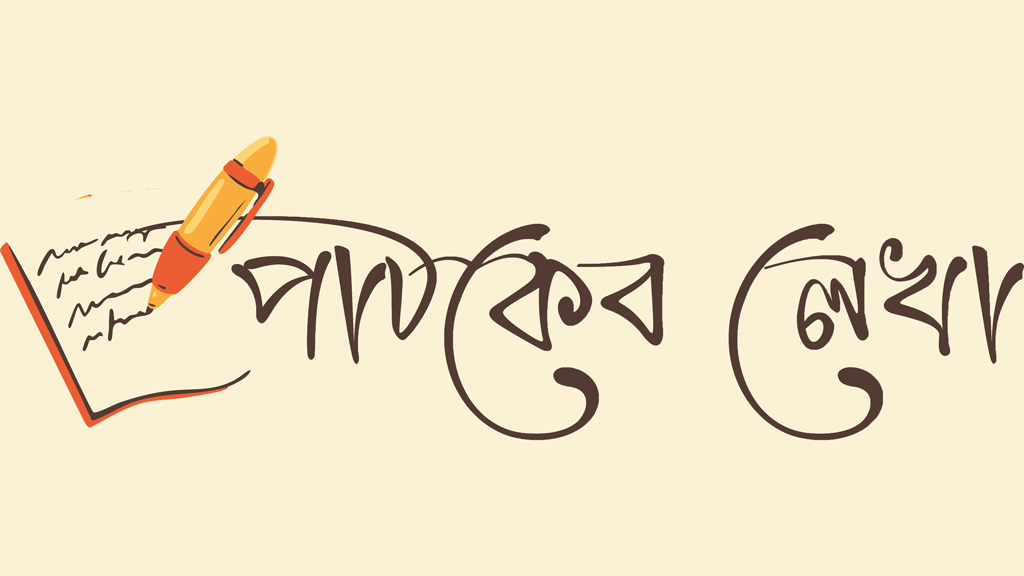
মানুষের জীবন শুধু বেঁচে থাকার নাম নয়; জীবন মানে হচ্ছে পূর্ণতার সন্ধান, মানসিক শান্তি ও শারীরিক সুস্থতার সুষম সমন্বয়। এই সমন্বয় সাধনের দুটি প্রধান উপাদান হলো সংগীত ও শরীরচর্চা। সংগীত আত্মাকে প্রশান্ত করে, মনকে উজ্জীবিত করে; আর শরীরচর্চা দেহকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখে।
১ দিন আগেসুধীর বরণ মাঝি
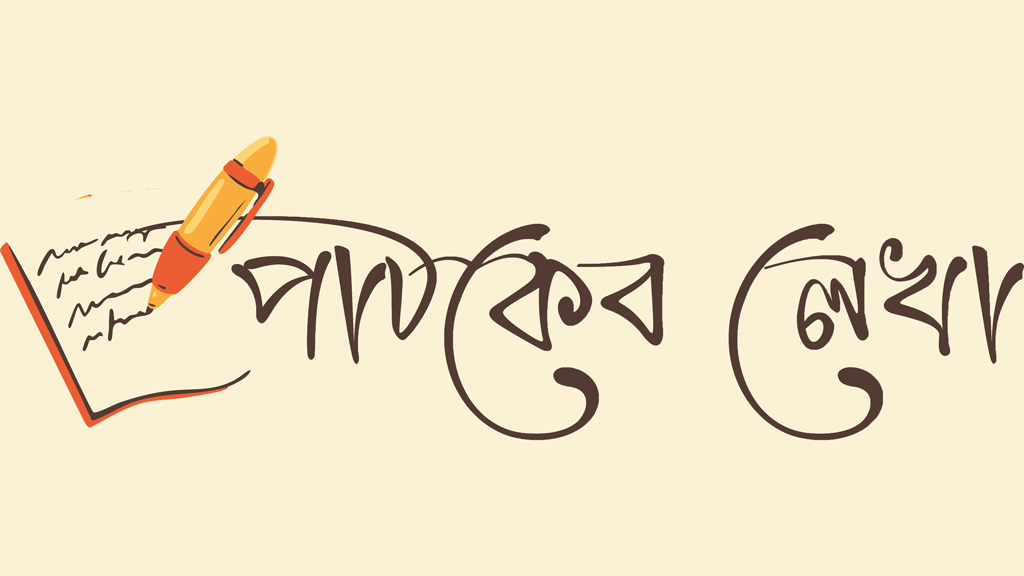
মানুষের জীবন শুধু বেঁচে থাকার নাম নয়; জীবন মানে হচ্ছে পূর্ণতার সন্ধান, মানসিক শান্তি ও শারীরিক সুস্থতার সুষম সমন্বয়। এই সমন্বয় সাধনের দুটি প্রধান উপাদান হলো সংগীত ও শরীরচর্চা। সংগীত আত্মাকে প্রশান্ত করে, মনকে উজ্জীবিত করে; আর শরীরচর্চা দেহকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখে। এই দুইয়ের মিলিত প্রভাবেই গড়ে ওঠে এক পরিপূর্ণ, ভারসাম্যপূর্ণ ও অর্থবহ জীবন। যে সমাজে মানুষ সংগীতের মাধুর্য ও শরীরচর্চার শৃঙ্খলাকে গ্রহণ করে, সে সমাজ হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত, সৃজনশীল ও মানবিক গুণে পরিপূর্ণ।
সংগীত মানুষের হৃদয়ের ভাষা। ভাষা যখন থেমে যায়, তখন সুরই হয়ে ওঠে প্রকাশের মাধ্যম। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ তার অনুভূতি, আনন্দ, দুঃখ, প্রেম, প্রার্থনা কিংবা প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে সংগীতকে বেছে নিয়েছে। প্রকৃতির শব্দের ভেতরেও সংগীতের ছোঁয়া—বৃষ্টির ঝরঝর শব্দ, পাখির কলতান, ঢেউয়ের মৃদু গর্জন—সবই জীবনের ছন্দের বহিঃপ্রকাশ। এই ছন্দ থেকেই মানুষ খুঁজে পেয়েছে সংগীতের রূপ, যা তাকে দিয়েছে মানসিক মুক্তি, সৃষ্টিশীলতার প্রেরণা ও আত্মার প্রশান্তি। আজও যখন কোনো মানুষ ক্লান্ত, উদ্বিগ্ন বা নিঃসঙ্গ হয়, তখন সংগীতই তার একমাত্র সান্ত্বনা হয়ে ওঠে।
মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখা যায়, সংগীত মানুষের মানসিক ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সংগীত থেরাপি আজ বিশ্বজুড়ে একটি স্বীকৃত চিকিৎসা পদ্ধতি। মানসিক অবসাদ, হতাশা বা উদ্বেগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা যখন সংগীতের ছন্দে নিজেকে মেলে ধরতে পারে, তখন তাদের মস্তিষ্কে ডোপামিন ও সেরোটোনিনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, যা মানসিক প্রশান্তি এনে দেয়। তাই সংগীত শুধু বিনোদন নয়, এটি এক গভীর মানসিক ও আত্মিক চিকিৎসা। শিশুরা যখন ছোটবেলা থেকেই সংগীতচর্চায় যুক্ত হয়, তখন তাদের মনোযোগ, স্মৃতিশক্তি, শৃঙ্খলা ও আবেগময় সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ সংগীত শুধু মনোরঞ্জন নয়, এটি চরিত্র গঠনেরও সহায়কশক্তি।
অন্যদিকে, শরীরচর্চা মানুষের শারীরিক ও মানসিক উভয় বিকাশের অন্যতম প্রধান অনুঘটক। একটি লাতিন প্রবাদ হলো, ‘সুস্থ দেহে সুস্থ মন’। শারীরিক সুস্থতা ছাড়া মানসিক উৎকর্ষ সম্ভব নয়। নিয়মিত শরীরচর্চা হৃদ্যন্ত্রকে শক্তিশালী করে, রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়, শরীরে অক্সিজেনের প্রবাহ উন্নত করে এবং বিভিন্ন রোগপ্রতিরোধে সহায়তা করে। কিন্তু এর থেকেও বড় কথা হলো, শরীরচর্চা মানুষকে দেয় আত্মনিয়ন্ত্রণ, অধ্যবসায়, সাহস ও ইতিবাচক মনোভাব। প্রতিদিনের শরীরচর্চা যেন জীবনের এক ধ্রুব অনুশাসন, যা আমাদের শেখায় পরিশ্রম, ধৈর্য ও শৃঙ্খলার মূল্য।
আজকের যুগে যখন প্রযুক্তিনির্ভর জীবন মানুষকে ক্রমেই নিস্তেজ ও স্থবির করে তুলছে, তখন শরীরচর্চা আমাদের জাগ্রত রাখে। অফিস, স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়—সব জায়গায় এখন বসে থাকার প্রবণতা বেড়েছে। ফলে স্থূলতা, ডায়াবেটিস, হৃদ্রোগ, বিষণ্নতা ইত্যাদি নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠছে। নিয়মিত ব্যায়াম, হাঁটা, দৌড়ানো, সাঁতার বা যোগব্যায়াম কেবল শরীরকে সুস্থ রাখে না, মানসিক চাপও কমায়।
সংগীত ও শরীরচর্চার মধ্যে এক গভীর সম্পর্কও রয়েছে। যেমন যোগব্যায়াম বা ধ্যানের সময় সুমধুর সংগীত মনকে কেন্দ্রীভূত করতে সাহায্য করে। আবার অনেক ব্যায়াম বা ক্রীড়া কার্যক্রমে ছন্দময় সংগীত শরীরকে উদ্দীপিত করে তোলে। জিমে ব্যায়াম করার সময় বা দৌড়ানোর সময় অনুপ্রেরণাদায়ক গান শুনলে শরীরে নতুন শক্তির সঞ্চার হয়।
শিক্ষার ক্ষেত্রেও সংগীত ও শরীরচর্চার ভূমিকা অপরিসীম। আধুনিক শিক্ষা শুধু বইয়ের জ্ঞান নয়; এটি দেহ, মন ও বুদ্ধির সমন্বিত বিকাশ চায়। তাই বিদ্যালয়ে সংগীত শিক্ষা ও শারীরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। সংগীত শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তি ও নান্দনিক বোধকে জাগিয়ে তোলে, আর শরীরচর্চা তাকে করে তোলে সুস্থ, পরিশ্রমী ও আত্মনিয়ন্ত্রিত। আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতিতেও এই দুই বিষয়কে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কারণ এ দুটি ছাড়া পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব গঠন অসম্ভব।
সংগীত ও শরীরচর্চা জীবনের দুটি অনিবার্য স্তম্ভ। একদিকে সংগীত আত্মাকে দেয় শান্তি, অন্যদিকে শরীরচর্চা দেহে আনে শক্তি। এই দুইয়ের সমন্বয়ই আমাদের দেয় জীবনকে উপভোগ করার সক্ষমতা। যে ব্যক্তি সংগীতের সৌন্দর্য বোঝে ও নিয়মিত শরীরচর্চা করে, সে শুধু দীর্ঘজীবীই নয়, প্রকৃত অর্থে সুখী মানুষ। জীবন তখন আর নিছক বেঁচে থাকা নয়; বরং এক সুরেলা, উদ্দীপনাময়, অর্থবহ যাত্রা। তাই বলা যায়, সংগীত ও শরীরচর্চা ছাড়া জীবন বোধহীন, প্রাণহীন এক জড় অস্তিত্বমাত্র।
শিক্ষক, হাইমচর সরকারি মহাবিদ্যালয়, চাঁদপুর
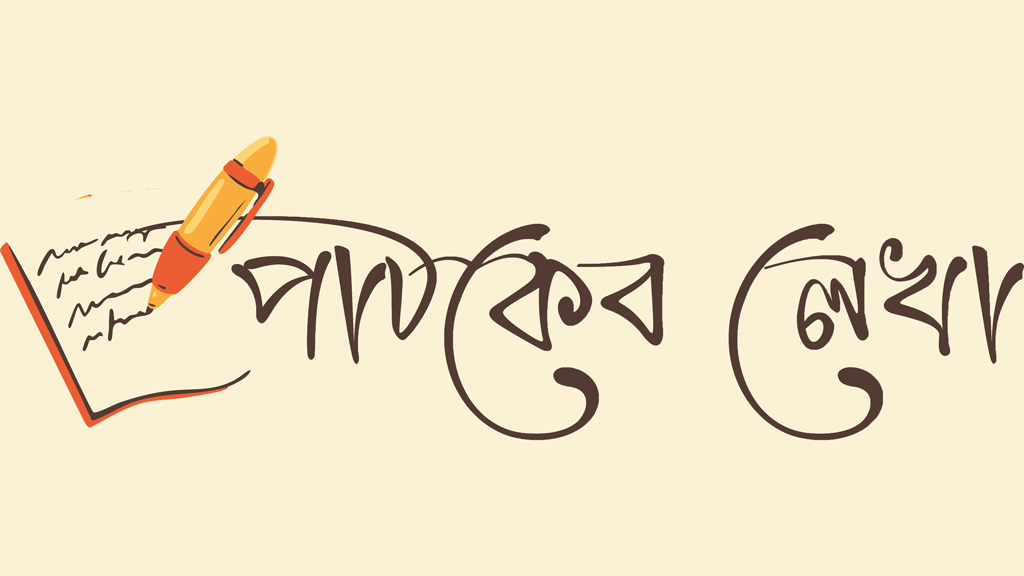
মানুষের জীবন শুধু বেঁচে থাকার নাম নয়; জীবন মানে হচ্ছে পূর্ণতার সন্ধান, মানসিক শান্তি ও শারীরিক সুস্থতার সুষম সমন্বয়। এই সমন্বয় সাধনের দুটি প্রধান উপাদান হলো সংগীত ও শরীরচর্চা। সংগীত আত্মাকে প্রশান্ত করে, মনকে উজ্জীবিত করে; আর শরীরচর্চা দেহকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখে। এই দুইয়ের মিলিত প্রভাবেই গড়ে ওঠে এক পরিপূর্ণ, ভারসাম্যপূর্ণ ও অর্থবহ জীবন। যে সমাজে মানুষ সংগীতের মাধুর্য ও শরীরচর্চার শৃঙ্খলাকে গ্রহণ করে, সে সমাজ হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত, সৃজনশীল ও মানবিক গুণে পরিপূর্ণ।
সংগীত মানুষের হৃদয়ের ভাষা। ভাষা যখন থেমে যায়, তখন সুরই হয়ে ওঠে প্রকাশের মাধ্যম। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ তার অনুভূতি, আনন্দ, দুঃখ, প্রেম, প্রার্থনা কিংবা প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে সংগীতকে বেছে নিয়েছে। প্রকৃতির শব্দের ভেতরেও সংগীতের ছোঁয়া—বৃষ্টির ঝরঝর শব্দ, পাখির কলতান, ঢেউয়ের মৃদু গর্জন—সবই জীবনের ছন্দের বহিঃপ্রকাশ। এই ছন্দ থেকেই মানুষ খুঁজে পেয়েছে সংগীতের রূপ, যা তাকে দিয়েছে মানসিক মুক্তি, সৃষ্টিশীলতার প্রেরণা ও আত্মার প্রশান্তি। আজও যখন কোনো মানুষ ক্লান্ত, উদ্বিগ্ন বা নিঃসঙ্গ হয়, তখন সংগীতই তার একমাত্র সান্ত্বনা হয়ে ওঠে।
মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখা যায়, সংগীত মানুষের মানসিক ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সংগীত থেরাপি আজ বিশ্বজুড়ে একটি স্বীকৃত চিকিৎসা পদ্ধতি। মানসিক অবসাদ, হতাশা বা উদ্বেগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা যখন সংগীতের ছন্দে নিজেকে মেলে ধরতে পারে, তখন তাদের মস্তিষ্কে ডোপামিন ও সেরোটোনিনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, যা মানসিক প্রশান্তি এনে দেয়। তাই সংগীত শুধু বিনোদন নয়, এটি এক গভীর মানসিক ও আত্মিক চিকিৎসা। শিশুরা যখন ছোটবেলা থেকেই সংগীতচর্চায় যুক্ত হয়, তখন তাদের মনোযোগ, স্মৃতিশক্তি, শৃঙ্খলা ও আবেগময় সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ সংগীত শুধু মনোরঞ্জন নয়, এটি চরিত্র গঠনেরও সহায়কশক্তি।
অন্যদিকে, শরীরচর্চা মানুষের শারীরিক ও মানসিক উভয় বিকাশের অন্যতম প্রধান অনুঘটক। একটি লাতিন প্রবাদ হলো, ‘সুস্থ দেহে সুস্থ মন’। শারীরিক সুস্থতা ছাড়া মানসিক উৎকর্ষ সম্ভব নয়। নিয়মিত শরীরচর্চা হৃদ্যন্ত্রকে শক্তিশালী করে, রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়, শরীরে অক্সিজেনের প্রবাহ উন্নত করে এবং বিভিন্ন রোগপ্রতিরোধে সহায়তা করে। কিন্তু এর থেকেও বড় কথা হলো, শরীরচর্চা মানুষকে দেয় আত্মনিয়ন্ত্রণ, অধ্যবসায়, সাহস ও ইতিবাচক মনোভাব। প্রতিদিনের শরীরচর্চা যেন জীবনের এক ধ্রুব অনুশাসন, যা আমাদের শেখায় পরিশ্রম, ধৈর্য ও শৃঙ্খলার মূল্য।
আজকের যুগে যখন প্রযুক্তিনির্ভর জীবন মানুষকে ক্রমেই নিস্তেজ ও স্থবির করে তুলছে, তখন শরীরচর্চা আমাদের জাগ্রত রাখে। অফিস, স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়—সব জায়গায় এখন বসে থাকার প্রবণতা বেড়েছে। ফলে স্থূলতা, ডায়াবেটিস, হৃদ্রোগ, বিষণ্নতা ইত্যাদি নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠছে। নিয়মিত ব্যায়াম, হাঁটা, দৌড়ানো, সাঁতার বা যোগব্যায়াম কেবল শরীরকে সুস্থ রাখে না, মানসিক চাপও কমায়।
সংগীত ও শরীরচর্চার মধ্যে এক গভীর সম্পর্কও রয়েছে। যেমন যোগব্যায়াম বা ধ্যানের সময় সুমধুর সংগীত মনকে কেন্দ্রীভূত করতে সাহায্য করে। আবার অনেক ব্যায়াম বা ক্রীড়া কার্যক্রমে ছন্দময় সংগীত শরীরকে উদ্দীপিত করে তোলে। জিমে ব্যায়াম করার সময় বা দৌড়ানোর সময় অনুপ্রেরণাদায়ক গান শুনলে শরীরে নতুন শক্তির সঞ্চার হয়।
শিক্ষার ক্ষেত্রেও সংগীত ও শরীরচর্চার ভূমিকা অপরিসীম। আধুনিক শিক্ষা শুধু বইয়ের জ্ঞান নয়; এটি দেহ, মন ও বুদ্ধির সমন্বিত বিকাশ চায়। তাই বিদ্যালয়ে সংগীত শিক্ষা ও শারীরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। সংগীত শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তি ও নান্দনিক বোধকে জাগিয়ে তোলে, আর শরীরচর্চা তাকে করে তোলে সুস্থ, পরিশ্রমী ও আত্মনিয়ন্ত্রিত। আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতিতেও এই দুই বিষয়কে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কারণ এ দুটি ছাড়া পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব গঠন অসম্ভব।
সংগীত ও শরীরচর্চা জীবনের দুটি অনিবার্য স্তম্ভ। একদিকে সংগীত আত্মাকে দেয় শান্তি, অন্যদিকে শরীরচর্চা দেহে আনে শক্তি। এই দুইয়ের সমন্বয়ই আমাদের দেয় জীবনকে উপভোগ করার সক্ষমতা। যে ব্যক্তি সংগীতের সৌন্দর্য বোঝে ও নিয়মিত শরীরচর্চা করে, সে শুধু দীর্ঘজীবীই নয়, প্রকৃত অর্থে সুখী মানুষ। জীবন তখন আর নিছক বেঁচে থাকা নয়; বরং এক সুরেলা, উদ্দীপনাময়, অর্থবহ যাত্রা। তাই বলা যায়, সংগীত ও শরীরচর্চা ছাড়া জীবন বোধহীন, প্রাণহীন এক জড় অস্তিত্বমাত্র।
শিক্ষক, হাইমচর সরকারি মহাবিদ্যালয়, চাঁদপুর
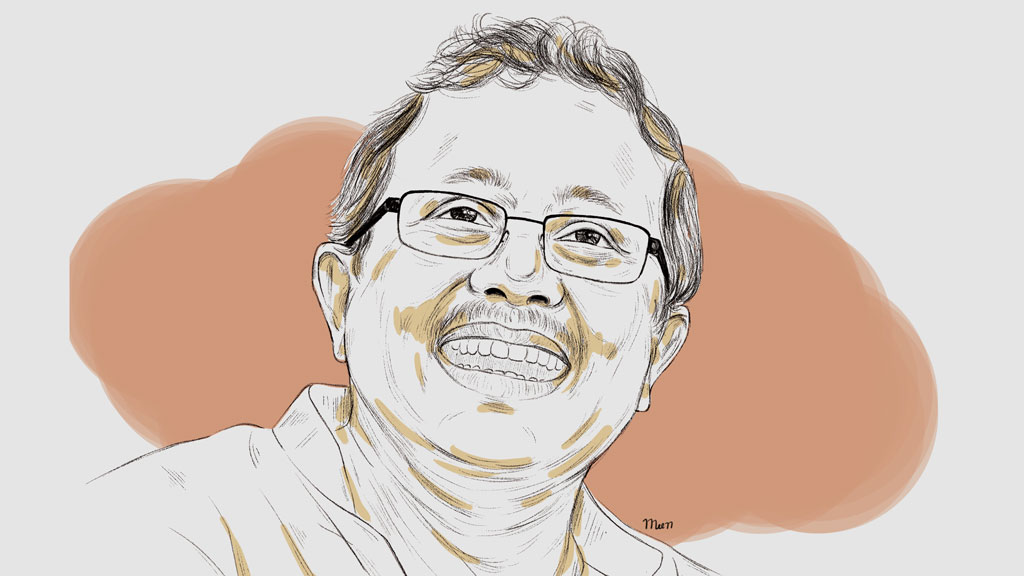
মুক্তবুদ্ধির চর্চাটা রয়ে গেল কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া তথাকথিত ‘শিক্ষিত’ মানুষের মধ্যে। এই ‘শিক্ষিত’ মানুষের বাইরে যে গোটা দেশটা ছিল, সেটা কিন্তু এই আলোয় উদ্ভাসিত হলো না। রাজনীতি থেকে একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টা খানিক স্পষ্ট হবে। এ দেশে সর্বস্ব ত্যাগ করে যারা রাজনীতি করল, তাদের সিংহভাগই ছিলেন সাম্যবাদী।
২২ অক্টোবর ২০২১
ঢাকা শহরের যানজটের সমস্যা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি দিয়েছে মেট্রোরেল। তবে এটা চালুর প্রায় দেড় বছরে এই আধুনিক গণপরিবহনব্যবস্থা মাঝে মাঝে বন্ধ হয়েছে। সেটা একটা ভাবনার বিষয়। মূলত এই সময়ের মধ্যে অন্তত ১০ বার মেট্রোরেল চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়েছে, যার বেশির ভাগই জনগণের গাফিলতির কারণে হয়েছে।
১ দিন আগে
আমরা এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখি, যেখানে নানা ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গের মানুষ পরস্পরের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করবে। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় জারিত হয়ে সমাজের বৈচিত্র্যকে উদ্যাপন করবে। আমরা এমন এক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখি, যে রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের মানবিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখবে।
১ দিন আগে
পথকুকুর বা বিড়াল হত্যা গুরুতর অপরাধ এবং এটি জনস্বাস্থ্য ও পশু সুরক্ষার দিক থেকে একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী, এই ধরনের পশু হত্যা নিষ্ঠুরতা এবং মানবিক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
১ দিন আগে