বিভুরঞ্জন সরকার
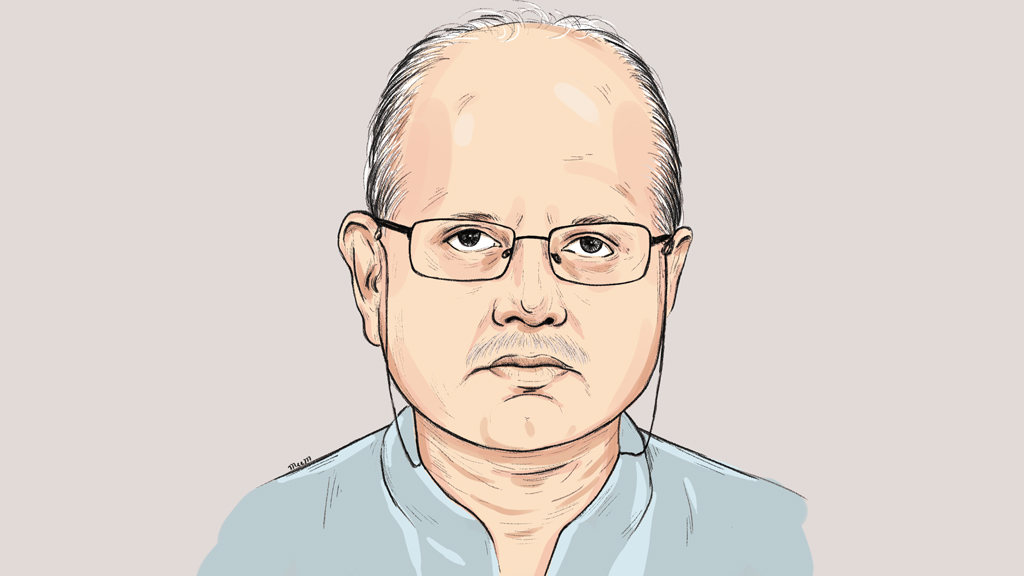
দত্তবাড়ির পর বোদার চন্দবাড়ির কথা না লিখলে চলে না। দত্তবাড়ির মতো চন্দবাড়িতেও আছে আমার সহপাঠী ও বন্ধু। আবার দত্ত ও চন্দবাড়ির মধ্যেও আছে পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক।
বোদার থানাপাড়া এখন অনেক বড়। অনেক বাড়িঘর। আর আমাদের ছোটবেলায় থানা, ওয়াপদা অফিস এবং একদিকে চন্দবাড়ি, অন্যদিকে হকিকুল ডাক্তার সাহেবের বাড়ি ছাড়া আর কোনো বাড়িঘর ছিল বলে মনে পড়ে না।
উমেশ চন্দ্র চন্দ ও মন্মথ চন্দ দুই ভাই। উমেশ চন্দের দুই ছেলে সুধীর চন্দ্র চন্দ ও অধীর চন্দ্র চন্দ। উমেশ বাবুকে আমি দেখিনি। তবে মন্মথ বাবুকে দেখেছি। তাঁর বাড়ি অবশ্য থানাপাড়ায় ছিল না। তাঁর বাড়ি বাজার থেকে সিরাজ সরকার সাহেবের বাড়ি যেতে আগে পড়ত। হাতের বাঁয়ে। এখনো আছে সেই বাড়ি। মন্মথ চন্দের মেয়ে ছায়াদিকে বিয়ে করেন দত্তবাড়ির শিবেন দত্ত।
উমেশ চন্দের দুই ছেলের থানাপাড়ার বাসায় আমার ছিল অবাধ যাতায়াত। বড় ছেলে সুধীর চন্দের তিন ছেলে ও তিন মেয়ে। শিবানী চন্দ, কল্যাণী চন্দ (সুনু), সুধাংশু চন্দ (স্বপন), নারায়ণী চন্দ (বেণু), হিমাংশু চন্দ (তপন/তপু) ও প্রবীর চন্দ (নয়ন)। শিবানী চন্দকে আমি দেখিনি। তিনি অবিভক্ত ভারতের জলপাইগুড়িতে মামাবাড়িতে একেবারে ছোট থেকেই বড় হয়েছেন। আর দেশে আসেননি। অন্য সবাই বোদায় ছিলেন বা আছেন। এর মধ্যে স্বপনদা অকালপ্রয়াত। সুনুদি, স্বপনদা ও বেণু আমার বড়। তবে বড় হলেও বেণু আর তপু আমার সহপাঠী। পরে সম্ভবত ক্লাস ফাইভ থেকে বেণু আমার ‘জুনিয়র’ হয়ে যায়। আর তপু হয়ে ওঠে আমার প্রিয় বন্ধুদের একজন। আমি, তপু ও দত্তবাড়ির বিজন—এই তিনজন ছিলাম (দেখা-সাক্ষাৎ কম হলেও এখনো আছি) ‘এক দেহ, এক প্রাণ’। কত কথাই না মনে পড়ছে। একটি ঘটনার কথা না বলে পারছি না। হাইস্কুলে পড়ার সময় আমরা কয়েকজন (এর মধ্যে বিজন, তপু আর আমি কমন) প্রতি বৃহস্পতিবার টিফিনের সময় স্কুল পালিয়ে ঠাকুরগাঁওয়ে যেতাম সিনেমা দেখার জন্য। শুক্রবার নতুন ছবি শুরু হতো, কাজেই বৃহস্পতিবার আমরা বিদায়ী ছবিটা দেখতাম। বলাকা টকিজ নামের সিনেমা হলটির মালিক ছিলেন মির্জা রুহুল আমিন (চখা মিয়া নামে সমধিক পরিচিত)। তিনি ছিলেন বর্তমান বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বাবা এবং সাবেক সেনাপ্রধান ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সাবেক সদস্য লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মাহবুবুর রহমানের শ্বশুর।
স্কুল থেকে পালিয়ে আমরা একত্রিত হতাম সাতখামারে শামসুদ্দিন ডাক্তার সাহেবের ডিসপেনসারিতে। দুপুরবেলা ওটা ফাঁকা থাকত। আমার বাড়ি ছিল তার পাশেই। ওটা ছিল ঠাকুরগাঁওয়ে যাওয়ার সড়কের একেবারে লাগোয়া। বাসস্ট্যান্ড থেকে বাসে উঠলে কেউ দেখে ফেলতে পারে—এই আশঙ্কা থেকেই আমরা একটু এগিয়ে গিয়ে বাসে উঠতাম। প্রবাদ আছে, ‘যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে রাত হয়’। একদিন আমাদের শামসুদ্দিন ডাক্তার চাচার ডিসপেনসারিতে জটলারত অবস্থায় দেখতে পান ডা. ফয়জুল করিম, আমাদের মশিয়ারের (মশিয়ার রহমান, এখন পল্লি কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা) বাবা। আমরা যে স্কুল পালিয়ে ওখানে সমবেত হয়েছি, সেটা তিনি বুঝতে পারেন। তিনি সম্ভবত রোগী দেখে সাইকেলে চেপে ফিরছিলেন। তিনি নিজে আমাদের কিছু বললেন না। তবে বাজারে গিয়ে তপুর বাবা সুধীর কাকুকে বিষয়টি অবগত করেন। কাকু দ্রুত ছুটে আসেন এবং আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই তপুকে পাকড়াও করে পায়ের কাবলি স্যান্ডেল দিয়ে বেদম পেটাতে থাকেন। তপু চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে মিনতি করে বলতে থাকে, ‘দোহাই বাবা, আর মেরো না।’ কাকু কোনো কথা শোনেন না। একপর্যায়ে পিটিয়ে ক্লান্ত হয়ে আমাদের সবাইকে শাসিয়ে তিনি চলে যান। আমরা ভাবলাম, অত পিটুনি খেয়ে তপু হয়তো আর সিনেমা দেখতে যাবে না। কিন্তু আমাদের অবাক করে তপু বলল, ‘মার তো খেয়েই ফেলেছি, তাহলে আর সিনেমা দেখা থেকে বঞ্চিত হব কেন?’
তপু ছিল আমাদের বন্ধুদের মধ্য সবচেয়ে ছোটখাটো। তাই ওকে নিয়ে কত ধরনের কাণ্ডই না আমরা করতাম। সেই তপু, হিমাংশু চন্দ এখন ঠাকুরগাঁওয়ে একটি বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) প্রধান নির্বাহী। তপুও খুব সরল মনের সাদাসিধে মানুষ। জীবনে টাকা-পয়সা যেমন উপার্জন করেছে, তেমন খরচও করেছে। ওর বাবা, আমাদের সুধীর কাকুও ছিলেন অত্যন্ত দরাজ দিল মানুষ। আমি তাঁর কাছ থেকে যে স্নেহ-ভালোবাসা পেয়েছি, তা বলে শেষ করা যাবে না।
আমার বন্ধু তপুর বাবা, আমাদের সুধীর কাকু ছিলেন আমার দেখা ‘অসাধারণ’ মানুষদের একজন। দেখতে ছিলেন সুদর্শন। অমন উন্নত নাক, গৌর বর্ণ, মাথা উঁচু করে হাঁটাচলা করা; দেখলেই মনের মধ্যে একটি সমীহ ভাব চলে আসত। তাঁকে আমরা একধরনের ভয়মিশ্রিত সমীহই করতাম। একেবারে ছোটবেলায় এড়িয়ে চলতাম। আস্তে আস্তে যতই তাঁর নৈকট্য লাভ করেছি, ততই মনে হয়েছে তাঁর মনের ভেতরটা কত নরম। পরিণত বয়সেও তিনি ঝুনা নারকেল না হয়ে কচি ডাবের মতোই ছিলেন।
প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন একজন নামকরা ফুটবল খেলোয়াড়। জলপাইগুড়ি জেলায়ও তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। আমরা ছোটবেলায়ও তাঁকে বোদা হাইস্কুল মাঠে শৌখিন খেলোয়াড় হিসেবে খেলতে দেখেছি। সুধীর কাকু, ডা. ফয়জুল চাচারা মাঠে নামলে জমে উঠত খেলা। তরুণদের উৎসাহিত করার জন্যই সে সময় তাঁরা নিয়মিত মাঠে যেতেন।
তপুর মা, মানে আমাদের কাকি মারা যান সম্ভবত ১৯৫৭ সালে। আমি হয়তো তাঁকে দেখিওনি। শুনেছি নয়নের তখন মাত্র দেড় বছর বয়স। তপুর তিন-সাড়ে তিন। কাজেই মায়ের কোনো স্মৃতি ওদের মনে থাকার কথা নয়। ওরা প্রকৃতপক্ষে মাতৃস্নেহে বড় হয়েছে দিদিমার কাছে। দিদিমা সরজুবালা দেবী ছিলেন সুধীর কাকুর মাসিমা। তিনি বাল্যবিধবা। বিয়ের অল্প পরই স্বামীহারা হয়ে সুধীর কাকুর সংসারে স্থায়ী হয়েছিলেন। তপু ও নয়ন এই দিদিমার কোলেপিঠে মানুষ। তাই তিনি ছিলেন ওদের মা, দিদিমা নয়!
এই মহীয়সী নারীকে যাঁরা না দেখেছেন, তাঁরা তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কোনো ধারণা করতে পারবেন না। তিনিই কার্যত চন্দবাড়িতে অভিভাবক ছিলেন। তাঁর ছায়া-মায়ায় তপুরা ভাইবোন মানুষ হয়েছে। আরও একজন তপুদের মায়ের অভাব পূরণে বড় ভূমিকা রেখেছেন—তপুদের কাকিমা, অধীর কাকুর স্ত্রী। এই কাকিমার নাম রেখা রানী চন্দ। নিজের তিন মেয়ে ও দুই ছেলেসন্তানের সঙ্গে ভাশুরের সন্তানদেরও তিনি অকৃপণ স্নেহ-ভালোবাসা দিয়েছেন।
সুধীর কাকুর স্ত্রীবিয়োগের পর অনেকে তাঁকে আবার বিয়ে করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তখন এমন রেওয়াজ ছিল, কিন্তু প্রথম স্ত্রীর প্রতি গভীর ভালোবাসা তাঁকে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণে নিরুৎসাহিত করেছিল। একসময় আমি চন্দবাড়ির সদস্যের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। ওই বাড়ির হাঁড়িতে আমার জন্য দুমুঠো চাল যেন দেওয়াই থাকত। আমি গেলে দিদিমা, কাকিমা কেউ বিরক্ত না হয়ে খুশি হতেন। হাসিমুখেই আমাকে স্বাগত জানাতেন। দিদিমা আর নেই। প্রায় ৯০ বছর বয়সে তিনি পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেছেন। কাকিমা এখনো সক্রিয় আছেন, সেঞ্চুরি করার অপেক্ষায়।
তপুর কাকাতো বোন রেবা রানী চন্দ; ডাক নাম পুতুল। আমাদের ছোট। দেখতে অনেকটা পুতুলের মতোই ছিল। আমি একটু বড় হওয়ার পর, অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ই মনে হয়, কেউ কেউ পুতুলের সঙ্গে আমার বিয়ের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করতেন বলে আমি শুনেছি। তবে বিষয়টি জোরালো হয়ে ওঠেনি।
তপুদের ভাইবোনেরা সবাই মুক্ত মনের অধিকারী। তপু আমার বন্ধু। ওর সঙ্গে মাখামাখি সম্পর্ক হওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু ওর বড় ভাই স্বপনদা এবং ছোট ভাই নয়নের সঙ্গেও গোড়া থেকেই আমার সম্পর্ক অত্যন্ত প্রীতিময়। নয়ন এখন বোদার একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি। কলেজে অধ্যাপনা থেকে সম্প্রতি অবসর নিয়ে সংস্কৃতি-সাহিত্য-সমাজ নিয়ে কাজ করেন, লেখালেখি করেন। কবিতা ও গদ্যে সমান পারদর্শী।
এই পরিবারের সঙ্গে আমার অতি ঘনিষ্ঠতার আরেকটি বড় কারণ বোধ হয় এটাই যে, এরা সবাই কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক ছিলেন। পার্টির সদস্য না হয়েও এরা ছিলেন পার্টি অন্তপ্রাণ। এ রকম পরিবার বোদায় আরও দু-চারটি ছিল।
চন্দবাড়ির সুধীর চন্দের জন্ম ১৯১৭ সালের কোনো এক বুধবার। ওই বছর পৃথিবীতে প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল। অক্টোবর বিপ্লব বলে পরিচিত সেই বিপ্লবের অভিঘাত তখনই বোদায় গিয়ে পৌঁছানোর কথা নয়। তাই সুধীর চন্দের চেতনায় বিপ্লব আঘাত হানেনি। তবে একধরনের উদার মানবতাবাদী চেতনার বিকাশ তাঁর মধ্যে লক্ষ করা গেছে। তাঁর বাড়ির পরিবেশ যে কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন হয়েছিল, সেটা আগে উল্লেখ করেছি। একটি কাকতালীয় ব্যাপার হলো তাঁর জন্ম এবং মৃত্যু একই বারে। বুধবার। ২০০০ সালের এক বুধবার তিনি চলে যান না ফেরার দেশে। প্রায় ৮৩ বছরের জীবন পেয়েছিলেন তিনি।
সুধীর চন্দ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাস করেছিলেন সম্ভবত ১৯৩৭ সালে। তাঁর সঙ্গে একই বছর প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেছিলেন বোদা হাইস্কুলের শিক্ষক সেলিমের বাবা সিদ্দিক সাহেব। ম্যাট্রিক পাসের পর সুধীর চন্দ আর পড়াশোনা না করে চাকরিতে ঢোকেন। তিনি অবিভক্ত ভারতেই জুট করপোরেশনে প্রথম চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। বন বিভাগেও নাকি তাঁর চাকরি হয়েছিল। সাপ, মশা ইত্যাদির ভয়ে তিনি সেই চাকরিতে যোগ দেননি।
ব্রিটিশরা ভারত ভাগ করে পাকিস্তান ও ভারত দুই রাষ্ট্রের জন্ম দিয়ে ১৯৪৭ সালে বিদায় নেয়। সে সময় সুধীর চন্দ তৎকালীন পাকিস্তানে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তখন তাঁর চাকরি ন্যস্ত হয় ডিসি কালেক্টরে তহসিল অফিসে, তহসিলদার হিসেবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় পর্যন্ত তিনি ওই চাকরি করেছেন। বোদা ছাড়াও দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ও সেতাবগঞ্জে তিনি তহসিলদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। স্বাধীনতার পর তিনি লুথার্ন ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন নামের একটি সাহায্য সংস্থায় চাকরি নেন। পরে এই সংগঠন আরডিআরএস নামে রূপান্তরিত হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে এই সংস্থা অনেক বড় ভূমিকা পালন করেছিল। তখন ঠাকুরগাঁও কলেজে পড়াশোনার পাশাপাশি বেশ কিছুদিন আরডিআরএসের কনস্ট্রাকশন বিভাগে কাজ করেছে আমার বন্ধু হিমাংশু চন্দ তপন বা তপু। বেশ কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিধ্বস্ত ভবন নতুন করে তৈরির কাজ তদারকির দায়িত্ব পালন করেছে তপু। সুধীর কাকু আরডিআরএসের চাকরি করেছেন ১৯৮০ সাল পর্যন্ত। ফলে তিনি স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে ঠাকুরগাঁওয়েই বসবাস করেছেন। বাসা ভাড়া নিয়ে দুই ছেলেকে নিয়ে তিনি থাকতেন। তপু ও নয়ন ঠাকুরগাঁও কলেজে পড়ত। তপু ওই কলেজ থেকে বিএ পাস করেছে আর নয়ন এইচএসসি পাস করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। দর্শনশাস্ত্রে মাস্টার্স করে বোদায় ফিরে পাথরাজ কলেজে শিক্ষকতা শুরু করে। তপু বিয়েশাদি করে ঠাকুরগাঁওয়েই স্থায়ী হয়েছে।
তপুদের ঠাকুরগাঁওয়ের বাসায়ও নানা কারণে আমাকে বহুদিন রাত কাটাতে হয়েছে এবং পাত পাততে হয়েছে। তখন ঢাকায় আসার জন্য আমাকে হয় দিনাজপুর অথবা ঠাকুরগাঁও থেকে গাড়ি ধরতে হতো। পঞ্চগড় থেকে কোনো কোচ ডে কিংবা নাইট তখনো চালু হয়নি। ঢাকা থেকে বাড়ি যাওয়া এবং বাড়ি থেকে ঢাকায় আসার জন্য ঠাকুরগাঁওয়ে আমার রাত্রিকালীন অবস্থান হতো তপুদের বাসায়। রান্নাঘরে একসঙ্গে বসে আমরা চারজন রাতের খাবার খেতাম। সুধীর কাকু পরম মমতায় আমাকে পুত্রবৎ পাশে বসাতেন। আহা, কত প্রীতিময় ছিল সেই দিনগুলো!
আগেই বলেছি, কাকু ছিলেন একজন ভালো ফুটবল খেলোয়াড়। তিনি জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাবের ক্যাপ্টেন ছিলেন। তিনি সাত-আটবার ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (আইএফএ) শিল্ড কাপ খেলেছেন। ট্রফি জিতেছেন। হেড করে গোল করায় তিনি খুব পারদর্শী ছিলেন। তখন মাঝগ্রামের আবদুর রহমান সাহেবও ভালো ফুটবল খেলতেন। তাঁর কর্নার কিক মানেই ছিল অবধারিত গোল। সে জন্যই তখন বলা হতো সুধীর চন্দের হেড আর আব্দুর রহমানের কর্নার কিক ইকুয়াল টু গোল। তিনি রংপুর ও দিনাজপুরে গিয়েও খেলেছেন।
সুধীর কাকু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছেন। অস্ত্র হাতে সম্মুখ সমরে অংশ না নিলেও শরণার্থীশিবিরে আশ্রয় নেওয়া মানুষদের নানা উপায়ে সাহায্য-সহযোগিতায় ছিলেন সদা তৎপর। যেসব রাজনৈতিক নেতাকর্মী ওপারে গিয়েছিলেন, তাঁদের জন্য বড় সহায় ছিলেন সুধীর কাকু। কিন্তু কিছু মানুষ যেমন যুদ্ধ শেষের পাওনা বুঝে নেওয়ার জন্য বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন, সুধীর কাকু ছিলেন সেখানে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।
চন্দবাড়ির স্বপনদা ছিলেন হাসিখুশি স্বভাবের, একটু যেন আপনভোলা মানুষ। সংসার করেছেন। কিন্তু প্রকৃত সংসারী বলতে যা বোঝায়, তিনি তা ছিলেন কি না, আমার সন্দেহ আছে। মাথার ওপর সুধীর কাকুর মতো বটবৃক্ষসম বাবা থাকলে অমনই বোধ হয় হওয়ার কথা।
স্বপনদা আমার বড়। বন্ধুর বড় ভাই। কিন্তু আমাদের মধ্যে একধরনের বন্ধুত্বের সম্পর্কই গড়ে উঠেছিল। তিনি আমার সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলতেন। রাজনীতি সচেতন ছিলেন। দেশ-দুনিয়া সম্পর্কে খোঁজখবর রাখতেন। নিয়মিত খবরের কাগজ পড়তেন।
১৯৭৩ সালের নির্বাচনে আমাদের এলাকা থেকে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন কামু ভাই, অ্যাডভোকেট কামরুল হোসেন। মনে আছে, ওই নির্বাচনী প্রচারে আমি আর স্বপনদা একসঙ্গে অনেক জায়গায় গিয়েছি। বিভিন্ন গ্রাম বা ইউনিয়নে আমাদের উভয়ের পরিচিতদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ভোট প্রার্থনা করেছি। আমি সাইকেল চালাতে পারতাম না। স্বপনদা সাইকেল চালিয়ে আমাকে নিয়ে যেতেন। তখন গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট ভালো ছিল না। আলপথে অনেক কষ্ট করেই আমাদের যেতে হতো। হাসিমুখেই এই কষ্টকর কাজটি স্বপনদা করতেন। আমরা বুঝতে পারতাম, জনমত আমাদের অনুকূলে নয়। তার পরও কিসের আশায়, কিসের নেশায় যে দিনরাত গ্রাম থেকে গ্রামে, বাড়ি থেকে বাড়ি ছুটে বেড়াতাম!
আমি ঢাকায় আসার পর স্বপনদার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই যোগাযোগ কমে গিয়েছিল। তার পরও ছুটিছাঁটায় বোদায় গেলে স্বপনদা ছুটে আসতেন। কত জিজ্ঞাসা নিয়ে আমার কাছে সেসবের উত্তর জানতে চাইতেন। তাঁর সব কৌতূহল মেটানোর সাধ্য আমার ছিল না। এর মধ্যে একটি দুর্ঘটনায় স্বপনদা একটি পা হারান। তিনি ক্র্যাচে ভর দিয়ে এক পায়ে হাঁটতেন। শেষদিকে সম্ভবত ছাত্র পড়িয়ে উপার্জন করতেন। ২০০৩ সালে স্বপনদার মৃত্যু হয়। তিনি রেখে গেছেন দুই মেয়ে ও এক ছেলেসন্তান। বৌদি তাঁর দেবরদের সহযোগিতায় ছেলেমেয়েদের মানুষ করেছেন। বড় মেয়ে চৈতালি চন্দ সোমার বর ঝাড়বাড়ি কলেজের অর্থনীতির সহকারী অধ্যাপক। ছোট মেয়ে বিপাশা চন্দ দোলন বরিশালে বিয়ে হলেও এখন সম্ভবত বোদাতেই আছে। ছেলে সৌমিত চন্দ জয়দ্বীপ কৃতী ছাত্র। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করে ভারতের গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি সম্পন্ন করে ঢাকায় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছে। জয়দ্বীপ জাহাঙ্গীরনগরে ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ছিল, সভাপতি হয়েছিল। বাম রাজনীতিতে তাঁর আগ্রহ হয়তো এখনো বহাল আছে। গুজরাটে যাওয়ার আগে দৈনিক সমকালে কিছুদিন সাংবাদিকতা করেছে। লেখালেখির হাত ভালো। এর মধ্যেই গবেষণামূলক কিছু গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লিখে সুনাম অর্জন করেছে।
আমার বন্ধু হিমাংশু তপুও একজন সফল মানুষ। ঠাকুরগাঁওয়ে ওর একটি এনজিও আছে। অনেকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। ছাত্রাবস্থাতেই তপু উপার্জনমুখী হয়েছে। প্রথমে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি, তারপর ঠাকুরগাঁওয়ে একটি কসমেটিকসের দোকান এবং সব শেষে শার্প নামে এনজিও প্রতিষ্ঠা। নানা ধরনের সামাজিক কাজকর্মেও তপু সময় দেয়। ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েও ছাত্রাবস্থায় তপুর ভেতরের এত প্রতিভা সম্পর্কে আমরা কিছু আন্দাজ করতে পারিনি। তপুর একমাত্র ছেলে বুদ্ধদেব চন্দ তমাল কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ করে এসে এখন বগুড়ায় একটি বেসরকারি ব্যাংকের কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করছে। তমাল বিয়ে করে এক সন্তানের জনকও হয়েছে। আমার বন্ধু তপু গর্বিত দাদু হিসেবে পরিতৃপ্তি নিয়ে সংসার করছে।
ভাইদের মধ্যে ছোট প্রবীর চন্দ নয়ন। মূলত সে-ই এখন চন্দবাড়ির অভিভাবক। বোদার একজন সচেতন ও সংস্কৃতি মনস্ক মানুষ। দর্শনশাস্ত্রে পড়াশোনা করেও সাহিত্যে তাঁর অনুরাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন থেকেই। নিয়মিত কবিতা এবং নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে থাকে। দুটি কবিতার বইও বের হয়েছে। দুটি প্রবন্ধের বই প্রকাশের অপেক্ষায়। তার স্ত্রীও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ছেলে শুভ্র প্রতিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ করে একটি অ্যাড ফার্মে চাকরি করছে। মেয়ে দেবলীনা দৈবী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের ছাত্রী।
চন্দবাড়ির মেয়েদের কথা কিছু না বললেই নয়। সুধীর চন্দের বড় মেয়ে জলপাইগুড়িতে থেকেছেন বলে তাঁর সঙ্গে আমার কখনো দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দু-তিনবার তিনি বোদায় এসেছেন। আমি তখন বোদা ছেড়েছি। ফলে শিবানী চন্দ আমার অদেখা বড় দিদি। কল্যাণী; অর্থাৎ সুনুদিই হলেন আমাদের দেখা বড় দিদি। কী হাসিখুশি মানুষ সুনুদি! মানুষকে আপন করে নেওয়ার শক্তি যেমন তাঁর আছে, তেমনি আছে প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে এগিয়ে চলার প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস।
আমাদের ছোটবেলায় সুনুদির বিয়ে হয়। প্রেমের বিয়ে। মধু জামাইবাবুও খুব সুন্দর ছিলেন। সুনুদি তো অবশ্যই সুন্দরী। ভালোই চলছিল সব। সময় গড়িয়ে দুটি ফুটফুটে পুত্রসন্তানের জনক-জননী হন তাঁরা। তারপর যে কোথা থেকে কী হয়। জামাইবাবুকে আর বোদায় দেখা যায় না। তিনি সংসারত্যাগী হন। কী দুঃসহ মর্মজ্বালা বুকে চেপে সুনুদি তাঁর দুই ছেলে মিহির ও বিজনকে মানুষ করার কাজটি সম্পন্ন করেছেন, তা ভুক্তভোগী ছাড়া কারও পক্ষে বোঝা কঠিন। বাবা এবং পরিবারের সহযোগিতা-সমর্থন তিনি পেয়েছেন। কিন্তু আমাদের কুচুটে সমাজের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করা যে কত কঠিন, সেটা না বললেও চলে। সুনুদি প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর ছোট ছেলে বিজন সরকারও একটি প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। বড় ছেলে মিহির সরকার একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করত বলে শুনেছিলাম।
চন্দবাড়ির আরেক মেয়ে বেণু ওরফে নারায়ণী চন্দ, আমার বন্ধু এবং মামি। আমার মায়ের কোনো ভাইবোন নেই। তিনি বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। তবে মায়ের কয়েকজন পাতানো ভাই আছে, যারা আমার মামা। এ রকম একজন হলেন নারায়ণ চন্দ্র সাহা। ঢাকার বিক্রমপুরে বাড়ি। চাকরির সুবাদে বোদায় যান গত শতকের ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে। তিনি কিছুদিন লজিং থাকতেন আমার পিসার বাসায়; অর্থাৎ কার্তিকদা-জ্যোতিষদাদের বাসায়। তখন অবশ্য পিসেমশাই শরৎ চন্দ্র সরকার জীবিত ছিলেন। যা হোক, ওই বাসায় লজিং থাকার সুবাদেই হয়তো আমার মায়ের ভাই হয়ে যান নারায়ণ সাহা। আমার মামা। এই মামাই বিয়ে করেন চন্দবাড়ির মেয়ে বেণুকে। বন্ধু হেয় গেল মামি। বিয়ের পর নতুন সংসার গোছানোর আগে কিছুদিন তাঁরা আমাদের বাড়িতেই ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এই পরিবারের সঙ্গেও আমার অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। একসময় এমনও ছিল যে, ঢাকা থেকে বাড়ি গেলে রাতটা আমি নারায়ণ মামার বাসাতেই কাটাতাম। ততদিনে তাঁদের মেয়ে ও ছেলে বড় হয়ে উঠতে শুরু করেছে। একটি বিষয় লক্ষণীয়। মামার নাম নারায়ণ আর যাকে বিয়ে করলেন তাঁর নাম নারায়ণী। আমাকে আমার দু-এক বন্ধু তখন ঠাট্টা করে বলত, আমার স্ত্রীর নাম নাকি হবে হয় বিভা, না হয় রঞ্জনা! না, সেটা হয়নি।
বেণুও প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করেছে। ছেলে বাপ্পা ওরফে স্বরূপ সাহা এসএসসি পাস করে কলকাতায় চলে যায়। এমবিএ পাস করে বাপ্পা এখন বেঙ্গালুরুতে আছে বলে শুনেছি। বাপ্পা আমাকে মামা বলে ডাকে। কী অদ্ভুত সামাজিক সম্পর্কগুলো! বেণুর মেয়ে শম্পা কিছুদিন ঢাকায় ছিল। তারপর নাকি আমেরিকায় চলে গেছে। নারায়ণ মামার জীবনাবসান হয়েছে। মামি এখন অবসরজীবন যাপন করছেন।
নটে গাছটি মুড়োল, চন্দবাড়ির গল্প ফুরোল।
লেখক: সহকারী সম্পাদক, আজকের পত্রিকা
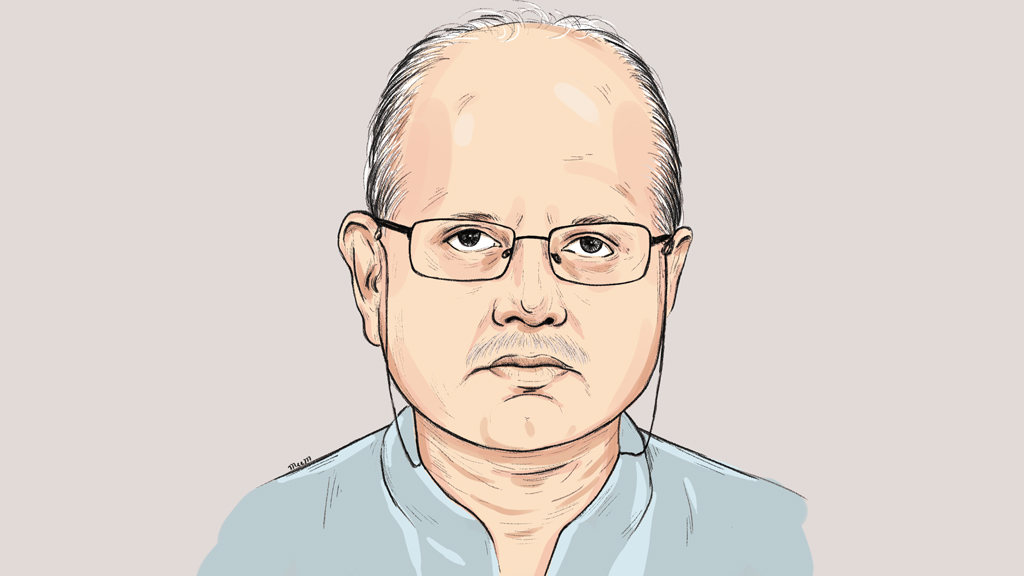
দত্তবাড়ির পর বোদার চন্দবাড়ির কথা না লিখলে চলে না। দত্তবাড়ির মতো চন্দবাড়িতেও আছে আমার সহপাঠী ও বন্ধু। আবার দত্ত ও চন্দবাড়ির মধ্যেও আছে পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক।
বোদার থানাপাড়া এখন অনেক বড়। অনেক বাড়িঘর। আর আমাদের ছোটবেলায় থানা, ওয়াপদা অফিস এবং একদিকে চন্দবাড়ি, অন্যদিকে হকিকুল ডাক্তার সাহেবের বাড়ি ছাড়া আর কোনো বাড়িঘর ছিল বলে মনে পড়ে না।
উমেশ চন্দ্র চন্দ ও মন্মথ চন্দ দুই ভাই। উমেশ চন্দের দুই ছেলে সুধীর চন্দ্র চন্দ ও অধীর চন্দ্র চন্দ। উমেশ বাবুকে আমি দেখিনি। তবে মন্মথ বাবুকে দেখেছি। তাঁর বাড়ি অবশ্য থানাপাড়ায় ছিল না। তাঁর বাড়ি বাজার থেকে সিরাজ সরকার সাহেবের বাড়ি যেতে আগে পড়ত। হাতের বাঁয়ে। এখনো আছে সেই বাড়ি। মন্মথ চন্দের মেয়ে ছায়াদিকে বিয়ে করেন দত্তবাড়ির শিবেন দত্ত।
উমেশ চন্দের দুই ছেলের থানাপাড়ার বাসায় আমার ছিল অবাধ যাতায়াত। বড় ছেলে সুধীর চন্দের তিন ছেলে ও তিন মেয়ে। শিবানী চন্দ, কল্যাণী চন্দ (সুনু), সুধাংশু চন্দ (স্বপন), নারায়ণী চন্দ (বেণু), হিমাংশু চন্দ (তপন/তপু) ও প্রবীর চন্দ (নয়ন)। শিবানী চন্দকে আমি দেখিনি। তিনি অবিভক্ত ভারতের জলপাইগুড়িতে মামাবাড়িতে একেবারে ছোট থেকেই বড় হয়েছেন। আর দেশে আসেননি। অন্য সবাই বোদায় ছিলেন বা আছেন। এর মধ্যে স্বপনদা অকালপ্রয়াত। সুনুদি, স্বপনদা ও বেণু আমার বড়। তবে বড় হলেও বেণু আর তপু আমার সহপাঠী। পরে সম্ভবত ক্লাস ফাইভ থেকে বেণু আমার ‘জুনিয়র’ হয়ে যায়। আর তপু হয়ে ওঠে আমার প্রিয় বন্ধুদের একজন। আমি, তপু ও দত্তবাড়ির বিজন—এই তিনজন ছিলাম (দেখা-সাক্ষাৎ কম হলেও এখনো আছি) ‘এক দেহ, এক প্রাণ’। কত কথাই না মনে পড়ছে। একটি ঘটনার কথা না বলে পারছি না। হাইস্কুলে পড়ার সময় আমরা কয়েকজন (এর মধ্যে বিজন, তপু আর আমি কমন) প্রতি বৃহস্পতিবার টিফিনের সময় স্কুল পালিয়ে ঠাকুরগাঁওয়ে যেতাম সিনেমা দেখার জন্য। শুক্রবার নতুন ছবি শুরু হতো, কাজেই বৃহস্পতিবার আমরা বিদায়ী ছবিটা দেখতাম। বলাকা টকিজ নামের সিনেমা হলটির মালিক ছিলেন মির্জা রুহুল আমিন (চখা মিয়া নামে সমধিক পরিচিত)। তিনি ছিলেন বর্তমান বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বাবা এবং সাবেক সেনাপ্রধান ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সাবেক সদস্য লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মাহবুবুর রহমানের শ্বশুর।
স্কুল থেকে পালিয়ে আমরা একত্রিত হতাম সাতখামারে শামসুদ্দিন ডাক্তার সাহেবের ডিসপেনসারিতে। দুপুরবেলা ওটা ফাঁকা থাকত। আমার বাড়ি ছিল তার পাশেই। ওটা ছিল ঠাকুরগাঁওয়ে যাওয়ার সড়কের একেবারে লাগোয়া। বাসস্ট্যান্ড থেকে বাসে উঠলে কেউ দেখে ফেলতে পারে—এই আশঙ্কা থেকেই আমরা একটু এগিয়ে গিয়ে বাসে উঠতাম। প্রবাদ আছে, ‘যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে রাত হয়’। একদিন আমাদের শামসুদ্দিন ডাক্তার চাচার ডিসপেনসারিতে জটলারত অবস্থায় দেখতে পান ডা. ফয়জুল করিম, আমাদের মশিয়ারের (মশিয়ার রহমান, এখন পল্লি কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা) বাবা। আমরা যে স্কুল পালিয়ে ওখানে সমবেত হয়েছি, সেটা তিনি বুঝতে পারেন। তিনি সম্ভবত রোগী দেখে সাইকেলে চেপে ফিরছিলেন। তিনি নিজে আমাদের কিছু বললেন না। তবে বাজারে গিয়ে তপুর বাবা সুধীর কাকুকে বিষয়টি অবগত করেন। কাকু দ্রুত ছুটে আসেন এবং আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই তপুকে পাকড়াও করে পায়ের কাবলি স্যান্ডেল দিয়ে বেদম পেটাতে থাকেন। তপু চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে মিনতি করে বলতে থাকে, ‘দোহাই বাবা, আর মেরো না।’ কাকু কোনো কথা শোনেন না। একপর্যায়ে পিটিয়ে ক্লান্ত হয়ে আমাদের সবাইকে শাসিয়ে তিনি চলে যান। আমরা ভাবলাম, অত পিটুনি খেয়ে তপু হয়তো আর সিনেমা দেখতে যাবে না। কিন্তু আমাদের অবাক করে তপু বলল, ‘মার তো খেয়েই ফেলেছি, তাহলে আর সিনেমা দেখা থেকে বঞ্চিত হব কেন?’
তপু ছিল আমাদের বন্ধুদের মধ্য সবচেয়ে ছোটখাটো। তাই ওকে নিয়ে কত ধরনের কাণ্ডই না আমরা করতাম। সেই তপু, হিমাংশু চন্দ এখন ঠাকুরগাঁওয়ে একটি বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) প্রধান নির্বাহী। তপুও খুব সরল মনের সাদাসিধে মানুষ। জীবনে টাকা-পয়সা যেমন উপার্জন করেছে, তেমন খরচও করেছে। ওর বাবা, আমাদের সুধীর কাকুও ছিলেন অত্যন্ত দরাজ দিল মানুষ। আমি তাঁর কাছ থেকে যে স্নেহ-ভালোবাসা পেয়েছি, তা বলে শেষ করা যাবে না।
আমার বন্ধু তপুর বাবা, আমাদের সুধীর কাকু ছিলেন আমার দেখা ‘অসাধারণ’ মানুষদের একজন। দেখতে ছিলেন সুদর্শন। অমন উন্নত নাক, গৌর বর্ণ, মাথা উঁচু করে হাঁটাচলা করা; দেখলেই মনের মধ্যে একটি সমীহ ভাব চলে আসত। তাঁকে আমরা একধরনের ভয়মিশ্রিত সমীহই করতাম। একেবারে ছোটবেলায় এড়িয়ে চলতাম। আস্তে আস্তে যতই তাঁর নৈকট্য লাভ করেছি, ততই মনে হয়েছে তাঁর মনের ভেতরটা কত নরম। পরিণত বয়সেও তিনি ঝুনা নারকেল না হয়ে কচি ডাবের মতোই ছিলেন।
প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন একজন নামকরা ফুটবল খেলোয়াড়। জলপাইগুড়ি জেলায়ও তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। আমরা ছোটবেলায়ও তাঁকে বোদা হাইস্কুল মাঠে শৌখিন খেলোয়াড় হিসেবে খেলতে দেখেছি। সুধীর কাকু, ডা. ফয়জুল চাচারা মাঠে নামলে জমে উঠত খেলা। তরুণদের উৎসাহিত করার জন্যই সে সময় তাঁরা নিয়মিত মাঠে যেতেন।
তপুর মা, মানে আমাদের কাকি মারা যান সম্ভবত ১৯৫৭ সালে। আমি হয়তো তাঁকে দেখিওনি। শুনেছি নয়নের তখন মাত্র দেড় বছর বয়স। তপুর তিন-সাড়ে তিন। কাজেই মায়ের কোনো স্মৃতি ওদের মনে থাকার কথা নয়। ওরা প্রকৃতপক্ষে মাতৃস্নেহে বড় হয়েছে দিদিমার কাছে। দিদিমা সরজুবালা দেবী ছিলেন সুধীর কাকুর মাসিমা। তিনি বাল্যবিধবা। বিয়ের অল্প পরই স্বামীহারা হয়ে সুধীর কাকুর সংসারে স্থায়ী হয়েছিলেন। তপু ও নয়ন এই দিদিমার কোলেপিঠে মানুষ। তাই তিনি ছিলেন ওদের মা, দিদিমা নয়!
এই মহীয়সী নারীকে যাঁরা না দেখেছেন, তাঁরা তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কোনো ধারণা করতে পারবেন না। তিনিই কার্যত চন্দবাড়িতে অভিভাবক ছিলেন। তাঁর ছায়া-মায়ায় তপুরা ভাইবোন মানুষ হয়েছে। আরও একজন তপুদের মায়ের অভাব পূরণে বড় ভূমিকা রেখেছেন—তপুদের কাকিমা, অধীর কাকুর স্ত্রী। এই কাকিমার নাম রেখা রানী চন্দ। নিজের তিন মেয়ে ও দুই ছেলেসন্তানের সঙ্গে ভাশুরের সন্তানদেরও তিনি অকৃপণ স্নেহ-ভালোবাসা দিয়েছেন।
সুধীর কাকুর স্ত্রীবিয়োগের পর অনেকে তাঁকে আবার বিয়ে করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তখন এমন রেওয়াজ ছিল, কিন্তু প্রথম স্ত্রীর প্রতি গভীর ভালোবাসা তাঁকে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণে নিরুৎসাহিত করেছিল। একসময় আমি চন্দবাড়ির সদস্যের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। ওই বাড়ির হাঁড়িতে আমার জন্য দুমুঠো চাল যেন দেওয়াই থাকত। আমি গেলে দিদিমা, কাকিমা কেউ বিরক্ত না হয়ে খুশি হতেন। হাসিমুখেই আমাকে স্বাগত জানাতেন। দিদিমা আর নেই। প্রায় ৯০ বছর বয়সে তিনি পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেছেন। কাকিমা এখনো সক্রিয় আছেন, সেঞ্চুরি করার অপেক্ষায়।
তপুর কাকাতো বোন রেবা রানী চন্দ; ডাক নাম পুতুল। আমাদের ছোট। দেখতে অনেকটা পুতুলের মতোই ছিল। আমি একটু বড় হওয়ার পর, অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ই মনে হয়, কেউ কেউ পুতুলের সঙ্গে আমার বিয়ের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করতেন বলে আমি শুনেছি। তবে বিষয়টি জোরালো হয়ে ওঠেনি।
তপুদের ভাইবোনেরা সবাই মুক্ত মনের অধিকারী। তপু আমার বন্ধু। ওর সঙ্গে মাখামাখি সম্পর্ক হওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু ওর বড় ভাই স্বপনদা এবং ছোট ভাই নয়নের সঙ্গেও গোড়া থেকেই আমার সম্পর্ক অত্যন্ত প্রীতিময়। নয়ন এখন বোদার একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি। কলেজে অধ্যাপনা থেকে সম্প্রতি অবসর নিয়ে সংস্কৃতি-সাহিত্য-সমাজ নিয়ে কাজ করেন, লেখালেখি করেন। কবিতা ও গদ্যে সমান পারদর্শী।
এই পরিবারের সঙ্গে আমার অতি ঘনিষ্ঠতার আরেকটি বড় কারণ বোধ হয় এটাই যে, এরা সবাই কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক ছিলেন। পার্টির সদস্য না হয়েও এরা ছিলেন পার্টি অন্তপ্রাণ। এ রকম পরিবার বোদায় আরও দু-চারটি ছিল।
চন্দবাড়ির সুধীর চন্দের জন্ম ১৯১৭ সালের কোনো এক বুধবার। ওই বছর পৃথিবীতে প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল। অক্টোবর বিপ্লব বলে পরিচিত সেই বিপ্লবের অভিঘাত তখনই বোদায় গিয়ে পৌঁছানোর কথা নয়। তাই সুধীর চন্দের চেতনায় বিপ্লব আঘাত হানেনি। তবে একধরনের উদার মানবতাবাদী চেতনার বিকাশ তাঁর মধ্যে লক্ষ করা গেছে। তাঁর বাড়ির পরিবেশ যে কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন হয়েছিল, সেটা আগে উল্লেখ করেছি। একটি কাকতালীয় ব্যাপার হলো তাঁর জন্ম এবং মৃত্যু একই বারে। বুধবার। ২০০০ সালের এক বুধবার তিনি চলে যান না ফেরার দেশে। প্রায় ৮৩ বছরের জীবন পেয়েছিলেন তিনি।
সুধীর চন্দ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাস করেছিলেন সম্ভবত ১৯৩৭ সালে। তাঁর সঙ্গে একই বছর প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেছিলেন বোদা হাইস্কুলের শিক্ষক সেলিমের বাবা সিদ্দিক সাহেব। ম্যাট্রিক পাসের পর সুধীর চন্দ আর পড়াশোনা না করে চাকরিতে ঢোকেন। তিনি অবিভক্ত ভারতেই জুট করপোরেশনে প্রথম চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। বন বিভাগেও নাকি তাঁর চাকরি হয়েছিল। সাপ, মশা ইত্যাদির ভয়ে তিনি সেই চাকরিতে যোগ দেননি।
ব্রিটিশরা ভারত ভাগ করে পাকিস্তান ও ভারত দুই রাষ্ট্রের জন্ম দিয়ে ১৯৪৭ সালে বিদায় নেয়। সে সময় সুধীর চন্দ তৎকালীন পাকিস্তানে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তখন তাঁর চাকরি ন্যস্ত হয় ডিসি কালেক্টরে তহসিল অফিসে, তহসিলদার হিসেবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় পর্যন্ত তিনি ওই চাকরি করেছেন। বোদা ছাড়াও দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ও সেতাবগঞ্জে তিনি তহসিলদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। স্বাধীনতার পর তিনি লুথার্ন ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন নামের একটি সাহায্য সংস্থায় চাকরি নেন। পরে এই সংগঠন আরডিআরএস নামে রূপান্তরিত হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে এই সংস্থা অনেক বড় ভূমিকা পালন করেছিল। তখন ঠাকুরগাঁও কলেজে পড়াশোনার পাশাপাশি বেশ কিছুদিন আরডিআরএসের কনস্ট্রাকশন বিভাগে কাজ করেছে আমার বন্ধু হিমাংশু চন্দ তপন বা তপু। বেশ কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিধ্বস্ত ভবন নতুন করে তৈরির কাজ তদারকির দায়িত্ব পালন করেছে তপু। সুধীর কাকু আরডিআরএসের চাকরি করেছেন ১৯৮০ সাল পর্যন্ত। ফলে তিনি স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে ঠাকুরগাঁওয়েই বসবাস করেছেন। বাসা ভাড়া নিয়ে দুই ছেলেকে নিয়ে তিনি থাকতেন। তপু ও নয়ন ঠাকুরগাঁও কলেজে পড়ত। তপু ওই কলেজ থেকে বিএ পাস করেছে আর নয়ন এইচএসসি পাস করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। দর্শনশাস্ত্রে মাস্টার্স করে বোদায় ফিরে পাথরাজ কলেজে শিক্ষকতা শুরু করে। তপু বিয়েশাদি করে ঠাকুরগাঁওয়েই স্থায়ী হয়েছে।
তপুদের ঠাকুরগাঁওয়ের বাসায়ও নানা কারণে আমাকে বহুদিন রাত কাটাতে হয়েছে এবং পাত পাততে হয়েছে। তখন ঢাকায় আসার জন্য আমাকে হয় দিনাজপুর অথবা ঠাকুরগাঁও থেকে গাড়ি ধরতে হতো। পঞ্চগড় থেকে কোনো কোচ ডে কিংবা নাইট তখনো চালু হয়নি। ঢাকা থেকে বাড়ি যাওয়া এবং বাড়ি থেকে ঢাকায় আসার জন্য ঠাকুরগাঁওয়ে আমার রাত্রিকালীন অবস্থান হতো তপুদের বাসায়। রান্নাঘরে একসঙ্গে বসে আমরা চারজন রাতের খাবার খেতাম। সুধীর কাকু পরম মমতায় আমাকে পুত্রবৎ পাশে বসাতেন। আহা, কত প্রীতিময় ছিল সেই দিনগুলো!
আগেই বলেছি, কাকু ছিলেন একজন ভালো ফুটবল খেলোয়াড়। তিনি জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাবের ক্যাপ্টেন ছিলেন। তিনি সাত-আটবার ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (আইএফএ) শিল্ড কাপ খেলেছেন। ট্রফি জিতেছেন। হেড করে গোল করায় তিনি খুব পারদর্শী ছিলেন। তখন মাঝগ্রামের আবদুর রহমান সাহেবও ভালো ফুটবল খেলতেন। তাঁর কর্নার কিক মানেই ছিল অবধারিত গোল। সে জন্যই তখন বলা হতো সুধীর চন্দের হেড আর আব্দুর রহমানের কর্নার কিক ইকুয়াল টু গোল। তিনি রংপুর ও দিনাজপুরে গিয়েও খেলেছেন।
সুধীর কাকু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছেন। অস্ত্র হাতে সম্মুখ সমরে অংশ না নিলেও শরণার্থীশিবিরে আশ্রয় নেওয়া মানুষদের নানা উপায়ে সাহায্য-সহযোগিতায় ছিলেন সদা তৎপর। যেসব রাজনৈতিক নেতাকর্মী ওপারে গিয়েছিলেন, তাঁদের জন্য বড় সহায় ছিলেন সুধীর কাকু। কিন্তু কিছু মানুষ যেমন যুদ্ধ শেষের পাওনা বুঝে নেওয়ার জন্য বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন, সুধীর কাকু ছিলেন সেখানে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।
চন্দবাড়ির স্বপনদা ছিলেন হাসিখুশি স্বভাবের, একটু যেন আপনভোলা মানুষ। সংসার করেছেন। কিন্তু প্রকৃত সংসারী বলতে যা বোঝায়, তিনি তা ছিলেন কি না, আমার সন্দেহ আছে। মাথার ওপর সুধীর কাকুর মতো বটবৃক্ষসম বাবা থাকলে অমনই বোধ হয় হওয়ার কথা।
স্বপনদা আমার বড়। বন্ধুর বড় ভাই। কিন্তু আমাদের মধ্যে একধরনের বন্ধুত্বের সম্পর্কই গড়ে উঠেছিল। তিনি আমার সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলতেন। রাজনীতি সচেতন ছিলেন। দেশ-দুনিয়া সম্পর্কে খোঁজখবর রাখতেন। নিয়মিত খবরের কাগজ পড়তেন।
১৯৭৩ সালের নির্বাচনে আমাদের এলাকা থেকে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন কামু ভাই, অ্যাডভোকেট কামরুল হোসেন। মনে আছে, ওই নির্বাচনী প্রচারে আমি আর স্বপনদা একসঙ্গে অনেক জায়গায় গিয়েছি। বিভিন্ন গ্রাম বা ইউনিয়নে আমাদের উভয়ের পরিচিতদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ভোট প্রার্থনা করেছি। আমি সাইকেল চালাতে পারতাম না। স্বপনদা সাইকেল চালিয়ে আমাকে নিয়ে যেতেন। তখন গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট ভালো ছিল না। আলপথে অনেক কষ্ট করেই আমাদের যেতে হতো। হাসিমুখেই এই কষ্টকর কাজটি স্বপনদা করতেন। আমরা বুঝতে পারতাম, জনমত আমাদের অনুকূলে নয়। তার পরও কিসের আশায়, কিসের নেশায় যে দিনরাত গ্রাম থেকে গ্রামে, বাড়ি থেকে বাড়ি ছুটে বেড়াতাম!
আমি ঢাকায় আসার পর স্বপনদার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই যোগাযোগ কমে গিয়েছিল। তার পরও ছুটিছাঁটায় বোদায় গেলে স্বপনদা ছুটে আসতেন। কত জিজ্ঞাসা নিয়ে আমার কাছে সেসবের উত্তর জানতে চাইতেন। তাঁর সব কৌতূহল মেটানোর সাধ্য আমার ছিল না। এর মধ্যে একটি দুর্ঘটনায় স্বপনদা একটি পা হারান। তিনি ক্র্যাচে ভর দিয়ে এক পায়ে হাঁটতেন। শেষদিকে সম্ভবত ছাত্র পড়িয়ে উপার্জন করতেন। ২০০৩ সালে স্বপনদার মৃত্যু হয়। তিনি রেখে গেছেন দুই মেয়ে ও এক ছেলেসন্তান। বৌদি তাঁর দেবরদের সহযোগিতায় ছেলেমেয়েদের মানুষ করেছেন। বড় মেয়ে চৈতালি চন্দ সোমার বর ঝাড়বাড়ি কলেজের অর্থনীতির সহকারী অধ্যাপক। ছোট মেয়ে বিপাশা চন্দ দোলন বরিশালে বিয়ে হলেও এখন সম্ভবত বোদাতেই আছে। ছেলে সৌমিত চন্দ জয়দ্বীপ কৃতী ছাত্র। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করে ভারতের গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি সম্পন্ন করে ঢাকায় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছে। জয়দ্বীপ জাহাঙ্গীরনগরে ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ছিল, সভাপতি হয়েছিল। বাম রাজনীতিতে তাঁর আগ্রহ হয়তো এখনো বহাল আছে। গুজরাটে যাওয়ার আগে দৈনিক সমকালে কিছুদিন সাংবাদিকতা করেছে। লেখালেখির হাত ভালো। এর মধ্যেই গবেষণামূলক কিছু গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লিখে সুনাম অর্জন করেছে।
আমার বন্ধু হিমাংশু তপুও একজন সফল মানুষ। ঠাকুরগাঁওয়ে ওর একটি এনজিও আছে। অনেকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। ছাত্রাবস্থাতেই তপু উপার্জনমুখী হয়েছে। প্রথমে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি, তারপর ঠাকুরগাঁওয়ে একটি কসমেটিকসের দোকান এবং সব শেষে শার্প নামে এনজিও প্রতিষ্ঠা। নানা ধরনের সামাজিক কাজকর্মেও তপু সময় দেয়। ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েও ছাত্রাবস্থায় তপুর ভেতরের এত প্রতিভা সম্পর্কে আমরা কিছু আন্দাজ করতে পারিনি। তপুর একমাত্র ছেলে বুদ্ধদেব চন্দ তমাল কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ করে এসে এখন বগুড়ায় একটি বেসরকারি ব্যাংকের কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করছে। তমাল বিয়ে করে এক সন্তানের জনকও হয়েছে। আমার বন্ধু তপু গর্বিত দাদু হিসেবে পরিতৃপ্তি নিয়ে সংসার করছে।
ভাইদের মধ্যে ছোট প্রবীর চন্দ নয়ন। মূলত সে-ই এখন চন্দবাড়ির অভিভাবক। বোদার একজন সচেতন ও সংস্কৃতি মনস্ক মানুষ। দর্শনশাস্ত্রে পড়াশোনা করেও সাহিত্যে তাঁর অনুরাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন থেকেই। নিয়মিত কবিতা এবং নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে থাকে। দুটি কবিতার বইও বের হয়েছে। দুটি প্রবন্ধের বই প্রকাশের অপেক্ষায়। তার স্ত্রীও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ছেলে শুভ্র প্রতিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ করে একটি অ্যাড ফার্মে চাকরি করছে। মেয়ে দেবলীনা দৈবী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের ছাত্রী।
চন্দবাড়ির মেয়েদের কথা কিছু না বললেই নয়। সুধীর চন্দের বড় মেয়ে জলপাইগুড়িতে থেকেছেন বলে তাঁর সঙ্গে আমার কখনো দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দু-তিনবার তিনি বোদায় এসেছেন। আমি তখন বোদা ছেড়েছি। ফলে শিবানী চন্দ আমার অদেখা বড় দিদি। কল্যাণী; অর্থাৎ সুনুদিই হলেন আমাদের দেখা বড় দিদি। কী হাসিখুশি মানুষ সুনুদি! মানুষকে আপন করে নেওয়ার শক্তি যেমন তাঁর আছে, তেমনি আছে প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে এগিয়ে চলার প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস।
আমাদের ছোটবেলায় সুনুদির বিয়ে হয়। প্রেমের বিয়ে। মধু জামাইবাবুও খুব সুন্দর ছিলেন। সুনুদি তো অবশ্যই সুন্দরী। ভালোই চলছিল সব। সময় গড়িয়ে দুটি ফুটফুটে পুত্রসন্তানের জনক-জননী হন তাঁরা। তারপর যে কোথা থেকে কী হয়। জামাইবাবুকে আর বোদায় দেখা যায় না। তিনি সংসারত্যাগী হন। কী দুঃসহ মর্মজ্বালা বুকে চেপে সুনুদি তাঁর দুই ছেলে মিহির ও বিজনকে মানুষ করার কাজটি সম্পন্ন করেছেন, তা ভুক্তভোগী ছাড়া কারও পক্ষে বোঝা কঠিন। বাবা এবং পরিবারের সহযোগিতা-সমর্থন তিনি পেয়েছেন। কিন্তু আমাদের কুচুটে সমাজের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করা যে কত কঠিন, সেটা না বললেও চলে। সুনুদি প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর ছোট ছেলে বিজন সরকারও একটি প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। বড় ছেলে মিহির সরকার একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করত বলে শুনেছিলাম।
চন্দবাড়ির আরেক মেয়ে বেণু ওরফে নারায়ণী চন্দ, আমার বন্ধু এবং মামি। আমার মায়ের কোনো ভাইবোন নেই। তিনি বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। তবে মায়ের কয়েকজন পাতানো ভাই আছে, যারা আমার মামা। এ রকম একজন হলেন নারায়ণ চন্দ্র সাহা। ঢাকার বিক্রমপুরে বাড়ি। চাকরির সুবাদে বোদায় যান গত শতকের ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে। তিনি কিছুদিন লজিং থাকতেন আমার পিসার বাসায়; অর্থাৎ কার্তিকদা-জ্যোতিষদাদের বাসায়। তখন অবশ্য পিসেমশাই শরৎ চন্দ্র সরকার জীবিত ছিলেন। যা হোক, ওই বাসায় লজিং থাকার সুবাদেই হয়তো আমার মায়ের ভাই হয়ে যান নারায়ণ সাহা। আমার মামা। এই মামাই বিয়ে করেন চন্দবাড়ির মেয়ে বেণুকে। বন্ধু হেয় গেল মামি। বিয়ের পর নতুন সংসার গোছানোর আগে কিছুদিন তাঁরা আমাদের বাড়িতেই ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এই পরিবারের সঙ্গেও আমার অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। একসময় এমনও ছিল যে, ঢাকা থেকে বাড়ি গেলে রাতটা আমি নারায়ণ মামার বাসাতেই কাটাতাম। ততদিনে তাঁদের মেয়ে ও ছেলে বড় হয়ে উঠতে শুরু করেছে। একটি বিষয় লক্ষণীয়। মামার নাম নারায়ণ আর যাকে বিয়ে করলেন তাঁর নাম নারায়ণী। আমাকে আমার দু-এক বন্ধু তখন ঠাট্টা করে বলত, আমার স্ত্রীর নাম নাকি হবে হয় বিভা, না হয় রঞ্জনা! না, সেটা হয়নি।
বেণুও প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করেছে। ছেলে বাপ্পা ওরফে স্বরূপ সাহা এসএসসি পাস করে কলকাতায় চলে যায়। এমবিএ পাস করে বাপ্পা এখন বেঙ্গালুরুতে আছে বলে শুনেছি। বাপ্পা আমাকে মামা বলে ডাকে। কী অদ্ভুত সামাজিক সম্পর্কগুলো! বেণুর মেয়ে শম্পা কিছুদিন ঢাকায় ছিল। তারপর নাকি আমেরিকায় চলে গেছে। নারায়ণ মামার জীবনাবসান হয়েছে। মামি এখন অবসরজীবন যাপন করছেন।
নটে গাছটি মুড়োল, চন্দবাড়ির গল্প ফুরোল।
লেখক: সহকারী সম্পাদক, আজকের পত্রিকা
বিভুরঞ্জন সরকার
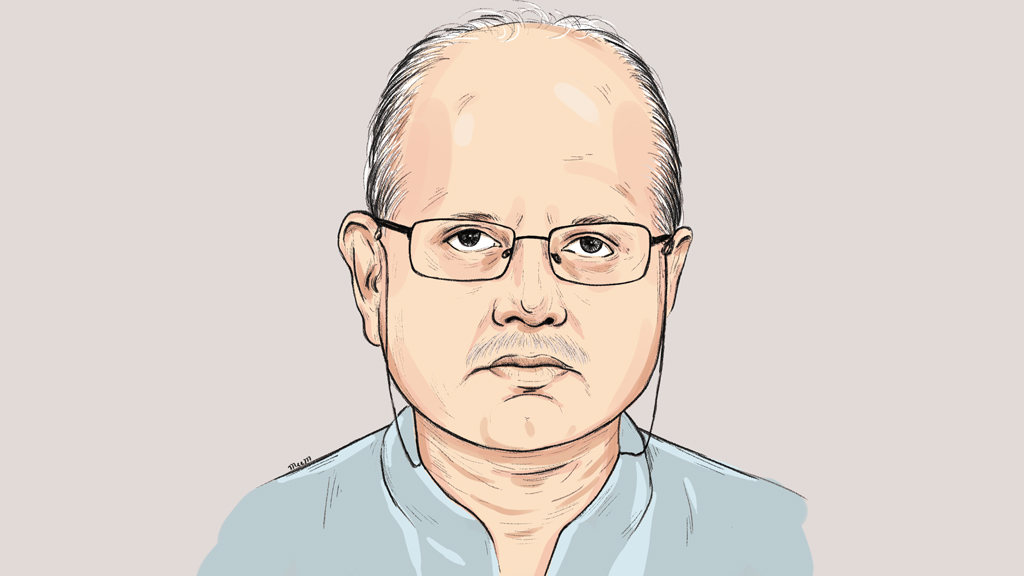
দত্তবাড়ির পর বোদার চন্দবাড়ির কথা না লিখলে চলে না। দত্তবাড়ির মতো চন্দবাড়িতেও আছে আমার সহপাঠী ও বন্ধু। আবার দত্ত ও চন্দবাড়ির মধ্যেও আছে পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক।
বোদার থানাপাড়া এখন অনেক বড়। অনেক বাড়িঘর। আর আমাদের ছোটবেলায় থানা, ওয়াপদা অফিস এবং একদিকে চন্দবাড়ি, অন্যদিকে হকিকুল ডাক্তার সাহেবের বাড়ি ছাড়া আর কোনো বাড়িঘর ছিল বলে মনে পড়ে না।
উমেশ চন্দ্র চন্দ ও মন্মথ চন্দ দুই ভাই। উমেশ চন্দের দুই ছেলে সুধীর চন্দ্র চন্দ ও অধীর চন্দ্র চন্দ। উমেশ বাবুকে আমি দেখিনি। তবে মন্মথ বাবুকে দেখেছি। তাঁর বাড়ি অবশ্য থানাপাড়ায় ছিল না। তাঁর বাড়ি বাজার থেকে সিরাজ সরকার সাহেবের বাড়ি যেতে আগে পড়ত। হাতের বাঁয়ে। এখনো আছে সেই বাড়ি। মন্মথ চন্দের মেয়ে ছায়াদিকে বিয়ে করেন দত্তবাড়ির শিবেন দত্ত।
উমেশ চন্দের দুই ছেলের থানাপাড়ার বাসায় আমার ছিল অবাধ যাতায়াত। বড় ছেলে সুধীর চন্দের তিন ছেলে ও তিন মেয়ে। শিবানী চন্দ, কল্যাণী চন্দ (সুনু), সুধাংশু চন্দ (স্বপন), নারায়ণী চন্দ (বেণু), হিমাংশু চন্দ (তপন/তপু) ও প্রবীর চন্দ (নয়ন)। শিবানী চন্দকে আমি দেখিনি। তিনি অবিভক্ত ভারতের জলপাইগুড়িতে মামাবাড়িতে একেবারে ছোট থেকেই বড় হয়েছেন। আর দেশে আসেননি। অন্য সবাই বোদায় ছিলেন বা আছেন। এর মধ্যে স্বপনদা অকালপ্রয়াত। সুনুদি, স্বপনদা ও বেণু আমার বড়। তবে বড় হলেও বেণু আর তপু আমার সহপাঠী। পরে সম্ভবত ক্লাস ফাইভ থেকে বেণু আমার ‘জুনিয়র’ হয়ে যায়। আর তপু হয়ে ওঠে আমার প্রিয় বন্ধুদের একজন। আমি, তপু ও দত্তবাড়ির বিজন—এই তিনজন ছিলাম (দেখা-সাক্ষাৎ কম হলেও এখনো আছি) ‘এক দেহ, এক প্রাণ’। কত কথাই না মনে পড়ছে। একটি ঘটনার কথা না বলে পারছি না। হাইস্কুলে পড়ার সময় আমরা কয়েকজন (এর মধ্যে বিজন, তপু আর আমি কমন) প্রতি বৃহস্পতিবার টিফিনের সময় স্কুল পালিয়ে ঠাকুরগাঁওয়ে যেতাম সিনেমা দেখার জন্য। শুক্রবার নতুন ছবি শুরু হতো, কাজেই বৃহস্পতিবার আমরা বিদায়ী ছবিটা দেখতাম। বলাকা টকিজ নামের সিনেমা হলটির মালিক ছিলেন মির্জা রুহুল আমিন (চখা মিয়া নামে সমধিক পরিচিত)। তিনি ছিলেন বর্তমান বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বাবা এবং সাবেক সেনাপ্রধান ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সাবেক সদস্য লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মাহবুবুর রহমানের শ্বশুর।
স্কুল থেকে পালিয়ে আমরা একত্রিত হতাম সাতখামারে শামসুদ্দিন ডাক্তার সাহেবের ডিসপেনসারিতে। দুপুরবেলা ওটা ফাঁকা থাকত। আমার বাড়ি ছিল তার পাশেই। ওটা ছিল ঠাকুরগাঁওয়ে যাওয়ার সড়কের একেবারে লাগোয়া। বাসস্ট্যান্ড থেকে বাসে উঠলে কেউ দেখে ফেলতে পারে—এই আশঙ্কা থেকেই আমরা একটু এগিয়ে গিয়ে বাসে উঠতাম। প্রবাদ আছে, ‘যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে রাত হয়’। একদিন আমাদের শামসুদ্দিন ডাক্তার চাচার ডিসপেনসারিতে জটলারত অবস্থায় দেখতে পান ডা. ফয়জুল করিম, আমাদের মশিয়ারের (মশিয়ার রহমান, এখন পল্লি কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা) বাবা। আমরা যে স্কুল পালিয়ে ওখানে সমবেত হয়েছি, সেটা তিনি বুঝতে পারেন। তিনি সম্ভবত রোগী দেখে সাইকেলে চেপে ফিরছিলেন। তিনি নিজে আমাদের কিছু বললেন না। তবে বাজারে গিয়ে তপুর বাবা সুধীর কাকুকে বিষয়টি অবগত করেন। কাকু দ্রুত ছুটে আসেন এবং আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই তপুকে পাকড়াও করে পায়ের কাবলি স্যান্ডেল দিয়ে বেদম পেটাতে থাকেন। তপু চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে মিনতি করে বলতে থাকে, ‘দোহাই বাবা, আর মেরো না।’ কাকু কোনো কথা শোনেন না। একপর্যায়ে পিটিয়ে ক্লান্ত হয়ে আমাদের সবাইকে শাসিয়ে তিনি চলে যান। আমরা ভাবলাম, অত পিটুনি খেয়ে তপু হয়তো আর সিনেমা দেখতে যাবে না। কিন্তু আমাদের অবাক করে তপু বলল, ‘মার তো খেয়েই ফেলেছি, তাহলে আর সিনেমা দেখা থেকে বঞ্চিত হব কেন?’
তপু ছিল আমাদের বন্ধুদের মধ্য সবচেয়ে ছোটখাটো। তাই ওকে নিয়ে কত ধরনের কাণ্ডই না আমরা করতাম। সেই তপু, হিমাংশু চন্দ এখন ঠাকুরগাঁওয়ে একটি বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) প্রধান নির্বাহী। তপুও খুব সরল মনের সাদাসিধে মানুষ। জীবনে টাকা-পয়সা যেমন উপার্জন করেছে, তেমন খরচও করেছে। ওর বাবা, আমাদের সুধীর কাকুও ছিলেন অত্যন্ত দরাজ দিল মানুষ। আমি তাঁর কাছ থেকে যে স্নেহ-ভালোবাসা পেয়েছি, তা বলে শেষ করা যাবে না।
আমার বন্ধু তপুর বাবা, আমাদের সুধীর কাকু ছিলেন আমার দেখা ‘অসাধারণ’ মানুষদের একজন। দেখতে ছিলেন সুদর্শন। অমন উন্নত নাক, গৌর বর্ণ, মাথা উঁচু করে হাঁটাচলা করা; দেখলেই মনের মধ্যে একটি সমীহ ভাব চলে আসত। তাঁকে আমরা একধরনের ভয়মিশ্রিত সমীহই করতাম। একেবারে ছোটবেলায় এড়িয়ে চলতাম। আস্তে আস্তে যতই তাঁর নৈকট্য লাভ করেছি, ততই মনে হয়েছে তাঁর মনের ভেতরটা কত নরম। পরিণত বয়সেও তিনি ঝুনা নারকেল না হয়ে কচি ডাবের মতোই ছিলেন।
প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন একজন নামকরা ফুটবল খেলোয়াড়। জলপাইগুড়ি জেলায়ও তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। আমরা ছোটবেলায়ও তাঁকে বোদা হাইস্কুল মাঠে শৌখিন খেলোয়াড় হিসেবে খেলতে দেখেছি। সুধীর কাকু, ডা. ফয়জুল চাচারা মাঠে নামলে জমে উঠত খেলা। তরুণদের উৎসাহিত করার জন্যই সে সময় তাঁরা নিয়মিত মাঠে যেতেন।
তপুর মা, মানে আমাদের কাকি মারা যান সম্ভবত ১৯৫৭ সালে। আমি হয়তো তাঁকে দেখিওনি। শুনেছি নয়নের তখন মাত্র দেড় বছর বয়স। তপুর তিন-সাড়ে তিন। কাজেই মায়ের কোনো স্মৃতি ওদের মনে থাকার কথা নয়। ওরা প্রকৃতপক্ষে মাতৃস্নেহে বড় হয়েছে দিদিমার কাছে। দিদিমা সরজুবালা দেবী ছিলেন সুধীর কাকুর মাসিমা। তিনি বাল্যবিধবা। বিয়ের অল্প পরই স্বামীহারা হয়ে সুধীর কাকুর সংসারে স্থায়ী হয়েছিলেন। তপু ও নয়ন এই দিদিমার কোলেপিঠে মানুষ। তাই তিনি ছিলেন ওদের মা, দিদিমা নয়!
এই মহীয়সী নারীকে যাঁরা না দেখেছেন, তাঁরা তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কোনো ধারণা করতে পারবেন না। তিনিই কার্যত চন্দবাড়িতে অভিভাবক ছিলেন। তাঁর ছায়া-মায়ায় তপুরা ভাইবোন মানুষ হয়েছে। আরও একজন তপুদের মায়ের অভাব পূরণে বড় ভূমিকা রেখেছেন—তপুদের কাকিমা, অধীর কাকুর স্ত্রী। এই কাকিমার নাম রেখা রানী চন্দ। নিজের তিন মেয়ে ও দুই ছেলেসন্তানের সঙ্গে ভাশুরের সন্তানদেরও তিনি অকৃপণ স্নেহ-ভালোবাসা দিয়েছেন।
সুধীর কাকুর স্ত্রীবিয়োগের পর অনেকে তাঁকে আবার বিয়ে করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তখন এমন রেওয়াজ ছিল, কিন্তু প্রথম স্ত্রীর প্রতি গভীর ভালোবাসা তাঁকে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণে নিরুৎসাহিত করেছিল। একসময় আমি চন্দবাড়ির সদস্যের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। ওই বাড়ির হাঁড়িতে আমার জন্য দুমুঠো চাল যেন দেওয়াই থাকত। আমি গেলে দিদিমা, কাকিমা কেউ বিরক্ত না হয়ে খুশি হতেন। হাসিমুখেই আমাকে স্বাগত জানাতেন। দিদিমা আর নেই। প্রায় ৯০ বছর বয়সে তিনি পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেছেন। কাকিমা এখনো সক্রিয় আছেন, সেঞ্চুরি করার অপেক্ষায়।
তপুর কাকাতো বোন রেবা রানী চন্দ; ডাক নাম পুতুল। আমাদের ছোট। দেখতে অনেকটা পুতুলের মতোই ছিল। আমি একটু বড় হওয়ার পর, অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ই মনে হয়, কেউ কেউ পুতুলের সঙ্গে আমার বিয়ের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করতেন বলে আমি শুনেছি। তবে বিষয়টি জোরালো হয়ে ওঠেনি।
তপুদের ভাইবোনেরা সবাই মুক্ত মনের অধিকারী। তপু আমার বন্ধু। ওর সঙ্গে মাখামাখি সম্পর্ক হওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু ওর বড় ভাই স্বপনদা এবং ছোট ভাই নয়নের সঙ্গেও গোড়া থেকেই আমার সম্পর্ক অত্যন্ত প্রীতিময়। নয়ন এখন বোদার একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি। কলেজে অধ্যাপনা থেকে সম্প্রতি অবসর নিয়ে সংস্কৃতি-সাহিত্য-সমাজ নিয়ে কাজ করেন, লেখালেখি করেন। কবিতা ও গদ্যে সমান পারদর্শী।
এই পরিবারের সঙ্গে আমার অতি ঘনিষ্ঠতার আরেকটি বড় কারণ বোধ হয় এটাই যে, এরা সবাই কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক ছিলেন। পার্টির সদস্য না হয়েও এরা ছিলেন পার্টি অন্তপ্রাণ। এ রকম পরিবার বোদায় আরও দু-চারটি ছিল।
চন্দবাড়ির সুধীর চন্দের জন্ম ১৯১৭ সালের কোনো এক বুধবার। ওই বছর পৃথিবীতে প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল। অক্টোবর বিপ্লব বলে পরিচিত সেই বিপ্লবের অভিঘাত তখনই বোদায় গিয়ে পৌঁছানোর কথা নয়। তাই সুধীর চন্দের চেতনায় বিপ্লব আঘাত হানেনি। তবে একধরনের উদার মানবতাবাদী চেতনার বিকাশ তাঁর মধ্যে লক্ষ করা গেছে। তাঁর বাড়ির পরিবেশ যে কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন হয়েছিল, সেটা আগে উল্লেখ করেছি। একটি কাকতালীয় ব্যাপার হলো তাঁর জন্ম এবং মৃত্যু একই বারে। বুধবার। ২০০০ সালের এক বুধবার তিনি চলে যান না ফেরার দেশে। প্রায় ৮৩ বছরের জীবন পেয়েছিলেন তিনি।
সুধীর চন্দ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাস করেছিলেন সম্ভবত ১৯৩৭ সালে। তাঁর সঙ্গে একই বছর প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেছিলেন বোদা হাইস্কুলের শিক্ষক সেলিমের বাবা সিদ্দিক সাহেব। ম্যাট্রিক পাসের পর সুধীর চন্দ আর পড়াশোনা না করে চাকরিতে ঢোকেন। তিনি অবিভক্ত ভারতেই জুট করপোরেশনে প্রথম চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। বন বিভাগেও নাকি তাঁর চাকরি হয়েছিল। সাপ, মশা ইত্যাদির ভয়ে তিনি সেই চাকরিতে যোগ দেননি।
ব্রিটিশরা ভারত ভাগ করে পাকিস্তান ও ভারত দুই রাষ্ট্রের জন্ম দিয়ে ১৯৪৭ সালে বিদায় নেয়। সে সময় সুধীর চন্দ তৎকালীন পাকিস্তানে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তখন তাঁর চাকরি ন্যস্ত হয় ডিসি কালেক্টরে তহসিল অফিসে, তহসিলদার হিসেবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় পর্যন্ত তিনি ওই চাকরি করেছেন। বোদা ছাড়াও দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ও সেতাবগঞ্জে তিনি তহসিলদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। স্বাধীনতার পর তিনি লুথার্ন ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন নামের একটি সাহায্য সংস্থায় চাকরি নেন। পরে এই সংগঠন আরডিআরএস নামে রূপান্তরিত হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে এই সংস্থা অনেক বড় ভূমিকা পালন করেছিল। তখন ঠাকুরগাঁও কলেজে পড়াশোনার পাশাপাশি বেশ কিছুদিন আরডিআরএসের কনস্ট্রাকশন বিভাগে কাজ করেছে আমার বন্ধু হিমাংশু চন্দ তপন বা তপু। বেশ কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিধ্বস্ত ভবন নতুন করে তৈরির কাজ তদারকির দায়িত্ব পালন করেছে তপু। সুধীর কাকু আরডিআরএসের চাকরি করেছেন ১৯৮০ সাল পর্যন্ত। ফলে তিনি স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে ঠাকুরগাঁওয়েই বসবাস করেছেন। বাসা ভাড়া নিয়ে দুই ছেলেকে নিয়ে তিনি থাকতেন। তপু ও নয়ন ঠাকুরগাঁও কলেজে পড়ত। তপু ওই কলেজ থেকে বিএ পাস করেছে আর নয়ন এইচএসসি পাস করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। দর্শনশাস্ত্রে মাস্টার্স করে বোদায় ফিরে পাথরাজ কলেজে শিক্ষকতা শুরু করে। তপু বিয়েশাদি করে ঠাকুরগাঁওয়েই স্থায়ী হয়েছে।
তপুদের ঠাকুরগাঁওয়ের বাসায়ও নানা কারণে আমাকে বহুদিন রাত কাটাতে হয়েছে এবং পাত পাততে হয়েছে। তখন ঢাকায় আসার জন্য আমাকে হয় দিনাজপুর অথবা ঠাকুরগাঁও থেকে গাড়ি ধরতে হতো। পঞ্চগড় থেকে কোনো কোচ ডে কিংবা নাইট তখনো চালু হয়নি। ঢাকা থেকে বাড়ি যাওয়া এবং বাড়ি থেকে ঢাকায় আসার জন্য ঠাকুরগাঁওয়ে আমার রাত্রিকালীন অবস্থান হতো তপুদের বাসায়। রান্নাঘরে একসঙ্গে বসে আমরা চারজন রাতের খাবার খেতাম। সুধীর কাকু পরম মমতায় আমাকে পুত্রবৎ পাশে বসাতেন। আহা, কত প্রীতিময় ছিল সেই দিনগুলো!
আগেই বলেছি, কাকু ছিলেন একজন ভালো ফুটবল খেলোয়াড়। তিনি জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাবের ক্যাপ্টেন ছিলেন। তিনি সাত-আটবার ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (আইএফএ) শিল্ড কাপ খেলেছেন। ট্রফি জিতেছেন। হেড করে গোল করায় তিনি খুব পারদর্শী ছিলেন। তখন মাঝগ্রামের আবদুর রহমান সাহেবও ভালো ফুটবল খেলতেন। তাঁর কর্নার কিক মানেই ছিল অবধারিত গোল। সে জন্যই তখন বলা হতো সুধীর চন্দের হেড আর আব্দুর রহমানের কর্নার কিক ইকুয়াল টু গোল। তিনি রংপুর ও দিনাজপুরে গিয়েও খেলেছেন।
সুধীর কাকু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছেন। অস্ত্র হাতে সম্মুখ সমরে অংশ না নিলেও শরণার্থীশিবিরে আশ্রয় নেওয়া মানুষদের নানা উপায়ে সাহায্য-সহযোগিতায় ছিলেন সদা তৎপর। যেসব রাজনৈতিক নেতাকর্মী ওপারে গিয়েছিলেন, তাঁদের জন্য বড় সহায় ছিলেন সুধীর কাকু। কিন্তু কিছু মানুষ যেমন যুদ্ধ শেষের পাওনা বুঝে নেওয়ার জন্য বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন, সুধীর কাকু ছিলেন সেখানে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।
চন্দবাড়ির স্বপনদা ছিলেন হাসিখুশি স্বভাবের, একটু যেন আপনভোলা মানুষ। সংসার করেছেন। কিন্তু প্রকৃত সংসারী বলতে যা বোঝায়, তিনি তা ছিলেন কি না, আমার সন্দেহ আছে। মাথার ওপর সুধীর কাকুর মতো বটবৃক্ষসম বাবা থাকলে অমনই বোধ হয় হওয়ার কথা।
স্বপনদা আমার বড়। বন্ধুর বড় ভাই। কিন্তু আমাদের মধ্যে একধরনের বন্ধুত্বের সম্পর্কই গড়ে উঠেছিল। তিনি আমার সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলতেন। রাজনীতি সচেতন ছিলেন। দেশ-দুনিয়া সম্পর্কে খোঁজখবর রাখতেন। নিয়মিত খবরের কাগজ পড়তেন।
১৯৭৩ সালের নির্বাচনে আমাদের এলাকা থেকে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন কামু ভাই, অ্যাডভোকেট কামরুল হোসেন। মনে আছে, ওই নির্বাচনী প্রচারে আমি আর স্বপনদা একসঙ্গে অনেক জায়গায় গিয়েছি। বিভিন্ন গ্রাম বা ইউনিয়নে আমাদের উভয়ের পরিচিতদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ভোট প্রার্থনা করেছি। আমি সাইকেল চালাতে পারতাম না। স্বপনদা সাইকেল চালিয়ে আমাকে নিয়ে যেতেন। তখন গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট ভালো ছিল না। আলপথে অনেক কষ্ট করেই আমাদের যেতে হতো। হাসিমুখেই এই কষ্টকর কাজটি স্বপনদা করতেন। আমরা বুঝতে পারতাম, জনমত আমাদের অনুকূলে নয়। তার পরও কিসের আশায়, কিসের নেশায় যে দিনরাত গ্রাম থেকে গ্রামে, বাড়ি থেকে বাড়ি ছুটে বেড়াতাম!
আমি ঢাকায় আসার পর স্বপনদার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই যোগাযোগ কমে গিয়েছিল। তার পরও ছুটিছাঁটায় বোদায় গেলে স্বপনদা ছুটে আসতেন। কত জিজ্ঞাসা নিয়ে আমার কাছে সেসবের উত্তর জানতে চাইতেন। তাঁর সব কৌতূহল মেটানোর সাধ্য আমার ছিল না। এর মধ্যে একটি দুর্ঘটনায় স্বপনদা একটি পা হারান। তিনি ক্র্যাচে ভর দিয়ে এক পায়ে হাঁটতেন। শেষদিকে সম্ভবত ছাত্র পড়িয়ে উপার্জন করতেন। ২০০৩ সালে স্বপনদার মৃত্যু হয়। তিনি রেখে গেছেন দুই মেয়ে ও এক ছেলেসন্তান। বৌদি তাঁর দেবরদের সহযোগিতায় ছেলেমেয়েদের মানুষ করেছেন। বড় মেয়ে চৈতালি চন্দ সোমার বর ঝাড়বাড়ি কলেজের অর্থনীতির সহকারী অধ্যাপক। ছোট মেয়ে বিপাশা চন্দ দোলন বরিশালে বিয়ে হলেও এখন সম্ভবত বোদাতেই আছে। ছেলে সৌমিত চন্দ জয়দ্বীপ কৃতী ছাত্র। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করে ভারতের গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি সম্পন্ন করে ঢাকায় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছে। জয়দ্বীপ জাহাঙ্গীরনগরে ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ছিল, সভাপতি হয়েছিল। বাম রাজনীতিতে তাঁর আগ্রহ হয়তো এখনো বহাল আছে। গুজরাটে যাওয়ার আগে দৈনিক সমকালে কিছুদিন সাংবাদিকতা করেছে। লেখালেখির হাত ভালো। এর মধ্যেই গবেষণামূলক কিছু গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লিখে সুনাম অর্জন করেছে।
আমার বন্ধু হিমাংশু তপুও একজন সফল মানুষ। ঠাকুরগাঁওয়ে ওর একটি এনজিও আছে। অনেকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। ছাত্রাবস্থাতেই তপু উপার্জনমুখী হয়েছে। প্রথমে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি, তারপর ঠাকুরগাঁওয়ে একটি কসমেটিকসের দোকান এবং সব শেষে শার্প নামে এনজিও প্রতিষ্ঠা। নানা ধরনের সামাজিক কাজকর্মেও তপু সময় দেয়। ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েও ছাত্রাবস্থায় তপুর ভেতরের এত প্রতিভা সম্পর্কে আমরা কিছু আন্দাজ করতে পারিনি। তপুর একমাত্র ছেলে বুদ্ধদেব চন্দ তমাল কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ করে এসে এখন বগুড়ায় একটি বেসরকারি ব্যাংকের কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করছে। তমাল বিয়ে করে এক সন্তানের জনকও হয়েছে। আমার বন্ধু তপু গর্বিত দাদু হিসেবে পরিতৃপ্তি নিয়ে সংসার করছে।
ভাইদের মধ্যে ছোট প্রবীর চন্দ নয়ন। মূলত সে-ই এখন চন্দবাড়ির অভিভাবক। বোদার একজন সচেতন ও সংস্কৃতি মনস্ক মানুষ। দর্শনশাস্ত্রে পড়াশোনা করেও সাহিত্যে তাঁর অনুরাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন থেকেই। নিয়মিত কবিতা এবং নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে থাকে। দুটি কবিতার বইও বের হয়েছে। দুটি প্রবন্ধের বই প্রকাশের অপেক্ষায়। তার স্ত্রীও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ছেলে শুভ্র প্রতিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ করে একটি অ্যাড ফার্মে চাকরি করছে। মেয়ে দেবলীনা দৈবী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের ছাত্রী।
চন্দবাড়ির মেয়েদের কথা কিছু না বললেই নয়। সুধীর চন্দের বড় মেয়ে জলপাইগুড়িতে থেকেছেন বলে তাঁর সঙ্গে আমার কখনো দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দু-তিনবার তিনি বোদায় এসেছেন। আমি তখন বোদা ছেড়েছি। ফলে শিবানী চন্দ আমার অদেখা বড় দিদি। কল্যাণী; অর্থাৎ সুনুদিই হলেন আমাদের দেখা বড় দিদি। কী হাসিখুশি মানুষ সুনুদি! মানুষকে আপন করে নেওয়ার শক্তি যেমন তাঁর আছে, তেমনি আছে প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে এগিয়ে চলার প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস।
আমাদের ছোটবেলায় সুনুদির বিয়ে হয়। প্রেমের বিয়ে। মধু জামাইবাবুও খুব সুন্দর ছিলেন। সুনুদি তো অবশ্যই সুন্দরী। ভালোই চলছিল সব। সময় গড়িয়ে দুটি ফুটফুটে পুত্রসন্তানের জনক-জননী হন তাঁরা। তারপর যে কোথা থেকে কী হয়। জামাইবাবুকে আর বোদায় দেখা যায় না। তিনি সংসারত্যাগী হন। কী দুঃসহ মর্মজ্বালা বুকে চেপে সুনুদি তাঁর দুই ছেলে মিহির ও বিজনকে মানুষ করার কাজটি সম্পন্ন করেছেন, তা ভুক্তভোগী ছাড়া কারও পক্ষে বোঝা কঠিন। বাবা এবং পরিবারের সহযোগিতা-সমর্থন তিনি পেয়েছেন। কিন্তু আমাদের কুচুটে সমাজের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করা যে কত কঠিন, সেটা না বললেও চলে। সুনুদি প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর ছোট ছেলে বিজন সরকারও একটি প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। বড় ছেলে মিহির সরকার একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করত বলে শুনেছিলাম।
চন্দবাড়ির আরেক মেয়ে বেণু ওরফে নারায়ণী চন্দ, আমার বন্ধু এবং মামি। আমার মায়ের কোনো ভাইবোন নেই। তিনি বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। তবে মায়ের কয়েকজন পাতানো ভাই আছে, যারা আমার মামা। এ রকম একজন হলেন নারায়ণ চন্দ্র সাহা। ঢাকার বিক্রমপুরে বাড়ি। চাকরির সুবাদে বোদায় যান গত শতকের ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে। তিনি কিছুদিন লজিং থাকতেন আমার পিসার বাসায়; অর্থাৎ কার্তিকদা-জ্যোতিষদাদের বাসায়। তখন অবশ্য পিসেমশাই শরৎ চন্দ্র সরকার জীবিত ছিলেন। যা হোক, ওই বাসায় লজিং থাকার সুবাদেই হয়তো আমার মায়ের ভাই হয়ে যান নারায়ণ সাহা। আমার মামা। এই মামাই বিয়ে করেন চন্দবাড়ির মেয়ে বেণুকে। বন্ধু হেয় গেল মামি। বিয়ের পর নতুন সংসার গোছানোর আগে কিছুদিন তাঁরা আমাদের বাড়িতেই ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এই পরিবারের সঙ্গেও আমার অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। একসময় এমনও ছিল যে, ঢাকা থেকে বাড়ি গেলে রাতটা আমি নারায়ণ মামার বাসাতেই কাটাতাম। ততদিনে তাঁদের মেয়ে ও ছেলে বড় হয়ে উঠতে শুরু করেছে। একটি বিষয় লক্ষণীয়। মামার নাম নারায়ণ আর যাকে বিয়ে করলেন তাঁর নাম নারায়ণী। আমাকে আমার দু-এক বন্ধু তখন ঠাট্টা করে বলত, আমার স্ত্রীর নাম নাকি হবে হয় বিভা, না হয় রঞ্জনা! না, সেটা হয়নি।
বেণুও প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করেছে। ছেলে বাপ্পা ওরফে স্বরূপ সাহা এসএসসি পাস করে কলকাতায় চলে যায়। এমবিএ পাস করে বাপ্পা এখন বেঙ্গালুরুতে আছে বলে শুনেছি। বাপ্পা আমাকে মামা বলে ডাকে। কী অদ্ভুত সামাজিক সম্পর্কগুলো! বেণুর মেয়ে শম্পা কিছুদিন ঢাকায় ছিল। তারপর নাকি আমেরিকায় চলে গেছে। নারায়ণ মামার জীবনাবসান হয়েছে। মামি এখন অবসরজীবন যাপন করছেন।
নটে গাছটি মুড়োল, চন্দবাড়ির গল্প ফুরোল।
লেখক: সহকারী সম্পাদক, আজকের পত্রিকা
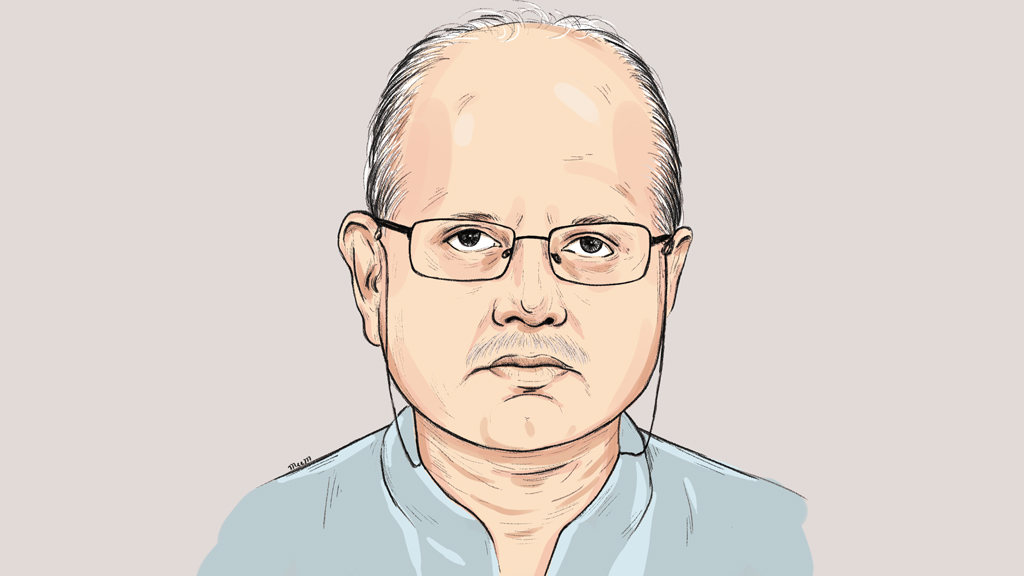
দত্তবাড়ির পর বোদার চন্দবাড়ির কথা না লিখলে চলে না। দত্তবাড়ির মতো চন্দবাড়িতেও আছে আমার সহপাঠী ও বন্ধু। আবার দত্ত ও চন্দবাড়ির মধ্যেও আছে পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক।
বোদার থানাপাড়া এখন অনেক বড়। অনেক বাড়িঘর। আর আমাদের ছোটবেলায় থানা, ওয়াপদা অফিস এবং একদিকে চন্দবাড়ি, অন্যদিকে হকিকুল ডাক্তার সাহেবের বাড়ি ছাড়া আর কোনো বাড়িঘর ছিল বলে মনে পড়ে না।
উমেশ চন্দ্র চন্দ ও মন্মথ চন্দ দুই ভাই। উমেশ চন্দের দুই ছেলে সুধীর চন্দ্র চন্দ ও অধীর চন্দ্র চন্দ। উমেশ বাবুকে আমি দেখিনি। তবে মন্মথ বাবুকে দেখেছি। তাঁর বাড়ি অবশ্য থানাপাড়ায় ছিল না। তাঁর বাড়ি বাজার থেকে সিরাজ সরকার সাহেবের বাড়ি যেতে আগে পড়ত। হাতের বাঁয়ে। এখনো আছে সেই বাড়ি। মন্মথ চন্দের মেয়ে ছায়াদিকে বিয়ে করেন দত্তবাড়ির শিবেন দত্ত।
উমেশ চন্দের দুই ছেলের থানাপাড়ার বাসায় আমার ছিল অবাধ যাতায়াত। বড় ছেলে সুধীর চন্দের তিন ছেলে ও তিন মেয়ে। শিবানী চন্দ, কল্যাণী চন্দ (সুনু), সুধাংশু চন্দ (স্বপন), নারায়ণী চন্দ (বেণু), হিমাংশু চন্দ (তপন/তপু) ও প্রবীর চন্দ (নয়ন)। শিবানী চন্দকে আমি দেখিনি। তিনি অবিভক্ত ভারতের জলপাইগুড়িতে মামাবাড়িতে একেবারে ছোট থেকেই বড় হয়েছেন। আর দেশে আসেননি। অন্য সবাই বোদায় ছিলেন বা আছেন। এর মধ্যে স্বপনদা অকালপ্রয়াত। সুনুদি, স্বপনদা ও বেণু আমার বড়। তবে বড় হলেও বেণু আর তপু আমার সহপাঠী। পরে সম্ভবত ক্লাস ফাইভ থেকে বেণু আমার ‘জুনিয়র’ হয়ে যায়। আর তপু হয়ে ওঠে আমার প্রিয় বন্ধুদের একজন। আমি, তপু ও দত্তবাড়ির বিজন—এই তিনজন ছিলাম (দেখা-সাক্ষাৎ কম হলেও এখনো আছি) ‘এক দেহ, এক প্রাণ’। কত কথাই না মনে পড়ছে। একটি ঘটনার কথা না বলে পারছি না। হাইস্কুলে পড়ার সময় আমরা কয়েকজন (এর মধ্যে বিজন, তপু আর আমি কমন) প্রতি বৃহস্পতিবার টিফিনের সময় স্কুল পালিয়ে ঠাকুরগাঁওয়ে যেতাম সিনেমা দেখার জন্য। শুক্রবার নতুন ছবি শুরু হতো, কাজেই বৃহস্পতিবার আমরা বিদায়ী ছবিটা দেখতাম। বলাকা টকিজ নামের সিনেমা হলটির মালিক ছিলেন মির্জা রুহুল আমিন (চখা মিয়া নামে সমধিক পরিচিত)। তিনি ছিলেন বর্তমান বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বাবা এবং সাবেক সেনাপ্রধান ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সাবেক সদস্য লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মাহবুবুর রহমানের শ্বশুর।
স্কুল থেকে পালিয়ে আমরা একত্রিত হতাম সাতখামারে শামসুদ্দিন ডাক্তার সাহেবের ডিসপেনসারিতে। দুপুরবেলা ওটা ফাঁকা থাকত। আমার বাড়ি ছিল তার পাশেই। ওটা ছিল ঠাকুরগাঁওয়ে যাওয়ার সড়কের একেবারে লাগোয়া। বাসস্ট্যান্ড থেকে বাসে উঠলে কেউ দেখে ফেলতে পারে—এই আশঙ্কা থেকেই আমরা একটু এগিয়ে গিয়ে বাসে উঠতাম। প্রবাদ আছে, ‘যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে রাত হয়’। একদিন আমাদের শামসুদ্দিন ডাক্তার চাচার ডিসপেনসারিতে জটলারত অবস্থায় দেখতে পান ডা. ফয়জুল করিম, আমাদের মশিয়ারের (মশিয়ার রহমান, এখন পল্লি কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা) বাবা। আমরা যে স্কুল পালিয়ে ওখানে সমবেত হয়েছি, সেটা তিনি বুঝতে পারেন। তিনি সম্ভবত রোগী দেখে সাইকেলে চেপে ফিরছিলেন। তিনি নিজে আমাদের কিছু বললেন না। তবে বাজারে গিয়ে তপুর বাবা সুধীর কাকুকে বিষয়টি অবগত করেন। কাকু দ্রুত ছুটে আসেন এবং আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই তপুকে পাকড়াও করে পায়ের কাবলি স্যান্ডেল দিয়ে বেদম পেটাতে থাকেন। তপু চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে মিনতি করে বলতে থাকে, ‘দোহাই বাবা, আর মেরো না।’ কাকু কোনো কথা শোনেন না। একপর্যায়ে পিটিয়ে ক্লান্ত হয়ে আমাদের সবাইকে শাসিয়ে তিনি চলে যান। আমরা ভাবলাম, অত পিটুনি খেয়ে তপু হয়তো আর সিনেমা দেখতে যাবে না। কিন্তু আমাদের অবাক করে তপু বলল, ‘মার তো খেয়েই ফেলেছি, তাহলে আর সিনেমা দেখা থেকে বঞ্চিত হব কেন?’
তপু ছিল আমাদের বন্ধুদের মধ্য সবচেয়ে ছোটখাটো। তাই ওকে নিয়ে কত ধরনের কাণ্ডই না আমরা করতাম। সেই তপু, হিমাংশু চন্দ এখন ঠাকুরগাঁওয়ে একটি বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) প্রধান নির্বাহী। তপুও খুব সরল মনের সাদাসিধে মানুষ। জীবনে টাকা-পয়সা যেমন উপার্জন করেছে, তেমন খরচও করেছে। ওর বাবা, আমাদের সুধীর কাকুও ছিলেন অত্যন্ত দরাজ দিল মানুষ। আমি তাঁর কাছ থেকে যে স্নেহ-ভালোবাসা পেয়েছি, তা বলে শেষ করা যাবে না।
আমার বন্ধু তপুর বাবা, আমাদের সুধীর কাকু ছিলেন আমার দেখা ‘অসাধারণ’ মানুষদের একজন। দেখতে ছিলেন সুদর্শন। অমন উন্নত নাক, গৌর বর্ণ, মাথা উঁচু করে হাঁটাচলা করা; দেখলেই মনের মধ্যে একটি সমীহ ভাব চলে আসত। তাঁকে আমরা একধরনের ভয়মিশ্রিত সমীহই করতাম। একেবারে ছোটবেলায় এড়িয়ে চলতাম। আস্তে আস্তে যতই তাঁর নৈকট্য লাভ করেছি, ততই মনে হয়েছে তাঁর মনের ভেতরটা কত নরম। পরিণত বয়সেও তিনি ঝুনা নারকেল না হয়ে কচি ডাবের মতোই ছিলেন।
প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন একজন নামকরা ফুটবল খেলোয়াড়। জলপাইগুড়ি জেলায়ও তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। আমরা ছোটবেলায়ও তাঁকে বোদা হাইস্কুল মাঠে শৌখিন খেলোয়াড় হিসেবে খেলতে দেখেছি। সুধীর কাকু, ডা. ফয়জুল চাচারা মাঠে নামলে জমে উঠত খেলা। তরুণদের উৎসাহিত করার জন্যই সে সময় তাঁরা নিয়মিত মাঠে যেতেন।
তপুর মা, মানে আমাদের কাকি মারা যান সম্ভবত ১৯৫৭ সালে। আমি হয়তো তাঁকে দেখিওনি। শুনেছি নয়নের তখন মাত্র দেড় বছর বয়স। তপুর তিন-সাড়ে তিন। কাজেই মায়ের কোনো স্মৃতি ওদের মনে থাকার কথা নয়। ওরা প্রকৃতপক্ষে মাতৃস্নেহে বড় হয়েছে দিদিমার কাছে। দিদিমা সরজুবালা দেবী ছিলেন সুধীর কাকুর মাসিমা। তিনি বাল্যবিধবা। বিয়ের অল্প পরই স্বামীহারা হয়ে সুধীর কাকুর সংসারে স্থায়ী হয়েছিলেন। তপু ও নয়ন এই দিদিমার কোলেপিঠে মানুষ। তাই তিনি ছিলেন ওদের মা, দিদিমা নয়!
এই মহীয়সী নারীকে যাঁরা না দেখেছেন, তাঁরা তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কোনো ধারণা করতে পারবেন না। তিনিই কার্যত চন্দবাড়িতে অভিভাবক ছিলেন। তাঁর ছায়া-মায়ায় তপুরা ভাইবোন মানুষ হয়েছে। আরও একজন তপুদের মায়ের অভাব পূরণে বড় ভূমিকা রেখেছেন—তপুদের কাকিমা, অধীর কাকুর স্ত্রী। এই কাকিমার নাম রেখা রানী চন্দ। নিজের তিন মেয়ে ও দুই ছেলেসন্তানের সঙ্গে ভাশুরের সন্তানদেরও তিনি অকৃপণ স্নেহ-ভালোবাসা দিয়েছেন।
সুধীর কাকুর স্ত্রীবিয়োগের পর অনেকে তাঁকে আবার বিয়ে করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তখন এমন রেওয়াজ ছিল, কিন্তু প্রথম স্ত্রীর প্রতি গভীর ভালোবাসা তাঁকে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণে নিরুৎসাহিত করেছিল। একসময় আমি চন্দবাড়ির সদস্যের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। ওই বাড়ির হাঁড়িতে আমার জন্য দুমুঠো চাল যেন দেওয়াই থাকত। আমি গেলে দিদিমা, কাকিমা কেউ বিরক্ত না হয়ে খুশি হতেন। হাসিমুখেই আমাকে স্বাগত জানাতেন। দিদিমা আর নেই। প্রায় ৯০ বছর বয়সে তিনি পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেছেন। কাকিমা এখনো সক্রিয় আছেন, সেঞ্চুরি করার অপেক্ষায়।
তপুর কাকাতো বোন রেবা রানী চন্দ; ডাক নাম পুতুল। আমাদের ছোট। দেখতে অনেকটা পুতুলের মতোই ছিল। আমি একটু বড় হওয়ার পর, অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ই মনে হয়, কেউ কেউ পুতুলের সঙ্গে আমার বিয়ের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করতেন বলে আমি শুনেছি। তবে বিষয়টি জোরালো হয়ে ওঠেনি।
তপুদের ভাইবোনেরা সবাই মুক্ত মনের অধিকারী। তপু আমার বন্ধু। ওর সঙ্গে মাখামাখি সম্পর্ক হওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু ওর বড় ভাই স্বপনদা এবং ছোট ভাই নয়নের সঙ্গেও গোড়া থেকেই আমার সম্পর্ক অত্যন্ত প্রীতিময়। নয়ন এখন বোদার একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি। কলেজে অধ্যাপনা থেকে সম্প্রতি অবসর নিয়ে সংস্কৃতি-সাহিত্য-সমাজ নিয়ে কাজ করেন, লেখালেখি করেন। কবিতা ও গদ্যে সমান পারদর্শী।
এই পরিবারের সঙ্গে আমার অতি ঘনিষ্ঠতার আরেকটি বড় কারণ বোধ হয় এটাই যে, এরা সবাই কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক ছিলেন। পার্টির সদস্য না হয়েও এরা ছিলেন পার্টি অন্তপ্রাণ। এ রকম পরিবার বোদায় আরও দু-চারটি ছিল।
চন্দবাড়ির সুধীর চন্দের জন্ম ১৯১৭ সালের কোনো এক বুধবার। ওই বছর পৃথিবীতে প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল। অক্টোবর বিপ্লব বলে পরিচিত সেই বিপ্লবের অভিঘাত তখনই বোদায় গিয়ে পৌঁছানোর কথা নয়। তাই সুধীর চন্দের চেতনায় বিপ্লব আঘাত হানেনি। তবে একধরনের উদার মানবতাবাদী চেতনার বিকাশ তাঁর মধ্যে লক্ষ করা গেছে। তাঁর বাড়ির পরিবেশ যে কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন হয়েছিল, সেটা আগে উল্লেখ করেছি। একটি কাকতালীয় ব্যাপার হলো তাঁর জন্ম এবং মৃত্যু একই বারে। বুধবার। ২০০০ সালের এক বুধবার তিনি চলে যান না ফেরার দেশে। প্রায় ৮৩ বছরের জীবন পেয়েছিলেন তিনি।
সুধীর চন্দ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাস করেছিলেন সম্ভবত ১৯৩৭ সালে। তাঁর সঙ্গে একই বছর প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেছিলেন বোদা হাইস্কুলের শিক্ষক সেলিমের বাবা সিদ্দিক সাহেব। ম্যাট্রিক পাসের পর সুধীর চন্দ আর পড়াশোনা না করে চাকরিতে ঢোকেন। তিনি অবিভক্ত ভারতেই জুট করপোরেশনে প্রথম চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। বন বিভাগেও নাকি তাঁর চাকরি হয়েছিল। সাপ, মশা ইত্যাদির ভয়ে তিনি সেই চাকরিতে যোগ দেননি।
ব্রিটিশরা ভারত ভাগ করে পাকিস্তান ও ভারত দুই রাষ্ট্রের জন্ম দিয়ে ১৯৪৭ সালে বিদায় নেয়। সে সময় সুধীর চন্দ তৎকালীন পাকিস্তানে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তখন তাঁর চাকরি ন্যস্ত হয় ডিসি কালেক্টরে তহসিল অফিসে, তহসিলদার হিসেবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় পর্যন্ত তিনি ওই চাকরি করেছেন। বোদা ছাড়াও দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ও সেতাবগঞ্জে তিনি তহসিলদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। স্বাধীনতার পর তিনি লুথার্ন ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন নামের একটি সাহায্য সংস্থায় চাকরি নেন। পরে এই সংগঠন আরডিআরএস নামে রূপান্তরিত হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে এই সংস্থা অনেক বড় ভূমিকা পালন করেছিল। তখন ঠাকুরগাঁও কলেজে পড়াশোনার পাশাপাশি বেশ কিছুদিন আরডিআরএসের কনস্ট্রাকশন বিভাগে কাজ করেছে আমার বন্ধু হিমাংশু চন্দ তপন বা তপু। বেশ কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিধ্বস্ত ভবন নতুন করে তৈরির কাজ তদারকির দায়িত্ব পালন করেছে তপু। সুধীর কাকু আরডিআরএসের চাকরি করেছেন ১৯৮০ সাল পর্যন্ত। ফলে তিনি স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে ঠাকুরগাঁওয়েই বসবাস করেছেন। বাসা ভাড়া নিয়ে দুই ছেলেকে নিয়ে তিনি থাকতেন। তপু ও নয়ন ঠাকুরগাঁও কলেজে পড়ত। তপু ওই কলেজ থেকে বিএ পাস করেছে আর নয়ন এইচএসসি পাস করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। দর্শনশাস্ত্রে মাস্টার্স করে বোদায় ফিরে পাথরাজ কলেজে শিক্ষকতা শুরু করে। তপু বিয়েশাদি করে ঠাকুরগাঁওয়েই স্থায়ী হয়েছে।
তপুদের ঠাকুরগাঁওয়ের বাসায়ও নানা কারণে আমাকে বহুদিন রাত কাটাতে হয়েছে এবং পাত পাততে হয়েছে। তখন ঢাকায় আসার জন্য আমাকে হয় দিনাজপুর অথবা ঠাকুরগাঁও থেকে গাড়ি ধরতে হতো। পঞ্চগড় থেকে কোনো কোচ ডে কিংবা নাইট তখনো চালু হয়নি। ঢাকা থেকে বাড়ি যাওয়া এবং বাড়ি থেকে ঢাকায় আসার জন্য ঠাকুরগাঁওয়ে আমার রাত্রিকালীন অবস্থান হতো তপুদের বাসায়। রান্নাঘরে একসঙ্গে বসে আমরা চারজন রাতের খাবার খেতাম। সুধীর কাকু পরম মমতায় আমাকে পুত্রবৎ পাশে বসাতেন। আহা, কত প্রীতিময় ছিল সেই দিনগুলো!
আগেই বলেছি, কাকু ছিলেন একজন ভালো ফুটবল খেলোয়াড়। তিনি জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাবের ক্যাপ্টেন ছিলেন। তিনি সাত-আটবার ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (আইএফএ) শিল্ড কাপ খেলেছেন। ট্রফি জিতেছেন। হেড করে গোল করায় তিনি খুব পারদর্শী ছিলেন। তখন মাঝগ্রামের আবদুর রহমান সাহেবও ভালো ফুটবল খেলতেন। তাঁর কর্নার কিক মানেই ছিল অবধারিত গোল। সে জন্যই তখন বলা হতো সুধীর চন্দের হেড আর আব্দুর রহমানের কর্নার কিক ইকুয়াল টু গোল। তিনি রংপুর ও দিনাজপুরে গিয়েও খেলেছেন।
সুধীর কাকু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছেন। অস্ত্র হাতে সম্মুখ সমরে অংশ না নিলেও শরণার্থীশিবিরে আশ্রয় নেওয়া মানুষদের নানা উপায়ে সাহায্য-সহযোগিতায় ছিলেন সদা তৎপর। যেসব রাজনৈতিক নেতাকর্মী ওপারে গিয়েছিলেন, তাঁদের জন্য বড় সহায় ছিলেন সুধীর কাকু। কিন্তু কিছু মানুষ যেমন যুদ্ধ শেষের পাওনা বুঝে নেওয়ার জন্য বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন, সুধীর কাকু ছিলেন সেখানে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।
চন্দবাড়ির স্বপনদা ছিলেন হাসিখুশি স্বভাবের, একটু যেন আপনভোলা মানুষ। সংসার করেছেন। কিন্তু প্রকৃত সংসারী বলতে যা বোঝায়, তিনি তা ছিলেন কি না, আমার সন্দেহ আছে। মাথার ওপর সুধীর কাকুর মতো বটবৃক্ষসম বাবা থাকলে অমনই বোধ হয় হওয়ার কথা।
স্বপনদা আমার বড়। বন্ধুর বড় ভাই। কিন্তু আমাদের মধ্যে একধরনের বন্ধুত্বের সম্পর্কই গড়ে উঠেছিল। তিনি আমার সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলতেন। রাজনীতি সচেতন ছিলেন। দেশ-দুনিয়া সম্পর্কে খোঁজখবর রাখতেন। নিয়মিত খবরের কাগজ পড়তেন।
১৯৭৩ সালের নির্বাচনে আমাদের এলাকা থেকে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন কামু ভাই, অ্যাডভোকেট কামরুল হোসেন। মনে আছে, ওই নির্বাচনী প্রচারে আমি আর স্বপনদা একসঙ্গে অনেক জায়গায় গিয়েছি। বিভিন্ন গ্রাম বা ইউনিয়নে আমাদের উভয়ের পরিচিতদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ভোট প্রার্থনা করেছি। আমি সাইকেল চালাতে পারতাম না। স্বপনদা সাইকেল চালিয়ে আমাকে নিয়ে যেতেন। তখন গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট ভালো ছিল না। আলপথে অনেক কষ্ট করেই আমাদের যেতে হতো। হাসিমুখেই এই কষ্টকর কাজটি স্বপনদা করতেন। আমরা বুঝতে পারতাম, জনমত আমাদের অনুকূলে নয়। তার পরও কিসের আশায়, কিসের নেশায় যে দিনরাত গ্রাম থেকে গ্রামে, বাড়ি থেকে বাড়ি ছুটে বেড়াতাম!
আমি ঢাকায় আসার পর স্বপনদার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই যোগাযোগ কমে গিয়েছিল। তার পরও ছুটিছাঁটায় বোদায় গেলে স্বপনদা ছুটে আসতেন। কত জিজ্ঞাসা নিয়ে আমার কাছে সেসবের উত্তর জানতে চাইতেন। তাঁর সব কৌতূহল মেটানোর সাধ্য আমার ছিল না। এর মধ্যে একটি দুর্ঘটনায় স্বপনদা একটি পা হারান। তিনি ক্র্যাচে ভর দিয়ে এক পায়ে হাঁটতেন। শেষদিকে সম্ভবত ছাত্র পড়িয়ে উপার্জন করতেন। ২০০৩ সালে স্বপনদার মৃত্যু হয়। তিনি রেখে গেছেন দুই মেয়ে ও এক ছেলেসন্তান। বৌদি তাঁর দেবরদের সহযোগিতায় ছেলেমেয়েদের মানুষ করেছেন। বড় মেয়ে চৈতালি চন্দ সোমার বর ঝাড়বাড়ি কলেজের অর্থনীতির সহকারী অধ্যাপক। ছোট মেয়ে বিপাশা চন্দ দোলন বরিশালে বিয়ে হলেও এখন সম্ভবত বোদাতেই আছে। ছেলে সৌমিত চন্দ জয়দ্বীপ কৃতী ছাত্র। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করে ভারতের গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি সম্পন্ন করে ঢাকায় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছে। জয়দ্বীপ জাহাঙ্গীরনগরে ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ছিল, সভাপতি হয়েছিল। বাম রাজনীতিতে তাঁর আগ্রহ হয়তো এখনো বহাল আছে। গুজরাটে যাওয়ার আগে দৈনিক সমকালে কিছুদিন সাংবাদিকতা করেছে। লেখালেখির হাত ভালো। এর মধ্যেই গবেষণামূলক কিছু গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লিখে সুনাম অর্জন করেছে।
আমার বন্ধু হিমাংশু তপুও একজন সফল মানুষ। ঠাকুরগাঁওয়ে ওর একটি এনজিও আছে। অনেকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। ছাত্রাবস্থাতেই তপু উপার্জনমুখী হয়েছে। প্রথমে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি, তারপর ঠাকুরগাঁওয়ে একটি কসমেটিকসের দোকান এবং সব শেষে শার্প নামে এনজিও প্রতিষ্ঠা। নানা ধরনের সামাজিক কাজকর্মেও তপু সময় দেয়। ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েও ছাত্রাবস্থায় তপুর ভেতরের এত প্রতিভা সম্পর্কে আমরা কিছু আন্দাজ করতে পারিনি। তপুর একমাত্র ছেলে বুদ্ধদেব চন্দ তমাল কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ করে এসে এখন বগুড়ায় একটি বেসরকারি ব্যাংকের কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করছে। তমাল বিয়ে করে এক সন্তানের জনকও হয়েছে। আমার বন্ধু তপু গর্বিত দাদু হিসেবে পরিতৃপ্তি নিয়ে সংসার করছে।
ভাইদের মধ্যে ছোট প্রবীর চন্দ নয়ন। মূলত সে-ই এখন চন্দবাড়ির অভিভাবক। বোদার একজন সচেতন ও সংস্কৃতি মনস্ক মানুষ। দর্শনশাস্ত্রে পড়াশোনা করেও সাহিত্যে তাঁর অনুরাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন থেকেই। নিয়মিত কবিতা এবং নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে থাকে। দুটি কবিতার বইও বের হয়েছে। দুটি প্রবন্ধের বই প্রকাশের অপেক্ষায়। তার স্ত্রীও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ছেলে শুভ্র প্রতিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ করে একটি অ্যাড ফার্মে চাকরি করছে। মেয়ে দেবলীনা দৈবী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের ছাত্রী।
চন্দবাড়ির মেয়েদের কথা কিছু না বললেই নয়। সুধীর চন্দের বড় মেয়ে জলপাইগুড়িতে থেকেছেন বলে তাঁর সঙ্গে আমার কখনো দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দু-তিনবার তিনি বোদায় এসেছেন। আমি তখন বোদা ছেড়েছি। ফলে শিবানী চন্দ আমার অদেখা বড় দিদি। কল্যাণী; অর্থাৎ সুনুদিই হলেন আমাদের দেখা বড় দিদি। কী হাসিখুশি মানুষ সুনুদি! মানুষকে আপন করে নেওয়ার শক্তি যেমন তাঁর আছে, তেমনি আছে প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে এগিয়ে চলার প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস।
আমাদের ছোটবেলায় সুনুদির বিয়ে হয়। প্রেমের বিয়ে। মধু জামাইবাবুও খুব সুন্দর ছিলেন। সুনুদি তো অবশ্যই সুন্দরী। ভালোই চলছিল সব। সময় গড়িয়ে দুটি ফুটফুটে পুত্রসন্তানের জনক-জননী হন তাঁরা। তারপর যে কোথা থেকে কী হয়। জামাইবাবুকে আর বোদায় দেখা যায় না। তিনি সংসারত্যাগী হন। কী দুঃসহ মর্মজ্বালা বুকে চেপে সুনুদি তাঁর দুই ছেলে মিহির ও বিজনকে মানুষ করার কাজটি সম্পন্ন করেছেন, তা ভুক্তভোগী ছাড়া কারও পক্ষে বোঝা কঠিন। বাবা এবং পরিবারের সহযোগিতা-সমর্থন তিনি পেয়েছেন। কিন্তু আমাদের কুচুটে সমাজের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করা যে কত কঠিন, সেটা না বললেও চলে। সুনুদি প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর ছোট ছেলে বিজন সরকারও একটি প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। বড় ছেলে মিহির সরকার একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করত বলে শুনেছিলাম।
চন্দবাড়ির আরেক মেয়ে বেণু ওরফে নারায়ণী চন্দ, আমার বন্ধু এবং মামি। আমার মায়ের কোনো ভাইবোন নেই। তিনি বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। তবে মায়ের কয়েকজন পাতানো ভাই আছে, যারা আমার মামা। এ রকম একজন হলেন নারায়ণ চন্দ্র সাহা। ঢাকার বিক্রমপুরে বাড়ি। চাকরির সুবাদে বোদায় যান গত শতকের ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে। তিনি কিছুদিন লজিং থাকতেন আমার পিসার বাসায়; অর্থাৎ কার্তিকদা-জ্যোতিষদাদের বাসায়। তখন অবশ্য পিসেমশাই শরৎ চন্দ্র সরকার জীবিত ছিলেন। যা হোক, ওই বাসায় লজিং থাকার সুবাদেই হয়তো আমার মায়ের ভাই হয়ে যান নারায়ণ সাহা। আমার মামা। এই মামাই বিয়ে করেন চন্দবাড়ির মেয়ে বেণুকে। বন্ধু হেয় গেল মামি। বিয়ের পর নতুন সংসার গোছানোর আগে কিছুদিন তাঁরা আমাদের বাড়িতেই ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এই পরিবারের সঙ্গেও আমার অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। একসময় এমনও ছিল যে, ঢাকা থেকে বাড়ি গেলে রাতটা আমি নারায়ণ মামার বাসাতেই কাটাতাম। ততদিনে তাঁদের মেয়ে ও ছেলে বড় হয়ে উঠতে শুরু করেছে। একটি বিষয় লক্ষণীয়। মামার নাম নারায়ণ আর যাকে বিয়ে করলেন তাঁর নাম নারায়ণী। আমাকে আমার দু-এক বন্ধু তখন ঠাট্টা করে বলত, আমার স্ত্রীর নাম নাকি হবে হয় বিভা, না হয় রঞ্জনা! না, সেটা হয়নি।
বেণুও প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করেছে। ছেলে বাপ্পা ওরফে স্বরূপ সাহা এসএসসি পাস করে কলকাতায় চলে যায়। এমবিএ পাস করে বাপ্পা এখন বেঙ্গালুরুতে আছে বলে শুনেছি। বাপ্পা আমাকে মামা বলে ডাকে। কী অদ্ভুত সামাজিক সম্পর্কগুলো! বেণুর মেয়ে শম্পা কিছুদিন ঢাকায় ছিল। তারপর নাকি আমেরিকায় চলে গেছে। নারায়ণ মামার জীবনাবসান হয়েছে। মামি এখন অবসরজীবন যাপন করছেন।
নটে গাছটি মুড়োল, চন্দবাড়ির গল্প ফুরোল।
লেখক: সহকারী সম্পাদক, আজকের পত্রিকা

অবশেষে ১১ ডিসেম্বর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হলো। ইতিমধ্যে সবাই জেনে গেছেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন একই দিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের পথরেখা বেঁধে দিলেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তফসিল নিয়ে তাদের মতামত জানিয়েছে।
৩ ঘণ্টা আগে
হঠাৎ করেই বিজয়ের মাসে দেখা গেল মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কটূক্তি করছে একদল মানুষ। এই প্রবণতাকে পাত্তা না দিলেও চলত, কিন্তু সেগুলো যদি জাতীয় প্রচারমাধ্যম থেকে প্রচারিত হয়, তখন সত্যিই একটু ভাবতে হয়। এর যে প্রতিবাদ হওয়া দরকার, সেটা অনুভব করতে হয়। আইন বিষয়ে পড়াশোনা করলে আইন ভালোভাবে শেখা হয় বটে...
৪ ঘণ্টা আগে
গত সপ্তাহে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ভারত সফর ও উভয় নেতার শীর্ষ বৈঠক অনেক কিছুরই ইঙ্গিত করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পুতিনকে যেভাবে আলিঙ্গন করেছেন, স্বাগত জানিয়েছেন, একই গাড়িতে যাত্রা করেছেন, তা আলাস্কায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে পুতিনের সাক্ষাতের কথাই মনে করিয়ে দেয়।
৪ ঘণ্টা আগে
ঢাকা শহরের যানজটের সমস্যা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি দিয়েছে মেট্রোরেল। তবে এটা চালুর প্রায় দেড় বছরে এই আধুনিক গণপরিবহনব্যবস্থা মাঝে মাঝে বন্ধ হয়েছে। সেটা একটা ভাবনার বিষয়। মূলত এই সময়ের মধ্যে অন্তত ১০ বার মেট্রোরেল চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়েছে, যার বেশির ভাগই জনগণের গাফিলতির কারণে হয়েছে।
১ দিন আগেসম্পাদকীয়

অবশেষে ১১ ডিসেম্বর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হলো। ইতিমধ্যে সবাই জেনে গেছেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন একই দিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের পথরেখা বেঁধে দিলেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তফসিল নিয়ে তাদের মতামত জানিয়েছে। প্রতিটি দলই এখন নির্বাচনী প্রস্তুতির জন্য উঠেপড়ে লাগবে। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত নির্বাচন একটি সুস্থির সমাজব্যবস্থার দিকে দেশকে পরিচালিত করবে কি না, সেটাই এখন দেখার বিষয়।
এরই মধ্যে বেশ কিছু ঘটনা ঘটে গেছে। তফসিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সদ্য পদত্যাগকারী দুই ছাত্র উপদেষ্টার পদত্যাগ কার্যকর হয়েছে। এই দুই উপদেষ্টার নির্বাচনে অংশ নেওয়া না-নেওয়া নিয়ে তুমুল আলোচনা-সমালোচনা চলছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। বিদেশি রাষ্ট্রদূতদেরও সক্রিয় দেখা গেছে নানাভাবে। বিভিন্ন দলের নেতাদের কাছে তাঁরা যাচ্ছেন, কথা বলছেন। এরই মধ্যে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা নিয়ে বেশ কিছু সংকট তৈরি হয়েছে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান কেন দেশে ফিরতে পারছেন না, তা নিয়ে জেগেছে প্রশ্ন। যে চাপের কথা তারেক রহমান নিজেই বলেছেন, সেই চাপ দেশের অভ্যন্তরের নাকি বিদেশি কোনো শক্তির তরফ থেকে—সে কথাও আলোচিত হয়েছে।
২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপির নেতৃত্বে গড়ে ওঠা জোট সরকারের বিরুদ্ধে অর্থ লোপাট, দুর্নীতি, হাওয়া ভবনের মাধ্যমে প্যারালাল সরকার চালানোর অভিযোগসহ নানা বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। এদিকে ডাকসু নেতাদের কিছু কথা, কিছু কর্মকাণ্ড নিয়েও প্রশ্ন জেগেছে মানুষের মনে। তফসিল ঘোষণার দিনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীল দলের এক নেতাকে একজন ডাকসু নেতার নেতৃত্বে হেনস্তা করার ঘটনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছে এই ন্যক্কারজনক ঘটনা। সবচেয়ে শঙ্কার বিষয় হলো, দেশে-বিদেশে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের মূল নায়কদের নিয়ে কটাক্ষ করে কথা বলার প্রবণতা বেড়েছে। যাঁরা বলছেন, তাঁরা দেশের মূলধারার সংবাদমাধ্যমকেও ব্যবহার করছেন। অজস্র মিথ্যার বেসাতি গড়ে তোলা হচ্ছে, অথচ তাঁদের বিরুদ্ধে সরকারকে কোনো দৃষ্টান্তমূলক অবস্থান নিতে দেখা যায়নি।
আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচনব্যবস্থা কলুষিত করা, দুর্নীতি, ব্যাংক লুট, প্রতিষ্ঠান ভেঙে ফেলাসহ বহু অভিযোগ ছিল। যে রাজনৈতিক দলগুলো নির্যাতিত হয়েছিল আওয়ামী লীগ আমলে, তারাই ৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের পর যে রূপে আবির্ভূত হয়েছে, তা মোটেই জনগণের প্রত্যাশিত রূপ নয়। সংবাদমাধ্যমে নিয়মিত বিভিন্ন দলের দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, পদ-বাণিজ্য, খুনোখুনির খবর ভেসে আসছে। যে ছাত্র নেতৃত্বের ওপর ভরসা রাখার কথা ভেবেছে তরুণ প্রজন্ম, সেই তরুণেরাও আজ দ্বিধান্বিত। এ রকম এক অস্থির সময়ে আসছে নির্বাচন। আশা থাকবে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি, ব্যবসায়ীদের অবাধে কাজের সুযোগ, শিক্ষাঙ্গনে শৃঙ্খলা, রাজনৈতিক দলের চাঁদাবাজি বন্ধ, সাধারণ মানুষের জীবন ও কাজের নিরাপত্তাসহ কল্যাণকর কাজগুলো করবে নির্বাচিত সরকার। তবেই অস্থিরতা থেকে বের হওয়ার একটা উপায় খুঁজে পাওয়া যাবে।

অবশেষে ১১ ডিসেম্বর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হলো। ইতিমধ্যে সবাই জেনে গেছেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন একই দিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের পথরেখা বেঁধে দিলেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তফসিল নিয়ে তাদের মতামত জানিয়েছে। প্রতিটি দলই এখন নির্বাচনী প্রস্তুতির জন্য উঠেপড়ে লাগবে। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত নির্বাচন একটি সুস্থির সমাজব্যবস্থার দিকে দেশকে পরিচালিত করবে কি না, সেটাই এখন দেখার বিষয়।
এরই মধ্যে বেশ কিছু ঘটনা ঘটে গেছে। তফসিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সদ্য পদত্যাগকারী দুই ছাত্র উপদেষ্টার পদত্যাগ কার্যকর হয়েছে। এই দুই উপদেষ্টার নির্বাচনে অংশ নেওয়া না-নেওয়া নিয়ে তুমুল আলোচনা-সমালোচনা চলছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। বিদেশি রাষ্ট্রদূতদেরও সক্রিয় দেখা গেছে নানাভাবে। বিভিন্ন দলের নেতাদের কাছে তাঁরা যাচ্ছেন, কথা বলছেন। এরই মধ্যে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা নিয়ে বেশ কিছু সংকট তৈরি হয়েছে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান কেন দেশে ফিরতে পারছেন না, তা নিয়ে জেগেছে প্রশ্ন। যে চাপের কথা তারেক রহমান নিজেই বলেছেন, সেই চাপ দেশের অভ্যন্তরের নাকি বিদেশি কোনো শক্তির তরফ থেকে—সে কথাও আলোচিত হয়েছে।
২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপির নেতৃত্বে গড়ে ওঠা জোট সরকারের বিরুদ্ধে অর্থ লোপাট, দুর্নীতি, হাওয়া ভবনের মাধ্যমে প্যারালাল সরকার চালানোর অভিযোগসহ নানা বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। এদিকে ডাকসু নেতাদের কিছু কথা, কিছু কর্মকাণ্ড নিয়েও প্রশ্ন জেগেছে মানুষের মনে। তফসিল ঘোষণার দিনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীল দলের এক নেতাকে একজন ডাকসু নেতার নেতৃত্বে হেনস্তা করার ঘটনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছে এই ন্যক্কারজনক ঘটনা। সবচেয়ে শঙ্কার বিষয় হলো, দেশে-বিদেশে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের মূল নায়কদের নিয়ে কটাক্ষ করে কথা বলার প্রবণতা বেড়েছে। যাঁরা বলছেন, তাঁরা দেশের মূলধারার সংবাদমাধ্যমকেও ব্যবহার করছেন। অজস্র মিথ্যার বেসাতি গড়ে তোলা হচ্ছে, অথচ তাঁদের বিরুদ্ধে সরকারকে কোনো দৃষ্টান্তমূলক অবস্থান নিতে দেখা যায়নি।
আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচনব্যবস্থা কলুষিত করা, দুর্নীতি, ব্যাংক লুট, প্রতিষ্ঠান ভেঙে ফেলাসহ বহু অভিযোগ ছিল। যে রাজনৈতিক দলগুলো নির্যাতিত হয়েছিল আওয়ামী লীগ আমলে, তারাই ৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের পর যে রূপে আবির্ভূত হয়েছে, তা মোটেই জনগণের প্রত্যাশিত রূপ নয়। সংবাদমাধ্যমে নিয়মিত বিভিন্ন দলের দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, পদ-বাণিজ্য, খুনোখুনির খবর ভেসে আসছে। যে ছাত্র নেতৃত্বের ওপর ভরসা রাখার কথা ভেবেছে তরুণ প্রজন্ম, সেই তরুণেরাও আজ দ্বিধান্বিত। এ রকম এক অস্থির সময়ে আসছে নির্বাচন। আশা থাকবে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি, ব্যবসায়ীদের অবাধে কাজের সুযোগ, শিক্ষাঙ্গনে শৃঙ্খলা, রাজনৈতিক দলের চাঁদাবাজি বন্ধ, সাধারণ মানুষের জীবন ও কাজের নিরাপত্তাসহ কল্যাণকর কাজগুলো করবে নির্বাচিত সরকার। তবেই অস্থিরতা থেকে বের হওয়ার একটা উপায় খুঁজে পাওয়া যাবে।
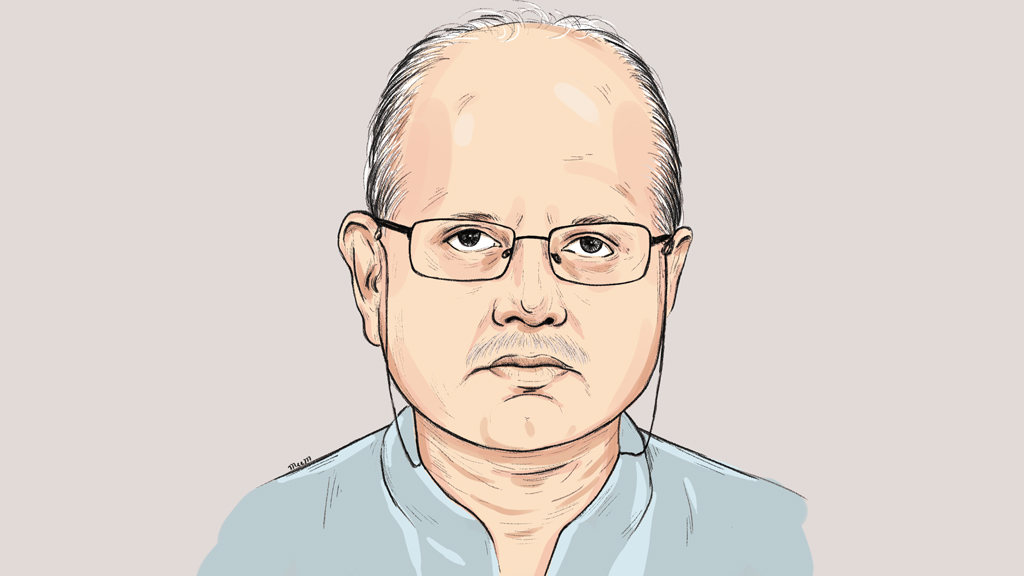
কাকু কোনো কথা শোনেন না। একপর্যায়ে পিটিয়ে ক্লান্ত হয়ে আমাদের সবাইকে শাসিয়ে তিনি চলে যান। আমরা ভাবলাম, অত পিটুনি খেয়ে তপু হয়তো আর সিনেমা দেখতে যাবে না। কিন্তু আমাদের অবাক করে তপু বলল, ‘মার তো খেয়েই ফেলেছি, তাহলে আর সিনেমা দেখা থেকে বঞ্চিত হব কেন?’
০৫ মে ২০২২
হঠাৎ করেই বিজয়ের মাসে দেখা গেল মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কটূক্তি করছে একদল মানুষ। এই প্রবণতাকে পাত্তা না দিলেও চলত, কিন্তু সেগুলো যদি জাতীয় প্রচারমাধ্যম থেকে প্রচারিত হয়, তখন সত্যিই একটু ভাবতে হয়। এর যে প্রতিবাদ হওয়া দরকার, সেটা অনুভব করতে হয়। আইন বিষয়ে পড়াশোনা করলে আইন ভালোভাবে শেখা হয় বটে...
৪ ঘণ্টা আগে
গত সপ্তাহে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ভারত সফর ও উভয় নেতার শীর্ষ বৈঠক অনেক কিছুরই ইঙ্গিত করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পুতিনকে যেভাবে আলিঙ্গন করেছেন, স্বাগত জানিয়েছেন, একই গাড়িতে যাত্রা করেছেন, তা আলাস্কায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে পুতিনের সাক্ষাতের কথাই মনে করিয়ে দেয়।
৪ ঘণ্টা আগে
ঢাকা শহরের যানজটের সমস্যা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি দিয়েছে মেট্রোরেল। তবে এটা চালুর প্রায় দেড় বছরে এই আধুনিক গণপরিবহনব্যবস্থা মাঝে মাঝে বন্ধ হয়েছে। সেটা একটা ভাবনার বিষয়। মূলত এই সময়ের মধ্যে অন্তত ১০ বার মেট্রোরেল চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়েছে, যার বেশির ভাগই জনগণের গাফিলতির কারণে হয়েছে।
১ দিন আগেজাহীদ রেজা নূর

হঠাৎ করেই বিজয়ের মাসে দেখা গেল মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কটূক্তি করছে একদল মানুষ। এই প্রবণতাকে পাত্তা না দিলেও চলত, কিন্তু সেগুলো যদি জাতীয় প্রচারমাধ্যম থেকে প্রচারিত হয়, তখন সত্যিই একটু ভাবতে হয়। এর যে প্রতিবাদ হওয়া দরকার, সেটা অনুভব করতে হয়। আইন বিষয়ে পড়াশোনা করলে আইন ভালোভাবে শেখা হয় বটে, কিন্তু ব্যারিস্টার বা উকিল হলেই দেশের ইতিহাস ভালো জানবে—এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। আমাদের দেশের কিছু আইন ব্যবসায়ী আমাদের বিজয় নিয়ে, বিজয়ের নায়কদের নিয়ে যেসব কথা বলে চলেছেন, তার তীব্র প্রতিবাদ হওয়া দরকার। তাঁদের ব্যাপারে সরকারের অবস্থানও পরিষ্কার করা উচিত। অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্বশীল কারও কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে করা কটাক্ষের ব্যাপারে তেমন কোনো কড়া কথা আমি অন্তত বলতে শুনিনি।
যতদূর স্মরণ করতে পারি, ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানটি স্বাধীনতা বা বিজয় দিবসকে ছোট করার জন্য সংঘটিত হয়নি। একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের অঙ্গীকারে শামিল হয়েছিল দেশের আপামর মানুষ। এদের সবাই একই ভাবনা নিয়ে সামনের পথে এগোয়নি। সরকার পতন হলে কী হতে পারে কৌশল—এ রকম ভাবনাও কারও মাথায় ছিল বলে মনে হয় না। দেশের ছাত্র-জনতা এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল প্রাণের তাগিদে। যখন লাশ পড়ছিল একের পর এক, তখন রাজপথকেই বেছে নিয়েছিল তারা। কিন্তু এই প্রচণ্ড আলোড়নে সরকার পড়ে যাবে—এ রকম ভাবনা হয়তো তাদের ছিল না। ছিল না সে রকম কোনো প্রস্তুতি। তাই গণ-অভ্যুত্থানের বিজয় কিছু প্রগাঢ় নীতিকথার জন্ম দিলেও রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক কোনো দিশা দেয়নি। শুধু কি নীতিকথা? অশ্রাব্য উচ্চারণ করে লাইক-কমেন্টে ছেয়ে যাওয়া একদল নেতার সন্ধান আজকাল পাওয়া যাচ্ছে, যাঁরা টিনের চালে কাউয়ার পাশাপাশি আরও কত কিছু দেখছেন! বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন করতে করতে চাঁদাবাজি করার পথে শামিল হচ্ছেন। আর এই ধরনের অরাজকতা চালানোর পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের গলায় জুতার মালা পরিয়ে প্রচার করছেন গণমাধ্যমে। তাঁরা ভাবছেন, স্বাধীনতার সব অর্জনকে কটাক্ষ করতে পারলে এ দেশের মানুষ একদিন ‘লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান’-এর সহযাত্রী হয়ে উঠবে আবারও।
কী হতে কী হয়ে গেল, এখন স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস নিয়ে কথা বলতে ভয় পায় মানুষ। একটি স্বাধীন দেশে স্বাধীনতা বা বিজয় শব্দগুলো কি নিষিদ্ধ হয়ে গেল নাকি? গত বছর শিল্পকলা একাডেমি যখন বিজয় উৎসব পালন করছিল, তখন ভয়ে ভয়ে তারা ‘বিজয় উৎসব’কে ‘ডিসেম্বর উৎসব’ লিখেছিল, সে কথা কি মনে আছে কারও? পরে প্রবল আপত্তির মুখে আবার তারা ‘বিজয় উৎসব’-এ ফিরে এসেছিল। স্বাধীনতা আর বিজয় শব্দ দুটি উচ্চারণ করার মতো বুকের পাটা নেই একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের—এটা যে কত বড় দুর্ভাবনার ব্যাপার, তা কি বলে বোঝানো যাবে?
১৯৭১ সালে যে ঘটনা ঘটেছিল এই ভূখণ্ডে, তার ছাপ পাওয়া যায় সারা বিশ্বে। সে সময়কার বিশ্বের দিকে তাকালে বোঝা যায়, কোন কোন ব্যাপার নিয়ে অস্থিরতা চলছিল। মনে করিয়ে দিই, রাশিয়া-চীনের দ্বন্দ্বের কারণে কমিউনিস্ট দুনিয়ার ভাঙন, পরাশক্তি হিসেবে মার্কিনদের বিজয়যাত্রা, সাম্রাজ্যবাদের বিকাশ, উপনিবেশগুলো ভেঙে নতুন নতুন স্বাধীন দেশ গঠন এবং তার কোনো কোনো দেশের বাম দিকে ঘেঁষা রাজনীতি, কিছু কিছু দেশে নব্য স্বৈরাচারের আবির্ভাব ইত্যাদি নানা প্যাঁচে পড়ে অস্থির হয়ে পড়েছিল বৈশ্বিক রাজনীতি। ভিয়েতনাম যুদ্ধ তখন আলোচনায় রয়েছে। এ রকমই একটা অবস্থায় ষাটের দশকের মধ্যভাগে ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করলেন ৬ দফা। সেই ৬ দফা নতুন কিছু ছিল না। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে কিংবা ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের ইশতেহারেও এই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টির দেখা মেলে। ১৯৬৬ সালের দিকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের চালানো শোষণ-বঞ্চনার বিষয়টি আমূল প্রকাশিত হয়ে পড়লে তা বাঙালির আবেগকে তাড়িত করেছিল। ফলে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এই ভূখণ্ডের মানুষ জানান দিয়েছিল, মাথায় হাত বোলানোর রাজনীতি আর চলবে না এখানে।
এত বড় বড় দল থাকতে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে কী করে আওয়ামী লীগ এত বড় বিজয় পেল, সে ইতিহাস নানাভাবে লেখা হয়েছে। এটাই ছিল বাংলার রায়। দেশের জনগণ সেই রায়ে ক্ষমতা দিয়েছিল ক্যারিশম্যাটিক নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে। সলিমুল্লাহ খানদের গুরু আহমদ ছফার বিখ্যাত উক্তিটি এখানে প্রযোজ্য। ছফা লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং শেখ মুজিবুর রহমান একটি যমজ শব্দ। একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটার অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না। শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি। যারা এই সত্য অস্বীকার করবে, তাদের সঙ্গে কোনো রকমের বিতর্ক, বাদ-প্রতিবাদ করতেও আমরা রাজি হব না।’ ভুল শোনেননি, ছফা এ কথাই বলেছেন। এবং এখানেই তা শেষ করেননি। তিনি যোগ করেছেন, ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতার সঙ্গে শেখ মুজিবের নাম এমন অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে, যত পণ্ডিত হোন না কেন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের নিপুণতা এবং যুক্তির মারপ্যাঁচ দেখিয়ে কোনো ব্যক্তি একটা থেকে আর একটাকে পৃথক করতে পারবেন না।’
ছফাকে এসব কথা বলতে হলো কেন? তিনি তো তাঁর শিষ্যদের মতোই শেখ মুজিবকে অগ্রাহ্য করে অথবা জাতির ভিলেন বানিয়ে উপস্থাপন করতে পারতেন। কেন ছফা সেটা করেননি? আমার মনে হয়, ছফা ভেবে দেখেছেন, ইতিহাস নিয়ে মিথ্যে তথ্য দিলে ইতিহাসের কোনো না কোনো পর্যায়ে এসে তা ধরা পড়বেই। তখন আত্মপরিচয়েই টান পড়বে। শেখ মুজিব সম্পর্কে নানা ধরনের নেতিবাচক মন্তব্য করলেও ছফা স্বাধীনতা ও শেখ মুজিবের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে নির্মোহ মতামত দিয়েছেন।
ইতিহাসবিমুখ পাকিস্তানপ্রেমী অর্বাচীনেরা এই স্বাধীন বাংলাদেশে বসে ইতিহাস বিকৃতি করে চলেছেন। এতে আমাদের তরুণসমাজ কতটা বিভ্রান্ত হবে, সে প্রশ্নের উত্তর এত দ্রুত পাওয়া যাবে না।
বিষয়টি বুঝতে চাইলে কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করা দরকার। আমাদের সমাজে এই প্রতীকগুলো কীভাবে আছে, তা বুঝতে পারলেই স্বাধীনতা বা বিজয় আমাদের দেশে এখন কোন মর্যাদায় আছে, তা বোঝা যাবে। স্বাধীনতা বা দেশপ্রেমকে হুমকির মুখে ফেলতে হলে এমন কিছু কাজ করতে হয়, যাতে শুরুতেই ভয় আর আতঙ্ককে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। তারপর প্রতিষ্ঠিত সত্যগুলো নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। পতাকা, জাতীয় সংগীত নিয়ে বাজে কথা বলা—এভাবেই আস্তে আস্তে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র তাদের পায়ের নিচে মাটি খোঁজে।
পাঠক, আপনি মনে করুন একটি পরীক্ষা দিতে বসেছেন। আমি কিছু প্রশ্ন রেখে যাব, পাঠক এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে নিজেই এই পরীক্ষার প্রশ্নগুলোয় নম্বর দেবেন। তাঁরাই নির্ধারণ করবেন, কেমন আছে আজকের বাংলাদেশ।
প্রশ্নগুলো এমন: কেমন আছে দেশের বিচারব্যবস্থা? কেমন আছে নির্বাচন কমিশন? তারা কি স্বাধীনভাবে নিজেদের কাজ করে যাচ্ছে?
গণমাধ্যমের স্বাধীনতা কোন অবস্থায় আছে? সাংবাদিক-লেখক-গবেষকেরা কি নির্দ্বিধায় নির্বিঘ্নে কাজ করার মতো পরিবেশ পাচ্ছেন?
সমাজে কোনো বড় সংঘাত নেই তো? ঐক্যের কথা বলা হচ্ছে সব জায়গা থেকে। দেশের ডাকসাইটে স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সেই ঐক্য কি দেখা যাচ্ছে? বিভাজনের রাজনীতিকে কি সরিয়ে দেওয়া গেছে? সন্দেহ-অবিশ্বাসের রাজনীতি কি আছে, নাকি বিদায় নিয়েছে?
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সাধারণ জনগণ কি সন্তুষ্ট? মব বলুন আর চাপ প্রয়োগের রাজনীতি বলুন, সেগুলো কি জনমনে ভীতি ছড়াচ্ছে?
আপনি কি এমন কিছু লক্ষ করছেন, যেখানে সত্য ও মিথ্যাকে কাছাকাছি রেখে নাগরিকদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দেওয়া হয়?
আপনি কি সামাজিক বন্ধন ভেঙে ফেলার প্রবণতা লক্ষ করেছেন? আউল-বাউলের দেশে গানবাজনা কি হুমকির মুখে পড়েছে? ‘তৌহিদি জনতা’ আদতে কাদের কোন লক্ষ্য বাস্তবায়ন করছে? সরকার কি এদের বিরুদ্ধে কোনো কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে? উত্তেজনা ছড়ায় যারা, তাদের পুলিশ ছেড়ে দিচ্ছে, আর যারা অত্যাচারিত হয়েছে, তাদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে—এ রকম কিছু কি আপনার নজরে পড়েছে?
সমষ্টিগত শক্তি ভেঙে দেওয়ার জন্য কোনো বাঁশিওয়ালা কি বাঁশি বাজাচ্ছে? আপনি কি লক্ষ করেছেন শুধু ধর্মীয় সংখ্যালঘুই নয়, নানাভাবে যাঁরা সংখ্যালঘু, তাঁদের মারধর করে সংখ্যাগুরু অংশ আখের গুছিয়ে নিচ্ছে?
আপনি কি বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এমন কোনো অঙ্গীকার দেখতে পাচ্ছেন, যাতে তাদের ইশতেহার অনুযায়ী জনগণ একটি ‘সোনার বাংলা’য় বসবাস করবে?
প্রশ্নগুলোর উত্তর নিজে লিখুন। প্রতিটি প্রশ্নের জন্য ১০ নম্বর বরাদ্দ করুন। যোগফল মেলান, তারপর একটা সিদ্ধান্তে আসুন।
আপনি তখন বুঝতে পারবেন, গণ-অভ্যুত্থানকে কেউ কেউ স্বাধীনতাবিরোধিতার জায়গায় সুকৌশলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। যে তরুণেরা সেই অপচেষ্টা রুখে দিতে পারে, সে তরুণদের প্রতীক্ষায় আছি।

হঠাৎ করেই বিজয়ের মাসে দেখা গেল মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কটূক্তি করছে একদল মানুষ। এই প্রবণতাকে পাত্তা না দিলেও চলত, কিন্তু সেগুলো যদি জাতীয় প্রচারমাধ্যম থেকে প্রচারিত হয়, তখন সত্যিই একটু ভাবতে হয়। এর যে প্রতিবাদ হওয়া দরকার, সেটা অনুভব করতে হয়। আইন বিষয়ে পড়াশোনা করলে আইন ভালোভাবে শেখা হয় বটে, কিন্তু ব্যারিস্টার বা উকিল হলেই দেশের ইতিহাস ভালো জানবে—এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। আমাদের দেশের কিছু আইন ব্যবসায়ী আমাদের বিজয় নিয়ে, বিজয়ের নায়কদের নিয়ে যেসব কথা বলে চলেছেন, তার তীব্র প্রতিবাদ হওয়া দরকার। তাঁদের ব্যাপারে সরকারের অবস্থানও পরিষ্কার করা উচিত। অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্বশীল কারও কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে করা কটাক্ষের ব্যাপারে তেমন কোনো কড়া কথা আমি অন্তত বলতে শুনিনি।
যতদূর স্মরণ করতে পারি, ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানটি স্বাধীনতা বা বিজয় দিবসকে ছোট করার জন্য সংঘটিত হয়নি। একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের অঙ্গীকারে শামিল হয়েছিল দেশের আপামর মানুষ। এদের সবাই একই ভাবনা নিয়ে সামনের পথে এগোয়নি। সরকার পতন হলে কী হতে পারে কৌশল—এ রকম ভাবনাও কারও মাথায় ছিল বলে মনে হয় না। দেশের ছাত্র-জনতা এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল প্রাণের তাগিদে। যখন লাশ পড়ছিল একের পর এক, তখন রাজপথকেই বেছে নিয়েছিল তারা। কিন্তু এই প্রচণ্ড আলোড়নে সরকার পড়ে যাবে—এ রকম ভাবনা হয়তো তাদের ছিল না। ছিল না সে রকম কোনো প্রস্তুতি। তাই গণ-অভ্যুত্থানের বিজয় কিছু প্রগাঢ় নীতিকথার জন্ম দিলেও রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক কোনো দিশা দেয়নি। শুধু কি নীতিকথা? অশ্রাব্য উচ্চারণ করে লাইক-কমেন্টে ছেয়ে যাওয়া একদল নেতার সন্ধান আজকাল পাওয়া যাচ্ছে, যাঁরা টিনের চালে কাউয়ার পাশাপাশি আরও কত কিছু দেখছেন! বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন করতে করতে চাঁদাবাজি করার পথে শামিল হচ্ছেন। আর এই ধরনের অরাজকতা চালানোর পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের গলায় জুতার মালা পরিয়ে প্রচার করছেন গণমাধ্যমে। তাঁরা ভাবছেন, স্বাধীনতার সব অর্জনকে কটাক্ষ করতে পারলে এ দেশের মানুষ একদিন ‘লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান’-এর সহযাত্রী হয়ে উঠবে আবারও।
কী হতে কী হয়ে গেল, এখন স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস নিয়ে কথা বলতে ভয় পায় মানুষ। একটি স্বাধীন দেশে স্বাধীনতা বা বিজয় শব্দগুলো কি নিষিদ্ধ হয়ে গেল নাকি? গত বছর শিল্পকলা একাডেমি যখন বিজয় উৎসব পালন করছিল, তখন ভয়ে ভয়ে তারা ‘বিজয় উৎসব’কে ‘ডিসেম্বর উৎসব’ লিখেছিল, সে কথা কি মনে আছে কারও? পরে প্রবল আপত্তির মুখে আবার তারা ‘বিজয় উৎসব’-এ ফিরে এসেছিল। স্বাধীনতা আর বিজয় শব্দ দুটি উচ্চারণ করার মতো বুকের পাটা নেই একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের—এটা যে কত বড় দুর্ভাবনার ব্যাপার, তা কি বলে বোঝানো যাবে?
১৯৭১ সালে যে ঘটনা ঘটেছিল এই ভূখণ্ডে, তার ছাপ পাওয়া যায় সারা বিশ্বে। সে সময়কার বিশ্বের দিকে তাকালে বোঝা যায়, কোন কোন ব্যাপার নিয়ে অস্থিরতা চলছিল। মনে করিয়ে দিই, রাশিয়া-চীনের দ্বন্দ্বের কারণে কমিউনিস্ট দুনিয়ার ভাঙন, পরাশক্তি হিসেবে মার্কিনদের বিজয়যাত্রা, সাম্রাজ্যবাদের বিকাশ, উপনিবেশগুলো ভেঙে নতুন নতুন স্বাধীন দেশ গঠন এবং তার কোনো কোনো দেশের বাম দিকে ঘেঁষা রাজনীতি, কিছু কিছু দেশে নব্য স্বৈরাচারের আবির্ভাব ইত্যাদি নানা প্যাঁচে পড়ে অস্থির হয়ে পড়েছিল বৈশ্বিক রাজনীতি। ভিয়েতনাম যুদ্ধ তখন আলোচনায় রয়েছে। এ রকমই একটা অবস্থায় ষাটের দশকের মধ্যভাগে ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করলেন ৬ দফা। সেই ৬ দফা নতুন কিছু ছিল না। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে কিংবা ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের ইশতেহারেও এই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টির দেখা মেলে। ১৯৬৬ সালের দিকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের চালানো শোষণ-বঞ্চনার বিষয়টি আমূল প্রকাশিত হয়ে পড়লে তা বাঙালির আবেগকে তাড়িত করেছিল। ফলে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এই ভূখণ্ডের মানুষ জানান দিয়েছিল, মাথায় হাত বোলানোর রাজনীতি আর চলবে না এখানে।
এত বড় বড় দল থাকতে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে কী করে আওয়ামী লীগ এত বড় বিজয় পেল, সে ইতিহাস নানাভাবে লেখা হয়েছে। এটাই ছিল বাংলার রায়। দেশের জনগণ সেই রায়ে ক্ষমতা দিয়েছিল ক্যারিশম্যাটিক নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে। সলিমুল্লাহ খানদের গুরু আহমদ ছফার বিখ্যাত উক্তিটি এখানে প্রযোজ্য। ছফা লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং শেখ মুজিবুর রহমান একটি যমজ শব্দ। একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটার অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না। শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি। যারা এই সত্য অস্বীকার করবে, তাদের সঙ্গে কোনো রকমের বিতর্ক, বাদ-প্রতিবাদ করতেও আমরা রাজি হব না।’ ভুল শোনেননি, ছফা এ কথাই বলেছেন। এবং এখানেই তা শেষ করেননি। তিনি যোগ করেছেন, ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতার সঙ্গে শেখ মুজিবের নাম এমন অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে, যত পণ্ডিত হোন না কেন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের নিপুণতা এবং যুক্তির মারপ্যাঁচ দেখিয়ে কোনো ব্যক্তি একটা থেকে আর একটাকে পৃথক করতে পারবেন না।’
ছফাকে এসব কথা বলতে হলো কেন? তিনি তো তাঁর শিষ্যদের মতোই শেখ মুজিবকে অগ্রাহ্য করে অথবা জাতির ভিলেন বানিয়ে উপস্থাপন করতে পারতেন। কেন ছফা সেটা করেননি? আমার মনে হয়, ছফা ভেবে দেখেছেন, ইতিহাস নিয়ে মিথ্যে তথ্য দিলে ইতিহাসের কোনো না কোনো পর্যায়ে এসে তা ধরা পড়বেই। তখন আত্মপরিচয়েই টান পড়বে। শেখ মুজিব সম্পর্কে নানা ধরনের নেতিবাচক মন্তব্য করলেও ছফা স্বাধীনতা ও শেখ মুজিবের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে নির্মোহ মতামত দিয়েছেন।
ইতিহাসবিমুখ পাকিস্তানপ্রেমী অর্বাচীনেরা এই স্বাধীন বাংলাদেশে বসে ইতিহাস বিকৃতি করে চলেছেন। এতে আমাদের তরুণসমাজ কতটা বিভ্রান্ত হবে, সে প্রশ্নের উত্তর এত দ্রুত পাওয়া যাবে না।
বিষয়টি বুঝতে চাইলে কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করা দরকার। আমাদের সমাজে এই প্রতীকগুলো কীভাবে আছে, তা বুঝতে পারলেই স্বাধীনতা বা বিজয় আমাদের দেশে এখন কোন মর্যাদায় আছে, তা বোঝা যাবে। স্বাধীনতা বা দেশপ্রেমকে হুমকির মুখে ফেলতে হলে এমন কিছু কাজ করতে হয়, যাতে শুরুতেই ভয় আর আতঙ্ককে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। তারপর প্রতিষ্ঠিত সত্যগুলো নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। পতাকা, জাতীয় সংগীত নিয়ে বাজে কথা বলা—এভাবেই আস্তে আস্তে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র তাদের পায়ের নিচে মাটি খোঁজে।
পাঠক, আপনি মনে করুন একটি পরীক্ষা দিতে বসেছেন। আমি কিছু প্রশ্ন রেখে যাব, পাঠক এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে নিজেই এই পরীক্ষার প্রশ্নগুলোয় নম্বর দেবেন। তাঁরাই নির্ধারণ করবেন, কেমন আছে আজকের বাংলাদেশ।
প্রশ্নগুলো এমন: কেমন আছে দেশের বিচারব্যবস্থা? কেমন আছে নির্বাচন কমিশন? তারা কি স্বাধীনভাবে নিজেদের কাজ করে যাচ্ছে?
গণমাধ্যমের স্বাধীনতা কোন অবস্থায় আছে? সাংবাদিক-লেখক-গবেষকেরা কি নির্দ্বিধায় নির্বিঘ্নে কাজ করার মতো পরিবেশ পাচ্ছেন?
সমাজে কোনো বড় সংঘাত নেই তো? ঐক্যের কথা বলা হচ্ছে সব জায়গা থেকে। দেশের ডাকসাইটে স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সেই ঐক্য কি দেখা যাচ্ছে? বিভাজনের রাজনীতিকে কি সরিয়ে দেওয়া গেছে? সন্দেহ-অবিশ্বাসের রাজনীতি কি আছে, নাকি বিদায় নিয়েছে?
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সাধারণ জনগণ কি সন্তুষ্ট? মব বলুন আর চাপ প্রয়োগের রাজনীতি বলুন, সেগুলো কি জনমনে ভীতি ছড়াচ্ছে?
আপনি কি এমন কিছু লক্ষ করছেন, যেখানে সত্য ও মিথ্যাকে কাছাকাছি রেখে নাগরিকদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দেওয়া হয়?
আপনি কি সামাজিক বন্ধন ভেঙে ফেলার প্রবণতা লক্ষ করেছেন? আউল-বাউলের দেশে গানবাজনা কি হুমকির মুখে পড়েছে? ‘তৌহিদি জনতা’ আদতে কাদের কোন লক্ষ্য বাস্তবায়ন করছে? সরকার কি এদের বিরুদ্ধে কোনো কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে? উত্তেজনা ছড়ায় যারা, তাদের পুলিশ ছেড়ে দিচ্ছে, আর যারা অত্যাচারিত হয়েছে, তাদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে—এ রকম কিছু কি আপনার নজরে পড়েছে?
সমষ্টিগত শক্তি ভেঙে দেওয়ার জন্য কোনো বাঁশিওয়ালা কি বাঁশি বাজাচ্ছে? আপনি কি লক্ষ করেছেন শুধু ধর্মীয় সংখ্যালঘুই নয়, নানাভাবে যাঁরা সংখ্যালঘু, তাঁদের মারধর করে সংখ্যাগুরু অংশ আখের গুছিয়ে নিচ্ছে?
আপনি কি বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এমন কোনো অঙ্গীকার দেখতে পাচ্ছেন, যাতে তাদের ইশতেহার অনুযায়ী জনগণ একটি ‘সোনার বাংলা’য় বসবাস করবে?
প্রশ্নগুলোর উত্তর নিজে লিখুন। প্রতিটি প্রশ্নের জন্য ১০ নম্বর বরাদ্দ করুন। যোগফল মেলান, তারপর একটা সিদ্ধান্তে আসুন।
আপনি তখন বুঝতে পারবেন, গণ-অভ্যুত্থানকে কেউ কেউ স্বাধীনতাবিরোধিতার জায়গায় সুকৌশলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। যে তরুণেরা সেই অপচেষ্টা রুখে দিতে পারে, সে তরুণদের প্রতীক্ষায় আছি।
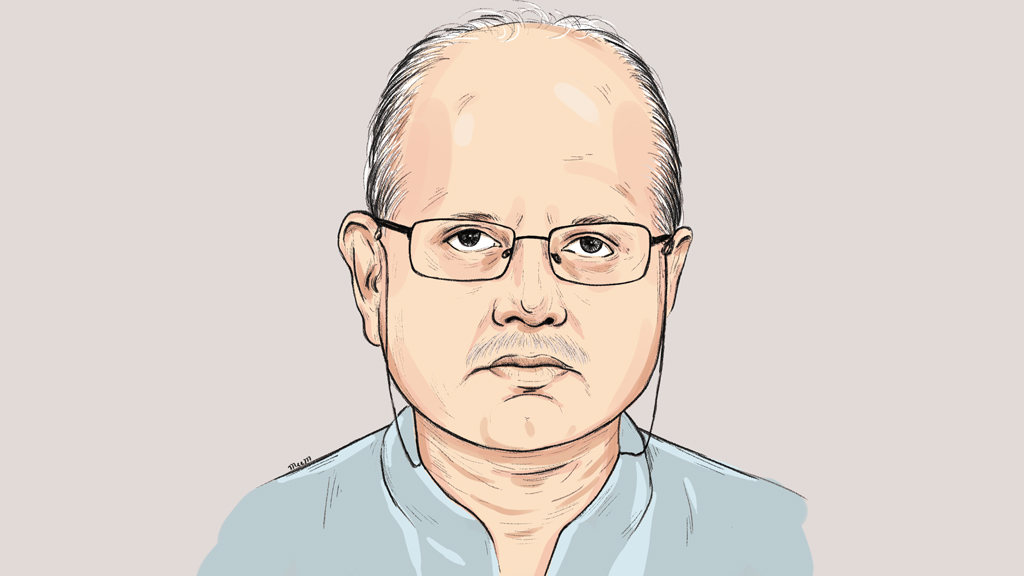
কাকু কোনো কথা শোনেন না। একপর্যায়ে পিটিয়ে ক্লান্ত হয়ে আমাদের সবাইকে শাসিয়ে তিনি চলে যান। আমরা ভাবলাম, অত পিটুনি খেয়ে তপু হয়তো আর সিনেমা দেখতে যাবে না। কিন্তু আমাদের অবাক করে তপু বলল, ‘মার তো খেয়েই ফেলেছি, তাহলে আর সিনেমা দেখা থেকে বঞ্চিত হব কেন?’
০৫ মে ২০২২
অবশেষে ১১ ডিসেম্বর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হলো। ইতিমধ্যে সবাই জেনে গেছেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন একই দিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের পথরেখা বেঁধে দিলেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তফসিল নিয়ে তাদের মতামত জানিয়েছে।
৩ ঘণ্টা আগে
গত সপ্তাহে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ভারত সফর ও উভয় নেতার শীর্ষ বৈঠক অনেক কিছুরই ইঙ্গিত করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পুতিনকে যেভাবে আলিঙ্গন করেছেন, স্বাগত জানিয়েছেন, একই গাড়িতে যাত্রা করেছেন, তা আলাস্কায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে পুতিনের সাক্ষাতের কথাই মনে করিয়ে দেয়।
৪ ঘণ্টা আগে
ঢাকা শহরের যানজটের সমস্যা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি দিয়েছে মেট্রোরেল। তবে এটা চালুর প্রায় দেড় বছরে এই আধুনিক গণপরিবহনব্যবস্থা মাঝে মাঝে বন্ধ হয়েছে। সেটা একটা ভাবনার বিষয়। মূলত এই সময়ের মধ্যে অন্তত ১০ বার মেট্রোরেল চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়েছে, যার বেশির ভাগই জনগণের গাফিলতির কারণে হয়েছে।
১ দিন আগেড. মঞ্জুরে খোদা

গত সপ্তাহে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ভারত সফর ও উভয় নেতার শীর্ষ বৈঠক অনেক কিছুরই ইঙ্গিত করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পুতিনকে যেভাবে আলিঙ্গন করেছেন, স্বাগত জানিয়েছেন, একই গাড়িতে যাত্রা করেছেন, তা আলাস্কায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে পুতিনের সাক্ষাতের কথাই মনে করিয়ে দেয়। মোদি প্রেসিডেন্ট পুতিনকে সময়ের পরীক্ষিত বন্ধু, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও আস্থার প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করেন। এই আস্থা ও হৃদ্যতা ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের গভীর মাত্রাকেই নির্দেশ করে। পুতিন তাঁর ক্ষমতা গ্রহণের ২৫ বছরে ১০ বার ভারত সফর করেছেন। তবে ২০২২ সালে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর এটিই ছিল তাঁর প্রথম ভারত সফর।
পুতিনের এই ভারত সফর নিছক কোনো রুটিন বিষয় ছিল না। ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের ধারাবাহিকতা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা প্রদান করে। তাঁদের সাক্ষাৎ ছিল বিশ্বরাজনীতির আগ্রহের বিষয়, কেননা ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর শুল্ক নিয়ে মোদির সঙ্গে যে সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছিল ও বরফ গলছিল, তখনই পুতিন ভারত সফর করলেন। প্রশ্ন হচ্ছে, ভারত-রাশিয়া এই বৈঠকে কে কী অর্জন করল, তার কয়েকটি দিক আলোচনা করা যাক।
প্রতিরক্ষা সহযোগিতা
পুতিনের এই সফরের মাধ্যমে ভারত তাদের প্রতিরক্ষা সহযোগিতার বিষয়টি পুনরায় নিশ্চিত করল। রাশিয়া এখনো ভারতের প্রধান সমরাস্ত্রের সরবরাহকারী। যদিও ১৯৭০-৮০-এর দশকে ভারতের অস্ত্রের প্রায় ৮০ ভাগই রাশিয়া সরবরাহ করত। পুতিন এবারের সফরে ভারতকে এস ৫০০ আন্তমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা সিস্টেম হস্তান্তর, অতিরিক্ত সামরিক প্ল্যাটফর্ম, হেলিকপ্টার ও ইঞ্জিন কো-প্রোডাকশনসহ দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পগুলো নিয়ে আবারও তাদের প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করেছে। ‘প্রিভিলেজ কম্প্রিহেনসিভ স্ট্র্যাটেজিকস পার্টনারশিপ’ চুক্তির আওতায় রাশিয়ার সেনাবাহিনী ভারতের যেকোনো স্থল, বিমান ও নৌবন্দরকে তাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবে। সামরিক প্রয়োজনে একে অন্যের ভূমিও ব্যবহার করতে পারবে। মার্কিন নিষেধাজ্ঞার ঝুঁকি সত্ত্বেও রাশিয়ার সঙ্গে এই প্রতিরক্ষা বোঝাপড়ার মাধ্যমে ভারত তাদের কৌশলগত নিজস্বতা নিশ্চিত করল।
জ্বালানি ও অর্থনৈতিক সুবিধা
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ-পরবর্তী পরিস্থিতিতে ভারত রাশিয়া থেকে অনেক কম মূল্যে বিপুল তেল আমদানি করছে। এই সফরের মাধ্যমে ভারত তাদের জ্বালানিনিরাপত্তা, পরিশোধন সক্ষমতা, দীর্ঘমেয়াদি তেল-গ্যাস চুক্তিকে আরও শক্তিশালী করল। রাশিয়ার সস্তা অপরিশোধিত তেল ভারতের মুদ্রাস্ফীতি কমাতে, বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় ও সঞ্চয় করতে এবং পরিশোধন মুনাফা বাড়াতে সাহায্য করছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে বিশ্বে জ্বালানির বাজার অস্থিতিশীল হলে রাশিয়ার জ্বালানি শক্তি এই অঞ্চলে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতেও ভূমিকা রাখবে।
বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ
২০২৪-২৫ অর্থবছরে ভারত-রাশিয়ার দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য প্রায় ৬৮ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। যদিও এই বাণিজ্য ভারসাম্যমূলক নয়। রাশিয়ায় ভারতীয় আমদানি প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলার। তবে পুতিন-মোদি শীর্ষ সম্মেলনে উভয় দেশ ২০৩০ সালের মধ্যে এই বাণিজ্য ১০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এ ক্ষেত্রে বাণিজ্যপণ্যের তালিকা সম্প্রসারণ ঘটবে।
রাশিয়া ভারতীয় সরঞ্জাম, কাঁচামাল এবং খাদ্যপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিসহ দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য প্রসারিত ও বৈচিত্র্যময় করার উপায়গুলো অনুসন্ধান করবে। অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং সাংস্কৃতিক সহযোগিতার ওপর ভারত-রাশিয়া আন্তসরকারি কমিশনও গঠিত হবে। মহাকাশ গবেষণা ও ভারত-রাশিয়ার যৌথ সামরিক যন্ত্রাংশ নির্মাণ এবং ভারত তা তৃতীয় কোনো দেশে নিজের উৎপাদিত পণ্য বলে বিক্রিও করার সুবিধা পাবে। ভারতে রুশ নকশায় দ্বিতীয় বৃহত্তম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনার কথা জানানো হয়।
ভূরাজনীতি ও কূটনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি
রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ভারতের জন্য চীন-রাশিয়া ব্লকের মধ্যে কিছুটা ভারসাম্য তৈরি করবে। ভবিষ্যতে চীন সীমান্ত সমস্যায় রাশিয়ার নিরপেক্ষতা বজায় রাখা ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মধ্য এশিয়া, আর্কটিক, নর্থ-সাউথ ট্রান্সপোর্ট করিডর—এইসব কৌশলগত এলাকায় সহযোগিতা বাড়ানো ভারতের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থ রক্ষায় সহজ হবে।
বর্তমান বিশ্ববাস্তবতায় রাশিয়া চীনের ওপর ক্রমেই নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে এবং একে অন্যের বন্ধুত্ব ও আস্থার সম্পর্ক তারা নিজেরাই ঘোষণা করেছে। এই পরিস্থিতিতে রাশিয়া-ভারতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখার মাধ্যমে চীনকেও জানিয়ে দেওয়া যে, রাশিয়া এখনো ভারতের গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অংশীদার।
রুশ প্রেসিডেন্টের ভারত সফরের আগে ভারতের সাংবাদিকেরা পুতিনের মুখপাত্র দমিত্রি পেসকভকে প্রশ্ন করেছিলেন, ভারত ও চীনের মধ্যে যদি কোনো সংঘাত ও যুদ্ধ হয়, সে ক্ষেত্রে ভারত কি আশা করতে পারে যে রাশিয়া তাদের পাশে দাঁড়াবে? তিনি বলেছিলেন, ‘আমরা আশা করি, ভারতের সঙ্গে চীনের যে বিরোধগুলো আছে, সেগুলো তারা মিটিয়ে ফেলবে। এ ক্ষেত্রে রাশিয়া একটি প্রস্তাবও দিয়েছিল হিমালয়ের ওপর দিয়ে সীমান্ত রেখা নিয়ে যে সমস্যা, সেটাকে তারা জিপিএস পদ্ধতি ব্যবহার করে সমাধান করতে পারে। সে ক্ষেত্রে রাশিয়া সহায়তা করতে পারে।’
পাকিস্তান রাশিয়া থেকে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কিছু সামরিক ও জ্বালানি সুবিধা নিতে চেয়েছিল, কিন্তু সেটা হয়ে ওঠেনি। পুতিনের ভারত সফর পরিষ্কার করে দিয়েছে যে দক্ষিণ এশিয়ায় রাশিয়ার মূল অংশীদার এখনো ভারতই। এটি ভারতের আঞ্চলিক নেতৃত্বের অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করবে।
ব্রিকস সম্প্রসারণের সময় ভারত-রাশিয়া সমন্বয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ব্রিকসের নেতৃত্বে জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্যপদের ভারতের আকাঙ্ক্ষাকে রাশিয়ার সমর্থন ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতির কথাও জানা গেছে। গ্লোবাল সাউথে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতায় ভারত দেখাতে চায় যে তার পশ্চিমা ও অ-পশ্চিমা উভয় ব্লকের ওপর প্রভাব আছে।
ভারতের যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্কের সমীকরণ
যুক্তরাষ্ট্র ভারতের প্রধান নিরাপত্তা অংশীদার হলেও ভারত রাশিয়ার সঙ্গে এই সংযোগ ও সম্পর্কের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছে যে মিত্রতা মানেই নির্ভরতা নয়, নিজেদের স্বকীয়তাকে বিসর্জন দেওয়া নয়। ভারতের এই অবস্থান ওয়াশিংটনের কাছে স্পষ্ট
বার্তা দেয় যে ‘India will cooperate, but not at the cost of its autonomy.’ ভারত-রাশিয়ার এই কৌশলগত সম্পর্ক দক্ষিণ এশিয়া ও ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলের সমীকরণে নতুন ভারসাম্য তৈরি করবে।
যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, জাপানসহ পশ্চিমা দেশগুলোর চাপ থাকা সত্ত্বেও ভারত রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে দেখিয়েছে যে ভারত কারও বা কোনো বলয়ে আবদ্ধ বা দায়বদ্ধ নয়। ভারতের এই স্বতন্ত্র অবস্থান বলে দেয়, জাতীয় স্বার্থ অনুযায়ী তারা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম এবং এটি তাদের একটি মূলনীতির দৃঢ় প্রকাশ।
সামগ্রিক মূল্যায়ন
পুতিনের ভারত সফর একটি ভূকৌশলগত বার্তা—ভারত তার বহুমুখী বৈদেশিক নীতি ও কৌশলগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চীন, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এক প্রভাবশালী মধ্যম শক্তি হিসেবে অবস্থান করছে। পুতিনের এই সফরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা হচ্ছে, ভারত রাশিয়ার সঙ্গে জ্বালানি, প্রতিরক্ষা ও ভূরাজনীতিতে ঘনিষ্ঠ থাকবে, একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অংশীদারত্বও বজায় রাখবে। অর্থাৎ ভারত কারও পরনির্ভর নয়; বরং নিজস্ব স্বার্থের ভিত্তিতে ‘ভারসাম্যপূর্ণ ক্ষমতার রাজনীতি করবে। রাশিয়া এই সম্পর্ককে ব্যবহার করে পশ্চিমা, বিশেষ করে ইউরোপ ও আমেরিকার একচেটিয়া কূটনীতির বিকল্প হিসেবে ভারতকে দেখছে।
কয়েক মাস ধরে আমেরিকার পক্ষ থেকে ভারতকে রাশিয়ার তেল আমদানি ও রাশিয়া-ভারত সম্পর্কের চাপ তৈরি করেছে শুল্ক বৃদ্ধির অস্ত্রকে ব্যবহার করে। তা সত্ত্বেও ভারত তাকে গুরুত্ব না দিয়ে তাদের নিজস্ব নীতিতে অগ্রসর হয়েছে। রাশিয়া ঐতিহাসিকভাবে ভারতের প্রতিরক্ষা অংশীদার—পাকিস্তান যত আমেরিকার দিকে ঝুঁকেছে, ভারত তত কাছে পেয়েছে রাশিয়াকে। এ জন্যই দেশ দুটি সামরিক ও সামরিক প্রযুক্তিগত অংশীদারত্বের অন্যতম প্রধান বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেছে। পুতিনের সফরের আগে এক ব্রিফিংয়ে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেছেন, ভারতের সঙ্গে যা ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে, তার সবই ভাগ করে নেওয়া হবে। পুতিনও এই সফরের মাধ্যমে রাশিয়াকে একঘরে করার যে পশ্চিমা প্রচার ছিল, তার অনেকটা ভুল প্রমাণ করেছেন।

গত সপ্তাহে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ভারত সফর ও উভয় নেতার শীর্ষ বৈঠক অনেক কিছুরই ইঙ্গিত করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পুতিনকে যেভাবে আলিঙ্গন করেছেন, স্বাগত জানিয়েছেন, একই গাড়িতে যাত্রা করেছেন, তা আলাস্কায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে পুতিনের সাক্ষাতের কথাই মনে করিয়ে দেয়। মোদি প্রেসিডেন্ট পুতিনকে সময়ের পরীক্ষিত বন্ধু, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও আস্থার প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করেন। এই আস্থা ও হৃদ্যতা ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের গভীর মাত্রাকেই নির্দেশ করে। পুতিন তাঁর ক্ষমতা গ্রহণের ২৫ বছরে ১০ বার ভারত সফর করেছেন। তবে ২০২২ সালে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর এটিই ছিল তাঁর প্রথম ভারত সফর।
পুতিনের এই ভারত সফর নিছক কোনো রুটিন বিষয় ছিল না। ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের ধারাবাহিকতা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা প্রদান করে। তাঁদের সাক্ষাৎ ছিল বিশ্বরাজনীতির আগ্রহের বিষয়, কেননা ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর শুল্ক নিয়ে মোদির সঙ্গে যে সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছিল ও বরফ গলছিল, তখনই পুতিন ভারত সফর করলেন। প্রশ্ন হচ্ছে, ভারত-রাশিয়া এই বৈঠকে কে কী অর্জন করল, তার কয়েকটি দিক আলোচনা করা যাক।
প্রতিরক্ষা সহযোগিতা
পুতিনের এই সফরের মাধ্যমে ভারত তাদের প্রতিরক্ষা সহযোগিতার বিষয়টি পুনরায় নিশ্চিত করল। রাশিয়া এখনো ভারতের প্রধান সমরাস্ত্রের সরবরাহকারী। যদিও ১৯৭০-৮০-এর দশকে ভারতের অস্ত্রের প্রায় ৮০ ভাগই রাশিয়া সরবরাহ করত। পুতিন এবারের সফরে ভারতকে এস ৫০০ আন্তমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা সিস্টেম হস্তান্তর, অতিরিক্ত সামরিক প্ল্যাটফর্ম, হেলিকপ্টার ও ইঞ্জিন কো-প্রোডাকশনসহ দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পগুলো নিয়ে আবারও তাদের প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করেছে। ‘প্রিভিলেজ কম্প্রিহেনসিভ স্ট্র্যাটেজিকস পার্টনারশিপ’ চুক্তির আওতায় রাশিয়ার সেনাবাহিনী ভারতের যেকোনো স্থল, বিমান ও নৌবন্দরকে তাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবে। সামরিক প্রয়োজনে একে অন্যের ভূমিও ব্যবহার করতে পারবে। মার্কিন নিষেধাজ্ঞার ঝুঁকি সত্ত্বেও রাশিয়ার সঙ্গে এই প্রতিরক্ষা বোঝাপড়ার মাধ্যমে ভারত তাদের কৌশলগত নিজস্বতা নিশ্চিত করল।
জ্বালানি ও অর্থনৈতিক সুবিধা
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ-পরবর্তী পরিস্থিতিতে ভারত রাশিয়া থেকে অনেক কম মূল্যে বিপুল তেল আমদানি করছে। এই সফরের মাধ্যমে ভারত তাদের জ্বালানিনিরাপত্তা, পরিশোধন সক্ষমতা, দীর্ঘমেয়াদি তেল-গ্যাস চুক্তিকে আরও শক্তিশালী করল। রাশিয়ার সস্তা অপরিশোধিত তেল ভারতের মুদ্রাস্ফীতি কমাতে, বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় ও সঞ্চয় করতে এবং পরিশোধন মুনাফা বাড়াতে সাহায্য করছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে বিশ্বে জ্বালানির বাজার অস্থিতিশীল হলে রাশিয়ার জ্বালানি শক্তি এই অঞ্চলে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতেও ভূমিকা রাখবে।
বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ
২০২৪-২৫ অর্থবছরে ভারত-রাশিয়ার দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য প্রায় ৬৮ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। যদিও এই বাণিজ্য ভারসাম্যমূলক নয়। রাশিয়ায় ভারতীয় আমদানি প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলার। তবে পুতিন-মোদি শীর্ষ সম্মেলনে উভয় দেশ ২০৩০ সালের মধ্যে এই বাণিজ্য ১০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এ ক্ষেত্রে বাণিজ্যপণ্যের তালিকা সম্প্রসারণ ঘটবে।
রাশিয়া ভারতীয় সরঞ্জাম, কাঁচামাল এবং খাদ্যপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিসহ দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য প্রসারিত ও বৈচিত্র্যময় করার উপায়গুলো অনুসন্ধান করবে। অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং সাংস্কৃতিক সহযোগিতার ওপর ভারত-রাশিয়া আন্তসরকারি কমিশনও গঠিত হবে। মহাকাশ গবেষণা ও ভারত-রাশিয়ার যৌথ সামরিক যন্ত্রাংশ নির্মাণ এবং ভারত তা তৃতীয় কোনো দেশে নিজের উৎপাদিত পণ্য বলে বিক্রিও করার সুবিধা পাবে। ভারতে রুশ নকশায় দ্বিতীয় বৃহত্তম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনার কথা জানানো হয়।
ভূরাজনীতি ও কূটনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি
রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ভারতের জন্য চীন-রাশিয়া ব্লকের মধ্যে কিছুটা ভারসাম্য তৈরি করবে। ভবিষ্যতে চীন সীমান্ত সমস্যায় রাশিয়ার নিরপেক্ষতা বজায় রাখা ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মধ্য এশিয়া, আর্কটিক, নর্থ-সাউথ ট্রান্সপোর্ট করিডর—এইসব কৌশলগত এলাকায় সহযোগিতা বাড়ানো ভারতের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থ রক্ষায় সহজ হবে।
বর্তমান বিশ্ববাস্তবতায় রাশিয়া চীনের ওপর ক্রমেই নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে এবং একে অন্যের বন্ধুত্ব ও আস্থার সম্পর্ক তারা নিজেরাই ঘোষণা করেছে। এই পরিস্থিতিতে রাশিয়া-ভারতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখার মাধ্যমে চীনকেও জানিয়ে দেওয়া যে, রাশিয়া এখনো ভারতের গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অংশীদার।
রুশ প্রেসিডেন্টের ভারত সফরের আগে ভারতের সাংবাদিকেরা পুতিনের মুখপাত্র দমিত্রি পেসকভকে প্রশ্ন করেছিলেন, ভারত ও চীনের মধ্যে যদি কোনো সংঘাত ও যুদ্ধ হয়, সে ক্ষেত্রে ভারত কি আশা করতে পারে যে রাশিয়া তাদের পাশে দাঁড়াবে? তিনি বলেছিলেন, ‘আমরা আশা করি, ভারতের সঙ্গে চীনের যে বিরোধগুলো আছে, সেগুলো তারা মিটিয়ে ফেলবে। এ ক্ষেত্রে রাশিয়া একটি প্রস্তাবও দিয়েছিল হিমালয়ের ওপর দিয়ে সীমান্ত রেখা নিয়ে যে সমস্যা, সেটাকে তারা জিপিএস পদ্ধতি ব্যবহার করে সমাধান করতে পারে। সে ক্ষেত্রে রাশিয়া সহায়তা করতে পারে।’
পাকিস্তান রাশিয়া থেকে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কিছু সামরিক ও জ্বালানি সুবিধা নিতে চেয়েছিল, কিন্তু সেটা হয়ে ওঠেনি। পুতিনের ভারত সফর পরিষ্কার করে দিয়েছে যে দক্ষিণ এশিয়ায় রাশিয়ার মূল অংশীদার এখনো ভারতই। এটি ভারতের আঞ্চলিক নেতৃত্বের অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করবে।
ব্রিকস সম্প্রসারণের সময় ভারত-রাশিয়া সমন্বয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ব্রিকসের নেতৃত্বে জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্যপদের ভারতের আকাঙ্ক্ষাকে রাশিয়ার সমর্থন ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতির কথাও জানা গেছে। গ্লোবাল সাউথে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতায় ভারত দেখাতে চায় যে তার পশ্চিমা ও অ-পশ্চিমা উভয় ব্লকের ওপর প্রভাব আছে।
ভারতের যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্কের সমীকরণ
যুক্তরাষ্ট্র ভারতের প্রধান নিরাপত্তা অংশীদার হলেও ভারত রাশিয়ার সঙ্গে এই সংযোগ ও সম্পর্কের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছে যে মিত্রতা মানেই নির্ভরতা নয়, নিজেদের স্বকীয়তাকে বিসর্জন দেওয়া নয়। ভারতের এই অবস্থান ওয়াশিংটনের কাছে স্পষ্ট
বার্তা দেয় যে ‘India will cooperate, but not at the cost of its autonomy.’ ভারত-রাশিয়ার এই কৌশলগত সম্পর্ক দক্ষিণ এশিয়া ও ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলের সমীকরণে নতুন ভারসাম্য তৈরি করবে।
যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, জাপানসহ পশ্চিমা দেশগুলোর চাপ থাকা সত্ত্বেও ভারত রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে দেখিয়েছে যে ভারত কারও বা কোনো বলয়ে আবদ্ধ বা দায়বদ্ধ নয়। ভারতের এই স্বতন্ত্র অবস্থান বলে দেয়, জাতীয় স্বার্থ অনুযায়ী তারা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম এবং এটি তাদের একটি মূলনীতির দৃঢ় প্রকাশ।
সামগ্রিক মূল্যায়ন
পুতিনের ভারত সফর একটি ভূকৌশলগত বার্তা—ভারত তার বহুমুখী বৈদেশিক নীতি ও কৌশলগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চীন, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এক প্রভাবশালী মধ্যম শক্তি হিসেবে অবস্থান করছে। পুতিনের এই সফরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা হচ্ছে, ভারত রাশিয়ার সঙ্গে জ্বালানি, প্রতিরক্ষা ও ভূরাজনীতিতে ঘনিষ্ঠ থাকবে, একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অংশীদারত্বও বজায় রাখবে। অর্থাৎ ভারত কারও পরনির্ভর নয়; বরং নিজস্ব স্বার্থের ভিত্তিতে ‘ভারসাম্যপূর্ণ ক্ষমতার রাজনীতি করবে। রাশিয়া এই সম্পর্ককে ব্যবহার করে পশ্চিমা, বিশেষ করে ইউরোপ ও আমেরিকার একচেটিয়া কূটনীতির বিকল্প হিসেবে ভারতকে দেখছে।
কয়েক মাস ধরে আমেরিকার পক্ষ থেকে ভারতকে রাশিয়ার তেল আমদানি ও রাশিয়া-ভারত সম্পর্কের চাপ তৈরি করেছে শুল্ক বৃদ্ধির অস্ত্রকে ব্যবহার করে। তা সত্ত্বেও ভারত তাকে গুরুত্ব না দিয়ে তাদের নিজস্ব নীতিতে অগ্রসর হয়েছে। রাশিয়া ঐতিহাসিকভাবে ভারতের প্রতিরক্ষা অংশীদার—পাকিস্তান যত আমেরিকার দিকে ঝুঁকেছে, ভারত তত কাছে পেয়েছে রাশিয়াকে। এ জন্যই দেশ দুটি সামরিক ও সামরিক প্রযুক্তিগত অংশীদারত্বের অন্যতম প্রধান বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেছে। পুতিনের সফরের আগে এক ব্রিফিংয়ে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেছেন, ভারতের সঙ্গে যা ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে, তার সবই ভাগ করে নেওয়া হবে। পুতিনও এই সফরের মাধ্যমে রাশিয়াকে একঘরে করার যে পশ্চিমা প্রচার ছিল, তার অনেকটা ভুল প্রমাণ করেছেন।
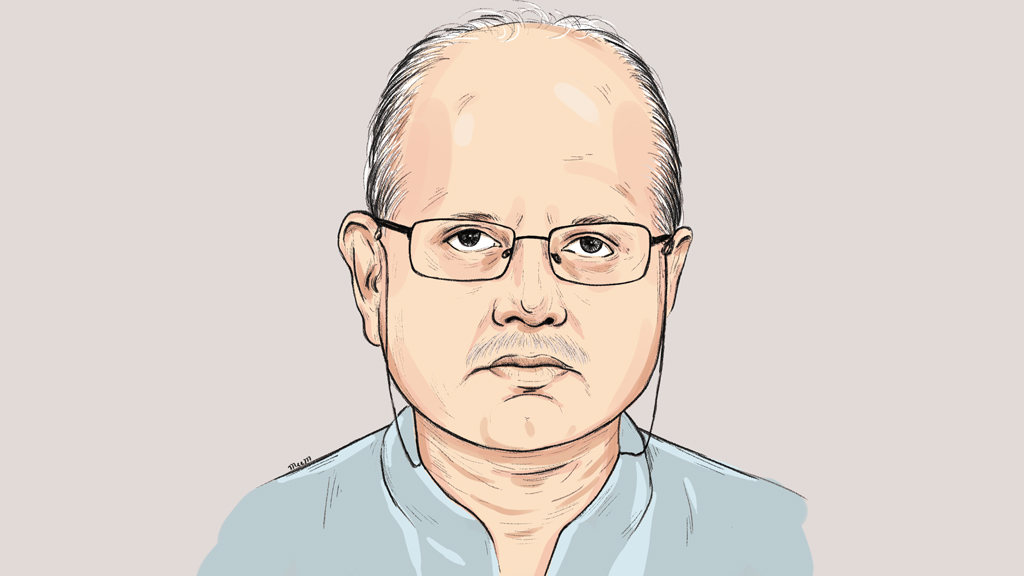
কাকু কোনো কথা শোনেন না। একপর্যায়ে পিটিয়ে ক্লান্ত হয়ে আমাদের সবাইকে শাসিয়ে তিনি চলে যান। আমরা ভাবলাম, অত পিটুনি খেয়ে তপু হয়তো আর সিনেমা দেখতে যাবে না। কিন্তু আমাদের অবাক করে তপু বলল, ‘মার তো খেয়েই ফেলেছি, তাহলে আর সিনেমা দেখা থেকে বঞ্চিত হব কেন?’
০৫ মে ২০২২
অবশেষে ১১ ডিসেম্বর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হলো। ইতিমধ্যে সবাই জেনে গেছেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন একই দিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের পথরেখা বেঁধে দিলেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তফসিল নিয়ে তাদের মতামত জানিয়েছে।
৩ ঘণ্টা আগে
হঠাৎ করেই বিজয়ের মাসে দেখা গেল মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কটূক্তি করছে একদল মানুষ। এই প্রবণতাকে পাত্তা না দিলেও চলত, কিন্তু সেগুলো যদি জাতীয় প্রচারমাধ্যম থেকে প্রচারিত হয়, তখন সত্যিই একটু ভাবতে হয়। এর যে প্রতিবাদ হওয়া দরকার, সেটা অনুভব করতে হয়। আইন বিষয়ে পড়াশোনা করলে আইন ভালোভাবে শেখা হয় বটে...
৪ ঘণ্টা আগে
ঢাকা শহরের যানজটের সমস্যা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি দিয়েছে মেট্রোরেল। তবে এটা চালুর প্রায় দেড় বছরে এই আধুনিক গণপরিবহনব্যবস্থা মাঝে মাঝে বন্ধ হয়েছে। সেটা একটা ভাবনার বিষয়। মূলত এই সময়ের মধ্যে অন্তত ১০ বার মেট্রোরেল চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়েছে, যার বেশির ভাগই জনগণের গাফিলতির কারণে হয়েছে।
১ দিন আগেসম্পাদকীয়

ঢাকা শহরের যানজটের সমস্যা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি দিয়েছে মেট্রোরেল। তবে এটা চালুর প্রায় দেড় বছরে এই আধুনিক গণপরিবহনব্যবস্থা মাঝে মাঝে বন্ধ হয়েছে। সেটা একটা ভাবনার বিষয়। মূলত এই সময়ের মধ্যে অন্তত ১০ বার মেট্রোরেল চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়েছে, যার বেশির ভাগই জনগণের গাফিলতির কারণে হয়েছে।
এই দেড় বছরে মেট্রোরেল লাইনে কাপড়, ব্যাগ, ড্রোন, তার নিক্ষেপের কারণে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে। এখনই যদি এসব সমস্যা সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ না করা যায়, তাহলে ভবিষ্যতে আরও বড় দুর্ঘটনার ঝুঁকি তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। একটা ভালো ব্যাপার যে, মেট্রোরেলের নিরাপত্তাব্যবস্থা এমন যে রেললাইনে সামান্যতম বাধা সৃষ্টি হলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেন থেমে যায়। এটি দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য ভালো দিক হলেও, মানবসৃষ্ট কারণে ঘন ঘন এই থমকে যাওয়া আধুনিক এই ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে কর্তৃপক্ষকে সেসব সমস্যা সমাধানের দিকে দৃষ্টি দেওয়া জরুরি।
জনগণ দ্বারা সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে করণীয় নিয়ে এখনই ভাবতে হবে কর্তৃপক্ষকে। তবে প্রযুক্তিগত সমস্যাও যে আছে, তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। কিছুদিন আগে ফার্মগেট এলাকায় বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ে একজনের নিহত হওয়ার ঘটনাটি এই আধুনিক পরিবহনব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা তৈরি করেছে। বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ার ঘটনায় ১১ ঘণ্টা পর্যন্ত ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। যান্ত্রিক ত্রুটি হতেই পারে, তবে গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা সরঞ্জাম বারবার বিকল হওয়া বা খুলে পড়ার ঘটনাটি মেট্রোরেলের কারিগরি তদারকি ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করেছে। এ ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত নজরদারি ও রক্ষণাবেক্ষণে আরও গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক। এক সূত্র থেকে জানা যায়, এই নিহতের ঘটনা এবং অন্যান্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মেট্রোরেলে আগের তুলনায় ১০ শতাংশ যাত্রী কমে গেছে।
যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা মেট্রোরেল চলাচল স্বাভাবিক রাখতে কিছু কার্যকর পদক্ষেপের পরামর্শ দিয়েছেন। যেমন মেট্রোরেলের লাইনে বস্তু শনাক্ত করতে ‘অবজেক্ট ডিটেকশন সেন্সর’ ও ‘এআই-চালিত সিসিটিভি’ স্থাপন করা, ড্রোন পড়া প্রতিরোধে ‘ড্রোন ডিটেকশন রাডার’ ও ‘জিওফেন্সিং সিস্টেম’ ব্যবহার করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া। এ ছাড়া বৈদ্যুতিক লাইনে সুরক্ষা নেট বসালে বাইরে থেকে তার বা বস্তু নিক্ষেপ ঠেকানো সম্ভব।
মেট্রোরেল দেশের সম্পদ। জনগণের মধ্যে সে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এর সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব। ডিএমটিসিএলকে প্রযুক্তিগত ত্রুটিগুলো দ্রুত সমাধান এবং রক্ষণাবেক্ষণে সর্বোচ্চ মান বজায় রাখতে হবে। একই সঙ্গে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে, যাতে মানুষ বুঝতে পারে তাদের সামান্য ভুল বা অসচেতনতা হাজার হাজার যাত্রীর ভোগান্তি এবং মারাত্মক দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। সচেতনতা ও প্রযুক্তিগত সুরক্ষা—এই দুইয়ের সমন্বয়েই কেবল মেট্রোরেলের মসৃণ ও নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করা সম্ভব। এই আধুনিক পরিষেবা যেন মাঝে মাঝে থমকে যাওয়ার দুর্নাম থেকে মুক্তি পায়, সেই প্রত্যাশা আমাদের।

ঢাকা শহরের যানজটের সমস্যা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি দিয়েছে মেট্রোরেল। তবে এটা চালুর প্রায় দেড় বছরে এই আধুনিক গণপরিবহনব্যবস্থা মাঝে মাঝে বন্ধ হয়েছে। সেটা একটা ভাবনার বিষয়। মূলত এই সময়ের মধ্যে অন্তত ১০ বার মেট্রোরেল চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়েছে, যার বেশির ভাগই জনগণের গাফিলতির কারণে হয়েছে।
এই দেড় বছরে মেট্রোরেল লাইনে কাপড়, ব্যাগ, ড্রোন, তার নিক্ষেপের কারণে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে। এখনই যদি এসব সমস্যা সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ না করা যায়, তাহলে ভবিষ্যতে আরও বড় দুর্ঘটনার ঝুঁকি তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। একটা ভালো ব্যাপার যে, মেট্রোরেলের নিরাপত্তাব্যবস্থা এমন যে রেললাইনে সামান্যতম বাধা সৃষ্টি হলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেন থেমে যায়। এটি দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য ভালো দিক হলেও, মানবসৃষ্ট কারণে ঘন ঘন এই থমকে যাওয়া আধুনিক এই ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে কর্তৃপক্ষকে সেসব সমস্যা সমাধানের দিকে দৃষ্টি দেওয়া জরুরি।
জনগণ দ্বারা সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে করণীয় নিয়ে এখনই ভাবতে হবে কর্তৃপক্ষকে। তবে প্রযুক্তিগত সমস্যাও যে আছে, তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। কিছুদিন আগে ফার্মগেট এলাকায় বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ে একজনের নিহত হওয়ার ঘটনাটি এই আধুনিক পরিবহনব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা তৈরি করেছে। বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ার ঘটনায় ১১ ঘণ্টা পর্যন্ত ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। যান্ত্রিক ত্রুটি হতেই পারে, তবে গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা সরঞ্জাম বারবার বিকল হওয়া বা খুলে পড়ার ঘটনাটি মেট্রোরেলের কারিগরি তদারকি ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করেছে। এ ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত নজরদারি ও রক্ষণাবেক্ষণে আরও গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক। এক সূত্র থেকে জানা যায়, এই নিহতের ঘটনা এবং অন্যান্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মেট্রোরেলে আগের তুলনায় ১০ শতাংশ যাত্রী কমে গেছে।
যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা মেট্রোরেল চলাচল স্বাভাবিক রাখতে কিছু কার্যকর পদক্ষেপের পরামর্শ দিয়েছেন। যেমন মেট্রোরেলের লাইনে বস্তু শনাক্ত করতে ‘অবজেক্ট ডিটেকশন সেন্সর’ ও ‘এআই-চালিত সিসিটিভি’ স্থাপন করা, ড্রোন পড়া প্রতিরোধে ‘ড্রোন ডিটেকশন রাডার’ ও ‘জিওফেন্সিং সিস্টেম’ ব্যবহার করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া। এ ছাড়া বৈদ্যুতিক লাইনে সুরক্ষা নেট বসালে বাইরে থেকে তার বা বস্তু নিক্ষেপ ঠেকানো সম্ভব।
মেট্রোরেল দেশের সম্পদ। জনগণের মধ্যে সে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এর সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব। ডিএমটিসিএলকে প্রযুক্তিগত ত্রুটিগুলো দ্রুত সমাধান এবং রক্ষণাবেক্ষণে সর্বোচ্চ মান বজায় রাখতে হবে। একই সঙ্গে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে, যাতে মানুষ বুঝতে পারে তাদের সামান্য ভুল বা অসচেতনতা হাজার হাজার যাত্রীর ভোগান্তি এবং মারাত্মক দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। সচেতনতা ও প্রযুক্তিগত সুরক্ষা—এই দুইয়ের সমন্বয়েই কেবল মেট্রোরেলের মসৃণ ও নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করা সম্ভব। এই আধুনিক পরিষেবা যেন মাঝে মাঝে থমকে যাওয়ার দুর্নাম থেকে মুক্তি পায়, সেই প্রত্যাশা আমাদের।
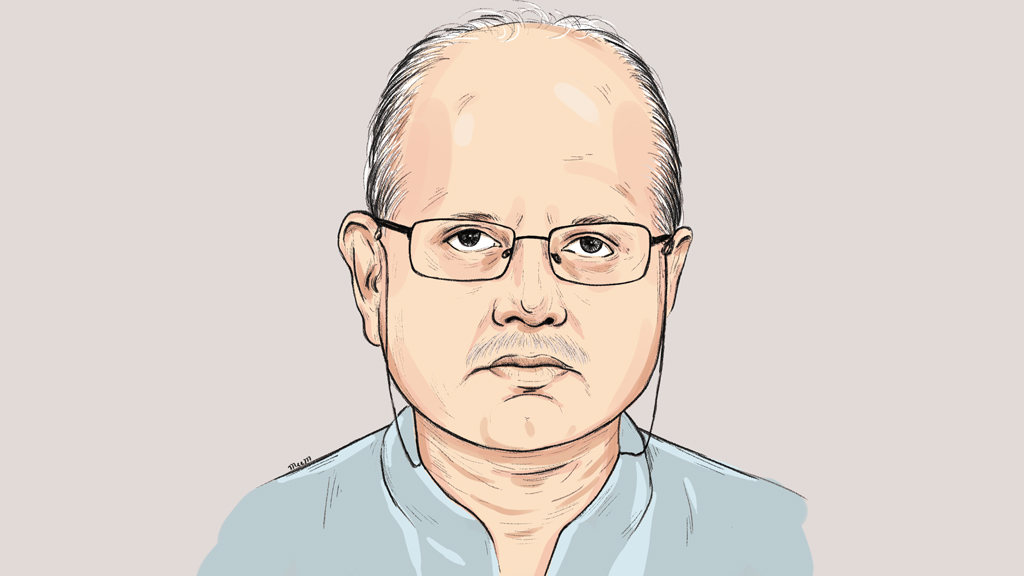
কাকু কোনো কথা শোনেন না। একপর্যায়ে পিটিয়ে ক্লান্ত হয়ে আমাদের সবাইকে শাসিয়ে তিনি চলে যান। আমরা ভাবলাম, অত পিটুনি খেয়ে তপু হয়তো আর সিনেমা দেখতে যাবে না। কিন্তু আমাদের অবাক করে তপু বলল, ‘মার তো খেয়েই ফেলেছি, তাহলে আর সিনেমা দেখা থেকে বঞ্চিত হব কেন?’
০৫ মে ২০২২
অবশেষে ১১ ডিসেম্বর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হলো। ইতিমধ্যে সবাই জেনে গেছেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন একই দিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের পথরেখা বেঁধে দিলেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তফসিল নিয়ে তাদের মতামত জানিয়েছে।
৩ ঘণ্টা আগে
হঠাৎ করেই বিজয়ের মাসে দেখা গেল মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কটূক্তি করছে একদল মানুষ। এই প্রবণতাকে পাত্তা না দিলেও চলত, কিন্তু সেগুলো যদি জাতীয় প্রচারমাধ্যম থেকে প্রচারিত হয়, তখন সত্যিই একটু ভাবতে হয়। এর যে প্রতিবাদ হওয়া দরকার, সেটা অনুভব করতে হয়। আইন বিষয়ে পড়াশোনা করলে আইন ভালোভাবে শেখা হয় বটে...
৪ ঘণ্টা আগে
গত সপ্তাহে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ভারত সফর ও উভয় নেতার শীর্ষ বৈঠক অনেক কিছুরই ইঙ্গিত করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পুতিনকে যেভাবে আলিঙ্গন করেছেন, স্বাগত জানিয়েছেন, একই গাড়িতে যাত্রা করেছেন, তা আলাস্কায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে পুতিনের সাক্ষাতের কথাই মনে করিয়ে দেয়।
৪ ঘণ্টা আগে