সম্পাদকীয়
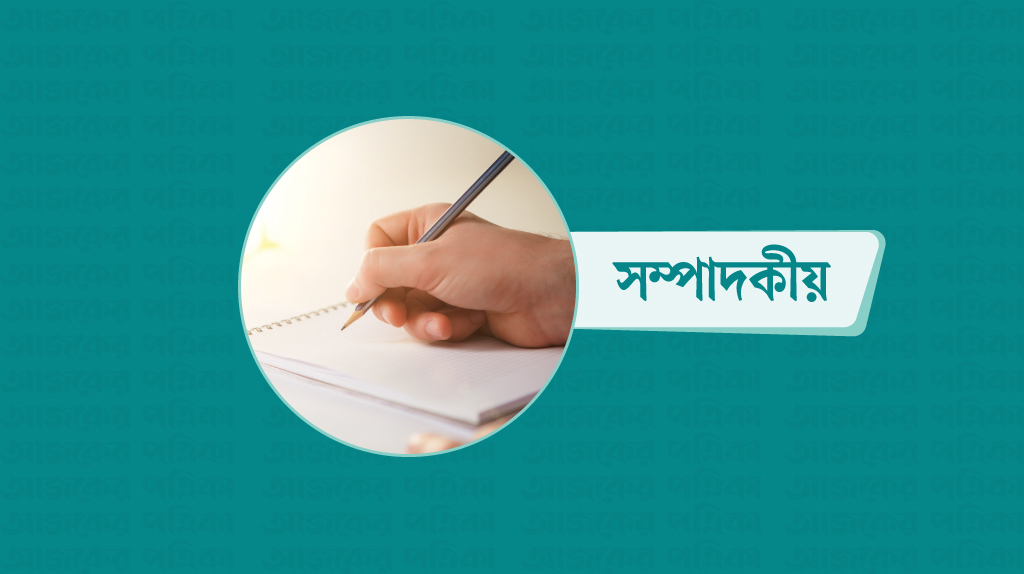
ঐতিহ্য সংরক্ষণের অঙ্গীকার না থাকলে যা হয়, তারই বেদনাদায়ক রূপ দেখা যাচ্ছে বড় কাটরা ঘিরে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর সামাজিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিরা গুঁড়িয়ে দিয়েছেন বড় কাটরার একাংশ। পুরান ঢাকার ঐতিহ্য এভাবেই একে একে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।
বড় কাটরার বিভিন্ন অংশ দখল করে নিয়ে নিজেরাই ওই অংশের মালিক দাবি করছেন কেউ কেউ। এই সংকট আজকের নয়, বহুদিন ধরেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাছে বাধা পড়েছে বড় কাটরা। সরকারের সদিচ্ছা থাকলে ইতিহাসের অংশ এই ভবন রক্ষা করা কোনো কঠিন ব্যাপার ছিল না। কিন্তু আমাদের দেশে কোনো সরকারই ঐতিহ্য সংরক্ষণের বিষয়টি আমলে নেয়নি। কিছু প্রবোধ দেওয়া কথাবার্তা বলে জনমন তুষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে বটে, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি।
ঢাকা যখন বাংলার মোগল রাজধানী, তখন চকবাজারের দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা নদীর পারে নির্মিত হয়েছিল বড় কাটরা। মোগল রাজকীয় স্থাপত্যরীতির সব বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ দেখা যায় বড় কাটরায়। মধ্য এশিয়ার ক্যারাভান সরাইয়ের ঐতিহ্য অনুসারে তা নির্মিত হয়েছিল।
ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়ানো এই ভবনের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বলে রাখা ভালো। বিশাল এক প্রবেশপথের পরে অপেক্ষাকৃত ছোট আরও তিনটি প্রবেশপথ ছিল। এরপর অষ্টকোনাকৃতির একটি হল ছিল। ছাদ ছিল গম্বুজাকৃতির। তাতে পলেস্তারার ওপর নানা রকম লতাপাতার অলংকরণ ছিল। কাটরার ভেতরে দোতলা আর তৃতীয় তলায় ওঠার সিঁড়ি আছে। এই ওপরের দুই তলায় ছিল বসবাসের কক্ষ। প্রবেশপথের ওপরের অংশই ছিল তিনতলাবিশিষ্ট। বাকি অংশ ছিল দ্বিতল। দুটো শিলালিপির একটিতে লেখা ছিল ইমারতটি ১৬৪৩-৪৪ খ্রিষ্টাব্দে
নির্মিত হয়। অন্যটিতে ১৬৪৫-৪৬ খ্রিষ্টাব্দে নির্মাণের কথা আছে।
বড় কাটরা নিয়ে অনেক বিবরণ শোনা যায়। কিন্তু এখন যদি কেউ বুড়িগঙ্গাপারের এই ইমারত দেখতে চান, তাহলে তিনি তাঁর কল্পনার সঙ্গে মেলাতেই পারবেন না। বড় কাটরা এখন পর্যন্ত শেষ আঘাতটি পেয়েছে এই আগস্ট মাসে। এই উন্মত্ত আচরণের প্রতিকার দরকার।
আরবান স্টাডি গ্রুপের প্রধান নির্বাহী বুধবার রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনি মিলনায়তনে ‘মুঘল স্থাপনা বড় কাটরায় ধ্বংসযজ্ঞ: পুরান ঢাকার সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের অশনিসংকেত’ শিরোনামে এক সংবাদ সম্মেলনে বিপদে পড়া বড় কাটরা নিয়ে কথা বলেন।
এই স্থাপনা বাঁচানোর জন্য শুধু আরবান স্টাডিকেই এগিয়ে আসতে হবে কেন? স্থানীয় এলাকাবাসী, সমাজের মাথা, জনপ্রতিনিধিরা কেন নিজ এলাকার ঐতিহ্য রক্ষায় এগিয়ে আসছেন না? মালিক বনে যাওয়া দখলদারদের হাত থেকেও তো এই স্থাপনা মুক্ত করা দরকার।
যে জাতি তার ঐতিহ্য সম্পর্কে নির্লিপ্ত থাকে, সে জাতি কোন ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ গড়বে? অন্তর্বর্তী সরকারের উচিত পুরান ঢাকা তথা পুরো বাংলাদেশের পুরোনো ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য অচিরেই ব্যবস্থা নেওয়া। এগুলো রক্ষা করার কথা বারবার বলতে হবে কেন? কেন তা আইনি পথেই সংরক্ষিত হবে না—এটাই আমাদের প্রশ্ন।
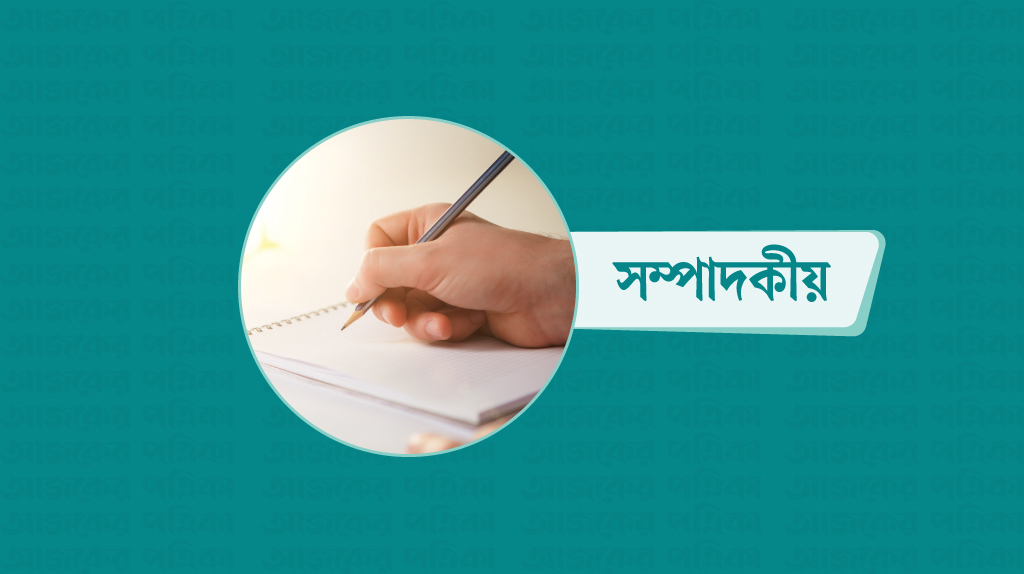
ঐতিহ্য সংরক্ষণের অঙ্গীকার না থাকলে যা হয়, তারই বেদনাদায়ক রূপ দেখা যাচ্ছে বড় কাটরা ঘিরে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর সামাজিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিরা গুঁড়িয়ে দিয়েছেন বড় কাটরার একাংশ। পুরান ঢাকার ঐতিহ্য এভাবেই একে একে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।
বড় কাটরার বিভিন্ন অংশ দখল করে নিয়ে নিজেরাই ওই অংশের মালিক দাবি করছেন কেউ কেউ। এই সংকট আজকের নয়, বহুদিন ধরেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাছে বাধা পড়েছে বড় কাটরা। সরকারের সদিচ্ছা থাকলে ইতিহাসের অংশ এই ভবন রক্ষা করা কোনো কঠিন ব্যাপার ছিল না। কিন্তু আমাদের দেশে কোনো সরকারই ঐতিহ্য সংরক্ষণের বিষয়টি আমলে নেয়নি। কিছু প্রবোধ দেওয়া কথাবার্তা বলে জনমন তুষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে বটে, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি।
ঢাকা যখন বাংলার মোগল রাজধানী, তখন চকবাজারের দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা নদীর পারে নির্মিত হয়েছিল বড় কাটরা। মোগল রাজকীয় স্থাপত্যরীতির সব বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ দেখা যায় বড় কাটরায়। মধ্য এশিয়ার ক্যারাভান সরাইয়ের ঐতিহ্য অনুসারে তা নির্মিত হয়েছিল।
ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়ানো এই ভবনের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বলে রাখা ভালো। বিশাল এক প্রবেশপথের পরে অপেক্ষাকৃত ছোট আরও তিনটি প্রবেশপথ ছিল। এরপর অষ্টকোনাকৃতির একটি হল ছিল। ছাদ ছিল গম্বুজাকৃতির। তাতে পলেস্তারার ওপর নানা রকম লতাপাতার অলংকরণ ছিল। কাটরার ভেতরে দোতলা আর তৃতীয় তলায় ওঠার সিঁড়ি আছে। এই ওপরের দুই তলায় ছিল বসবাসের কক্ষ। প্রবেশপথের ওপরের অংশই ছিল তিনতলাবিশিষ্ট। বাকি অংশ ছিল দ্বিতল। দুটো শিলালিপির একটিতে লেখা ছিল ইমারতটি ১৬৪৩-৪৪ খ্রিষ্টাব্দে
নির্মিত হয়। অন্যটিতে ১৬৪৫-৪৬ খ্রিষ্টাব্দে নির্মাণের কথা আছে।
বড় কাটরা নিয়ে অনেক বিবরণ শোনা যায়। কিন্তু এখন যদি কেউ বুড়িগঙ্গাপারের এই ইমারত দেখতে চান, তাহলে তিনি তাঁর কল্পনার সঙ্গে মেলাতেই পারবেন না। বড় কাটরা এখন পর্যন্ত শেষ আঘাতটি পেয়েছে এই আগস্ট মাসে। এই উন্মত্ত আচরণের প্রতিকার দরকার।
আরবান স্টাডি গ্রুপের প্রধান নির্বাহী বুধবার রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনি মিলনায়তনে ‘মুঘল স্থাপনা বড় কাটরায় ধ্বংসযজ্ঞ: পুরান ঢাকার সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের অশনিসংকেত’ শিরোনামে এক সংবাদ সম্মেলনে বিপদে পড়া বড় কাটরা নিয়ে কথা বলেন।
এই স্থাপনা বাঁচানোর জন্য শুধু আরবান স্টাডিকেই এগিয়ে আসতে হবে কেন? স্থানীয় এলাকাবাসী, সমাজের মাথা, জনপ্রতিনিধিরা কেন নিজ এলাকার ঐতিহ্য রক্ষায় এগিয়ে আসছেন না? মালিক বনে যাওয়া দখলদারদের হাত থেকেও তো এই স্থাপনা মুক্ত করা দরকার।
যে জাতি তার ঐতিহ্য সম্পর্কে নির্লিপ্ত থাকে, সে জাতি কোন ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ গড়বে? অন্তর্বর্তী সরকারের উচিত পুরান ঢাকা তথা পুরো বাংলাদেশের পুরোনো ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য অচিরেই ব্যবস্থা নেওয়া। এগুলো রক্ষা করার কথা বারবার বলতে হবে কেন? কেন তা আইনি পথেই সংরক্ষিত হবে না—এটাই আমাদের প্রশ্ন।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লা এলাকায় যাত্রীবাহী বাসে ডাকাতি বেড়েই চলছে। এ কারণে চালক ও যাত্রীদের কাছে আতঙ্কের নাম হয়ে উঠছে এই সড়ক। ডাকাতির শিকার বেশি হচ্ছেন প্রবাসফেরত লোকজন। ডাকাতেরা অস্ত্র ঠেকিয়ে লুট করে নিচ্ছে সর্বস্ব। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়েও ঘটছে ডাকাতির ঘটনা।
০২ মার্চ ২০২৫
বিআরটিসির বাস দিয়ে চালু করা বিশেষায়িত বাস র্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) লেনে অনুমতি না নিয়েই চলছে বেসরকারি কোম্পানির কিছু বাস। ঢুকে পড়ছে সিএনজিচালিত অটোরিকশা, ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা। উল্টো পথে চলছে মোটরসাইকেল। অন্যদিকে বিআরটিসির মাত্র ১০টি বাস চলাচল করায় সোয়া চার হাজার কোটি টাকার এই প্রকল্প থেকে...
১৬ জানুয়ারি ২০২৫
গাজীপুর মহানগরের বোর্ডবাজার এলাকার ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির (আইইউটি) মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থীরা পিকনিকে যাচ্ছিলেন শ্রীপুরের মাটির মায়া ইকো রিসোর্টে। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক থেকে বাসগুলো গ্রামের সরু সড়কে ঢোকার পর বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে যায় বিআরটিসির একটি দোতলা বাস...
২৪ নভেম্বর ২০২৪
ঝড়-জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষায় সন্দ্বীপের ব্লক বেড়িবাঁধসহ একাধিক প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ৫৬২ কোটি টাকা। এ জন্য টেন্ডারও হয়েছে। প্রায় এক বছর পেরিয়ে গেলেও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ শুরু করছে না। পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) তাগাদায়ও কোনো কাজ হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন...
২০ নভেম্বর ২০২৪