কাঠমান্ডু পোস্টের নিবন্ধ
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
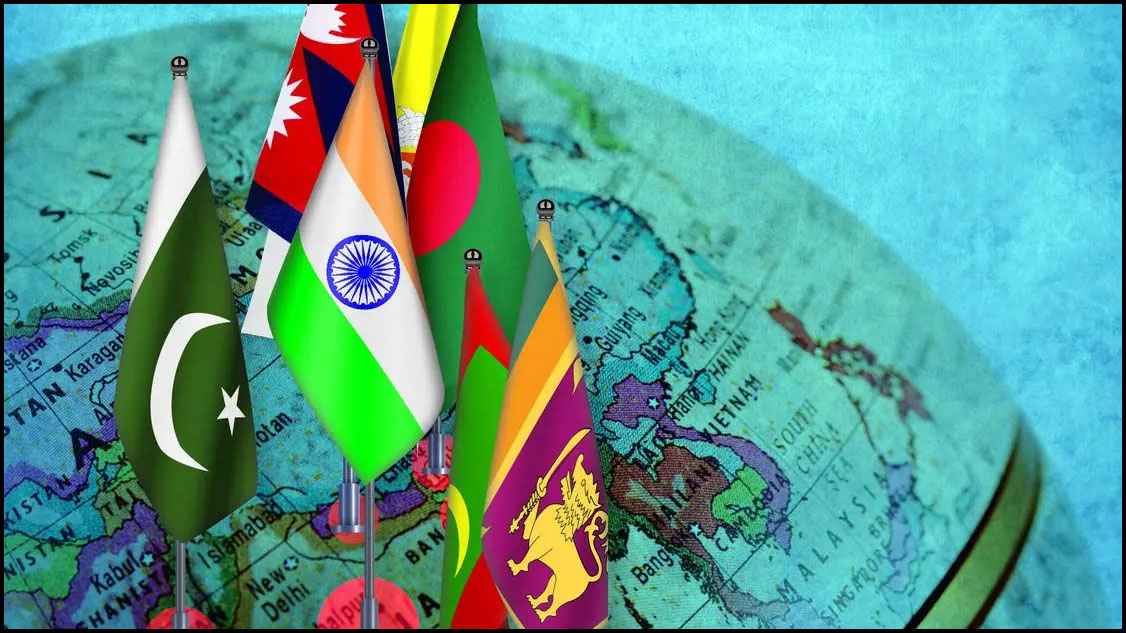
দক্ষিণ এশিয়া এখন সার্বভৌম ঋণ তথা সরকারের ঋণ ও রাজস্ব ঘাটতির ভারসাম্য রক্ষায় হিমশিম খাচ্ছে। স্থায়ী বাজেট ঘাটতির কারণে এ অঞ্চলের ঋণ বিশ্বের অন্যান্য উদীয়মান অর্থনীতির তুলনায় দ্রুত বেড়ে গেছে। ২০২৩ সালে সরকারগুলোর গড় ঋণের পরিমাণ পৌঁছেছে মোট জিডিপির ৭৭ শতাংশে।
এর আগে, ২০২২ সালে শ্রীলঙ্কা ঋণ সংকটে পড়ে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়। ২০২৩ সালে পাকিস্তান অল্পের জন্য একই পরিণতি থেকে রক্ষা পায়। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে যাওয়ায় আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল—আইএমএফের সহায়তা চাওয়ার ঘটনাও বাংলাদেশের পরিস্থিতির গভীরতা তুলে ধরেছে। দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় অর্থনীতি ভারতও এখন জিডিপির ৮০ শতাংশ সমপরিমাণ সরকারি ঋণের বোঝা বহন করছে। অন্যদিকে নেপাল, ভুটান ও মালদ্বীপের মতো ছোট দেশগুলো টিকে থাকতে অনুদানভিত্তিক বা ছাড়সুবিধাযুক্ত ঋণের ওপর নির্ভর করছে।
এই বিপুল ঋণসংকটের ঝুঁকি কেবল এর পরিমাণেই নয়, দেশগুলোর অর্থনৈতিক কাঠামোতেও লুকিয়ে আছে। একদিকে, সীমিত করভিত্তি, অদক্ষ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, জ্বালানি ও অন্যান্য পণ্য আমদানির ওপর অতিনির্ভরতা আর্থিক ব্যবস্থাকে সংকুচিত করেছে। অন্যদিকে, আঞ্চলিক বাণিজ্য ও সহযোগিতার সীমাবদ্ধতা দক্ষিণ এশিয়াকে আরও বেশি নির্ভরশীল করে তুলেছে বাইরের অংশীদারদের ওপর। ঋণের চাপ বাড়ায় উন্নয়ন খাত ও সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে ব্যয় করার মতো অর্থ কমে যাচ্ছে। ফলে জন–অর্থনীতি ক্রমেই নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে, আর রাষ্ট্রের অগ্রাধিকারও পরিবর্তিত হচ্ছে।
কোভিড–১৯ মহামারি ও রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট করে দিয়েছে। বিশ্ববাজারে মূল্য অস্থিরতার ওপর নির্ভরশীল এই অঞ্চলের দেশগুলো ২০২০ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে তীব্র সংকটে পড়ে যায়। ওই সময় জ্বালানি ও খাদ্যের দাম হঠাৎ বেড়ে যায়। এতে আমদানি ব্যয় বেড়ে যায় এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে যায়। রিজার্ভে চাপ পড়ায় সরকারগুলো বাধ্য হয় ঋণ নিতে—দেশের স্বাভাবিক কার্যক্রম চালু রাখা ও জ্বালানি–পণ্য মজুত রাখার জন্য।
এর ফলেই পুরো অঞ্চলে মুদ্রাস্ফীতি বাড়তে থাকে। এই মূল্যবৃদ্ধি অতিরিক্ত চাহিদার কারণে নয়, বরং আমদানি ব্যয় বেড়ে যাওয়া ও বৈশ্বিক সরবরাহব্যবস্থার ব্যাঘাতের ফল। উদাহরণ হিসেবে, ২০২২ সালে শ্রীলঙ্কায় ভোক্তা মূল্য বেড়ে যায় ৫০ শতাংশ। পাকিস্তানে ২০২৩ সালে তা ৩০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। এমনকি ‘টাইগার ইকোনমি’ খ্যাত বাংলাদেশেও ২০২৫ সালে মুদ্রাস্ফীতি ৮ শতাংশের বেশি হয়ে যায়। ভারতের বহুমুখী অর্থনীতি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল হলেও, রাশিয়ার সঙ্গে ছাড়মূল্যে জ্বালানি চুক্তির সহায়তায় ৩ শতাংশের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতি ধরে রাখতে সরকারকে ভর্তুকি দিতে হচ্ছে।
দক্ষিণ এশিয়ার কোটি মানুষের জন্য এখন প্রতিটি বৈশ্বিক সংকটের প্রথম আঘাত আসে পেট্রলপাম্পে ও মুদি দোকানে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুন বাণিজ্যিক বাস্তবতা। ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র—যা দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় তৈরি পোশাক ক্রেতা—২০ থেকে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে এই অঞ্চলের পোশাক ও শ্রমনির্ভর রপ্তানির ওপর। এতে বাংলাদেশের গার্মেন্টস, শ্রীলঙ্কার অ্যাপারেলস ও ভারতের পোশাক খাতের বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা ব্যাপকভাবে কমে গেছে।
রপ্তানি আয়ের ওপর নির্ভরশীল দেশগুলোর জন্য এটি বড় ধাক্কা। কারণ এই শুল্ক তাদের প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে দিচ্ছে এবং দীর্ঘদিনের কাঠামোগত দুর্বলতাকে আরও গভীর করছে।
দেশীয় অর্থনৈতিক কাঠামোগত সমস্যা—যেমন দুর্বল রাজস্বব্যবস্থা ও রাজনৈতিকভাবে জনপ্রিয় ভর্তুকি—দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সরকারকে বাইরের ধাক্কা সামলানোর ক্ষেত্রে দুর্বল করে তুলেছে। এতে আর্থিক খাতও দুর্বল হয়ে পড়েছে। উদাহরণ হিসেবে পাকিস্তানের কথা বলা যায়। দেশটিতে কৃত্রিমভাবে কমিয়ে রাখা বিদ্যুতের দর ‘সার্কুলার ঋণের’ ফাঁদ তৈরি করেছে, যা ঘুরে ফিরে রাষ্ট্রের ঘাড়েই এসে পড়ে। কারণ, সরকার পর্যাপ্ত রাজস্ব আদায় করতে পারছে না, আবার বেশি ভর্তুকি দিতে গিয়ে অন্য খাতে বরাদ্দ করা অর্থও ভর্তুকি মেটাতে সরিয়ে নিতে হচ্ছে। পুরো অঞ্চলেরই চিত্র এক—ভর্তুকি এখন অর্থনৈতিক প্রয়োজনের চেয়ে রাজনৈতিক স্বার্থের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে।
তা ছাড়া, দুর্বল করভিত্তি আর্থিক সক্ষমতাকে আরও সীমিত করছে। তথ্য বলছে, ২০২৪ সালে পাকিস্তানে মাত্র ৩ শতাংশ নাগরিক আয়কর রিটার্ন দাখিল করেছেন। ২০২২ সালে বাংলাদেশে তা ছিল মাত্র ১ দশমিক ৪ শতাংশ, আর ভারতে প্রায় ৭ শতাংশ। শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত জ্বালানি প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো সরকারি অর্থের ওপর বড় চাপ সৃষ্টি করছে। এগুলো শুধু অর্থনৈতিক দুর্বলতা নয়, বরং নীতিনির্ধারণে কাঠামোগত ভুল সিদ্ধান্তের ফল। দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক শৃঙ্খলার চেয়ে স্বল্পমেয়াদি জনপ্রিয় পদক্ষেপই বেশি প্রাধান্য পায়। এই প্রবণতা সংকটকালে সরকারের কার্যকর সাড়া দেওয়ার সক্ষমতা কমিয়ে দেয় এবং পুনরুদ্ধারের পথকে কঠিন করে তোলে।
জলবায়ু পরিবর্তন দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর আর্থিক সংকটকে আরও জটিল করে তুলছে। এই অঞ্চল এখনো বন্যা, তাপপ্রবাহ আর অনিয়মিত মৌসুমি বৃষ্টির মতো জলবায়ু-ঝুঁকির প্রবল শিকার। এসব দুর্যোগ ফসল, জীবিকা, মানববসতি ও অবকাঠামো ধ্বংস করে দিয়েছে। শুধু পাকিস্তানেই ২০২২ সালের ভয়াবহ বন্যায় ৩০ বিলিয়ন ডলারের বেশি ক্ষতি হয় এবং লাখ লাখ মানুষের জীবিকা বিপর্যস্ত হয়। বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান গরমে প্রতিবছর আনুমানিক ২ কোটি ৫০ লাখ কর্মদিবস নষ্ট হয় এবং অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১৮০ কোটি ডলার। অন্যদিকে ভারত, নেপাল ও ভুটানে অনিয়মিত জলবায়ুর প্রভাবে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, শীতলীকরণের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় জ্বালানি আমদানি ও সরকারি ব্যয়ও বাড়ছে।
এ ধরনের জলবায়ু-দুর্যোগের পর দেশগুলোকে নতুন করে ঋণ নিতে হয়। কারণ অভিযোজন বা টেকসই উন্নয়ন তহবিলের বড় অংশই ঋণভিত্তিক। ফলে টিকে থাকার লড়াইয়ে সরকারগুলো ঋণের ভারে জর্জরিত হয়ে পড়ে। এতে আর্থিক চাপ বাড়লেও ভবিষ্যৎ ঝুঁকি খুব একটা কমে না। এই অবস্থাকে বলা হচ্ছে ‘জলবায়ু-ঋণ ফাঁদ’—যেখানে দেশগুলোকে প্রথমে দুর্যোগে এবং পরে ঋণের বোঝায় শাস্তি পেতে হয়। যথেষ্ট পরিমাণে স্বল্পসুদ বা অনুদানভিত্তিক তহবিল না থাকলে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বারবার জলবায়ুর চক্রাকারে আঘাতের কাছে জিম্মি হয়ে থাকবে।
ঋণমুক্ত সহায়তার পথ যেমন ‘ঋণ-বিনিময়ে জলবায়ু তহবিল’ বা আঞ্চলিক ঝুঁকি-ভাগাভাগি তহবিল দুর্যোগের সময় তাৎক্ষণিক অর্থায়নের সুযোগ দিতে পারে। তবে রাজনৈতিক জটিলতা ও আঞ্চলিক সহযোগিতার অভাবে এসব উদ্যোগের বাস্তবায়ন এখনো খুব ধীর গতির।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দক্ষিণ এশিয়ার সরকারগুলো বারবার দেউলিয়া পরিস্থিতি এড়াতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) দ্বারস্থ হয়েছে। শ্রীলঙ্কাকে ৪০০ কোটি ডলারের আর্থিক সহায়তা দিয়েছে ভারত। পাশাপাশি ২০২৩ সালে দেশটি ১৭০ কোটি ডলারের একটি ‘এক্সটেনডেড ফান্ড ফ্যাসিলিটি’ পেয়েছে, যা দেশটির মুদ্রাবাজার স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করেছে। তবে সরকারি ঋণের চাপ এখনো টেকসই নয়। পাকিস্তান ২০২৩ সালে ৩০০ কোটি ডলার এবং ২০২৪ সালে আরও ৭০০ কোটি ডলার সহায়তা নিয়েছে আইএমএফ থেকে। এতে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কিছুটা সাফল্য এসেছে, কিন্তু ঋণ পরিশোধেই দেশটির মোট রাজস্ব আয়ের প্রায় ৬০ শতাংশ ব্যয় হয়।
বাংলাদেশও ৪৭০ কোটি ডলারের একটি আইএমএফ কর্মসূচি নিয়েছে চলতি হিসাব ঘাটতি ও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে, যা বিনিময় হার সমন্বয়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্থিতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। তবে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার এখনো ধীর গতির। ছোট দেশগুলো—যেমন নেপাল ও ভুটান—সংকীর্ণ রাজস্ব ঘাটতির মধ্যে বিদেশি সহায়তা, রেমিট্যান্স ও স্বল্পসুদে ঋণের ওপর নির্ভর করেই টিকে আছে। সব মিলিয়ে এই অঞ্চলে আইএমএফের সহায়তা জরুরি সংকটকালীন সময়ে কিছুটা সময় ও স্বস্তি এনে দিয়েছে। তবে দেশগুলোর উচিত এই সময়টাকে কাজে লাগিয়ে আর্থিক শৃঙ্খলা ও ঋণ ব্যবস্থাপনাকে নতুনভাবে গড়ে তোলা।
মধ্য মেয়াদে দক্ষিণ এশিয়ার দরকার একটি সমন্বিত কাঠামো, যা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বাড়াবে। এর একটি ভালো উদাহরণ হতে পারে—ভুটান, নেপাল ও ভারতের মধ্যে আঞ্চলিক বিদ্যুৎ বাণিজ্যের সম্ভাবনা, যা বাস্তবায়িত হলে ২০৪০ সালের মধ্যে বছরে প্রায় ৯০০ কোটি ডলার সাশ্রয় সম্ভব। বর্তমানে অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ২ হাজার ৩০০ কোটি ডলার, যেখানে সম্ভাবনা রয়েছে ৬ হাজার ৭০০ কোটি ডলার পর্যন্ত—এটি বাড়ানো গেলে বৈশ্বিক সরবরাহ ঝুঁকি মোকাবিলায় সহায়ক হবে।
একই সঙ্গে একটি ঝুঁকি বিমা তহবিল গঠন জরুরি, যা ক্যারিবীয় অঞ্চলের ‘ক্লাইমেট রিস্ক ইন্স্যুরেন্স ফ্যাসিলিটি’-এর মতো কাজ করবে। এতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর দ্রুত আর্থিক সহায়তা পাওয়া যাবে, নতুন ঋণের বোঝা না বাড়িয়ে। এ ধরনের যৌথ ঝুঁকি ভাগাভাগির ব্যবস্থা অঞ্চলটির অর্থনৈতিক দুর্বলতাকে টেকসই শক্তিতে রূপ দিতে পারে—যা পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য কার্যকর প্রণোদনা হতে পারে।
অভ্যন্তরীণ সংস্কারের মাধ্যমে সরকারকে করের আওতা বাড়াতে হবে, রাজনৈতিক কারণে দেওয়া ভর্তুকি কমাতে হবে এবং লোকসানি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর কাঠামোগত সংস্কার করতে হবে। জ্বালানি ও বিদ্যুতের দাম বাজারমূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য করলে রাজস্ব ঘাটতি কমানো যাবে, তবে নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে—বিশেষ করে জ্বালানি খাতে।
এ ছাড়া, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বাড়াতে হবে, যাতে তারা স্বচ্ছভাবে ঋণ ব্যবস্থাপনা ও হিসাব প্রকাশ করতে পারে। মধ্যমেয়াদি ব্যয় কাঠামো গ্রহণ এবং বাজেটে জলবায়ু ঝুঁকি অন্তর্ভুক্ত করাও জরুরি। সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে, নতুন ঋণ যেন উৎপাদনশীল বিনিয়োগে ব্যয় হয়, রাজনৈতিক জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য নয়।
দক্ষিণ এশিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে—দেশগুলো কি একা লড়াই করবে, নাকি একসঙ্গে মিলে আর্থিক স্থিতি গড়বে। বারবার আইএমএফের সহায়তায় টিকে থাকা নয়, বরং টেকসই প্রবৃদ্ধি ও পারস্পরিক স্থিতিশীলতার দিকেই এগোতে হবে এখন। যৌথ উদ্যোগে এই অঞ্চলই পারে দুর্বলতাকে রূপান্তর করতে অর্থনৈতিক সক্ষমতায়—যা দক্ষিণ এশিয়ার জন্য হতে পারে নতুন সূচনা।
লেখক:
বিজ্ঞান বাবু রেজমি, সুইজারল্যান্ডের ইএইচটি জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির পিএইচডি গবেষক
শিশির ভান্ডারি, নিউইয়র্কভিত্তিক অর্থনীতিবিদ ও গবেষক
কাঠমান্ডু পোস্ট থেকে অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান
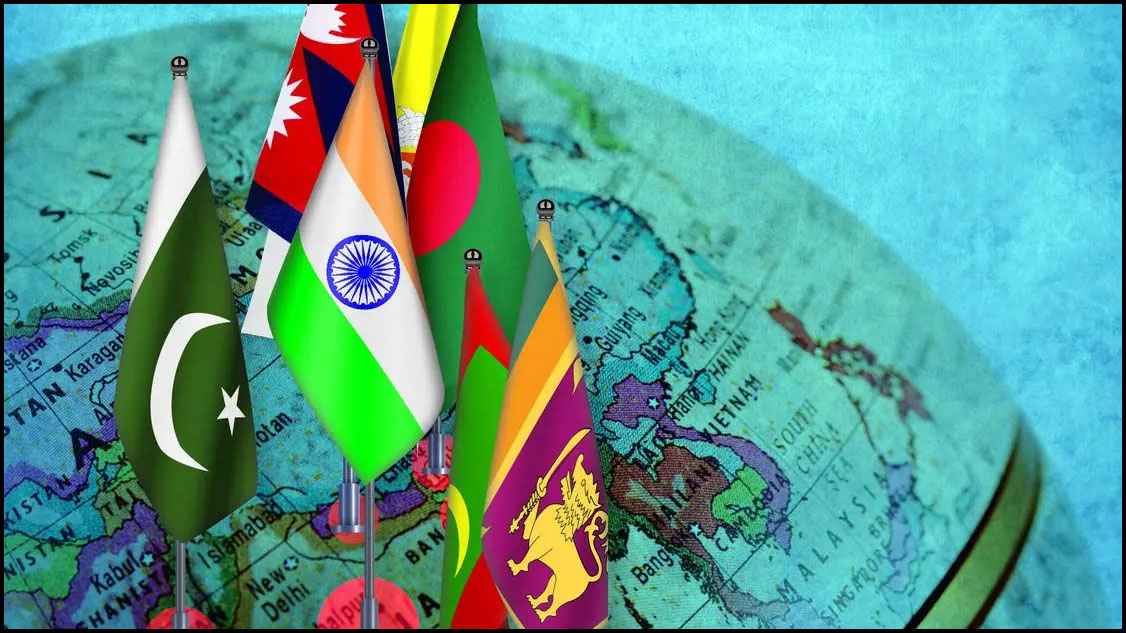
দক্ষিণ এশিয়া এখন সার্বভৌম ঋণ তথা সরকারের ঋণ ও রাজস্ব ঘাটতির ভারসাম্য রক্ষায় হিমশিম খাচ্ছে। স্থায়ী বাজেট ঘাটতির কারণে এ অঞ্চলের ঋণ বিশ্বের অন্যান্য উদীয়মান অর্থনীতির তুলনায় দ্রুত বেড়ে গেছে। ২০২৩ সালে সরকারগুলোর গড় ঋণের পরিমাণ পৌঁছেছে মোট জিডিপির ৭৭ শতাংশে।
এর আগে, ২০২২ সালে শ্রীলঙ্কা ঋণ সংকটে পড়ে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়। ২০২৩ সালে পাকিস্তান অল্পের জন্য একই পরিণতি থেকে রক্ষা পায়। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে যাওয়ায় আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল—আইএমএফের সহায়তা চাওয়ার ঘটনাও বাংলাদেশের পরিস্থিতির গভীরতা তুলে ধরেছে। দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় অর্থনীতি ভারতও এখন জিডিপির ৮০ শতাংশ সমপরিমাণ সরকারি ঋণের বোঝা বহন করছে। অন্যদিকে নেপাল, ভুটান ও মালদ্বীপের মতো ছোট দেশগুলো টিকে থাকতে অনুদানভিত্তিক বা ছাড়সুবিধাযুক্ত ঋণের ওপর নির্ভর করছে।
এই বিপুল ঋণসংকটের ঝুঁকি কেবল এর পরিমাণেই নয়, দেশগুলোর অর্থনৈতিক কাঠামোতেও লুকিয়ে আছে। একদিকে, সীমিত করভিত্তি, অদক্ষ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, জ্বালানি ও অন্যান্য পণ্য আমদানির ওপর অতিনির্ভরতা আর্থিক ব্যবস্থাকে সংকুচিত করেছে। অন্যদিকে, আঞ্চলিক বাণিজ্য ও সহযোগিতার সীমাবদ্ধতা দক্ষিণ এশিয়াকে আরও বেশি নির্ভরশীল করে তুলেছে বাইরের অংশীদারদের ওপর। ঋণের চাপ বাড়ায় উন্নয়ন খাত ও সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে ব্যয় করার মতো অর্থ কমে যাচ্ছে। ফলে জন–অর্থনীতি ক্রমেই নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে, আর রাষ্ট্রের অগ্রাধিকারও পরিবর্তিত হচ্ছে।
কোভিড–১৯ মহামারি ও রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট করে দিয়েছে। বিশ্ববাজারে মূল্য অস্থিরতার ওপর নির্ভরশীল এই অঞ্চলের দেশগুলো ২০২০ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে তীব্র সংকটে পড়ে যায়। ওই সময় জ্বালানি ও খাদ্যের দাম হঠাৎ বেড়ে যায়। এতে আমদানি ব্যয় বেড়ে যায় এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে যায়। রিজার্ভে চাপ পড়ায় সরকারগুলো বাধ্য হয় ঋণ নিতে—দেশের স্বাভাবিক কার্যক্রম চালু রাখা ও জ্বালানি–পণ্য মজুত রাখার জন্য।
এর ফলেই পুরো অঞ্চলে মুদ্রাস্ফীতি বাড়তে থাকে। এই মূল্যবৃদ্ধি অতিরিক্ত চাহিদার কারণে নয়, বরং আমদানি ব্যয় বেড়ে যাওয়া ও বৈশ্বিক সরবরাহব্যবস্থার ব্যাঘাতের ফল। উদাহরণ হিসেবে, ২০২২ সালে শ্রীলঙ্কায় ভোক্তা মূল্য বেড়ে যায় ৫০ শতাংশ। পাকিস্তানে ২০২৩ সালে তা ৩০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। এমনকি ‘টাইগার ইকোনমি’ খ্যাত বাংলাদেশেও ২০২৫ সালে মুদ্রাস্ফীতি ৮ শতাংশের বেশি হয়ে যায়। ভারতের বহুমুখী অর্থনীতি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল হলেও, রাশিয়ার সঙ্গে ছাড়মূল্যে জ্বালানি চুক্তির সহায়তায় ৩ শতাংশের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতি ধরে রাখতে সরকারকে ভর্তুকি দিতে হচ্ছে।
দক্ষিণ এশিয়ার কোটি মানুষের জন্য এখন প্রতিটি বৈশ্বিক সংকটের প্রথম আঘাত আসে পেট্রলপাম্পে ও মুদি দোকানে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুন বাণিজ্যিক বাস্তবতা। ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র—যা দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় তৈরি পোশাক ক্রেতা—২০ থেকে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে এই অঞ্চলের পোশাক ও শ্রমনির্ভর রপ্তানির ওপর। এতে বাংলাদেশের গার্মেন্টস, শ্রীলঙ্কার অ্যাপারেলস ও ভারতের পোশাক খাতের বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা ব্যাপকভাবে কমে গেছে।
রপ্তানি আয়ের ওপর নির্ভরশীল দেশগুলোর জন্য এটি বড় ধাক্কা। কারণ এই শুল্ক তাদের প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে দিচ্ছে এবং দীর্ঘদিনের কাঠামোগত দুর্বলতাকে আরও গভীর করছে।
দেশীয় অর্থনৈতিক কাঠামোগত সমস্যা—যেমন দুর্বল রাজস্বব্যবস্থা ও রাজনৈতিকভাবে জনপ্রিয় ভর্তুকি—দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সরকারকে বাইরের ধাক্কা সামলানোর ক্ষেত্রে দুর্বল করে তুলেছে। এতে আর্থিক খাতও দুর্বল হয়ে পড়েছে। উদাহরণ হিসেবে পাকিস্তানের কথা বলা যায়। দেশটিতে কৃত্রিমভাবে কমিয়ে রাখা বিদ্যুতের দর ‘সার্কুলার ঋণের’ ফাঁদ তৈরি করেছে, যা ঘুরে ফিরে রাষ্ট্রের ঘাড়েই এসে পড়ে। কারণ, সরকার পর্যাপ্ত রাজস্ব আদায় করতে পারছে না, আবার বেশি ভর্তুকি দিতে গিয়ে অন্য খাতে বরাদ্দ করা অর্থও ভর্তুকি মেটাতে সরিয়ে নিতে হচ্ছে। পুরো অঞ্চলেরই চিত্র এক—ভর্তুকি এখন অর্থনৈতিক প্রয়োজনের চেয়ে রাজনৈতিক স্বার্থের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে।
তা ছাড়া, দুর্বল করভিত্তি আর্থিক সক্ষমতাকে আরও সীমিত করছে। তথ্য বলছে, ২০২৪ সালে পাকিস্তানে মাত্র ৩ শতাংশ নাগরিক আয়কর রিটার্ন দাখিল করেছেন। ২০২২ সালে বাংলাদেশে তা ছিল মাত্র ১ দশমিক ৪ শতাংশ, আর ভারতে প্রায় ৭ শতাংশ। শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত জ্বালানি প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো সরকারি অর্থের ওপর বড় চাপ সৃষ্টি করছে। এগুলো শুধু অর্থনৈতিক দুর্বলতা নয়, বরং নীতিনির্ধারণে কাঠামোগত ভুল সিদ্ধান্তের ফল। দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক শৃঙ্খলার চেয়ে স্বল্পমেয়াদি জনপ্রিয় পদক্ষেপই বেশি প্রাধান্য পায়। এই প্রবণতা সংকটকালে সরকারের কার্যকর সাড়া দেওয়ার সক্ষমতা কমিয়ে দেয় এবং পুনরুদ্ধারের পথকে কঠিন করে তোলে।
জলবায়ু পরিবর্তন দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর আর্থিক সংকটকে আরও জটিল করে তুলছে। এই অঞ্চল এখনো বন্যা, তাপপ্রবাহ আর অনিয়মিত মৌসুমি বৃষ্টির মতো জলবায়ু-ঝুঁকির প্রবল শিকার। এসব দুর্যোগ ফসল, জীবিকা, মানববসতি ও অবকাঠামো ধ্বংস করে দিয়েছে। শুধু পাকিস্তানেই ২০২২ সালের ভয়াবহ বন্যায় ৩০ বিলিয়ন ডলারের বেশি ক্ষতি হয় এবং লাখ লাখ মানুষের জীবিকা বিপর্যস্ত হয়। বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান গরমে প্রতিবছর আনুমানিক ২ কোটি ৫০ লাখ কর্মদিবস নষ্ট হয় এবং অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১৮০ কোটি ডলার। অন্যদিকে ভারত, নেপাল ও ভুটানে অনিয়মিত জলবায়ুর প্রভাবে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, শীতলীকরণের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় জ্বালানি আমদানি ও সরকারি ব্যয়ও বাড়ছে।
এ ধরনের জলবায়ু-দুর্যোগের পর দেশগুলোকে নতুন করে ঋণ নিতে হয়। কারণ অভিযোজন বা টেকসই উন্নয়ন তহবিলের বড় অংশই ঋণভিত্তিক। ফলে টিকে থাকার লড়াইয়ে সরকারগুলো ঋণের ভারে জর্জরিত হয়ে পড়ে। এতে আর্থিক চাপ বাড়লেও ভবিষ্যৎ ঝুঁকি খুব একটা কমে না। এই অবস্থাকে বলা হচ্ছে ‘জলবায়ু-ঋণ ফাঁদ’—যেখানে দেশগুলোকে প্রথমে দুর্যোগে এবং পরে ঋণের বোঝায় শাস্তি পেতে হয়। যথেষ্ট পরিমাণে স্বল্পসুদ বা অনুদানভিত্তিক তহবিল না থাকলে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বারবার জলবায়ুর চক্রাকারে আঘাতের কাছে জিম্মি হয়ে থাকবে।
ঋণমুক্ত সহায়তার পথ যেমন ‘ঋণ-বিনিময়ে জলবায়ু তহবিল’ বা আঞ্চলিক ঝুঁকি-ভাগাভাগি তহবিল দুর্যোগের সময় তাৎক্ষণিক অর্থায়নের সুযোগ দিতে পারে। তবে রাজনৈতিক জটিলতা ও আঞ্চলিক সহযোগিতার অভাবে এসব উদ্যোগের বাস্তবায়ন এখনো খুব ধীর গতির।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দক্ষিণ এশিয়ার সরকারগুলো বারবার দেউলিয়া পরিস্থিতি এড়াতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) দ্বারস্থ হয়েছে। শ্রীলঙ্কাকে ৪০০ কোটি ডলারের আর্থিক সহায়তা দিয়েছে ভারত। পাশাপাশি ২০২৩ সালে দেশটি ১৭০ কোটি ডলারের একটি ‘এক্সটেনডেড ফান্ড ফ্যাসিলিটি’ পেয়েছে, যা দেশটির মুদ্রাবাজার স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করেছে। তবে সরকারি ঋণের চাপ এখনো টেকসই নয়। পাকিস্তান ২০২৩ সালে ৩০০ কোটি ডলার এবং ২০২৪ সালে আরও ৭০০ কোটি ডলার সহায়তা নিয়েছে আইএমএফ থেকে। এতে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কিছুটা সাফল্য এসেছে, কিন্তু ঋণ পরিশোধেই দেশটির মোট রাজস্ব আয়ের প্রায় ৬০ শতাংশ ব্যয় হয়।
বাংলাদেশও ৪৭০ কোটি ডলারের একটি আইএমএফ কর্মসূচি নিয়েছে চলতি হিসাব ঘাটতি ও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে, যা বিনিময় হার সমন্বয়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্থিতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। তবে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার এখনো ধীর গতির। ছোট দেশগুলো—যেমন নেপাল ও ভুটান—সংকীর্ণ রাজস্ব ঘাটতির মধ্যে বিদেশি সহায়তা, রেমিট্যান্স ও স্বল্পসুদে ঋণের ওপর নির্ভর করেই টিকে আছে। সব মিলিয়ে এই অঞ্চলে আইএমএফের সহায়তা জরুরি সংকটকালীন সময়ে কিছুটা সময় ও স্বস্তি এনে দিয়েছে। তবে দেশগুলোর উচিত এই সময়টাকে কাজে লাগিয়ে আর্থিক শৃঙ্খলা ও ঋণ ব্যবস্থাপনাকে নতুনভাবে গড়ে তোলা।
মধ্য মেয়াদে দক্ষিণ এশিয়ার দরকার একটি সমন্বিত কাঠামো, যা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বাড়াবে। এর একটি ভালো উদাহরণ হতে পারে—ভুটান, নেপাল ও ভারতের মধ্যে আঞ্চলিক বিদ্যুৎ বাণিজ্যের সম্ভাবনা, যা বাস্তবায়িত হলে ২০৪০ সালের মধ্যে বছরে প্রায় ৯০০ কোটি ডলার সাশ্রয় সম্ভব। বর্তমানে অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ২ হাজার ৩০০ কোটি ডলার, যেখানে সম্ভাবনা রয়েছে ৬ হাজার ৭০০ কোটি ডলার পর্যন্ত—এটি বাড়ানো গেলে বৈশ্বিক সরবরাহ ঝুঁকি মোকাবিলায় সহায়ক হবে।
একই সঙ্গে একটি ঝুঁকি বিমা তহবিল গঠন জরুরি, যা ক্যারিবীয় অঞ্চলের ‘ক্লাইমেট রিস্ক ইন্স্যুরেন্স ফ্যাসিলিটি’-এর মতো কাজ করবে। এতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর দ্রুত আর্থিক সহায়তা পাওয়া যাবে, নতুন ঋণের বোঝা না বাড়িয়ে। এ ধরনের যৌথ ঝুঁকি ভাগাভাগির ব্যবস্থা অঞ্চলটির অর্থনৈতিক দুর্বলতাকে টেকসই শক্তিতে রূপ দিতে পারে—যা পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য কার্যকর প্রণোদনা হতে পারে।
অভ্যন্তরীণ সংস্কারের মাধ্যমে সরকারকে করের আওতা বাড়াতে হবে, রাজনৈতিক কারণে দেওয়া ভর্তুকি কমাতে হবে এবং লোকসানি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর কাঠামোগত সংস্কার করতে হবে। জ্বালানি ও বিদ্যুতের দাম বাজারমূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য করলে রাজস্ব ঘাটতি কমানো যাবে, তবে নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে—বিশেষ করে জ্বালানি খাতে।
এ ছাড়া, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বাড়াতে হবে, যাতে তারা স্বচ্ছভাবে ঋণ ব্যবস্থাপনা ও হিসাব প্রকাশ করতে পারে। মধ্যমেয়াদি ব্যয় কাঠামো গ্রহণ এবং বাজেটে জলবায়ু ঝুঁকি অন্তর্ভুক্ত করাও জরুরি। সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে, নতুন ঋণ যেন উৎপাদনশীল বিনিয়োগে ব্যয় হয়, রাজনৈতিক জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য নয়।
দক্ষিণ এশিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে—দেশগুলো কি একা লড়াই করবে, নাকি একসঙ্গে মিলে আর্থিক স্থিতি গড়বে। বারবার আইএমএফের সহায়তায় টিকে থাকা নয়, বরং টেকসই প্রবৃদ্ধি ও পারস্পরিক স্থিতিশীলতার দিকেই এগোতে হবে এখন। যৌথ উদ্যোগে এই অঞ্চলই পারে দুর্বলতাকে রূপান্তর করতে অর্থনৈতিক সক্ষমতায়—যা দক্ষিণ এশিয়ার জন্য হতে পারে নতুন সূচনা।
লেখক:
বিজ্ঞান বাবু রেজমি, সুইজারল্যান্ডের ইএইচটি জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির পিএইচডি গবেষক
শিশির ভান্ডারি, নিউইয়র্কভিত্তিক অর্থনীতিবিদ ও গবেষক
কাঠমান্ডু পোস্ট থেকে অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান

সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে ভেনেজুয়েলায় মাদক পাচারের অভিযোগে অন্তত ২১টি নৌযানে মার্কিন সামরিক বাহিনী হামলা চালিয়েছে, যাতে অন্তত ৮৭ জন নিহত হয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসন দাবি করছে, এসব নৌকা যুক্তরাষ্ট্রে বিপুল পরিমাণ মাদক পাচার করছিল এবং তা মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি।
১৩ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ইসহাক দার জানিয়েছেন, বাংলাদেশ, চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্প্রতি যে ত্রিপক্ষীয় উদ্যোগ শুরু হয়েছে, তা অন্য আঞ্চলিক দেশ এবং এর বাইরেও ‘বিস্তৃত’ হতে পারে। তিনি গত বুধবার ইসলামাবাদ কনক্লেভ ফোরামে বলেন, ‘আমরা শূন্য-সমষ্টিগত পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছি এবং সংঘাতের বদলে সহযোগিতার
২০ ঘণ্টা আগে
ভ্লাদিস্লাভ ইনোজেমতসেভ বলেন, ‘পুতিন ভালোভাবেই জানেন যে ইউক্রেনের হাতে সময় ফুরিয়ে আসছে। তাই, পুতিন সবকিছু নিয়ে খুব আত্মবিশ্বাসী। তাঁর হাতে সময় আছে। তিনি এক বা দুই বছর ধরে লড়তে পারেন। সমস্যাটা বরং পশ্চিমের (এবং তাদের লড়াইয়ের ইচ্ছার)। তাই, হ্যাঁ, তিনি দেরি করতে প্রস্তুত—ইউক্রেন ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দেও
২১ ঘণ্টা আগে
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতদের মধ্যে ইউক্রেন শান্তি চুক্তি নিয়ে আলোচনা হলেও প্রকাশ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। পুতিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ইউরি উশাকভ, এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে অমীমাংসিত ‘আঞ্চলিক সমস্যাই’ মূল বাধা। আর এই অঞ্চল আর কোনোটিই নয়, দোনেৎস্ক।
২ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে মার্কিন নৌবাহিনীর উপস্থিতি বাড়ছে, পাল্লা দিয়ে চড়া হচ্ছে রাজনৈতিক বক্তব্য। এমন পরিস্থিতিতে ভেনেজুয়েলার ওপর সম্ভাব্য মার্কিন সামরিক হামলার আশঙ্কা ক্রমে ঘনিয়ে আসছে।
ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটির (ডিএইচএস) তথ্য অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে ভেনেজুয়েলায় মাদক পাচারের অভিযোগে অন্তত ২১টি নৌযানে মার্কিন সামরিক বাহিনী হামলা চালিয়েছে, যাতে অন্তত ৮৭ জন নিহত হয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসন দাবি করছে, এসব নৌকা যুক্তরাষ্ট্রে বিপুল পরিমাণ মাদক পাচার করছিল এবং তা মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি। তবে এই অভিযোগের পক্ষে কোনো প্রমাণ তারা দেয়নি। বিশেষজ্ঞরাও বলছেন, কোকেনসহ মাদক যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছানোর প্রধান উৎস ভেনেজুয়েলা নয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কখনো বলেছেন, ভেনেজুয়েলার ভেতরে স্থল অভিযান বিবেচনায় নেই, আবার কখনো বলেছেন, তিনি তা বাতিলও করছেন না। তবে তিনি সিআইএকে ভেনেজুয়েলার ভেতরে কার্যক্রম পরিচালনার অনুমোদন দিয়েছেন।
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো দাবি করছেন, ট্রাম্পের উদ্দেশ্য হলো তাঁকে ক্ষমতা থেকে সরানো। তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন, তাঁর দেশ যুক্তরাষ্ট্রের এ ধরনের সব চেষ্টা প্রতিহত করবে।
ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলা কীভাবে হতে পারে
বিশ্লেষকদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের হাতে ভেনেজুয়েলাকে লক্ষ্য করে একাধিক সামরিক বিকল্প রয়েছে। এর মধ্যে বেশির ভাগই স্থলবাহিনীর পরিবর্তে বিমান ও নৌশক্তি ব্যবহার করা হতে পারে।
সাম্প্রতিক মাসগুলোয় যুক্তরাষ্ট্র ক্যারিবিয়ান সাগরে নৌ ও বিমানবাহিনীর উপস্থিতি বাড়িয়েছে। এর মধ্যে আছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিমানবাহী রণতরি ইউএসএস জেরাল্ড ফোর্ড।
সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের (সিএসআইসি) উপদেষ্টা এবং সাবেক মেরিন কর্নেল মার্ক ক্যানসিয়ান আল জাজিরাকে বলেন, বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার সব প্রস্তুতি নেওয়া আছে। তবে ভেনেজুয়েলার শক্তিশালী বিমান প্রতিরক্ষাব্যবস্থার কারণে প্রথম হামলা সম্ভবত দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হবে।
ট্রাম্প প্রশাসন সাম্প্রতিক বক্তব্যে মাদুরো সরকারের সঙ্গে কথিত ড্রাগ কার্টেল-সংযোগের কথা বলছে। বিশ্লেষকদের মতে, মাদকসম্পর্কিত অবকাঠামো লক্ষ্য করে হামলা চালালে আন্তর্জাতিকভাবে সহজেই এটিকে ন্যায্যতা দেওয়া যাবে এবং দ্রুত অভিযান শেষ করাও সহজ।
স্থলযুদ্ধের সম্ভাবনা প্রায় নেই
প্রায় সব বিশেষজ্ঞ স্থল আক্রমণের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছেন। অরিনোকো রিসার্চের প্রতিষ্ঠাতা এলিয়াস ফেরর বলেন, এই মুহূর্তে হামলার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ, এই অঞ্চলে স্থল আক্রমণের জন্য মার্কিন বাহিনীর যথেষ্ট শক্তি নেই।
নেদারল্যান্ডসের লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক বিজ্ঞানী সান্তিনো রেজিলমে বলেন, ‘স্থল অভিযান আইনগত জটিলতা, কংগ্রেসের বিরোধিতা এবং ইরাক-আফগানিস্তানের অভিজ্ঞতার কারণে খুব একটা সমর্থন পাবে না।’
সান্তিনো রেজিলমে আরও বলেন, বিষয়টি ‘হামলা হবে’ নাকি ‘হবে না’, এই দ্বৈততার বদলে ‘সীমিত কিন্তু ক্রমবর্ধমান সামরিক ব্যবহারের বিস্তৃত পরিসর’ হিসেবে দেখা উচিত।
ভেনেজুয়েলার জন্য এর অর্থ কী
ওয়াশিংটনের কিছু নীতিনির্ধারক মনে করেন, হামলা হলে দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন আসতে পারে। তবে বিশ্লেষকেরা সতর্ক করছেন, এটি বরং অস্থিরতা বাড়াবে।
ফেরর বলেন, এমন হামলা ‘প্যান্ডোরার বাক্স’ খুলে দেবে। সশস্ত্র গোষ্ঠী ক্ষমতাশালী হয়ে উঠবে। সেনাবাহিনী বা রাজনৈতিক অপরাধী প্যারামিলিশিয়ারা দেশের বিভিন্ন অংশ দখলে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। তাঁর মতে, এমন পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বিরোধী দল; কারণ, তাদের কোনো সশস্ত্র শাখা নেই।
লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক বিজ্ঞানী সান্তিনো রেজিলমে বলেন, কোনো দেশে বাইরের আগ্রাসন সাধারণত ওই দেশের সরকারকে শক্তিশালী করে। এর ফলে ‘র্যালি-অ্যারাউন্ড-দ্য-ফ্ল্যাগ এফেক্ট’ তৈরি হবে। এটি জাতীয়তাবাদী সমর্থন তৈরি করবে এবং সরকার ভিন্নমত দমন করার অজুহাত পাবে।
লিবিয়া, ইরাকসহ বহু দেশের উদাহরণ দেখিয়ে সান্তিনো রেজিলমে বলেন, বহিরাগত হস্তক্ষেপ খুব কম দেশেই স্থিতিশীল গণতন্ত্র এনেছে।
মাদুরো সরকারও প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জিং ভঙ্গি নিয়েছে। নভেম্বরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিওসদাদো কাবেলো বলেন, ‘তারা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) মনে করে, বোমা ফেলে সব শেষ করবে। এখানে? এই দেশে?’
মাদুরোও বলেন, ‘আমরা শান্তি চাই, কিন্তু দাসের মতো শান্তি নয়। সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে শান্তি চাই।’
মার্কিন কৌশল কী
সিএসআইসির উপদেষ্টা এবং সাবেক মেরিন কর্নেল মার্ক ক্যানসিয়ান জানান, মাদুরোর প্রতি ভেনেজুয়েলার সামরিক বাহিনীর যে আনুগত্য, সেটা দুর্বল করতে কাজ করছে সিআইএ। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র সামরিক বাহিনীকে বার্তা দিতে পারে, তারা যদি লড়াই না করে ব্যারাকে থাকে, তাহলে তাদের ওপর হামলা হবে না।
১৯৯১ সালের ডেজার্ট স্টর্মে (উপসাগরীয় যুদ্ধের সময়) যুক্তরাষ্ট্র একই কৌশল ব্যবহার করেছিল। এখানে মার্কিন কর্মকর্তারা গোপনে কিছু ইরাকি ইউনিটকে সংকেত দিয়েছিলেন যে তারা যদি লড়াই না করে ব্যারাকে থাকে, তবে তাদের লক্ষ্যবস্তু করা হবে না। এই কৌশল প্রতিরোধের মাত্রা কমাতে সাহায্য করেছিল।
তবে ক্যানসিয়ান মনে করেন, মাদুরোর সরকার ইতিমধ্যে সেনাবাহিনী থেকে তাদের বিরোধী মতাদর্শীদের সরিয়ে ফেলেছে এবং লড়াইয়ের সম্ভাবনাই বেশি।
ভেনেজুয়েলার সেনাবাহিনী কী করতে পারে
অরিনোকো রিসার্চের প্রতিষ্ঠাতা এলিয়াস ফেরর বলেন, সবকিছু নির্ভর করবে হামলার আগে যুক্তরাষ্ট্র তাদের কী বার্তা দেয় তার ওপর।
ওয়াশিংটনের সামনে দুটি পথ রয়েছে। প্রথমত, তারা সামরিক বাহিনীকে বলবে, ‘আমরা সফল হলে তোমরা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, ব্যবসা ও ক্ষমতায় থাকতে পারবে।’ দ্বিতীয়ত, ইরাকে ‘ডি-বাথিফিকেশনের’ মতো সব অফিসার-সৈন্যকে সরিয়ে দেওয়া।
ফেররের মতে, সামরিক বাহিনীকে কোণঠাসা করলে দেশজুড়ে বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ দেখা দিতে পারে।
প্রসঙ্গত, ডি-বাথিফিকেশন (De-Ba’athification) হলো ২০০৩ সালে ইরাক আক্রমণের পর মার্কিন নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন প্রোভিশনাল অথরিটির (সিপিএ) একটি নীতি। এর লক্ষ্য ছিল সাদ্দাম হোসেনের বাথ পার্টির (Ba’ath Party) সব সদস্যকে সরকারি পদ, প্রশাসন ও সামরিক বাহিনী থেকে অপসারণ করে ইরাকের সমাজকে বাথবাদী প্রভাবমুক্ত করা।
সাধারণ ভেনেজুয়েলানদের প্রতিক্রিয়া কেমন হতে পারে
বিশ্লেষকদের মতে, পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হবে। হাইপারইনফ্লেশন বা চরম মুদ্রাস্ফীতি, দীর্ঘমেয়াদি সংকট, আর্থিক পতন, আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা এবং বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বাস্তু সংকট তৈরি হতে পারে।
২০২৫ সালের হিসাব অনুযায়ী, ভেনেজুয়েলার ৭৯ লাখ অর্থাৎ ২৮-৩০ শতাংশ মানুষের মানবিক সহায়তার প্রয়োজন।
রাজনৈতিক বিজ্ঞানী সান্তিনো রেজিলমে বলেন, এমন অবস্থায় মার্কিন হামলা জনগণের কাছে হবে ভয়াবহ নিরাপত্তাহীনতা। খাদ্য, ওষুধ, বিদ্যুৎ ও মৌলিক সেবার ওপর আরও চাপ তৈরি হবে।
আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া কেমন হবে
চীন ভেনেজুয়েলার অন্যতম বড় অর্থনৈতিক অংশীদার ও ঋণদাতা। বিশ্লেষকদের মতে, তারা মাদুরোর প্রতি কূটনৈতিক সমর্থন বজায় রাখবে, কিন্তু যুদ্ধ শুরু হলে সরাসরি ভূমিকা সীমিত থাকবে।
ভেনেজুয়েলান বিশ্লেষক কার্লোস পিনা বলেন, সশস্ত্র সংঘাত শুরু হলে চীনের প্রভাব সীমিত হবে। অন্যদিকে রাশিয়া ভেনেজুয়েলার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে অস্ত্র, প্রশিক্ষণ, গোয়েন্দা সহায়তাসহ সামরিক সহযোগিতা বজায় রেখেছে। পিনার মতে, রাশিয়া সামরিক পরামর্শে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। তবে দুই দেশই রাজনৈতিকভাবে মাদুরোর পাশে থাকবে।
মার্কিন আক্রমণ কি অন্য দেশেও ছড়াতে পারে
বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন, ভেনেজুয়েলার ঘটনাকে সামনে রেখে লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশেও একই মডেল প্রয়োগ করা হতে পারে। চলতি সপ্তাহে এক বৈঠকে ট্রাম্প সতর্ক করেন, যেকোনো মাদক উৎপাদনকারী দেশই যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে তিনি কলম্বিয়ার কোকেন উৎপাদনের কথা তুলে ধরেন।
লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক বিজ্ঞানী সান্তিনো রেজিলমে বলেন, ভেনেজুয়েলাকে ঘিরে মার্কিন পদক্ষেপ একক দেশের নীতি নয়; বরং জটিল রাজনৈতিক সংকটগুলোকে ‘নার্কো-টেররিস্ট’ হিসেবে চিহ্নিত করে সামরিক হস্তক্ষেপ বৈধ করার এক নতুন ছক। যদি এই পদ্ধতি অন্যান্য দেশে প্রয়োগ করা হয়, তবে আন্তর্জাতিক আইন ও আঞ্চলিক শান্তি প্রক্রিয়া আরও দুর্বল হয়ে পড়বে। তিনি বলেন, এতে ড্রাগ ট্রাফিকিং, অভিবাসন সংকটসহ আরও অনেক সমস্যার সমাধান সামরিকীকরণের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। এগুলো আর সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যা থাকবে না।
(কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা থেকে অনুবাদ করেছেন জগৎপতি বর্মা)

ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে মার্কিন নৌবাহিনীর উপস্থিতি বাড়ছে, পাল্লা দিয়ে চড়া হচ্ছে রাজনৈতিক বক্তব্য। এমন পরিস্থিতিতে ভেনেজুয়েলার ওপর সম্ভাব্য মার্কিন সামরিক হামলার আশঙ্কা ক্রমে ঘনিয়ে আসছে।
ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটির (ডিএইচএস) তথ্য অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে ভেনেজুয়েলায় মাদক পাচারের অভিযোগে অন্তত ২১টি নৌযানে মার্কিন সামরিক বাহিনী হামলা চালিয়েছে, যাতে অন্তত ৮৭ জন নিহত হয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসন দাবি করছে, এসব নৌকা যুক্তরাষ্ট্রে বিপুল পরিমাণ মাদক পাচার করছিল এবং তা মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি। তবে এই অভিযোগের পক্ষে কোনো প্রমাণ তারা দেয়নি। বিশেষজ্ঞরাও বলছেন, কোকেনসহ মাদক যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছানোর প্রধান উৎস ভেনেজুয়েলা নয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কখনো বলেছেন, ভেনেজুয়েলার ভেতরে স্থল অভিযান বিবেচনায় নেই, আবার কখনো বলেছেন, তিনি তা বাতিলও করছেন না। তবে তিনি সিআইএকে ভেনেজুয়েলার ভেতরে কার্যক্রম পরিচালনার অনুমোদন দিয়েছেন।
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো দাবি করছেন, ট্রাম্পের উদ্দেশ্য হলো তাঁকে ক্ষমতা থেকে সরানো। তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন, তাঁর দেশ যুক্তরাষ্ট্রের এ ধরনের সব চেষ্টা প্রতিহত করবে।
ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলা কীভাবে হতে পারে
বিশ্লেষকদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের হাতে ভেনেজুয়েলাকে লক্ষ্য করে একাধিক সামরিক বিকল্প রয়েছে। এর মধ্যে বেশির ভাগই স্থলবাহিনীর পরিবর্তে বিমান ও নৌশক্তি ব্যবহার করা হতে পারে।
সাম্প্রতিক মাসগুলোয় যুক্তরাষ্ট্র ক্যারিবিয়ান সাগরে নৌ ও বিমানবাহিনীর উপস্থিতি বাড়িয়েছে। এর মধ্যে আছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিমানবাহী রণতরি ইউএসএস জেরাল্ড ফোর্ড।
সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের (সিএসআইসি) উপদেষ্টা এবং সাবেক মেরিন কর্নেল মার্ক ক্যানসিয়ান আল জাজিরাকে বলেন, বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার সব প্রস্তুতি নেওয়া আছে। তবে ভেনেজুয়েলার শক্তিশালী বিমান প্রতিরক্ষাব্যবস্থার কারণে প্রথম হামলা সম্ভবত দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হবে।
ট্রাম্প প্রশাসন সাম্প্রতিক বক্তব্যে মাদুরো সরকারের সঙ্গে কথিত ড্রাগ কার্টেল-সংযোগের কথা বলছে। বিশ্লেষকদের মতে, মাদকসম্পর্কিত অবকাঠামো লক্ষ্য করে হামলা চালালে আন্তর্জাতিকভাবে সহজেই এটিকে ন্যায্যতা দেওয়া যাবে এবং দ্রুত অভিযান শেষ করাও সহজ।
স্থলযুদ্ধের সম্ভাবনা প্রায় নেই
প্রায় সব বিশেষজ্ঞ স্থল আক্রমণের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছেন। অরিনোকো রিসার্চের প্রতিষ্ঠাতা এলিয়াস ফেরর বলেন, এই মুহূর্তে হামলার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ, এই অঞ্চলে স্থল আক্রমণের জন্য মার্কিন বাহিনীর যথেষ্ট শক্তি নেই।
নেদারল্যান্ডসের লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক বিজ্ঞানী সান্তিনো রেজিলমে বলেন, ‘স্থল অভিযান আইনগত জটিলতা, কংগ্রেসের বিরোধিতা এবং ইরাক-আফগানিস্তানের অভিজ্ঞতার কারণে খুব একটা সমর্থন পাবে না।’
সান্তিনো রেজিলমে আরও বলেন, বিষয়টি ‘হামলা হবে’ নাকি ‘হবে না’, এই দ্বৈততার বদলে ‘সীমিত কিন্তু ক্রমবর্ধমান সামরিক ব্যবহারের বিস্তৃত পরিসর’ হিসেবে দেখা উচিত।
ভেনেজুয়েলার জন্য এর অর্থ কী
ওয়াশিংটনের কিছু নীতিনির্ধারক মনে করেন, হামলা হলে দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন আসতে পারে। তবে বিশ্লেষকেরা সতর্ক করছেন, এটি বরং অস্থিরতা বাড়াবে।
ফেরর বলেন, এমন হামলা ‘প্যান্ডোরার বাক্স’ খুলে দেবে। সশস্ত্র গোষ্ঠী ক্ষমতাশালী হয়ে উঠবে। সেনাবাহিনী বা রাজনৈতিক অপরাধী প্যারামিলিশিয়ারা দেশের বিভিন্ন অংশ দখলে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। তাঁর মতে, এমন পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বিরোধী দল; কারণ, তাদের কোনো সশস্ত্র শাখা নেই।
লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক বিজ্ঞানী সান্তিনো রেজিলমে বলেন, কোনো দেশে বাইরের আগ্রাসন সাধারণত ওই দেশের সরকারকে শক্তিশালী করে। এর ফলে ‘র্যালি-অ্যারাউন্ড-দ্য-ফ্ল্যাগ এফেক্ট’ তৈরি হবে। এটি জাতীয়তাবাদী সমর্থন তৈরি করবে এবং সরকার ভিন্নমত দমন করার অজুহাত পাবে।
লিবিয়া, ইরাকসহ বহু দেশের উদাহরণ দেখিয়ে সান্তিনো রেজিলমে বলেন, বহিরাগত হস্তক্ষেপ খুব কম দেশেই স্থিতিশীল গণতন্ত্র এনেছে।
মাদুরো সরকারও প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জিং ভঙ্গি নিয়েছে। নভেম্বরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিওসদাদো কাবেলো বলেন, ‘তারা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) মনে করে, বোমা ফেলে সব শেষ করবে। এখানে? এই দেশে?’
মাদুরোও বলেন, ‘আমরা শান্তি চাই, কিন্তু দাসের মতো শান্তি নয়। সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে শান্তি চাই।’
মার্কিন কৌশল কী
সিএসআইসির উপদেষ্টা এবং সাবেক মেরিন কর্নেল মার্ক ক্যানসিয়ান জানান, মাদুরোর প্রতি ভেনেজুয়েলার সামরিক বাহিনীর যে আনুগত্য, সেটা দুর্বল করতে কাজ করছে সিআইএ। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র সামরিক বাহিনীকে বার্তা দিতে পারে, তারা যদি লড়াই না করে ব্যারাকে থাকে, তাহলে তাদের ওপর হামলা হবে না।
১৯৯১ সালের ডেজার্ট স্টর্মে (উপসাগরীয় যুদ্ধের সময়) যুক্তরাষ্ট্র একই কৌশল ব্যবহার করেছিল। এখানে মার্কিন কর্মকর্তারা গোপনে কিছু ইরাকি ইউনিটকে সংকেত দিয়েছিলেন যে তারা যদি লড়াই না করে ব্যারাকে থাকে, তবে তাদের লক্ষ্যবস্তু করা হবে না। এই কৌশল প্রতিরোধের মাত্রা কমাতে সাহায্য করেছিল।
তবে ক্যানসিয়ান মনে করেন, মাদুরোর সরকার ইতিমধ্যে সেনাবাহিনী থেকে তাদের বিরোধী মতাদর্শীদের সরিয়ে ফেলেছে এবং লড়াইয়ের সম্ভাবনাই বেশি।
ভেনেজুয়েলার সেনাবাহিনী কী করতে পারে
অরিনোকো রিসার্চের প্রতিষ্ঠাতা এলিয়াস ফেরর বলেন, সবকিছু নির্ভর করবে হামলার আগে যুক্তরাষ্ট্র তাদের কী বার্তা দেয় তার ওপর।
ওয়াশিংটনের সামনে দুটি পথ রয়েছে। প্রথমত, তারা সামরিক বাহিনীকে বলবে, ‘আমরা সফল হলে তোমরা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, ব্যবসা ও ক্ষমতায় থাকতে পারবে।’ দ্বিতীয়ত, ইরাকে ‘ডি-বাথিফিকেশনের’ মতো সব অফিসার-সৈন্যকে সরিয়ে দেওয়া।
ফেররের মতে, সামরিক বাহিনীকে কোণঠাসা করলে দেশজুড়ে বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ দেখা দিতে পারে।
প্রসঙ্গত, ডি-বাথিফিকেশন (De-Ba’athification) হলো ২০০৩ সালে ইরাক আক্রমণের পর মার্কিন নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন প্রোভিশনাল অথরিটির (সিপিএ) একটি নীতি। এর লক্ষ্য ছিল সাদ্দাম হোসেনের বাথ পার্টির (Ba’ath Party) সব সদস্যকে সরকারি পদ, প্রশাসন ও সামরিক বাহিনী থেকে অপসারণ করে ইরাকের সমাজকে বাথবাদী প্রভাবমুক্ত করা।
সাধারণ ভেনেজুয়েলানদের প্রতিক্রিয়া কেমন হতে পারে
বিশ্লেষকদের মতে, পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হবে। হাইপারইনফ্লেশন বা চরম মুদ্রাস্ফীতি, দীর্ঘমেয়াদি সংকট, আর্থিক পতন, আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা এবং বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বাস্তু সংকট তৈরি হতে পারে।
২০২৫ সালের হিসাব অনুযায়ী, ভেনেজুয়েলার ৭৯ লাখ অর্থাৎ ২৮-৩০ শতাংশ মানুষের মানবিক সহায়তার প্রয়োজন।
রাজনৈতিক বিজ্ঞানী সান্তিনো রেজিলমে বলেন, এমন অবস্থায় মার্কিন হামলা জনগণের কাছে হবে ভয়াবহ নিরাপত্তাহীনতা। খাদ্য, ওষুধ, বিদ্যুৎ ও মৌলিক সেবার ওপর আরও চাপ তৈরি হবে।
আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া কেমন হবে
চীন ভেনেজুয়েলার অন্যতম বড় অর্থনৈতিক অংশীদার ও ঋণদাতা। বিশ্লেষকদের মতে, তারা মাদুরোর প্রতি কূটনৈতিক সমর্থন বজায় রাখবে, কিন্তু যুদ্ধ শুরু হলে সরাসরি ভূমিকা সীমিত থাকবে।
ভেনেজুয়েলান বিশ্লেষক কার্লোস পিনা বলেন, সশস্ত্র সংঘাত শুরু হলে চীনের প্রভাব সীমিত হবে। অন্যদিকে রাশিয়া ভেনেজুয়েলার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে অস্ত্র, প্রশিক্ষণ, গোয়েন্দা সহায়তাসহ সামরিক সহযোগিতা বজায় রেখেছে। পিনার মতে, রাশিয়া সামরিক পরামর্শে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। তবে দুই দেশই রাজনৈতিকভাবে মাদুরোর পাশে থাকবে।
মার্কিন আক্রমণ কি অন্য দেশেও ছড়াতে পারে
বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন, ভেনেজুয়েলার ঘটনাকে সামনে রেখে লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশেও একই মডেল প্রয়োগ করা হতে পারে। চলতি সপ্তাহে এক বৈঠকে ট্রাম্প সতর্ক করেন, যেকোনো মাদক উৎপাদনকারী দেশই যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে তিনি কলম্বিয়ার কোকেন উৎপাদনের কথা তুলে ধরেন।
লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক বিজ্ঞানী সান্তিনো রেজিলমে বলেন, ভেনেজুয়েলাকে ঘিরে মার্কিন পদক্ষেপ একক দেশের নীতি নয়; বরং জটিল রাজনৈতিক সংকটগুলোকে ‘নার্কো-টেররিস্ট’ হিসেবে চিহ্নিত করে সামরিক হস্তক্ষেপ বৈধ করার এক নতুন ছক। যদি এই পদ্ধতি অন্যান্য দেশে প্রয়োগ করা হয়, তবে আন্তর্জাতিক আইন ও আঞ্চলিক শান্তি প্রক্রিয়া আরও দুর্বল হয়ে পড়বে। তিনি বলেন, এতে ড্রাগ ট্রাফিকিং, অভিবাসন সংকটসহ আরও অনেক সমস্যার সমাধান সামরিকীকরণের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। এগুলো আর সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যা থাকবে না।
(কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা থেকে অনুবাদ করেছেন জগৎপতি বর্মা)
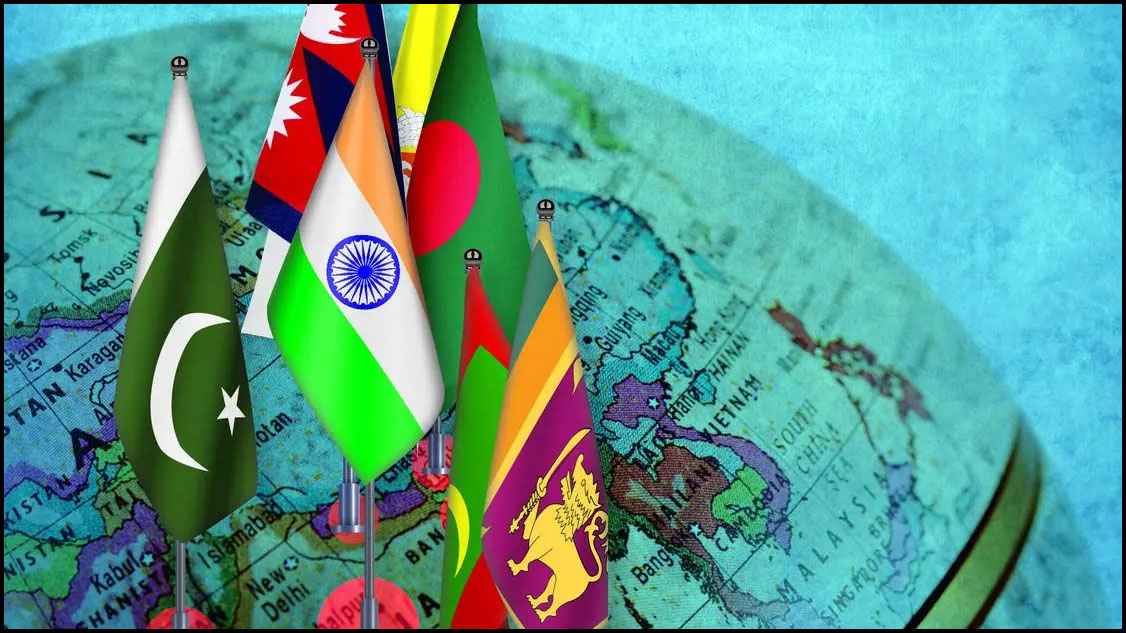
দক্ষিণ এশিয়া এখন সার্বভৌম ঋণ তথা সরকারের ঋণ ও রাজস্ব ঘাটতির ভারসাম্য রক্ষায় হিমশিম খাচ্ছে। স্থায়ী বাজেট ঘাটতির কারণে এ অঞ্চলের ঋণ বিশ্বের অন্যান্য উদীয়মান অর্থনীতির তুলনায় দ্রুত বেড়ে গেছে। ২০২৩ সালে সরকারগুলোর গড় ঋণের পরিমাণ পৌঁছেছে মোট জিডিপির ৭৭ শতাংশে।
১৯ অক্টোবর ২০২৫
পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ইসহাক দার জানিয়েছেন, বাংলাদেশ, চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্প্রতি যে ত্রিপক্ষীয় উদ্যোগ শুরু হয়েছে, তা অন্য আঞ্চলিক দেশ এবং এর বাইরেও ‘বিস্তৃত’ হতে পারে। তিনি গত বুধবার ইসলামাবাদ কনক্লেভ ফোরামে বলেন, ‘আমরা শূন্য-সমষ্টিগত পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছি এবং সংঘাতের বদলে সহযোগিতার
২০ ঘণ্টা আগে
ভ্লাদিস্লাভ ইনোজেমতসেভ বলেন, ‘পুতিন ভালোভাবেই জানেন যে ইউক্রেনের হাতে সময় ফুরিয়ে আসছে। তাই, পুতিন সবকিছু নিয়ে খুব আত্মবিশ্বাসী। তাঁর হাতে সময় আছে। তিনি এক বা দুই বছর ধরে লড়তে পারেন। সমস্যাটা বরং পশ্চিমের (এবং তাদের লড়াইয়ের ইচ্ছার)। তাই, হ্যাঁ, তিনি দেরি করতে প্রস্তুত—ইউক্রেন ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দেও
২১ ঘণ্টা আগে
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতদের মধ্যে ইউক্রেন শান্তি চুক্তি নিয়ে আলোচনা হলেও প্রকাশ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। পুতিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ইউরি উশাকভ, এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে অমীমাংসিত ‘আঞ্চলিক সমস্যাই’ মূল বাধা। আর এই অঞ্চল আর কোনোটিই নয়, দোনেৎস্ক।
২ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ইসহাক দার জানিয়েছেন, বাংলাদেশ, চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্প্রতি যে ত্রিপক্ষীয় উদ্যোগ শুরু হয়েছে, তা অন্য আঞ্চলিক দেশ এবং এর বাইরেও ‘বিস্তৃত’ হতে পারে। তিনি গত বুধবার ইসলামাবাদ কনক্লেভ ফোরামে বলেন, ‘আমরা শূন্য-সমষ্টিগত পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছি এবং সংঘাতের বদলে সহযোগিতার আবশ্যকতার ওপর ধারাবাহিকভাবে জোর দিয়েছি।’
বস্তুত, এই প্রস্তাব দক্ষিণ এশিয়ার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চীনকে সঙ্গে নিয়ে একটি বিকল্প জোট তৈরির ইঙ্গিত। বিশেষত এমন এক সময়ে যখন ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনার কারণে এই অঞ্চলের প্রধান সংস্থা সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজওনাল কো-অপারেশন বা দক্ষিণ এশীয় সহযোগিতা সংস্থা–সার্ক কার্যকারিতা প্রায় হারিয়ে ফেলেছে।
গত জুনে চীন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের কূটনীতিকেরা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান বাড়ানোর ওপর মনোযোগ দিয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা বলেন, এই সহযোগিতা ‘কোনো তৃতীয় পক্ষের প্রতি লক্ষ্য করে নয়।’
দারের এই মন্তব্য এমন এক প্রেক্ষাপটে এল, যখন আঞ্চলিক উত্তেজনা বাড়ছে। এর মধ্যে রয়েছে—পাকিস্তান–ভারতের কয়েক দশকের পুরোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই দুই পরমাণু শক্তিধর প্রতিবেশী গত মে মাসে চার দিনের যুদ্ধে জড়িয়েছিল, যা সম্পর্ককে আরও টানাপোড়েনের দিকে ঠেলে দিয়েছে।
এদিকে, বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত বছরের আগস্টে গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ঢাকা–নয়াদিল্লি সম্পর্কও ব্যাপক খারাপ হয়েছে। হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ভারতে পালিয়ে যান এবং নয়াদিল্লি এখন পর্যন্ত সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে রাজি হয়নি। গত নভেম্বরে বাংলাদেশের ট্রাইব্যুনাল তাঁকে মানবতাবিরোধী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দেয়।
কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলো–সার্কে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, মালদ্বীপ, ভুটান এবং আফগানিস্তান রয়েছে–তারা কি এই নতুন আঞ্চলিক জোটকে মেনে নেবে? মনে হচ্ছে এই জোট ভারতকে বাদ দেওয়ার, কিংবা অন্তত দেশটির প্রভাবকে সীমিত করার লক্ষ্য নিয়ে গঠিত হচ্ছে।
উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার বলেছেন, বাংলাদেশ ও চীনের সঙ্গে এই ত্রিপক্ষীয় উদ্যোগের লক্ষ্য হলো—অভিন্ন স্বার্থের ক্ষেত্রগুলোতে ‘পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি’ করা এবং এই ধারণাটি আরও দেশ ও অঞ্চলে ‘বিস্তৃত ও অনুকরণযোগ্য’ হতে পারে। তিনি ইসলামাবাদ কনক্লেভে বলেন, ‘আমি আগেও বলেছি, অর্থনীতি থেকে প্রযুক্তি এবং যোগাযোগ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে বহুমুখী বাস্তবতা থাকতে পারে।’
তিনি ভারতকে ইঙ্গিত করে বলেন, ‘আমাদের নিজেদের জাতীয় উন্নয়নের প্রয়োজন এবং আঞ্চলিক অগ্রাধিকারগুলো কারও গোঁড়ামির কাছে জিম্মি থাকতে পারে না এবং আপনারা জানেন, আমি কাকে ইঙ্গিত করছি।’ ইসলামাবাদ ও নয়াদিল্লির মধ্যেকার উত্তেজনা প্রসঙ্গে দার উল্লেখ করেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ‘কাঠামোগত আলোচনার’ প্রক্রিয়া ‘১১ বছরের বেশি’ সময় ধরে থমকে আছে। তিনি আরও যোগ করেন, অন্যান্য আঞ্চলিক দেশগুলোরও ‘আমাদের প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে দোদুল্যমান সম্পর্কের’ অভিজ্ঞতা রয়েছে।
পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, পাকিস্তান এমন একটি দক্ষিণ এশিয়ার স্বপ্ন দেখে যেখানে ‘বিভাজনের’ জায়গায় যোগাযোগ ও সহযোগিতা স্থান নেবে, যেখানে অর্থনীতিগুলো পারস্পরিক সমন্বয়ে বৃদ্ধি পাবে, আন্তর্জাতিক বৈধতা অনুসারে শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধের সমাধান হবে এবং যেখানে মর্যাদা ও সম্মানের সঙ্গে শান্তি বজায় থাকবে। শিক্ষাবিদ রাবিয়া আখতারের মতে, এই পর্যায়ে প্রস্তাবটি ‘কার্যকর হওয়ার চেয়ে আকাঙ্ক্ষামূলক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।’
লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর সিকিউরিটি, স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড পলিসি রিসার্চের (সিএসএসপিআর) পরিচালক আখতার বলেন, ‘কিন্তু এটি এমন এক সময়ে আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রক্রিয়াকে বৈচিত্র্যময় করে তোলার ও নতুন করে সাজানোর পাকিস্তানের উদ্দেশ্যকে তুলে ধরেছে, যখন সার্ক স্থবির হয়ে আছে।’
সার্ক ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশের ঢাকায় একটি শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর সাতটি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশ ছিল—বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা। ২০০৭ সালে আফগানিস্তান অষ্টম সদস্য হিসেবে যোগ দেয়। সার্কের উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ এশীয়দের কল্যাণ ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটানো।
এর মহৎ উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও, সংস্থাটি গত ৪০ বছর ধরেই লক্ষ্য অর্জনে লড়াই করেছে। এর মূল কারণ হলো ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেকার কয়েক দশকের পুরোনো উত্তেজনা। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা এবং উপমহাদেশ বিভাজনের পর এই দুই প্রতিবেশী তিনটি পূর্ণ মাত্রার যুদ্ধে জড়িয়েছে। ২০১৬ সালে ইসলামাবাদে ১৯ তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনের কথা ছিল। কিন্তু ভারত শাসিত কাশ্মীরে এক প্রাণঘাতী হামলার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করে ভারত সম্মেলন থেকে সরে দাঁড়ানোর পর তা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে যায়।
সিএসএসপিআর-এর আখতার বলেন, ‘এই সংস্থাটির কাজ করার জন্য ঐকমত্যের প্রয়োজন, আর দুটি বৃহত্তম সদস্য দেশের কাছ থেকে আঞ্চলিক সহযোগিতাকে দ্বিপক্ষীয় বিরোধ থেকে আলাদা রাখার রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছাড়া সার্ক সামনে এগোতে পারে না।’
আঞ্চলিক এই সংস্থাটির শেষ শীর্ষ সম্মেলন ২০১৪ সালে নেপালের কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তবে বিশ্লেষকেরা বলেন, সার্ক নিষ্ক্রিয় থাকলেও এই অঞ্চলের জন্য কাজ করার সম্ভাবনা তার আছে–যদি ভারত ও পাকিস্তান তাদের সেই সুযোগ দেয়। ২০২৫ সালের হিসেব অনুযায়ী, সার্কভুক্ত দেশগুলোতে বিশ্বের দুই বিলিয়নেরও বেশি মানুষ বসবাস করে, যা দক্ষিণ এশিয়াকে বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল করে তুলেছে।
তবুও, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য খুবই কম, যা এই অঞ্চলের সামগ্রিক বাণিজ্যের মাত্র প্রায় ৫ শতাংশ। অর্থাৎ প্রায় ২৩ বিলিয়ন ডলার বলে জানিয়েছে বিশ্বব্যাংক। বিপরীতে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১১টি দেশের একটি জোট আসিয়ানের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার বাণিজ্য তাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ২৫ শতাংশ। আসিয়ান জোটের জনসংখ্যা প্রায় ৭০ কোটি।
বিশ্বব্যাংকের অনুমান, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো যদি বাণিজ্য বাধাগুলো হ্রাস করে, তাহলে তারা ৬৭ বিলিয়ন ডলারের পণ্য বিনিময় করতে পারত–যা তাদের বর্তমান বাণিজ্যের তিন গুণ। বিশেষ করে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বাণিজ্য এখনো করুণ। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে আনুষ্ঠানিক বাণিজ্য ছিল মাত্র ২ দশমিক ৪১ বিলিয়ন ডলার। ২০২৪ সাল নাগাদ তা আরও কমে অর্ধেকে অর্থাৎ ১ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। যদিও অন্যান্য দেশের মাধ্যমে পরিচালিত তাদের অনানুষ্ঠানিক বাণিজ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলারের।
আঞ্চলিক যোগাযোগের অভাবকে এই অঞ্চলের দুর্বল বাণিজ্য সংযোগের একটি প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ২০১৪ সালে, এই জোট একটি মোটর ভেহিক্যালস চুক্তি স্বাক্ষরের দ্বারপ্রান্তে ছিল, যার ফলে ইউরোপের মতো দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে গাড়ি ও ট্রাক চলাচল করতে পারত। কিন্তু ভারতের সঙ্গে উত্তেজনার মধ্যে পাকিস্তান সেই চুক্তি–এবং আঞ্চলিক রেল সহযোগিতা সম্পর্কিত একটি পৃথক চুক্তি–আটকে দেয়।
তারপর থেকে এই জোটের একত্রে আসার ক্ষমতা কয়েকটি উপলক্ষে সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন কোভিড-১৯ মহামারির সময় যখন সদস্য রাষ্ট্রগুলো একটি জরুরি তহবিল গঠন করে এবং জনস্বাস্থ্য সংকট মোকাবিলায় সাহায্য করার জন্য ৭ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করে। বিশ্লেষক ফারওয়া আমের বলেন, ‘যদি এই দুটি দেশ (ভারত ও পাকিস্তান) বৃহত্তর আঞ্চলিক স্বার্থে সহযোগিতার সীমিত পথও চিহ্নিত করতে পারত, তাহলে নীতিগতভাবে সার্ককে পুনরুজ্জীবিত করা যেত।’
এশিয়া সোসাইটি পলিসি ইনস্টিটিউটের (এএসপিআই) দক্ষিণ এশিয়া প্রোগ্রামের পরিচালক আমের যোগ করেন, ‘তবে, বর্তমান রাজনৈতিক গতিশীলতা বিবেচনা করে, এমন একটি সাফল্য একটি সুদূর সম্ভাবনা বলে মনে হচ্ছে।’
তবে আঞ্চলিক অংশীদারত্ব গড়ে তুলতে সার্ককে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা পাকিস্তানই প্রথম করছে না। সার্ক একটি আঞ্চলিক পরিবহন চুক্তি অনুমোদন করতে ব্যর্থ হওয়ার পর, বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত ও নেপাল–দেশগুলোর আদ্যক্ষর অনুসারে বিবিআইএন নামে একটি জোট তৈরি করে–নিজেদের মধ্যে একই ধরনের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। আমের উল্লেখ করেন, ভারত অন্যান্য আঞ্চলিক সংস্থা, যেমন বে অব বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টরাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কো-অপারেশনের (বিমসটেক) অংশ। বিমসটেকে ভারত, বাংলাদেশ, ভুটান, মিয়ানমার, নেপাল, শ্রীলঙ্কা এবং থাইল্যান্ড রয়েছে।
তবুও, আমের সামগ্রিকভাবে বলেন, ‘অল্প বা মাঝারি মেয়াদে’ আঞ্চলিক বহুপাক্ষিকতার চেয়ে ‘দ্বিপক্ষীয় ও ত্রয়ী ব্যবস্থাগুলোই প্রাধান্য’ পাবে। কারণ, এক বা দুটি দেশের সঙ্গে একবারে কাজ করা ‘বেশি নমনীয়তা, পরিষ্কার প্রণোদনা এবং বাস্তব ফলাফল পাওয়ার বৃহত্তর সম্ভাবনা’ দেয়।
এই অবস্থায় পাকিস্তান যে প্রস্তাব দিচ্ছে, নতুন জোটের তা কার্যকর হবে কী—এই বিষয়ে শিক্ষাবিদ আখতার বলেন, ‘প্রস্তাবটি কার্যকর হবে কিনা তা দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করবে। প্রথমত, প্রথাগত কাঠামো যখন থমকে আছে, তখন সম্ভাব্য দেশগুলো ছোট, বিষয়-কেন্দ্রিক দলগুলোতে কার্যকরী মূল্য দেখতে পাচ্ছে কিনা এবং দ্বিতীয়ত, এই অংশগ্রহণের কারণে ভারতের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে কোনো মূল্য দিতে হচ্ছে কিনা।’
আখতার বলেন, বেশ কয়েকটি দক্ষিণ এশীয় দেশ পাকিস্তানের প্রস্তাবিত আঞ্চলিক উদ্যোগে প্রাথমিক আগ্রহ দেখাতে পারে, যদিও আনুষ্ঠানিক অংশগ্রহণের দিকে কোনো পদক্ষেপ সীমাবদ্ধ থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ‘আমার মনে হয় শ্রীলঙ্কা, নেপাল, মালদ্বীপ এবং হয়তো ভুটানের মতো দেশগুলো অনুসন্ধানী আলোচনায়, বিশেষ করে যোগাযোগ, জলবায়ু অভিযোজন ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে, খোলা থাকতে পারে।’
তবে আখতার উল্লেখ করেন, ভারতের আঞ্চলিক সংবেদনশীলতা এবং পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে বৃহত্তর ভূ-রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে ‘আসল সদস্যপদ গ্রহণ সতর্কতার সঙ্গে হবে।’ এই বিষয়ে এএসপিআই-এর আমের মনে করেন পাকিস্তানের প্রস্তাবটি ‘কৌশলগতভাবে সুসংগত।’ তিনি বলেন, ‘দেশটি এখন কূটনৈতিক তৎপরতার মধ্যে আছে। তারা চীনের সঙ্গে শক্তিশালী সম্পর্ক বজায় রেখেছে এবং একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও উপসাগরীয় দেশগুলোর সঙ্গে নতুন ও উন্নত সম্পর্ক তৈরি করেছে।’
আমেরের মতে, ‘এই দ্বৈত-পথের সম্পৃক্ততা ইসলামাবাদকে এক ধরনের আত্মবিশ্বাস এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক অভিনেতা হিসেবে নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা দিয়েছে। কার্যত, আঞ্চলিক কূটনীতির কেন্দ্রে একটি আসন ফিরে পাওয়ার সুযোগ দিয়েছে।’
আল–জাজিরা থেকে অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান

পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ইসহাক দার জানিয়েছেন, বাংলাদেশ, চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্প্রতি যে ত্রিপক্ষীয় উদ্যোগ শুরু হয়েছে, তা অন্য আঞ্চলিক দেশ এবং এর বাইরেও ‘বিস্তৃত’ হতে পারে। তিনি গত বুধবার ইসলামাবাদ কনক্লেভ ফোরামে বলেন, ‘আমরা শূন্য-সমষ্টিগত পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছি এবং সংঘাতের বদলে সহযোগিতার আবশ্যকতার ওপর ধারাবাহিকভাবে জোর দিয়েছি।’
বস্তুত, এই প্রস্তাব দক্ষিণ এশিয়ার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চীনকে সঙ্গে নিয়ে একটি বিকল্প জোট তৈরির ইঙ্গিত। বিশেষত এমন এক সময়ে যখন ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনার কারণে এই অঞ্চলের প্রধান সংস্থা সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজওনাল কো-অপারেশন বা দক্ষিণ এশীয় সহযোগিতা সংস্থা–সার্ক কার্যকারিতা প্রায় হারিয়ে ফেলেছে।
গত জুনে চীন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের কূটনীতিকেরা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান বাড়ানোর ওপর মনোযোগ দিয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা বলেন, এই সহযোগিতা ‘কোনো তৃতীয় পক্ষের প্রতি লক্ষ্য করে নয়।’
দারের এই মন্তব্য এমন এক প্রেক্ষাপটে এল, যখন আঞ্চলিক উত্তেজনা বাড়ছে। এর মধ্যে রয়েছে—পাকিস্তান–ভারতের কয়েক দশকের পুরোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই দুই পরমাণু শক্তিধর প্রতিবেশী গত মে মাসে চার দিনের যুদ্ধে জড়িয়েছিল, যা সম্পর্ককে আরও টানাপোড়েনের দিকে ঠেলে দিয়েছে।
এদিকে, বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত বছরের আগস্টে গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ঢাকা–নয়াদিল্লি সম্পর্কও ব্যাপক খারাপ হয়েছে। হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ভারতে পালিয়ে যান এবং নয়াদিল্লি এখন পর্যন্ত সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে রাজি হয়নি। গত নভেম্বরে বাংলাদেশের ট্রাইব্যুনাল তাঁকে মানবতাবিরোধী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দেয়।
কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলো–সার্কে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, মালদ্বীপ, ভুটান এবং আফগানিস্তান রয়েছে–তারা কি এই নতুন আঞ্চলিক জোটকে মেনে নেবে? মনে হচ্ছে এই জোট ভারতকে বাদ দেওয়ার, কিংবা অন্তত দেশটির প্রভাবকে সীমিত করার লক্ষ্য নিয়ে গঠিত হচ্ছে।
উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার বলেছেন, বাংলাদেশ ও চীনের সঙ্গে এই ত্রিপক্ষীয় উদ্যোগের লক্ষ্য হলো—অভিন্ন স্বার্থের ক্ষেত্রগুলোতে ‘পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি’ করা এবং এই ধারণাটি আরও দেশ ও অঞ্চলে ‘বিস্তৃত ও অনুকরণযোগ্য’ হতে পারে। তিনি ইসলামাবাদ কনক্লেভে বলেন, ‘আমি আগেও বলেছি, অর্থনীতি থেকে প্রযুক্তি এবং যোগাযোগ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে বহুমুখী বাস্তবতা থাকতে পারে।’
তিনি ভারতকে ইঙ্গিত করে বলেন, ‘আমাদের নিজেদের জাতীয় উন্নয়নের প্রয়োজন এবং আঞ্চলিক অগ্রাধিকারগুলো কারও গোঁড়ামির কাছে জিম্মি থাকতে পারে না এবং আপনারা জানেন, আমি কাকে ইঙ্গিত করছি।’ ইসলামাবাদ ও নয়াদিল্লির মধ্যেকার উত্তেজনা প্রসঙ্গে দার উল্লেখ করেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ‘কাঠামোগত আলোচনার’ প্রক্রিয়া ‘১১ বছরের বেশি’ সময় ধরে থমকে আছে। তিনি আরও যোগ করেন, অন্যান্য আঞ্চলিক দেশগুলোরও ‘আমাদের প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে দোদুল্যমান সম্পর্কের’ অভিজ্ঞতা রয়েছে।
পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, পাকিস্তান এমন একটি দক্ষিণ এশিয়ার স্বপ্ন দেখে যেখানে ‘বিভাজনের’ জায়গায় যোগাযোগ ও সহযোগিতা স্থান নেবে, যেখানে অর্থনীতিগুলো পারস্পরিক সমন্বয়ে বৃদ্ধি পাবে, আন্তর্জাতিক বৈধতা অনুসারে শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধের সমাধান হবে এবং যেখানে মর্যাদা ও সম্মানের সঙ্গে শান্তি বজায় থাকবে। শিক্ষাবিদ রাবিয়া আখতারের মতে, এই পর্যায়ে প্রস্তাবটি ‘কার্যকর হওয়ার চেয়ে আকাঙ্ক্ষামূলক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।’
লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর সিকিউরিটি, স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড পলিসি রিসার্চের (সিএসএসপিআর) পরিচালক আখতার বলেন, ‘কিন্তু এটি এমন এক সময়ে আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রক্রিয়াকে বৈচিত্র্যময় করে তোলার ও নতুন করে সাজানোর পাকিস্তানের উদ্দেশ্যকে তুলে ধরেছে, যখন সার্ক স্থবির হয়ে আছে।’
সার্ক ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশের ঢাকায় একটি শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর সাতটি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশ ছিল—বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা। ২০০৭ সালে আফগানিস্তান অষ্টম সদস্য হিসেবে যোগ দেয়। সার্কের উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ এশীয়দের কল্যাণ ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটানো।
এর মহৎ উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও, সংস্থাটি গত ৪০ বছর ধরেই লক্ষ্য অর্জনে লড়াই করেছে। এর মূল কারণ হলো ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেকার কয়েক দশকের পুরোনো উত্তেজনা। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা এবং উপমহাদেশ বিভাজনের পর এই দুই প্রতিবেশী তিনটি পূর্ণ মাত্রার যুদ্ধে জড়িয়েছে। ২০১৬ সালে ইসলামাবাদে ১৯ তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনের কথা ছিল। কিন্তু ভারত শাসিত কাশ্মীরে এক প্রাণঘাতী হামলার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করে ভারত সম্মেলন থেকে সরে দাঁড়ানোর পর তা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে যায়।
সিএসএসপিআর-এর আখতার বলেন, ‘এই সংস্থাটির কাজ করার জন্য ঐকমত্যের প্রয়োজন, আর দুটি বৃহত্তম সদস্য দেশের কাছ থেকে আঞ্চলিক সহযোগিতাকে দ্বিপক্ষীয় বিরোধ থেকে আলাদা রাখার রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছাড়া সার্ক সামনে এগোতে পারে না।’
আঞ্চলিক এই সংস্থাটির শেষ শীর্ষ সম্মেলন ২০১৪ সালে নেপালের কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তবে বিশ্লেষকেরা বলেন, সার্ক নিষ্ক্রিয় থাকলেও এই অঞ্চলের জন্য কাজ করার সম্ভাবনা তার আছে–যদি ভারত ও পাকিস্তান তাদের সেই সুযোগ দেয়। ২০২৫ সালের হিসেব অনুযায়ী, সার্কভুক্ত দেশগুলোতে বিশ্বের দুই বিলিয়নেরও বেশি মানুষ বসবাস করে, যা দক্ষিণ এশিয়াকে বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল করে তুলেছে।
তবুও, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য খুবই কম, যা এই অঞ্চলের সামগ্রিক বাণিজ্যের মাত্র প্রায় ৫ শতাংশ। অর্থাৎ প্রায় ২৩ বিলিয়ন ডলার বলে জানিয়েছে বিশ্বব্যাংক। বিপরীতে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১১টি দেশের একটি জোট আসিয়ানের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার বাণিজ্য তাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ২৫ শতাংশ। আসিয়ান জোটের জনসংখ্যা প্রায় ৭০ কোটি।
বিশ্বব্যাংকের অনুমান, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো যদি বাণিজ্য বাধাগুলো হ্রাস করে, তাহলে তারা ৬৭ বিলিয়ন ডলারের পণ্য বিনিময় করতে পারত–যা তাদের বর্তমান বাণিজ্যের তিন গুণ। বিশেষ করে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বাণিজ্য এখনো করুণ। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে আনুষ্ঠানিক বাণিজ্য ছিল মাত্র ২ দশমিক ৪১ বিলিয়ন ডলার। ২০২৪ সাল নাগাদ তা আরও কমে অর্ধেকে অর্থাৎ ১ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। যদিও অন্যান্য দেশের মাধ্যমে পরিচালিত তাদের অনানুষ্ঠানিক বাণিজ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলারের।
আঞ্চলিক যোগাযোগের অভাবকে এই অঞ্চলের দুর্বল বাণিজ্য সংযোগের একটি প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ২০১৪ সালে, এই জোট একটি মোটর ভেহিক্যালস চুক্তি স্বাক্ষরের দ্বারপ্রান্তে ছিল, যার ফলে ইউরোপের মতো দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে গাড়ি ও ট্রাক চলাচল করতে পারত। কিন্তু ভারতের সঙ্গে উত্তেজনার মধ্যে পাকিস্তান সেই চুক্তি–এবং আঞ্চলিক রেল সহযোগিতা সম্পর্কিত একটি পৃথক চুক্তি–আটকে দেয়।
তারপর থেকে এই জোটের একত্রে আসার ক্ষমতা কয়েকটি উপলক্ষে সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন কোভিড-১৯ মহামারির সময় যখন সদস্য রাষ্ট্রগুলো একটি জরুরি তহবিল গঠন করে এবং জনস্বাস্থ্য সংকট মোকাবিলায় সাহায্য করার জন্য ৭ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করে। বিশ্লেষক ফারওয়া আমের বলেন, ‘যদি এই দুটি দেশ (ভারত ও পাকিস্তান) বৃহত্তর আঞ্চলিক স্বার্থে সহযোগিতার সীমিত পথও চিহ্নিত করতে পারত, তাহলে নীতিগতভাবে সার্ককে পুনরুজ্জীবিত করা যেত।’
এশিয়া সোসাইটি পলিসি ইনস্টিটিউটের (এএসপিআই) দক্ষিণ এশিয়া প্রোগ্রামের পরিচালক আমের যোগ করেন, ‘তবে, বর্তমান রাজনৈতিক গতিশীলতা বিবেচনা করে, এমন একটি সাফল্য একটি সুদূর সম্ভাবনা বলে মনে হচ্ছে।’
তবে আঞ্চলিক অংশীদারত্ব গড়ে তুলতে সার্ককে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা পাকিস্তানই প্রথম করছে না। সার্ক একটি আঞ্চলিক পরিবহন চুক্তি অনুমোদন করতে ব্যর্থ হওয়ার পর, বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত ও নেপাল–দেশগুলোর আদ্যক্ষর অনুসারে বিবিআইএন নামে একটি জোট তৈরি করে–নিজেদের মধ্যে একই ধরনের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। আমের উল্লেখ করেন, ভারত অন্যান্য আঞ্চলিক সংস্থা, যেমন বে অব বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টরাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কো-অপারেশনের (বিমসটেক) অংশ। বিমসটেকে ভারত, বাংলাদেশ, ভুটান, মিয়ানমার, নেপাল, শ্রীলঙ্কা এবং থাইল্যান্ড রয়েছে।
তবুও, আমের সামগ্রিকভাবে বলেন, ‘অল্প বা মাঝারি মেয়াদে’ আঞ্চলিক বহুপাক্ষিকতার চেয়ে ‘দ্বিপক্ষীয় ও ত্রয়ী ব্যবস্থাগুলোই প্রাধান্য’ পাবে। কারণ, এক বা দুটি দেশের সঙ্গে একবারে কাজ করা ‘বেশি নমনীয়তা, পরিষ্কার প্রণোদনা এবং বাস্তব ফলাফল পাওয়ার বৃহত্তর সম্ভাবনা’ দেয়।
এই অবস্থায় পাকিস্তান যে প্রস্তাব দিচ্ছে, নতুন জোটের তা কার্যকর হবে কী—এই বিষয়ে শিক্ষাবিদ আখতার বলেন, ‘প্রস্তাবটি কার্যকর হবে কিনা তা দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করবে। প্রথমত, প্রথাগত কাঠামো যখন থমকে আছে, তখন সম্ভাব্য দেশগুলো ছোট, বিষয়-কেন্দ্রিক দলগুলোতে কার্যকরী মূল্য দেখতে পাচ্ছে কিনা এবং দ্বিতীয়ত, এই অংশগ্রহণের কারণে ভারতের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে কোনো মূল্য দিতে হচ্ছে কিনা।’
আখতার বলেন, বেশ কয়েকটি দক্ষিণ এশীয় দেশ পাকিস্তানের প্রস্তাবিত আঞ্চলিক উদ্যোগে প্রাথমিক আগ্রহ দেখাতে পারে, যদিও আনুষ্ঠানিক অংশগ্রহণের দিকে কোনো পদক্ষেপ সীমাবদ্ধ থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ‘আমার মনে হয় শ্রীলঙ্কা, নেপাল, মালদ্বীপ এবং হয়তো ভুটানের মতো দেশগুলো অনুসন্ধানী আলোচনায়, বিশেষ করে যোগাযোগ, জলবায়ু অভিযোজন ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে, খোলা থাকতে পারে।’
তবে আখতার উল্লেখ করেন, ভারতের আঞ্চলিক সংবেদনশীলতা এবং পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে বৃহত্তর ভূ-রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে ‘আসল সদস্যপদ গ্রহণ সতর্কতার সঙ্গে হবে।’ এই বিষয়ে এএসপিআই-এর আমের মনে করেন পাকিস্তানের প্রস্তাবটি ‘কৌশলগতভাবে সুসংগত।’ তিনি বলেন, ‘দেশটি এখন কূটনৈতিক তৎপরতার মধ্যে আছে। তারা চীনের সঙ্গে শক্তিশালী সম্পর্ক বজায় রেখেছে এবং একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও উপসাগরীয় দেশগুলোর সঙ্গে নতুন ও উন্নত সম্পর্ক তৈরি করেছে।’
আমেরের মতে, ‘এই দ্বৈত-পথের সম্পৃক্ততা ইসলামাবাদকে এক ধরনের আত্মবিশ্বাস এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক অভিনেতা হিসেবে নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা দিয়েছে। কার্যত, আঞ্চলিক কূটনীতির কেন্দ্রে একটি আসন ফিরে পাওয়ার সুযোগ দিয়েছে।’
আল–জাজিরা থেকে অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান
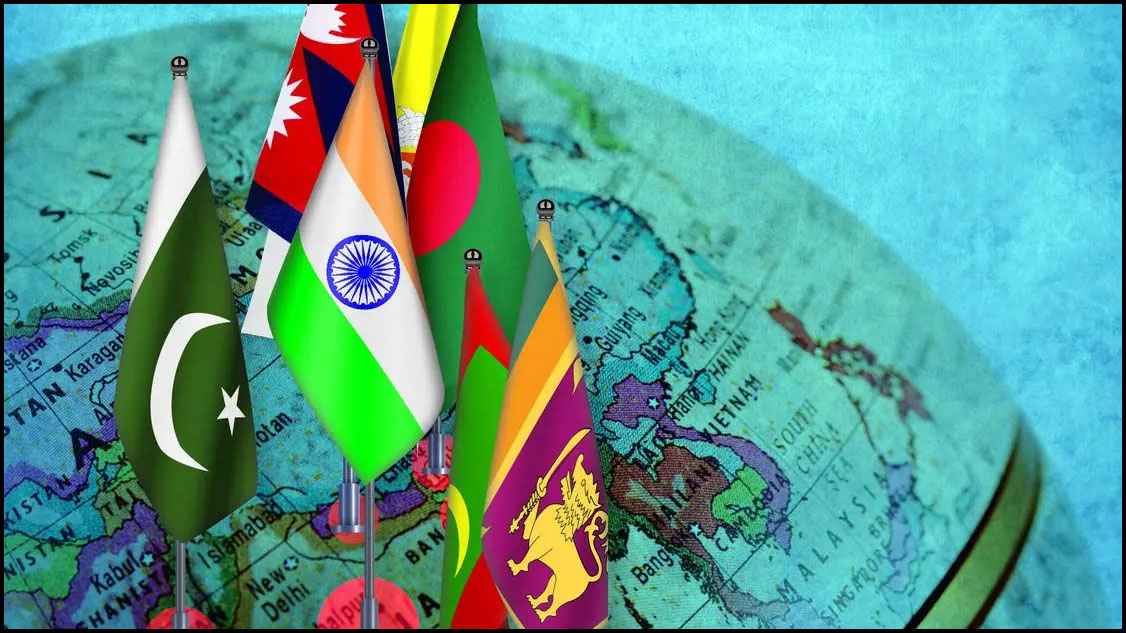
দক্ষিণ এশিয়া এখন সার্বভৌম ঋণ তথা সরকারের ঋণ ও রাজস্ব ঘাটতির ভারসাম্য রক্ষায় হিমশিম খাচ্ছে। স্থায়ী বাজেট ঘাটতির কারণে এ অঞ্চলের ঋণ বিশ্বের অন্যান্য উদীয়মান অর্থনীতির তুলনায় দ্রুত বেড়ে গেছে। ২০২৩ সালে সরকারগুলোর গড় ঋণের পরিমাণ পৌঁছেছে মোট জিডিপির ৭৭ শতাংশে।
১৯ অক্টোবর ২০২৫
সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে ভেনেজুয়েলায় মাদক পাচারের অভিযোগে অন্তত ২১টি নৌযানে মার্কিন সামরিক বাহিনী হামলা চালিয়েছে, যাতে অন্তত ৮৭ জন নিহত হয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসন দাবি করছে, এসব নৌকা যুক্তরাষ্ট্রে বিপুল পরিমাণ মাদক পাচার করছিল এবং তা মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি।
১৩ ঘণ্টা আগে
ভ্লাদিস্লাভ ইনোজেমতসেভ বলেন, ‘পুতিন ভালোভাবেই জানেন যে ইউক্রেনের হাতে সময় ফুরিয়ে আসছে। তাই, পুতিন সবকিছু নিয়ে খুব আত্মবিশ্বাসী। তাঁর হাতে সময় আছে। তিনি এক বা দুই বছর ধরে লড়তে পারেন। সমস্যাটা বরং পশ্চিমের (এবং তাদের লড়াইয়ের ইচ্ছার)। তাই, হ্যাঁ, তিনি দেরি করতে প্রস্তুত—ইউক্রেন ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দেও
২১ ঘণ্টা আগে
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতদের মধ্যে ইউক্রেন শান্তি চুক্তি নিয়ে আলোচনা হলেও প্রকাশ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। পুতিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ইউরি উশাকভ, এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে অমীমাংসিত ‘আঞ্চলিক সমস্যাই’ মূল বাধা। আর এই অঞ্চল আর কোনোটিই নয়, দোনেৎস্ক।
২ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

রুশদের মতে যুদ্ধ শেষ করার জন্য ইউক্রেন তাদের শর্তগুলো মানতে চাইছে না, সেটাই শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রধান অন্তরায়। অন্যদিকে কিয়েভ এবং তার অধিকাংশ ইউরোপীয় মিত্রদের বক্তব্য, এই যুদ্ধবিরতির চুক্তির পথে প্রধান বাধা হলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। মঙ্গলবার, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদল মস্কোয় যান। সেখানে পুতিনের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়, যা চলে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে। এই দলে ছিলেন আমেরিকার বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার।
পুতিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ইউরি উশাকভ এই বৈঠককে ‘খুবই কাজের এবং গঠনমূলক’ বললেও স্বীকার করেন যে, ‘সামনে অনেক পথ বাকি।’ তিনি বলেন, ইউক্রেনের ন্যাটোতে যোগদানের ইচ্ছা হলো ‘মূল প্রশ্ন।’ তবে তিনি এটাও মেনে নেন যে, ভূখণ্ড সংক্রান্ত প্রশ্নে কোনো সমঝোতা হয়নি।
ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা রাশিয়ার অবস্থানকে একেবারেই হাস্যকর মনে করছেন। কারণ, মস্কোই ২০২২ সালে ইউক্রেনে সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু করে। তাদের ধারণা, ইউক্রেনীয় শহরগুলোতে লাগাতার বোমা হামলা চলার কারণে পুতিনের আসলে শান্তিতে কোনো প্রকৃত আগ্রহ নেই।
আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলের ভিজিটিং ফেলো ও রুশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ইলিয়া বুদ্রাইৎস্কিস বলেন, ‘যেমনটা প্রত্যাশা করা গিয়েছিল, এই আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি। কারণ, আমেরিকান এবং ক্রেমলিনের মধ্যে যা ঘটছে, তা নিয়ে তাদের ধারণা মূলত আলাদা।’ তিনি বলেন, ‘শান্তি প্রস্তাবের মূল ধারণা হিসেবে আমেরিকানরা ভূখণ্ড বিনিময়ের যে চেষ্টা করেছিল, তাতে পুতিনের বিশেষ আগ্রহ নেই। তিনি আসলে পূর্ব ইউরোপের সামগ্রিক নিরাপত্তা কাঠামো পাল্টে দিতে আগ্রহী।’
রাশিয়ার অনেকে ক্রেমলিনের বক্তব্যকেই সমর্থন করেন এবং অনেকটা একই ভাষায় কথা বলেন। মস্কোভিত্তিক থিংক ট্যাংক ডিগোরিয়া এক্সপার্ট ক্লাবের সদস্য ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্পার্টাক বারানভস্কির মতামত রুশ সরকারের সঙ্গে মিলে যায়। তিনি বলেন, ‘শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথে কিয়েভ সরকারের ক্রমাগত নাশকতা, তথ্য বিকৃত করা এবং অনিবার্যকে বিলম্বিত করার চেষ্টা আলোচনা প্রক্রিয়াকে অনেক জটিল করে তুলেছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘ইউক্রেনীয় পক্ষ প্রথমে মিনস্ক চুক্তি কার্যকর করতে রাজি হয়নি এবং পরে ইস্তাম্বুলে আলোচনা হওয়া প্রাথমিক শান্তি চুক্তির শর্তগুলো প্রত্যাখ্যান করে। এমন এক ভরসা করার অযোগ্য প্রতিপক্ষের সঙ্গে গঠনমূলক আলাপ চালানো সত্যিই কঠিন।’
মিনস্ক চুক্তি ছিল ২০১৪ ও ২০১৫ সালে সই হওয়া একাধিক চুক্তিমালা, যার উদ্দেশ্য ছিল ইউক্রেনের দনবাসে চলা যুদ্ধ থামানো, যেখানে রুশ সমর্থিত বিচ্ছিন্নতাবাদীরা কিয়েভ সরকারের বিরুদ্ধে লড়ছিল। ২০২২ সালের পূর্ণ মাত্রায় আক্রমণের পর রাশিয়া ও ইউক্রেনের প্রতিনিধিদের মধ্যে বেলারুশ ও তুরস্কে বেশ কয়েকটি বৈঠক হয়েছে, কিন্তু কোনোটিই শান্তি আনতে পারেনি।
যদিও মস্কোয় সর্বশেষ বৈঠকে কী আলোচিত হয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ফাঁস হয়নি, তবু রাশিয়ায় সামান্য হলেও একটা আশার আলো দেখা যাচ্ছে যে, যুদ্ধের শেষ হয়তো কাছাকাছি। সেন্ট পিটার্সবার্গের ষাটোর্ধ্ব ব্যবসায়ী তাতিয়ানা এই যুদ্ধের জন্য রাশিয়াকেই দোষ দেন। তবে তিনি মনে করেন, ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে তাঁর ইউরোপীয় মিত্ররাই যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করতে বাধ্য করছেন।
তিনি আক্ষেপ করে প্রশ্ন করেন, ‘এই পরিস্থিতিতে যখন একমাত্র ট্রাম্পকেই কিছুটা বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন বলে মনে হচ্ছে। যিনি কিনা আবার স্বভাবগতভাবেই সম্পূর্ণ উন্মাদ। তাহলে বুঝুন দুনিয়ার কী হাল হয়েছে?’ তিনি আরও বলেন, ‘এখন পরিস্থিতি সবার জন্যই আরও খারাপ। একটা সিদ্ধান্ত তো নিতেই হবে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে স্পষ্টতই রাশিয়ার পাল্লা ভারী, যা আমেরিকান জেনারেলরাও ভালোই বোঝেন।’
গত মঙ্গলবার ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ ঘোষণা করেন, রুশ সৈন্যরা অবশেষে পূর্ব ইউক্রেনের কৌশলগত শহর পোকরোভস্ক দখল করেছে। এর ফলে দুই বছরের অবরোধের অবসান ঘটেছে। ইউক্রেন শহর পতনের কথা অস্বীকার করলেও, সম্প্রতি বেশ কয়েকটি অঞ্চলে রুশদের অগ্রযাত্রা থামাতে তাদের সেনারা বেশ বেগ পেতে হচ্ছে।
প্রস্তাবিত চুক্তির শর্তগুলোর মধ্যে রয়েছে—ইউক্রেনকে দনবাস অঞ্চলের যেসব অংশ এখনো রাশিয়ার দখলে যায়নি, সেখান থেকে সেনা সরাতে হবে। ওই এলাকা একটি নিরপেক্ষ নিরস্ত্রীকরণ অঞ্চল হবে, তবে আন্তর্জাতিকভাবে তা রাশিয়ার ভূখণ্ড হিসেবে স্বীকৃত হবে। একই সঙ্গে ক্রিমিয়া উপদ্বীপ এবং দোনেৎস্ক ও লুহানস্ক পিপলস রিপাবলিকস, যা ২০১৪ সাল থেকে রাশিয়া বা রুশ-সমর্থিতদের নিয়ন্ত্রণে, সেগুলোকে রাশিয়ার অংশ হিসেবে মেনে নিতে হবে। ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর সংখ্যা ৬ লাখের মধ্যে সীমিত রাখতে হবে এবং ইউক্রেনকে ন্যাটোতে যোগদানের সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে হবে, তবে ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।
এর বিনিময়ে, রাশিয়াকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে তারা আর কোনো ইউরোপীয় দেশ আক্রমণ করবে না এবং এই প্রতিশ্রুতি তাদের আইনে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এ ছাড়া, যুদ্ধাপরাধের জন্য সাধারণ ক্ষমার প্রস্তাবও আছে। গত সপ্তাহে পুতিন স্বীকার করেন যে এই পরিকল্পনা ‘ভবিষ্যতের চুক্তির ভিত্তি হতে পারে।’ তবে তিনি যোগ করেন, ‘যদি ইউক্রেনীয় সৈন্যরা তাদের দখল করা এলাকাগুলো ছেড়ে যায়, তবে আমরা যুদ্ধ থামাব। যদি না যায়, তবে আমরা সামরিকভাবেই আমাদের লক্ষ্য পূরণ করব।’
সূত্র মারফত জানা যায়, গত সপ্তাহান্তে ইউক্রেনীয় মধ্যস্থতাকারীরা তাদের আমেরিকান প্রতিপক্ষকে আবারও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে—কোনো ভূখণ্ড ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্নই আসে না।
ওয়াশিংটন ডিসিতে বসবাসকারী রুশ অর্থনীতিবিদ ভ্লাদিস্লাভ ইনোজেমতসেভ বলেন, ‘পুতিন ভালোভাবেই জানেন যে ইউক্রেনের হাতে সময় ফুরিয়ে আসছে। তাই, পুতিন সবকিছু নিয়ে খুব আত্মবিশ্বাসী। তাঁর হাতে সময় আছে। তিনি এক বা দুই বছর ধরে লড়তে পারেন। সমস্যাটা বরং পশ্চিমের (এবং তাদের লড়াইয়ের ইচ্ছার)। তাই, হ্যাঁ, তিনি দেরি করতে প্রস্তুত—ইউক্রেন ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দেওয়া পর্যন্ত নয়, বরং তার শর্তগুলো পূরণ হওয়া পর্যন্ত।’
মঙ্গলবার বৈঠকের আগে, পুতিন ইউরোপকে হুমকি দিয়ে আরও এক ধাপ এগিয়ে যান। তিনি সতর্ক করে দেন যে রাশিয়া ইউরোপের সঙ্গে যুদ্ধের পরিকল্পনা করছে না, ‘তবে ইউরোপ যদি চায় এবং শুরু করে, আমরা এই মুহূর্তেই প্রস্তুত।’
বুদ্রাইৎস্কিস বলেন, ‘পুতিন এর জন্যই প্রস্তুতি নেবেন, ঠিক যেমন ২০২২ সালের আগে তিনি বলেছিলেন যে—রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করতে যাচ্ছে না, যা বিপরীতটাই ইঙ্গিত করেছিল।’ দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা থাকার পরও ইনোজেমতসেভ এবং বারানভস্কি দুজনেই একমত যে রাশিয়া অনির্দিষ্টকাল ধরে তাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম। ইনোজেমতসেভ বলেন, ‘এতটা তীব্রতায় বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া মোটেও কোনো সমস্যা নয়।’
তাঁর ভাষায়, ‘যুদ্ধের শুরুতে যত সমস্যা ছিল, এখন তার চেয়ে কম। কারণ, শুরুতে আমরা দেখেছি তাদের লোক জড়ো করতে হয়েছিল; এখন তারা বেশ ভালো বেতন দেয় এবং (নতুন স্বেচ্ছাসেবকেরা) ক্রমাগত তালিকাভুক্ত হচ্ছে। এ ছাড়া, তাদের অস্ত্রের সমস্যা ছিল এবং ভাষ্যকাররা লিখেছিলেন যে তিন মাসের মধ্যে তাদের শেল ফুরিয়ে যাবে। বাস্তবে, এখন যুদ্ধের আগের চেয়েও বেশি সক্রিয়ভাবে অস্ত্র উৎপাদন হচ্ছে।’
ইনোজেমতসেভ মনে করেন, এখন ‘আমেরিকানরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে—হয় এই যুদ্ধ শেষ করতে হবে, না হয় ইউক্রেনের প্রতি সব রকম সমর্থন সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করতে হবে।’ তিনি বলেন, ‘আমার মনে হয় এই বার্তা এখন কিয়েভকে স্পষ্টভাবে দেওয়া হয়েছে। আর তাই, ইউক্রেনীয়দের কোনো না কোনোভাবে রাজি করানো হবে...ইউক্রেনীয়রা জানে যে ইউরোপ তাদের রক্ষা করতে পারবে না। অর্থাৎ, যদি এখন আমেরিকানরা এই প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে সরে দাঁড়ায়, তবে ইউরোপের কাছে বছরের পর বছর ধরে এই কারণকে সমর্থন করার মতো অর্থ বা সংকল্প কোনোটাই থাকবে না।’
ইনোজেমতসেভ উল্লেখ করেন, একটি চুক্তি হলেও তা ইউক্রেনের স্বার্থে আসতে পারে। তিনি বলেন, ‘যদি তারা নিজেদের সেনাবাহিনীর জন্য ৬ লাখ সৈন্য এবং অন্তত কয়েক বছরের জন্য একটি বিরতি নিশ্চিত করতে পারে, তবে বাস্তবে এটিই সমস্যার সমাধান।’ তিনি বলেন, ‘পুতিন সব সময়ই একটি হুমকি হয়ে থাকবেন এবং তাই পশ্চিমের প্রধান কাজ হলো (৭৩ বছর বয়সী) পুতিনকে উতরে যাওয়া। যদি তিন থেকে পাঁচ বছরের জন্য লড়াইয়ে বিরতি আসে, তবে এটি তার জীবনের শেষের দিকে পৌঁছে যাবে, যা স্বভাবতই তাঁকে কম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করবে।’
এ ছাড়া, যেকোনো সম্ভাব্য শান্তি চুক্তি এবং নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার রুশ অর্থনীতির জন্য উপকারী হবে। তবে ইনোজেমতসেভ ও বুদ্রাইৎস্কিস সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, জীবন ২০২২ সালের আগের মতো স্বাভাবিক হবে। তাঁদের অনুমান, সমাজ প্রবলভাবে সামরিক এবং কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত থাকবে। বুদ্রাইৎস্কিস বলেন, ‘শান্তি আসতে পারে না। এমন এক স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও ফেরা সম্ভব নয় যেখানে পূর্ণাঙ্গ দমনমূলক সর্বাত্মক একনায়কতন্ত্রের উপযোগী এই সমস্ত ব্যবস্থা তুলে নেওয়া হবে, কারণ আমাদের আর কোনো সরাসরি বাহ্যিক হুমকি নেই।’
তাঁর মতে, ‘এটাই রাশিয়ার পুতিন রেজিমের নকশা। তাঁর ক্ষমতা এভাবেই সাজানো হয়েছে যে, এখানে এক অন্তহীন যুদ্ধ চলবে, যেখানে রুশ অভিজাতরা পতাকার নিচে একত্রিত থাকবে, দেশের অভ্যন্তরে যে কোনো ভিন্নমতের বিরুদ্ধে দমন-পীড়ন চলবে...এগুলো কেবল সাময়িকভাবে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে চালু করা কিছু অসাধারণ ব্যবস্থা নয়, বরং এভাবেই তিনি শাসন চালিয়ে যাবেন।’
তিনি আরও যোগ করেন, ইউক্রেন, ইউরোপ, বাল্টিক রাষ্ট্র বা ‘যে কারও বিরুদ্ধে যেকোনো রূপে যুদ্ধ’ হলো পুতিন ২০২২ সালের পরে রাশিয়ায় যে ‘স্বাভাবিকতা’ প্রতিষ্ঠা করেছেন, তার অবিচ্ছেদ্য চালিকাশক্তি। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন, ‘সুতরাং, এই রেজিম টিকে থাকার জন্য বিভিন্ন ফ্রন্টে যুদ্ধ চলতে থাকবে।’
কিছু রুশ নাগরিক ইতিমধ্যেই দীর্ঘস্থায়ী পরিস্থিতির জন্য নিজেদের মানিয়ে নিয়েছেন। মস্কোর গণমাধ্যম সের্গেই কালেনিক বলেন, ‘আমেরিকা যত দিন ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে তাদের দখলদার সৈন্য প্রত্যাহার না করবে, তত দিন যুদ্ধ শেষ হবে না।’
আল–জাজিরা থেকে অনুবাদ করেছেন আব্দুর রহমান

রুশদের মতে যুদ্ধ শেষ করার জন্য ইউক্রেন তাদের শর্তগুলো মানতে চাইছে না, সেটাই শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রধান অন্তরায়। অন্যদিকে কিয়েভ এবং তার অধিকাংশ ইউরোপীয় মিত্রদের বক্তব্য, এই যুদ্ধবিরতির চুক্তির পথে প্রধান বাধা হলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। মঙ্গলবার, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদল মস্কোয় যান। সেখানে পুতিনের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়, যা চলে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে। এই দলে ছিলেন আমেরিকার বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার।
পুতিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ইউরি উশাকভ এই বৈঠককে ‘খুবই কাজের এবং গঠনমূলক’ বললেও স্বীকার করেন যে, ‘সামনে অনেক পথ বাকি।’ তিনি বলেন, ইউক্রেনের ন্যাটোতে যোগদানের ইচ্ছা হলো ‘মূল প্রশ্ন।’ তবে তিনি এটাও মেনে নেন যে, ভূখণ্ড সংক্রান্ত প্রশ্নে কোনো সমঝোতা হয়নি।
ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা রাশিয়ার অবস্থানকে একেবারেই হাস্যকর মনে করছেন। কারণ, মস্কোই ২০২২ সালে ইউক্রেনে সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু করে। তাদের ধারণা, ইউক্রেনীয় শহরগুলোতে লাগাতার বোমা হামলা চলার কারণে পুতিনের আসলে শান্তিতে কোনো প্রকৃত আগ্রহ নেই।
আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলের ভিজিটিং ফেলো ও রুশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ইলিয়া বুদ্রাইৎস্কিস বলেন, ‘যেমনটা প্রত্যাশা করা গিয়েছিল, এই আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি। কারণ, আমেরিকান এবং ক্রেমলিনের মধ্যে যা ঘটছে, তা নিয়ে তাদের ধারণা মূলত আলাদা।’ তিনি বলেন, ‘শান্তি প্রস্তাবের মূল ধারণা হিসেবে আমেরিকানরা ভূখণ্ড বিনিময়ের যে চেষ্টা করেছিল, তাতে পুতিনের বিশেষ আগ্রহ নেই। তিনি আসলে পূর্ব ইউরোপের সামগ্রিক নিরাপত্তা কাঠামো পাল্টে দিতে আগ্রহী।’
রাশিয়ার অনেকে ক্রেমলিনের বক্তব্যকেই সমর্থন করেন এবং অনেকটা একই ভাষায় কথা বলেন। মস্কোভিত্তিক থিংক ট্যাংক ডিগোরিয়া এক্সপার্ট ক্লাবের সদস্য ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্পার্টাক বারানভস্কির মতামত রুশ সরকারের সঙ্গে মিলে যায়। তিনি বলেন, ‘শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথে কিয়েভ সরকারের ক্রমাগত নাশকতা, তথ্য বিকৃত করা এবং অনিবার্যকে বিলম্বিত করার চেষ্টা আলোচনা প্রক্রিয়াকে অনেক জটিল করে তুলেছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘ইউক্রেনীয় পক্ষ প্রথমে মিনস্ক চুক্তি কার্যকর করতে রাজি হয়নি এবং পরে ইস্তাম্বুলে আলোচনা হওয়া প্রাথমিক শান্তি চুক্তির শর্তগুলো প্রত্যাখ্যান করে। এমন এক ভরসা করার অযোগ্য প্রতিপক্ষের সঙ্গে গঠনমূলক আলাপ চালানো সত্যিই কঠিন।’
মিনস্ক চুক্তি ছিল ২০১৪ ও ২০১৫ সালে সই হওয়া একাধিক চুক্তিমালা, যার উদ্দেশ্য ছিল ইউক্রেনের দনবাসে চলা যুদ্ধ থামানো, যেখানে রুশ সমর্থিত বিচ্ছিন্নতাবাদীরা কিয়েভ সরকারের বিরুদ্ধে লড়ছিল। ২০২২ সালের পূর্ণ মাত্রায় আক্রমণের পর রাশিয়া ও ইউক্রেনের প্রতিনিধিদের মধ্যে বেলারুশ ও তুরস্কে বেশ কয়েকটি বৈঠক হয়েছে, কিন্তু কোনোটিই শান্তি আনতে পারেনি।
যদিও মস্কোয় সর্বশেষ বৈঠকে কী আলোচিত হয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ফাঁস হয়নি, তবু রাশিয়ায় সামান্য হলেও একটা আশার আলো দেখা যাচ্ছে যে, যুদ্ধের শেষ হয়তো কাছাকাছি। সেন্ট পিটার্সবার্গের ষাটোর্ধ্ব ব্যবসায়ী তাতিয়ানা এই যুদ্ধের জন্য রাশিয়াকেই দোষ দেন। তবে তিনি মনে করেন, ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে তাঁর ইউরোপীয় মিত্ররাই যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করতে বাধ্য করছেন।
তিনি আক্ষেপ করে প্রশ্ন করেন, ‘এই পরিস্থিতিতে যখন একমাত্র ট্রাম্পকেই কিছুটা বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন বলে মনে হচ্ছে। যিনি কিনা আবার স্বভাবগতভাবেই সম্পূর্ণ উন্মাদ। তাহলে বুঝুন দুনিয়ার কী হাল হয়েছে?’ তিনি আরও বলেন, ‘এখন পরিস্থিতি সবার জন্যই আরও খারাপ। একটা সিদ্ধান্ত তো নিতেই হবে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে স্পষ্টতই রাশিয়ার পাল্লা ভারী, যা আমেরিকান জেনারেলরাও ভালোই বোঝেন।’
গত মঙ্গলবার ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ ঘোষণা করেন, রুশ সৈন্যরা অবশেষে পূর্ব ইউক্রেনের কৌশলগত শহর পোকরোভস্ক দখল করেছে। এর ফলে দুই বছরের অবরোধের অবসান ঘটেছে। ইউক্রেন শহর পতনের কথা অস্বীকার করলেও, সম্প্রতি বেশ কয়েকটি অঞ্চলে রুশদের অগ্রযাত্রা থামাতে তাদের সেনারা বেশ বেগ পেতে হচ্ছে।
প্রস্তাবিত চুক্তির শর্তগুলোর মধ্যে রয়েছে—ইউক্রেনকে দনবাস অঞ্চলের যেসব অংশ এখনো রাশিয়ার দখলে যায়নি, সেখান থেকে সেনা সরাতে হবে। ওই এলাকা একটি নিরপেক্ষ নিরস্ত্রীকরণ অঞ্চল হবে, তবে আন্তর্জাতিকভাবে তা রাশিয়ার ভূখণ্ড হিসেবে স্বীকৃত হবে। একই সঙ্গে ক্রিমিয়া উপদ্বীপ এবং দোনেৎস্ক ও লুহানস্ক পিপলস রিপাবলিকস, যা ২০১৪ সাল থেকে রাশিয়া বা রুশ-সমর্থিতদের নিয়ন্ত্রণে, সেগুলোকে রাশিয়ার অংশ হিসেবে মেনে নিতে হবে। ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর সংখ্যা ৬ লাখের মধ্যে সীমিত রাখতে হবে এবং ইউক্রেনকে ন্যাটোতে যোগদানের সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে হবে, তবে ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।
এর বিনিময়ে, রাশিয়াকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে তারা আর কোনো ইউরোপীয় দেশ আক্রমণ করবে না এবং এই প্রতিশ্রুতি তাদের আইনে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এ ছাড়া, যুদ্ধাপরাধের জন্য সাধারণ ক্ষমার প্রস্তাবও আছে। গত সপ্তাহে পুতিন স্বীকার করেন যে এই পরিকল্পনা ‘ভবিষ্যতের চুক্তির ভিত্তি হতে পারে।’ তবে তিনি যোগ করেন, ‘যদি ইউক্রেনীয় সৈন্যরা তাদের দখল করা এলাকাগুলো ছেড়ে যায়, তবে আমরা যুদ্ধ থামাব। যদি না যায়, তবে আমরা সামরিকভাবেই আমাদের লক্ষ্য পূরণ করব।’
সূত্র মারফত জানা যায়, গত সপ্তাহান্তে ইউক্রেনীয় মধ্যস্থতাকারীরা তাদের আমেরিকান প্রতিপক্ষকে আবারও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে—কোনো ভূখণ্ড ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্নই আসে না।
ওয়াশিংটন ডিসিতে বসবাসকারী রুশ অর্থনীতিবিদ ভ্লাদিস্লাভ ইনোজেমতসেভ বলেন, ‘পুতিন ভালোভাবেই জানেন যে ইউক্রেনের হাতে সময় ফুরিয়ে আসছে। তাই, পুতিন সবকিছু নিয়ে খুব আত্মবিশ্বাসী। তাঁর হাতে সময় আছে। তিনি এক বা দুই বছর ধরে লড়তে পারেন। সমস্যাটা বরং পশ্চিমের (এবং তাদের লড়াইয়ের ইচ্ছার)। তাই, হ্যাঁ, তিনি দেরি করতে প্রস্তুত—ইউক্রেন ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দেওয়া পর্যন্ত নয়, বরং তার শর্তগুলো পূরণ হওয়া পর্যন্ত।’
মঙ্গলবার বৈঠকের আগে, পুতিন ইউরোপকে হুমকি দিয়ে আরও এক ধাপ এগিয়ে যান। তিনি সতর্ক করে দেন যে রাশিয়া ইউরোপের সঙ্গে যুদ্ধের পরিকল্পনা করছে না, ‘তবে ইউরোপ যদি চায় এবং শুরু করে, আমরা এই মুহূর্তেই প্রস্তুত।’
বুদ্রাইৎস্কিস বলেন, ‘পুতিন এর জন্যই প্রস্তুতি নেবেন, ঠিক যেমন ২০২২ সালের আগে তিনি বলেছিলেন যে—রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করতে যাচ্ছে না, যা বিপরীতটাই ইঙ্গিত করেছিল।’ দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা থাকার পরও ইনোজেমতসেভ এবং বারানভস্কি দুজনেই একমত যে রাশিয়া অনির্দিষ্টকাল ধরে তাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম। ইনোজেমতসেভ বলেন, ‘এতটা তীব্রতায় বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া মোটেও কোনো সমস্যা নয়।’
তাঁর ভাষায়, ‘যুদ্ধের শুরুতে যত সমস্যা ছিল, এখন তার চেয়ে কম। কারণ, শুরুতে আমরা দেখেছি তাদের লোক জড়ো করতে হয়েছিল; এখন তারা বেশ ভালো বেতন দেয় এবং (নতুন স্বেচ্ছাসেবকেরা) ক্রমাগত তালিকাভুক্ত হচ্ছে। এ ছাড়া, তাদের অস্ত্রের সমস্যা ছিল এবং ভাষ্যকাররা লিখেছিলেন যে তিন মাসের মধ্যে তাদের শেল ফুরিয়ে যাবে। বাস্তবে, এখন যুদ্ধের আগের চেয়েও বেশি সক্রিয়ভাবে অস্ত্র উৎপাদন হচ্ছে।’
ইনোজেমতসেভ মনে করেন, এখন ‘আমেরিকানরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে—হয় এই যুদ্ধ শেষ করতে হবে, না হয় ইউক্রেনের প্রতি সব রকম সমর্থন সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করতে হবে।’ তিনি বলেন, ‘আমার মনে হয় এই বার্তা এখন কিয়েভকে স্পষ্টভাবে দেওয়া হয়েছে। আর তাই, ইউক্রেনীয়দের কোনো না কোনোভাবে রাজি করানো হবে...ইউক্রেনীয়রা জানে যে ইউরোপ তাদের রক্ষা করতে পারবে না। অর্থাৎ, যদি এখন আমেরিকানরা এই প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে সরে দাঁড়ায়, তবে ইউরোপের কাছে বছরের পর বছর ধরে এই কারণকে সমর্থন করার মতো অর্থ বা সংকল্প কোনোটাই থাকবে না।’
ইনোজেমতসেভ উল্লেখ করেন, একটি চুক্তি হলেও তা ইউক্রেনের স্বার্থে আসতে পারে। তিনি বলেন, ‘যদি তারা নিজেদের সেনাবাহিনীর জন্য ৬ লাখ সৈন্য এবং অন্তত কয়েক বছরের জন্য একটি বিরতি নিশ্চিত করতে পারে, তবে বাস্তবে এটিই সমস্যার সমাধান।’ তিনি বলেন, ‘পুতিন সব সময়ই একটি হুমকি হয়ে থাকবেন এবং তাই পশ্চিমের প্রধান কাজ হলো (৭৩ বছর বয়সী) পুতিনকে উতরে যাওয়া। যদি তিন থেকে পাঁচ বছরের জন্য লড়াইয়ে বিরতি আসে, তবে এটি তার জীবনের শেষের দিকে পৌঁছে যাবে, যা স্বভাবতই তাঁকে কম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করবে।’
এ ছাড়া, যেকোনো সম্ভাব্য শান্তি চুক্তি এবং নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার রুশ অর্থনীতির জন্য উপকারী হবে। তবে ইনোজেমতসেভ ও বুদ্রাইৎস্কিস সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, জীবন ২০২২ সালের আগের মতো স্বাভাবিক হবে। তাঁদের অনুমান, সমাজ প্রবলভাবে সামরিক এবং কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত থাকবে। বুদ্রাইৎস্কিস বলেন, ‘শান্তি আসতে পারে না। এমন এক স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও ফেরা সম্ভব নয় যেখানে পূর্ণাঙ্গ দমনমূলক সর্বাত্মক একনায়কতন্ত্রের উপযোগী এই সমস্ত ব্যবস্থা তুলে নেওয়া হবে, কারণ আমাদের আর কোনো সরাসরি বাহ্যিক হুমকি নেই।’
তাঁর মতে, ‘এটাই রাশিয়ার পুতিন রেজিমের নকশা। তাঁর ক্ষমতা এভাবেই সাজানো হয়েছে যে, এখানে এক অন্তহীন যুদ্ধ চলবে, যেখানে রুশ অভিজাতরা পতাকার নিচে একত্রিত থাকবে, দেশের অভ্যন্তরে যে কোনো ভিন্নমতের বিরুদ্ধে দমন-পীড়ন চলবে...এগুলো কেবল সাময়িকভাবে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে চালু করা কিছু অসাধারণ ব্যবস্থা নয়, বরং এভাবেই তিনি শাসন চালিয়ে যাবেন।’
তিনি আরও যোগ করেন, ইউক্রেন, ইউরোপ, বাল্টিক রাষ্ট্র বা ‘যে কারও বিরুদ্ধে যেকোনো রূপে যুদ্ধ’ হলো পুতিন ২০২২ সালের পরে রাশিয়ায় যে ‘স্বাভাবিকতা’ প্রতিষ্ঠা করেছেন, তার অবিচ্ছেদ্য চালিকাশক্তি। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন, ‘সুতরাং, এই রেজিম টিকে থাকার জন্য বিভিন্ন ফ্রন্টে যুদ্ধ চলতে থাকবে।’
কিছু রুশ নাগরিক ইতিমধ্যেই দীর্ঘস্থায়ী পরিস্থিতির জন্য নিজেদের মানিয়ে নিয়েছেন। মস্কোর গণমাধ্যম সের্গেই কালেনিক বলেন, ‘আমেরিকা যত দিন ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে তাদের দখলদার সৈন্য প্রত্যাহার না করবে, তত দিন যুদ্ধ শেষ হবে না।’
আল–জাজিরা থেকে অনুবাদ করেছেন আব্দুর রহমান
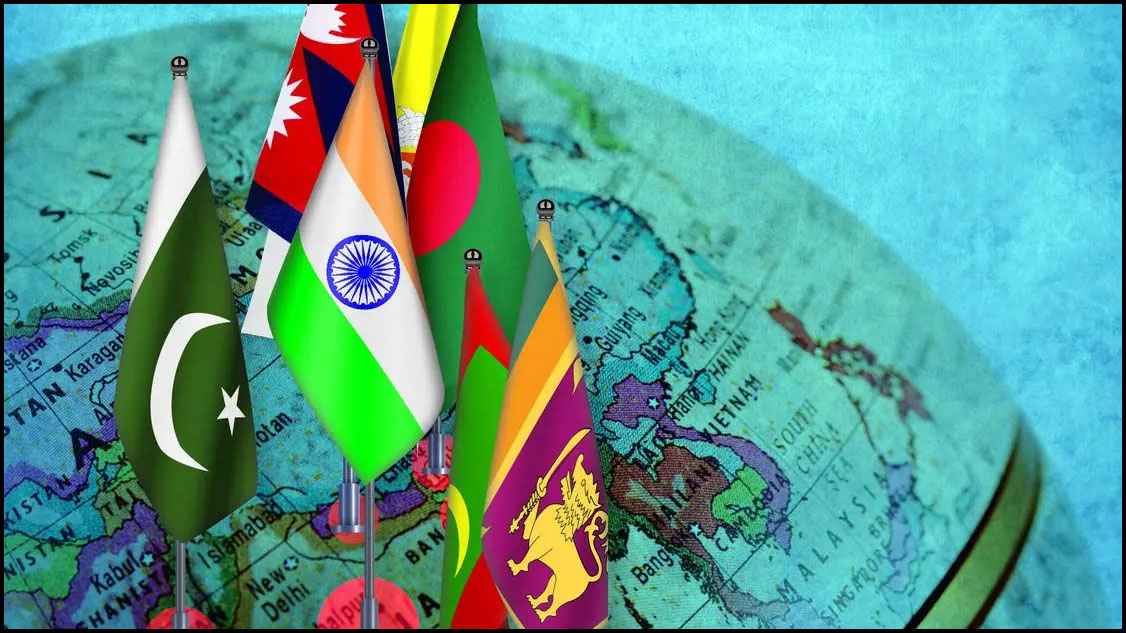
দক্ষিণ এশিয়া এখন সার্বভৌম ঋণ তথা সরকারের ঋণ ও রাজস্ব ঘাটতির ভারসাম্য রক্ষায় হিমশিম খাচ্ছে। স্থায়ী বাজেট ঘাটতির কারণে এ অঞ্চলের ঋণ বিশ্বের অন্যান্য উদীয়মান অর্থনীতির তুলনায় দ্রুত বেড়ে গেছে। ২০২৩ সালে সরকারগুলোর গড় ঋণের পরিমাণ পৌঁছেছে মোট জিডিপির ৭৭ শতাংশে।
১৯ অক্টোবর ২০২৫
সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে ভেনেজুয়েলায় মাদক পাচারের অভিযোগে অন্তত ২১টি নৌযানে মার্কিন সামরিক বাহিনী হামলা চালিয়েছে, যাতে অন্তত ৮৭ জন নিহত হয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসন দাবি করছে, এসব নৌকা যুক্তরাষ্ট্রে বিপুল পরিমাণ মাদক পাচার করছিল এবং তা মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি।
১৩ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ইসহাক দার জানিয়েছেন, বাংলাদেশ, চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্প্রতি যে ত্রিপক্ষীয় উদ্যোগ শুরু হয়েছে, তা অন্য আঞ্চলিক দেশ এবং এর বাইরেও ‘বিস্তৃত’ হতে পারে। তিনি গত বুধবার ইসলামাবাদ কনক্লেভ ফোরামে বলেন, ‘আমরা শূন্য-সমষ্টিগত পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছি এবং সংঘাতের বদলে সহযোগিতার
২০ ঘণ্টা আগে
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতদের মধ্যে ইউক্রেন শান্তি চুক্তি নিয়ে আলোচনা হলেও প্রকাশ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। পুতিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ইউরি উশাকভ, এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে অমীমাংসিত ‘আঞ্চলিক সমস্যাই’ মূল বাধা। আর এই অঞ্চল আর কোনোটিই নয়, দোনেৎস্ক।
২ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতদের মধ্যে ইউক্রেন শান্তি চুক্তি নিয়ে আলোচনা হলেও প্রকাশ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। পুতিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ইউরি উশাকভ, এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে অমীমাংসিত ‘আঞ্চলিক সমস্যাই’ মূল বাধা। আর এই অঞ্চল আর কোনোটিই নয়, দোনেৎস্ক।
উশাকভ মূলত ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় দোনেৎস্কের সম্পূর্ণ এলাকার ওপর রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণ দাবির কথাই বলেছিলেন। পুতিন ইউক্রেনে হাজার হাজার সৈন্য পাঠানোর প্রায় ৪ বছর পরও এবং দোনেৎস্কে রাশিয়া সমর্থিত বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহের এক দশকেরও বেশি সময় পর অঞ্চলটির কিছু অংশ এখনো ইউক্রেনের হাতে আছে।
প্রায় সব দেশই দোনেৎস্ককে ইউক্রেনের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু এটি ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলের চারটি অঞ্চলের মধ্যে একটি, যা মস্কো ২০২২ সালে একটি গণভোটের পর সংযুক্ত করার কথা ঘোষণা করে। কিয়েভ ও পশ্চিমা দেশগুলো সেই গণভোটকে ‘প্রহসন’ বলে বাতিল করে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও ফক্স নিউজকে বলেছিলেন, যুদ্ধটি এখন দোনেৎস্কের সেই ২০ শতাংশ বা ৫ হাজার বর্গকিলোমিটারের এলাকা নিয়ে, যা রাশিয়া নিয়ন্ত্রণ করে না কিন্তু চায়।
পুতিন ২০২২ সালে ইউক্রেনে সৈন্য পাঠানোর সময় বলেছিলেন, তাঁর লক্ষ্য হলো ‘গত আট বছর ধরে যারা ভয়ভীতি ও গণহত্যার শিকার হয়েছেন...সেই মানুষগুলোকে রক্ষা করা।’ ইউক্রেন এবং তার মিত্ররা বলেছিল, পুতিনের এই দাবি ঔপনিবেশিক ধাঁচের এবং এলাকা দখলের জন্য একটি মিথ্যা অজুহাত মাত্র।
পুতিনের এই দাবি মূলত দোনেৎস্ক এবং লুহানস্ক অঞ্চলে রাশিয়া সমর্থিত বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে ইউক্রেনের লড়াইয়ের দিকে ইঙ্গিত করে, যারা ২০১৪ সালে ইউক্রেনীয় সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিছু এলাকা দখল করেছিল। পূর্ব ইউক্রেনে এর পরের সংঘর্ষে উভয় পক্ষই শহর ও বেসামরিক নাগরিকদের ওপর গোলাবর্ষণের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ করেছিল। মস্কো এই অঞ্চলের বিশাল রুশভাষী জনসংখ্যাকে উদ্ধৃত করে বলেছিল যে,২০২২ সালে হস্তক্ষেপ করা তাদের নৈতিক কর্তব্য।
কিয়েভ বলেছিল, ২০১৪ সালে ইউক্রেনের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায় শক্তি দিয়ে জবাব দেওয়া ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় ছিল না এবং তারাও বিচ্ছিন্নতাবাদী বাহিনীর বিরুদ্ধে শহর ও বেসামরিক নাগরিকদের ওপর গোলাবর্ষণের অভিযোগ এনেছিল। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, ২০১৪ সাল থেকে ২০২২ সালের শুরু পর্যন্ত ইউক্রেনীয় সরকারি বাহিনী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মধ্যে সংঘাতে উভয় পক্ষে ৩ হাজার ১০৬ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং ৯ হাজার বেসামরিক নাগরিক আহত হয়েছিলেন।
দোনেৎস্কের বাকি যে অংশটি রাশিয়া চায়, তার মধ্যে রয়েছে স্লোভিয়ানস্ক এবং ক্রামাতোরস্ক—দুটি ‘দুর্গনগরী’ যা ২০১৪ সাল থেকে ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। এই শহরগুলো ইউক্রেনের বাকি অঞ্চল রক্ষার জন্য কিয়েভের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দোনেৎস্কের পশ্চিমের ভূমি অনেকটাই সমতল এবং বিশাল খোলা মাঠ; যা রাশিয়াকে দোনেৎস্কের বাইরে অগ্রসর হতে এবং দিনিপ্রো নদীর পূর্ব তীর পর্যন্ত এলাকা দখল করার পথ সহজ করে দেবে।
শহরগুলো পরিখা, ট্যাংক-বিধ্বংসী বাধা, বাংকার এবং মাইনক্ষেত্রসহ অত্যন্ত সুরক্ষিত প্রতিরক্ষা লাইনের অংশ। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, গণভোট ছাড়া দোনেৎস্কের বাকি অংশ রাশিয়ার হাতে তুলে দেওয়া অবৈধ হবে এবং তা ভবিষ্যতে ইউক্রেনের গভীরে আক্রমণের জন্য রাশিয়াকে একটি পথ খুলে দেবে।
কিয়েভের আশঙ্কা, যদি তারা দোনেৎস্কের বাকি অংশ ছেড়ে দেয়, তবে রাশিয়া আবার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হবে এবং একসময় দোনেৎস্ক ব্যবহার করে পশ্চিম দিকে আক্রমণ চালাবে।
উভয় পক্ষই দোনেৎস্ককে কেন্দ্র করে যুদ্ধে ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছে এবং প্রচুর অর্থ ও সরঞ্জাম ব্যয় করেছে। এর মধ্যে বাখমুত শহরের লড়াইও রয়েছে। যেখানে রাশিয়া হাজার হাজার দণ্ডিত অপরাধীকে ভাড়াটে সৈন্যে পরিণত করে রণক্ষেত্রে নামিয়েছিল। এ কারণে, দোনেৎস্ক উভয় দেশের জনমানসে আরও বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। ফলে কারও পক্ষে তাদের অবস্থান পরিবর্তন করা কঠিন।
ইউক্রেন চায় না যে, রাশিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে জয় করতে ব্যর্থ হওয়া ভূখণ্ডকে উপহার হিসেবে পাক এবং জেলেনস্কি বলেছেন, যে যুদ্ধ রাশিয়া শুরু করেছে, তার জন্য তাদের পুরস্কৃত করা উচিত নয়। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ইনস্টিটিউট ফর দ্য স্টাডি অব ওয়ার অক্টোবর মাসে বলেছিল, রাশিয়ার অগ্রগতির হার দেখে মনে হয় না যে তারা খুব শিগগিরই দোনেৎস্কের বাকি অংশ দখল করতে চলেছে। তবে ‘রাশিয়ার অগ্রগতির একটি অপরিবর্তনীয় হার ধরে নিলে’ তারা ২০২৭ সালের আগস্টের মধ্যে তা নিতে পারে।
রাশিয়ার কমান্ডাররা অবশ্য আরও বেশি আশাবাদী। জেনারেল স্টাফের প্রধান ভ্যালেরি গেরাসিমভ রোববার পুতিনকে বলেছেন, মস্কোর বাহিনী পুরো ফ্রন্ট লাইন বরাবর অগ্রসর হচ্ছে এবং দনবাসের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য কাজ করছে।
দোনেৎস্ক বন্দর, রেলপথ এবং অন্যান্য ভারী শিল্পের কেন্দ্র। এটি একসময় ইউক্রেনের কয়লা, পরিশোধিত ইস্পাত, কোক, ঢালাই লোহা এবং ইস্পাত উৎপাদনের অর্ধেকেরও বেশি সরবরাহ করত, তবে যুদ্ধের কারণে অনেক খনি ও কারখানা ধ্বংস হয়ে গেছে। এ ছাড়া, দোনেৎস্কে বিরল মৃত্তিকা, টাইটানিয়াম এবং জিরকোনিয়াম রয়েছে—যা এটিকে নিয়ন্ত্রণকারী পক্ষের জন্য আয়ের উৎস।
দোনেৎস্কের ভাগ্য পুতিন এবং জেলেনস্কি উভয়ের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারকে প্রভাবিত করতে পারে। পুতিন নিজেকে জাতিগত রুশদের রক্ষক হিসেবে তুলে ধরেছেন, তারা যেখানেই থাকুক না কেন। পুরো দোনেৎস্ককে সুরক্ষিত করা এই বক্তব্যের মূল কেন্দ্রবিন্দু। জেলেনস্কি ২০১৯ সালে পূর্ব ইউক্রেনের যুদ্ধ অবসান ঘটানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন। ২০২২ সাল থেকে তিনি অনেক বড়, বৈরী প্রতিবেশীর মুখে অস্ত্র এবং সংখ্যায় কম ইউক্রেনের এক দৃঢ় রক্ষক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন।
লড়াই না করে দোনেৎস্ক ছেড়ে দেওয়া—যেখানে অন্তত আড়াই লাখ ইউক্রেনীয় বাস করে—ইউক্রেনীয়দের কাছে বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে দেখা হতে পারে, যাদের অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে স্বজন হারিয়েছেন। কিয়েভ ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সোসিওলজির সাম্প্রতিক এক জরিপ অনুসারে, ইউক্রেনীয়দের একটি সংকীর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এখনো আঞ্চলিক ছাড়ের বিরোধিতা করে।
জেলেনস্কিসহ ইউক্রেনের কর্মকর্তারা যেকোনো শান্তি চুক্তির অধীনে কিয়েভের নিয়ন্ত্রণে থাকা ভূমি ছাড়ার সম্ভাবনা প্রত্যাখ্যান করেছেন। জেলেনস্কি বলেন, তাঁর ভূখণ্ড ছেড়ে দেওয়ার কোনো ম্যান্ডেট নেই এবং রাষ্ট্রের ভূমি ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতো কেনা-বেচা করা যায় না। ইউক্রেনের সংবিধান অনুসারে, আঞ্চলিক পরিবর্তন অবশ্যই একটি গণভোটের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে, যা ইউক্রেনের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ, অন্তত ৩০ লাখ ইউক্রেনীয় ভোটারের স্বাক্ষর থাকলে আয়োজন করা যেতে পারে।
তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই গণভোটের বিষয়টির সমালোচনা করেছেন এবং তিনি বলেছিলেন, ‘কিছু ভূমি অদল-বদল হবে।’ এখন ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের আলোচনা মূলত এই দোনেৎস্কের নিয়ন্ত্রণ কার হাতে যাবে সেটাই নিয়েই থমকে আছে।
রয়টার্স থেকে পরিমার্জিত

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতদের মধ্যে ইউক্রেন শান্তি চুক্তি নিয়ে আলোচনা হলেও প্রকাশ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। পুতিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ইউরি উশাকভ, এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে অমীমাংসিত ‘আঞ্চলিক সমস্যাই’ মূল বাধা। আর এই অঞ্চল আর কোনোটিই নয়, দোনেৎস্ক।
উশাকভ মূলত ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় দোনেৎস্কের সম্পূর্ণ এলাকার ওপর রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণ দাবির কথাই বলেছিলেন। পুতিন ইউক্রেনে হাজার হাজার সৈন্য পাঠানোর প্রায় ৪ বছর পরও এবং দোনেৎস্কে রাশিয়া সমর্থিত বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহের এক দশকেরও বেশি সময় পর অঞ্চলটির কিছু অংশ এখনো ইউক্রেনের হাতে আছে।
প্রায় সব দেশই দোনেৎস্ককে ইউক্রেনের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু এটি ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলের চারটি অঞ্চলের মধ্যে একটি, যা মস্কো ২০২২ সালে একটি গণভোটের পর সংযুক্ত করার কথা ঘোষণা করে। কিয়েভ ও পশ্চিমা দেশগুলো সেই গণভোটকে ‘প্রহসন’ বলে বাতিল করে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও ফক্স নিউজকে বলেছিলেন, যুদ্ধটি এখন দোনেৎস্কের সেই ২০ শতাংশ বা ৫ হাজার বর্গকিলোমিটারের এলাকা নিয়ে, যা রাশিয়া নিয়ন্ত্রণ করে না কিন্তু চায়।
পুতিন ২০২২ সালে ইউক্রেনে সৈন্য পাঠানোর সময় বলেছিলেন, তাঁর লক্ষ্য হলো ‘গত আট বছর ধরে যারা ভয়ভীতি ও গণহত্যার শিকার হয়েছেন...সেই মানুষগুলোকে রক্ষা করা।’ ইউক্রেন এবং তার মিত্ররা বলেছিল, পুতিনের এই দাবি ঔপনিবেশিক ধাঁচের এবং এলাকা দখলের জন্য একটি মিথ্যা অজুহাত মাত্র।
পুতিনের এই দাবি মূলত দোনেৎস্ক এবং লুহানস্ক অঞ্চলে রাশিয়া সমর্থিত বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে ইউক্রেনের লড়াইয়ের দিকে ইঙ্গিত করে, যারা ২০১৪ সালে ইউক্রেনীয় সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিছু এলাকা দখল করেছিল। পূর্ব ইউক্রেনে এর পরের সংঘর্ষে উভয় পক্ষই শহর ও বেসামরিক নাগরিকদের ওপর গোলাবর্ষণের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ করেছিল। মস্কো এই অঞ্চলের বিশাল রুশভাষী জনসংখ্যাকে উদ্ধৃত করে বলেছিল যে,২০২২ সালে হস্তক্ষেপ করা তাদের নৈতিক কর্তব্য।
কিয়েভ বলেছিল, ২০১৪ সালে ইউক্রেনের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায় শক্তি দিয়ে জবাব দেওয়া ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় ছিল না এবং তারাও বিচ্ছিন্নতাবাদী বাহিনীর বিরুদ্ধে শহর ও বেসামরিক নাগরিকদের ওপর গোলাবর্ষণের অভিযোগ এনেছিল। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, ২০১৪ সাল থেকে ২০২২ সালের শুরু পর্যন্ত ইউক্রেনীয় সরকারি বাহিনী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মধ্যে সংঘাতে উভয় পক্ষে ৩ হাজার ১০৬ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং ৯ হাজার বেসামরিক নাগরিক আহত হয়েছিলেন।
দোনেৎস্কের বাকি যে অংশটি রাশিয়া চায়, তার মধ্যে রয়েছে স্লোভিয়ানস্ক এবং ক্রামাতোরস্ক—দুটি ‘দুর্গনগরী’ যা ২০১৪ সাল থেকে ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। এই শহরগুলো ইউক্রেনের বাকি অঞ্চল রক্ষার জন্য কিয়েভের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দোনেৎস্কের পশ্চিমের ভূমি অনেকটাই সমতল এবং বিশাল খোলা মাঠ; যা রাশিয়াকে দোনেৎস্কের বাইরে অগ্রসর হতে এবং দিনিপ্রো নদীর পূর্ব তীর পর্যন্ত এলাকা দখল করার পথ সহজ করে দেবে।
শহরগুলো পরিখা, ট্যাংক-বিধ্বংসী বাধা, বাংকার এবং মাইনক্ষেত্রসহ অত্যন্ত সুরক্ষিত প্রতিরক্ষা লাইনের অংশ। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, গণভোট ছাড়া দোনেৎস্কের বাকি অংশ রাশিয়ার হাতে তুলে দেওয়া অবৈধ হবে এবং তা ভবিষ্যতে ইউক্রেনের গভীরে আক্রমণের জন্য রাশিয়াকে একটি পথ খুলে দেবে।
কিয়েভের আশঙ্কা, যদি তারা দোনেৎস্কের বাকি অংশ ছেড়ে দেয়, তবে রাশিয়া আবার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হবে এবং একসময় দোনেৎস্ক ব্যবহার করে পশ্চিম দিকে আক্রমণ চালাবে।
উভয় পক্ষই দোনেৎস্ককে কেন্দ্র করে যুদ্ধে ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছে এবং প্রচুর অর্থ ও সরঞ্জাম ব্যয় করেছে। এর মধ্যে বাখমুত শহরের লড়াইও রয়েছে। যেখানে রাশিয়া হাজার হাজার দণ্ডিত অপরাধীকে ভাড়াটে সৈন্যে পরিণত করে রণক্ষেত্রে নামিয়েছিল। এ কারণে, দোনেৎস্ক উভয় দেশের জনমানসে আরও বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। ফলে কারও পক্ষে তাদের অবস্থান পরিবর্তন করা কঠিন।
ইউক্রেন চায় না যে, রাশিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে জয় করতে ব্যর্থ হওয়া ভূখণ্ডকে উপহার হিসেবে পাক এবং জেলেনস্কি বলেছেন, যে যুদ্ধ রাশিয়া শুরু করেছে, তার জন্য তাদের পুরস্কৃত করা উচিত নয়। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ইনস্টিটিউট ফর দ্য স্টাডি অব ওয়ার অক্টোবর মাসে বলেছিল, রাশিয়ার অগ্রগতির হার দেখে মনে হয় না যে তারা খুব শিগগিরই দোনেৎস্কের বাকি অংশ দখল করতে চলেছে। তবে ‘রাশিয়ার অগ্রগতির একটি অপরিবর্তনীয় হার ধরে নিলে’ তারা ২০২৭ সালের আগস্টের মধ্যে তা নিতে পারে।
রাশিয়ার কমান্ডাররা অবশ্য আরও বেশি আশাবাদী। জেনারেল স্টাফের প্রধান ভ্যালেরি গেরাসিমভ রোববার পুতিনকে বলেছেন, মস্কোর বাহিনী পুরো ফ্রন্ট লাইন বরাবর অগ্রসর হচ্ছে এবং দনবাসের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য কাজ করছে।
দোনেৎস্ক বন্দর, রেলপথ এবং অন্যান্য ভারী শিল্পের কেন্দ্র। এটি একসময় ইউক্রেনের কয়লা, পরিশোধিত ইস্পাত, কোক, ঢালাই লোহা এবং ইস্পাত উৎপাদনের অর্ধেকেরও বেশি সরবরাহ করত, তবে যুদ্ধের কারণে অনেক খনি ও কারখানা ধ্বংস হয়ে গেছে। এ ছাড়া, দোনেৎস্কে বিরল মৃত্তিকা, টাইটানিয়াম এবং জিরকোনিয়াম রয়েছে—যা এটিকে নিয়ন্ত্রণকারী পক্ষের জন্য আয়ের উৎস।
দোনেৎস্কের ভাগ্য পুতিন এবং জেলেনস্কি উভয়ের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারকে প্রভাবিত করতে পারে। পুতিন নিজেকে জাতিগত রুশদের রক্ষক হিসেবে তুলে ধরেছেন, তারা যেখানেই থাকুক না কেন। পুরো দোনেৎস্ককে সুরক্ষিত করা এই বক্তব্যের মূল কেন্দ্রবিন্দু। জেলেনস্কি ২০১৯ সালে পূর্ব ইউক্রেনের যুদ্ধ অবসান ঘটানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন। ২০২২ সাল থেকে তিনি অনেক বড়, বৈরী প্রতিবেশীর মুখে অস্ত্র এবং সংখ্যায় কম ইউক্রেনের এক দৃঢ় রক্ষক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন।
লড়াই না করে দোনেৎস্ক ছেড়ে দেওয়া—যেখানে অন্তত আড়াই লাখ ইউক্রেনীয় বাস করে—ইউক্রেনীয়দের কাছে বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে দেখা হতে পারে, যাদের অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে স্বজন হারিয়েছেন। কিয়েভ ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সোসিওলজির সাম্প্রতিক এক জরিপ অনুসারে, ইউক্রেনীয়দের একটি সংকীর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এখনো আঞ্চলিক ছাড়ের বিরোধিতা করে।
জেলেনস্কিসহ ইউক্রেনের কর্মকর্তারা যেকোনো শান্তি চুক্তির অধীনে কিয়েভের নিয়ন্ত্রণে থাকা ভূমি ছাড়ার সম্ভাবনা প্রত্যাখ্যান করেছেন। জেলেনস্কি বলেন, তাঁর ভূখণ্ড ছেড়ে দেওয়ার কোনো ম্যান্ডেট নেই এবং রাষ্ট্রের ভূমি ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতো কেনা-বেচা করা যায় না। ইউক্রেনের সংবিধান অনুসারে, আঞ্চলিক পরিবর্তন অবশ্যই একটি গণভোটের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে, যা ইউক্রেনের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ, অন্তত ৩০ লাখ ইউক্রেনীয় ভোটারের স্বাক্ষর থাকলে আয়োজন করা যেতে পারে।
তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই গণভোটের বিষয়টির সমালোচনা করেছেন এবং তিনি বলেছিলেন, ‘কিছু ভূমি অদল-বদল হবে।’ এখন ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের আলোচনা মূলত এই দোনেৎস্কের নিয়ন্ত্রণ কার হাতে যাবে সেটাই নিয়েই থমকে আছে।
রয়টার্স থেকে পরিমার্জিত
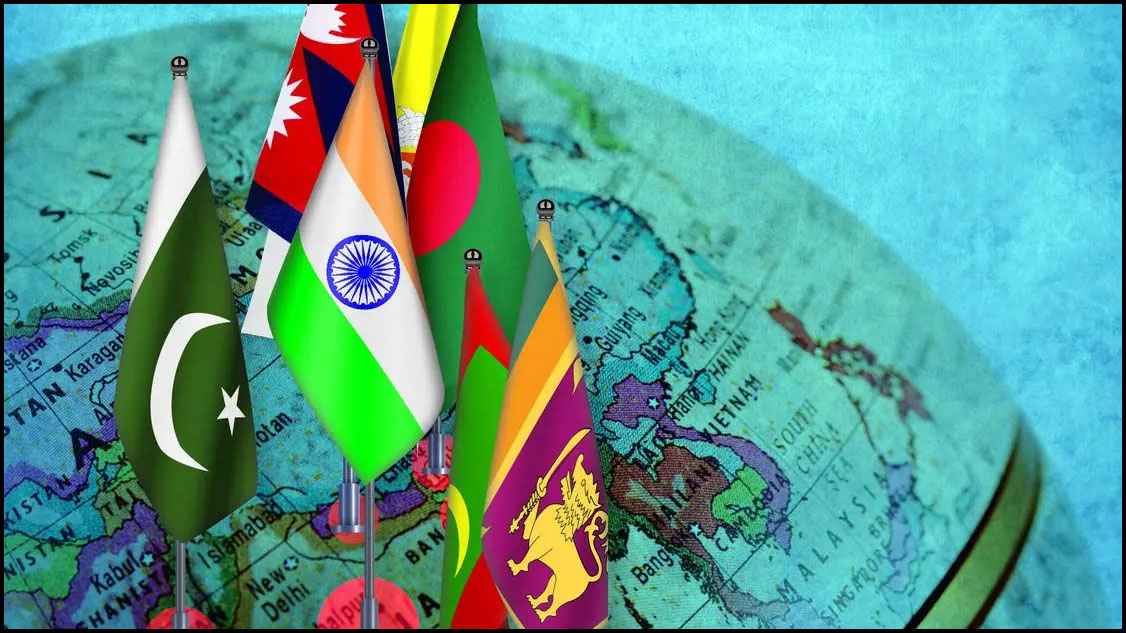
দক্ষিণ এশিয়া এখন সার্বভৌম ঋণ তথা সরকারের ঋণ ও রাজস্ব ঘাটতির ভারসাম্য রক্ষায় হিমশিম খাচ্ছে। স্থায়ী বাজেট ঘাটতির কারণে এ অঞ্চলের ঋণ বিশ্বের অন্যান্য উদীয়মান অর্থনীতির তুলনায় দ্রুত বেড়ে গেছে। ২০২৩ সালে সরকারগুলোর গড় ঋণের পরিমাণ পৌঁছেছে মোট জিডিপির ৭৭ শতাংশে।
১৯ অক্টোবর ২০২৫
সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে ভেনেজুয়েলায় মাদক পাচারের অভিযোগে অন্তত ২১টি নৌযানে মার্কিন সামরিক বাহিনী হামলা চালিয়েছে, যাতে অন্তত ৮৭ জন নিহত হয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসন দাবি করছে, এসব নৌকা যুক্তরাষ্ট্রে বিপুল পরিমাণ মাদক পাচার করছিল এবং তা মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি।
১৩ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ইসহাক দার জানিয়েছেন, বাংলাদেশ, চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্প্রতি যে ত্রিপক্ষীয় উদ্যোগ শুরু হয়েছে, তা অন্য আঞ্চলিক দেশ এবং এর বাইরেও ‘বিস্তৃত’ হতে পারে। তিনি গত বুধবার ইসলামাবাদ কনক্লেভ ফোরামে বলেন, ‘আমরা শূন্য-সমষ্টিগত পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছি এবং সংঘাতের বদলে সহযোগিতার
২০ ঘণ্টা আগে
ভ্লাদিস্লাভ ইনোজেমতসেভ বলেন, ‘পুতিন ভালোভাবেই জানেন যে ইউক্রেনের হাতে সময় ফুরিয়ে আসছে। তাই, পুতিন সবকিছু নিয়ে খুব আত্মবিশ্বাসী। তাঁর হাতে সময় আছে। তিনি এক বা দুই বছর ধরে লড়তে পারেন। সমস্যাটা বরং পশ্চিমের (এবং তাদের লড়াইয়ের ইচ্ছার)। তাই, হ্যাঁ, তিনি দেরি করতে প্রস্তুত—ইউক্রেন ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দেও
২১ ঘণ্টা আগে