মোহাম্মদ ইদ্রিস

১৯২০-এর দশকের কোনো এক দিন। ড্যান্ডি শহরের কোনো এক জুট মিলের মালিক মাথায় সোলার হ্যাট পরে আমাদের ফরিদপুর শহরের পাটের বাজার দেখতে এসেছিলেন, দাদার মুখে সে গল্প শুনেছি।
সে ঘটনার প্রায় ১০২ বছর পর অবশেষে দেখলাম স্কটল্যান্ডের ড্যান্ডি শহরে বিশ্বের প্রথম জুটমিল। মিল ঠিক নয়, জুট মিউজিয়াম। পাট উৎপন্ন করত বাংলার কৃষক, আর সব পাটকল ছিল স্কটল্যান্ডে। সহজ বাংলা ভাষায় এরই নাম ছিল সাম্রাজ্যবাদ।
ভারডান্ট ওয়ার্কস মিউজিয়াম
‘গতস্য শোচনা নাস্তি’ অতি পুরোনো সংস্কৃত শ্লোক। তবুও বয়স্কা নর্তকী বারবার আয়না দেখে, বিগত যৌবনের সৌন্দর্য খোঁজে। আর বৃদ্ধ মানুষ চোখ বন্ধ করে বিগত যৌবনের সুখ চিন্তা করে। আমাদের এক কালের প্রভুদের অবস্থাও ঠিক তাই। এখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নেই, ড্যান্ডি শহরে জুট মিলও নেই। বন্ধ হয়ে যাওয়া একটা জুট মিলকে মিউজিয়াম বানিয়ে স্কটিশেরা পুরোনো শৌর্য ও ঐশ্বর্য মনে রাখার চেষ্টা করছে।
১৯৫৪ সালে হক-ভাসানি মুসলিম লীগকে ডুবিয়ে দিয়ে যেদিন সরকার গঠনের শপথ নিচ্ছিল, ঠিক সেই দিন নারায়ণগঞ্জের পাটকলে বিহারি আর বাঙালি শ্রমিকদের মধ্য রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা বাঁধিয়ে মুসলিম লীগের গুন্ডারা গণপ্রতিনিধিত্বের সরকারকে খাটো করবার চেষ্টা করেছিল। সে কথা ইতিহাস বইতে পড়েছি। ‘আমরা পাট রপ্তানি করে যে পরিমাণ বিদেশি টাকা আয় করি, তার বেশির ভাগ টাকা পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে ব্যয় করা হয়’, এই নিয়ে মুসলিম লীগ সমর্থকদের সঙ্গে ঝগড়া করেছি। বাংলার সোনালি আঁশ পাট। স্কুলের পরীক্ষায় ইংরেজি ভাষায় ‘জুট’ রচনা লিখেছি। কিন্তু হাজি আদমজীর ছেলেদের উদ্যোগে তৈরি, দাউদ, বাওয়ানী অথবা খোদ আদমজী জুট মিলটাও কোনো দিন দেখিনি। তাই স্কটল্যান্ডের ড্যান্ডি শহরে বেড়াতে এসে ‘ভারডান্ট ওয়ার্কস’ মিউজিয়াম দেখার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। সুন্দর সাজানো-গোছানো মিউজিয়ামের ভেতর পাটকলে ব্যবহার করা সব যন্ত্রপাতি দেখলাম, আর গাইডের মুখে শুনলাম এক রূপকথার গল্প।
 সোনালি আঁশের উত্থান
সোনালি আঁশের উত্থান
তিসির তেল আমরা বেশ চিনি। বাংলাদেশে তিসি ফলানো হয় মূলত তেলের জন্য। এ তেল কাঠের বার্নিশ উজ্জ্বল করে, আর ক্রিকেট ব্যাটের স্ট্রোক বাড়ায়। তবে মিসর ও জর্জিয়ায় তিসির চাষ করা করা হয় এ উদ্ভিদের ছাল থেকে সুতা তৈরির জন্য। তিসি গাছের ছাল পাটের মতো প্রক্রিয়াজাত করে যে সুতা বানানো হয়, তার ইংরেজি নাম ফ্ল্যাক্স। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ড্যান্ডি শহরে অনেকগুলো ফ্ল্যাক্স মিল ছিল। সেখানে এই সুতা দিয়ে মোটা ক্যানভাস ও লিনেন কাপড় তৈরি করা হতো। ড্যান্ডি শহরে ফ্ল্যাক্স আমদানি করা হতো কৃষ্ণ সাগর পারের ক্রিমিয়া ও জর্জিয়া অঞ্চল থেকে। রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের লড়াইয়ে উনিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে ফ্ল্যাক্সের উৎপাদন এবং সরবরাহ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।
প্রায় একই সময় কলকাতা বন্দরে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিকেরা ফ্ল্যাক্স আঁশের মতো দেখতে বাংলা পাটের প্রতি নজর দেয়। ১৮২০ সালে প্রথমবারের মতো আড়াই মন ওজনের একটি পাটের বেল ড্যান্ডি শহরে এসে পৌঁছায়।
কিন্তু পাটের আঁশ শক্ত। ফলে ফ্ল্যাক্সের বদলে পাট ব্যবহার করা গেল না। অনেক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেল যে, তিমি মাছের তেলে পাট ভেজালে তা নরম হয়, যা ফ্ল্যাক্স মিলে ব্যবহার কর যায়। তায়ে (Tay) নদীর তীরে অবস্থিত ড্যান্ডি নৌবন্দর অনেক আগে থেকেই তিমি মাছ ধরা এবং বেচাকেনার বাজার হিসেবে বিখ্যাত ছিল। সেখানে তিমি মাছের তেল সস্তায় এবং প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। লাভ-ক্ষতির অঙ্ক করতে ব্যাপারীদের বেশি সময় লাগল না। ড্যান্ডি শহরে ডেভিড লিন্ডসে তাঁর ফ্ল্যাক্স মিল ‘ভারডান্ট ওয়ার্কস’-এর কিছু বিবর্তন করে ১৮৩৫ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন বিশ্বের প্রথম জুট মিল বা পাটকল।
শুরু হলো পাটের অগ্রযাত্রা। একে একে ড্যান্ডির ফ্ল্যাক্স মিলগুলো জুট মিলে পরিণত হতে থাকল। ড্যান্ডি ডকইয়ার্ডে তৈরি হতে থাকল বড় বড় জাহাজ। ১৮৬৯ সালে সুয়েজ খাল খুলে গেলে এশিয়া আর ইউরোপের মধ্যে নৌপথের দূরত্ব কমে যায়। ফলে কাঁচা পাট কলকাতা বন্দর থেকে ৯০ দিনে ড্যান্ডি বন্দরে পৌঁছাতে থাকল। সোনায় সোহাগা। নতুন জুট মিল তৈরি হতে থাকল সেখানে। নেহাত বাংলা ঘরের ছনের চালে আটন-ছাটন আর রুয়া-ফুসসির বাঁধনে কাজে লাগা বাংলার পাট বিলেতি জুট মিলের সৌজন্যে হয়ে উঠল আন্তর্জাতিক বেস্ট সেলার এক পণ্য। আমাদের দেশের প্রধান অর্থকরী ফসল, যার নাম হলো সোনালি আঁশ। আর নারায়ণগঞ্জ নৌবন্দর বাংলার ড্যান্ডি নামে বিখ্যাত হলো।
 বাংলার পাট, ড্যান্ডির নারী
বাংলার পাট, ড্যান্ডির নারী
পাট হাটের ফড়িয়া, দালাল, আর পাট গুদামের মালিকদের ব্যাংক ব্যালান্স এবং পেটের ভুঁড়ি দুটোই সমানুপাতিক হারে বাড়তে থাকল। কুষ্টিয়া রেল স্টেশনের পাশে ঠাকুর অ্যান্ড কোম্পানির গুদাম খুলে, ধুতি কাছা দিয়ে পাটের ব্যবসায় নেমে গেলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তবে, কবির নোবেল প্রাইজ পাওয়া জ্ঞানে কাজ হলো না। পাটের ব্যবসা লাটে উঠল। ধনী হলো ড্যান্ডির জুটমিল মালিকেরা। দিনে দিনে, মাসে মাসে সেখানে বাড়তে থাকল পাটকলের সংখ্যা। ১৯০৯ সালে ড্যান্ডি শহরে ছিল ১৩০টি পাটকল। ১৯০১ সালে ড্যান্ডি শহরের মোট ৮৬ হাজার শ্রমিকের অর্ধেক ছিল পাট শ্রমিক। এর পঁচাত্তর ভাগ ছিল নারী।
হাতে চালানো তাঁতের কাজ কষ্টসাধ্য হওয়ায় তাঁত বুননের কাজে প্রথম দিকে নারী শ্রমিক নেওয়া হতো না। কিন্তু বৈদ্যুতিক তাঁত চালু হলে নারীরা পাটকলে কাজ করার উপযুক্ত বিবেচিত হয়। অর্থনৈতিক প্রয়োজন, ঘরের বাঁধন ছিঁড়ে বাইরে যাওয়ার উৎসাহ আর কম বেতনে কাজ করতে রাজি হওয়া বিপুলসংখ্যক নারী শ্রমিক পাটকলে নিয়োগ পেতে থাকে।
ড্যান্ডিতে এক সময় ৪১ হাজার পাটকল শ্রমিকের মধ্যে ৩১ হাজার ছিল নারী। সে শহরে নারীদের কাজ আছে, নগদ টাকায় বেতন আছে, নারী শ্রমিকদের মধ্যে কমরেডশিপ আছে—কথাগুলো পুরো স্কটল্যান্ডে ছড়িয়ে পড়ল। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, আর স্বাধীনচেতা নারীরা দলে দলে ড্যান্ডি শহরে আসতে থাকল। ১৯১১ সালে সেখানে প্রতি ১০০ জন পুরুষের অনুপাতে নারীর সংখ্যা ছিল ১৫০ জন। সে সময় ড্যান্ডি শহরের মেয়েরা বিয়ের জন্য ঘরজামাই খুঁজত। ছেলে রান্নাবান্না পারে কি না, বাচ্চাকাচ্চা দেখাশোনা করতে পারবে কি না, জামা কাপড় ধোয়া, ইস্তিরি করার কাজ করতে পারে কি না, বিয়ের জন্য এসব প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হতো ছেলেদের।
 কেটল-বয়লার, জ্যামের শহর কিংবা শি টাউনের গল্প
কেটল-বয়লার, জ্যামের শহর কিংবা শি টাউনের গল্প
এই শহরে শ্রমজীবী নারীরা বেকার পুরুষদের বিয়ে করে ঘরে রাখত, আর নিজেরা জুট মিলে কাজ করে টাকা উপার্জন করত। পুরুষেরা বাড়িতে বসে ঘর গৃহস্থালির অবসরে আশপাশের বাগান থেকে স্ট্রবেরি আর ব্ল্যাক কারেন্ট সংগ্রহ করে জ্যাম বানাত। সে সময় ড্যান্ডি ‘জ্যামের শহর’ বলেও প্রভূত খ্যাতি অর্জন করে। পাটের ফিরতি জাহাজে আসা ড্যান্ডির জ্যাম কলকাতার মধ্যবিত্তের ঘরে পৌঁছে যেত। এখন সে শহরে জ্যাম তৈরি হয় না। তবুও কলকাতার মধ্যবিত্ত ঘরে বিকেলের নাশতায় পাউরুটির টোস্ট, আর জ্যাম দিয়ে অতিথি আপ্যায়নের রেওয়াজ রয়ে গেছে।
এক কাপ চা দিয়ে অতিথি আপ্যায়নের রীতি ড্যান্ডি শহরেও ছিল। তবে চা বানানোর দায়িত্ব ছিল পুরুষদের। কেটলিতে পানি গরম করে চা বানাতে হতো। তাই ড্যান্ডির পুরুষদের নাম হয়ে যায় ‘কেটল-বয়লার’। স্কটল্যান্ডের অন্য শহরের মানুষ ড্যান্ডির নাম দেয় ‘শি টাউন’ বা ‘নারীদের শহর’। কিন্তু এ সমস্ত টিটকারি দেওয়া কথা ড্যান্ডির নারীদের একটুকুও বদলাতে পারেনি। তারা দিনে দশ ঘণ্টা কাজ করত। প্রয়োজন হলে রাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল করত। রাতে সুন্দর কাপড় পরে দলে দলে শহরে ঘুরে বেড়াত, থিয়েটার দেখত, নাইট ক্লাবে নাচত, পানাহার করত, আনন্দ ফুর্তি করত। তাদের আনন্দ ফুর্তির মাত্রা একটু বেশি হলে পুলিশ বাধা দিত। দুপক্ষের মধ্যে লড়াই বেধে যেত। কোনো কোনো রাতে ড্যান্ডি শহরের কেন্দ্রস্থল কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হতো। বিশ শতকের প্রথম দশকের কোনো এক বছর ড্যান্ডি শহরে শান্তি ভঙ্গের দায়ে হাজত খাটা ১ হাজার ৪০০ মানুষের মধ্যে ৮০০ জনই ছিল নারী।
উপমহাদেশের রক্ত শোষণ করে ধনী হওয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নারী বা পুরুষদের বাহবা দেওয়ার মানুষ আমি নই। তারপরও ড্যান্ডির নারীদের সাহসে বাহবা না দিয়ে পারি না।
 শি টাউনের নারীদের শ্রমিক আন্দোলন
শি টাউনের নারীদের শ্রমিক আন্দোলন
ড্যান্ডি শহরে শ্রমিক আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল জুট মিলের নারী শ্রমিকেরা। তবে তারা কোনো দিন পুরুষ নিয়ন্ত্রিত শ্রমিক সংগঠনের নিয়ম মেনে চলত না। তারা শ্রমের ন্যায্য মূল্য আদায় করা, কারখানা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ধর্মঘট, মিটিং-মিছিল নিজেরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করত এবং মাঝেমধ্যে সফলতা লাভ করত।
‘সমান কাজের সমান মূল্য’ পুরুষ-নারীর সমান বেতন এবং বৃহত্তর সমাজে নারী-পুরুষের সমঅধিকার অর্জনের সংগ্রামে তারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তাদের দাবি মানতে বাধ্য হয়েই ড্যান্ডি টাউন কাউন্সিল কর্মজীবী মায়েদের শিশুদের দেখাশোনা করার জন্য ক্রেস ও নার্সারি প্রতিষ্ঠা করে এবং শুধুমাত্র নারীদের বসবাসের জন্য ঘরবাড়ি তৈরি করে।
ইংল্যান্ডে নারীদের ভোটের অধিকার অর্জনে ‘সাফরাজেট’ আন্দোলনে ড্যান্ডির নারী শ্রমিকেরা প্রভূত অবদান রাখে। তাদের কাজের দক্ষতা, অর্থনৈতিক শক্তি আর স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের মুখে ব্রিটিশ শাসক শ্রেণি অবশেষে ১৯১৮ সালে প্রথমবারের মতো নারীদের ভোটের অধিকার দিতে বাধ্য হয়। ড্যান্ডির নারীরা ১৯২২ সালের সাধারণ নির্বাচনে প্রথমবারের মতো ভোট দিয়ে তাদের নতুন অধিকারের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। তারা এই ভোটে নারীদের ভোটাধিকার বিরোধী, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কট্টর সমর্থক এবং ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলকে পরাজিত করে।
 বাংলার বস্ত্রবালিকারা
বাংলার বস্ত্রবালিকারা
পাট ব্যবসায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোনো উন্নতি হয়নি। বাংলার নেংটি পরা কৃষকদের ভাগ্য খোলেনি। কিন্তু ড্যান্ডি শহরের মেয়েরা পাটকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের ভাগ্য বদল করতে পেরেছিল। পুরো ব্রিটেনে, তথা পশ্চিম ইউরোপীয় মেয়েদের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রগামী ভূমিকা পালন করতে পেরেছিল।
ড্যান্ডির জুট মিউজিয়াম দেখছি, গাইডের কথা শুনছি, আর আমার কল্পনার চোখে ভেসে উঠছিল তাদেরই উত্তরসূরি পাটের দেশের মানুষ আমার স্বজাতি, অন্য এক তন্তু, তুলার কাপড় সেলাইয়ের কাজে নিয়োজিত ঢাকা শহরের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কর্মরত নারী শ্রমিকদের চেহারা। কী জুটছে তাদের কপালে?
আমি যখন বাংলাদেশে যাই, তখন এয়ারপোর্ট থেকে ফরিদপুর যাওয়ার পথে বাংলাদেশ গার্মেন্টস শিল্পের কেন্দ্রবিন্দু আশুলিয়া শিল্পাঞ্চলের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। আমি গাড়িতে বসে দেখি হাজার হাজার গার্মেন্টস শ্রমিক রাস্তার দুধারে সুশৃঙ্খলভাবে হেঁটে যাচ্ছে। রং-বেরঙের পোশাকে এরা সবাই দেখতে সুন্দর, প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। এরা সবাই নারী। এরাই বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। এদের সংখ্যা ৩২ লাখ। এরা বছরে ৩ দশমিক ১ লাখ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। তবুও গার্মেন্টস শ্রমিক নারীদের অবস্থা এমন কেন? বেতন কম, কাজের নিরাপত্তা নেই, জীবনের নিরাপত্তা নেই। কেন?
১৯৭২ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় ছিল ৯৪ ডলার বা ৮ হাজার ৪০০ টাকা। বর্তমানে তা ২ হাজার ৮৮২ ডলার বা ২ লাখ ৬০ হাজার টাকা। আমরা এখন পাকিস্তান ও ভারতকে ছাড়িয়ে গেছি এবং আরও ওপরে যাচ্ছি। কিন্তু যে শিলাখণ্ডের শক্ত ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে আমরা আরও ওপরে উঠছি, গার্মেন্টস শিল্পের সেই নারী শ্রমিকদের আমরা কতটা মর্যাদা দিতে শিখেছি? আশা করি বাংলাদেশের পাট যেমন একদিন পশ্চিমা দেশগুলোর নারীমুক্তিতে কার্যকারী ভূমিকা পালন করেছে, তেমনি আজকের দিনে বাংলাদেশ গার্মেন্টস শিল্পে কর্মরত নারীরা অদূর ভবিষ্যতে পূর্বাঞ্চলের দেশগুলোতে নারীমুক্তির সূচনা করবে।
 বাংলায় পাটকল ও ড্যান্ডির পতন
বাংলায় পাটকল ও ড্যান্ডির পতন
১৮৭০ সালে মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীরা কলকাতার প্রথম পাটকল প্রতিষ্ঠা করে। তখন থেকে এ ব্যবসায় ড্যান্ডির একচেটিয়া আধিপত্য কমতে থাকে। বিশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে কলকাতা পাটকলের শ্রমিক সংখ্যা ড্যান্ডিকে ছাড়িয়ে যায় এবং পরিবর্তনের গতিধারা অব্যাহত থাকে। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের তীব্রতা এই পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে। ১৯৪৭ সালের পর পাকিস্তান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্ব পাকিস্তানে নতুন নতুন এবং বড় বড় পাটকল প্রতিষ্ঠিত হলে ড্যান্ডির অবস্থা রাতারাতি বদলে যায়। ১৯৫০-এর দশকে সেখানে পাটকলের সংখ্যা পঞ্চাশের নিচে নেমে যায়।
১৯৯৮ সালের ১৯ অক্টোবর। চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ৩১০ টন কাঁচা পাট নিয়ে এমভি বাংলার ঊর্মি যখন স্কটল্যান্ডের ড্যান্ডি বন্দরে পৌঁছায়, তখন সে শহরের মিলের সংখ্যা ছিল মাত্র একটি। এর পর ড্যান্ডি বন্দরে আর কোনো দিন পাটের জাহাজ নোঙর করেনি।
শেষ লটের পাটের শেষ কোস্টার কাজ ১৯৯৯ সালের মে মাসে শেষ হলে, তায়েব্যাংক পাওয়ার লুমসের মালিক সব মেশিনপত্র বিক্রি করে দেয় কলকাতা পাটকলের মালিক জি জে ওয়াদওহার কাছে। ১৯৯৯ সালের আগস্ট মাসে ফিরতি যাত্রায় বাংলার ঊর্মি ড্যান্ডির শেষ পাটকলের শেষ যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে কলকাতা বন্দরে পৌঁছে দেয়। এ যেন বাংলার ছেলে বাংলায় ফিরে আসা।
 ‘দ্যাট ওয়াজ দি এন্ড’, বলে আমার গাইডের চোখ ছলছল করে উঠল। একজন বয়স্ক পুরুষের চোখে জল দেখে আমিও আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লাম। নরম সুরে জিজ্ঞেস করলাম, ‘তুমি এই মিলে কাজ করেছ নাকি?’ একটু মৃদু হেসে তিনি জবাব দিলেন, ‘না, আমার মা করেছে। আমি কাজের বয়সী হওয়ার আগেই এই মিল বন্ধ হয়ে গেছে। মায়ের মুখে অনেক গল্প শুনেছি। আমার মা এখন বেঁচে নেই। মাকে সম্মান জানানোর জন্য আমি সপ্তাহে একদিন এই জুট মিউজিয়ামে ভলান্টিয়ার গাইড হিসেবে কাজ করি। বেতন পাই না। কিন্তু আনন্দ পাই।’
‘দ্যাট ওয়াজ দি এন্ড’, বলে আমার গাইডের চোখ ছলছল করে উঠল। একজন বয়স্ক পুরুষের চোখে জল দেখে আমিও আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লাম। নরম সুরে জিজ্ঞেস করলাম, ‘তুমি এই মিলে কাজ করেছ নাকি?’ একটু মৃদু হেসে তিনি জবাব দিলেন, ‘না, আমার মা করেছে। আমি কাজের বয়সী হওয়ার আগেই এই মিল বন্ধ হয়ে গেছে। মায়ের মুখে অনেক গল্প শুনেছি। আমার মা এখন বেঁচে নেই। মাকে সম্মান জানানোর জন্য আমি সপ্তাহে একদিন এই জুট মিউজিয়ামে ভলান্টিয়ার গাইড হিসেবে কাজ করি। বেতন পাই না। কিন্তু আনন্দ পাই।’
এবার আমার চোখ ছলছল করে উঠল। পেছনে পরের ব্যাচের দর্শক জমা হয়ে গেছে, কথা বাড়াতে পারলাম না। ‘ইউ আর ডুয়িং এ গ্রেট জব, কিপ ইট আপ’, বললাম। হ্যান্ডশেক করে বিদায় নিলাম। সুভেনির শপে ঢুকতেই চোখে পড়ল একখানা বই ‘জুট নো মোর’। বইখানা কিনলাম।
লেখক: ডিরেক্টর, এশিয়ান রিসোর্স সেন্টার, বার্মিংহাম, ইংল্যান্ড

১৯২০-এর দশকের কোনো এক দিন। ড্যান্ডি শহরের কোনো এক জুট মিলের মালিক মাথায় সোলার হ্যাট পরে আমাদের ফরিদপুর শহরের পাটের বাজার দেখতে এসেছিলেন, দাদার মুখে সে গল্প শুনেছি।
সে ঘটনার প্রায় ১০২ বছর পর অবশেষে দেখলাম স্কটল্যান্ডের ড্যান্ডি শহরে বিশ্বের প্রথম জুটমিল। মিল ঠিক নয়, জুট মিউজিয়াম। পাট উৎপন্ন করত বাংলার কৃষক, আর সব পাটকল ছিল স্কটল্যান্ডে। সহজ বাংলা ভাষায় এরই নাম ছিল সাম্রাজ্যবাদ।
ভারডান্ট ওয়ার্কস মিউজিয়াম
‘গতস্য শোচনা নাস্তি’ অতি পুরোনো সংস্কৃত শ্লোক। তবুও বয়স্কা নর্তকী বারবার আয়না দেখে, বিগত যৌবনের সৌন্দর্য খোঁজে। আর বৃদ্ধ মানুষ চোখ বন্ধ করে বিগত যৌবনের সুখ চিন্তা করে। আমাদের এক কালের প্রভুদের অবস্থাও ঠিক তাই। এখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নেই, ড্যান্ডি শহরে জুট মিলও নেই। বন্ধ হয়ে যাওয়া একটা জুট মিলকে মিউজিয়াম বানিয়ে স্কটিশেরা পুরোনো শৌর্য ও ঐশ্বর্য মনে রাখার চেষ্টা করছে।
১৯৫৪ সালে হক-ভাসানি মুসলিম লীগকে ডুবিয়ে দিয়ে যেদিন সরকার গঠনের শপথ নিচ্ছিল, ঠিক সেই দিন নারায়ণগঞ্জের পাটকলে বিহারি আর বাঙালি শ্রমিকদের মধ্য রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা বাঁধিয়ে মুসলিম লীগের গুন্ডারা গণপ্রতিনিধিত্বের সরকারকে খাটো করবার চেষ্টা করেছিল। সে কথা ইতিহাস বইতে পড়েছি। ‘আমরা পাট রপ্তানি করে যে পরিমাণ বিদেশি টাকা আয় করি, তার বেশির ভাগ টাকা পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে ব্যয় করা হয়’, এই নিয়ে মুসলিম লীগ সমর্থকদের সঙ্গে ঝগড়া করেছি। বাংলার সোনালি আঁশ পাট। স্কুলের পরীক্ষায় ইংরেজি ভাষায় ‘জুট’ রচনা লিখেছি। কিন্তু হাজি আদমজীর ছেলেদের উদ্যোগে তৈরি, দাউদ, বাওয়ানী অথবা খোদ আদমজী জুট মিলটাও কোনো দিন দেখিনি। তাই স্কটল্যান্ডের ড্যান্ডি শহরে বেড়াতে এসে ‘ভারডান্ট ওয়ার্কস’ মিউজিয়াম দেখার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। সুন্দর সাজানো-গোছানো মিউজিয়ামের ভেতর পাটকলে ব্যবহার করা সব যন্ত্রপাতি দেখলাম, আর গাইডের মুখে শুনলাম এক রূপকথার গল্প।
 সোনালি আঁশের উত্থান
সোনালি আঁশের উত্থান
তিসির তেল আমরা বেশ চিনি। বাংলাদেশে তিসি ফলানো হয় মূলত তেলের জন্য। এ তেল কাঠের বার্নিশ উজ্জ্বল করে, আর ক্রিকেট ব্যাটের স্ট্রোক বাড়ায়। তবে মিসর ও জর্জিয়ায় তিসির চাষ করা করা হয় এ উদ্ভিদের ছাল থেকে সুতা তৈরির জন্য। তিসি গাছের ছাল পাটের মতো প্রক্রিয়াজাত করে যে সুতা বানানো হয়, তার ইংরেজি নাম ফ্ল্যাক্স। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ড্যান্ডি শহরে অনেকগুলো ফ্ল্যাক্স মিল ছিল। সেখানে এই সুতা দিয়ে মোটা ক্যানভাস ও লিনেন কাপড় তৈরি করা হতো। ড্যান্ডি শহরে ফ্ল্যাক্স আমদানি করা হতো কৃষ্ণ সাগর পারের ক্রিমিয়া ও জর্জিয়া অঞ্চল থেকে। রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের লড়াইয়ে উনিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে ফ্ল্যাক্সের উৎপাদন এবং সরবরাহ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।
প্রায় একই সময় কলকাতা বন্দরে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিকেরা ফ্ল্যাক্স আঁশের মতো দেখতে বাংলা পাটের প্রতি নজর দেয়। ১৮২০ সালে প্রথমবারের মতো আড়াই মন ওজনের একটি পাটের বেল ড্যান্ডি শহরে এসে পৌঁছায়।
কিন্তু পাটের আঁশ শক্ত। ফলে ফ্ল্যাক্সের বদলে পাট ব্যবহার করা গেল না। অনেক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেল যে, তিমি মাছের তেলে পাট ভেজালে তা নরম হয়, যা ফ্ল্যাক্স মিলে ব্যবহার কর যায়। তায়ে (Tay) নদীর তীরে অবস্থিত ড্যান্ডি নৌবন্দর অনেক আগে থেকেই তিমি মাছ ধরা এবং বেচাকেনার বাজার হিসেবে বিখ্যাত ছিল। সেখানে তিমি মাছের তেল সস্তায় এবং প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। লাভ-ক্ষতির অঙ্ক করতে ব্যাপারীদের বেশি সময় লাগল না। ড্যান্ডি শহরে ডেভিড লিন্ডসে তাঁর ফ্ল্যাক্স মিল ‘ভারডান্ট ওয়ার্কস’-এর কিছু বিবর্তন করে ১৮৩৫ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন বিশ্বের প্রথম জুট মিল বা পাটকল।
শুরু হলো পাটের অগ্রযাত্রা। একে একে ড্যান্ডির ফ্ল্যাক্স মিলগুলো জুট মিলে পরিণত হতে থাকল। ড্যান্ডি ডকইয়ার্ডে তৈরি হতে থাকল বড় বড় জাহাজ। ১৮৬৯ সালে সুয়েজ খাল খুলে গেলে এশিয়া আর ইউরোপের মধ্যে নৌপথের দূরত্ব কমে যায়। ফলে কাঁচা পাট কলকাতা বন্দর থেকে ৯০ দিনে ড্যান্ডি বন্দরে পৌঁছাতে থাকল। সোনায় সোহাগা। নতুন জুট মিল তৈরি হতে থাকল সেখানে। নেহাত বাংলা ঘরের ছনের চালে আটন-ছাটন আর রুয়া-ফুসসির বাঁধনে কাজে লাগা বাংলার পাট বিলেতি জুট মিলের সৌজন্যে হয়ে উঠল আন্তর্জাতিক বেস্ট সেলার এক পণ্য। আমাদের দেশের প্রধান অর্থকরী ফসল, যার নাম হলো সোনালি আঁশ। আর নারায়ণগঞ্জ নৌবন্দর বাংলার ড্যান্ডি নামে বিখ্যাত হলো।
 বাংলার পাট, ড্যান্ডির নারী
বাংলার পাট, ড্যান্ডির নারী
পাট হাটের ফড়িয়া, দালাল, আর পাট গুদামের মালিকদের ব্যাংক ব্যালান্স এবং পেটের ভুঁড়ি দুটোই সমানুপাতিক হারে বাড়তে থাকল। কুষ্টিয়া রেল স্টেশনের পাশে ঠাকুর অ্যান্ড কোম্পানির গুদাম খুলে, ধুতি কাছা দিয়ে পাটের ব্যবসায় নেমে গেলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তবে, কবির নোবেল প্রাইজ পাওয়া জ্ঞানে কাজ হলো না। পাটের ব্যবসা লাটে উঠল। ধনী হলো ড্যান্ডির জুটমিল মালিকেরা। দিনে দিনে, মাসে মাসে সেখানে বাড়তে থাকল পাটকলের সংখ্যা। ১৯০৯ সালে ড্যান্ডি শহরে ছিল ১৩০টি পাটকল। ১৯০১ সালে ড্যান্ডি শহরের মোট ৮৬ হাজার শ্রমিকের অর্ধেক ছিল পাট শ্রমিক। এর পঁচাত্তর ভাগ ছিল নারী।
হাতে চালানো তাঁতের কাজ কষ্টসাধ্য হওয়ায় তাঁত বুননের কাজে প্রথম দিকে নারী শ্রমিক নেওয়া হতো না। কিন্তু বৈদ্যুতিক তাঁত চালু হলে নারীরা পাটকলে কাজ করার উপযুক্ত বিবেচিত হয়। অর্থনৈতিক প্রয়োজন, ঘরের বাঁধন ছিঁড়ে বাইরে যাওয়ার উৎসাহ আর কম বেতনে কাজ করতে রাজি হওয়া বিপুলসংখ্যক নারী শ্রমিক পাটকলে নিয়োগ পেতে থাকে।
ড্যান্ডিতে এক সময় ৪১ হাজার পাটকল শ্রমিকের মধ্যে ৩১ হাজার ছিল নারী। সে শহরে নারীদের কাজ আছে, নগদ টাকায় বেতন আছে, নারী শ্রমিকদের মধ্যে কমরেডশিপ আছে—কথাগুলো পুরো স্কটল্যান্ডে ছড়িয়ে পড়ল। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, আর স্বাধীনচেতা নারীরা দলে দলে ড্যান্ডি শহরে আসতে থাকল। ১৯১১ সালে সেখানে প্রতি ১০০ জন পুরুষের অনুপাতে নারীর সংখ্যা ছিল ১৫০ জন। সে সময় ড্যান্ডি শহরের মেয়েরা বিয়ের জন্য ঘরজামাই খুঁজত। ছেলে রান্নাবান্না পারে কি না, বাচ্চাকাচ্চা দেখাশোনা করতে পারবে কি না, জামা কাপড় ধোয়া, ইস্তিরি করার কাজ করতে পারে কি না, বিয়ের জন্য এসব প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হতো ছেলেদের।
 কেটল-বয়লার, জ্যামের শহর কিংবা শি টাউনের গল্প
কেটল-বয়লার, জ্যামের শহর কিংবা শি টাউনের গল্প
এই শহরে শ্রমজীবী নারীরা বেকার পুরুষদের বিয়ে করে ঘরে রাখত, আর নিজেরা জুট মিলে কাজ করে টাকা উপার্জন করত। পুরুষেরা বাড়িতে বসে ঘর গৃহস্থালির অবসরে আশপাশের বাগান থেকে স্ট্রবেরি আর ব্ল্যাক কারেন্ট সংগ্রহ করে জ্যাম বানাত। সে সময় ড্যান্ডি ‘জ্যামের শহর’ বলেও প্রভূত খ্যাতি অর্জন করে। পাটের ফিরতি জাহাজে আসা ড্যান্ডির জ্যাম কলকাতার মধ্যবিত্তের ঘরে পৌঁছে যেত। এখন সে শহরে জ্যাম তৈরি হয় না। তবুও কলকাতার মধ্যবিত্ত ঘরে বিকেলের নাশতায় পাউরুটির টোস্ট, আর জ্যাম দিয়ে অতিথি আপ্যায়নের রেওয়াজ রয়ে গেছে।
এক কাপ চা দিয়ে অতিথি আপ্যায়নের রীতি ড্যান্ডি শহরেও ছিল। তবে চা বানানোর দায়িত্ব ছিল পুরুষদের। কেটলিতে পানি গরম করে চা বানাতে হতো। তাই ড্যান্ডির পুরুষদের নাম হয়ে যায় ‘কেটল-বয়লার’। স্কটল্যান্ডের অন্য শহরের মানুষ ড্যান্ডির নাম দেয় ‘শি টাউন’ বা ‘নারীদের শহর’। কিন্তু এ সমস্ত টিটকারি দেওয়া কথা ড্যান্ডির নারীদের একটুকুও বদলাতে পারেনি। তারা দিনে দশ ঘণ্টা কাজ করত। প্রয়োজন হলে রাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল করত। রাতে সুন্দর কাপড় পরে দলে দলে শহরে ঘুরে বেড়াত, থিয়েটার দেখত, নাইট ক্লাবে নাচত, পানাহার করত, আনন্দ ফুর্তি করত। তাদের আনন্দ ফুর্তির মাত্রা একটু বেশি হলে পুলিশ বাধা দিত। দুপক্ষের মধ্যে লড়াই বেধে যেত। কোনো কোনো রাতে ড্যান্ডি শহরের কেন্দ্রস্থল কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হতো। বিশ শতকের প্রথম দশকের কোনো এক বছর ড্যান্ডি শহরে শান্তি ভঙ্গের দায়ে হাজত খাটা ১ হাজার ৪০০ মানুষের মধ্যে ৮০০ জনই ছিল নারী।
উপমহাদেশের রক্ত শোষণ করে ধনী হওয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নারী বা পুরুষদের বাহবা দেওয়ার মানুষ আমি নই। তারপরও ড্যান্ডির নারীদের সাহসে বাহবা না দিয়ে পারি না।
 শি টাউনের নারীদের শ্রমিক আন্দোলন
শি টাউনের নারীদের শ্রমিক আন্দোলন
ড্যান্ডি শহরে শ্রমিক আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল জুট মিলের নারী শ্রমিকেরা। তবে তারা কোনো দিন পুরুষ নিয়ন্ত্রিত শ্রমিক সংগঠনের নিয়ম মেনে চলত না। তারা শ্রমের ন্যায্য মূল্য আদায় করা, কারখানা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ধর্মঘট, মিটিং-মিছিল নিজেরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করত এবং মাঝেমধ্যে সফলতা লাভ করত।
‘সমান কাজের সমান মূল্য’ পুরুষ-নারীর সমান বেতন এবং বৃহত্তর সমাজে নারী-পুরুষের সমঅধিকার অর্জনের সংগ্রামে তারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তাদের দাবি মানতে বাধ্য হয়েই ড্যান্ডি টাউন কাউন্সিল কর্মজীবী মায়েদের শিশুদের দেখাশোনা করার জন্য ক্রেস ও নার্সারি প্রতিষ্ঠা করে এবং শুধুমাত্র নারীদের বসবাসের জন্য ঘরবাড়ি তৈরি করে।
ইংল্যান্ডে নারীদের ভোটের অধিকার অর্জনে ‘সাফরাজেট’ আন্দোলনে ড্যান্ডির নারী শ্রমিকেরা প্রভূত অবদান রাখে। তাদের কাজের দক্ষতা, অর্থনৈতিক শক্তি আর স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের মুখে ব্রিটিশ শাসক শ্রেণি অবশেষে ১৯১৮ সালে প্রথমবারের মতো নারীদের ভোটের অধিকার দিতে বাধ্য হয়। ড্যান্ডির নারীরা ১৯২২ সালের সাধারণ নির্বাচনে প্রথমবারের মতো ভোট দিয়ে তাদের নতুন অধিকারের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। তারা এই ভোটে নারীদের ভোটাধিকার বিরোধী, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কট্টর সমর্থক এবং ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলকে পরাজিত করে।
 বাংলার বস্ত্রবালিকারা
বাংলার বস্ত্রবালিকারা
পাট ব্যবসায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোনো উন্নতি হয়নি। বাংলার নেংটি পরা কৃষকদের ভাগ্য খোলেনি। কিন্তু ড্যান্ডি শহরের মেয়েরা পাটকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের ভাগ্য বদল করতে পেরেছিল। পুরো ব্রিটেনে, তথা পশ্চিম ইউরোপীয় মেয়েদের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রগামী ভূমিকা পালন করতে পেরেছিল।
ড্যান্ডির জুট মিউজিয়াম দেখছি, গাইডের কথা শুনছি, আর আমার কল্পনার চোখে ভেসে উঠছিল তাদেরই উত্তরসূরি পাটের দেশের মানুষ আমার স্বজাতি, অন্য এক তন্তু, তুলার কাপড় সেলাইয়ের কাজে নিয়োজিত ঢাকা শহরের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কর্মরত নারী শ্রমিকদের চেহারা। কী জুটছে তাদের কপালে?
আমি যখন বাংলাদেশে যাই, তখন এয়ারপোর্ট থেকে ফরিদপুর যাওয়ার পথে বাংলাদেশ গার্মেন্টস শিল্পের কেন্দ্রবিন্দু আশুলিয়া শিল্পাঞ্চলের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। আমি গাড়িতে বসে দেখি হাজার হাজার গার্মেন্টস শ্রমিক রাস্তার দুধারে সুশৃঙ্খলভাবে হেঁটে যাচ্ছে। রং-বেরঙের পোশাকে এরা সবাই দেখতে সুন্দর, প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। এরা সবাই নারী। এরাই বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। এদের সংখ্যা ৩২ লাখ। এরা বছরে ৩ দশমিক ১ লাখ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। তবুও গার্মেন্টস শ্রমিক নারীদের অবস্থা এমন কেন? বেতন কম, কাজের নিরাপত্তা নেই, জীবনের নিরাপত্তা নেই। কেন?
১৯৭২ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় ছিল ৯৪ ডলার বা ৮ হাজার ৪০০ টাকা। বর্তমানে তা ২ হাজার ৮৮২ ডলার বা ২ লাখ ৬০ হাজার টাকা। আমরা এখন পাকিস্তান ও ভারতকে ছাড়িয়ে গেছি এবং আরও ওপরে যাচ্ছি। কিন্তু যে শিলাখণ্ডের শক্ত ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে আমরা আরও ওপরে উঠছি, গার্মেন্টস শিল্পের সেই নারী শ্রমিকদের আমরা কতটা মর্যাদা দিতে শিখেছি? আশা করি বাংলাদেশের পাট যেমন একদিন পশ্চিমা দেশগুলোর নারীমুক্তিতে কার্যকারী ভূমিকা পালন করেছে, তেমনি আজকের দিনে বাংলাদেশ গার্মেন্টস শিল্পে কর্মরত নারীরা অদূর ভবিষ্যতে পূর্বাঞ্চলের দেশগুলোতে নারীমুক্তির সূচনা করবে।
 বাংলায় পাটকল ও ড্যান্ডির পতন
বাংলায় পাটকল ও ড্যান্ডির পতন
১৮৭০ সালে মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীরা কলকাতার প্রথম পাটকল প্রতিষ্ঠা করে। তখন থেকে এ ব্যবসায় ড্যান্ডির একচেটিয়া আধিপত্য কমতে থাকে। বিশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে কলকাতা পাটকলের শ্রমিক সংখ্যা ড্যান্ডিকে ছাড়িয়ে যায় এবং পরিবর্তনের গতিধারা অব্যাহত থাকে। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের তীব্রতা এই পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে। ১৯৪৭ সালের পর পাকিস্তান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্ব পাকিস্তানে নতুন নতুন এবং বড় বড় পাটকল প্রতিষ্ঠিত হলে ড্যান্ডির অবস্থা রাতারাতি বদলে যায়। ১৯৫০-এর দশকে সেখানে পাটকলের সংখ্যা পঞ্চাশের নিচে নেমে যায়।
১৯৯৮ সালের ১৯ অক্টোবর। চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ৩১০ টন কাঁচা পাট নিয়ে এমভি বাংলার ঊর্মি যখন স্কটল্যান্ডের ড্যান্ডি বন্দরে পৌঁছায়, তখন সে শহরের মিলের সংখ্যা ছিল মাত্র একটি। এর পর ড্যান্ডি বন্দরে আর কোনো দিন পাটের জাহাজ নোঙর করেনি।
শেষ লটের পাটের শেষ কোস্টার কাজ ১৯৯৯ সালের মে মাসে শেষ হলে, তায়েব্যাংক পাওয়ার লুমসের মালিক সব মেশিনপত্র বিক্রি করে দেয় কলকাতা পাটকলের মালিক জি জে ওয়াদওহার কাছে। ১৯৯৯ সালের আগস্ট মাসে ফিরতি যাত্রায় বাংলার ঊর্মি ড্যান্ডির শেষ পাটকলের শেষ যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে কলকাতা বন্দরে পৌঁছে দেয়। এ যেন বাংলার ছেলে বাংলায় ফিরে আসা।
 ‘দ্যাট ওয়াজ দি এন্ড’, বলে আমার গাইডের চোখ ছলছল করে উঠল। একজন বয়স্ক পুরুষের চোখে জল দেখে আমিও আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লাম। নরম সুরে জিজ্ঞেস করলাম, ‘তুমি এই মিলে কাজ করেছ নাকি?’ একটু মৃদু হেসে তিনি জবাব দিলেন, ‘না, আমার মা করেছে। আমি কাজের বয়সী হওয়ার আগেই এই মিল বন্ধ হয়ে গেছে। মায়ের মুখে অনেক গল্প শুনেছি। আমার মা এখন বেঁচে নেই। মাকে সম্মান জানানোর জন্য আমি সপ্তাহে একদিন এই জুট মিউজিয়ামে ভলান্টিয়ার গাইড হিসেবে কাজ করি। বেতন পাই না। কিন্তু আনন্দ পাই।’
‘দ্যাট ওয়াজ দি এন্ড’, বলে আমার গাইডের চোখ ছলছল করে উঠল। একজন বয়স্ক পুরুষের চোখে জল দেখে আমিও আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লাম। নরম সুরে জিজ্ঞেস করলাম, ‘তুমি এই মিলে কাজ করেছ নাকি?’ একটু মৃদু হেসে তিনি জবাব দিলেন, ‘না, আমার মা করেছে। আমি কাজের বয়সী হওয়ার আগেই এই মিল বন্ধ হয়ে গেছে। মায়ের মুখে অনেক গল্প শুনেছি। আমার মা এখন বেঁচে নেই। মাকে সম্মান জানানোর জন্য আমি সপ্তাহে একদিন এই জুট মিউজিয়ামে ভলান্টিয়ার গাইড হিসেবে কাজ করি। বেতন পাই না। কিন্তু আনন্দ পাই।’
এবার আমার চোখ ছলছল করে উঠল। পেছনে পরের ব্যাচের দর্শক জমা হয়ে গেছে, কথা বাড়াতে পারলাম না। ‘ইউ আর ডুয়িং এ গ্রেট জব, কিপ ইট আপ’, বললাম। হ্যান্ডশেক করে বিদায় নিলাম। সুভেনির শপে ঢুকতেই চোখে পড়ল একখানা বই ‘জুট নো মোর’। বইখানা কিনলাম।
লেখক: ডিরেক্টর, এশিয়ান রিসোর্স সেন্টার, বার্মিংহাম, ইংল্যান্ড
মোহাম্মদ ইদ্রিস

১৯২০-এর দশকের কোনো এক দিন। ড্যান্ডি শহরের কোনো এক জুট মিলের মালিক মাথায় সোলার হ্যাট পরে আমাদের ফরিদপুর শহরের পাটের বাজার দেখতে এসেছিলেন, দাদার মুখে সে গল্প শুনেছি।
সে ঘটনার প্রায় ১০২ বছর পর অবশেষে দেখলাম স্কটল্যান্ডের ড্যান্ডি শহরে বিশ্বের প্রথম জুটমিল। মিল ঠিক নয়, জুট মিউজিয়াম। পাট উৎপন্ন করত বাংলার কৃষক, আর সব পাটকল ছিল স্কটল্যান্ডে। সহজ বাংলা ভাষায় এরই নাম ছিল সাম্রাজ্যবাদ।
ভারডান্ট ওয়ার্কস মিউজিয়াম
‘গতস্য শোচনা নাস্তি’ অতি পুরোনো সংস্কৃত শ্লোক। তবুও বয়স্কা নর্তকী বারবার আয়না দেখে, বিগত যৌবনের সৌন্দর্য খোঁজে। আর বৃদ্ধ মানুষ চোখ বন্ধ করে বিগত যৌবনের সুখ চিন্তা করে। আমাদের এক কালের প্রভুদের অবস্থাও ঠিক তাই। এখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নেই, ড্যান্ডি শহরে জুট মিলও নেই। বন্ধ হয়ে যাওয়া একটা জুট মিলকে মিউজিয়াম বানিয়ে স্কটিশেরা পুরোনো শৌর্য ও ঐশ্বর্য মনে রাখার চেষ্টা করছে।
১৯৫৪ সালে হক-ভাসানি মুসলিম লীগকে ডুবিয়ে দিয়ে যেদিন সরকার গঠনের শপথ নিচ্ছিল, ঠিক সেই দিন নারায়ণগঞ্জের পাটকলে বিহারি আর বাঙালি শ্রমিকদের মধ্য রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা বাঁধিয়ে মুসলিম লীগের গুন্ডারা গণপ্রতিনিধিত্বের সরকারকে খাটো করবার চেষ্টা করেছিল। সে কথা ইতিহাস বইতে পড়েছি। ‘আমরা পাট রপ্তানি করে যে পরিমাণ বিদেশি টাকা আয় করি, তার বেশির ভাগ টাকা পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে ব্যয় করা হয়’, এই নিয়ে মুসলিম লীগ সমর্থকদের সঙ্গে ঝগড়া করেছি। বাংলার সোনালি আঁশ পাট। স্কুলের পরীক্ষায় ইংরেজি ভাষায় ‘জুট’ রচনা লিখেছি। কিন্তু হাজি আদমজীর ছেলেদের উদ্যোগে তৈরি, দাউদ, বাওয়ানী অথবা খোদ আদমজী জুট মিলটাও কোনো দিন দেখিনি। তাই স্কটল্যান্ডের ড্যান্ডি শহরে বেড়াতে এসে ‘ভারডান্ট ওয়ার্কস’ মিউজিয়াম দেখার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। সুন্দর সাজানো-গোছানো মিউজিয়ামের ভেতর পাটকলে ব্যবহার করা সব যন্ত্রপাতি দেখলাম, আর গাইডের মুখে শুনলাম এক রূপকথার গল্প।
 সোনালি আঁশের উত্থান
সোনালি আঁশের উত্থান
তিসির তেল আমরা বেশ চিনি। বাংলাদেশে তিসি ফলানো হয় মূলত তেলের জন্য। এ তেল কাঠের বার্নিশ উজ্জ্বল করে, আর ক্রিকেট ব্যাটের স্ট্রোক বাড়ায়। তবে মিসর ও জর্জিয়ায় তিসির চাষ করা করা হয় এ উদ্ভিদের ছাল থেকে সুতা তৈরির জন্য। তিসি গাছের ছাল পাটের মতো প্রক্রিয়াজাত করে যে সুতা বানানো হয়, তার ইংরেজি নাম ফ্ল্যাক্স। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ড্যান্ডি শহরে অনেকগুলো ফ্ল্যাক্স মিল ছিল। সেখানে এই সুতা দিয়ে মোটা ক্যানভাস ও লিনেন কাপড় তৈরি করা হতো। ড্যান্ডি শহরে ফ্ল্যাক্স আমদানি করা হতো কৃষ্ণ সাগর পারের ক্রিমিয়া ও জর্জিয়া অঞ্চল থেকে। রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের লড়াইয়ে উনিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে ফ্ল্যাক্সের উৎপাদন এবং সরবরাহ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।
প্রায় একই সময় কলকাতা বন্দরে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিকেরা ফ্ল্যাক্স আঁশের মতো দেখতে বাংলা পাটের প্রতি নজর দেয়। ১৮২০ সালে প্রথমবারের মতো আড়াই মন ওজনের একটি পাটের বেল ড্যান্ডি শহরে এসে পৌঁছায়।
কিন্তু পাটের আঁশ শক্ত। ফলে ফ্ল্যাক্সের বদলে পাট ব্যবহার করা গেল না। অনেক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেল যে, তিমি মাছের তেলে পাট ভেজালে তা নরম হয়, যা ফ্ল্যাক্স মিলে ব্যবহার কর যায়। তায়ে (Tay) নদীর তীরে অবস্থিত ড্যান্ডি নৌবন্দর অনেক আগে থেকেই তিমি মাছ ধরা এবং বেচাকেনার বাজার হিসেবে বিখ্যাত ছিল। সেখানে তিমি মাছের তেল সস্তায় এবং প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। লাভ-ক্ষতির অঙ্ক করতে ব্যাপারীদের বেশি সময় লাগল না। ড্যান্ডি শহরে ডেভিড লিন্ডসে তাঁর ফ্ল্যাক্স মিল ‘ভারডান্ট ওয়ার্কস’-এর কিছু বিবর্তন করে ১৮৩৫ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন বিশ্বের প্রথম জুট মিল বা পাটকল।
শুরু হলো পাটের অগ্রযাত্রা। একে একে ড্যান্ডির ফ্ল্যাক্স মিলগুলো জুট মিলে পরিণত হতে থাকল। ড্যান্ডি ডকইয়ার্ডে তৈরি হতে থাকল বড় বড় জাহাজ। ১৮৬৯ সালে সুয়েজ খাল খুলে গেলে এশিয়া আর ইউরোপের মধ্যে নৌপথের দূরত্ব কমে যায়। ফলে কাঁচা পাট কলকাতা বন্দর থেকে ৯০ দিনে ড্যান্ডি বন্দরে পৌঁছাতে থাকল। সোনায় সোহাগা। নতুন জুট মিল তৈরি হতে থাকল সেখানে। নেহাত বাংলা ঘরের ছনের চালে আটন-ছাটন আর রুয়া-ফুসসির বাঁধনে কাজে লাগা বাংলার পাট বিলেতি জুট মিলের সৌজন্যে হয়ে উঠল আন্তর্জাতিক বেস্ট সেলার এক পণ্য। আমাদের দেশের প্রধান অর্থকরী ফসল, যার নাম হলো সোনালি আঁশ। আর নারায়ণগঞ্জ নৌবন্দর বাংলার ড্যান্ডি নামে বিখ্যাত হলো।
 বাংলার পাট, ড্যান্ডির নারী
বাংলার পাট, ড্যান্ডির নারী
পাট হাটের ফড়িয়া, দালাল, আর পাট গুদামের মালিকদের ব্যাংক ব্যালান্স এবং পেটের ভুঁড়ি দুটোই সমানুপাতিক হারে বাড়তে থাকল। কুষ্টিয়া রেল স্টেশনের পাশে ঠাকুর অ্যান্ড কোম্পানির গুদাম খুলে, ধুতি কাছা দিয়ে পাটের ব্যবসায় নেমে গেলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তবে, কবির নোবেল প্রাইজ পাওয়া জ্ঞানে কাজ হলো না। পাটের ব্যবসা লাটে উঠল। ধনী হলো ড্যান্ডির জুটমিল মালিকেরা। দিনে দিনে, মাসে মাসে সেখানে বাড়তে থাকল পাটকলের সংখ্যা। ১৯০৯ সালে ড্যান্ডি শহরে ছিল ১৩০টি পাটকল। ১৯০১ সালে ড্যান্ডি শহরের মোট ৮৬ হাজার শ্রমিকের অর্ধেক ছিল পাট শ্রমিক। এর পঁচাত্তর ভাগ ছিল নারী।
হাতে চালানো তাঁতের কাজ কষ্টসাধ্য হওয়ায় তাঁত বুননের কাজে প্রথম দিকে নারী শ্রমিক নেওয়া হতো না। কিন্তু বৈদ্যুতিক তাঁত চালু হলে নারীরা পাটকলে কাজ করার উপযুক্ত বিবেচিত হয়। অর্থনৈতিক প্রয়োজন, ঘরের বাঁধন ছিঁড়ে বাইরে যাওয়ার উৎসাহ আর কম বেতনে কাজ করতে রাজি হওয়া বিপুলসংখ্যক নারী শ্রমিক পাটকলে নিয়োগ পেতে থাকে।
ড্যান্ডিতে এক সময় ৪১ হাজার পাটকল শ্রমিকের মধ্যে ৩১ হাজার ছিল নারী। সে শহরে নারীদের কাজ আছে, নগদ টাকায় বেতন আছে, নারী শ্রমিকদের মধ্যে কমরেডশিপ আছে—কথাগুলো পুরো স্কটল্যান্ডে ছড়িয়ে পড়ল। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, আর স্বাধীনচেতা নারীরা দলে দলে ড্যান্ডি শহরে আসতে থাকল। ১৯১১ সালে সেখানে প্রতি ১০০ জন পুরুষের অনুপাতে নারীর সংখ্যা ছিল ১৫০ জন। সে সময় ড্যান্ডি শহরের মেয়েরা বিয়ের জন্য ঘরজামাই খুঁজত। ছেলে রান্নাবান্না পারে কি না, বাচ্চাকাচ্চা দেখাশোনা করতে পারবে কি না, জামা কাপড় ধোয়া, ইস্তিরি করার কাজ করতে পারে কি না, বিয়ের জন্য এসব প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হতো ছেলেদের।
 কেটল-বয়লার, জ্যামের শহর কিংবা শি টাউনের গল্প
কেটল-বয়লার, জ্যামের শহর কিংবা শি টাউনের গল্প
এই শহরে শ্রমজীবী নারীরা বেকার পুরুষদের বিয়ে করে ঘরে রাখত, আর নিজেরা জুট মিলে কাজ করে টাকা উপার্জন করত। পুরুষেরা বাড়িতে বসে ঘর গৃহস্থালির অবসরে আশপাশের বাগান থেকে স্ট্রবেরি আর ব্ল্যাক কারেন্ট সংগ্রহ করে জ্যাম বানাত। সে সময় ড্যান্ডি ‘জ্যামের শহর’ বলেও প্রভূত খ্যাতি অর্জন করে। পাটের ফিরতি জাহাজে আসা ড্যান্ডির জ্যাম কলকাতার মধ্যবিত্তের ঘরে পৌঁছে যেত। এখন সে শহরে জ্যাম তৈরি হয় না। তবুও কলকাতার মধ্যবিত্ত ঘরে বিকেলের নাশতায় পাউরুটির টোস্ট, আর জ্যাম দিয়ে অতিথি আপ্যায়নের রেওয়াজ রয়ে গেছে।
এক কাপ চা দিয়ে অতিথি আপ্যায়নের রীতি ড্যান্ডি শহরেও ছিল। তবে চা বানানোর দায়িত্ব ছিল পুরুষদের। কেটলিতে পানি গরম করে চা বানাতে হতো। তাই ড্যান্ডির পুরুষদের নাম হয়ে যায় ‘কেটল-বয়লার’। স্কটল্যান্ডের অন্য শহরের মানুষ ড্যান্ডির নাম দেয় ‘শি টাউন’ বা ‘নারীদের শহর’। কিন্তু এ সমস্ত টিটকারি দেওয়া কথা ড্যান্ডির নারীদের একটুকুও বদলাতে পারেনি। তারা দিনে দশ ঘণ্টা কাজ করত। প্রয়োজন হলে রাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল করত। রাতে সুন্দর কাপড় পরে দলে দলে শহরে ঘুরে বেড়াত, থিয়েটার দেখত, নাইট ক্লাবে নাচত, পানাহার করত, আনন্দ ফুর্তি করত। তাদের আনন্দ ফুর্তির মাত্রা একটু বেশি হলে পুলিশ বাধা দিত। দুপক্ষের মধ্যে লড়াই বেধে যেত। কোনো কোনো রাতে ড্যান্ডি শহরের কেন্দ্রস্থল কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হতো। বিশ শতকের প্রথম দশকের কোনো এক বছর ড্যান্ডি শহরে শান্তি ভঙ্গের দায়ে হাজত খাটা ১ হাজার ৪০০ মানুষের মধ্যে ৮০০ জনই ছিল নারী।
উপমহাদেশের রক্ত শোষণ করে ধনী হওয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নারী বা পুরুষদের বাহবা দেওয়ার মানুষ আমি নই। তারপরও ড্যান্ডির নারীদের সাহসে বাহবা না দিয়ে পারি না।
 শি টাউনের নারীদের শ্রমিক আন্দোলন
শি টাউনের নারীদের শ্রমিক আন্দোলন
ড্যান্ডি শহরে শ্রমিক আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল জুট মিলের নারী শ্রমিকেরা। তবে তারা কোনো দিন পুরুষ নিয়ন্ত্রিত শ্রমিক সংগঠনের নিয়ম মেনে চলত না। তারা শ্রমের ন্যায্য মূল্য আদায় করা, কারখানা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ধর্মঘট, মিটিং-মিছিল নিজেরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করত এবং মাঝেমধ্যে সফলতা লাভ করত।
‘সমান কাজের সমান মূল্য’ পুরুষ-নারীর সমান বেতন এবং বৃহত্তর সমাজে নারী-পুরুষের সমঅধিকার অর্জনের সংগ্রামে তারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তাদের দাবি মানতে বাধ্য হয়েই ড্যান্ডি টাউন কাউন্সিল কর্মজীবী মায়েদের শিশুদের দেখাশোনা করার জন্য ক্রেস ও নার্সারি প্রতিষ্ঠা করে এবং শুধুমাত্র নারীদের বসবাসের জন্য ঘরবাড়ি তৈরি করে।
ইংল্যান্ডে নারীদের ভোটের অধিকার অর্জনে ‘সাফরাজেট’ আন্দোলনে ড্যান্ডির নারী শ্রমিকেরা প্রভূত অবদান রাখে। তাদের কাজের দক্ষতা, অর্থনৈতিক শক্তি আর স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের মুখে ব্রিটিশ শাসক শ্রেণি অবশেষে ১৯১৮ সালে প্রথমবারের মতো নারীদের ভোটের অধিকার দিতে বাধ্য হয়। ড্যান্ডির নারীরা ১৯২২ সালের সাধারণ নির্বাচনে প্রথমবারের মতো ভোট দিয়ে তাদের নতুন অধিকারের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। তারা এই ভোটে নারীদের ভোটাধিকার বিরোধী, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কট্টর সমর্থক এবং ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলকে পরাজিত করে।
 বাংলার বস্ত্রবালিকারা
বাংলার বস্ত্রবালিকারা
পাট ব্যবসায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোনো উন্নতি হয়নি। বাংলার নেংটি পরা কৃষকদের ভাগ্য খোলেনি। কিন্তু ড্যান্ডি শহরের মেয়েরা পাটকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের ভাগ্য বদল করতে পেরেছিল। পুরো ব্রিটেনে, তথা পশ্চিম ইউরোপীয় মেয়েদের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রগামী ভূমিকা পালন করতে পেরেছিল।
ড্যান্ডির জুট মিউজিয়াম দেখছি, গাইডের কথা শুনছি, আর আমার কল্পনার চোখে ভেসে উঠছিল তাদেরই উত্তরসূরি পাটের দেশের মানুষ আমার স্বজাতি, অন্য এক তন্তু, তুলার কাপড় সেলাইয়ের কাজে নিয়োজিত ঢাকা শহরের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কর্মরত নারী শ্রমিকদের চেহারা। কী জুটছে তাদের কপালে?
আমি যখন বাংলাদেশে যাই, তখন এয়ারপোর্ট থেকে ফরিদপুর যাওয়ার পথে বাংলাদেশ গার্মেন্টস শিল্পের কেন্দ্রবিন্দু আশুলিয়া শিল্পাঞ্চলের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। আমি গাড়িতে বসে দেখি হাজার হাজার গার্মেন্টস শ্রমিক রাস্তার দুধারে সুশৃঙ্খলভাবে হেঁটে যাচ্ছে। রং-বেরঙের পোশাকে এরা সবাই দেখতে সুন্দর, প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। এরা সবাই নারী। এরাই বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। এদের সংখ্যা ৩২ লাখ। এরা বছরে ৩ দশমিক ১ লাখ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। তবুও গার্মেন্টস শ্রমিক নারীদের অবস্থা এমন কেন? বেতন কম, কাজের নিরাপত্তা নেই, জীবনের নিরাপত্তা নেই। কেন?
১৯৭২ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় ছিল ৯৪ ডলার বা ৮ হাজার ৪০০ টাকা। বর্তমানে তা ২ হাজার ৮৮২ ডলার বা ২ লাখ ৬০ হাজার টাকা। আমরা এখন পাকিস্তান ও ভারতকে ছাড়িয়ে গেছি এবং আরও ওপরে যাচ্ছি। কিন্তু যে শিলাখণ্ডের শক্ত ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে আমরা আরও ওপরে উঠছি, গার্মেন্টস শিল্পের সেই নারী শ্রমিকদের আমরা কতটা মর্যাদা দিতে শিখেছি? আশা করি বাংলাদেশের পাট যেমন একদিন পশ্চিমা দেশগুলোর নারীমুক্তিতে কার্যকারী ভূমিকা পালন করেছে, তেমনি আজকের দিনে বাংলাদেশ গার্মেন্টস শিল্পে কর্মরত নারীরা অদূর ভবিষ্যতে পূর্বাঞ্চলের দেশগুলোতে নারীমুক্তির সূচনা করবে।
 বাংলায় পাটকল ও ড্যান্ডির পতন
বাংলায় পাটকল ও ড্যান্ডির পতন
১৮৭০ সালে মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীরা কলকাতার প্রথম পাটকল প্রতিষ্ঠা করে। তখন থেকে এ ব্যবসায় ড্যান্ডির একচেটিয়া আধিপত্য কমতে থাকে। বিশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে কলকাতা পাটকলের শ্রমিক সংখ্যা ড্যান্ডিকে ছাড়িয়ে যায় এবং পরিবর্তনের গতিধারা অব্যাহত থাকে। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের তীব্রতা এই পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে। ১৯৪৭ সালের পর পাকিস্তান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্ব পাকিস্তানে নতুন নতুন এবং বড় বড় পাটকল প্রতিষ্ঠিত হলে ড্যান্ডির অবস্থা রাতারাতি বদলে যায়। ১৯৫০-এর দশকে সেখানে পাটকলের সংখ্যা পঞ্চাশের নিচে নেমে যায়।
১৯৯৮ সালের ১৯ অক্টোবর। চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ৩১০ টন কাঁচা পাট নিয়ে এমভি বাংলার ঊর্মি যখন স্কটল্যান্ডের ড্যান্ডি বন্দরে পৌঁছায়, তখন সে শহরের মিলের সংখ্যা ছিল মাত্র একটি। এর পর ড্যান্ডি বন্দরে আর কোনো দিন পাটের জাহাজ নোঙর করেনি।
শেষ লটের পাটের শেষ কোস্টার কাজ ১৯৯৯ সালের মে মাসে শেষ হলে, তায়েব্যাংক পাওয়ার লুমসের মালিক সব মেশিনপত্র বিক্রি করে দেয় কলকাতা পাটকলের মালিক জি জে ওয়াদওহার কাছে। ১৯৯৯ সালের আগস্ট মাসে ফিরতি যাত্রায় বাংলার ঊর্মি ড্যান্ডির শেষ পাটকলের শেষ যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে কলকাতা বন্দরে পৌঁছে দেয়। এ যেন বাংলার ছেলে বাংলায় ফিরে আসা।
 ‘দ্যাট ওয়াজ দি এন্ড’, বলে আমার গাইডের চোখ ছলছল করে উঠল। একজন বয়স্ক পুরুষের চোখে জল দেখে আমিও আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লাম। নরম সুরে জিজ্ঞেস করলাম, ‘তুমি এই মিলে কাজ করেছ নাকি?’ একটু মৃদু হেসে তিনি জবাব দিলেন, ‘না, আমার মা করেছে। আমি কাজের বয়সী হওয়ার আগেই এই মিল বন্ধ হয়ে গেছে। মায়ের মুখে অনেক গল্প শুনেছি। আমার মা এখন বেঁচে নেই। মাকে সম্মান জানানোর জন্য আমি সপ্তাহে একদিন এই জুট মিউজিয়ামে ভলান্টিয়ার গাইড হিসেবে কাজ করি। বেতন পাই না। কিন্তু আনন্দ পাই।’
‘দ্যাট ওয়াজ দি এন্ড’, বলে আমার গাইডের চোখ ছলছল করে উঠল। একজন বয়স্ক পুরুষের চোখে জল দেখে আমিও আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লাম। নরম সুরে জিজ্ঞেস করলাম, ‘তুমি এই মিলে কাজ করেছ নাকি?’ একটু মৃদু হেসে তিনি জবাব দিলেন, ‘না, আমার মা করেছে। আমি কাজের বয়সী হওয়ার আগেই এই মিল বন্ধ হয়ে গেছে। মায়ের মুখে অনেক গল্প শুনেছি। আমার মা এখন বেঁচে নেই। মাকে সম্মান জানানোর জন্য আমি সপ্তাহে একদিন এই জুট মিউজিয়ামে ভলান্টিয়ার গাইড হিসেবে কাজ করি। বেতন পাই না। কিন্তু আনন্দ পাই।’
এবার আমার চোখ ছলছল করে উঠল। পেছনে পরের ব্যাচের দর্শক জমা হয়ে গেছে, কথা বাড়াতে পারলাম না। ‘ইউ আর ডুয়িং এ গ্রেট জব, কিপ ইট আপ’, বললাম। হ্যান্ডশেক করে বিদায় নিলাম। সুভেনির শপে ঢুকতেই চোখে পড়ল একখানা বই ‘জুট নো মোর’। বইখানা কিনলাম।
লেখক: ডিরেক্টর, এশিয়ান রিসোর্স সেন্টার, বার্মিংহাম, ইংল্যান্ড

১৯২০-এর দশকের কোনো এক দিন। ড্যান্ডি শহরের কোনো এক জুট মিলের মালিক মাথায় সোলার হ্যাট পরে আমাদের ফরিদপুর শহরের পাটের বাজার দেখতে এসেছিলেন, দাদার মুখে সে গল্প শুনেছি।
সে ঘটনার প্রায় ১০২ বছর পর অবশেষে দেখলাম স্কটল্যান্ডের ড্যান্ডি শহরে বিশ্বের প্রথম জুটমিল। মিল ঠিক নয়, জুট মিউজিয়াম। পাট উৎপন্ন করত বাংলার কৃষক, আর সব পাটকল ছিল স্কটল্যান্ডে। সহজ বাংলা ভাষায় এরই নাম ছিল সাম্রাজ্যবাদ।
ভারডান্ট ওয়ার্কস মিউজিয়াম
‘গতস্য শোচনা নাস্তি’ অতি পুরোনো সংস্কৃত শ্লোক। তবুও বয়স্কা নর্তকী বারবার আয়না দেখে, বিগত যৌবনের সৌন্দর্য খোঁজে। আর বৃদ্ধ মানুষ চোখ বন্ধ করে বিগত যৌবনের সুখ চিন্তা করে। আমাদের এক কালের প্রভুদের অবস্থাও ঠিক তাই। এখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নেই, ড্যান্ডি শহরে জুট মিলও নেই। বন্ধ হয়ে যাওয়া একটা জুট মিলকে মিউজিয়াম বানিয়ে স্কটিশেরা পুরোনো শৌর্য ও ঐশ্বর্য মনে রাখার চেষ্টা করছে।
১৯৫৪ সালে হক-ভাসানি মুসলিম লীগকে ডুবিয়ে দিয়ে যেদিন সরকার গঠনের শপথ নিচ্ছিল, ঠিক সেই দিন নারায়ণগঞ্জের পাটকলে বিহারি আর বাঙালি শ্রমিকদের মধ্য রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা বাঁধিয়ে মুসলিম লীগের গুন্ডারা গণপ্রতিনিধিত্বের সরকারকে খাটো করবার চেষ্টা করেছিল। সে কথা ইতিহাস বইতে পড়েছি। ‘আমরা পাট রপ্তানি করে যে পরিমাণ বিদেশি টাকা আয় করি, তার বেশির ভাগ টাকা পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে ব্যয় করা হয়’, এই নিয়ে মুসলিম লীগ সমর্থকদের সঙ্গে ঝগড়া করেছি। বাংলার সোনালি আঁশ পাট। স্কুলের পরীক্ষায় ইংরেজি ভাষায় ‘জুট’ রচনা লিখেছি। কিন্তু হাজি আদমজীর ছেলেদের উদ্যোগে তৈরি, দাউদ, বাওয়ানী অথবা খোদ আদমজী জুট মিলটাও কোনো দিন দেখিনি। তাই স্কটল্যান্ডের ড্যান্ডি শহরে বেড়াতে এসে ‘ভারডান্ট ওয়ার্কস’ মিউজিয়াম দেখার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। সুন্দর সাজানো-গোছানো মিউজিয়ামের ভেতর পাটকলে ব্যবহার করা সব যন্ত্রপাতি দেখলাম, আর গাইডের মুখে শুনলাম এক রূপকথার গল্প।
 সোনালি আঁশের উত্থান
সোনালি আঁশের উত্থান
তিসির তেল আমরা বেশ চিনি। বাংলাদেশে তিসি ফলানো হয় মূলত তেলের জন্য। এ তেল কাঠের বার্নিশ উজ্জ্বল করে, আর ক্রিকেট ব্যাটের স্ট্রোক বাড়ায়। তবে মিসর ও জর্জিয়ায় তিসির চাষ করা করা হয় এ উদ্ভিদের ছাল থেকে সুতা তৈরির জন্য। তিসি গাছের ছাল পাটের মতো প্রক্রিয়াজাত করে যে সুতা বানানো হয়, তার ইংরেজি নাম ফ্ল্যাক্স। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ড্যান্ডি শহরে অনেকগুলো ফ্ল্যাক্স মিল ছিল। সেখানে এই সুতা দিয়ে মোটা ক্যানভাস ও লিনেন কাপড় তৈরি করা হতো। ড্যান্ডি শহরে ফ্ল্যাক্স আমদানি করা হতো কৃষ্ণ সাগর পারের ক্রিমিয়া ও জর্জিয়া অঞ্চল থেকে। রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের লড়াইয়ে উনিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে ফ্ল্যাক্সের উৎপাদন এবং সরবরাহ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।
প্রায় একই সময় কলকাতা বন্দরে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিকেরা ফ্ল্যাক্স আঁশের মতো দেখতে বাংলা পাটের প্রতি নজর দেয়। ১৮২০ সালে প্রথমবারের মতো আড়াই মন ওজনের একটি পাটের বেল ড্যান্ডি শহরে এসে পৌঁছায়।
কিন্তু পাটের আঁশ শক্ত। ফলে ফ্ল্যাক্সের বদলে পাট ব্যবহার করা গেল না। অনেক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেল যে, তিমি মাছের তেলে পাট ভেজালে তা নরম হয়, যা ফ্ল্যাক্স মিলে ব্যবহার কর যায়। তায়ে (Tay) নদীর তীরে অবস্থিত ড্যান্ডি নৌবন্দর অনেক আগে থেকেই তিমি মাছ ধরা এবং বেচাকেনার বাজার হিসেবে বিখ্যাত ছিল। সেখানে তিমি মাছের তেল সস্তায় এবং প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। লাভ-ক্ষতির অঙ্ক করতে ব্যাপারীদের বেশি সময় লাগল না। ড্যান্ডি শহরে ডেভিড লিন্ডসে তাঁর ফ্ল্যাক্স মিল ‘ভারডান্ট ওয়ার্কস’-এর কিছু বিবর্তন করে ১৮৩৫ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন বিশ্বের প্রথম জুট মিল বা পাটকল।
শুরু হলো পাটের অগ্রযাত্রা। একে একে ড্যান্ডির ফ্ল্যাক্স মিলগুলো জুট মিলে পরিণত হতে থাকল। ড্যান্ডি ডকইয়ার্ডে তৈরি হতে থাকল বড় বড় জাহাজ। ১৮৬৯ সালে সুয়েজ খাল খুলে গেলে এশিয়া আর ইউরোপের মধ্যে নৌপথের দূরত্ব কমে যায়। ফলে কাঁচা পাট কলকাতা বন্দর থেকে ৯০ দিনে ড্যান্ডি বন্দরে পৌঁছাতে থাকল। সোনায় সোহাগা। নতুন জুট মিল তৈরি হতে থাকল সেখানে। নেহাত বাংলা ঘরের ছনের চালে আটন-ছাটন আর রুয়া-ফুসসির বাঁধনে কাজে লাগা বাংলার পাট বিলেতি জুট মিলের সৌজন্যে হয়ে উঠল আন্তর্জাতিক বেস্ট সেলার এক পণ্য। আমাদের দেশের প্রধান অর্থকরী ফসল, যার নাম হলো সোনালি আঁশ। আর নারায়ণগঞ্জ নৌবন্দর বাংলার ড্যান্ডি নামে বিখ্যাত হলো।
 বাংলার পাট, ড্যান্ডির নারী
বাংলার পাট, ড্যান্ডির নারী
পাট হাটের ফড়িয়া, দালাল, আর পাট গুদামের মালিকদের ব্যাংক ব্যালান্স এবং পেটের ভুঁড়ি দুটোই সমানুপাতিক হারে বাড়তে থাকল। কুষ্টিয়া রেল স্টেশনের পাশে ঠাকুর অ্যান্ড কোম্পানির গুদাম খুলে, ধুতি কাছা দিয়ে পাটের ব্যবসায় নেমে গেলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তবে, কবির নোবেল প্রাইজ পাওয়া জ্ঞানে কাজ হলো না। পাটের ব্যবসা লাটে উঠল। ধনী হলো ড্যান্ডির জুটমিল মালিকেরা। দিনে দিনে, মাসে মাসে সেখানে বাড়তে থাকল পাটকলের সংখ্যা। ১৯০৯ সালে ড্যান্ডি শহরে ছিল ১৩০টি পাটকল। ১৯০১ সালে ড্যান্ডি শহরের মোট ৮৬ হাজার শ্রমিকের অর্ধেক ছিল পাট শ্রমিক। এর পঁচাত্তর ভাগ ছিল নারী।
হাতে চালানো তাঁতের কাজ কষ্টসাধ্য হওয়ায় তাঁত বুননের কাজে প্রথম দিকে নারী শ্রমিক নেওয়া হতো না। কিন্তু বৈদ্যুতিক তাঁত চালু হলে নারীরা পাটকলে কাজ করার উপযুক্ত বিবেচিত হয়। অর্থনৈতিক প্রয়োজন, ঘরের বাঁধন ছিঁড়ে বাইরে যাওয়ার উৎসাহ আর কম বেতনে কাজ করতে রাজি হওয়া বিপুলসংখ্যক নারী শ্রমিক পাটকলে নিয়োগ পেতে থাকে।
ড্যান্ডিতে এক সময় ৪১ হাজার পাটকল শ্রমিকের মধ্যে ৩১ হাজার ছিল নারী। সে শহরে নারীদের কাজ আছে, নগদ টাকায় বেতন আছে, নারী শ্রমিকদের মধ্যে কমরেডশিপ আছে—কথাগুলো পুরো স্কটল্যান্ডে ছড়িয়ে পড়ল। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, আর স্বাধীনচেতা নারীরা দলে দলে ড্যান্ডি শহরে আসতে থাকল। ১৯১১ সালে সেখানে প্রতি ১০০ জন পুরুষের অনুপাতে নারীর সংখ্যা ছিল ১৫০ জন। সে সময় ড্যান্ডি শহরের মেয়েরা বিয়ের জন্য ঘরজামাই খুঁজত। ছেলে রান্নাবান্না পারে কি না, বাচ্চাকাচ্চা দেখাশোনা করতে পারবে কি না, জামা কাপড় ধোয়া, ইস্তিরি করার কাজ করতে পারে কি না, বিয়ের জন্য এসব প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হতো ছেলেদের।
 কেটল-বয়লার, জ্যামের শহর কিংবা শি টাউনের গল্প
কেটল-বয়লার, জ্যামের শহর কিংবা শি টাউনের গল্প
এই শহরে শ্রমজীবী নারীরা বেকার পুরুষদের বিয়ে করে ঘরে রাখত, আর নিজেরা জুট মিলে কাজ করে টাকা উপার্জন করত। পুরুষেরা বাড়িতে বসে ঘর গৃহস্থালির অবসরে আশপাশের বাগান থেকে স্ট্রবেরি আর ব্ল্যাক কারেন্ট সংগ্রহ করে জ্যাম বানাত। সে সময় ড্যান্ডি ‘জ্যামের শহর’ বলেও প্রভূত খ্যাতি অর্জন করে। পাটের ফিরতি জাহাজে আসা ড্যান্ডির জ্যাম কলকাতার মধ্যবিত্তের ঘরে পৌঁছে যেত। এখন সে শহরে জ্যাম তৈরি হয় না। তবুও কলকাতার মধ্যবিত্ত ঘরে বিকেলের নাশতায় পাউরুটির টোস্ট, আর জ্যাম দিয়ে অতিথি আপ্যায়নের রেওয়াজ রয়ে গেছে।
এক কাপ চা দিয়ে অতিথি আপ্যায়নের রীতি ড্যান্ডি শহরেও ছিল। তবে চা বানানোর দায়িত্ব ছিল পুরুষদের। কেটলিতে পানি গরম করে চা বানাতে হতো। তাই ড্যান্ডির পুরুষদের নাম হয়ে যায় ‘কেটল-বয়লার’। স্কটল্যান্ডের অন্য শহরের মানুষ ড্যান্ডির নাম দেয় ‘শি টাউন’ বা ‘নারীদের শহর’। কিন্তু এ সমস্ত টিটকারি দেওয়া কথা ড্যান্ডির নারীদের একটুকুও বদলাতে পারেনি। তারা দিনে দশ ঘণ্টা কাজ করত। প্রয়োজন হলে রাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল করত। রাতে সুন্দর কাপড় পরে দলে দলে শহরে ঘুরে বেড়াত, থিয়েটার দেখত, নাইট ক্লাবে নাচত, পানাহার করত, আনন্দ ফুর্তি করত। তাদের আনন্দ ফুর্তির মাত্রা একটু বেশি হলে পুলিশ বাধা দিত। দুপক্ষের মধ্যে লড়াই বেধে যেত। কোনো কোনো রাতে ড্যান্ডি শহরের কেন্দ্রস্থল কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হতো। বিশ শতকের প্রথম দশকের কোনো এক বছর ড্যান্ডি শহরে শান্তি ভঙ্গের দায়ে হাজত খাটা ১ হাজার ৪০০ মানুষের মধ্যে ৮০০ জনই ছিল নারী।
উপমহাদেশের রক্ত শোষণ করে ধনী হওয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নারী বা পুরুষদের বাহবা দেওয়ার মানুষ আমি নই। তারপরও ড্যান্ডির নারীদের সাহসে বাহবা না দিয়ে পারি না।
 শি টাউনের নারীদের শ্রমিক আন্দোলন
শি টাউনের নারীদের শ্রমিক আন্দোলন
ড্যান্ডি শহরে শ্রমিক আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল জুট মিলের নারী শ্রমিকেরা। তবে তারা কোনো দিন পুরুষ নিয়ন্ত্রিত শ্রমিক সংগঠনের নিয়ম মেনে চলত না। তারা শ্রমের ন্যায্য মূল্য আদায় করা, কারখানা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ধর্মঘট, মিটিং-মিছিল নিজেরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করত এবং মাঝেমধ্যে সফলতা লাভ করত।
‘সমান কাজের সমান মূল্য’ পুরুষ-নারীর সমান বেতন এবং বৃহত্তর সমাজে নারী-পুরুষের সমঅধিকার অর্জনের সংগ্রামে তারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তাদের দাবি মানতে বাধ্য হয়েই ড্যান্ডি টাউন কাউন্সিল কর্মজীবী মায়েদের শিশুদের দেখাশোনা করার জন্য ক্রেস ও নার্সারি প্রতিষ্ঠা করে এবং শুধুমাত্র নারীদের বসবাসের জন্য ঘরবাড়ি তৈরি করে।
ইংল্যান্ডে নারীদের ভোটের অধিকার অর্জনে ‘সাফরাজেট’ আন্দোলনে ড্যান্ডির নারী শ্রমিকেরা প্রভূত অবদান রাখে। তাদের কাজের দক্ষতা, অর্থনৈতিক শক্তি আর স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের মুখে ব্রিটিশ শাসক শ্রেণি অবশেষে ১৯১৮ সালে প্রথমবারের মতো নারীদের ভোটের অধিকার দিতে বাধ্য হয়। ড্যান্ডির নারীরা ১৯২২ সালের সাধারণ নির্বাচনে প্রথমবারের মতো ভোট দিয়ে তাদের নতুন অধিকারের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। তারা এই ভোটে নারীদের ভোটাধিকার বিরোধী, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কট্টর সমর্থক এবং ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলকে পরাজিত করে।
 বাংলার বস্ত্রবালিকারা
বাংলার বস্ত্রবালিকারা
পাট ব্যবসায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোনো উন্নতি হয়নি। বাংলার নেংটি পরা কৃষকদের ভাগ্য খোলেনি। কিন্তু ড্যান্ডি শহরের মেয়েরা পাটকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের ভাগ্য বদল করতে পেরেছিল। পুরো ব্রিটেনে, তথা পশ্চিম ইউরোপীয় মেয়েদের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রগামী ভূমিকা পালন করতে পেরেছিল।
ড্যান্ডির জুট মিউজিয়াম দেখছি, গাইডের কথা শুনছি, আর আমার কল্পনার চোখে ভেসে উঠছিল তাদেরই উত্তরসূরি পাটের দেশের মানুষ আমার স্বজাতি, অন্য এক তন্তু, তুলার কাপড় সেলাইয়ের কাজে নিয়োজিত ঢাকা শহরের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কর্মরত নারী শ্রমিকদের চেহারা। কী জুটছে তাদের কপালে?
আমি যখন বাংলাদেশে যাই, তখন এয়ারপোর্ট থেকে ফরিদপুর যাওয়ার পথে বাংলাদেশ গার্মেন্টস শিল্পের কেন্দ্রবিন্দু আশুলিয়া শিল্পাঞ্চলের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। আমি গাড়িতে বসে দেখি হাজার হাজার গার্মেন্টস শ্রমিক রাস্তার দুধারে সুশৃঙ্খলভাবে হেঁটে যাচ্ছে। রং-বেরঙের পোশাকে এরা সবাই দেখতে সুন্দর, প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। এরা সবাই নারী। এরাই বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। এদের সংখ্যা ৩২ লাখ। এরা বছরে ৩ দশমিক ১ লাখ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। তবুও গার্মেন্টস শ্রমিক নারীদের অবস্থা এমন কেন? বেতন কম, কাজের নিরাপত্তা নেই, জীবনের নিরাপত্তা নেই। কেন?
১৯৭২ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় ছিল ৯৪ ডলার বা ৮ হাজার ৪০০ টাকা। বর্তমানে তা ২ হাজার ৮৮২ ডলার বা ২ লাখ ৬০ হাজার টাকা। আমরা এখন পাকিস্তান ও ভারতকে ছাড়িয়ে গেছি এবং আরও ওপরে যাচ্ছি। কিন্তু যে শিলাখণ্ডের শক্ত ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে আমরা আরও ওপরে উঠছি, গার্মেন্টস শিল্পের সেই নারী শ্রমিকদের আমরা কতটা মর্যাদা দিতে শিখেছি? আশা করি বাংলাদেশের পাট যেমন একদিন পশ্চিমা দেশগুলোর নারীমুক্তিতে কার্যকারী ভূমিকা পালন করেছে, তেমনি আজকের দিনে বাংলাদেশ গার্মেন্টস শিল্পে কর্মরত নারীরা অদূর ভবিষ্যতে পূর্বাঞ্চলের দেশগুলোতে নারীমুক্তির সূচনা করবে।
 বাংলায় পাটকল ও ড্যান্ডির পতন
বাংলায় পাটকল ও ড্যান্ডির পতন
১৮৭০ সালে মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীরা কলকাতার প্রথম পাটকল প্রতিষ্ঠা করে। তখন থেকে এ ব্যবসায় ড্যান্ডির একচেটিয়া আধিপত্য কমতে থাকে। বিশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে কলকাতা পাটকলের শ্রমিক সংখ্যা ড্যান্ডিকে ছাড়িয়ে যায় এবং পরিবর্তনের গতিধারা অব্যাহত থাকে। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের তীব্রতা এই পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে। ১৯৪৭ সালের পর পাকিস্তান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্ব পাকিস্তানে নতুন নতুন এবং বড় বড় পাটকল প্রতিষ্ঠিত হলে ড্যান্ডির অবস্থা রাতারাতি বদলে যায়। ১৯৫০-এর দশকে সেখানে পাটকলের সংখ্যা পঞ্চাশের নিচে নেমে যায়।
১৯৯৮ সালের ১৯ অক্টোবর। চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ৩১০ টন কাঁচা পাট নিয়ে এমভি বাংলার ঊর্মি যখন স্কটল্যান্ডের ড্যান্ডি বন্দরে পৌঁছায়, তখন সে শহরের মিলের সংখ্যা ছিল মাত্র একটি। এর পর ড্যান্ডি বন্দরে আর কোনো দিন পাটের জাহাজ নোঙর করেনি।
শেষ লটের পাটের শেষ কোস্টার কাজ ১৯৯৯ সালের মে মাসে শেষ হলে, তায়েব্যাংক পাওয়ার লুমসের মালিক সব মেশিনপত্র বিক্রি করে দেয় কলকাতা পাটকলের মালিক জি জে ওয়াদওহার কাছে। ১৯৯৯ সালের আগস্ট মাসে ফিরতি যাত্রায় বাংলার ঊর্মি ড্যান্ডির শেষ পাটকলের শেষ যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে কলকাতা বন্দরে পৌঁছে দেয়। এ যেন বাংলার ছেলে বাংলায় ফিরে আসা।
 ‘দ্যাট ওয়াজ দি এন্ড’, বলে আমার গাইডের চোখ ছলছল করে উঠল। একজন বয়স্ক পুরুষের চোখে জল দেখে আমিও আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লাম। নরম সুরে জিজ্ঞেস করলাম, ‘তুমি এই মিলে কাজ করেছ নাকি?’ একটু মৃদু হেসে তিনি জবাব দিলেন, ‘না, আমার মা করেছে। আমি কাজের বয়সী হওয়ার আগেই এই মিল বন্ধ হয়ে গেছে। মায়ের মুখে অনেক গল্প শুনেছি। আমার মা এখন বেঁচে নেই। মাকে সম্মান জানানোর জন্য আমি সপ্তাহে একদিন এই জুট মিউজিয়ামে ভলান্টিয়ার গাইড হিসেবে কাজ করি। বেতন পাই না। কিন্তু আনন্দ পাই।’
‘দ্যাট ওয়াজ দি এন্ড’, বলে আমার গাইডের চোখ ছলছল করে উঠল। একজন বয়স্ক পুরুষের চোখে জল দেখে আমিও আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লাম। নরম সুরে জিজ্ঞেস করলাম, ‘তুমি এই মিলে কাজ করেছ নাকি?’ একটু মৃদু হেসে তিনি জবাব দিলেন, ‘না, আমার মা করেছে। আমি কাজের বয়সী হওয়ার আগেই এই মিল বন্ধ হয়ে গেছে। মায়ের মুখে অনেক গল্প শুনেছি। আমার মা এখন বেঁচে নেই। মাকে সম্মান জানানোর জন্য আমি সপ্তাহে একদিন এই জুট মিউজিয়ামে ভলান্টিয়ার গাইড হিসেবে কাজ করি। বেতন পাই না। কিন্তু আনন্দ পাই।’
এবার আমার চোখ ছলছল করে উঠল। পেছনে পরের ব্যাচের দর্শক জমা হয়ে গেছে, কথা বাড়াতে পারলাম না। ‘ইউ আর ডুয়িং এ গ্রেট জব, কিপ ইট আপ’, বললাম। হ্যান্ডশেক করে বিদায় নিলাম। সুভেনির শপে ঢুকতেই চোখে পড়ল একখানা বই ‘জুট নো মোর’। বইখানা কিনলাম।
লেখক: ডিরেক্টর, এশিয়ান রিসোর্স সেন্টার, বার্মিংহাম, ইংল্যান্ড

আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, স্বাধীনতা-সংগ্রামী, কবি-লেখক চিত্তরঞ্জন দাশ ‘দেশবন্ধু’ নামেই বিখ্যাত। তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন শচীমোহন গোপ, যিনি পঞ্চাশের দশকে রাস্তার মোড়ে বিক্রি করতেন দুধ, দই আর মাঠা। ১৯৫৮ সালে হাটখোলা রোডে ইত্তেফাক মোড়ে রেস্তোরাঁ খুলে বসেন।
২ দিন আগে
কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে কবি শাহীনা সোবহানের সম্মানে কবি ও সাহিত্যিকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে সাহিত্য আড্ডা। গতকাল শনিবার (১৮ অক্টোবর) বিকেলে কুমারখালী পৌর শহরের সাংবাদিক কাঙাল হরিনাথ মজুমদার স্মৃতি জাদুঘরে ড. নাসের ফাউন্ডেশনের আয়োজনে এই আড্ডার আয়োজন করা হয়।
৫ দিন আগে
১৯৬০-এর দশকে হাজি নান্না মিয়া তাঁর দুই ভাই জুম্মুন মিয়া ও চান মিয়ার সঙ্গে শুরু করেন খাবারের ব্যবসা। পুরান ঢাকার মৌলভীবাজারে ছোট্ট একটা দোকানে পাতলা মাদুর বিছিয়ে তাঁরা পরিবেশন করতেন মোরগ পোলাও। সেই মোরগ পোলাওয়ের সুঘ্রাণের সঙ্গে এর সুখ্যাতি ছড়াতে সময় লাগেনি। মৌলভীবাজার থেকে পরে বেচারাম দেউড়ির...
৭ দিন আগে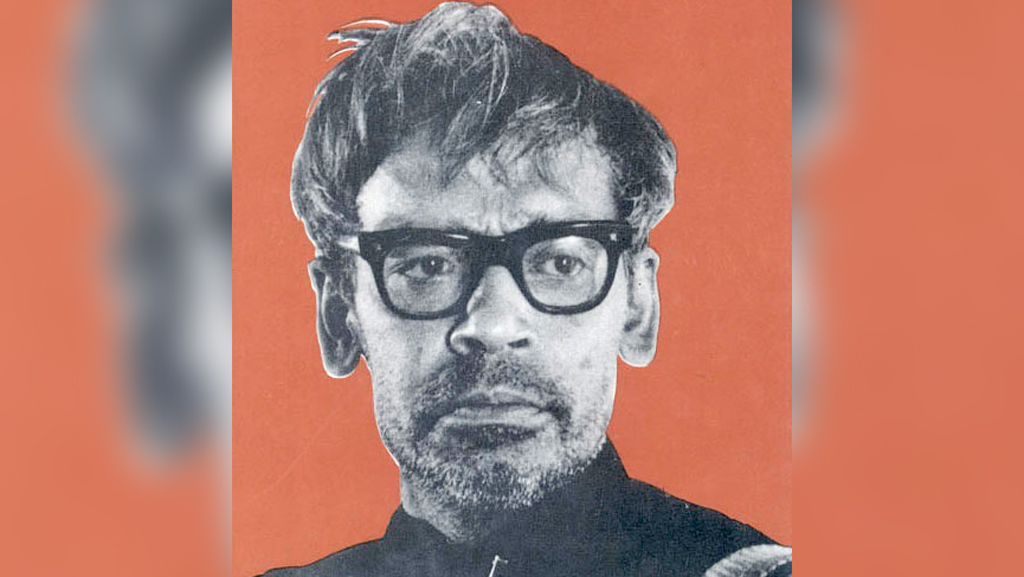
চলচ্চিত্র নির্মাণের পদ্ধতি-টদ্ধতি বুঝি না মশাই। আমার কাছে আজও প্রমথেশ বড়ুয়া ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালক। আমরা কেউই তাঁর পায়ের নখের যোগ্য নই। আমার আজও মনে পড়ে ‘গৃহদাহ’র সেই অসম্ভব ট্রানজিশন—সেই যে হাইহিল জুতো-পরা দুটো পা থেকে সোজা কেটে দুটো আলতা-মাখা পা পালকি থেকে নামছে—আমি কখনো ভুলব না।
৮ দিন আগেসম্পাদকীয়

আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, স্বাধীনতা-সংগ্রামী, কবি-লেখক চিত্তরঞ্জন দাশ ‘দেশবন্ধু’ নামেই বিখ্যাত। তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন শচীমোহন গোপ, যিনি পঞ্চাশের দশকে রাস্তার মোড়ে বিক্রি করতেন দুধ, দই আর মাঠা। ১৯৫৮ সালে হাটখোলা রোডে ইত্তেফাক মোড়ে রেস্তোরাঁ খুলে বসেন। বলা হয়, চিত্তরঞ্জন দাশের জীবনদর্শনে প্রভাবিত হয়েই শচীমোহন রেস্তোরাঁটির নাম দেন ‘দেশবন্ধু সুইটমিট অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট’। এর উল্টো দিকে তখন ছিল ইত্তেফাক পত্রিকার অফিস।
সেখানকার সাংবাদিকেরা দেশবন্ধুর পরোটা-লুচি-ভাজি-হালুয়া খেতে যেতেন নিয়মিত। কবি-সাহিত্যিক-অভিনয়শিল্পীরাও পছন্দ করতেন এই রেস্তোরাঁর খাবার। এমনকি এফডিসিতে ফরমাশ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো দেশবন্ধুর নাশতা। এখন হয়তো মানিক মিয়া, রাজ্জাক, কবরী কিংবা শাবানাদের মতো বিখ্যাতরা সেখানে যান না কিন্তু তাতে দেশবন্ধুর জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েনি একটুও। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এখনো ঢাকাবাসীর ভিড় দেখা যায় এই রেস্তোরাঁয়। ভাবা যায়, সারা দিনই এখানকার পরোটা-ভাজি বিক্রি হতে থাকে! দুপুরে অবশ্য খাবারের তালিকায় ভাত-মাছ-মাংসও আছে। ছবি: মেহেদী হাসান

আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, স্বাধীনতা-সংগ্রামী, কবি-লেখক চিত্তরঞ্জন দাশ ‘দেশবন্ধু’ নামেই বিখ্যাত। তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন শচীমোহন গোপ, যিনি পঞ্চাশের দশকে রাস্তার মোড়ে বিক্রি করতেন দুধ, দই আর মাঠা। ১৯৫৮ সালে হাটখোলা রোডে ইত্তেফাক মোড়ে রেস্তোরাঁ খুলে বসেন। বলা হয়, চিত্তরঞ্জন দাশের জীবনদর্শনে প্রভাবিত হয়েই শচীমোহন রেস্তোরাঁটির নাম দেন ‘দেশবন্ধু সুইটমিট অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট’। এর উল্টো দিকে তখন ছিল ইত্তেফাক পত্রিকার অফিস।
সেখানকার সাংবাদিকেরা দেশবন্ধুর পরোটা-লুচি-ভাজি-হালুয়া খেতে যেতেন নিয়মিত। কবি-সাহিত্যিক-অভিনয়শিল্পীরাও পছন্দ করতেন এই রেস্তোরাঁর খাবার। এমনকি এফডিসিতে ফরমাশ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো দেশবন্ধুর নাশতা। এখন হয়তো মানিক মিয়া, রাজ্জাক, কবরী কিংবা শাবানাদের মতো বিখ্যাতরা সেখানে যান না কিন্তু তাতে দেশবন্ধুর জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েনি একটুও। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এখনো ঢাকাবাসীর ভিড় দেখা যায় এই রেস্তোরাঁয়। ভাবা যায়, সারা দিনই এখানকার পরোটা-ভাজি বিক্রি হতে থাকে! দুপুরে অবশ্য খাবারের তালিকায় ভাত-মাছ-মাংসও আছে। ছবি: মেহেদী হাসান

ডান্ডি শহরে ডেভিড লিন্ডসে তাঁর ফ্ল্যাক্স মিল ‘ভারডান্ট ওয়ার্কস’এর কিছু বিবর্তন করে ১৮৩৫ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন বিশ্বের প্রথম জুট মিল বা পাটকল।
২১ জুন ২০২২
কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে কবি শাহীনা সোবহানের সম্মানে কবি ও সাহিত্যিকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে সাহিত্য আড্ডা। গতকাল শনিবার (১৮ অক্টোবর) বিকেলে কুমারখালী পৌর শহরের সাংবাদিক কাঙাল হরিনাথ মজুমদার স্মৃতি জাদুঘরে ড. নাসের ফাউন্ডেশনের আয়োজনে এই আড্ডার আয়োজন করা হয়।
৫ দিন আগে
১৯৬০-এর দশকে হাজি নান্না মিয়া তাঁর দুই ভাই জুম্মুন মিয়া ও চান মিয়ার সঙ্গে শুরু করেন খাবারের ব্যবসা। পুরান ঢাকার মৌলভীবাজারে ছোট্ট একটা দোকানে পাতলা মাদুর বিছিয়ে তাঁরা পরিবেশন করতেন মোরগ পোলাও। সেই মোরগ পোলাওয়ের সুঘ্রাণের সঙ্গে এর সুখ্যাতি ছড়াতে সময় লাগেনি। মৌলভীবাজার থেকে পরে বেচারাম দেউড়ির...
৭ দিন আগে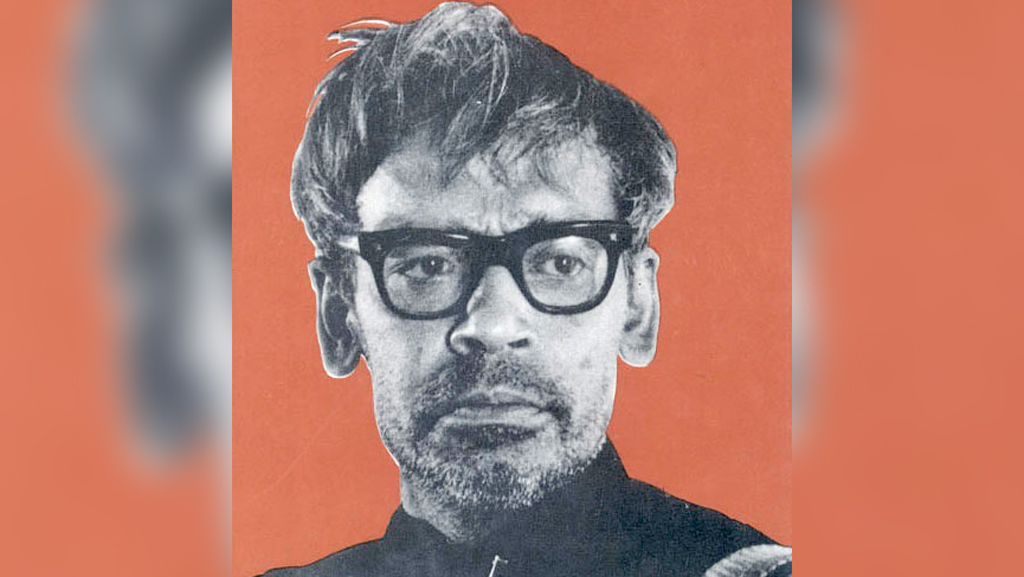
চলচ্চিত্র নির্মাণের পদ্ধতি-টদ্ধতি বুঝি না মশাই। আমার কাছে আজও প্রমথেশ বড়ুয়া ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালক। আমরা কেউই তাঁর পায়ের নখের যোগ্য নই। আমার আজও মনে পড়ে ‘গৃহদাহ’র সেই অসম্ভব ট্রানজিশন—সেই যে হাইহিল জুতো-পরা দুটো পা থেকে সোজা কেটে দুটো আলতা-মাখা পা পালকি থেকে নামছে—আমি কখনো ভুলব না।
৮ দিন আগেকুমারখালী (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে কবি শাহীনা সোবহানের সম্মানে কবি ও সাহিত্যিকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে সাহিত্য আড্ডা। গতকাল শনিবার (১৮ অক্টোবর) বিকেলে কুমারখালী পৌর শহরের সাংবাদিক কাঙাল হরিনাথ মজুমদার স্মৃতি জাদুঘরে ড. নাসের ফাউন্ডেশনের আয়োজনে এই আড্ডার আয়োজন করা হয়।
কবি ও নাট্যকার লিটন আব্বাসের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সদস্য ও সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশনের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক সৈয়দা শাহীনা সোবহান।
ড. নাসের ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. আবু নাসের রাজীবের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় কিডনি ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক জামানুল ইসলাম ভূঁইয়া, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা বিশ্বজিৎ সাহা, কুমারখালী সাহিত্য সংসদের সভাপতি কবি রহমান আজিজ, কবি রজত হুদা ও কবি সবুর বাদশা। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন কবি ও কথাসাহিত্যিক সোহেল আমিন বাবু, কবি বাবলু জোয়ার্দার, কবি ও সাংবাদিক মাহমুদ শরীফ, জিটিভির কুষ্টিয়া প্রতিনিধি সাংবাদিক কাজী সাইফুল, দৈনিক নয়া দিগন্তের কুষ্টিয়া প্রতিনিধি (মাল্টিমিডিয়া) সোহাগ মাহমুদ প্রমুখ।
এ সাহিত্য আড্ডায় কুষ্টিয়া ও কুমারখালীর কবি-সাহিত্যিকেরা অংশ নিয়ে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন সংগীতশিল্পী জিয়াউর রহমান মানিক।

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে কবি শাহীনা সোবহানের সম্মানে কবি ও সাহিত্যিকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে সাহিত্য আড্ডা। গতকাল শনিবার (১৮ অক্টোবর) বিকেলে কুমারখালী পৌর শহরের সাংবাদিক কাঙাল হরিনাথ মজুমদার স্মৃতি জাদুঘরে ড. নাসের ফাউন্ডেশনের আয়োজনে এই আড্ডার আয়োজন করা হয়।
কবি ও নাট্যকার লিটন আব্বাসের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সদস্য ও সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশনের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক সৈয়দা শাহীনা সোবহান।
ড. নাসের ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. আবু নাসের রাজীবের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় কিডনি ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক জামানুল ইসলাম ভূঁইয়া, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা বিশ্বজিৎ সাহা, কুমারখালী সাহিত্য সংসদের সভাপতি কবি রহমান আজিজ, কবি রজত হুদা ও কবি সবুর বাদশা। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন কবি ও কথাসাহিত্যিক সোহেল আমিন বাবু, কবি বাবলু জোয়ার্দার, কবি ও সাংবাদিক মাহমুদ শরীফ, জিটিভির কুষ্টিয়া প্রতিনিধি সাংবাদিক কাজী সাইফুল, দৈনিক নয়া দিগন্তের কুষ্টিয়া প্রতিনিধি (মাল্টিমিডিয়া) সোহাগ মাহমুদ প্রমুখ।
এ সাহিত্য আড্ডায় কুষ্টিয়া ও কুমারখালীর কবি-সাহিত্যিকেরা অংশ নিয়ে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন সংগীতশিল্পী জিয়াউর রহমান মানিক।

ডান্ডি শহরে ডেভিড লিন্ডসে তাঁর ফ্ল্যাক্স মিল ‘ভারডান্ট ওয়ার্কস’এর কিছু বিবর্তন করে ১৮৩৫ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন বিশ্বের প্রথম জুট মিল বা পাটকল।
২১ জুন ২০২২
আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, স্বাধীনতা-সংগ্রামী, কবি-লেখক চিত্তরঞ্জন দাশ ‘দেশবন্ধু’ নামেই বিখ্যাত। তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন শচীমোহন গোপ, যিনি পঞ্চাশের দশকে রাস্তার মোড়ে বিক্রি করতেন দুধ, দই আর মাঠা। ১৯৫৮ সালে হাটখোলা রোডে ইত্তেফাক মোড়ে রেস্তোরাঁ খুলে বসেন।
২ দিন আগে
১৯৬০-এর দশকে হাজি নান্না মিয়া তাঁর দুই ভাই জুম্মুন মিয়া ও চান মিয়ার সঙ্গে শুরু করেন খাবারের ব্যবসা। পুরান ঢাকার মৌলভীবাজারে ছোট্ট একটা দোকানে পাতলা মাদুর বিছিয়ে তাঁরা পরিবেশন করতেন মোরগ পোলাও। সেই মোরগ পোলাওয়ের সুঘ্রাণের সঙ্গে এর সুখ্যাতি ছড়াতে সময় লাগেনি। মৌলভীবাজার থেকে পরে বেচারাম দেউড়ির...
৭ দিন আগে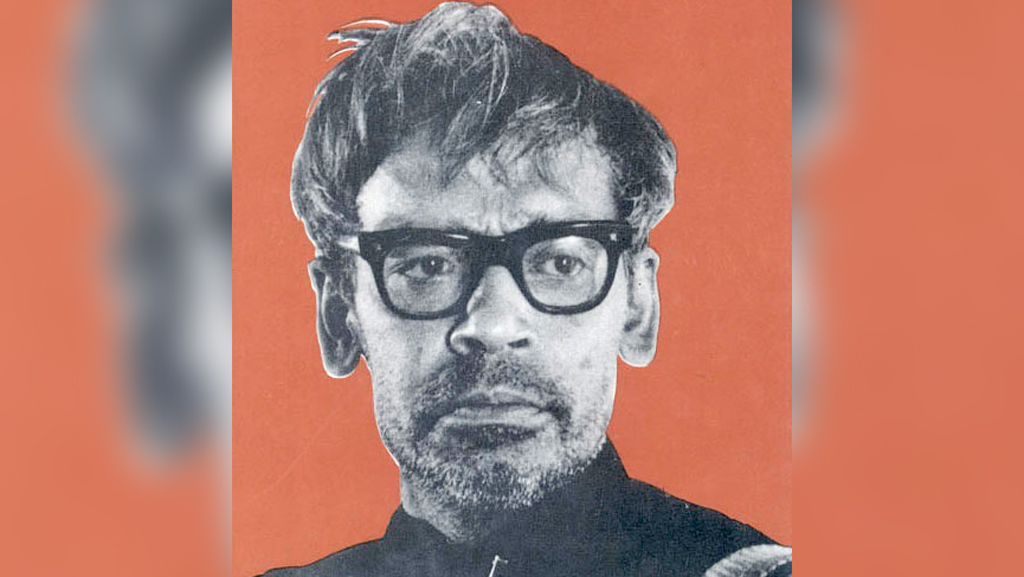
চলচ্চিত্র নির্মাণের পদ্ধতি-টদ্ধতি বুঝি না মশাই। আমার কাছে আজও প্রমথেশ বড়ুয়া ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালক। আমরা কেউই তাঁর পায়ের নখের যোগ্য নই। আমার আজও মনে পড়ে ‘গৃহদাহ’র সেই অসম্ভব ট্রানজিশন—সেই যে হাইহিল জুতো-পরা দুটো পা থেকে সোজা কেটে দুটো আলতা-মাখা পা পালকি থেকে নামছে—আমি কখনো ভুলব না।
৮ দিন আগেসম্পাদকীয়

১৯৬০-এর দশকে হাজি নান্না মিয়া তাঁর দুই ভাই জুম্মুন মিয়া ও চান মিয়ার সঙ্গে শুরু করেন খাবারের ব্যবসা। পুরান ঢাকার মৌলভীবাজারে ছোট্ট একটা দোকানে পাতলা মাদুর বিছিয়ে তাঁরা পরিবেশন করতেন মোরগ পোলাও। সেই মোরগ পোলাওয়ের সুঘ্রাণের সঙ্গে এর সুখ্যাতি ছড়াতে সময় লাগেনি। মৌলভীবাজার থেকে পরে বেচারাম দেউড়ির সরদার ভবনে সরে আসে নান্না মিয়ার ব্যবসা। দোকানের নাম হয় হাজি নান্না বিরিয়ানি।
একে একে লালবাগ চৌরাস্তা, নবাবগঞ্জ বাজার, ফকিরাপুল ও নাজিমুদ্দিন রোডে এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। একই নামে শত শত ভুয়া প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও আসল নান্নার মোরগ পোলাওয়ের স্বাদকে টেক্কা দিতে পারেনি কেউ। তাই তো ভোজনপ্রেমীরা ঠিকই চিনে নেন আদি রেসিপিটি। মোরগ পোলাওয়ের পাশাপাশি হাজি নান্না বিরিয়ানিতে পাওয়া যায় খাসির বিরিয়ানি, খাসির কাচ্চি বিরিয়ানি, বোরহানি, টিকিয়া, লাবাং ও ফিরনি। প্রতি মাসের ৫ তারিখে থাকে বিশেষ আয়োজন—আস্ত মুরগির পোলাও। ছবি: জাহিদুল ইসলাম

১৯৬০-এর দশকে হাজি নান্না মিয়া তাঁর দুই ভাই জুম্মুন মিয়া ও চান মিয়ার সঙ্গে শুরু করেন খাবারের ব্যবসা। পুরান ঢাকার মৌলভীবাজারে ছোট্ট একটা দোকানে পাতলা মাদুর বিছিয়ে তাঁরা পরিবেশন করতেন মোরগ পোলাও। সেই মোরগ পোলাওয়ের সুঘ্রাণের সঙ্গে এর সুখ্যাতি ছড়াতে সময় লাগেনি। মৌলভীবাজার থেকে পরে বেচারাম দেউড়ির সরদার ভবনে সরে আসে নান্না মিয়ার ব্যবসা। দোকানের নাম হয় হাজি নান্না বিরিয়ানি।
একে একে লালবাগ চৌরাস্তা, নবাবগঞ্জ বাজার, ফকিরাপুল ও নাজিমুদ্দিন রোডে এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। একই নামে শত শত ভুয়া প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও আসল নান্নার মোরগ পোলাওয়ের স্বাদকে টেক্কা দিতে পারেনি কেউ। তাই তো ভোজনপ্রেমীরা ঠিকই চিনে নেন আদি রেসিপিটি। মোরগ পোলাওয়ের পাশাপাশি হাজি নান্না বিরিয়ানিতে পাওয়া যায় খাসির বিরিয়ানি, খাসির কাচ্চি বিরিয়ানি, বোরহানি, টিকিয়া, লাবাং ও ফিরনি। প্রতি মাসের ৫ তারিখে থাকে বিশেষ আয়োজন—আস্ত মুরগির পোলাও। ছবি: জাহিদুল ইসলাম

ডান্ডি শহরে ডেভিড লিন্ডসে তাঁর ফ্ল্যাক্স মিল ‘ভারডান্ট ওয়ার্কস’এর কিছু বিবর্তন করে ১৮৩৫ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন বিশ্বের প্রথম জুট মিল বা পাটকল।
২১ জুন ২০২২
আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, স্বাধীনতা-সংগ্রামী, কবি-লেখক চিত্তরঞ্জন দাশ ‘দেশবন্ধু’ নামেই বিখ্যাত। তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন শচীমোহন গোপ, যিনি পঞ্চাশের দশকে রাস্তার মোড়ে বিক্রি করতেন দুধ, দই আর মাঠা। ১৯৫৮ সালে হাটখোলা রোডে ইত্তেফাক মোড়ে রেস্তোরাঁ খুলে বসেন।
২ দিন আগে
কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে কবি শাহীনা সোবহানের সম্মানে কবি ও সাহিত্যিকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে সাহিত্য আড্ডা। গতকাল শনিবার (১৮ অক্টোবর) বিকেলে কুমারখালী পৌর শহরের সাংবাদিক কাঙাল হরিনাথ মজুমদার স্মৃতি জাদুঘরে ড. নাসের ফাউন্ডেশনের আয়োজনে এই আড্ডার আয়োজন করা হয়।
৫ দিন আগে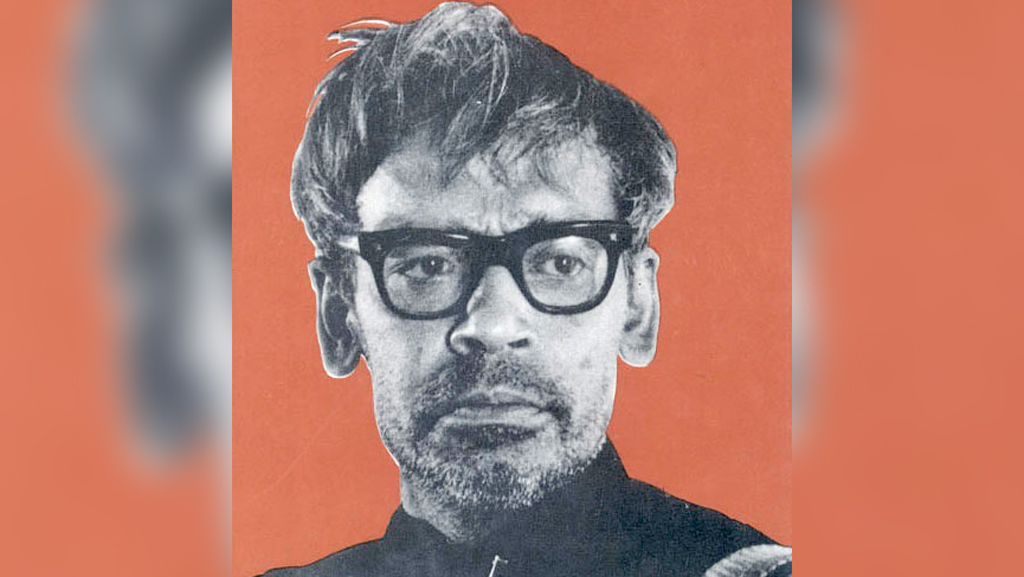
চলচ্চিত্র নির্মাণের পদ্ধতি-টদ্ধতি বুঝি না মশাই। আমার কাছে আজও প্রমথেশ বড়ুয়া ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালক। আমরা কেউই তাঁর পায়ের নখের যোগ্য নই। আমার আজও মনে পড়ে ‘গৃহদাহ’র সেই অসম্ভব ট্রানজিশন—সেই যে হাইহিল জুতো-পরা দুটো পা থেকে সোজা কেটে দুটো আলতা-মাখা পা পালকি থেকে নামছে—আমি কখনো ভুলব না।
৮ দিন আগেসম্পাদকীয়
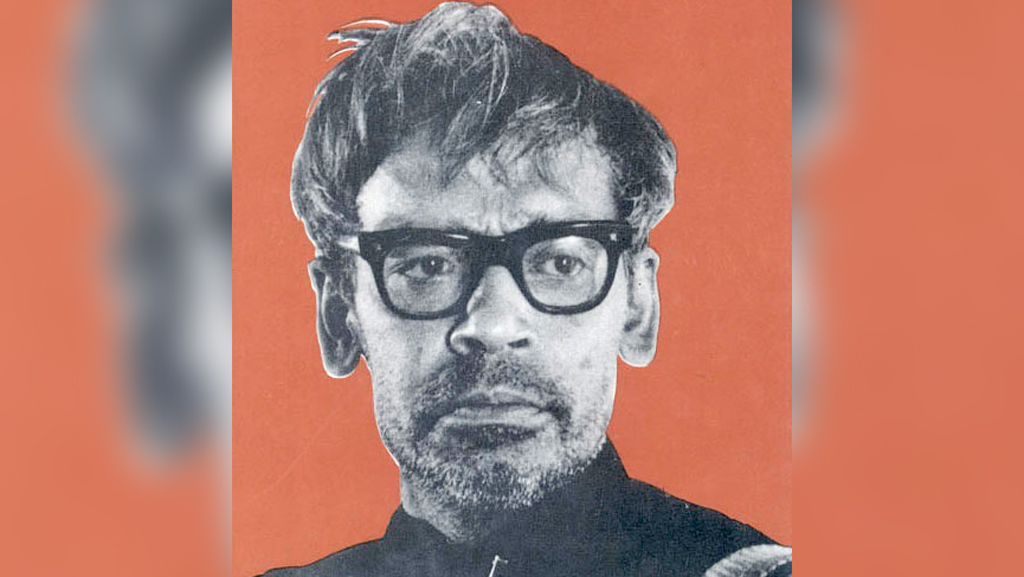
চলচ্চিত্র নির্মাণের পদ্ধতি-টদ্ধতি বুঝি না মশাই। আমার কাছে আজও প্রমথেশ বড়ুয়া ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালক। আমরা কেউই তাঁর পায়ের নখের যোগ্য নই। আমার আজও মনে পড়ে ‘গৃহদাহ’র সেই অসম্ভব ট্রানজিশন—সেই যে হাইহিল জুতো-পরা দুটো পা থেকে সোজা কেটে দুটো আলতা-মাখা পা পালকি থেকে নামছে—আমি কখনো ভুলব না। ব্যাপারটা ভদ্রলোক করেছিলেন ১৯৩৬ সালে, এ কথা ভুলবেন না। আর সেই যে সেই ‘উত্তরায়ণ’-এ বড়ুয়া সাহেবের জ্বর হওয়ার পরে ক্যামেরা সোজা সিঁড়ি দিয়ে উঠে বিছানায় গিয়ে আছড়ে পড়ল—সেটাই কি ভোলা যায়! কাণ্ডটা ঘটিয়েছেন ভদ্রলোক ডেভিড লিনের ‘অলিভার টুইস্ট’-এর বহু আগে। সাবজেকটিভ ক্যামেরা সম্পর্কে অনেক কথা আজকাল শুনতে পাই, বিভিন্ন পরিচালক নাকি খুব ভালোভাবে ব্যবহার করছেন।
...আমার কাছে গুলিয়ে গেছে সিনেমার প্রাচীন আর আধুনিক বলতে আপনারা কী বোঝাতে চেয়েছেন। এসব ধরনের কথা শুনলে আমার একটা কথাই মনে হয়, কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায় ‘দে গরুর গা ধুইয়ে’।
...চলচ্চিত্রের সামাজিক দায়িত্ব সব সময়ে হয়েছে। হয় পজিটিভ, না হয় নেগেটিভভাবে। ছবিটাকে আমি একটা শিল্প বলি। কাজেই মনে করি সর্বশিল্পের শর্ত পালিত হচ্ছে এখানেও। আমি মনে করি না যে সত্যজিৎ রায়ের ‘চারুলতা’ চ্যাপলিনের ‘এসানে’ যুগের এক রিলের ছবিগুলোর চেয়ে বেশি সচেতন।
১৯২৫ সালে তোলা আইজেনস্টাইনের ‘স্ট্রাইক’ ছবির চেয়ে বেশি সমাজসচেতন ছবি কি আজ পর্যন্ত তোলা হয়েছে? পাবস্ট-এর ‘কামেরা ডে শেফট’ আজও পর্যন্ত আমার কাছে মনে হয় সবচেয়ে বেশি সমাজসচেতন একটি ছবি। চারু রায়ের ‘বাংলার মেয়ে’ বহু আগে তোলা—প্রথম বাংলা ছবি, যাতে আউটডোর ব্যবহৃত হয় সবচেয়ে বেশিভাবে, তাতেও সমাজচেতনা পরিপূর্ণ ছিল।
...রবিঠাকুর মশায় একটা বড় ভালো কথা বলে গিয়েছিলেন, ‘শিল্পকে শিল্প হতে হলে সর্বাগ্রে সত্যনিষ্ঠ হতে হয়, তারপরে সৌন্দর্যনিষ্ঠ’। কথাটা ভাবার মতো। যদি পারেন ভেবে দেখবেন।
সূত্র: ঋত্বিক ঘটকের গৃহীত সাক্ষাৎকার, ‘সাক্ষাৎ ঋত্বিক’, শিবাদিত্য দাশগুপ্ত ও সন্দীপন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ১৮-১৯
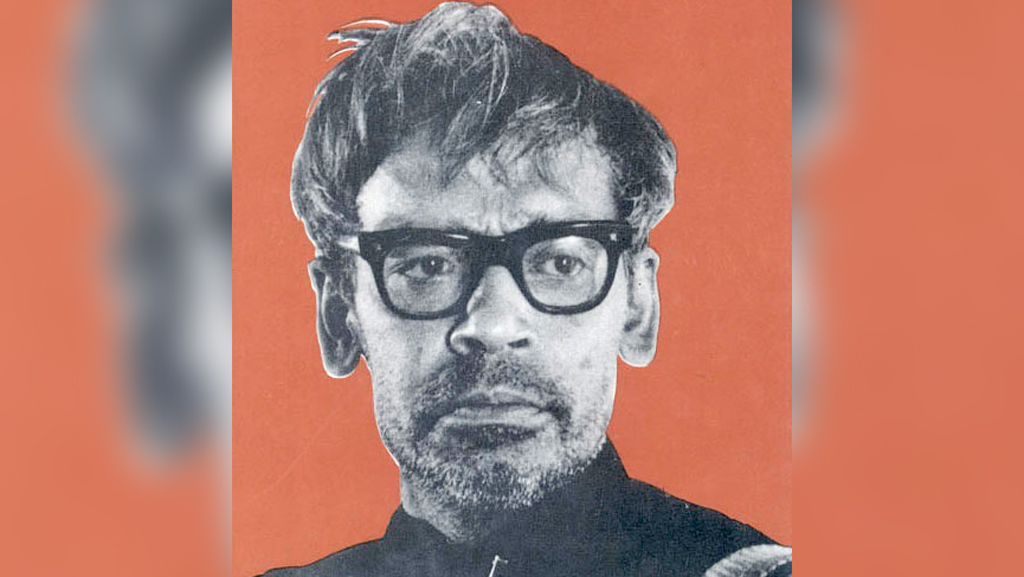
চলচ্চিত্র নির্মাণের পদ্ধতি-টদ্ধতি বুঝি না মশাই। আমার কাছে আজও প্রমথেশ বড়ুয়া ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালক। আমরা কেউই তাঁর পায়ের নখের যোগ্য নই। আমার আজও মনে পড়ে ‘গৃহদাহ’র সেই অসম্ভব ট্রানজিশন—সেই যে হাইহিল জুতো-পরা দুটো পা থেকে সোজা কেটে দুটো আলতা-মাখা পা পালকি থেকে নামছে—আমি কখনো ভুলব না। ব্যাপারটা ভদ্রলোক করেছিলেন ১৯৩৬ সালে, এ কথা ভুলবেন না। আর সেই যে সেই ‘উত্তরায়ণ’-এ বড়ুয়া সাহেবের জ্বর হওয়ার পরে ক্যামেরা সোজা সিঁড়ি দিয়ে উঠে বিছানায় গিয়ে আছড়ে পড়ল—সেটাই কি ভোলা যায়! কাণ্ডটা ঘটিয়েছেন ভদ্রলোক ডেভিড লিনের ‘অলিভার টুইস্ট’-এর বহু আগে। সাবজেকটিভ ক্যামেরা সম্পর্কে অনেক কথা আজকাল শুনতে পাই, বিভিন্ন পরিচালক নাকি খুব ভালোভাবে ব্যবহার করছেন।
...আমার কাছে গুলিয়ে গেছে সিনেমার প্রাচীন আর আধুনিক বলতে আপনারা কী বোঝাতে চেয়েছেন। এসব ধরনের কথা শুনলে আমার একটা কথাই মনে হয়, কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায় ‘দে গরুর গা ধুইয়ে’।
...চলচ্চিত্রের সামাজিক দায়িত্ব সব সময়ে হয়েছে। হয় পজিটিভ, না হয় নেগেটিভভাবে। ছবিটাকে আমি একটা শিল্প বলি। কাজেই মনে করি সর্বশিল্পের শর্ত পালিত হচ্ছে এখানেও। আমি মনে করি না যে সত্যজিৎ রায়ের ‘চারুলতা’ চ্যাপলিনের ‘এসানে’ যুগের এক রিলের ছবিগুলোর চেয়ে বেশি সচেতন।
১৯২৫ সালে তোলা আইজেনস্টাইনের ‘স্ট্রাইক’ ছবির চেয়ে বেশি সমাজসচেতন ছবি কি আজ পর্যন্ত তোলা হয়েছে? পাবস্ট-এর ‘কামেরা ডে শেফট’ আজও পর্যন্ত আমার কাছে মনে হয় সবচেয়ে বেশি সমাজসচেতন একটি ছবি। চারু রায়ের ‘বাংলার মেয়ে’ বহু আগে তোলা—প্রথম বাংলা ছবি, যাতে আউটডোর ব্যবহৃত হয় সবচেয়ে বেশিভাবে, তাতেও সমাজচেতনা পরিপূর্ণ ছিল।
...রবিঠাকুর মশায় একটা বড় ভালো কথা বলে গিয়েছিলেন, ‘শিল্পকে শিল্প হতে হলে সর্বাগ্রে সত্যনিষ্ঠ হতে হয়, তারপরে সৌন্দর্যনিষ্ঠ’। কথাটা ভাবার মতো। যদি পারেন ভেবে দেখবেন।
সূত্র: ঋত্বিক ঘটকের গৃহীত সাক্ষাৎকার, ‘সাক্ষাৎ ঋত্বিক’, শিবাদিত্য দাশগুপ্ত ও সন্দীপন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ১৮-১৯

ডান্ডি শহরে ডেভিড লিন্ডসে তাঁর ফ্ল্যাক্স মিল ‘ভারডান্ট ওয়ার্কস’এর কিছু বিবর্তন করে ১৮৩৫ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন বিশ্বের প্রথম জুট মিল বা পাটকল।
২১ জুন ২০২২
আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, স্বাধীনতা-সংগ্রামী, কবি-লেখক চিত্তরঞ্জন দাশ ‘দেশবন্ধু’ নামেই বিখ্যাত। তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন শচীমোহন গোপ, যিনি পঞ্চাশের দশকে রাস্তার মোড়ে বিক্রি করতেন দুধ, দই আর মাঠা। ১৯৫৮ সালে হাটখোলা রোডে ইত্তেফাক মোড়ে রেস্তোরাঁ খুলে বসেন।
২ দিন আগে
কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে কবি শাহীনা সোবহানের সম্মানে কবি ও সাহিত্যিকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে সাহিত্য আড্ডা। গতকাল শনিবার (১৮ অক্টোবর) বিকেলে কুমারখালী পৌর শহরের সাংবাদিক কাঙাল হরিনাথ মজুমদার স্মৃতি জাদুঘরে ড. নাসের ফাউন্ডেশনের আয়োজনে এই আড্ডার আয়োজন করা হয়।
৫ দিন আগে
১৯৬০-এর দশকে হাজি নান্না মিয়া তাঁর দুই ভাই জুম্মুন মিয়া ও চান মিয়ার সঙ্গে শুরু করেন খাবারের ব্যবসা। পুরান ঢাকার মৌলভীবাজারে ছোট্ট একটা দোকানে পাতলা মাদুর বিছিয়ে তাঁরা পরিবেশন করতেন মোরগ পোলাও। সেই মোরগ পোলাওয়ের সুঘ্রাণের সঙ্গে এর সুখ্যাতি ছড়াতে সময় লাগেনি। মৌলভীবাজার থেকে পরে বেচারাম দেউড়ির...
৭ দিন আগে