অনির্বাণ সরকার

সাহিত্যিক, সমাজ সংস্কারক ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন-বঙ্গসমাজ’-এ বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস বিধৃত করে গেছেন। এ কথা আজ সবাই জানেন—ইন্দো-পর্তুগিজ যুবক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) হিন্দু কলেজে শিক্ষক থাকার সময় এবং তারও পরে কিছুকাল তাঁর অকালমৃত্যু পর্যন্ত বাংলার যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে কী বিপুল বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন। ডিরোজিওর সরাসরি ছাত্রদের বলা হতো ইয়ং বেঙ্গলস অথবা ডিরোজিয়ানস। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী ছিল তৎকালীন গোঁড়া হিন্দু সমাজের প্রচলিত প্রথা ও কুসংস্কারবিরোধী। ইয়ং বেঙ্গলরা বিশ্বাস করতেন যুক্তিবাদে, মুক্তচিন্তা ও মানবিকতায়। ধর্মীয় ও সামাজিক গোঁড়ামির বিরুদ্ধে প্রবল ছিল তাঁদের অবস্থান। এ গোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, প্যারীচাঁদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধানাথ শিকদার প্রমুখ। পরিণত বয়সে তাঁরা ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্য, প্রবন্ধ রচনায় যেমন অবদান রেখেছেন, তেমনি নারীশিক্ষা, বিধবা বিবাহের মতো সমাজ পরিবর্তনকারী আন্দোলনেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন।
শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর বইয়ে ইয়ং বেঙ্গলদের একজনকে বলেছেন—‘ডিরোজিও-বৃক্ষের একটি উৎকৃষ্ট ফল।’ এ ব্যক্তির নাম রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-১৮৭০)। অনেকেই জানেন, তিনি হিমালয় পর্বতের ‘পিক নাম্বার ফিফটিন’কে নির্ভুল গণনায় পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন, যেটি আজ পরিচিত ‘মাউন্ট এভারেস্ট’ নামে।
রাধানাথ শিকদারের এই আবিষ্কারের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে ব্যক্তি রাধানাথের জীবন ও অন্যান্য কর্মের ইতিহাস। এ ছাড়া রাধানাথ শিকদারকে নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ লেখা ও গ্রন্থও সুলভ নয়। বিদ্যোৎসাহী রাধানাথ শিকদার তাঁর পুরো জীবন ব্যয় করেছেন গণিত ও বিজ্ঞানচর্চায়। কর্ম থেকে অবসর গ্রহণের পর সামাজিক আন্দোলনেও ছিলেন প্রথম সারির একজন—এ কথা অনেকেই বিস্মৃত হয়েছেন। ঊনবিংশ শতকের একটি বিশেষ সময় নিয়ে লেখা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘সেই সময়’-এ পরিণত বয়সের ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর একটি কল্পিত আড্ডার চিত্র আছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে—রাধানাথ শিকদার তাঁর যৌবনের বন্ধুদের সঙ্গে আলাপচারিতায় ধীরে ধীরে পরিচিত হচ্ছেন বাংলার সাম্প্রতিক সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কে, জানতে পারছেন বাংলা ভাষায় সাম্প্রতিক বিভিন্ন রচনার নিদর্শন সম্পর্কে। এই আলাপচারিতা কাল্পনিক হলেও রাধানাথ শিকদার বস্তুত বাংলার ভৌগোলিক সীমানা থেকে অনেক দূরেই অতিবাহিত করছিলেন তাঁর কর্মজীবন। হয়তো বাংলার সামাজিক সংস্কার ও আন্দোলনে অন্যান্য প্রগতিশীল চিন্তক ও কর্মদ্যোগীদের কাজে কিছুটা পরে রাধানাথ শিকদার নিজেকে শামিল করেছিলেন বলে বাংলার সমাজ উন্নয়নের ইতিহাসে রাধানাথ শিকদারের নামটি পেছনেই পড়ে গেছে।
কলকাতার জোড়াসাঁকো, যে স্থান বিখ্যাত হয়ে আছে ঠাকুর পরিবারের জন্য, যেখানে জন্মেছিলেন বিখ্যাত সিংহ পরিবারের কালীপ্রসন্ন সিংহ, যিনি বাংলা ভাষায় প্রথম সমগ্র ‘মহাভারত’-এর অনুবাদ সম্পন্ন করেছিলেন; সেই জোড়াসাঁকো এলাকাতেই ১৮১৩ সালে জন্ম রাধানাথ শিকদারের। তবে সেখানকার অন্য বিখ্যাত পরিবারের মতো অবস্থা ছিল না তাঁর পরিবারের। রাধানাথের পরিবার ছিল দরিদ্র। পিতা তিতুরাম শিকদার বুঝেছিলেন, পাশ্চাত্যের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত না হলে পরে ইংরেজ অধিকৃত ভারতবর্ষে কর্মের সুযোগ সীমিত হয়ে আসবে। তাই তিনি বালক রাধানাথকে প্রথমে পড়তে পাঠান চিৎপুর রোডের ফিরিঙ্গি কমল বসুর স্কুলে। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর ১৮২৪ সালে রাধানাথ ভর্তি হন হিন্দু কলেজে। এ কলেজেই তিনি ডিরোজিওকে শিক্ষক হিসেবে পান এবং এই সাক্ষাতে সমাজ ও ধর্ম সম্পর্কে তাঁর ভাবনাজগতে পরিবর্তন সূচিত হয়, যে মানবিক ভাবনা তিনি আজীবন বহন করেছেন।
ডিরোজিও যদি রাধানাথের মানসগঠনের শিক্ষক হন, তবে বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ে রাধানাথের আগ্রহ জাগিয়েছিলেন হিন্দু কলেজের আরেকজন শিক্ষক ডা. জন টাইটলার। টাইটলার তাঁর ছাত্র রাধানাথের মধ্যে অমিত প্রতিভার সন্ধান পেয়েছিলেন এবং তিনি রাধানাথকে পড়িয়েছিলেন আইজ্যাক নিউটনের বিখ্যাত বই ‘প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা’। রাধানাথ উচ্চতর গণিতের পাঠ নিয়েছিলেন এই টাইটলারের কাছেই। রাধানাথের প্রতিভা বোঝা যায়, যখন মাত্র ১৭ বছর বয়সে তাঁর উদ্ভাবিত একটি সম্পাদ্যের সমাধান বিখ্যাত ‘গ্লিনিংস ইন সায়েন্স’ (জানুয়ারি-ডিসেম্বর, ১৮৩১) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ বয়সেই প্রথম শ্রেণির (বর্তমান দশম শ্রেণি) ছাত্র রাধানাথ হিন্দু কলেজের সভায় পাঠ করেন তাঁর স্বরচিত প্রবন্ধ, যার বিষয় ছিল—‘The cultivation of the sciences is not more favourable to individual happiness, nor more useful and honourable to a nation, than that of polite literature.’ ‘দ্য এশিয়াটিক জার্নাল অ্যান্ড মান্থলি মিসেলেনি’-এর ১৮৩১ আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিতও হয়েছিল সেই প্রবন্ধ। ইংরেজি ব্যাকরণ, ভাষা, পদ্য ইত্যাদিতেও রাধানাথ ছাত্রজীবনে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন হিন্দু কলেজের শিক্ষক মলিস সাহেবের কাছ থেকে।
হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালেই রাধানাথকে সার্ভে অফিসে চাকরিতে ঢুকতে হয়েছিল; কারণ, পরিবারে অর্থাভাব। কিন্তু সে সময় যা প্রচলিত ছিল, অর্থাৎ দেশীয় রীতি অনুসারে একটি অল্প বয়সী বালিকাকে বিয়ে করা—সেটিতে রাধানাথ সম্মতি দেননি। কারণ, বাল্যবিবাহের প্রতি রাধানাথ আন্তরিক ঘৃণা পোষণ করতেন। শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত রাধানাথের জীবনের এই অংশ পড়ে বোঝা যায়, রাধানাথ মানুষ হিসেবে কেমন ছিলেন।
রাধানাথ শিকদারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায় তাঁর বন্ধু প্যারীচাঁদ মিত্রের লেখা থেকে। তিনি জানাচ্ছেন, ‘রাধানাথ খুব বলিষ্ঠদেহী ও তেজস্বী ছিলেন।’ প্যারীচাঁদ আরও জানাচ্ছেন, ‘সর্বপ্রযত্নে দেশের উপকার সাধন করাই রাধানাথ শিকদারের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। তাঁহার খেয়ালের মধ্যে গোমাংস ভক্ষণ প্রচলন করাই প্রধান, তিনি বলিতেন গোখাদকরা কখন পরাভূত হয় না। বাঙালিদিগের উন্নতি করিতে হইলে প্রথমে শারীরিক উন্নতি আবশ্যক। অথবা যুগপৎ শরীর ও চরিত্র উভয়েরই উৎকর্ষসাধনে তৎপর হওয়া আবশ্যক।’ রাধানাথের মৃত্যুর পর ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, ‘তিনি কড়া ধরনের লোক ছিলেন এবং সদ্য সদ্য কর্মনির্বাহ করিতেন এবং কার্যকারণকালে ক্ষিপ্রকারিতার ন্যূনতা তাহাতে কখন পরিলক্ষিত হয় নাই। রাধানাথ অসাধারণ লোক ছিলেন ও তাঁহার অনেক সদ্গুণ ছিল।’
গণিত বিষয়ে অনন্য প্রতিভাসম্পন্ন রাধানাথ কর্মজীবনের শুরুতে তাঁর মনের মতো চাকরিই পেয়েছিলেন—এ কথা বলা যায়। ‘গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া’-এর সার্ভেয়ার জেনারেল স্যার জর্জ এভারেস্ট সরাসরি রাধানাথকে জরিপকাজে শিক্ষা দিয়েছিলেন। কাজ মনের মতো হলেও বেতনের ব্যাপারে রাধানাথ সন্তুষ্ট ছিলেন না। কারণ, তাঁর ওপর ছিল পিতামাতা ও ভাইদের অন্নসংস্থানের ভার। এ জন্য ১৮৩৭ সালে রাধানাথ ডেপুটি কালেক্টরের পদে চাকরির জন্য দরখাস্ত করেন। কিন্তু জর্জ এভারেস্ট বুঝেছিলেন, রাধানাথের আসল প্রতিভা কোথায়। তিনি চাননি রাধানাথের প্রতিভার অপমৃত্যু হোক। এভারেস্টের অনুরোধে সরকার এমন ব্যবস্থা করেন, যাতে এসব ক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রধানের অনুমতি ছাড়া কোনো দেশীয় কর্মচারী বিভাগ পাল্টাতে না পারেন। তাই রাধানাথ সার্ভেতেই রয়ে যান। ১৮৪৩ সাল থেকে রাধানাথ সারভেয়ার জেনারেল হিসেবে পান স্যার অ্যান্ড্রু ওয়াকে। ওয়া রাধানাথের কাজ সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। সার্ভে বিভাগের সম্পদ রাধানাথকে চিনতে ভুল করেননি ওয়া। তাই ১৮৫০ সালে আবার যখন ডেপুটি কালেক্টরের পদে আবেদন করেন রাধানাথ, অ্যান্ড্রু ওয়া বিশেষ চেষ্টায় তা স্থগিত করেন এবং রাধানাথের বেতন বৃদ্ধি করেন। এর এক বছর আগেই; অর্থাৎ ১৮৪৯ সালে রাধানাথ অবশ্য দেরাদুন সার্ভে অফিস থেকে কলকাতায় ‘চিফ কমপিউটার’ পদে বদলি হয়ে চলে আসেন।
১৮৫২ সাল, বছরটি কেবল রাধানাথ শিকদারের জন্য নয়, ভৌগোলিক জরিপের ইতিহাসেও একটি উল্লেখযোগ্য বছর। ‘গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া’ দীর্ঘকাল যে জরিপকার্য করছিল ভারতবর্ষের পাহাড়ে পাহাড়ে, তাতে একটি চূড়ান্ত অর্জন হয় ওই বছর। পরিমাপকদের সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে রাধানাথ হিমালয়ের ‘XV’; অর্থাৎ ‘পিক নাম্বার ফিফটিন’কে পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্থান হিসেবে চিহ্নিত করেন। সে সময় এর উচ্চতা নির্ধারিত হয়েছিল ২৯ হাজার ২ ফুট। জনশ্রুতি আছে, বারবার গণনা করে রাধানাথ ‘পিক নাম্বার ফিফটিন’-এর উচ্চতা নিশ্চিত হওয়ার পর এতটাই উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলেন যে ছুটতে ছুটতে এসে ওয়াকে জানিয়েছিলেন, ‘আমরা পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্থান আবিষ্কার করে ফেলেছি।’ সরকারিভাবে এই শৃঙ্গের উচ্চতা ১৮৫৬ সালে নির্ধারিত হয় ২৯ হাজার ২৮ ফুট (আরও পরে ২৯ হাজার ৩২ ফুট) এবং সে বছরই স্যার জর্জ এভারেস্টের নামে এর নাম দেওয়া হয় মাউন্ট এভারেস্ট।
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অধিকৃত ভারতবর্ষের কোনো ইংরেজি সংবাদপত্রেই অবশ্য সদ্য আবিষ্কৃত মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা পরিমাপের কৃতিত্ব রাধানাথকে দেওয়া হয়নি। এমনকি তাঁর নামও উল্লেখ করা হয়নি। বস্তুত বহুকাল মানুষ জানতেই পারেনি রাধানাথের এই পরিশ্রম ও অর্জন সম্পর্কে। শিবনাথ শাস্ত্রীও রাধানাথের মানবিক বৈশিষ্ট্য বিষয়ে লিখে গেছেন, এভারেস্ট-বিষয়ক কোনো কথা তাতে নেই। রাধানাথ শিকদারের মৃত্যুর বহু বছর পর ১৯২৮ সালে ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় এভারেস্টের উচ্চতা নির্ণয়ে রাধানাথ শিকদারের অবদানের কথা এবং ১৯৩২ সালে ইতিহাসবিদ যোগেশচন্দ্র বাগল রাধানাথকে বিশ্বের উচ্চতম শৃঙ্গের গণনাকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।
রাধানাথ শিকদার ছিলেন ভারতবর্ষে জরিপকাজের পথপ্রদর্শক। ১৮৫১ সালে প্রকাশিত জরিপ-সংক্রান্ত কাজের ‘আ ম্যানুয়াল অব সার্ভেইং ফর ইন্ডিয়া’ গ্রন্থে গাণিতিক অধ্যায় রচনা করেন রাধানাথ। তাঁর রচিত অধ্যায়ের শিরোনাম ছিল ‘প্র্যাকটিক্যাল অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড ইটস অ্যাপ্লিকেশনস টু সার্ভেইং’। এই লেখায় জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে রাধানাথের গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। যে বছর রাধানাথ এভারেস্টের উচ্চতা নিরূপণ করেছিলেন, সে বছরই (১৮৫২) তাঁকে আলিপুরে কলকাতা অবজারভেটরির অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। এটিই ছিল রাধানাথের জীবনের শেষ চাকরি। এখানেও রাধানাথ তাঁর মেধার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছিলেন। ১৮৫২ সালের আগে এই আবহাওয়া অফিসের সংগৃহীত তথ্যে অনেক ভুলভ্রান্তি ছিল। রাধানাথ নিজ উদ্যোগে এর পরিমার্জনে নিয়োজিত হন এবং একটি বিজ্ঞানসম্মত তথ্যসারণি তৈরি করেন।
জরিপকার্য এবং আবহাওয়াবিজ্ঞানে অসামান্য অবদান রাখা রাধানাথ শিকদারের জীবনের অন্য দিকটি কেমন ছিল? অকৃতদার এই মানুষ কর্মসূত্রে দীর্ঘকাল কাটিয়েছিলেন বাংলার বাইরে। কথিত আছে, বাংলা ভাষা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বাংলায় ফিরে আসার পর কর্মযোগী রাধানাথের সঙ্গে যখন হিন্দু কলেজের পুরোনো বন্ধুদের যোগসূত্র স্থাপিত হয়, তিনি দেখলেন—নারীশিক্ষা থেকে শুরু করে সামাজিক নানা আন্দোলনে তাঁর বন্ধুরা জড়িয়ে আছে। রাধানাথও এসব কল্যাণমূলক কাজে জড়িত হলেন। তিনি এবং তার বন্ধুরা দৃঢ়ভাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। সুহৃদ প্যারীচাঁদ মিত্র যখন সমাজের জন্য কল্যাণমূলক একটি পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন, রাধানাথও তাতে অংশ নেন। এই দুজনের যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ‘মাসিক পত্রিকা’। রাধানাথ বুঝেছিলেন, সমাজের কুসংস্কার দূর করতে হলে সাধারণ মানুষের কাছে তাঁদের কথা প্রচারিত হওয়া দরকার। তাই তাঁদের এ পত্রিকায় যেসব প্রবন্ধ, অনুবাদ ও অন্যান্য লেখা প্রকাশিত হতো, তা ছিল মৌখিক বাংলা ভাষার কাছাকাছি ভাষায় লেখা, লক্ষ্য ছিল নারী পাঠকেরা। এ পত্রিকা মাত্র চার বছর চললেও এটি ছিল জনপ্রিয় পত্রিকা এবং বাংলার সমাজের কুসংস্কার দূর করতে এর অবদান ইতিহাসে স্থায়ী হয়ে আছে।
১৮৬২ সালে রাধানাথ শিকদার তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনের সমাপ্তি টানেন। এরপর তাঁর মৃত্যু অবধি রাধানাথ এককভাবে এবং তাঁর বাংলার বন্ধুবর্গের সঙ্গে মিলে বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত ছিলেন। পরাধীন বাংলার সমাজের বিভিন্ন স্তরের কুসংস্কার দূর করা এবং বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনই ছিল রাধানাথের বাসনা। ১৮৭০ সালে রাধানাথের জীবনের অবসান ঘটে চন্দননগরে নিজের বাগানবাড়িতে। চন্দননগরেই এই বিজ্ঞানসাধক, কর্মযোগী ও বলিষ্ঠ চরিত্রের মানুষটির সমাধি রয়েছে।
রাধানাথ ছিলেন তাঁর সময়ের চেয়ে অগ্রসর এক ব্যক্তি। সুদীর্ঘকাল রাধানাথ সম্পর্কে কিছু জানা না গেলেও পরবর্তী সময়ে বাংলার ইতিহাসের গবেষকেরা রাধানাথের জীবন ও কর্মের বহু অজানা তথ্য উদ্ধার করেছেন। অবিভক্ত ভারতবর্ষের প্রথম বিজ্ঞানী হিসেবে রাধানাথ শিকদারের নামই প্রথমে আসবে—এ কথায় আজ আর কোনো দ্বিধা বা সংশয়ের অবকাশ নেই।
তথ্যসূত্র:
১. রাধানাথ শিকদারের আত্মকথা ও মূল্যায়ন: দীপক দাঁ (সম্পা.)
২. রাধানাথ শিকদার/তথ্যের আলোয়: শঙ্করকুমার নাথ
৩. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ: শিবনাথ শাস্ত্রী
৪. সেই সময়: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সাহিত্যিক, সমাজ সংস্কারক ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন-বঙ্গসমাজ’-এ বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস বিধৃত করে গেছেন। এ কথা আজ সবাই জানেন—ইন্দো-পর্তুগিজ যুবক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) হিন্দু কলেজে শিক্ষক থাকার সময় এবং তারও পরে কিছুকাল তাঁর অকালমৃত্যু পর্যন্ত বাংলার যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে কী বিপুল বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন। ডিরোজিওর সরাসরি ছাত্রদের বলা হতো ইয়ং বেঙ্গলস অথবা ডিরোজিয়ানস। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী ছিল তৎকালীন গোঁড়া হিন্দু সমাজের প্রচলিত প্রথা ও কুসংস্কারবিরোধী। ইয়ং বেঙ্গলরা বিশ্বাস করতেন যুক্তিবাদে, মুক্তচিন্তা ও মানবিকতায়। ধর্মীয় ও সামাজিক গোঁড়ামির বিরুদ্ধে প্রবল ছিল তাঁদের অবস্থান। এ গোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, প্যারীচাঁদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধানাথ শিকদার প্রমুখ। পরিণত বয়সে তাঁরা ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্য, প্রবন্ধ রচনায় যেমন অবদান রেখেছেন, তেমনি নারীশিক্ষা, বিধবা বিবাহের মতো সমাজ পরিবর্তনকারী আন্দোলনেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন।
শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর বইয়ে ইয়ং বেঙ্গলদের একজনকে বলেছেন—‘ডিরোজিও-বৃক্ষের একটি উৎকৃষ্ট ফল।’ এ ব্যক্তির নাম রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-১৮৭০)। অনেকেই জানেন, তিনি হিমালয় পর্বতের ‘পিক নাম্বার ফিফটিন’কে নির্ভুল গণনায় পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন, যেটি আজ পরিচিত ‘মাউন্ট এভারেস্ট’ নামে।
রাধানাথ শিকদারের এই আবিষ্কারের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে ব্যক্তি রাধানাথের জীবন ও অন্যান্য কর্মের ইতিহাস। এ ছাড়া রাধানাথ শিকদারকে নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ লেখা ও গ্রন্থও সুলভ নয়। বিদ্যোৎসাহী রাধানাথ শিকদার তাঁর পুরো জীবন ব্যয় করেছেন গণিত ও বিজ্ঞানচর্চায়। কর্ম থেকে অবসর গ্রহণের পর সামাজিক আন্দোলনেও ছিলেন প্রথম সারির একজন—এ কথা অনেকেই বিস্মৃত হয়েছেন। ঊনবিংশ শতকের একটি বিশেষ সময় নিয়ে লেখা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘সেই সময়’-এ পরিণত বয়সের ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর একটি কল্পিত আড্ডার চিত্র আছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে—রাধানাথ শিকদার তাঁর যৌবনের বন্ধুদের সঙ্গে আলাপচারিতায় ধীরে ধীরে পরিচিত হচ্ছেন বাংলার সাম্প্রতিক সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কে, জানতে পারছেন বাংলা ভাষায় সাম্প্রতিক বিভিন্ন রচনার নিদর্শন সম্পর্কে। এই আলাপচারিতা কাল্পনিক হলেও রাধানাথ শিকদার বস্তুত বাংলার ভৌগোলিক সীমানা থেকে অনেক দূরেই অতিবাহিত করছিলেন তাঁর কর্মজীবন। হয়তো বাংলার সামাজিক সংস্কার ও আন্দোলনে অন্যান্য প্রগতিশীল চিন্তক ও কর্মদ্যোগীদের কাজে কিছুটা পরে রাধানাথ শিকদার নিজেকে শামিল করেছিলেন বলে বাংলার সমাজ উন্নয়নের ইতিহাসে রাধানাথ শিকদারের নামটি পেছনেই পড়ে গেছে।
কলকাতার জোড়াসাঁকো, যে স্থান বিখ্যাত হয়ে আছে ঠাকুর পরিবারের জন্য, যেখানে জন্মেছিলেন বিখ্যাত সিংহ পরিবারের কালীপ্রসন্ন সিংহ, যিনি বাংলা ভাষায় প্রথম সমগ্র ‘মহাভারত’-এর অনুবাদ সম্পন্ন করেছিলেন; সেই জোড়াসাঁকো এলাকাতেই ১৮১৩ সালে জন্ম রাধানাথ শিকদারের। তবে সেখানকার অন্য বিখ্যাত পরিবারের মতো অবস্থা ছিল না তাঁর পরিবারের। রাধানাথের পরিবার ছিল দরিদ্র। পিতা তিতুরাম শিকদার বুঝেছিলেন, পাশ্চাত্যের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত না হলে পরে ইংরেজ অধিকৃত ভারতবর্ষে কর্মের সুযোগ সীমিত হয়ে আসবে। তাই তিনি বালক রাধানাথকে প্রথমে পড়তে পাঠান চিৎপুর রোডের ফিরিঙ্গি কমল বসুর স্কুলে। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর ১৮২৪ সালে রাধানাথ ভর্তি হন হিন্দু কলেজে। এ কলেজেই তিনি ডিরোজিওকে শিক্ষক হিসেবে পান এবং এই সাক্ষাতে সমাজ ও ধর্ম সম্পর্কে তাঁর ভাবনাজগতে পরিবর্তন সূচিত হয়, যে মানবিক ভাবনা তিনি আজীবন বহন করেছেন।
ডিরোজিও যদি রাধানাথের মানসগঠনের শিক্ষক হন, তবে বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ে রাধানাথের আগ্রহ জাগিয়েছিলেন হিন্দু কলেজের আরেকজন শিক্ষক ডা. জন টাইটলার। টাইটলার তাঁর ছাত্র রাধানাথের মধ্যে অমিত প্রতিভার সন্ধান পেয়েছিলেন এবং তিনি রাধানাথকে পড়িয়েছিলেন আইজ্যাক নিউটনের বিখ্যাত বই ‘প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা’। রাধানাথ উচ্চতর গণিতের পাঠ নিয়েছিলেন এই টাইটলারের কাছেই। রাধানাথের প্রতিভা বোঝা যায়, যখন মাত্র ১৭ বছর বয়সে তাঁর উদ্ভাবিত একটি সম্পাদ্যের সমাধান বিখ্যাত ‘গ্লিনিংস ইন সায়েন্স’ (জানুয়ারি-ডিসেম্বর, ১৮৩১) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ বয়সেই প্রথম শ্রেণির (বর্তমান দশম শ্রেণি) ছাত্র রাধানাথ হিন্দু কলেজের সভায় পাঠ করেন তাঁর স্বরচিত প্রবন্ধ, যার বিষয় ছিল—‘The cultivation of the sciences is not more favourable to individual happiness, nor more useful and honourable to a nation, than that of polite literature.’ ‘দ্য এশিয়াটিক জার্নাল অ্যান্ড মান্থলি মিসেলেনি’-এর ১৮৩১ আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিতও হয়েছিল সেই প্রবন্ধ। ইংরেজি ব্যাকরণ, ভাষা, পদ্য ইত্যাদিতেও রাধানাথ ছাত্রজীবনে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন হিন্দু কলেজের শিক্ষক মলিস সাহেবের কাছ থেকে।
হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালেই রাধানাথকে সার্ভে অফিসে চাকরিতে ঢুকতে হয়েছিল; কারণ, পরিবারে অর্থাভাব। কিন্তু সে সময় যা প্রচলিত ছিল, অর্থাৎ দেশীয় রীতি অনুসারে একটি অল্প বয়সী বালিকাকে বিয়ে করা—সেটিতে রাধানাথ সম্মতি দেননি। কারণ, বাল্যবিবাহের প্রতি রাধানাথ আন্তরিক ঘৃণা পোষণ করতেন। শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত রাধানাথের জীবনের এই অংশ পড়ে বোঝা যায়, রাধানাথ মানুষ হিসেবে কেমন ছিলেন।
রাধানাথ শিকদারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায় তাঁর বন্ধু প্যারীচাঁদ মিত্রের লেখা থেকে। তিনি জানাচ্ছেন, ‘রাধানাথ খুব বলিষ্ঠদেহী ও তেজস্বী ছিলেন।’ প্যারীচাঁদ আরও জানাচ্ছেন, ‘সর্বপ্রযত্নে দেশের উপকার সাধন করাই রাধানাথ শিকদারের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। তাঁহার খেয়ালের মধ্যে গোমাংস ভক্ষণ প্রচলন করাই প্রধান, তিনি বলিতেন গোখাদকরা কখন পরাভূত হয় না। বাঙালিদিগের উন্নতি করিতে হইলে প্রথমে শারীরিক উন্নতি আবশ্যক। অথবা যুগপৎ শরীর ও চরিত্র উভয়েরই উৎকর্ষসাধনে তৎপর হওয়া আবশ্যক।’ রাধানাথের মৃত্যুর পর ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, ‘তিনি কড়া ধরনের লোক ছিলেন এবং সদ্য সদ্য কর্মনির্বাহ করিতেন এবং কার্যকারণকালে ক্ষিপ্রকারিতার ন্যূনতা তাহাতে কখন পরিলক্ষিত হয় নাই। রাধানাথ অসাধারণ লোক ছিলেন ও তাঁহার অনেক সদ্গুণ ছিল।’
গণিত বিষয়ে অনন্য প্রতিভাসম্পন্ন রাধানাথ কর্মজীবনের শুরুতে তাঁর মনের মতো চাকরিই পেয়েছিলেন—এ কথা বলা যায়। ‘গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া’-এর সার্ভেয়ার জেনারেল স্যার জর্জ এভারেস্ট সরাসরি রাধানাথকে জরিপকাজে শিক্ষা দিয়েছিলেন। কাজ মনের মতো হলেও বেতনের ব্যাপারে রাধানাথ সন্তুষ্ট ছিলেন না। কারণ, তাঁর ওপর ছিল পিতামাতা ও ভাইদের অন্নসংস্থানের ভার। এ জন্য ১৮৩৭ সালে রাধানাথ ডেপুটি কালেক্টরের পদে চাকরির জন্য দরখাস্ত করেন। কিন্তু জর্জ এভারেস্ট বুঝেছিলেন, রাধানাথের আসল প্রতিভা কোথায়। তিনি চাননি রাধানাথের প্রতিভার অপমৃত্যু হোক। এভারেস্টের অনুরোধে সরকার এমন ব্যবস্থা করেন, যাতে এসব ক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রধানের অনুমতি ছাড়া কোনো দেশীয় কর্মচারী বিভাগ পাল্টাতে না পারেন। তাই রাধানাথ সার্ভেতেই রয়ে যান। ১৮৪৩ সাল থেকে রাধানাথ সারভেয়ার জেনারেল হিসেবে পান স্যার অ্যান্ড্রু ওয়াকে। ওয়া রাধানাথের কাজ সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। সার্ভে বিভাগের সম্পদ রাধানাথকে চিনতে ভুল করেননি ওয়া। তাই ১৮৫০ সালে আবার যখন ডেপুটি কালেক্টরের পদে আবেদন করেন রাধানাথ, অ্যান্ড্রু ওয়া বিশেষ চেষ্টায় তা স্থগিত করেন এবং রাধানাথের বেতন বৃদ্ধি করেন। এর এক বছর আগেই; অর্থাৎ ১৮৪৯ সালে রাধানাথ অবশ্য দেরাদুন সার্ভে অফিস থেকে কলকাতায় ‘চিফ কমপিউটার’ পদে বদলি হয়ে চলে আসেন।
১৮৫২ সাল, বছরটি কেবল রাধানাথ শিকদারের জন্য নয়, ভৌগোলিক জরিপের ইতিহাসেও একটি উল্লেখযোগ্য বছর। ‘গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া’ দীর্ঘকাল যে জরিপকার্য করছিল ভারতবর্ষের পাহাড়ে পাহাড়ে, তাতে একটি চূড়ান্ত অর্জন হয় ওই বছর। পরিমাপকদের সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে রাধানাথ হিমালয়ের ‘XV’; অর্থাৎ ‘পিক নাম্বার ফিফটিন’কে পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্থান হিসেবে চিহ্নিত করেন। সে সময় এর উচ্চতা নির্ধারিত হয়েছিল ২৯ হাজার ২ ফুট। জনশ্রুতি আছে, বারবার গণনা করে রাধানাথ ‘পিক নাম্বার ফিফটিন’-এর উচ্চতা নিশ্চিত হওয়ার পর এতটাই উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলেন যে ছুটতে ছুটতে এসে ওয়াকে জানিয়েছিলেন, ‘আমরা পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্থান আবিষ্কার করে ফেলেছি।’ সরকারিভাবে এই শৃঙ্গের উচ্চতা ১৮৫৬ সালে নির্ধারিত হয় ২৯ হাজার ২৮ ফুট (আরও পরে ২৯ হাজার ৩২ ফুট) এবং সে বছরই স্যার জর্জ এভারেস্টের নামে এর নাম দেওয়া হয় মাউন্ট এভারেস্ট।
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অধিকৃত ভারতবর্ষের কোনো ইংরেজি সংবাদপত্রেই অবশ্য সদ্য আবিষ্কৃত মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা পরিমাপের কৃতিত্ব রাধানাথকে দেওয়া হয়নি। এমনকি তাঁর নামও উল্লেখ করা হয়নি। বস্তুত বহুকাল মানুষ জানতেই পারেনি রাধানাথের এই পরিশ্রম ও অর্জন সম্পর্কে। শিবনাথ শাস্ত্রীও রাধানাথের মানবিক বৈশিষ্ট্য বিষয়ে লিখে গেছেন, এভারেস্ট-বিষয়ক কোনো কথা তাতে নেই। রাধানাথ শিকদারের মৃত্যুর বহু বছর পর ১৯২৮ সালে ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় এভারেস্টের উচ্চতা নির্ণয়ে রাধানাথ শিকদারের অবদানের কথা এবং ১৯৩২ সালে ইতিহাসবিদ যোগেশচন্দ্র বাগল রাধানাথকে বিশ্বের উচ্চতম শৃঙ্গের গণনাকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।
রাধানাথ শিকদার ছিলেন ভারতবর্ষে জরিপকাজের পথপ্রদর্শক। ১৮৫১ সালে প্রকাশিত জরিপ-সংক্রান্ত কাজের ‘আ ম্যানুয়াল অব সার্ভেইং ফর ইন্ডিয়া’ গ্রন্থে গাণিতিক অধ্যায় রচনা করেন রাধানাথ। তাঁর রচিত অধ্যায়ের শিরোনাম ছিল ‘প্র্যাকটিক্যাল অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড ইটস অ্যাপ্লিকেশনস টু সার্ভেইং’। এই লেখায় জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে রাধানাথের গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। যে বছর রাধানাথ এভারেস্টের উচ্চতা নিরূপণ করেছিলেন, সে বছরই (১৮৫২) তাঁকে আলিপুরে কলকাতা অবজারভেটরির অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। এটিই ছিল রাধানাথের জীবনের শেষ চাকরি। এখানেও রাধানাথ তাঁর মেধার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছিলেন। ১৮৫২ সালের আগে এই আবহাওয়া অফিসের সংগৃহীত তথ্যে অনেক ভুলভ্রান্তি ছিল। রাধানাথ নিজ উদ্যোগে এর পরিমার্জনে নিয়োজিত হন এবং একটি বিজ্ঞানসম্মত তথ্যসারণি তৈরি করেন।
জরিপকার্য এবং আবহাওয়াবিজ্ঞানে অসামান্য অবদান রাখা রাধানাথ শিকদারের জীবনের অন্য দিকটি কেমন ছিল? অকৃতদার এই মানুষ কর্মসূত্রে দীর্ঘকাল কাটিয়েছিলেন বাংলার বাইরে। কথিত আছে, বাংলা ভাষা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বাংলায় ফিরে আসার পর কর্মযোগী রাধানাথের সঙ্গে যখন হিন্দু কলেজের পুরোনো বন্ধুদের যোগসূত্র স্থাপিত হয়, তিনি দেখলেন—নারীশিক্ষা থেকে শুরু করে সামাজিক নানা আন্দোলনে তাঁর বন্ধুরা জড়িয়ে আছে। রাধানাথও এসব কল্যাণমূলক কাজে জড়িত হলেন। তিনি এবং তার বন্ধুরা দৃঢ়ভাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। সুহৃদ প্যারীচাঁদ মিত্র যখন সমাজের জন্য কল্যাণমূলক একটি পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন, রাধানাথও তাতে অংশ নেন। এই দুজনের যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ‘মাসিক পত্রিকা’। রাধানাথ বুঝেছিলেন, সমাজের কুসংস্কার দূর করতে হলে সাধারণ মানুষের কাছে তাঁদের কথা প্রচারিত হওয়া দরকার। তাই তাঁদের এ পত্রিকায় যেসব প্রবন্ধ, অনুবাদ ও অন্যান্য লেখা প্রকাশিত হতো, তা ছিল মৌখিক বাংলা ভাষার কাছাকাছি ভাষায় লেখা, লক্ষ্য ছিল নারী পাঠকেরা। এ পত্রিকা মাত্র চার বছর চললেও এটি ছিল জনপ্রিয় পত্রিকা এবং বাংলার সমাজের কুসংস্কার দূর করতে এর অবদান ইতিহাসে স্থায়ী হয়ে আছে।
১৮৬২ সালে রাধানাথ শিকদার তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনের সমাপ্তি টানেন। এরপর তাঁর মৃত্যু অবধি রাধানাথ এককভাবে এবং তাঁর বাংলার বন্ধুবর্গের সঙ্গে মিলে বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত ছিলেন। পরাধীন বাংলার সমাজের বিভিন্ন স্তরের কুসংস্কার দূর করা এবং বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনই ছিল রাধানাথের বাসনা। ১৮৭০ সালে রাধানাথের জীবনের অবসান ঘটে চন্দননগরে নিজের বাগানবাড়িতে। চন্দননগরেই এই বিজ্ঞানসাধক, কর্মযোগী ও বলিষ্ঠ চরিত্রের মানুষটির সমাধি রয়েছে।
রাধানাথ ছিলেন তাঁর সময়ের চেয়ে অগ্রসর এক ব্যক্তি। সুদীর্ঘকাল রাধানাথ সম্পর্কে কিছু জানা না গেলেও পরবর্তী সময়ে বাংলার ইতিহাসের গবেষকেরা রাধানাথের জীবন ও কর্মের বহু অজানা তথ্য উদ্ধার করেছেন। অবিভক্ত ভারতবর্ষের প্রথম বিজ্ঞানী হিসেবে রাধানাথ শিকদারের নামই প্রথমে আসবে—এ কথায় আজ আর কোনো দ্বিধা বা সংশয়ের অবকাশ নেই।
তথ্যসূত্র:
১. রাধানাথ শিকদারের আত্মকথা ও মূল্যায়ন: দীপক দাঁ (সম্পা.)
২. রাধানাথ শিকদার/তথ্যের আলোয়: শঙ্করকুমার নাথ
৩. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ: শিবনাথ শাস্ত্রী
৪. সেই সময়: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
অনির্বাণ সরকার

সাহিত্যিক, সমাজ সংস্কারক ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন-বঙ্গসমাজ’-এ বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস বিধৃত করে গেছেন। এ কথা আজ সবাই জানেন—ইন্দো-পর্তুগিজ যুবক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) হিন্দু কলেজে শিক্ষক থাকার সময় এবং তারও পরে কিছুকাল তাঁর অকালমৃত্যু পর্যন্ত বাংলার যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে কী বিপুল বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন। ডিরোজিওর সরাসরি ছাত্রদের বলা হতো ইয়ং বেঙ্গলস অথবা ডিরোজিয়ানস। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী ছিল তৎকালীন গোঁড়া হিন্দু সমাজের প্রচলিত প্রথা ও কুসংস্কারবিরোধী। ইয়ং বেঙ্গলরা বিশ্বাস করতেন যুক্তিবাদে, মুক্তচিন্তা ও মানবিকতায়। ধর্মীয় ও সামাজিক গোঁড়ামির বিরুদ্ধে প্রবল ছিল তাঁদের অবস্থান। এ গোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, প্যারীচাঁদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধানাথ শিকদার প্রমুখ। পরিণত বয়সে তাঁরা ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্য, প্রবন্ধ রচনায় যেমন অবদান রেখেছেন, তেমনি নারীশিক্ষা, বিধবা বিবাহের মতো সমাজ পরিবর্তনকারী আন্দোলনেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন।
শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর বইয়ে ইয়ং বেঙ্গলদের একজনকে বলেছেন—‘ডিরোজিও-বৃক্ষের একটি উৎকৃষ্ট ফল।’ এ ব্যক্তির নাম রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-১৮৭০)। অনেকেই জানেন, তিনি হিমালয় পর্বতের ‘পিক নাম্বার ফিফটিন’কে নির্ভুল গণনায় পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন, যেটি আজ পরিচিত ‘মাউন্ট এভারেস্ট’ নামে।
রাধানাথ শিকদারের এই আবিষ্কারের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে ব্যক্তি রাধানাথের জীবন ও অন্যান্য কর্মের ইতিহাস। এ ছাড়া রাধানাথ শিকদারকে নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ লেখা ও গ্রন্থও সুলভ নয়। বিদ্যোৎসাহী রাধানাথ শিকদার তাঁর পুরো জীবন ব্যয় করেছেন গণিত ও বিজ্ঞানচর্চায়। কর্ম থেকে অবসর গ্রহণের পর সামাজিক আন্দোলনেও ছিলেন প্রথম সারির একজন—এ কথা অনেকেই বিস্মৃত হয়েছেন। ঊনবিংশ শতকের একটি বিশেষ সময় নিয়ে লেখা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘সেই সময়’-এ পরিণত বয়সের ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর একটি কল্পিত আড্ডার চিত্র আছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে—রাধানাথ শিকদার তাঁর যৌবনের বন্ধুদের সঙ্গে আলাপচারিতায় ধীরে ধীরে পরিচিত হচ্ছেন বাংলার সাম্প্রতিক সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কে, জানতে পারছেন বাংলা ভাষায় সাম্প্রতিক বিভিন্ন রচনার নিদর্শন সম্পর্কে। এই আলাপচারিতা কাল্পনিক হলেও রাধানাথ শিকদার বস্তুত বাংলার ভৌগোলিক সীমানা থেকে অনেক দূরেই অতিবাহিত করছিলেন তাঁর কর্মজীবন। হয়তো বাংলার সামাজিক সংস্কার ও আন্দোলনে অন্যান্য প্রগতিশীল চিন্তক ও কর্মদ্যোগীদের কাজে কিছুটা পরে রাধানাথ শিকদার নিজেকে শামিল করেছিলেন বলে বাংলার সমাজ উন্নয়নের ইতিহাসে রাধানাথ শিকদারের নামটি পেছনেই পড়ে গেছে।
কলকাতার জোড়াসাঁকো, যে স্থান বিখ্যাত হয়ে আছে ঠাকুর পরিবারের জন্য, যেখানে জন্মেছিলেন বিখ্যাত সিংহ পরিবারের কালীপ্রসন্ন সিংহ, যিনি বাংলা ভাষায় প্রথম সমগ্র ‘মহাভারত’-এর অনুবাদ সম্পন্ন করেছিলেন; সেই জোড়াসাঁকো এলাকাতেই ১৮১৩ সালে জন্ম রাধানাথ শিকদারের। তবে সেখানকার অন্য বিখ্যাত পরিবারের মতো অবস্থা ছিল না তাঁর পরিবারের। রাধানাথের পরিবার ছিল দরিদ্র। পিতা তিতুরাম শিকদার বুঝেছিলেন, পাশ্চাত্যের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত না হলে পরে ইংরেজ অধিকৃত ভারতবর্ষে কর্মের সুযোগ সীমিত হয়ে আসবে। তাই তিনি বালক রাধানাথকে প্রথমে পড়তে পাঠান চিৎপুর রোডের ফিরিঙ্গি কমল বসুর স্কুলে। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর ১৮২৪ সালে রাধানাথ ভর্তি হন হিন্দু কলেজে। এ কলেজেই তিনি ডিরোজিওকে শিক্ষক হিসেবে পান এবং এই সাক্ষাতে সমাজ ও ধর্ম সম্পর্কে তাঁর ভাবনাজগতে পরিবর্তন সূচিত হয়, যে মানবিক ভাবনা তিনি আজীবন বহন করেছেন।
ডিরোজিও যদি রাধানাথের মানসগঠনের শিক্ষক হন, তবে বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ে রাধানাথের আগ্রহ জাগিয়েছিলেন হিন্দু কলেজের আরেকজন শিক্ষক ডা. জন টাইটলার। টাইটলার তাঁর ছাত্র রাধানাথের মধ্যে অমিত প্রতিভার সন্ধান পেয়েছিলেন এবং তিনি রাধানাথকে পড়িয়েছিলেন আইজ্যাক নিউটনের বিখ্যাত বই ‘প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা’। রাধানাথ উচ্চতর গণিতের পাঠ নিয়েছিলেন এই টাইটলারের কাছেই। রাধানাথের প্রতিভা বোঝা যায়, যখন মাত্র ১৭ বছর বয়সে তাঁর উদ্ভাবিত একটি সম্পাদ্যের সমাধান বিখ্যাত ‘গ্লিনিংস ইন সায়েন্স’ (জানুয়ারি-ডিসেম্বর, ১৮৩১) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ বয়সেই প্রথম শ্রেণির (বর্তমান দশম শ্রেণি) ছাত্র রাধানাথ হিন্দু কলেজের সভায় পাঠ করেন তাঁর স্বরচিত প্রবন্ধ, যার বিষয় ছিল—‘The cultivation of the sciences is not more favourable to individual happiness, nor more useful and honourable to a nation, than that of polite literature.’ ‘দ্য এশিয়াটিক জার্নাল অ্যান্ড মান্থলি মিসেলেনি’-এর ১৮৩১ আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিতও হয়েছিল সেই প্রবন্ধ। ইংরেজি ব্যাকরণ, ভাষা, পদ্য ইত্যাদিতেও রাধানাথ ছাত্রজীবনে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন হিন্দু কলেজের শিক্ষক মলিস সাহেবের কাছ থেকে।
হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালেই রাধানাথকে সার্ভে অফিসে চাকরিতে ঢুকতে হয়েছিল; কারণ, পরিবারে অর্থাভাব। কিন্তু সে সময় যা প্রচলিত ছিল, অর্থাৎ দেশীয় রীতি অনুসারে একটি অল্প বয়সী বালিকাকে বিয়ে করা—সেটিতে রাধানাথ সম্মতি দেননি। কারণ, বাল্যবিবাহের প্রতি রাধানাথ আন্তরিক ঘৃণা পোষণ করতেন। শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত রাধানাথের জীবনের এই অংশ পড়ে বোঝা যায়, রাধানাথ মানুষ হিসেবে কেমন ছিলেন।
রাধানাথ শিকদারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায় তাঁর বন্ধু প্যারীচাঁদ মিত্রের লেখা থেকে। তিনি জানাচ্ছেন, ‘রাধানাথ খুব বলিষ্ঠদেহী ও তেজস্বী ছিলেন।’ প্যারীচাঁদ আরও জানাচ্ছেন, ‘সর্বপ্রযত্নে দেশের উপকার সাধন করাই রাধানাথ শিকদারের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। তাঁহার খেয়ালের মধ্যে গোমাংস ভক্ষণ প্রচলন করাই প্রধান, তিনি বলিতেন গোখাদকরা কখন পরাভূত হয় না। বাঙালিদিগের উন্নতি করিতে হইলে প্রথমে শারীরিক উন্নতি আবশ্যক। অথবা যুগপৎ শরীর ও চরিত্র উভয়েরই উৎকর্ষসাধনে তৎপর হওয়া আবশ্যক।’ রাধানাথের মৃত্যুর পর ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, ‘তিনি কড়া ধরনের লোক ছিলেন এবং সদ্য সদ্য কর্মনির্বাহ করিতেন এবং কার্যকারণকালে ক্ষিপ্রকারিতার ন্যূনতা তাহাতে কখন পরিলক্ষিত হয় নাই। রাধানাথ অসাধারণ লোক ছিলেন ও তাঁহার অনেক সদ্গুণ ছিল।’
গণিত বিষয়ে অনন্য প্রতিভাসম্পন্ন রাধানাথ কর্মজীবনের শুরুতে তাঁর মনের মতো চাকরিই পেয়েছিলেন—এ কথা বলা যায়। ‘গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া’-এর সার্ভেয়ার জেনারেল স্যার জর্জ এভারেস্ট সরাসরি রাধানাথকে জরিপকাজে শিক্ষা দিয়েছিলেন। কাজ মনের মতো হলেও বেতনের ব্যাপারে রাধানাথ সন্তুষ্ট ছিলেন না। কারণ, তাঁর ওপর ছিল পিতামাতা ও ভাইদের অন্নসংস্থানের ভার। এ জন্য ১৮৩৭ সালে রাধানাথ ডেপুটি কালেক্টরের পদে চাকরির জন্য দরখাস্ত করেন। কিন্তু জর্জ এভারেস্ট বুঝেছিলেন, রাধানাথের আসল প্রতিভা কোথায়। তিনি চাননি রাধানাথের প্রতিভার অপমৃত্যু হোক। এভারেস্টের অনুরোধে সরকার এমন ব্যবস্থা করেন, যাতে এসব ক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রধানের অনুমতি ছাড়া কোনো দেশীয় কর্মচারী বিভাগ পাল্টাতে না পারেন। তাই রাধানাথ সার্ভেতেই রয়ে যান। ১৮৪৩ সাল থেকে রাধানাথ সারভেয়ার জেনারেল হিসেবে পান স্যার অ্যান্ড্রু ওয়াকে। ওয়া রাধানাথের কাজ সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। সার্ভে বিভাগের সম্পদ রাধানাথকে চিনতে ভুল করেননি ওয়া। তাই ১৮৫০ সালে আবার যখন ডেপুটি কালেক্টরের পদে আবেদন করেন রাধানাথ, অ্যান্ড্রু ওয়া বিশেষ চেষ্টায় তা স্থগিত করেন এবং রাধানাথের বেতন বৃদ্ধি করেন। এর এক বছর আগেই; অর্থাৎ ১৮৪৯ সালে রাধানাথ অবশ্য দেরাদুন সার্ভে অফিস থেকে কলকাতায় ‘চিফ কমপিউটার’ পদে বদলি হয়ে চলে আসেন।
১৮৫২ সাল, বছরটি কেবল রাধানাথ শিকদারের জন্য নয়, ভৌগোলিক জরিপের ইতিহাসেও একটি উল্লেখযোগ্য বছর। ‘গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া’ দীর্ঘকাল যে জরিপকার্য করছিল ভারতবর্ষের পাহাড়ে পাহাড়ে, তাতে একটি চূড়ান্ত অর্জন হয় ওই বছর। পরিমাপকদের সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে রাধানাথ হিমালয়ের ‘XV’; অর্থাৎ ‘পিক নাম্বার ফিফটিন’কে পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্থান হিসেবে চিহ্নিত করেন। সে সময় এর উচ্চতা নির্ধারিত হয়েছিল ২৯ হাজার ২ ফুট। জনশ্রুতি আছে, বারবার গণনা করে রাধানাথ ‘পিক নাম্বার ফিফটিন’-এর উচ্চতা নিশ্চিত হওয়ার পর এতটাই উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলেন যে ছুটতে ছুটতে এসে ওয়াকে জানিয়েছিলেন, ‘আমরা পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্থান আবিষ্কার করে ফেলেছি।’ সরকারিভাবে এই শৃঙ্গের উচ্চতা ১৮৫৬ সালে নির্ধারিত হয় ২৯ হাজার ২৮ ফুট (আরও পরে ২৯ হাজার ৩২ ফুট) এবং সে বছরই স্যার জর্জ এভারেস্টের নামে এর নাম দেওয়া হয় মাউন্ট এভারেস্ট।
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অধিকৃত ভারতবর্ষের কোনো ইংরেজি সংবাদপত্রেই অবশ্য সদ্য আবিষ্কৃত মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা পরিমাপের কৃতিত্ব রাধানাথকে দেওয়া হয়নি। এমনকি তাঁর নামও উল্লেখ করা হয়নি। বস্তুত বহুকাল মানুষ জানতেই পারেনি রাধানাথের এই পরিশ্রম ও অর্জন সম্পর্কে। শিবনাথ শাস্ত্রীও রাধানাথের মানবিক বৈশিষ্ট্য বিষয়ে লিখে গেছেন, এভারেস্ট-বিষয়ক কোনো কথা তাতে নেই। রাধানাথ শিকদারের মৃত্যুর বহু বছর পর ১৯২৮ সালে ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় এভারেস্টের উচ্চতা নির্ণয়ে রাধানাথ শিকদারের অবদানের কথা এবং ১৯৩২ সালে ইতিহাসবিদ যোগেশচন্দ্র বাগল রাধানাথকে বিশ্বের উচ্চতম শৃঙ্গের গণনাকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।
রাধানাথ শিকদার ছিলেন ভারতবর্ষে জরিপকাজের পথপ্রদর্শক। ১৮৫১ সালে প্রকাশিত জরিপ-সংক্রান্ত কাজের ‘আ ম্যানুয়াল অব সার্ভেইং ফর ইন্ডিয়া’ গ্রন্থে গাণিতিক অধ্যায় রচনা করেন রাধানাথ। তাঁর রচিত অধ্যায়ের শিরোনাম ছিল ‘প্র্যাকটিক্যাল অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড ইটস অ্যাপ্লিকেশনস টু সার্ভেইং’। এই লেখায় জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে রাধানাথের গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। যে বছর রাধানাথ এভারেস্টের উচ্চতা নিরূপণ করেছিলেন, সে বছরই (১৮৫২) তাঁকে আলিপুরে কলকাতা অবজারভেটরির অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। এটিই ছিল রাধানাথের জীবনের শেষ চাকরি। এখানেও রাধানাথ তাঁর মেধার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছিলেন। ১৮৫২ সালের আগে এই আবহাওয়া অফিসের সংগৃহীত তথ্যে অনেক ভুলভ্রান্তি ছিল। রাধানাথ নিজ উদ্যোগে এর পরিমার্জনে নিয়োজিত হন এবং একটি বিজ্ঞানসম্মত তথ্যসারণি তৈরি করেন।
জরিপকার্য এবং আবহাওয়াবিজ্ঞানে অসামান্য অবদান রাখা রাধানাথ শিকদারের জীবনের অন্য দিকটি কেমন ছিল? অকৃতদার এই মানুষ কর্মসূত্রে দীর্ঘকাল কাটিয়েছিলেন বাংলার বাইরে। কথিত আছে, বাংলা ভাষা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বাংলায় ফিরে আসার পর কর্মযোগী রাধানাথের সঙ্গে যখন হিন্দু কলেজের পুরোনো বন্ধুদের যোগসূত্র স্থাপিত হয়, তিনি দেখলেন—নারীশিক্ষা থেকে শুরু করে সামাজিক নানা আন্দোলনে তাঁর বন্ধুরা জড়িয়ে আছে। রাধানাথও এসব কল্যাণমূলক কাজে জড়িত হলেন। তিনি এবং তার বন্ধুরা দৃঢ়ভাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। সুহৃদ প্যারীচাঁদ মিত্র যখন সমাজের জন্য কল্যাণমূলক একটি পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন, রাধানাথও তাতে অংশ নেন। এই দুজনের যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ‘মাসিক পত্রিকা’। রাধানাথ বুঝেছিলেন, সমাজের কুসংস্কার দূর করতে হলে সাধারণ মানুষের কাছে তাঁদের কথা প্রচারিত হওয়া দরকার। তাই তাঁদের এ পত্রিকায় যেসব প্রবন্ধ, অনুবাদ ও অন্যান্য লেখা প্রকাশিত হতো, তা ছিল মৌখিক বাংলা ভাষার কাছাকাছি ভাষায় লেখা, লক্ষ্য ছিল নারী পাঠকেরা। এ পত্রিকা মাত্র চার বছর চললেও এটি ছিল জনপ্রিয় পত্রিকা এবং বাংলার সমাজের কুসংস্কার দূর করতে এর অবদান ইতিহাসে স্থায়ী হয়ে আছে।
১৮৬২ সালে রাধানাথ শিকদার তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনের সমাপ্তি টানেন। এরপর তাঁর মৃত্যু অবধি রাধানাথ এককভাবে এবং তাঁর বাংলার বন্ধুবর্গের সঙ্গে মিলে বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত ছিলেন। পরাধীন বাংলার সমাজের বিভিন্ন স্তরের কুসংস্কার দূর করা এবং বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনই ছিল রাধানাথের বাসনা। ১৮৭০ সালে রাধানাথের জীবনের অবসান ঘটে চন্দননগরে নিজের বাগানবাড়িতে। চন্দননগরেই এই বিজ্ঞানসাধক, কর্মযোগী ও বলিষ্ঠ চরিত্রের মানুষটির সমাধি রয়েছে।
রাধানাথ ছিলেন তাঁর সময়ের চেয়ে অগ্রসর এক ব্যক্তি। সুদীর্ঘকাল রাধানাথ সম্পর্কে কিছু জানা না গেলেও পরবর্তী সময়ে বাংলার ইতিহাসের গবেষকেরা রাধানাথের জীবন ও কর্মের বহু অজানা তথ্য উদ্ধার করেছেন। অবিভক্ত ভারতবর্ষের প্রথম বিজ্ঞানী হিসেবে রাধানাথ শিকদারের নামই প্রথমে আসবে—এ কথায় আজ আর কোনো দ্বিধা বা সংশয়ের অবকাশ নেই।
তথ্যসূত্র:
১. রাধানাথ শিকদারের আত্মকথা ও মূল্যায়ন: দীপক দাঁ (সম্পা.)
২. রাধানাথ শিকদার/তথ্যের আলোয়: শঙ্করকুমার নাথ
৩. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ: শিবনাথ শাস্ত্রী
৪. সেই সময়: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সাহিত্যিক, সমাজ সংস্কারক ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন-বঙ্গসমাজ’-এ বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস বিধৃত করে গেছেন। এ কথা আজ সবাই জানেন—ইন্দো-পর্তুগিজ যুবক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) হিন্দু কলেজে শিক্ষক থাকার সময় এবং তারও পরে কিছুকাল তাঁর অকালমৃত্যু পর্যন্ত বাংলার যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে কী বিপুল বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন। ডিরোজিওর সরাসরি ছাত্রদের বলা হতো ইয়ং বেঙ্গলস অথবা ডিরোজিয়ানস। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী ছিল তৎকালীন গোঁড়া হিন্দু সমাজের প্রচলিত প্রথা ও কুসংস্কারবিরোধী। ইয়ং বেঙ্গলরা বিশ্বাস করতেন যুক্তিবাদে, মুক্তচিন্তা ও মানবিকতায়। ধর্মীয় ও সামাজিক গোঁড়ামির বিরুদ্ধে প্রবল ছিল তাঁদের অবস্থান। এ গোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, প্যারীচাঁদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধানাথ শিকদার প্রমুখ। পরিণত বয়সে তাঁরা ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্য, প্রবন্ধ রচনায় যেমন অবদান রেখেছেন, তেমনি নারীশিক্ষা, বিধবা বিবাহের মতো সমাজ পরিবর্তনকারী আন্দোলনেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন।
শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর বইয়ে ইয়ং বেঙ্গলদের একজনকে বলেছেন—‘ডিরোজিও-বৃক্ষের একটি উৎকৃষ্ট ফল।’ এ ব্যক্তির নাম রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-১৮৭০)। অনেকেই জানেন, তিনি হিমালয় পর্বতের ‘পিক নাম্বার ফিফটিন’কে নির্ভুল গণনায় পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন, যেটি আজ পরিচিত ‘মাউন্ট এভারেস্ট’ নামে।
রাধানাথ শিকদারের এই আবিষ্কারের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে ব্যক্তি রাধানাথের জীবন ও অন্যান্য কর্মের ইতিহাস। এ ছাড়া রাধানাথ শিকদারকে নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ লেখা ও গ্রন্থও সুলভ নয়। বিদ্যোৎসাহী রাধানাথ শিকদার তাঁর পুরো জীবন ব্যয় করেছেন গণিত ও বিজ্ঞানচর্চায়। কর্ম থেকে অবসর গ্রহণের পর সামাজিক আন্দোলনেও ছিলেন প্রথম সারির একজন—এ কথা অনেকেই বিস্মৃত হয়েছেন। ঊনবিংশ শতকের একটি বিশেষ সময় নিয়ে লেখা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘সেই সময়’-এ পরিণত বয়সের ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর একটি কল্পিত আড্ডার চিত্র আছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে—রাধানাথ শিকদার তাঁর যৌবনের বন্ধুদের সঙ্গে আলাপচারিতায় ধীরে ধীরে পরিচিত হচ্ছেন বাংলার সাম্প্রতিক সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কে, জানতে পারছেন বাংলা ভাষায় সাম্প্রতিক বিভিন্ন রচনার নিদর্শন সম্পর্কে। এই আলাপচারিতা কাল্পনিক হলেও রাধানাথ শিকদার বস্তুত বাংলার ভৌগোলিক সীমানা থেকে অনেক দূরেই অতিবাহিত করছিলেন তাঁর কর্মজীবন। হয়তো বাংলার সামাজিক সংস্কার ও আন্দোলনে অন্যান্য প্রগতিশীল চিন্তক ও কর্মদ্যোগীদের কাজে কিছুটা পরে রাধানাথ শিকদার নিজেকে শামিল করেছিলেন বলে বাংলার সমাজ উন্নয়নের ইতিহাসে রাধানাথ শিকদারের নামটি পেছনেই পড়ে গেছে।
কলকাতার জোড়াসাঁকো, যে স্থান বিখ্যাত হয়ে আছে ঠাকুর পরিবারের জন্য, যেখানে জন্মেছিলেন বিখ্যাত সিংহ পরিবারের কালীপ্রসন্ন সিংহ, যিনি বাংলা ভাষায় প্রথম সমগ্র ‘মহাভারত’-এর অনুবাদ সম্পন্ন করেছিলেন; সেই জোড়াসাঁকো এলাকাতেই ১৮১৩ সালে জন্ম রাধানাথ শিকদারের। তবে সেখানকার অন্য বিখ্যাত পরিবারের মতো অবস্থা ছিল না তাঁর পরিবারের। রাধানাথের পরিবার ছিল দরিদ্র। পিতা তিতুরাম শিকদার বুঝেছিলেন, পাশ্চাত্যের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত না হলে পরে ইংরেজ অধিকৃত ভারতবর্ষে কর্মের সুযোগ সীমিত হয়ে আসবে। তাই তিনি বালক রাধানাথকে প্রথমে পড়তে পাঠান চিৎপুর রোডের ফিরিঙ্গি কমল বসুর স্কুলে। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর ১৮২৪ সালে রাধানাথ ভর্তি হন হিন্দু কলেজে। এ কলেজেই তিনি ডিরোজিওকে শিক্ষক হিসেবে পান এবং এই সাক্ষাতে সমাজ ও ধর্ম সম্পর্কে তাঁর ভাবনাজগতে পরিবর্তন সূচিত হয়, যে মানবিক ভাবনা তিনি আজীবন বহন করেছেন।
ডিরোজিও যদি রাধানাথের মানসগঠনের শিক্ষক হন, তবে বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ে রাধানাথের আগ্রহ জাগিয়েছিলেন হিন্দু কলেজের আরেকজন শিক্ষক ডা. জন টাইটলার। টাইটলার তাঁর ছাত্র রাধানাথের মধ্যে অমিত প্রতিভার সন্ধান পেয়েছিলেন এবং তিনি রাধানাথকে পড়িয়েছিলেন আইজ্যাক নিউটনের বিখ্যাত বই ‘প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা’। রাধানাথ উচ্চতর গণিতের পাঠ নিয়েছিলেন এই টাইটলারের কাছেই। রাধানাথের প্রতিভা বোঝা যায়, যখন মাত্র ১৭ বছর বয়সে তাঁর উদ্ভাবিত একটি সম্পাদ্যের সমাধান বিখ্যাত ‘গ্লিনিংস ইন সায়েন্স’ (জানুয়ারি-ডিসেম্বর, ১৮৩১) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ বয়সেই প্রথম শ্রেণির (বর্তমান দশম শ্রেণি) ছাত্র রাধানাথ হিন্দু কলেজের সভায় পাঠ করেন তাঁর স্বরচিত প্রবন্ধ, যার বিষয় ছিল—‘The cultivation of the sciences is not more favourable to individual happiness, nor more useful and honourable to a nation, than that of polite literature.’ ‘দ্য এশিয়াটিক জার্নাল অ্যান্ড মান্থলি মিসেলেনি’-এর ১৮৩১ আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিতও হয়েছিল সেই প্রবন্ধ। ইংরেজি ব্যাকরণ, ভাষা, পদ্য ইত্যাদিতেও রাধানাথ ছাত্রজীবনে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন হিন্দু কলেজের শিক্ষক মলিস সাহেবের কাছ থেকে।
হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালেই রাধানাথকে সার্ভে অফিসে চাকরিতে ঢুকতে হয়েছিল; কারণ, পরিবারে অর্থাভাব। কিন্তু সে সময় যা প্রচলিত ছিল, অর্থাৎ দেশীয় রীতি অনুসারে একটি অল্প বয়সী বালিকাকে বিয়ে করা—সেটিতে রাধানাথ সম্মতি দেননি। কারণ, বাল্যবিবাহের প্রতি রাধানাথ আন্তরিক ঘৃণা পোষণ করতেন। শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত রাধানাথের জীবনের এই অংশ পড়ে বোঝা যায়, রাধানাথ মানুষ হিসেবে কেমন ছিলেন।
রাধানাথ শিকদারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায় তাঁর বন্ধু প্যারীচাঁদ মিত্রের লেখা থেকে। তিনি জানাচ্ছেন, ‘রাধানাথ খুব বলিষ্ঠদেহী ও তেজস্বী ছিলেন।’ প্যারীচাঁদ আরও জানাচ্ছেন, ‘সর্বপ্রযত্নে দেশের উপকার সাধন করাই রাধানাথ শিকদারের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। তাঁহার খেয়ালের মধ্যে গোমাংস ভক্ষণ প্রচলন করাই প্রধান, তিনি বলিতেন গোখাদকরা কখন পরাভূত হয় না। বাঙালিদিগের উন্নতি করিতে হইলে প্রথমে শারীরিক উন্নতি আবশ্যক। অথবা যুগপৎ শরীর ও চরিত্র উভয়েরই উৎকর্ষসাধনে তৎপর হওয়া আবশ্যক।’ রাধানাথের মৃত্যুর পর ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, ‘তিনি কড়া ধরনের লোক ছিলেন এবং সদ্য সদ্য কর্মনির্বাহ করিতেন এবং কার্যকারণকালে ক্ষিপ্রকারিতার ন্যূনতা তাহাতে কখন পরিলক্ষিত হয় নাই। রাধানাথ অসাধারণ লোক ছিলেন ও তাঁহার অনেক সদ্গুণ ছিল।’
গণিত বিষয়ে অনন্য প্রতিভাসম্পন্ন রাধানাথ কর্মজীবনের শুরুতে তাঁর মনের মতো চাকরিই পেয়েছিলেন—এ কথা বলা যায়। ‘গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া’-এর সার্ভেয়ার জেনারেল স্যার জর্জ এভারেস্ট সরাসরি রাধানাথকে জরিপকাজে শিক্ষা দিয়েছিলেন। কাজ মনের মতো হলেও বেতনের ব্যাপারে রাধানাথ সন্তুষ্ট ছিলেন না। কারণ, তাঁর ওপর ছিল পিতামাতা ও ভাইদের অন্নসংস্থানের ভার। এ জন্য ১৮৩৭ সালে রাধানাথ ডেপুটি কালেক্টরের পদে চাকরির জন্য দরখাস্ত করেন। কিন্তু জর্জ এভারেস্ট বুঝেছিলেন, রাধানাথের আসল প্রতিভা কোথায়। তিনি চাননি রাধানাথের প্রতিভার অপমৃত্যু হোক। এভারেস্টের অনুরোধে সরকার এমন ব্যবস্থা করেন, যাতে এসব ক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রধানের অনুমতি ছাড়া কোনো দেশীয় কর্মচারী বিভাগ পাল্টাতে না পারেন। তাই রাধানাথ সার্ভেতেই রয়ে যান। ১৮৪৩ সাল থেকে রাধানাথ সারভেয়ার জেনারেল হিসেবে পান স্যার অ্যান্ড্রু ওয়াকে। ওয়া রাধানাথের কাজ সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। সার্ভে বিভাগের সম্পদ রাধানাথকে চিনতে ভুল করেননি ওয়া। তাই ১৮৫০ সালে আবার যখন ডেপুটি কালেক্টরের পদে আবেদন করেন রাধানাথ, অ্যান্ড্রু ওয়া বিশেষ চেষ্টায় তা স্থগিত করেন এবং রাধানাথের বেতন বৃদ্ধি করেন। এর এক বছর আগেই; অর্থাৎ ১৮৪৯ সালে রাধানাথ অবশ্য দেরাদুন সার্ভে অফিস থেকে কলকাতায় ‘চিফ কমপিউটার’ পদে বদলি হয়ে চলে আসেন।
১৮৫২ সাল, বছরটি কেবল রাধানাথ শিকদারের জন্য নয়, ভৌগোলিক জরিপের ইতিহাসেও একটি উল্লেখযোগ্য বছর। ‘গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া’ দীর্ঘকাল যে জরিপকার্য করছিল ভারতবর্ষের পাহাড়ে পাহাড়ে, তাতে একটি চূড়ান্ত অর্জন হয় ওই বছর। পরিমাপকদের সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে রাধানাথ হিমালয়ের ‘XV’; অর্থাৎ ‘পিক নাম্বার ফিফটিন’কে পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্থান হিসেবে চিহ্নিত করেন। সে সময় এর উচ্চতা নির্ধারিত হয়েছিল ২৯ হাজার ২ ফুট। জনশ্রুতি আছে, বারবার গণনা করে রাধানাথ ‘পিক নাম্বার ফিফটিন’-এর উচ্চতা নিশ্চিত হওয়ার পর এতটাই উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলেন যে ছুটতে ছুটতে এসে ওয়াকে জানিয়েছিলেন, ‘আমরা পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্থান আবিষ্কার করে ফেলেছি।’ সরকারিভাবে এই শৃঙ্গের উচ্চতা ১৮৫৬ সালে নির্ধারিত হয় ২৯ হাজার ২৮ ফুট (আরও পরে ২৯ হাজার ৩২ ফুট) এবং সে বছরই স্যার জর্জ এভারেস্টের নামে এর নাম দেওয়া হয় মাউন্ট এভারেস্ট।
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অধিকৃত ভারতবর্ষের কোনো ইংরেজি সংবাদপত্রেই অবশ্য সদ্য আবিষ্কৃত মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা পরিমাপের কৃতিত্ব রাধানাথকে দেওয়া হয়নি। এমনকি তাঁর নামও উল্লেখ করা হয়নি। বস্তুত বহুকাল মানুষ জানতেই পারেনি রাধানাথের এই পরিশ্রম ও অর্জন সম্পর্কে। শিবনাথ শাস্ত্রীও রাধানাথের মানবিক বৈশিষ্ট্য বিষয়ে লিখে গেছেন, এভারেস্ট-বিষয়ক কোনো কথা তাতে নেই। রাধানাথ শিকদারের মৃত্যুর বহু বছর পর ১৯২৮ সালে ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় এভারেস্টের উচ্চতা নির্ণয়ে রাধানাথ শিকদারের অবদানের কথা এবং ১৯৩২ সালে ইতিহাসবিদ যোগেশচন্দ্র বাগল রাধানাথকে বিশ্বের উচ্চতম শৃঙ্গের গণনাকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।
রাধানাথ শিকদার ছিলেন ভারতবর্ষে জরিপকাজের পথপ্রদর্শক। ১৮৫১ সালে প্রকাশিত জরিপ-সংক্রান্ত কাজের ‘আ ম্যানুয়াল অব সার্ভেইং ফর ইন্ডিয়া’ গ্রন্থে গাণিতিক অধ্যায় রচনা করেন রাধানাথ। তাঁর রচিত অধ্যায়ের শিরোনাম ছিল ‘প্র্যাকটিক্যাল অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড ইটস অ্যাপ্লিকেশনস টু সার্ভেইং’। এই লেখায় জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে রাধানাথের গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। যে বছর রাধানাথ এভারেস্টের উচ্চতা নিরূপণ করেছিলেন, সে বছরই (১৮৫২) তাঁকে আলিপুরে কলকাতা অবজারভেটরির অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। এটিই ছিল রাধানাথের জীবনের শেষ চাকরি। এখানেও রাধানাথ তাঁর মেধার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছিলেন। ১৮৫২ সালের আগে এই আবহাওয়া অফিসের সংগৃহীত তথ্যে অনেক ভুলভ্রান্তি ছিল। রাধানাথ নিজ উদ্যোগে এর পরিমার্জনে নিয়োজিত হন এবং একটি বিজ্ঞানসম্মত তথ্যসারণি তৈরি করেন।
জরিপকার্য এবং আবহাওয়াবিজ্ঞানে অসামান্য অবদান রাখা রাধানাথ শিকদারের জীবনের অন্য দিকটি কেমন ছিল? অকৃতদার এই মানুষ কর্মসূত্রে দীর্ঘকাল কাটিয়েছিলেন বাংলার বাইরে। কথিত আছে, বাংলা ভাষা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বাংলায় ফিরে আসার পর কর্মযোগী রাধানাথের সঙ্গে যখন হিন্দু কলেজের পুরোনো বন্ধুদের যোগসূত্র স্থাপিত হয়, তিনি দেখলেন—নারীশিক্ষা থেকে শুরু করে সামাজিক নানা আন্দোলনে তাঁর বন্ধুরা জড়িয়ে আছে। রাধানাথও এসব কল্যাণমূলক কাজে জড়িত হলেন। তিনি এবং তার বন্ধুরা দৃঢ়ভাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। সুহৃদ প্যারীচাঁদ মিত্র যখন সমাজের জন্য কল্যাণমূলক একটি পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন, রাধানাথও তাতে অংশ নেন। এই দুজনের যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ‘মাসিক পত্রিকা’। রাধানাথ বুঝেছিলেন, সমাজের কুসংস্কার দূর করতে হলে সাধারণ মানুষের কাছে তাঁদের কথা প্রচারিত হওয়া দরকার। তাই তাঁদের এ পত্রিকায় যেসব প্রবন্ধ, অনুবাদ ও অন্যান্য লেখা প্রকাশিত হতো, তা ছিল মৌখিক বাংলা ভাষার কাছাকাছি ভাষায় লেখা, লক্ষ্য ছিল নারী পাঠকেরা। এ পত্রিকা মাত্র চার বছর চললেও এটি ছিল জনপ্রিয় পত্রিকা এবং বাংলার সমাজের কুসংস্কার দূর করতে এর অবদান ইতিহাসে স্থায়ী হয়ে আছে।
১৮৬২ সালে রাধানাথ শিকদার তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনের সমাপ্তি টানেন। এরপর তাঁর মৃত্যু অবধি রাধানাথ এককভাবে এবং তাঁর বাংলার বন্ধুবর্গের সঙ্গে মিলে বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত ছিলেন। পরাধীন বাংলার সমাজের বিভিন্ন স্তরের কুসংস্কার দূর করা এবং বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনই ছিল রাধানাথের বাসনা। ১৮৭০ সালে রাধানাথের জীবনের অবসান ঘটে চন্দননগরে নিজের বাগানবাড়িতে। চন্দননগরেই এই বিজ্ঞানসাধক, কর্মযোগী ও বলিষ্ঠ চরিত্রের মানুষটির সমাধি রয়েছে।
রাধানাথ ছিলেন তাঁর সময়ের চেয়ে অগ্রসর এক ব্যক্তি। সুদীর্ঘকাল রাধানাথ সম্পর্কে কিছু জানা না গেলেও পরবর্তী সময়ে বাংলার ইতিহাসের গবেষকেরা রাধানাথের জীবন ও কর্মের বহু অজানা তথ্য উদ্ধার করেছেন। অবিভক্ত ভারতবর্ষের প্রথম বিজ্ঞানী হিসেবে রাধানাথ শিকদারের নামই প্রথমে আসবে—এ কথায় আজ আর কোনো দ্বিধা বা সংশয়ের অবকাশ নেই।
তথ্যসূত্র:
১. রাধানাথ শিকদারের আত্মকথা ও মূল্যায়ন: দীপক দাঁ (সম্পা.)
২. রাধানাথ শিকদার/তথ্যের আলোয়: শঙ্করকুমার নাথ
৩. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ: শিবনাথ শাস্ত্রী
৪. সেই সময়: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে কবি শাহীনা সোবহানের সম্মানে কবি ও সাহিত্যিকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে সাহিত্য আড্ডা। গতকাল শনিবার (১৮ অক্টোবর) বিকেলে কুমারখালী পৌর শহরের সাংবাদিক কাঙাল হরিনাথ মজুমদার স্মৃতি জাদুঘরে ড. নাসের ফাউন্ডেশনের আয়োজনে এই আড্ডার আয়োজন করা হয়।
২ দিন আগে
১৯৬০-এর দশকে হাজি নান্না মিয়া তাঁর দুই ভাই জুম্মুন মিয়া ও চান মিয়ার সঙ্গে শুরু করেন খাবারের ব্যবসা। পুরান ঢাকার মৌলভীবাজারে ছোট্ট একটা দোকানে পাতলা মাদুর বিছিয়ে তাঁরা পরিবেশন করতেন মোরগ পোলাও। সেই মোরগ পোলাওয়ের সুঘ্রাণের সঙ্গে এর সুখ্যাতি ছড়াতে সময় লাগেনি। মৌলভীবাজার থেকে পরে বেচারাম দেউড়ির...
৪ দিন আগে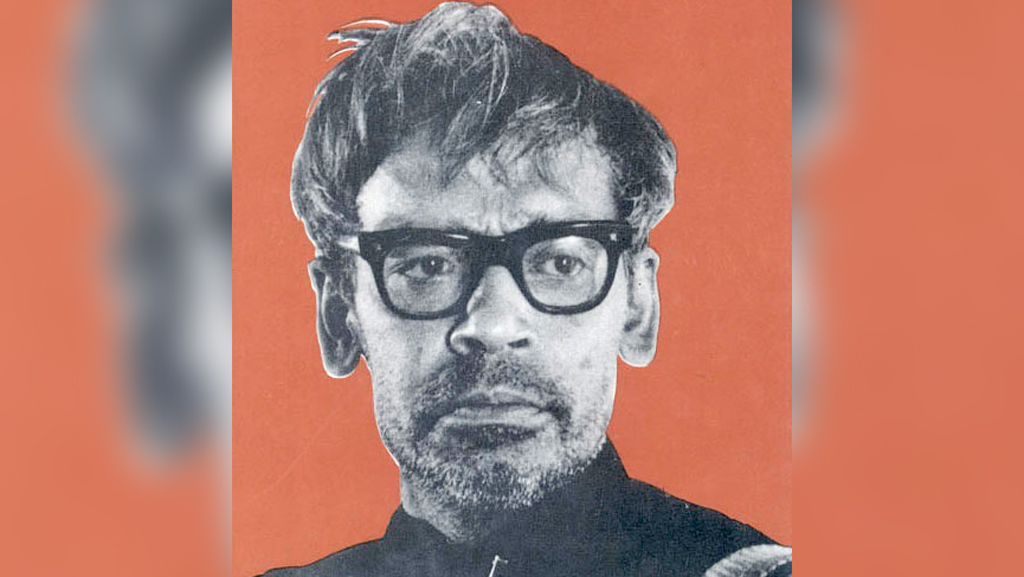
চলচ্চিত্র নির্মাণের পদ্ধতি-টদ্ধতি বুঝি না মশাই। আমার কাছে আজও প্রমথেশ বড়ুয়া ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালক। আমরা কেউই তাঁর পায়ের নখের যোগ্য নই। আমার আজও মনে পড়ে ‘গৃহদাহ’র সেই অসম্ভব ট্রানজিশন—সেই যে হাইহিল জুতো-পরা দুটো পা থেকে সোজা কেটে দুটো আলতা-মাখা পা পালকি থেকে নামছে—আমি কখনো ভুলব না।
৫ দিন আগে
বিরিয়ানি কিংবা কাবাব-পরোটা খেতে মন চাইলে পুরান ঢাকার নাজিরাবাজারের কথা মনে পড়তেই পারে। এসব খেয়ে কেউ কেউ বিউটি কিংবা নূরানীর লাচ্ছি খেয়ে ভোজ শেষ করতে পারেন। আবার কেউ ধোঁয়া ওঠা গরম চা পিরিচে নিয়ে ফুঁকে ফুঁকে গলায় ঢালতে পারেন। যাঁরা নিয়মিত যান নাজিরাবাজারে, তাঁরা জানেন এসব চা-প্রেমীর ভিড় লেগে...
৬ দিন আগেকুমারখালী (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে কবি শাহীনা সোবহানের সম্মানে কবি ও সাহিত্যিকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে সাহিত্য আড্ডা। গতকাল শনিবার (১৮ অক্টোবর) বিকেলে কুমারখালী পৌর শহরের সাংবাদিক কাঙাল হরিনাথ মজুমদার স্মৃতি জাদুঘরে ড. নাসের ফাউন্ডেশনের আয়োজনে এই আড্ডার আয়োজন করা হয়।
কবি ও নাট্যকার লিটন আব্বাসের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সদস্য ও সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশনের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক সৈয়দা শাহীনা সোবহান।
ড. নাসের ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. আবু নাসের রাজীবের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় কিডনি ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক জামানুল ইসলাম ভূঁইয়া, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা বিশ্বজিৎ সাহা, কুমারখালী সাহিত্য সংসদের সভাপতি কবি রহমান আজিজ, কবি রজত হুদা ও কবি সবুর বাদশা। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন কবি ও কথাসাহিত্যিক সোহেল আমিন বাবু, কবি বাবলু জোয়ার্দার, কবি ও সাংবাদিক মাহমুদ শরীফ, জিটিভির কুষ্টিয়া প্রতিনিধি সাংবাদিক কাজী সাইফুল, দৈনিক নয়া দিগন্তের কুষ্টিয়া প্রতিনিধি (মাল্টিমিডিয়া) সোহাগ মাহমুদ প্রমুখ।
এ সাহিত্য আড্ডায় কুষ্টিয়া ও কুমারখালীর কবি-সাহিত্যিকেরা অংশ নিয়ে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন সংগীতশিল্পী জিয়াউর রহমান মানিক।

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে কবি শাহীনা সোবহানের সম্মানে কবি ও সাহিত্যিকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে সাহিত্য আড্ডা। গতকাল শনিবার (১৮ অক্টোবর) বিকেলে কুমারখালী পৌর শহরের সাংবাদিক কাঙাল হরিনাথ মজুমদার স্মৃতি জাদুঘরে ড. নাসের ফাউন্ডেশনের আয়োজনে এই আড্ডার আয়োজন করা হয়।
কবি ও নাট্যকার লিটন আব্বাসের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সদস্য ও সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশনের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক সৈয়দা শাহীনা সোবহান।
ড. নাসের ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. আবু নাসের রাজীবের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় কিডনি ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক জামানুল ইসলাম ভূঁইয়া, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা বিশ্বজিৎ সাহা, কুমারখালী সাহিত্য সংসদের সভাপতি কবি রহমান আজিজ, কবি রজত হুদা ও কবি সবুর বাদশা। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন কবি ও কথাসাহিত্যিক সোহেল আমিন বাবু, কবি বাবলু জোয়ার্দার, কবি ও সাংবাদিক মাহমুদ শরীফ, জিটিভির কুষ্টিয়া প্রতিনিধি সাংবাদিক কাজী সাইফুল, দৈনিক নয়া দিগন্তের কুষ্টিয়া প্রতিনিধি (মাল্টিমিডিয়া) সোহাগ মাহমুদ প্রমুখ।
এ সাহিত্য আড্ডায় কুষ্টিয়া ও কুমারখালীর কবি-সাহিত্যিকেরা অংশ নিয়ে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন সংগীতশিল্পী জিয়াউর রহমান মানিক।

কলকাতার জোড়াসাঁকো, যে স্থান বিখ্যাত হয়ে আছে ঠাকুর পরিবারের জন্য, যেখানে জন্মেছিলেন বিখ্যাত সিংহ পরিবারের কালীপ্রসন্ন সিংহ, যিনি বাংলা ভাষায় প্রথম সমগ্র ‘মহাভারত’-এর অনুবাদ সম্পন্ন করেছিলেন; সেই জোড়াসাঁকো এলাকাতেই ১৮১৩ সালে জন্ম রাধানাথ শিকদারের। তবে সেখানকার অন্য বিখ্যাত পরিবারের মতো অবস্থা ছিল না ত
০৪ মার্চ ২০২২
১৯৬০-এর দশকে হাজি নান্না মিয়া তাঁর দুই ভাই জুম্মুন মিয়া ও চান মিয়ার সঙ্গে শুরু করেন খাবারের ব্যবসা। পুরান ঢাকার মৌলভীবাজারে ছোট্ট একটা দোকানে পাতলা মাদুর বিছিয়ে তাঁরা পরিবেশন করতেন মোরগ পোলাও। সেই মোরগ পোলাওয়ের সুঘ্রাণের সঙ্গে এর সুখ্যাতি ছড়াতে সময় লাগেনি। মৌলভীবাজার থেকে পরে বেচারাম দেউড়ির...
৪ দিন আগে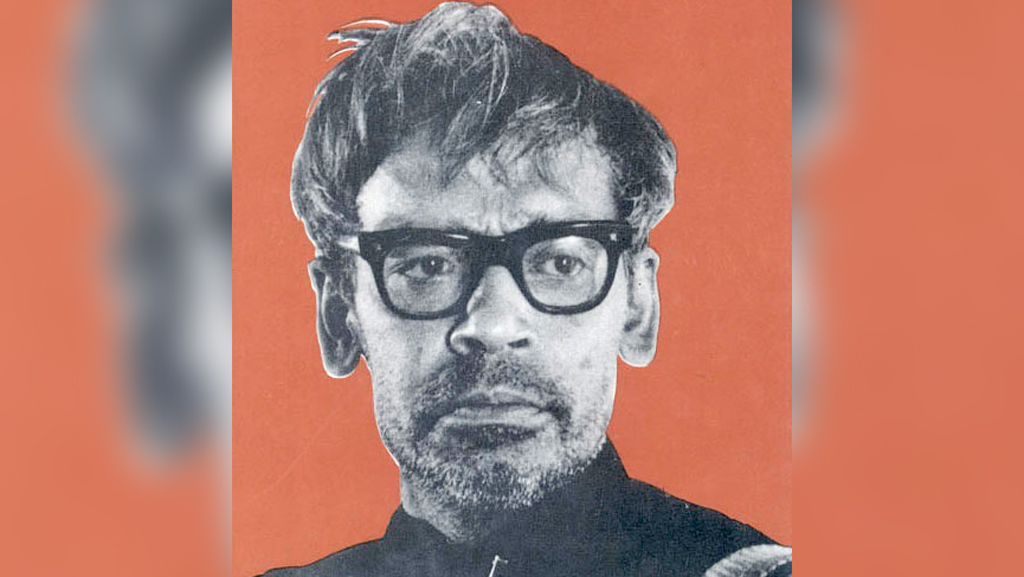
চলচ্চিত্র নির্মাণের পদ্ধতি-টদ্ধতি বুঝি না মশাই। আমার কাছে আজও প্রমথেশ বড়ুয়া ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালক। আমরা কেউই তাঁর পায়ের নখের যোগ্য নই। আমার আজও মনে পড়ে ‘গৃহদাহ’র সেই অসম্ভব ট্রানজিশন—সেই যে হাইহিল জুতো-পরা দুটো পা থেকে সোজা কেটে দুটো আলতা-মাখা পা পালকি থেকে নামছে—আমি কখনো ভুলব না।
৫ দিন আগে
বিরিয়ানি কিংবা কাবাব-পরোটা খেতে মন চাইলে পুরান ঢাকার নাজিরাবাজারের কথা মনে পড়তেই পারে। এসব খেয়ে কেউ কেউ বিউটি কিংবা নূরানীর লাচ্ছি খেয়ে ভোজ শেষ করতে পারেন। আবার কেউ ধোঁয়া ওঠা গরম চা পিরিচে নিয়ে ফুঁকে ফুঁকে গলায় ঢালতে পারেন। যাঁরা নিয়মিত যান নাজিরাবাজারে, তাঁরা জানেন এসব চা-প্রেমীর ভিড় লেগে...
৬ দিন আগেসম্পাদকীয়

১৯৬০-এর দশকে হাজি নান্না মিয়া তাঁর দুই ভাই জুম্মুন মিয়া ও চান মিয়ার সঙ্গে শুরু করেন খাবারের ব্যবসা। পুরান ঢাকার মৌলভীবাজারে ছোট্ট একটা দোকানে পাতলা মাদুর বিছিয়ে তাঁরা পরিবেশন করতেন মোরগ পোলাও। সেই মোরগ পোলাওয়ের সুঘ্রাণের সঙ্গে এর সুখ্যাতি ছড়াতে সময় লাগেনি। মৌলভীবাজার থেকে পরে বেচারাম দেউড়ির সরদার ভবনে সরে আসে নান্না মিয়ার ব্যবসা। দোকানের নাম হয় হাজি নান্না বিরিয়ানি।
একে একে লালবাগ চৌরাস্তা, নবাবগঞ্জ বাজার, ফকিরাপুল ও নাজিমুদ্দিন রোডে এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। একই নামে শত শত ভুয়া প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও আসল নান্নার মোরগ পোলাওয়ের স্বাদকে টেক্কা দিতে পারেনি কেউ। তাই তো ভোজনপ্রেমীরা ঠিকই চিনে নেন আদি রেসিপিটি। মোরগ পোলাওয়ের পাশাপাশি হাজি নান্না বিরিয়ানিতে পাওয়া যায় খাসির বিরিয়ানি, খাসির কাচ্চি বিরিয়ানি, বোরহানি, টিকিয়া, লাবাং ও ফিরনি। প্রতি মাসের ৫ তারিখে থাকে বিশেষ আয়োজন—আস্ত মুরগির পোলাও। ছবি: জাহিদুল ইসলাম

১৯৬০-এর দশকে হাজি নান্না মিয়া তাঁর দুই ভাই জুম্মুন মিয়া ও চান মিয়ার সঙ্গে শুরু করেন খাবারের ব্যবসা। পুরান ঢাকার মৌলভীবাজারে ছোট্ট একটা দোকানে পাতলা মাদুর বিছিয়ে তাঁরা পরিবেশন করতেন মোরগ পোলাও। সেই মোরগ পোলাওয়ের সুঘ্রাণের সঙ্গে এর সুখ্যাতি ছড়াতে সময় লাগেনি। মৌলভীবাজার থেকে পরে বেচারাম দেউড়ির সরদার ভবনে সরে আসে নান্না মিয়ার ব্যবসা। দোকানের নাম হয় হাজি নান্না বিরিয়ানি।
একে একে লালবাগ চৌরাস্তা, নবাবগঞ্জ বাজার, ফকিরাপুল ও নাজিমুদ্দিন রোডে এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। একই নামে শত শত ভুয়া প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও আসল নান্নার মোরগ পোলাওয়ের স্বাদকে টেক্কা দিতে পারেনি কেউ। তাই তো ভোজনপ্রেমীরা ঠিকই চিনে নেন আদি রেসিপিটি। মোরগ পোলাওয়ের পাশাপাশি হাজি নান্না বিরিয়ানিতে পাওয়া যায় খাসির বিরিয়ানি, খাসির কাচ্চি বিরিয়ানি, বোরহানি, টিকিয়া, লাবাং ও ফিরনি। প্রতি মাসের ৫ তারিখে থাকে বিশেষ আয়োজন—আস্ত মুরগির পোলাও। ছবি: জাহিদুল ইসলাম

কলকাতার জোড়াসাঁকো, যে স্থান বিখ্যাত হয়ে আছে ঠাকুর পরিবারের জন্য, যেখানে জন্মেছিলেন বিখ্যাত সিংহ পরিবারের কালীপ্রসন্ন সিংহ, যিনি বাংলা ভাষায় প্রথম সমগ্র ‘মহাভারত’-এর অনুবাদ সম্পন্ন করেছিলেন; সেই জোড়াসাঁকো এলাকাতেই ১৮১৩ সালে জন্ম রাধানাথ শিকদারের। তবে সেখানকার অন্য বিখ্যাত পরিবারের মতো অবস্থা ছিল না ত
০৪ মার্চ ২০২২
কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে কবি শাহীনা সোবহানের সম্মানে কবি ও সাহিত্যিকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে সাহিত্য আড্ডা। গতকাল শনিবার (১৮ অক্টোবর) বিকেলে কুমারখালী পৌর শহরের সাংবাদিক কাঙাল হরিনাথ মজুমদার স্মৃতি জাদুঘরে ড. নাসের ফাউন্ডেশনের আয়োজনে এই আড্ডার আয়োজন করা হয়।
২ দিন আগে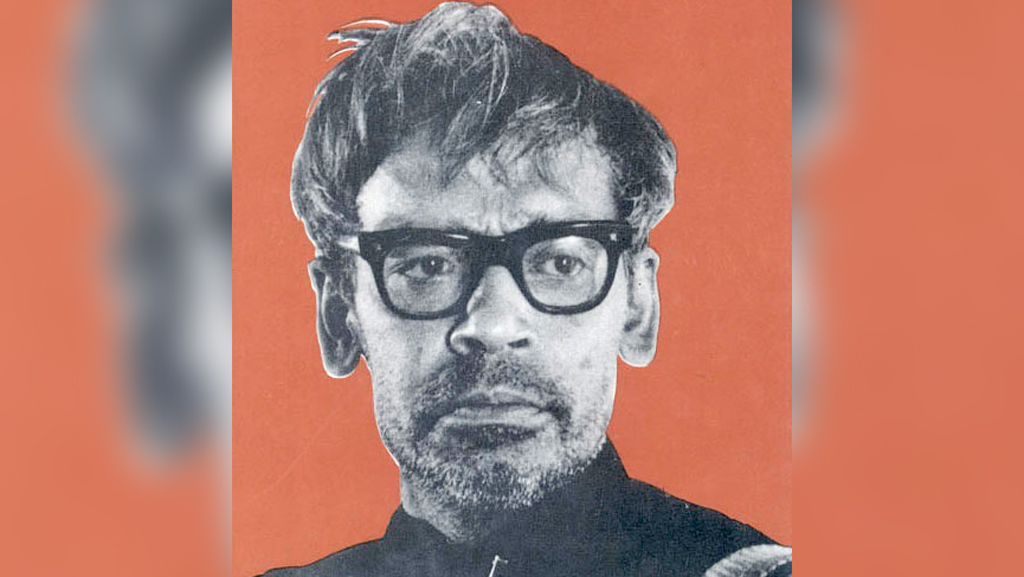
চলচ্চিত্র নির্মাণের পদ্ধতি-টদ্ধতি বুঝি না মশাই। আমার কাছে আজও প্রমথেশ বড়ুয়া ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালক। আমরা কেউই তাঁর পায়ের নখের যোগ্য নই। আমার আজও মনে পড়ে ‘গৃহদাহ’র সেই অসম্ভব ট্রানজিশন—সেই যে হাইহিল জুতো-পরা দুটো পা থেকে সোজা কেটে দুটো আলতা-মাখা পা পালকি থেকে নামছে—আমি কখনো ভুলব না।
৫ দিন আগে
বিরিয়ানি কিংবা কাবাব-পরোটা খেতে মন চাইলে পুরান ঢাকার নাজিরাবাজারের কথা মনে পড়তেই পারে। এসব খেয়ে কেউ কেউ বিউটি কিংবা নূরানীর লাচ্ছি খেয়ে ভোজ শেষ করতে পারেন। আবার কেউ ধোঁয়া ওঠা গরম চা পিরিচে নিয়ে ফুঁকে ফুঁকে গলায় ঢালতে পারেন। যাঁরা নিয়মিত যান নাজিরাবাজারে, তাঁরা জানেন এসব চা-প্রেমীর ভিড় লেগে...
৬ দিন আগেসম্পাদকীয়
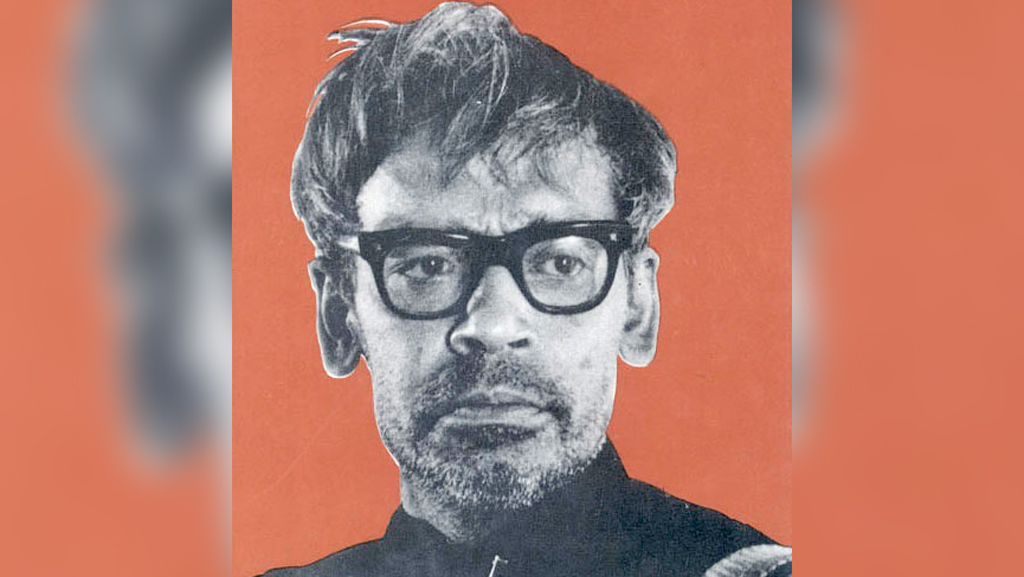
চলচ্চিত্র নির্মাণের পদ্ধতি-টদ্ধতি বুঝি না মশাই। আমার কাছে আজও প্রমথেশ বড়ুয়া ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালক। আমরা কেউই তাঁর পায়ের নখের যোগ্য নই। আমার আজও মনে পড়ে ‘গৃহদাহ’র সেই অসম্ভব ট্রানজিশন—সেই যে হাইহিল জুতো-পরা দুটো পা থেকে সোজা কেটে দুটো আলতা-মাখা পা পালকি থেকে নামছে—আমি কখনো ভুলব না। ব্যাপারটা ভদ্রলোক করেছিলেন ১৯৩৬ সালে, এ কথা ভুলবেন না। আর সেই যে সেই ‘উত্তরায়ণ’-এ বড়ুয়া সাহেবের জ্বর হওয়ার পরে ক্যামেরা সোজা সিঁড়ি দিয়ে উঠে বিছানায় গিয়ে আছড়ে পড়ল—সেটাই কি ভোলা যায়! কাণ্ডটা ঘটিয়েছেন ভদ্রলোক ডেভিড লিনের ‘অলিভার টুইস্ট’-এর বহু আগে। সাবজেকটিভ ক্যামেরা সম্পর্কে অনেক কথা আজকাল শুনতে পাই, বিভিন্ন পরিচালক নাকি খুব ভালোভাবে ব্যবহার করছেন।
...আমার কাছে গুলিয়ে গেছে সিনেমার প্রাচীন আর আধুনিক বলতে আপনারা কী বোঝাতে চেয়েছেন। এসব ধরনের কথা শুনলে আমার একটা কথাই মনে হয়, কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায় ‘দে গরুর গা ধুইয়ে’।
...চলচ্চিত্রের সামাজিক দায়িত্ব সব সময়ে হয়েছে। হয় পজিটিভ, না হয় নেগেটিভভাবে। ছবিটাকে আমি একটা শিল্প বলি। কাজেই মনে করি সর্বশিল্পের শর্ত পালিত হচ্ছে এখানেও। আমি মনে করি না যে সত্যজিৎ রায়ের ‘চারুলতা’ চ্যাপলিনের ‘এসানে’ যুগের এক রিলের ছবিগুলোর চেয়ে বেশি সচেতন।
১৯২৫ সালে তোলা আইজেনস্টাইনের ‘স্ট্রাইক’ ছবির চেয়ে বেশি সমাজসচেতন ছবি কি আজ পর্যন্ত তোলা হয়েছে? পাবস্ট-এর ‘কামেরা ডে শেফট’ আজও পর্যন্ত আমার কাছে মনে হয় সবচেয়ে বেশি সমাজসচেতন একটি ছবি। চারু রায়ের ‘বাংলার মেয়ে’ বহু আগে তোলা—প্রথম বাংলা ছবি, যাতে আউটডোর ব্যবহৃত হয় সবচেয়ে বেশিভাবে, তাতেও সমাজচেতনা পরিপূর্ণ ছিল।
...রবিঠাকুর মশায় একটা বড় ভালো কথা বলে গিয়েছিলেন, ‘শিল্পকে শিল্প হতে হলে সর্বাগ্রে সত্যনিষ্ঠ হতে হয়, তারপরে সৌন্দর্যনিষ্ঠ’। কথাটা ভাবার মতো। যদি পারেন ভেবে দেখবেন।
সূত্র: ঋত্বিক ঘটকের গৃহীত সাক্ষাৎকার, ‘সাক্ষাৎ ঋত্বিক’, শিবাদিত্য দাশগুপ্ত ও সন্দীপন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ১৮-১৯
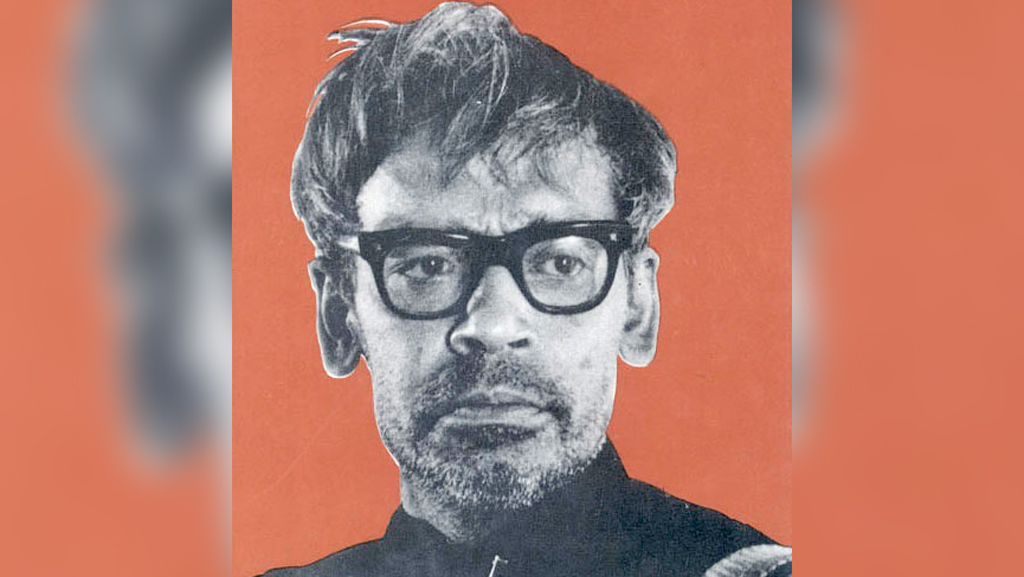
চলচ্চিত্র নির্মাণের পদ্ধতি-টদ্ধতি বুঝি না মশাই। আমার কাছে আজও প্রমথেশ বড়ুয়া ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালক। আমরা কেউই তাঁর পায়ের নখের যোগ্য নই। আমার আজও মনে পড়ে ‘গৃহদাহ’র সেই অসম্ভব ট্রানজিশন—সেই যে হাইহিল জুতো-পরা দুটো পা থেকে সোজা কেটে দুটো আলতা-মাখা পা পালকি থেকে নামছে—আমি কখনো ভুলব না। ব্যাপারটা ভদ্রলোক করেছিলেন ১৯৩৬ সালে, এ কথা ভুলবেন না। আর সেই যে সেই ‘উত্তরায়ণ’-এ বড়ুয়া সাহেবের জ্বর হওয়ার পরে ক্যামেরা সোজা সিঁড়ি দিয়ে উঠে বিছানায় গিয়ে আছড়ে পড়ল—সেটাই কি ভোলা যায়! কাণ্ডটা ঘটিয়েছেন ভদ্রলোক ডেভিড লিনের ‘অলিভার টুইস্ট’-এর বহু আগে। সাবজেকটিভ ক্যামেরা সম্পর্কে অনেক কথা আজকাল শুনতে পাই, বিভিন্ন পরিচালক নাকি খুব ভালোভাবে ব্যবহার করছেন।
...আমার কাছে গুলিয়ে গেছে সিনেমার প্রাচীন আর আধুনিক বলতে আপনারা কী বোঝাতে চেয়েছেন। এসব ধরনের কথা শুনলে আমার একটা কথাই মনে হয়, কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায় ‘দে গরুর গা ধুইয়ে’।
...চলচ্চিত্রের সামাজিক দায়িত্ব সব সময়ে হয়েছে। হয় পজিটিভ, না হয় নেগেটিভভাবে। ছবিটাকে আমি একটা শিল্প বলি। কাজেই মনে করি সর্বশিল্পের শর্ত পালিত হচ্ছে এখানেও। আমি মনে করি না যে সত্যজিৎ রায়ের ‘চারুলতা’ চ্যাপলিনের ‘এসানে’ যুগের এক রিলের ছবিগুলোর চেয়ে বেশি সচেতন।
১৯২৫ সালে তোলা আইজেনস্টাইনের ‘স্ট্রাইক’ ছবির চেয়ে বেশি সমাজসচেতন ছবি কি আজ পর্যন্ত তোলা হয়েছে? পাবস্ট-এর ‘কামেরা ডে শেফট’ আজও পর্যন্ত আমার কাছে মনে হয় সবচেয়ে বেশি সমাজসচেতন একটি ছবি। চারু রায়ের ‘বাংলার মেয়ে’ বহু আগে তোলা—প্রথম বাংলা ছবি, যাতে আউটডোর ব্যবহৃত হয় সবচেয়ে বেশিভাবে, তাতেও সমাজচেতনা পরিপূর্ণ ছিল।
...রবিঠাকুর মশায় একটা বড় ভালো কথা বলে গিয়েছিলেন, ‘শিল্পকে শিল্প হতে হলে সর্বাগ্রে সত্যনিষ্ঠ হতে হয়, তারপরে সৌন্দর্যনিষ্ঠ’। কথাটা ভাবার মতো। যদি পারেন ভেবে দেখবেন।
সূত্র: ঋত্বিক ঘটকের গৃহীত সাক্ষাৎকার, ‘সাক্ষাৎ ঋত্বিক’, শিবাদিত্য দাশগুপ্ত ও সন্দীপন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ১৮-১৯

কলকাতার জোড়াসাঁকো, যে স্থান বিখ্যাত হয়ে আছে ঠাকুর পরিবারের জন্য, যেখানে জন্মেছিলেন বিখ্যাত সিংহ পরিবারের কালীপ্রসন্ন সিংহ, যিনি বাংলা ভাষায় প্রথম সমগ্র ‘মহাভারত’-এর অনুবাদ সম্পন্ন করেছিলেন; সেই জোড়াসাঁকো এলাকাতেই ১৮১৩ সালে জন্ম রাধানাথ শিকদারের। তবে সেখানকার অন্য বিখ্যাত পরিবারের মতো অবস্থা ছিল না ত
০৪ মার্চ ২০২২
কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে কবি শাহীনা সোবহানের সম্মানে কবি ও সাহিত্যিকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে সাহিত্য আড্ডা। গতকাল শনিবার (১৮ অক্টোবর) বিকেলে কুমারখালী পৌর শহরের সাংবাদিক কাঙাল হরিনাথ মজুমদার স্মৃতি জাদুঘরে ড. নাসের ফাউন্ডেশনের আয়োজনে এই আড্ডার আয়োজন করা হয়।
২ দিন আগে
১৯৬০-এর দশকে হাজি নান্না মিয়া তাঁর দুই ভাই জুম্মুন মিয়া ও চান মিয়ার সঙ্গে শুরু করেন খাবারের ব্যবসা। পুরান ঢাকার মৌলভীবাজারে ছোট্ট একটা দোকানে পাতলা মাদুর বিছিয়ে তাঁরা পরিবেশন করতেন মোরগ পোলাও। সেই মোরগ পোলাওয়ের সুঘ্রাণের সঙ্গে এর সুখ্যাতি ছড়াতে সময় লাগেনি। মৌলভীবাজার থেকে পরে বেচারাম দেউড়ির...
৪ দিন আগে
বিরিয়ানি কিংবা কাবাব-পরোটা খেতে মন চাইলে পুরান ঢাকার নাজিরাবাজারের কথা মনে পড়তেই পারে। এসব খেয়ে কেউ কেউ বিউটি কিংবা নূরানীর লাচ্ছি খেয়ে ভোজ শেষ করতে পারেন। আবার কেউ ধোঁয়া ওঠা গরম চা পিরিচে নিয়ে ফুঁকে ফুঁকে গলায় ঢালতে পারেন। যাঁরা নিয়মিত যান নাজিরাবাজারে, তাঁরা জানেন এসব চা-প্রেমীর ভিড় লেগে...
৬ দিন আগেসম্পাদকীয়

বিরিয়ানি কিংবা কাবাব-পরোটা খেতে মন চাইলে পুরান ঢাকার নাজিরাবাজারের কথা মনে পড়তেই পারে। এসব খেয়ে কেউ কেউ বিউটি কিংবা নূরানীর লাচ্ছি খেয়ে ভোজ শেষ করতে পারেন। আবার কেউ ধোঁয়া ওঠা গরম চা পিরিচে নিয়ে ফুঁকে ফুঁকে গলায় ঢালতে পারেন। যাঁরা নিয়মিত যান নাজিরাবাজারে, তাঁরা জানেন এসব চা-প্রেমীর ভিড় লেগে থাকে পান্নু খান টি স্টোরে।
পান্নুর চা নামেই সমধিক পরিচিত কাজী আলাউদ্দিন রোডের ৩৭/২ নম্বরের ছোট দোকানটি। সাধারণ চায়ের পাশাপাশি মালাই চা, কফি চা, পনির চা, বাদাম চা—এ রকম নানা চায়ের সঙ্গে চাইলে বিস্কুট, পাউরুটি বা বাকরখানি ডুবিয়ে খেতে পারেন, এই দোকানে বসে। বসার জায়গা পাওয়াটা বেশির ভাগ সময় দুষ্কর হয়ে পড়ে। তাই দাঁড়িয়েই নিতে হয় পান্নুর চায়ের স্বাদ। ২০০৮ সালে প্রথমে নিউমার্কেটে চালু হলেও দোকানটি এখন নাজিরাবাজারে। খুব অল্প সময়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এর চা।
ছবি: মেহেদী হাসান

বিরিয়ানি কিংবা কাবাব-পরোটা খেতে মন চাইলে পুরান ঢাকার নাজিরাবাজারের কথা মনে পড়তেই পারে। এসব খেয়ে কেউ কেউ বিউটি কিংবা নূরানীর লাচ্ছি খেয়ে ভোজ শেষ করতে পারেন। আবার কেউ ধোঁয়া ওঠা গরম চা পিরিচে নিয়ে ফুঁকে ফুঁকে গলায় ঢালতে পারেন। যাঁরা নিয়মিত যান নাজিরাবাজারে, তাঁরা জানেন এসব চা-প্রেমীর ভিড় লেগে থাকে পান্নু খান টি স্টোরে।
পান্নুর চা নামেই সমধিক পরিচিত কাজী আলাউদ্দিন রোডের ৩৭/২ নম্বরের ছোট দোকানটি। সাধারণ চায়ের পাশাপাশি মালাই চা, কফি চা, পনির চা, বাদাম চা—এ রকম নানা চায়ের সঙ্গে চাইলে বিস্কুট, পাউরুটি বা বাকরখানি ডুবিয়ে খেতে পারেন, এই দোকানে বসে। বসার জায়গা পাওয়াটা বেশির ভাগ সময় দুষ্কর হয়ে পড়ে। তাই দাঁড়িয়েই নিতে হয় পান্নুর চায়ের স্বাদ। ২০০৮ সালে প্রথমে নিউমার্কেটে চালু হলেও দোকানটি এখন নাজিরাবাজারে। খুব অল্প সময়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এর চা।
ছবি: মেহেদী হাসান

কলকাতার জোড়াসাঁকো, যে স্থান বিখ্যাত হয়ে আছে ঠাকুর পরিবারের জন্য, যেখানে জন্মেছিলেন বিখ্যাত সিংহ পরিবারের কালীপ্রসন্ন সিংহ, যিনি বাংলা ভাষায় প্রথম সমগ্র ‘মহাভারত’-এর অনুবাদ সম্পন্ন করেছিলেন; সেই জোড়াসাঁকো এলাকাতেই ১৮১৩ সালে জন্ম রাধানাথ শিকদারের। তবে সেখানকার অন্য বিখ্যাত পরিবারের মতো অবস্থা ছিল না ত
০৪ মার্চ ২০২২
কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে কবি শাহীনা সোবহানের সম্মানে কবি ও সাহিত্যিকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে সাহিত্য আড্ডা। গতকাল শনিবার (১৮ অক্টোবর) বিকেলে কুমারখালী পৌর শহরের সাংবাদিক কাঙাল হরিনাথ মজুমদার স্মৃতি জাদুঘরে ড. নাসের ফাউন্ডেশনের আয়োজনে এই আড্ডার আয়োজন করা হয়।
২ দিন আগে
১৯৬০-এর দশকে হাজি নান্না মিয়া তাঁর দুই ভাই জুম্মুন মিয়া ও চান মিয়ার সঙ্গে শুরু করেন খাবারের ব্যবসা। পুরান ঢাকার মৌলভীবাজারে ছোট্ট একটা দোকানে পাতলা মাদুর বিছিয়ে তাঁরা পরিবেশন করতেন মোরগ পোলাও। সেই মোরগ পোলাওয়ের সুঘ্রাণের সঙ্গে এর সুখ্যাতি ছড়াতে সময় লাগেনি। মৌলভীবাজার থেকে পরে বেচারাম দেউড়ির...
৪ দিন আগে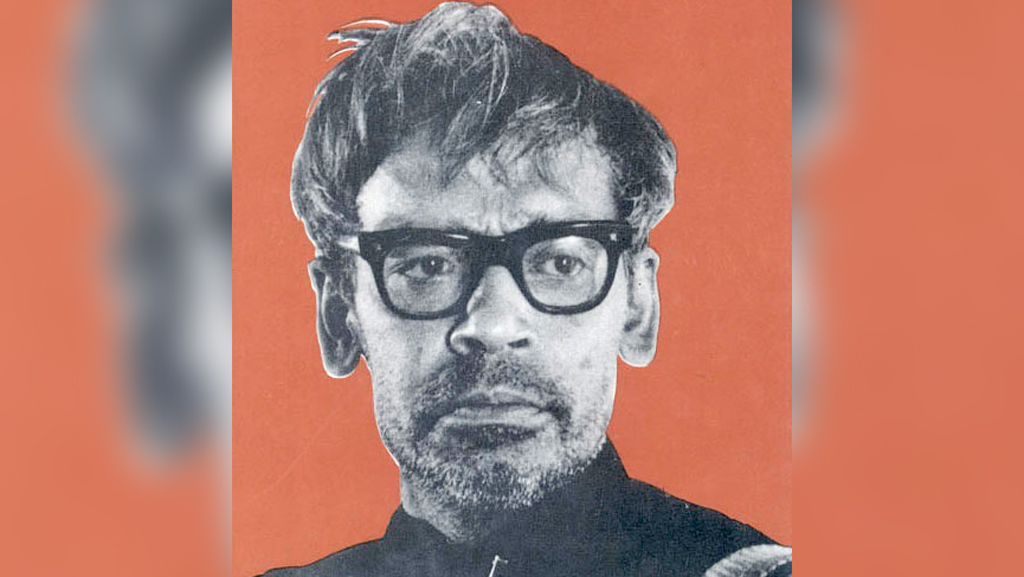
চলচ্চিত্র নির্মাণের পদ্ধতি-টদ্ধতি বুঝি না মশাই। আমার কাছে আজও প্রমথেশ বড়ুয়া ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালক। আমরা কেউই তাঁর পায়ের নখের যোগ্য নই। আমার আজও মনে পড়ে ‘গৃহদাহ’র সেই অসম্ভব ট্রানজিশন—সেই যে হাইহিল জুতো-পরা দুটো পা থেকে সোজা কেটে দুটো আলতা-মাখা পা পালকি থেকে নামছে—আমি কখনো ভুলব না।
৫ দিন আগে