আরিফ আবেদ আদিত্য

বুড়িগঙ্গার পাড় থেকে টেমসের তীরে আসার প্রায় এক বছর হয়ে এল। গত বছর অক্টোবরে সূর্যালোক উদ্ভাসিত প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর এক দেশ ছেড়ে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পাড়ে হাড়কাঁপানো ধূসর ভূমিতে পদার্পণ করি। আমার আগমনের সময়টায় বিলাতে শীত আসি-আসি করছে—জাঁকিয়ে বসেনি। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা আগেই বলেছিলেন, ইউরোপের শীত কোনো ছেলেখেলা নয়। গরমের দেশ থেকে গিয়ে শীত নিয়ে সামান্য হেলাফেলা করলেই সর্দি-কাশি আর জ্বরে জীবন জেরবার করে দেবে। কনকনে মাঘের ঠান্ডার চেয়েও অধিক হাড়কাঁপানো শুধু নয়, হাড় ফুটা করা শীত এখানে বিরাজ করে। কয়েক পরতের গরম কাপড়েও এই কনকনে ঠান্ডা নিবারণ সম্ভব হয় না। লন্ডনে যেদিন আসি, এয়ারপোর্ট থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডা একটা হালকা ঝাপটা এসে লাগে নাকে-মুখে। আগেভাগে প্রস্তুতির কয়েক প্রস্থ কাপড়ে অবগুণ্ঠিত শরীর টের না পেলেও ঠান্ডার দাপটের ঈষৎ বিজ্ঞাপন নাকের ডগা ছুঁয়ে ঝাঁজের আঁচ দিয়েছিল বৈকি!
আমার ইংল্যান্ডে আসার কারণ, দ্বিতীয় মাস্টার্স করা—একটা ডিগ্রি অর্জনের চেয়ে ইংরেজি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে কিছুটা ঘনিষ্ঠভাবে অবলোকন-পর্যবেক্ষণ করা। সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে—প্রায় দুই শ বছর যারা শাসন করল, যাদের সাংস্কৃতিক প্রভাববলয় কলোনিয়াল দেশগুলোতে এখনো বিরাজমান, তাদের যাপিত জীবনপদ্ধতি ও সমাজকে কাছ থেকে দেখার আগ্রহই আমাকে এখানে নিয়ে আসে।
বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটে লন্ডনের হিথরো এয়ারপোর্টে নামি রাত ১০টার দিকে। ইমিগ্রেশন, লাগেজ বেল্ট থেকে ব্যাগপত্র নিয়ে বের হতে হতে সাড়ে ১১টা। বাইরে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল বন্ধু ও সহকর্মী কিংস কলেজে পিএইচডি ফেলো জগদীশ। হিথরো ইমিগ্রেশনে লম্বা লাইন, ফ্লাইট সরাসরি বিমান বাংলাদেশের হওয়ায় লাইনে সবাই বাংলাদেশি নাগরিকই ছিলেন। নানা পেশার বিভিন্ন বয়সী নারী-পুরুষ লম্বা লাইন দাঁড়িয়ে। ইমিগ্রেশনের কাউন্টার অনেক; মাথার ওপরে বড় করে সাইনবোর্ডে স্থানে স্থানে লেখা ‘ইউকে বর্ডার’। লাইনে দাঁড়িয়ে লেখাটায় চোখ পড়তেই মনে হলো নতুন কোনো দেশে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। বাংলাদেশ থেকে উড়াল দেওয়ার আগ পর্যন্ত এমন মনে হয়নি।
লন্ডনে ইমিগ্রেশন অফিসাররা ভিসা-পাসপোর্ট চেক করার সময় যাত্রীদের অনেক ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। এতে এয়ারপোর্ট থেকে বের হতে বেশ সময় লেগে যায়। ইমিগ্রেশনের জেরায় আমার মতো পড়তে আসা শিক্ষার্থী ছাড়াও প্রথমবার যারা ব্রিটেনে এসেছে, সবাইকেই দেখলাম কমবেশি উদ্বিগ্ন হতে। এর পেছনে কারণও আছে বৈকি! কারও প্রশ্নের উত্তর মনঃপূত না হলে তাকে আলাদা করে অন্য একটি রুমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কালো উর্দির ওপর পুলিশ লেখা ব্যক্তিরা যখন কাউকে আলাদা করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায়, তখন পেছনে লাইনে দাঁড়ানো যাত্রীদের মানসিক অবস্থা কেমন হয়, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ইউএসএ, ইউকের ইমিগ্রেশনের কড়াকড়ি নিয়ে নতুন কিছু বলার নেই আসলে। তবে আমার কাছে যত দূর মনে হয়েছে, ভাষা সমস্যাই ইমিগ্রেশনে ভোগান্তির অন্যতম কারণ। অনেককে দেখলাম দোভাষীর আশ্রয় নিতে। লাইনে দাঁড়ানো ব্যক্তিদের মধ্য থেকেই কেউ দোভাষী হিসেবে সাহায্য করবে কি না, জিজ্ঞেস করা হয়। ইমিগ্রেশন অফিসারদের নিজস্ব ব্রিটিশ উচ্চারণে বলা প্রশ্ন অনেকের পক্ষেই বোঝা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বুঝে বা না বুঝে ‘ইয়েস’, ‘নো’-এর মতো উত্তর দিয়ে কোনোমতে ইমিগ্রেশন পার হওয়ার চিন্তা করতে গিয়েই অনেকে ঝামেলা বাড়ায়। এরা সঠিক উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত পাসপোর্টে ছাড়পত্রের সিল দেবেই না। আমার সামনে তখন ৮-১০ জন। এমন সময় জিজ্ঞেস করা হয়, কেউ দোভাষী হবে কি না। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পা ব্যথা হওয়ার জোগাড়। যারা দোভাষী হিসেবে সাহায্য করেছে, দেখলাম, তারা তাড়াতাড়ি বের হয়ে গেছে। তাই আমিও এবার সুযোগটা নিই। একজনকে সাহায্য করলাম। তাকে ইউকেতে কে থাকে, কোথায় থাকবে, কী জন্য এসেছে ইত্যাদি কয়েকটা প্রশ্ন করেই ছেড়ে দেয়। এবার আমার পালা। ব্রিটিশদের একটা খুব ভালো দিক আছে। কাউকে সামান্য সাহায্য করলে, ফুটপাতে হাঁটার সময় একটু রাস্তা ছেড়ে দিলে, কোনো লাইনে আগে যেতে দিলে ধন্যবাদ দিতে দিতে মুখে ফেনা তুলে ফেলে। আগের যাত্রীকে সাহায্য করেছি—এ জন্যই হয়তো ইমিগ্রেশন কাউন্টারে বসা প্রায় পঞ্চাশোর্ধ্ব স্থূলকায় শ্বেতাঙ্গ অফিসার আমার পাসপোর্ট হাতে নিয়ে কেবল একটা প্রশ্নই করেন, ‘কোন বিষয়ে পড়তে এসেছ?’ উত্তর দেওয়ার আগেই সিল মেরে পাসপোর্ট ফেরত দিতে দিতে হাস্যোজ্জ্বল ভঙ্গিতে তিনি বলেন, ‘ওয়েলকাম টু ইউনাইটেড কিংডম মাই বয়।’ অপ্রত্যাশিত এমন উষ্ণ অভ্যর্থনায় দীর্ঘ ভ্রমণক্লান্তি নিমেষে উবে গেল।
 ইমিগ্রেশন শেষ করে লাগেজসহ গেট পেরোতেই বন্ধু জগদীশের দেখা পাই। বেচারা তিন-চার ঘণ্টা ধরে অপেক্ষায় আছে। লন্ডনের বিখ্যাত টিউবে চড়ার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। টিউব অনেকটা মেট্রোরেলের মতো—পার্থক্য হলো টিউব মাটির নিচ দিয়ে চলে। হিথরো থেকে বন্ধুর বাসা পূর্ব লন্ডনের ফরেস্ট গেটে আসতে আসতে রাত ১২টা পার হয়ে যায়। মজার ব্যাপার হলো, টিউবে সেই মধ্যরাতেও দেখলাম মেয়েরা নির্বিঘ্নে চলাফেরা করছে। কোথাও কোনো ভয়-শঙ্কার লেশমাত্র নেই। এ ছাড়া লন্ডনে নেমেই একবারের দর্শনে যে বিষয়টা দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়, তা হলো টিউবের কামরায় দেখা জাতিগত বৈচিত্র্যের সমাহার। ধরা যাক, একেকটা কামরায় ১০ জন যাত্রী—তাদের আটজনই দেখা যাবে ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রতিনিধিত্ব করছে। কী চুলের বাহার, কী বেশভূষা, গাত্রবর্ণ বা ভাষা ইত্যাদি সব মিলিয়ে মনে হবে একটি আন্তর্জাতিক কামরায় বসে আছি। লন্ডনে এই বিষয় বেশ উপভোগ্য লেগেছে—এই শহরে নিজেকে সংখ্যালঘু বা আগন্তুক মনে হয় না; ফলে হীনম্মন্যতা আসে না; যেমনটা ইংল্যান্ডের অন্য শহরগুলোতে কিছুটা অনুভব হয়। শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ বা এশীয়দের সমান পদচারণে মুখর এখানকার পাবলিক পরিবহন। চলার পথে কেউ বই পড়ছে, কেউ মোবাইলে গেমস খেলছে, কেউ হেডফোনে গান শুনছে—যে যার জগতে আত্মমগ্ন, কর্মক্লান্ত কেউবা বাসায় ফেরার আগে একটু ঝিম মেরে ঘুমিয়ে নিচ্ছে—গন্তব্যস্থলে পৌঁছামাত্র টুপ করে নেমে পড়ছে। আবার কোনো স্টেশন থেকে এক জোড়া কপোত-কপোতী উঠে সিট না পেয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গনরত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে জীবনের প্রতিটা মুহূর্তকে উপভোগ করে নিচ্ছে। কারও প্রতি কারও কোনো বিকার-অনুযোগ নেই।
ইমিগ্রেশন শেষ করে লাগেজসহ গেট পেরোতেই বন্ধু জগদীশের দেখা পাই। বেচারা তিন-চার ঘণ্টা ধরে অপেক্ষায় আছে। লন্ডনের বিখ্যাত টিউবে চড়ার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। টিউব অনেকটা মেট্রোরেলের মতো—পার্থক্য হলো টিউব মাটির নিচ দিয়ে চলে। হিথরো থেকে বন্ধুর বাসা পূর্ব লন্ডনের ফরেস্ট গেটে আসতে আসতে রাত ১২টা পার হয়ে যায়। মজার ব্যাপার হলো, টিউবে সেই মধ্যরাতেও দেখলাম মেয়েরা নির্বিঘ্নে চলাফেরা করছে। কোথাও কোনো ভয়-শঙ্কার লেশমাত্র নেই। এ ছাড়া লন্ডনে নেমেই একবারের দর্শনে যে বিষয়টা দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়, তা হলো টিউবের কামরায় দেখা জাতিগত বৈচিত্র্যের সমাহার। ধরা যাক, একেকটা কামরায় ১০ জন যাত্রী—তাদের আটজনই দেখা যাবে ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রতিনিধিত্ব করছে। কী চুলের বাহার, কী বেশভূষা, গাত্রবর্ণ বা ভাষা ইত্যাদি সব মিলিয়ে মনে হবে একটি আন্তর্জাতিক কামরায় বসে আছি। লন্ডনে এই বিষয় বেশ উপভোগ্য লেগেছে—এই শহরে নিজেকে সংখ্যালঘু বা আগন্তুক মনে হয় না; ফলে হীনম্মন্যতা আসে না; যেমনটা ইংল্যান্ডের অন্য শহরগুলোতে কিছুটা অনুভব হয়। শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ বা এশীয়দের সমান পদচারণে মুখর এখানকার পাবলিক পরিবহন। চলার পথে কেউ বই পড়ছে, কেউ মোবাইলে গেমস খেলছে, কেউ হেডফোনে গান শুনছে—যে যার জগতে আত্মমগ্ন, কর্মক্লান্ত কেউবা বাসায় ফেরার আগে একটু ঝিম মেরে ঘুমিয়ে নিচ্ছে—গন্তব্যস্থলে পৌঁছামাত্র টুপ করে নেমে পড়ছে। আবার কোনো স্টেশন থেকে এক জোড়া কপোত-কপোতী উঠে সিট না পেয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গনরত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে জীবনের প্রতিটা মুহূর্তকে উপভোগ করে নিচ্ছে। কারও প্রতি কারও কোনো বিকার-অনুযোগ নেই।
 মূল সড়ক থেকে পাতাল স্টেশনে যাওয়ার জন্য বেশ কয়েকবার চলন্ত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে হয়। আমাদের প্রাথমিক গন্তব্য স্ট্র্যাটফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল রেলস্টেশন। সেখান থেকে ট্যাক্সি বা উবার নিয়ে বাসায় যাওয়ার পরিকল্পনা। হিথরো থেকে ফরেস্টগেট যেতে কয়েকবার টিউব পরিবর্তন করতে হয়। এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। কারণ, সরাসরি ট্যাক্সিতে গেলে অনেক ভাড়া। এখানকার টিউব স্টেশন মাটির গভীরে অবস্থিত। টিউবে চড়ার জন্য বেশ কয়েকটা চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয়। আমাদের দেশের শপিং মলের এস্কেলেটরের চেয়ে প্রায় ১০ গুণ দৈর্ঘ্যের হবে এসব চলন্ত সিঁড়ি। লন্ডনের পাতাল রেললাইন-টিউব ব্যবস্থা এক এলাহি কারবার। এগুলো দেখলে যে কারও মনে হবে মাটির নিচে আরেক লন্ডন শহর অবস্থিত। আক্ষরিক অর্থেই, মাটির ওপরে ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে বা ফুটপাতে হাঁটতে গিয়ে মাটির নিচে টিউব-ট্রেন চলার কম্পন অনুভূত হয়। যদিও এগুলো মাটির নিচে প্রায় ২০-৩০ তলা বিল্ডিংয়ের সমান গভীরে অবস্থিত। দিন নেই, রাত নেই—মাটির ওপরে ও নিচে বিরামহীনভাবে চলে লন্ডনের পাবলিক পরিবহন।
মূল সড়ক থেকে পাতাল স্টেশনে যাওয়ার জন্য বেশ কয়েকবার চলন্ত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে হয়। আমাদের প্রাথমিক গন্তব্য স্ট্র্যাটফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল রেলস্টেশন। সেখান থেকে ট্যাক্সি বা উবার নিয়ে বাসায় যাওয়ার পরিকল্পনা। হিথরো থেকে ফরেস্টগেট যেতে কয়েকবার টিউব পরিবর্তন করতে হয়। এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। কারণ, সরাসরি ট্যাক্সিতে গেলে অনেক ভাড়া। এখানকার টিউব স্টেশন মাটির গভীরে অবস্থিত। টিউবে চড়ার জন্য বেশ কয়েকটা চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয়। আমাদের দেশের শপিং মলের এস্কেলেটরের চেয়ে প্রায় ১০ গুণ দৈর্ঘ্যের হবে এসব চলন্ত সিঁড়ি। লন্ডনের পাতাল রেললাইন-টিউব ব্যবস্থা এক এলাহি কারবার। এগুলো দেখলে যে কারও মনে হবে মাটির নিচে আরেক লন্ডন শহর অবস্থিত। আক্ষরিক অর্থেই, মাটির ওপরে ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে বা ফুটপাতে হাঁটতে গিয়ে মাটির নিচে টিউব-ট্রেন চলার কম্পন অনুভূত হয়। যদিও এগুলো মাটির নিচে প্রায় ২০-৩০ তলা বিল্ডিংয়ের সমান গভীরে অবস্থিত। দিন নেই, রাত নেই—মাটির ওপরে ও নিচে বিরামহীনভাবে চলে লন্ডনের পাবলিক পরিবহন।
রাতে বন্ধুর বাসায় আতিথেয়তা গ্রহণ করে পরদিন রওনা দিই নিজ গন্তব্য শহর—ক্যান্টাবরিতে। ক্যান্টাবরি সাহিত্যের ছাত্রদের কাছে এক অবিস্মরণীয় নাম। ইংরেজি সাহিত্যের জনক জিওফ্রে চসারের ‘ক্যান্টাবরি টেলস’-এর সেই ক্যান্টাবরি শহরে কাটে আমার ১১ মাস। এই শহরের আনাচকানাচে ছড়িয়ে আছে ইংল্যান্ডের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির হাজার বছরের ইতিহাস।
ক্যান্টাবরিকে বলা হয় ‘লন্ডন বিফোর লন্ডন’। রাজধানী লন্ডন গড়ে ওঠার আগে ইংল্যান্ডের লন্ডন ছিল এই শহর। এই গল্প হবে পরের পর্বে।
(চলবে)

বুড়িগঙ্গার পাড় থেকে টেমসের তীরে আসার প্রায় এক বছর হয়ে এল। গত বছর অক্টোবরে সূর্যালোক উদ্ভাসিত প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর এক দেশ ছেড়ে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পাড়ে হাড়কাঁপানো ধূসর ভূমিতে পদার্পণ করি। আমার আগমনের সময়টায় বিলাতে শীত আসি-আসি করছে—জাঁকিয়ে বসেনি। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা আগেই বলেছিলেন, ইউরোপের শীত কোনো ছেলেখেলা নয়। গরমের দেশ থেকে গিয়ে শীত নিয়ে সামান্য হেলাফেলা করলেই সর্দি-কাশি আর জ্বরে জীবন জেরবার করে দেবে। কনকনে মাঘের ঠান্ডার চেয়েও অধিক হাড়কাঁপানো শুধু নয়, হাড় ফুটা করা শীত এখানে বিরাজ করে। কয়েক পরতের গরম কাপড়েও এই কনকনে ঠান্ডা নিবারণ সম্ভব হয় না। লন্ডনে যেদিন আসি, এয়ারপোর্ট থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডা একটা হালকা ঝাপটা এসে লাগে নাকে-মুখে। আগেভাগে প্রস্তুতির কয়েক প্রস্থ কাপড়ে অবগুণ্ঠিত শরীর টের না পেলেও ঠান্ডার দাপটের ঈষৎ বিজ্ঞাপন নাকের ডগা ছুঁয়ে ঝাঁজের আঁচ দিয়েছিল বৈকি!
আমার ইংল্যান্ডে আসার কারণ, দ্বিতীয় মাস্টার্স করা—একটা ডিগ্রি অর্জনের চেয়ে ইংরেজি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে কিছুটা ঘনিষ্ঠভাবে অবলোকন-পর্যবেক্ষণ করা। সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে—প্রায় দুই শ বছর যারা শাসন করল, যাদের সাংস্কৃতিক প্রভাববলয় কলোনিয়াল দেশগুলোতে এখনো বিরাজমান, তাদের যাপিত জীবনপদ্ধতি ও সমাজকে কাছ থেকে দেখার আগ্রহই আমাকে এখানে নিয়ে আসে।
বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটে লন্ডনের হিথরো এয়ারপোর্টে নামি রাত ১০টার দিকে। ইমিগ্রেশন, লাগেজ বেল্ট থেকে ব্যাগপত্র নিয়ে বের হতে হতে সাড়ে ১১টা। বাইরে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল বন্ধু ও সহকর্মী কিংস কলেজে পিএইচডি ফেলো জগদীশ। হিথরো ইমিগ্রেশনে লম্বা লাইন, ফ্লাইট সরাসরি বিমান বাংলাদেশের হওয়ায় লাইনে সবাই বাংলাদেশি নাগরিকই ছিলেন। নানা পেশার বিভিন্ন বয়সী নারী-পুরুষ লম্বা লাইন দাঁড়িয়ে। ইমিগ্রেশনের কাউন্টার অনেক; মাথার ওপরে বড় করে সাইনবোর্ডে স্থানে স্থানে লেখা ‘ইউকে বর্ডার’। লাইনে দাঁড়িয়ে লেখাটায় চোখ পড়তেই মনে হলো নতুন কোনো দেশে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। বাংলাদেশ থেকে উড়াল দেওয়ার আগ পর্যন্ত এমন মনে হয়নি।
লন্ডনে ইমিগ্রেশন অফিসাররা ভিসা-পাসপোর্ট চেক করার সময় যাত্রীদের অনেক ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। এতে এয়ারপোর্ট থেকে বের হতে বেশ সময় লেগে যায়। ইমিগ্রেশনের জেরায় আমার মতো পড়তে আসা শিক্ষার্থী ছাড়াও প্রথমবার যারা ব্রিটেনে এসেছে, সবাইকেই দেখলাম কমবেশি উদ্বিগ্ন হতে। এর পেছনে কারণও আছে বৈকি! কারও প্রশ্নের উত্তর মনঃপূত না হলে তাকে আলাদা করে অন্য একটি রুমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কালো উর্দির ওপর পুলিশ লেখা ব্যক্তিরা যখন কাউকে আলাদা করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায়, তখন পেছনে লাইনে দাঁড়ানো যাত্রীদের মানসিক অবস্থা কেমন হয়, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ইউএসএ, ইউকের ইমিগ্রেশনের কড়াকড়ি নিয়ে নতুন কিছু বলার নেই আসলে। তবে আমার কাছে যত দূর মনে হয়েছে, ভাষা সমস্যাই ইমিগ্রেশনে ভোগান্তির অন্যতম কারণ। অনেককে দেখলাম দোভাষীর আশ্রয় নিতে। লাইনে দাঁড়ানো ব্যক্তিদের মধ্য থেকেই কেউ দোভাষী হিসেবে সাহায্য করবে কি না, জিজ্ঞেস করা হয়। ইমিগ্রেশন অফিসারদের নিজস্ব ব্রিটিশ উচ্চারণে বলা প্রশ্ন অনেকের পক্ষেই বোঝা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বুঝে বা না বুঝে ‘ইয়েস’, ‘নো’-এর মতো উত্তর দিয়ে কোনোমতে ইমিগ্রেশন পার হওয়ার চিন্তা করতে গিয়েই অনেকে ঝামেলা বাড়ায়। এরা সঠিক উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত পাসপোর্টে ছাড়পত্রের সিল দেবেই না। আমার সামনে তখন ৮-১০ জন। এমন সময় জিজ্ঞেস করা হয়, কেউ দোভাষী হবে কি না। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পা ব্যথা হওয়ার জোগাড়। যারা দোভাষী হিসেবে সাহায্য করেছে, দেখলাম, তারা তাড়াতাড়ি বের হয়ে গেছে। তাই আমিও এবার সুযোগটা নিই। একজনকে সাহায্য করলাম। তাকে ইউকেতে কে থাকে, কোথায় থাকবে, কী জন্য এসেছে ইত্যাদি কয়েকটা প্রশ্ন করেই ছেড়ে দেয়। এবার আমার পালা। ব্রিটিশদের একটা খুব ভালো দিক আছে। কাউকে সামান্য সাহায্য করলে, ফুটপাতে হাঁটার সময় একটু রাস্তা ছেড়ে দিলে, কোনো লাইনে আগে যেতে দিলে ধন্যবাদ দিতে দিতে মুখে ফেনা তুলে ফেলে। আগের যাত্রীকে সাহায্য করেছি—এ জন্যই হয়তো ইমিগ্রেশন কাউন্টারে বসা প্রায় পঞ্চাশোর্ধ্ব স্থূলকায় শ্বেতাঙ্গ অফিসার আমার পাসপোর্ট হাতে নিয়ে কেবল একটা প্রশ্নই করেন, ‘কোন বিষয়ে পড়তে এসেছ?’ উত্তর দেওয়ার আগেই সিল মেরে পাসপোর্ট ফেরত দিতে দিতে হাস্যোজ্জ্বল ভঙ্গিতে তিনি বলেন, ‘ওয়েলকাম টু ইউনাইটেড কিংডম মাই বয়।’ অপ্রত্যাশিত এমন উষ্ণ অভ্যর্থনায় দীর্ঘ ভ্রমণক্লান্তি নিমেষে উবে গেল।
 ইমিগ্রেশন শেষ করে লাগেজসহ গেট পেরোতেই বন্ধু জগদীশের দেখা পাই। বেচারা তিন-চার ঘণ্টা ধরে অপেক্ষায় আছে। লন্ডনের বিখ্যাত টিউবে চড়ার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। টিউব অনেকটা মেট্রোরেলের মতো—পার্থক্য হলো টিউব মাটির নিচ দিয়ে চলে। হিথরো থেকে বন্ধুর বাসা পূর্ব লন্ডনের ফরেস্ট গেটে আসতে আসতে রাত ১২টা পার হয়ে যায়। মজার ব্যাপার হলো, টিউবে সেই মধ্যরাতেও দেখলাম মেয়েরা নির্বিঘ্নে চলাফেরা করছে। কোথাও কোনো ভয়-শঙ্কার লেশমাত্র নেই। এ ছাড়া লন্ডনে নেমেই একবারের দর্শনে যে বিষয়টা দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়, তা হলো টিউবের কামরায় দেখা জাতিগত বৈচিত্র্যের সমাহার। ধরা যাক, একেকটা কামরায় ১০ জন যাত্রী—তাদের আটজনই দেখা যাবে ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রতিনিধিত্ব করছে। কী চুলের বাহার, কী বেশভূষা, গাত্রবর্ণ বা ভাষা ইত্যাদি সব মিলিয়ে মনে হবে একটি আন্তর্জাতিক কামরায় বসে আছি। লন্ডনে এই বিষয় বেশ উপভোগ্য লেগেছে—এই শহরে নিজেকে সংখ্যালঘু বা আগন্তুক মনে হয় না; ফলে হীনম্মন্যতা আসে না; যেমনটা ইংল্যান্ডের অন্য শহরগুলোতে কিছুটা অনুভব হয়। শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ বা এশীয়দের সমান পদচারণে মুখর এখানকার পাবলিক পরিবহন। চলার পথে কেউ বই পড়ছে, কেউ মোবাইলে গেমস খেলছে, কেউ হেডফোনে গান শুনছে—যে যার জগতে আত্মমগ্ন, কর্মক্লান্ত কেউবা বাসায় ফেরার আগে একটু ঝিম মেরে ঘুমিয়ে নিচ্ছে—গন্তব্যস্থলে পৌঁছামাত্র টুপ করে নেমে পড়ছে। আবার কোনো স্টেশন থেকে এক জোড়া কপোত-কপোতী উঠে সিট না পেয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গনরত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে জীবনের প্রতিটা মুহূর্তকে উপভোগ করে নিচ্ছে। কারও প্রতি কারও কোনো বিকার-অনুযোগ নেই।
ইমিগ্রেশন শেষ করে লাগেজসহ গেট পেরোতেই বন্ধু জগদীশের দেখা পাই। বেচারা তিন-চার ঘণ্টা ধরে অপেক্ষায় আছে। লন্ডনের বিখ্যাত টিউবে চড়ার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। টিউব অনেকটা মেট্রোরেলের মতো—পার্থক্য হলো টিউব মাটির নিচ দিয়ে চলে। হিথরো থেকে বন্ধুর বাসা পূর্ব লন্ডনের ফরেস্ট গেটে আসতে আসতে রাত ১২টা পার হয়ে যায়। মজার ব্যাপার হলো, টিউবে সেই মধ্যরাতেও দেখলাম মেয়েরা নির্বিঘ্নে চলাফেরা করছে। কোথাও কোনো ভয়-শঙ্কার লেশমাত্র নেই। এ ছাড়া লন্ডনে নেমেই একবারের দর্শনে যে বিষয়টা দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়, তা হলো টিউবের কামরায় দেখা জাতিগত বৈচিত্র্যের সমাহার। ধরা যাক, একেকটা কামরায় ১০ জন যাত্রী—তাদের আটজনই দেখা যাবে ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রতিনিধিত্ব করছে। কী চুলের বাহার, কী বেশভূষা, গাত্রবর্ণ বা ভাষা ইত্যাদি সব মিলিয়ে মনে হবে একটি আন্তর্জাতিক কামরায় বসে আছি। লন্ডনে এই বিষয় বেশ উপভোগ্য লেগেছে—এই শহরে নিজেকে সংখ্যালঘু বা আগন্তুক মনে হয় না; ফলে হীনম্মন্যতা আসে না; যেমনটা ইংল্যান্ডের অন্য শহরগুলোতে কিছুটা অনুভব হয়। শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ বা এশীয়দের সমান পদচারণে মুখর এখানকার পাবলিক পরিবহন। চলার পথে কেউ বই পড়ছে, কেউ মোবাইলে গেমস খেলছে, কেউ হেডফোনে গান শুনছে—যে যার জগতে আত্মমগ্ন, কর্মক্লান্ত কেউবা বাসায় ফেরার আগে একটু ঝিম মেরে ঘুমিয়ে নিচ্ছে—গন্তব্যস্থলে পৌঁছামাত্র টুপ করে নেমে পড়ছে। আবার কোনো স্টেশন থেকে এক জোড়া কপোত-কপোতী উঠে সিট না পেয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গনরত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে জীবনের প্রতিটা মুহূর্তকে উপভোগ করে নিচ্ছে। কারও প্রতি কারও কোনো বিকার-অনুযোগ নেই।
 মূল সড়ক থেকে পাতাল স্টেশনে যাওয়ার জন্য বেশ কয়েকবার চলন্ত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে হয়। আমাদের প্রাথমিক গন্তব্য স্ট্র্যাটফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল রেলস্টেশন। সেখান থেকে ট্যাক্সি বা উবার নিয়ে বাসায় যাওয়ার পরিকল্পনা। হিথরো থেকে ফরেস্টগেট যেতে কয়েকবার টিউব পরিবর্তন করতে হয়। এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। কারণ, সরাসরি ট্যাক্সিতে গেলে অনেক ভাড়া। এখানকার টিউব স্টেশন মাটির গভীরে অবস্থিত। টিউবে চড়ার জন্য বেশ কয়েকটা চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয়। আমাদের দেশের শপিং মলের এস্কেলেটরের চেয়ে প্রায় ১০ গুণ দৈর্ঘ্যের হবে এসব চলন্ত সিঁড়ি। লন্ডনের পাতাল রেললাইন-টিউব ব্যবস্থা এক এলাহি কারবার। এগুলো দেখলে যে কারও মনে হবে মাটির নিচে আরেক লন্ডন শহর অবস্থিত। আক্ষরিক অর্থেই, মাটির ওপরে ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে বা ফুটপাতে হাঁটতে গিয়ে মাটির নিচে টিউব-ট্রেন চলার কম্পন অনুভূত হয়। যদিও এগুলো মাটির নিচে প্রায় ২০-৩০ তলা বিল্ডিংয়ের সমান গভীরে অবস্থিত। দিন নেই, রাত নেই—মাটির ওপরে ও নিচে বিরামহীনভাবে চলে লন্ডনের পাবলিক পরিবহন।
মূল সড়ক থেকে পাতাল স্টেশনে যাওয়ার জন্য বেশ কয়েকবার চলন্ত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে হয়। আমাদের প্রাথমিক গন্তব্য স্ট্র্যাটফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল রেলস্টেশন। সেখান থেকে ট্যাক্সি বা উবার নিয়ে বাসায় যাওয়ার পরিকল্পনা। হিথরো থেকে ফরেস্টগেট যেতে কয়েকবার টিউব পরিবর্তন করতে হয়। এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। কারণ, সরাসরি ট্যাক্সিতে গেলে অনেক ভাড়া। এখানকার টিউব স্টেশন মাটির গভীরে অবস্থিত। টিউবে চড়ার জন্য বেশ কয়েকটা চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয়। আমাদের দেশের শপিং মলের এস্কেলেটরের চেয়ে প্রায় ১০ গুণ দৈর্ঘ্যের হবে এসব চলন্ত সিঁড়ি। লন্ডনের পাতাল রেললাইন-টিউব ব্যবস্থা এক এলাহি কারবার। এগুলো দেখলে যে কারও মনে হবে মাটির নিচে আরেক লন্ডন শহর অবস্থিত। আক্ষরিক অর্থেই, মাটির ওপরে ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে বা ফুটপাতে হাঁটতে গিয়ে মাটির নিচে টিউব-ট্রেন চলার কম্পন অনুভূত হয়। যদিও এগুলো মাটির নিচে প্রায় ২০-৩০ তলা বিল্ডিংয়ের সমান গভীরে অবস্থিত। দিন নেই, রাত নেই—মাটির ওপরে ও নিচে বিরামহীনভাবে চলে লন্ডনের পাবলিক পরিবহন।
রাতে বন্ধুর বাসায় আতিথেয়তা গ্রহণ করে পরদিন রওনা দিই নিজ গন্তব্য শহর—ক্যান্টাবরিতে। ক্যান্টাবরি সাহিত্যের ছাত্রদের কাছে এক অবিস্মরণীয় নাম। ইংরেজি সাহিত্যের জনক জিওফ্রে চসারের ‘ক্যান্টাবরি টেলস’-এর সেই ক্যান্টাবরি শহরে কাটে আমার ১১ মাস। এই শহরের আনাচকানাচে ছড়িয়ে আছে ইংল্যান্ডের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির হাজার বছরের ইতিহাস।
ক্যান্টাবরিকে বলা হয় ‘লন্ডন বিফোর লন্ডন’। রাজধানী লন্ডন গড়ে ওঠার আগে ইংল্যান্ডের লন্ডন ছিল এই শহর। এই গল্প হবে পরের পর্বে।
(চলবে)
আরিফ আবেদ আদিত্য

বুড়িগঙ্গার পাড় থেকে টেমসের তীরে আসার প্রায় এক বছর হয়ে এল। গত বছর অক্টোবরে সূর্যালোক উদ্ভাসিত প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর এক দেশ ছেড়ে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পাড়ে হাড়কাঁপানো ধূসর ভূমিতে পদার্পণ করি। আমার আগমনের সময়টায় বিলাতে শীত আসি-আসি করছে—জাঁকিয়ে বসেনি। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা আগেই বলেছিলেন, ইউরোপের শীত কোনো ছেলেখেলা নয়। গরমের দেশ থেকে গিয়ে শীত নিয়ে সামান্য হেলাফেলা করলেই সর্দি-কাশি আর জ্বরে জীবন জেরবার করে দেবে। কনকনে মাঘের ঠান্ডার চেয়েও অধিক হাড়কাঁপানো শুধু নয়, হাড় ফুটা করা শীত এখানে বিরাজ করে। কয়েক পরতের গরম কাপড়েও এই কনকনে ঠান্ডা নিবারণ সম্ভব হয় না। লন্ডনে যেদিন আসি, এয়ারপোর্ট থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডা একটা হালকা ঝাপটা এসে লাগে নাকে-মুখে। আগেভাগে প্রস্তুতির কয়েক প্রস্থ কাপড়ে অবগুণ্ঠিত শরীর টের না পেলেও ঠান্ডার দাপটের ঈষৎ বিজ্ঞাপন নাকের ডগা ছুঁয়ে ঝাঁজের আঁচ দিয়েছিল বৈকি!
আমার ইংল্যান্ডে আসার কারণ, দ্বিতীয় মাস্টার্স করা—একটা ডিগ্রি অর্জনের চেয়ে ইংরেজি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে কিছুটা ঘনিষ্ঠভাবে অবলোকন-পর্যবেক্ষণ করা। সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে—প্রায় দুই শ বছর যারা শাসন করল, যাদের সাংস্কৃতিক প্রভাববলয় কলোনিয়াল দেশগুলোতে এখনো বিরাজমান, তাদের যাপিত জীবনপদ্ধতি ও সমাজকে কাছ থেকে দেখার আগ্রহই আমাকে এখানে নিয়ে আসে।
বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটে লন্ডনের হিথরো এয়ারপোর্টে নামি রাত ১০টার দিকে। ইমিগ্রেশন, লাগেজ বেল্ট থেকে ব্যাগপত্র নিয়ে বের হতে হতে সাড়ে ১১টা। বাইরে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল বন্ধু ও সহকর্মী কিংস কলেজে পিএইচডি ফেলো জগদীশ। হিথরো ইমিগ্রেশনে লম্বা লাইন, ফ্লাইট সরাসরি বিমান বাংলাদেশের হওয়ায় লাইনে সবাই বাংলাদেশি নাগরিকই ছিলেন। নানা পেশার বিভিন্ন বয়সী নারী-পুরুষ লম্বা লাইন দাঁড়িয়ে। ইমিগ্রেশনের কাউন্টার অনেক; মাথার ওপরে বড় করে সাইনবোর্ডে স্থানে স্থানে লেখা ‘ইউকে বর্ডার’। লাইনে দাঁড়িয়ে লেখাটায় চোখ পড়তেই মনে হলো নতুন কোনো দেশে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। বাংলাদেশ থেকে উড়াল দেওয়ার আগ পর্যন্ত এমন মনে হয়নি।
লন্ডনে ইমিগ্রেশন অফিসাররা ভিসা-পাসপোর্ট চেক করার সময় যাত্রীদের অনেক ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। এতে এয়ারপোর্ট থেকে বের হতে বেশ সময় লেগে যায়। ইমিগ্রেশনের জেরায় আমার মতো পড়তে আসা শিক্ষার্থী ছাড়াও প্রথমবার যারা ব্রিটেনে এসেছে, সবাইকেই দেখলাম কমবেশি উদ্বিগ্ন হতে। এর পেছনে কারণও আছে বৈকি! কারও প্রশ্নের উত্তর মনঃপূত না হলে তাকে আলাদা করে অন্য একটি রুমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কালো উর্দির ওপর পুলিশ লেখা ব্যক্তিরা যখন কাউকে আলাদা করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায়, তখন পেছনে লাইনে দাঁড়ানো যাত্রীদের মানসিক অবস্থা কেমন হয়, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ইউএসএ, ইউকের ইমিগ্রেশনের কড়াকড়ি নিয়ে নতুন কিছু বলার নেই আসলে। তবে আমার কাছে যত দূর মনে হয়েছে, ভাষা সমস্যাই ইমিগ্রেশনে ভোগান্তির অন্যতম কারণ। অনেককে দেখলাম দোভাষীর আশ্রয় নিতে। লাইনে দাঁড়ানো ব্যক্তিদের মধ্য থেকেই কেউ দোভাষী হিসেবে সাহায্য করবে কি না, জিজ্ঞেস করা হয়। ইমিগ্রেশন অফিসারদের নিজস্ব ব্রিটিশ উচ্চারণে বলা প্রশ্ন অনেকের পক্ষেই বোঝা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বুঝে বা না বুঝে ‘ইয়েস’, ‘নো’-এর মতো উত্তর দিয়ে কোনোমতে ইমিগ্রেশন পার হওয়ার চিন্তা করতে গিয়েই অনেকে ঝামেলা বাড়ায়। এরা সঠিক উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত পাসপোর্টে ছাড়পত্রের সিল দেবেই না। আমার সামনে তখন ৮-১০ জন। এমন সময় জিজ্ঞেস করা হয়, কেউ দোভাষী হবে কি না। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পা ব্যথা হওয়ার জোগাড়। যারা দোভাষী হিসেবে সাহায্য করেছে, দেখলাম, তারা তাড়াতাড়ি বের হয়ে গেছে। তাই আমিও এবার সুযোগটা নিই। একজনকে সাহায্য করলাম। তাকে ইউকেতে কে থাকে, কোথায় থাকবে, কী জন্য এসেছে ইত্যাদি কয়েকটা প্রশ্ন করেই ছেড়ে দেয়। এবার আমার পালা। ব্রিটিশদের একটা খুব ভালো দিক আছে। কাউকে সামান্য সাহায্য করলে, ফুটপাতে হাঁটার সময় একটু রাস্তা ছেড়ে দিলে, কোনো লাইনে আগে যেতে দিলে ধন্যবাদ দিতে দিতে মুখে ফেনা তুলে ফেলে। আগের যাত্রীকে সাহায্য করেছি—এ জন্যই হয়তো ইমিগ্রেশন কাউন্টারে বসা প্রায় পঞ্চাশোর্ধ্ব স্থূলকায় শ্বেতাঙ্গ অফিসার আমার পাসপোর্ট হাতে নিয়ে কেবল একটা প্রশ্নই করেন, ‘কোন বিষয়ে পড়তে এসেছ?’ উত্তর দেওয়ার আগেই সিল মেরে পাসপোর্ট ফেরত দিতে দিতে হাস্যোজ্জ্বল ভঙ্গিতে তিনি বলেন, ‘ওয়েলকাম টু ইউনাইটেড কিংডম মাই বয়।’ অপ্রত্যাশিত এমন উষ্ণ অভ্যর্থনায় দীর্ঘ ভ্রমণক্লান্তি নিমেষে উবে গেল।
 ইমিগ্রেশন শেষ করে লাগেজসহ গেট পেরোতেই বন্ধু জগদীশের দেখা পাই। বেচারা তিন-চার ঘণ্টা ধরে অপেক্ষায় আছে। লন্ডনের বিখ্যাত টিউবে চড়ার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। টিউব অনেকটা মেট্রোরেলের মতো—পার্থক্য হলো টিউব মাটির নিচ দিয়ে চলে। হিথরো থেকে বন্ধুর বাসা পূর্ব লন্ডনের ফরেস্ট গেটে আসতে আসতে রাত ১২টা পার হয়ে যায়। মজার ব্যাপার হলো, টিউবে সেই মধ্যরাতেও দেখলাম মেয়েরা নির্বিঘ্নে চলাফেরা করছে। কোথাও কোনো ভয়-শঙ্কার লেশমাত্র নেই। এ ছাড়া লন্ডনে নেমেই একবারের দর্শনে যে বিষয়টা দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়, তা হলো টিউবের কামরায় দেখা জাতিগত বৈচিত্র্যের সমাহার। ধরা যাক, একেকটা কামরায় ১০ জন যাত্রী—তাদের আটজনই দেখা যাবে ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রতিনিধিত্ব করছে। কী চুলের বাহার, কী বেশভূষা, গাত্রবর্ণ বা ভাষা ইত্যাদি সব মিলিয়ে মনে হবে একটি আন্তর্জাতিক কামরায় বসে আছি। লন্ডনে এই বিষয় বেশ উপভোগ্য লেগেছে—এই শহরে নিজেকে সংখ্যালঘু বা আগন্তুক মনে হয় না; ফলে হীনম্মন্যতা আসে না; যেমনটা ইংল্যান্ডের অন্য শহরগুলোতে কিছুটা অনুভব হয়। শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ বা এশীয়দের সমান পদচারণে মুখর এখানকার পাবলিক পরিবহন। চলার পথে কেউ বই পড়ছে, কেউ মোবাইলে গেমস খেলছে, কেউ হেডফোনে গান শুনছে—যে যার জগতে আত্মমগ্ন, কর্মক্লান্ত কেউবা বাসায় ফেরার আগে একটু ঝিম মেরে ঘুমিয়ে নিচ্ছে—গন্তব্যস্থলে পৌঁছামাত্র টুপ করে নেমে পড়ছে। আবার কোনো স্টেশন থেকে এক জোড়া কপোত-কপোতী উঠে সিট না পেয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গনরত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে জীবনের প্রতিটা মুহূর্তকে উপভোগ করে নিচ্ছে। কারও প্রতি কারও কোনো বিকার-অনুযোগ নেই।
ইমিগ্রেশন শেষ করে লাগেজসহ গেট পেরোতেই বন্ধু জগদীশের দেখা পাই। বেচারা তিন-চার ঘণ্টা ধরে অপেক্ষায় আছে। লন্ডনের বিখ্যাত টিউবে চড়ার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। টিউব অনেকটা মেট্রোরেলের মতো—পার্থক্য হলো টিউব মাটির নিচ দিয়ে চলে। হিথরো থেকে বন্ধুর বাসা পূর্ব লন্ডনের ফরেস্ট গেটে আসতে আসতে রাত ১২টা পার হয়ে যায়। মজার ব্যাপার হলো, টিউবে সেই মধ্যরাতেও দেখলাম মেয়েরা নির্বিঘ্নে চলাফেরা করছে। কোথাও কোনো ভয়-শঙ্কার লেশমাত্র নেই। এ ছাড়া লন্ডনে নেমেই একবারের দর্শনে যে বিষয়টা দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়, তা হলো টিউবের কামরায় দেখা জাতিগত বৈচিত্র্যের সমাহার। ধরা যাক, একেকটা কামরায় ১০ জন যাত্রী—তাদের আটজনই দেখা যাবে ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রতিনিধিত্ব করছে। কী চুলের বাহার, কী বেশভূষা, গাত্রবর্ণ বা ভাষা ইত্যাদি সব মিলিয়ে মনে হবে একটি আন্তর্জাতিক কামরায় বসে আছি। লন্ডনে এই বিষয় বেশ উপভোগ্য লেগেছে—এই শহরে নিজেকে সংখ্যালঘু বা আগন্তুক মনে হয় না; ফলে হীনম্মন্যতা আসে না; যেমনটা ইংল্যান্ডের অন্য শহরগুলোতে কিছুটা অনুভব হয়। শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ বা এশীয়দের সমান পদচারণে মুখর এখানকার পাবলিক পরিবহন। চলার পথে কেউ বই পড়ছে, কেউ মোবাইলে গেমস খেলছে, কেউ হেডফোনে গান শুনছে—যে যার জগতে আত্মমগ্ন, কর্মক্লান্ত কেউবা বাসায় ফেরার আগে একটু ঝিম মেরে ঘুমিয়ে নিচ্ছে—গন্তব্যস্থলে পৌঁছামাত্র টুপ করে নেমে পড়ছে। আবার কোনো স্টেশন থেকে এক জোড়া কপোত-কপোতী উঠে সিট না পেয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গনরত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে জীবনের প্রতিটা মুহূর্তকে উপভোগ করে নিচ্ছে। কারও প্রতি কারও কোনো বিকার-অনুযোগ নেই।
 মূল সড়ক থেকে পাতাল স্টেশনে যাওয়ার জন্য বেশ কয়েকবার চলন্ত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে হয়। আমাদের প্রাথমিক গন্তব্য স্ট্র্যাটফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল রেলস্টেশন। সেখান থেকে ট্যাক্সি বা উবার নিয়ে বাসায় যাওয়ার পরিকল্পনা। হিথরো থেকে ফরেস্টগেট যেতে কয়েকবার টিউব পরিবর্তন করতে হয়। এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। কারণ, সরাসরি ট্যাক্সিতে গেলে অনেক ভাড়া। এখানকার টিউব স্টেশন মাটির গভীরে অবস্থিত। টিউবে চড়ার জন্য বেশ কয়েকটা চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয়। আমাদের দেশের শপিং মলের এস্কেলেটরের চেয়ে প্রায় ১০ গুণ দৈর্ঘ্যের হবে এসব চলন্ত সিঁড়ি। লন্ডনের পাতাল রেললাইন-টিউব ব্যবস্থা এক এলাহি কারবার। এগুলো দেখলে যে কারও মনে হবে মাটির নিচে আরেক লন্ডন শহর অবস্থিত। আক্ষরিক অর্থেই, মাটির ওপরে ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে বা ফুটপাতে হাঁটতে গিয়ে মাটির নিচে টিউব-ট্রেন চলার কম্পন অনুভূত হয়। যদিও এগুলো মাটির নিচে প্রায় ২০-৩০ তলা বিল্ডিংয়ের সমান গভীরে অবস্থিত। দিন নেই, রাত নেই—মাটির ওপরে ও নিচে বিরামহীনভাবে চলে লন্ডনের পাবলিক পরিবহন।
মূল সড়ক থেকে পাতাল স্টেশনে যাওয়ার জন্য বেশ কয়েকবার চলন্ত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে হয়। আমাদের প্রাথমিক গন্তব্য স্ট্র্যাটফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল রেলস্টেশন। সেখান থেকে ট্যাক্সি বা উবার নিয়ে বাসায় যাওয়ার পরিকল্পনা। হিথরো থেকে ফরেস্টগেট যেতে কয়েকবার টিউব পরিবর্তন করতে হয়। এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। কারণ, সরাসরি ট্যাক্সিতে গেলে অনেক ভাড়া। এখানকার টিউব স্টেশন মাটির গভীরে অবস্থিত। টিউবে চড়ার জন্য বেশ কয়েকটা চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয়। আমাদের দেশের শপিং মলের এস্কেলেটরের চেয়ে প্রায় ১০ গুণ দৈর্ঘ্যের হবে এসব চলন্ত সিঁড়ি। লন্ডনের পাতাল রেললাইন-টিউব ব্যবস্থা এক এলাহি কারবার। এগুলো দেখলে যে কারও মনে হবে মাটির নিচে আরেক লন্ডন শহর অবস্থিত। আক্ষরিক অর্থেই, মাটির ওপরে ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে বা ফুটপাতে হাঁটতে গিয়ে মাটির নিচে টিউব-ট্রেন চলার কম্পন অনুভূত হয়। যদিও এগুলো মাটির নিচে প্রায় ২০-৩০ তলা বিল্ডিংয়ের সমান গভীরে অবস্থিত। দিন নেই, রাত নেই—মাটির ওপরে ও নিচে বিরামহীনভাবে চলে লন্ডনের পাবলিক পরিবহন।
রাতে বন্ধুর বাসায় আতিথেয়তা গ্রহণ করে পরদিন রওনা দিই নিজ গন্তব্য শহর—ক্যান্টাবরিতে। ক্যান্টাবরি সাহিত্যের ছাত্রদের কাছে এক অবিস্মরণীয় নাম। ইংরেজি সাহিত্যের জনক জিওফ্রে চসারের ‘ক্যান্টাবরি টেলস’-এর সেই ক্যান্টাবরি শহরে কাটে আমার ১১ মাস। এই শহরের আনাচকানাচে ছড়িয়ে আছে ইংল্যান্ডের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির হাজার বছরের ইতিহাস।
ক্যান্টাবরিকে বলা হয় ‘লন্ডন বিফোর লন্ডন’। রাজধানী লন্ডন গড়ে ওঠার আগে ইংল্যান্ডের লন্ডন ছিল এই শহর। এই গল্প হবে পরের পর্বে।
(চলবে)

বুড়িগঙ্গার পাড় থেকে টেমসের তীরে আসার প্রায় এক বছর হয়ে এল। গত বছর অক্টোবরে সূর্যালোক উদ্ভাসিত প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর এক দেশ ছেড়ে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পাড়ে হাড়কাঁপানো ধূসর ভূমিতে পদার্পণ করি। আমার আগমনের সময়টায় বিলাতে শীত আসি-আসি করছে—জাঁকিয়ে বসেনি। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা আগেই বলেছিলেন, ইউরোপের শীত কোনো ছেলেখেলা নয়। গরমের দেশ থেকে গিয়ে শীত নিয়ে সামান্য হেলাফেলা করলেই সর্দি-কাশি আর জ্বরে জীবন জেরবার করে দেবে। কনকনে মাঘের ঠান্ডার চেয়েও অধিক হাড়কাঁপানো শুধু নয়, হাড় ফুটা করা শীত এখানে বিরাজ করে। কয়েক পরতের গরম কাপড়েও এই কনকনে ঠান্ডা নিবারণ সম্ভব হয় না। লন্ডনে যেদিন আসি, এয়ারপোর্ট থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডা একটা হালকা ঝাপটা এসে লাগে নাকে-মুখে। আগেভাগে প্রস্তুতির কয়েক প্রস্থ কাপড়ে অবগুণ্ঠিত শরীর টের না পেলেও ঠান্ডার দাপটের ঈষৎ বিজ্ঞাপন নাকের ডগা ছুঁয়ে ঝাঁজের আঁচ দিয়েছিল বৈকি!
আমার ইংল্যান্ডে আসার কারণ, দ্বিতীয় মাস্টার্স করা—একটা ডিগ্রি অর্জনের চেয়ে ইংরেজি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে কিছুটা ঘনিষ্ঠভাবে অবলোকন-পর্যবেক্ষণ করা। সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে—প্রায় দুই শ বছর যারা শাসন করল, যাদের সাংস্কৃতিক প্রভাববলয় কলোনিয়াল দেশগুলোতে এখনো বিরাজমান, তাদের যাপিত জীবনপদ্ধতি ও সমাজকে কাছ থেকে দেখার আগ্রহই আমাকে এখানে নিয়ে আসে।
বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটে লন্ডনের হিথরো এয়ারপোর্টে নামি রাত ১০টার দিকে। ইমিগ্রেশন, লাগেজ বেল্ট থেকে ব্যাগপত্র নিয়ে বের হতে হতে সাড়ে ১১টা। বাইরে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল বন্ধু ও সহকর্মী কিংস কলেজে পিএইচডি ফেলো জগদীশ। হিথরো ইমিগ্রেশনে লম্বা লাইন, ফ্লাইট সরাসরি বিমান বাংলাদেশের হওয়ায় লাইনে সবাই বাংলাদেশি নাগরিকই ছিলেন। নানা পেশার বিভিন্ন বয়সী নারী-পুরুষ লম্বা লাইন দাঁড়িয়ে। ইমিগ্রেশনের কাউন্টার অনেক; মাথার ওপরে বড় করে সাইনবোর্ডে স্থানে স্থানে লেখা ‘ইউকে বর্ডার’। লাইনে দাঁড়িয়ে লেখাটায় চোখ পড়তেই মনে হলো নতুন কোনো দেশে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। বাংলাদেশ থেকে উড়াল দেওয়ার আগ পর্যন্ত এমন মনে হয়নি।
লন্ডনে ইমিগ্রেশন অফিসাররা ভিসা-পাসপোর্ট চেক করার সময় যাত্রীদের অনেক ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। এতে এয়ারপোর্ট থেকে বের হতে বেশ সময় লেগে যায়। ইমিগ্রেশনের জেরায় আমার মতো পড়তে আসা শিক্ষার্থী ছাড়াও প্রথমবার যারা ব্রিটেনে এসেছে, সবাইকেই দেখলাম কমবেশি উদ্বিগ্ন হতে। এর পেছনে কারণও আছে বৈকি! কারও প্রশ্নের উত্তর মনঃপূত না হলে তাকে আলাদা করে অন্য একটি রুমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কালো উর্দির ওপর পুলিশ লেখা ব্যক্তিরা যখন কাউকে আলাদা করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায়, তখন পেছনে লাইনে দাঁড়ানো যাত্রীদের মানসিক অবস্থা কেমন হয়, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ইউএসএ, ইউকের ইমিগ্রেশনের কড়াকড়ি নিয়ে নতুন কিছু বলার নেই আসলে। তবে আমার কাছে যত দূর মনে হয়েছে, ভাষা সমস্যাই ইমিগ্রেশনে ভোগান্তির অন্যতম কারণ। অনেককে দেখলাম দোভাষীর আশ্রয় নিতে। লাইনে দাঁড়ানো ব্যক্তিদের মধ্য থেকেই কেউ দোভাষী হিসেবে সাহায্য করবে কি না, জিজ্ঞেস করা হয়। ইমিগ্রেশন অফিসারদের নিজস্ব ব্রিটিশ উচ্চারণে বলা প্রশ্ন অনেকের পক্ষেই বোঝা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বুঝে বা না বুঝে ‘ইয়েস’, ‘নো’-এর মতো উত্তর দিয়ে কোনোমতে ইমিগ্রেশন পার হওয়ার চিন্তা করতে গিয়েই অনেকে ঝামেলা বাড়ায়। এরা সঠিক উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত পাসপোর্টে ছাড়পত্রের সিল দেবেই না। আমার সামনে তখন ৮-১০ জন। এমন সময় জিজ্ঞেস করা হয়, কেউ দোভাষী হবে কি না। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পা ব্যথা হওয়ার জোগাড়। যারা দোভাষী হিসেবে সাহায্য করেছে, দেখলাম, তারা তাড়াতাড়ি বের হয়ে গেছে। তাই আমিও এবার সুযোগটা নিই। একজনকে সাহায্য করলাম। তাকে ইউকেতে কে থাকে, কোথায় থাকবে, কী জন্য এসেছে ইত্যাদি কয়েকটা প্রশ্ন করেই ছেড়ে দেয়। এবার আমার পালা। ব্রিটিশদের একটা খুব ভালো দিক আছে। কাউকে সামান্য সাহায্য করলে, ফুটপাতে হাঁটার সময় একটু রাস্তা ছেড়ে দিলে, কোনো লাইনে আগে যেতে দিলে ধন্যবাদ দিতে দিতে মুখে ফেনা তুলে ফেলে। আগের যাত্রীকে সাহায্য করেছি—এ জন্যই হয়তো ইমিগ্রেশন কাউন্টারে বসা প্রায় পঞ্চাশোর্ধ্ব স্থূলকায় শ্বেতাঙ্গ অফিসার আমার পাসপোর্ট হাতে নিয়ে কেবল একটা প্রশ্নই করেন, ‘কোন বিষয়ে পড়তে এসেছ?’ উত্তর দেওয়ার আগেই সিল মেরে পাসপোর্ট ফেরত দিতে দিতে হাস্যোজ্জ্বল ভঙ্গিতে তিনি বলেন, ‘ওয়েলকাম টু ইউনাইটেড কিংডম মাই বয়।’ অপ্রত্যাশিত এমন উষ্ণ অভ্যর্থনায় দীর্ঘ ভ্রমণক্লান্তি নিমেষে উবে গেল।
 ইমিগ্রেশন শেষ করে লাগেজসহ গেট পেরোতেই বন্ধু জগদীশের দেখা পাই। বেচারা তিন-চার ঘণ্টা ধরে অপেক্ষায় আছে। লন্ডনের বিখ্যাত টিউবে চড়ার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। টিউব অনেকটা মেট্রোরেলের মতো—পার্থক্য হলো টিউব মাটির নিচ দিয়ে চলে। হিথরো থেকে বন্ধুর বাসা পূর্ব লন্ডনের ফরেস্ট গেটে আসতে আসতে রাত ১২টা পার হয়ে যায়। মজার ব্যাপার হলো, টিউবে সেই মধ্যরাতেও দেখলাম মেয়েরা নির্বিঘ্নে চলাফেরা করছে। কোথাও কোনো ভয়-শঙ্কার লেশমাত্র নেই। এ ছাড়া লন্ডনে নেমেই একবারের দর্শনে যে বিষয়টা দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়, তা হলো টিউবের কামরায় দেখা জাতিগত বৈচিত্র্যের সমাহার। ধরা যাক, একেকটা কামরায় ১০ জন যাত্রী—তাদের আটজনই দেখা যাবে ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রতিনিধিত্ব করছে। কী চুলের বাহার, কী বেশভূষা, গাত্রবর্ণ বা ভাষা ইত্যাদি সব মিলিয়ে মনে হবে একটি আন্তর্জাতিক কামরায় বসে আছি। লন্ডনে এই বিষয় বেশ উপভোগ্য লেগেছে—এই শহরে নিজেকে সংখ্যালঘু বা আগন্তুক মনে হয় না; ফলে হীনম্মন্যতা আসে না; যেমনটা ইংল্যান্ডের অন্য শহরগুলোতে কিছুটা অনুভব হয়। শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ বা এশীয়দের সমান পদচারণে মুখর এখানকার পাবলিক পরিবহন। চলার পথে কেউ বই পড়ছে, কেউ মোবাইলে গেমস খেলছে, কেউ হেডফোনে গান শুনছে—যে যার জগতে আত্মমগ্ন, কর্মক্লান্ত কেউবা বাসায় ফেরার আগে একটু ঝিম মেরে ঘুমিয়ে নিচ্ছে—গন্তব্যস্থলে পৌঁছামাত্র টুপ করে নেমে পড়ছে। আবার কোনো স্টেশন থেকে এক জোড়া কপোত-কপোতী উঠে সিট না পেয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গনরত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে জীবনের প্রতিটা মুহূর্তকে উপভোগ করে নিচ্ছে। কারও প্রতি কারও কোনো বিকার-অনুযোগ নেই।
ইমিগ্রেশন শেষ করে লাগেজসহ গেট পেরোতেই বন্ধু জগদীশের দেখা পাই। বেচারা তিন-চার ঘণ্টা ধরে অপেক্ষায় আছে। লন্ডনের বিখ্যাত টিউবে চড়ার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। টিউব অনেকটা মেট্রোরেলের মতো—পার্থক্য হলো টিউব মাটির নিচ দিয়ে চলে। হিথরো থেকে বন্ধুর বাসা পূর্ব লন্ডনের ফরেস্ট গেটে আসতে আসতে রাত ১২টা পার হয়ে যায়। মজার ব্যাপার হলো, টিউবে সেই মধ্যরাতেও দেখলাম মেয়েরা নির্বিঘ্নে চলাফেরা করছে। কোথাও কোনো ভয়-শঙ্কার লেশমাত্র নেই। এ ছাড়া লন্ডনে নেমেই একবারের দর্শনে যে বিষয়টা দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়, তা হলো টিউবের কামরায় দেখা জাতিগত বৈচিত্র্যের সমাহার। ধরা যাক, একেকটা কামরায় ১০ জন যাত্রী—তাদের আটজনই দেখা যাবে ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রতিনিধিত্ব করছে। কী চুলের বাহার, কী বেশভূষা, গাত্রবর্ণ বা ভাষা ইত্যাদি সব মিলিয়ে মনে হবে একটি আন্তর্জাতিক কামরায় বসে আছি। লন্ডনে এই বিষয় বেশ উপভোগ্য লেগেছে—এই শহরে নিজেকে সংখ্যালঘু বা আগন্তুক মনে হয় না; ফলে হীনম্মন্যতা আসে না; যেমনটা ইংল্যান্ডের অন্য শহরগুলোতে কিছুটা অনুভব হয়। শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ বা এশীয়দের সমান পদচারণে মুখর এখানকার পাবলিক পরিবহন। চলার পথে কেউ বই পড়ছে, কেউ মোবাইলে গেমস খেলছে, কেউ হেডফোনে গান শুনছে—যে যার জগতে আত্মমগ্ন, কর্মক্লান্ত কেউবা বাসায় ফেরার আগে একটু ঝিম মেরে ঘুমিয়ে নিচ্ছে—গন্তব্যস্থলে পৌঁছামাত্র টুপ করে নেমে পড়ছে। আবার কোনো স্টেশন থেকে এক জোড়া কপোত-কপোতী উঠে সিট না পেয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গনরত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে জীবনের প্রতিটা মুহূর্তকে উপভোগ করে নিচ্ছে। কারও প্রতি কারও কোনো বিকার-অনুযোগ নেই।
 মূল সড়ক থেকে পাতাল স্টেশনে যাওয়ার জন্য বেশ কয়েকবার চলন্ত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে হয়। আমাদের প্রাথমিক গন্তব্য স্ট্র্যাটফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল রেলস্টেশন। সেখান থেকে ট্যাক্সি বা উবার নিয়ে বাসায় যাওয়ার পরিকল্পনা। হিথরো থেকে ফরেস্টগেট যেতে কয়েকবার টিউব পরিবর্তন করতে হয়। এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। কারণ, সরাসরি ট্যাক্সিতে গেলে অনেক ভাড়া। এখানকার টিউব স্টেশন মাটির গভীরে অবস্থিত। টিউবে চড়ার জন্য বেশ কয়েকটা চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয়। আমাদের দেশের শপিং মলের এস্কেলেটরের চেয়ে প্রায় ১০ গুণ দৈর্ঘ্যের হবে এসব চলন্ত সিঁড়ি। লন্ডনের পাতাল রেললাইন-টিউব ব্যবস্থা এক এলাহি কারবার। এগুলো দেখলে যে কারও মনে হবে মাটির নিচে আরেক লন্ডন শহর অবস্থিত। আক্ষরিক অর্থেই, মাটির ওপরে ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে বা ফুটপাতে হাঁটতে গিয়ে মাটির নিচে টিউব-ট্রেন চলার কম্পন অনুভূত হয়। যদিও এগুলো মাটির নিচে প্রায় ২০-৩০ তলা বিল্ডিংয়ের সমান গভীরে অবস্থিত। দিন নেই, রাত নেই—মাটির ওপরে ও নিচে বিরামহীনভাবে চলে লন্ডনের পাবলিক পরিবহন।
মূল সড়ক থেকে পাতাল স্টেশনে যাওয়ার জন্য বেশ কয়েকবার চলন্ত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে হয়। আমাদের প্রাথমিক গন্তব্য স্ট্র্যাটফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল রেলস্টেশন। সেখান থেকে ট্যাক্সি বা উবার নিয়ে বাসায় যাওয়ার পরিকল্পনা। হিথরো থেকে ফরেস্টগেট যেতে কয়েকবার টিউব পরিবর্তন করতে হয়। এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। কারণ, সরাসরি ট্যাক্সিতে গেলে অনেক ভাড়া। এখানকার টিউব স্টেশন মাটির গভীরে অবস্থিত। টিউবে চড়ার জন্য বেশ কয়েকটা চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয়। আমাদের দেশের শপিং মলের এস্কেলেটরের চেয়ে প্রায় ১০ গুণ দৈর্ঘ্যের হবে এসব চলন্ত সিঁড়ি। লন্ডনের পাতাল রেললাইন-টিউব ব্যবস্থা এক এলাহি কারবার। এগুলো দেখলে যে কারও মনে হবে মাটির নিচে আরেক লন্ডন শহর অবস্থিত। আক্ষরিক অর্থেই, মাটির ওপরে ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে বা ফুটপাতে হাঁটতে গিয়ে মাটির নিচে টিউব-ট্রেন চলার কম্পন অনুভূত হয়। যদিও এগুলো মাটির নিচে প্রায় ২০-৩০ তলা বিল্ডিংয়ের সমান গভীরে অবস্থিত। দিন নেই, রাত নেই—মাটির ওপরে ও নিচে বিরামহীনভাবে চলে লন্ডনের পাবলিক পরিবহন।
রাতে বন্ধুর বাসায় আতিথেয়তা গ্রহণ করে পরদিন রওনা দিই নিজ গন্তব্য শহর—ক্যান্টাবরিতে। ক্যান্টাবরি সাহিত্যের ছাত্রদের কাছে এক অবিস্মরণীয় নাম। ইংরেজি সাহিত্যের জনক জিওফ্রে চসারের ‘ক্যান্টাবরি টেলস’-এর সেই ক্যান্টাবরি শহরে কাটে আমার ১১ মাস। এই শহরের আনাচকানাচে ছড়িয়ে আছে ইংল্যান্ডের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির হাজার বছরের ইতিহাস।
ক্যান্টাবরিকে বলা হয় ‘লন্ডন বিফোর লন্ডন’। রাজধানী লন্ডন গড়ে ওঠার আগে ইংল্যান্ডের লন্ডন ছিল এই শহর। এই গল্প হবে পরের পর্বে।
(চলবে)

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল।
১ দিন আগে
জনপ্রিয় কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা রকিব হাসান মারা গেছেন। আজ বুধবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস চলাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।
৬ দিন আগে
হাঙ্গেরির ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই এবার (২০২৫ সালে) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তাঁর দীর্ঘ, দার্শনিক বাক্য ও মানবজীবনের বিশৃঙ্খলার গভীর অনুসন্ধানী সাহিত্যকর্মের জন্য। সুইডিশ একাডেমি তাঁকে সম্মান জানিয়েছে ‘শিল্পের শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার’ জন্য।
১২ দিন আগে
হাঙ্গেরির সাহিত্যে অসীম জনপ্রিয়তা ও প্রভাব তাঁর; বিশ্বজোড়া আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের দাপটেও শিল্পের শক্তি চেনায় তাঁর কলম। তিনি হাঙ্গেরিয়ান ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই; সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৫ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।
১২ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল। কিন্তু ভাষাবিদ ও সাহিত্য ইতিহাসবিদদের মতে, এই ধারণা আসলে পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ থেকে তৈরি এক ‘ঔপনিবেশিক কল্পনা’ মাত্র। বাস্তবে আরবি সাহিত্য কখনোই থেমে যায়নি।
প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, অষ্টম শতাব্দীতে আব্বাসীয় খলিফাদের অধীনে বিজ্ঞান, দর্শন ও কবিতার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল বাগদাদ। আবু নুয়াস, আল-মুতানাব্বি, আল-ফারাবি ও ইবনে সিনার মতো কবি ও দার্শনিকদের হাত ধরে শুরু হয়েছিল এক স্বর্ণযুগ। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় গবেষকেরা—যেমন ফরাসি চিন্তাবিদ আর্নেস্ট রেনাঁ ও ডাচ ইতিহাসবিদ রেইনহার্ট দোজি সেই আমলটিকেই আরবি বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের শিখর বলে স্বীকার করেছিলেন এবং দাবি করেছিলেন, একাদশ শতাব্দীর পর এই ধারাবাহিকতার পতন ঘটে। তাঁদের মতে, এরপর প্রায় ৮০০ বছর আরবে আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক বা দার্শনিক কাজ হয়নি—যতক্ষণ না ইউরোপে রেনেসাঁ শুরু হয়।
কিন্তু আধুনিক গবেষকেরা বলছেন, এই ধারণা সরলীকৃত ও পক্ষপাতদুষ্ট। ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বইমেলায় শেখ জায়েদ বুক অ্যাওয়ার্ডের আয়োজিত এক আলোচনায় ভাষাবিদেরা দাবি করেছেন, আরবি রচনা শৈলী কখনো বিলুপ্ত হয়নি; বরং তা ধারাবাহিকভাবে কপি, অনুবাদ ও পাঠের মাধ্যমে বেঁচে ছিল।
জার্মান গবেষক বেয়াট্রিস গ্রুন্ডলার তাঁর ‘দ্য রাইজ অব দ্য অ্যারাবিক বুক’ গ্রন্থে দাবি করেছেন, আরবি সাহিত্যে ‘হারানো শতাব্দী’ হিসেবে যে ধারণাটি প্রচলিত আছে তা আসলে গাল-গল্প। এই বইটি এবারের শেখ জায়েদ পুরস্কারের শর্টলিস্টে রয়েছে। গ্রুন্ডলার এতে দেখিয়েছেন, নবম শতাব্দীর বাগদাদে বইয়ের ব্যবসা, কপিকারদের প্রতিযোগিতা, জনসম্মুখে পাঠ ও লেখার প্রচলন—সবই ছিল আধুনিক প্রকাশনা সংস্কৃতির পূর্বসূরি। তিনি মত দিয়েছেন, ‘বাগদাদের রাস্তায় হাঁটলে আপনি দেখতেন লোকেরা হস্তলিপি বিক্রি করছে, বিরামচিহ্ন নিয়ে তর্ক করছে—এ যেন এক জীবন্ত প্রকাশনা বাজার।’
গবেষণা বলছে, আরবি সাহিত্য আসলে কখনো এক জায়গায় স্থির থাকেনি। এর কেন্দ্র এক সময় বাগদাদ থেকে কায়রো, দামেস্ক ও আন্দালুসিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু ধারাটি অব্যাহতই থাকে। নতুন ঘরানা তৈরি হয়, পুরোনো ঘরানা রূপান্তরিত হয়।
ফরাসি অধ্যাপক হাকান ওজকান তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, ‘জাজাল’ নামের কথ্য ছন্দভিত্তিক কবিতার ধারা আব্বাসীয় যুগের পরও বিকশিত হতে থাকে। তাঁর মতে, ‘এই কবিরা নিয়ম ভেঙে নতুন রূপ দিয়েছে—তাঁদের ছন্দ ও ব্যঙ্গ আধুনিক র্যাপের মতো প্রাণবন্ত।’
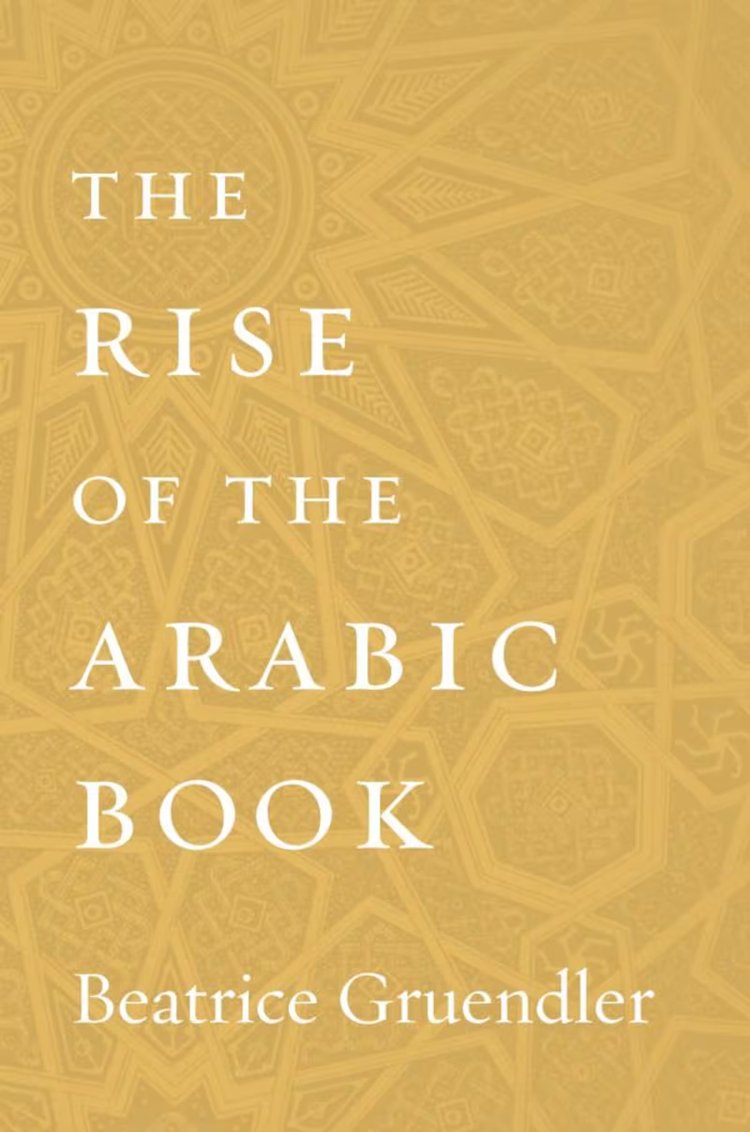
এদিকে এই বিষয়ে এক প্রতিবেদনে সোমবার (২০ অক্টোবর) আমিরাতভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য ন্যাশনাল জানিয়েছে, আবুধাবির নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির ‘আরবি সাহিত্য লাইব্রেরি’ প্রকল্প ইতিমধ্যেই ‘হারানো শতাব্দী’ বলে বিবেচিত সময়ের ৬০ টিরও বেশি আরবি সাহিত্যকর্ম পুনরুদ্ধার করেছে। প্রকল্পটির সম্পাদক অধ্যাপক মরিস পোমেরান্টজ বলেছেন, ‘এই বইগুলো সম্পাদনা করা মানে এক চলমান সংলাপে অংশ নেওয়া—যেখানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম লেখক, অনুবাদক ও সমালোচকেরা একে অপরকে উত্তর দিয়ে গেছেন।’
মরিস মনে করেন, আরবি সাহিত্য স্থবির হয়ে যাওয়ার ধারণাটি মূলত অনুবাদের অভাব থেকেই জন্ম নিয়েছে। তিনি বলেন, ‘যখন কোনো লেখা অনুবাদ করা হয় না, তখন সেটি বৈশ্বিক অস্তিত্ব হারায়।’
মরিসের মতে, এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো এই সাহিত্যকে আবার জনসাধারণের কল্পনায় ফিরিয়ে আনা—স্কুলে পড়ানো, মঞ্চে উপস্থাপন করা, অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া। তা না হলে আরবি সাহিত্যের ‘হারানো শতাব্দী’ হিসেবে চিহ্নিত সময়টি অধরাই থেকে যাবে।

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল। কিন্তু ভাষাবিদ ও সাহিত্য ইতিহাসবিদদের মতে, এই ধারণা আসলে পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ থেকে তৈরি এক ‘ঔপনিবেশিক কল্পনা’ মাত্র। বাস্তবে আরবি সাহিত্য কখনোই থেমে যায়নি।
প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, অষ্টম শতাব্দীতে আব্বাসীয় খলিফাদের অধীনে বিজ্ঞান, দর্শন ও কবিতার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল বাগদাদ। আবু নুয়াস, আল-মুতানাব্বি, আল-ফারাবি ও ইবনে সিনার মতো কবি ও দার্শনিকদের হাত ধরে শুরু হয়েছিল এক স্বর্ণযুগ। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় গবেষকেরা—যেমন ফরাসি চিন্তাবিদ আর্নেস্ট রেনাঁ ও ডাচ ইতিহাসবিদ রেইনহার্ট দোজি সেই আমলটিকেই আরবি বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের শিখর বলে স্বীকার করেছিলেন এবং দাবি করেছিলেন, একাদশ শতাব্দীর পর এই ধারাবাহিকতার পতন ঘটে। তাঁদের মতে, এরপর প্রায় ৮০০ বছর আরবে আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক বা দার্শনিক কাজ হয়নি—যতক্ষণ না ইউরোপে রেনেসাঁ শুরু হয়।
কিন্তু আধুনিক গবেষকেরা বলছেন, এই ধারণা সরলীকৃত ও পক্ষপাতদুষ্ট। ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বইমেলায় শেখ জায়েদ বুক অ্যাওয়ার্ডের আয়োজিত এক আলোচনায় ভাষাবিদেরা দাবি করেছেন, আরবি রচনা শৈলী কখনো বিলুপ্ত হয়নি; বরং তা ধারাবাহিকভাবে কপি, অনুবাদ ও পাঠের মাধ্যমে বেঁচে ছিল।
জার্মান গবেষক বেয়াট্রিস গ্রুন্ডলার তাঁর ‘দ্য রাইজ অব দ্য অ্যারাবিক বুক’ গ্রন্থে দাবি করেছেন, আরবি সাহিত্যে ‘হারানো শতাব্দী’ হিসেবে যে ধারণাটি প্রচলিত আছে তা আসলে গাল-গল্প। এই বইটি এবারের শেখ জায়েদ পুরস্কারের শর্টলিস্টে রয়েছে। গ্রুন্ডলার এতে দেখিয়েছেন, নবম শতাব্দীর বাগদাদে বইয়ের ব্যবসা, কপিকারদের প্রতিযোগিতা, জনসম্মুখে পাঠ ও লেখার প্রচলন—সবই ছিল আধুনিক প্রকাশনা সংস্কৃতির পূর্বসূরি। তিনি মত দিয়েছেন, ‘বাগদাদের রাস্তায় হাঁটলে আপনি দেখতেন লোকেরা হস্তলিপি বিক্রি করছে, বিরামচিহ্ন নিয়ে তর্ক করছে—এ যেন এক জীবন্ত প্রকাশনা বাজার।’
গবেষণা বলছে, আরবি সাহিত্য আসলে কখনো এক জায়গায় স্থির থাকেনি। এর কেন্দ্র এক সময় বাগদাদ থেকে কায়রো, দামেস্ক ও আন্দালুসিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু ধারাটি অব্যাহতই থাকে। নতুন ঘরানা তৈরি হয়, পুরোনো ঘরানা রূপান্তরিত হয়।
ফরাসি অধ্যাপক হাকান ওজকান তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, ‘জাজাল’ নামের কথ্য ছন্দভিত্তিক কবিতার ধারা আব্বাসীয় যুগের পরও বিকশিত হতে থাকে। তাঁর মতে, ‘এই কবিরা নিয়ম ভেঙে নতুন রূপ দিয়েছে—তাঁদের ছন্দ ও ব্যঙ্গ আধুনিক র্যাপের মতো প্রাণবন্ত।’
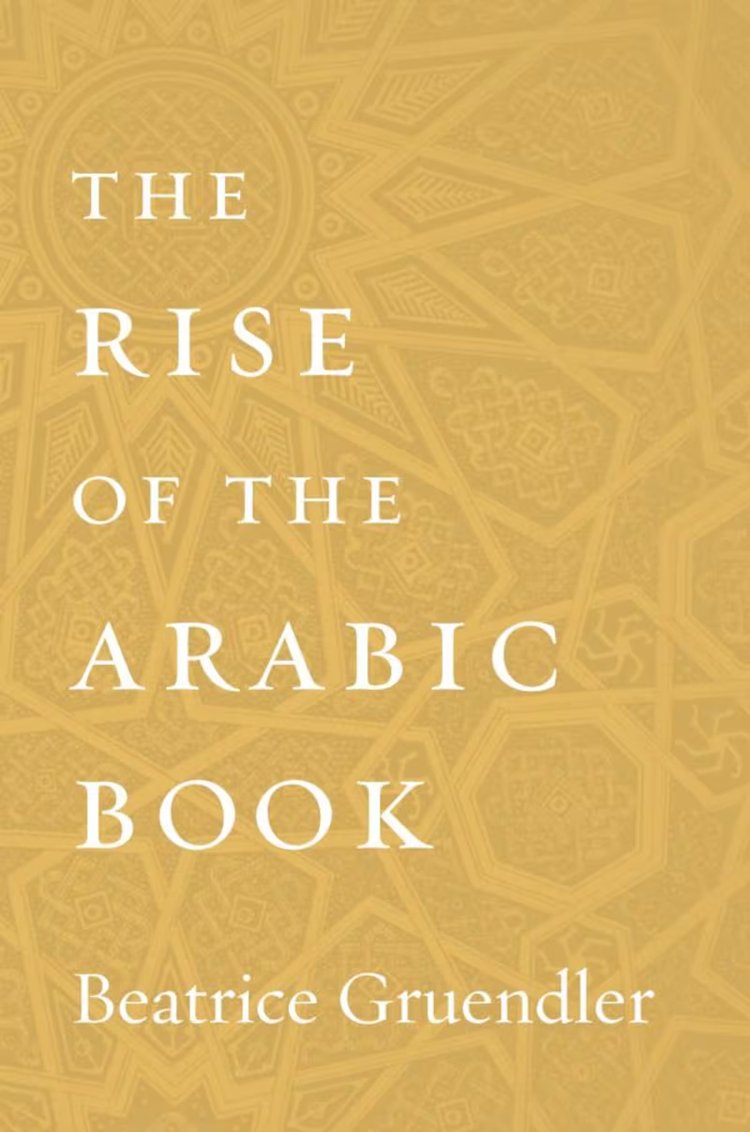
এদিকে এই বিষয়ে এক প্রতিবেদনে সোমবার (২০ অক্টোবর) আমিরাতভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য ন্যাশনাল জানিয়েছে, আবুধাবির নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির ‘আরবি সাহিত্য লাইব্রেরি’ প্রকল্প ইতিমধ্যেই ‘হারানো শতাব্দী’ বলে বিবেচিত সময়ের ৬০ টিরও বেশি আরবি সাহিত্যকর্ম পুনরুদ্ধার করেছে। প্রকল্পটির সম্পাদক অধ্যাপক মরিস পোমেরান্টজ বলেছেন, ‘এই বইগুলো সম্পাদনা করা মানে এক চলমান সংলাপে অংশ নেওয়া—যেখানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম লেখক, অনুবাদক ও সমালোচকেরা একে অপরকে উত্তর দিয়ে গেছেন।’
মরিস মনে করেন, আরবি সাহিত্য স্থবির হয়ে যাওয়ার ধারণাটি মূলত অনুবাদের অভাব থেকেই জন্ম নিয়েছে। তিনি বলেন, ‘যখন কোনো লেখা অনুবাদ করা হয় না, তখন সেটি বৈশ্বিক অস্তিত্ব হারায়।’
মরিসের মতে, এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো এই সাহিত্যকে আবার জনসাধারণের কল্পনায় ফিরিয়ে আনা—স্কুলে পড়ানো, মঞ্চে উপস্থাপন করা, অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া। তা না হলে আরবি সাহিত্যের ‘হারানো শতাব্দী’ হিসেবে চিহ্নিত সময়টি অধরাই থেকে যাবে।

বুড়িগঙ্গার পাড় থেকে টেমসের তীরে আসার প্রায় এক বছর হয়ে এল। গত বছর অক্টোবরে সূর্যালোক উদ্ভাসিত প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর এক দেশ ছেড়ে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পাড়ে হাড়কাঁপানো ধূসর ভূমিতে পদার্পণ করি। আমার আগমনের সময়টায় বিলাতে শীত আসি-আসি করছে—জাঁকিয়ে বসেনি। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা আগেই বলেছিলেন, ইউরোপের শীত কোনো ছেলেখ
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২২
জনপ্রিয় কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা রকিব হাসান মারা গেছেন। আজ বুধবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস চলাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।
৬ দিন আগে
হাঙ্গেরির ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই এবার (২০২৫ সালে) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তাঁর দীর্ঘ, দার্শনিক বাক্য ও মানবজীবনের বিশৃঙ্খলার গভীর অনুসন্ধানী সাহিত্যকর্মের জন্য। সুইডিশ একাডেমি তাঁকে সম্মান জানিয়েছে ‘শিল্পের শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার’ জন্য।
১২ দিন আগে
হাঙ্গেরির সাহিত্যে অসীম জনপ্রিয়তা ও প্রভাব তাঁর; বিশ্বজোড়া আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের দাপটেও শিল্পের শক্তি চেনায় তাঁর কলম। তিনি হাঙ্গেরিয়ান ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই; সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৫ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।
১২ দিন আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জনপ্রিয় কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা রকিব হাসান মারা গেছেন। আজ বুধবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস চলাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।
রকিব হাসানের মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেছেন সেবা প্রকাশনীর উপদেষ্টা মাসুমা মায়মুর। তিনি সেবা প্রকাশনীর প্রতিষ্ঠাতা কাজী আনোয়ার হোসেনের ছোট ছেলে কাজী মায়মুর হোসেনের স্ত্রী।
মাসুমা মায়মুর ফেসবুকে লিখেছেন, ‘তিন গোয়েন্দা ও সেবা প্রকাশনীর পাঠকদেরকে আন্তরিক দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, কিছুক্ষণ আগে রকিব হাসান সাহেব পরলোক গমন করেছেন। ডায়ালাইসিস চলাকালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ওনার জীবনাবসান ঘটে। আপনারা ওনার পবিত্র আত্মার মাগফেরাত কামনা করুন।’
১৯৫০ সালের ১২ ডিসেম্বর কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন রকিব হাসান। বাবার চাকরির কারণে শৈশব কেটেছে ফেনীতে। সেখান থেকে স্কুলজীবন শেষ করে ভর্তি হন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে। পড়াশোনা শেষে বিভিন্ন চাকরিতে যুক্ত হলেও অফিসের বাঁধাধরা জীবনে তাঁর মন টেকেনি। অবশেষে তিনি লেখালেখিকে বেছে নেন জীবনের একমাত্র পথ হিসেবে।

সেবা প্রকাশনী থেকে তাঁর লেখকজীবনের সূচনা হয়। প্রথমদিকে বিশ্বসেরা ক্ল্যাসিক বই অনুবাদ করে লেখালেখির জগতে প্রবেশ করেন তিনি। এরপর টারজান, গোয়েন্দা রাজু, রেজা-সুজা সিরিজসহ চার শতাধিক জনপ্রিয় বই লেখেন। তবে তাঁর পরিচয়ের সবচেয়ে বড় জায়গা হলো তিন গোয়েন্দা সিরিজ। এই সিরিজ বাংলাদেশের অসংখ্য কিশোর-কিশোরীর কৈশোরের সঙ্গী।
মূলত রবার্ট আর্থারের থ্রি ইনভেস্টিগেটরস সিরিজ অবলম্বনে তিন গোয়েন্দার সূচনা হয়। তবে রকিব হাসানের লেখনশৈলীতে এটি পেয়েছে একেবারে নতুন রূপ। বাংলাদেশি সাহিত্য হয়ে উঠেছে এটি। এই সিরিজের মাধ্যমে তিনি হয়ে ওঠেন হাজারো কিশোর পাঠকের প্রিয় লেখক।
নিজ নামে লেখার পাশাপাশি তিনি ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন ছদ্মনাম। শামসুদ্দীন নওয়াব নামে তিনি অনুবাদ করেছিলেন জুল ভার্নের বইগুলো।
বাংলাদেশের পাঠকদের কাছে রকিব হাসান শুধু একজন গোয়েন্দা লেখক নন, তিনি কয়েক প্রজন্মের শৈশব-কৈশোরের ভালোবাসার মানুষ।

জনপ্রিয় কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা রকিব হাসান মারা গেছেন। আজ বুধবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস চলাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।
রকিব হাসানের মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেছেন সেবা প্রকাশনীর উপদেষ্টা মাসুমা মায়মুর। তিনি সেবা প্রকাশনীর প্রতিষ্ঠাতা কাজী আনোয়ার হোসেনের ছোট ছেলে কাজী মায়মুর হোসেনের স্ত্রী।
মাসুমা মায়মুর ফেসবুকে লিখেছেন, ‘তিন গোয়েন্দা ও সেবা প্রকাশনীর পাঠকদেরকে আন্তরিক দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, কিছুক্ষণ আগে রকিব হাসান সাহেব পরলোক গমন করেছেন। ডায়ালাইসিস চলাকালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ওনার জীবনাবসান ঘটে। আপনারা ওনার পবিত্র আত্মার মাগফেরাত কামনা করুন।’
১৯৫০ সালের ১২ ডিসেম্বর কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন রকিব হাসান। বাবার চাকরির কারণে শৈশব কেটেছে ফেনীতে। সেখান থেকে স্কুলজীবন শেষ করে ভর্তি হন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে। পড়াশোনা শেষে বিভিন্ন চাকরিতে যুক্ত হলেও অফিসের বাঁধাধরা জীবনে তাঁর মন টেকেনি। অবশেষে তিনি লেখালেখিকে বেছে নেন জীবনের একমাত্র পথ হিসেবে।

সেবা প্রকাশনী থেকে তাঁর লেখকজীবনের সূচনা হয়। প্রথমদিকে বিশ্বসেরা ক্ল্যাসিক বই অনুবাদ করে লেখালেখির জগতে প্রবেশ করেন তিনি। এরপর টারজান, গোয়েন্দা রাজু, রেজা-সুজা সিরিজসহ চার শতাধিক জনপ্রিয় বই লেখেন। তবে তাঁর পরিচয়ের সবচেয়ে বড় জায়গা হলো তিন গোয়েন্দা সিরিজ। এই সিরিজ বাংলাদেশের অসংখ্য কিশোর-কিশোরীর কৈশোরের সঙ্গী।
মূলত রবার্ট আর্থারের থ্রি ইনভেস্টিগেটরস সিরিজ অবলম্বনে তিন গোয়েন্দার সূচনা হয়। তবে রকিব হাসানের লেখনশৈলীতে এটি পেয়েছে একেবারে নতুন রূপ। বাংলাদেশি সাহিত্য হয়ে উঠেছে এটি। এই সিরিজের মাধ্যমে তিনি হয়ে ওঠেন হাজারো কিশোর পাঠকের প্রিয় লেখক।
নিজ নামে লেখার পাশাপাশি তিনি ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন ছদ্মনাম। শামসুদ্দীন নওয়াব নামে তিনি অনুবাদ করেছিলেন জুল ভার্নের বইগুলো।
বাংলাদেশের পাঠকদের কাছে রকিব হাসান শুধু একজন গোয়েন্দা লেখক নন, তিনি কয়েক প্রজন্মের শৈশব-কৈশোরের ভালোবাসার মানুষ।

বুড়িগঙ্গার পাড় থেকে টেমসের তীরে আসার প্রায় এক বছর হয়ে এল। গত বছর অক্টোবরে সূর্যালোক উদ্ভাসিত প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর এক দেশ ছেড়ে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পাড়ে হাড়কাঁপানো ধূসর ভূমিতে পদার্পণ করি। আমার আগমনের সময়টায় বিলাতে শীত আসি-আসি করছে—জাঁকিয়ে বসেনি। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা আগেই বলেছিলেন, ইউরোপের শীত কোনো ছেলেখ
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২২
জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল।
১ দিন আগে
হাঙ্গেরির ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই এবার (২০২৫ সালে) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তাঁর দীর্ঘ, দার্শনিক বাক্য ও মানবজীবনের বিশৃঙ্খলার গভীর অনুসন্ধানী সাহিত্যকর্মের জন্য। সুইডিশ একাডেমি তাঁকে সম্মান জানিয়েছে ‘শিল্পের শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার’ জন্য।
১২ দিন আগে
হাঙ্গেরির সাহিত্যে অসীম জনপ্রিয়তা ও প্রভাব তাঁর; বিশ্বজোড়া আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের দাপটেও শিল্পের শক্তি চেনায় তাঁর কলম। তিনি হাঙ্গেরিয়ান ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই; সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৫ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।
১২ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

হাঙ্গেরির ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই এবার (২০২৫ সালে) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তাঁর দীর্ঘ, দার্শনিক বাক্য ও মানবজীবনের বিশৃঙ্খলার গভীর অনুসন্ধানী সাহিত্যকর্মের জন্য। সুইডিশ একাডেমি তাঁকে সম্মান জানিয়েছে ‘শিল্পের শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার’ জন্য। লেখক সুসান সনটাগ অবশ্য তাঁকে একসময় ‘মহাপ্রলয়ের হাঙ্গেরিয়ান গুরু’ আখ্যা দিয়েছিলেন।
সাহিত্যজগতে অনেকের কাছে ক্রাসনাহোরকাইয়ের নোবেল পাওয়ার এই ঘোষণাটি যেন কয়েক দশক ধরে চলা একটি বাক্যের সমাপ্তি।
১৯৫৪ সালে হাঙ্গেরির ছোট শহর জিউলা-তে জন্ম নেওয়া ক্রাসনাহোরকাই ১৯৮০-এর দশকের শুরুতে গল্প লেখা শুরু করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস স্যাটানট্যাঙ্গো (১৯৮৫) একটি বৃষ্টিস্নাত, ধ্বংসপ্রায় গ্রামের কাহিনি—যেখানে প্রতারক, মাতাল ও হতাশ মানুষেরা মিথ্যা আশায় আঁকড়ে থাকে। পরিচালক বেলা-তার তাঁর এই উপন্যাসটিকে দীর্ঘ ৭ ঘণ্টার এক সাদাকালো চলচ্চিত্রে রূপ দেন। এই বইতেই ধরা পড়ে ক্রাসনাহোরকাইয়ের লেখার বৈশিষ্ট্যসমূহ, যেমন—অবিরাম দীর্ঘ বাক্য, দার্শনিক হাস্যরস ও পতনের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের প্রতিচ্ছবি।
তাঁর পরবর্তী উপন্যাসগুলো—দ্য মেলানকোলি অব রেজিস্ট্যান্স (১৯৮৯), ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার (১৯৯৯) ও সেইবো দেয়ার বিলো (২০০৮)—তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিকে মহাজাগতিক পরিসরে বিস্তৃত করেছে। ‘ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার’–এ তিনি এক নথি প্রহরীর গল্প বলেছেন, যিনি রহস্যময় এক পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করতে নিউইয়র্কে পালিয়ে যান এবং আত্মহত্যা করেন—যেন ক্রম বিলীন পৃথিবীতে অর্থ ধরে রাখার এক মরিয়া চেষ্টা তাঁর।
ক্রাসনাহোরকাইয়ের লেখায় কাহিনি প্রায় সময়ই বাক্যের ভেতর হারিয়ে যায়। তিনি লিখেছেন এমন বাক্য, যা একাধিক পৃষ্ঠা জুড়ে পাঠককে টেনে নেয় অবচেতনে, অবিরাম প্রবাহে।
তাঁর সাহিত্যে হাস্যরস ও ট্র্যাজেডি পাশাপাশি চলে। স্যাটানট্যাঙ্গো–এর মাতাল নাচের দৃশ্য যেমন নিঃশেষের প্রতীক, তেমনি ‘ব্যারন ওয়েঙ্কহাইমস হোমকামিং’ (২০১৬)-এ দেখা যায়, ফিরে আসা এক পরাজিত অভিজাতকে। যার মাধ্যমে প্রকাশ পায় সভ্যতার পচন ও মানুষের হাস্যকর ভ্রান্তি।
২০১৫ সালে ম্যান বুকার পুরস্কার পাওয়ার মধ্য দিয়েই প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পান ক্রাসনাহোরকাই। অনুবাদক জর্জ সির্টেস ও ওটিলি মুলজেট তাঁর জটিল হাঙ্গেরিয়ান ভাষাকে ইংরেজিতে রূপ দিতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। ‘হাডসন রিভিউ’ তাঁকে বর্ণনা করেছিল ‘অন্তহীন বাক্যের ভ্রমণশিল্পী’ হিসেবে।
চল্লিশ বছরের সৃষ্টিতে ক্রাসনাহোরকাইয়ের ভুবন চিত্র, সংগীত, দর্শন ও ভাষার মিলনে বিস্তৃত। সাম্প্রতিক উপন্যাস ‘হার্শট ০৭৭৬৯’ (২০২৪)–এ তিনি এক প্রবাহিত বাক্যে লিখেছেন নব্য-নাৎসি, নেকড়ে আর এক হতভাগ্য পদার্থবিদের কাহিনি—আধুনিক ইউরোপের নৈতিক পক্ষাঘাতের রূপক হিসেবে।
তাঁর সমগ্র সাহিত্যজগৎ এক অন্ধকার ও ধ্যানমগ্ন মহাবিশ্ব—যেখানে পতন, শূন্যতা ও করুণা পাশাপাশি থাকে। ‘সেইবো দেয়ার বিলো’ বইটিতে তিনি লিখেছেন, ‘সৌন্দর্য, যত ক্ষণস্থায়ীই হোক না কেন, তা পবিত্রতার প্রতিবিম্ব।’ এই বিশ্বাসই লাসলো ক্রাসনাহোরকাইকে সেই বিরল লেখক করে তুলেছে, যাঁর নৈরাশ্যও মুক্তির মতো দীপ্ত।

হাঙ্গেরির ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই এবার (২০২৫ সালে) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তাঁর দীর্ঘ, দার্শনিক বাক্য ও মানবজীবনের বিশৃঙ্খলার গভীর অনুসন্ধানী সাহিত্যকর্মের জন্য। সুইডিশ একাডেমি তাঁকে সম্মান জানিয়েছে ‘শিল্পের শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার’ জন্য। লেখক সুসান সনটাগ অবশ্য তাঁকে একসময় ‘মহাপ্রলয়ের হাঙ্গেরিয়ান গুরু’ আখ্যা দিয়েছিলেন।
সাহিত্যজগতে অনেকের কাছে ক্রাসনাহোরকাইয়ের নোবেল পাওয়ার এই ঘোষণাটি যেন কয়েক দশক ধরে চলা একটি বাক্যের সমাপ্তি।
১৯৫৪ সালে হাঙ্গেরির ছোট শহর জিউলা-তে জন্ম নেওয়া ক্রাসনাহোরকাই ১৯৮০-এর দশকের শুরুতে গল্প লেখা শুরু করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস স্যাটানট্যাঙ্গো (১৯৮৫) একটি বৃষ্টিস্নাত, ধ্বংসপ্রায় গ্রামের কাহিনি—যেখানে প্রতারক, মাতাল ও হতাশ মানুষেরা মিথ্যা আশায় আঁকড়ে থাকে। পরিচালক বেলা-তার তাঁর এই উপন্যাসটিকে দীর্ঘ ৭ ঘণ্টার এক সাদাকালো চলচ্চিত্রে রূপ দেন। এই বইতেই ধরা পড়ে ক্রাসনাহোরকাইয়ের লেখার বৈশিষ্ট্যসমূহ, যেমন—অবিরাম দীর্ঘ বাক্য, দার্শনিক হাস্যরস ও পতনের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের প্রতিচ্ছবি।
তাঁর পরবর্তী উপন্যাসগুলো—দ্য মেলানকোলি অব রেজিস্ট্যান্স (১৯৮৯), ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার (১৯৯৯) ও সেইবো দেয়ার বিলো (২০০৮)—তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিকে মহাজাগতিক পরিসরে বিস্তৃত করেছে। ‘ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার’–এ তিনি এক নথি প্রহরীর গল্প বলেছেন, যিনি রহস্যময় এক পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করতে নিউইয়র্কে পালিয়ে যান এবং আত্মহত্যা করেন—যেন ক্রম বিলীন পৃথিবীতে অর্থ ধরে রাখার এক মরিয়া চেষ্টা তাঁর।
ক্রাসনাহোরকাইয়ের লেখায় কাহিনি প্রায় সময়ই বাক্যের ভেতর হারিয়ে যায়। তিনি লিখেছেন এমন বাক্য, যা একাধিক পৃষ্ঠা জুড়ে পাঠককে টেনে নেয় অবচেতনে, অবিরাম প্রবাহে।
তাঁর সাহিত্যে হাস্যরস ও ট্র্যাজেডি পাশাপাশি চলে। স্যাটানট্যাঙ্গো–এর মাতাল নাচের দৃশ্য যেমন নিঃশেষের প্রতীক, তেমনি ‘ব্যারন ওয়েঙ্কহাইমস হোমকামিং’ (২০১৬)-এ দেখা যায়, ফিরে আসা এক পরাজিত অভিজাতকে। যার মাধ্যমে প্রকাশ পায় সভ্যতার পচন ও মানুষের হাস্যকর ভ্রান্তি।
২০১৫ সালে ম্যান বুকার পুরস্কার পাওয়ার মধ্য দিয়েই প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পান ক্রাসনাহোরকাই। অনুবাদক জর্জ সির্টেস ও ওটিলি মুলজেট তাঁর জটিল হাঙ্গেরিয়ান ভাষাকে ইংরেজিতে রূপ দিতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। ‘হাডসন রিভিউ’ তাঁকে বর্ণনা করেছিল ‘অন্তহীন বাক্যের ভ্রমণশিল্পী’ হিসেবে।
চল্লিশ বছরের সৃষ্টিতে ক্রাসনাহোরকাইয়ের ভুবন চিত্র, সংগীত, দর্শন ও ভাষার মিলনে বিস্তৃত। সাম্প্রতিক উপন্যাস ‘হার্শট ০৭৭৬৯’ (২০২৪)–এ তিনি এক প্রবাহিত বাক্যে লিখেছেন নব্য-নাৎসি, নেকড়ে আর এক হতভাগ্য পদার্থবিদের কাহিনি—আধুনিক ইউরোপের নৈতিক পক্ষাঘাতের রূপক হিসেবে।
তাঁর সমগ্র সাহিত্যজগৎ এক অন্ধকার ও ধ্যানমগ্ন মহাবিশ্ব—যেখানে পতন, শূন্যতা ও করুণা পাশাপাশি থাকে। ‘সেইবো দেয়ার বিলো’ বইটিতে তিনি লিখেছেন, ‘সৌন্দর্য, যত ক্ষণস্থায়ীই হোক না কেন, তা পবিত্রতার প্রতিবিম্ব।’ এই বিশ্বাসই লাসলো ক্রাসনাহোরকাইকে সেই বিরল লেখক করে তুলেছে, যাঁর নৈরাশ্যও মুক্তির মতো দীপ্ত।

বুড়িগঙ্গার পাড় থেকে টেমসের তীরে আসার প্রায় এক বছর হয়ে এল। গত বছর অক্টোবরে সূর্যালোক উদ্ভাসিত প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর এক দেশ ছেড়ে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পাড়ে হাড়কাঁপানো ধূসর ভূমিতে পদার্পণ করি। আমার আগমনের সময়টায় বিলাতে শীত আসি-আসি করছে—জাঁকিয়ে বসেনি। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা আগেই বলেছিলেন, ইউরোপের শীত কোনো ছেলেখ
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২২
জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল।
১ দিন আগে
জনপ্রিয় কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা রকিব হাসান মারা গেছেন। আজ বুধবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস চলাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।
৬ দিন আগে
হাঙ্গেরির সাহিত্যে অসীম জনপ্রিয়তা ও প্রভাব তাঁর; বিশ্বজোড়া আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের দাপটেও শিল্পের শক্তি চেনায় তাঁর কলম। তিনি হাঙ্গেরিয়ান ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই; সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৫ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।
১২ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

হাঙ্গেরির সাহিত্যে অসীম জনপ্রিয়তা ও প্রভাব তাঁর; বিশ্বজোড়া আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের দাপটেও শিল্পের শক্তি চেনায় তাঁর কলম। তিনি হাঙ্গেরিয়ান ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই; সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৫ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।
আধুনিক হাঙ্গেরীয় সাহিত্যের একজন অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব লাসলো। অভিনব শৈলীর পাশাপাশি দার্শনিক গভীরতার জন্য তাঁর সাহিত্য সমাদৃত হয়েছে। তাঁকে ফ্রানৎস কাফকা ও স্যামুয়েল বেকেটের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বজোড়া আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের মধ্যেও শিল্পের লেলিহান ঔজ্জ্বল্য ফুটে ওঠে লাসলোর লেখায়। তাই যুদ্ধবিধ্বস্ত সময়ের বুকে ফুলের মতো স্থান করে নিল তাঁর সাহিত্য।
লাসলোর জন্য সাহিত্যে এটা প্রথম পুরস্কার নয়, ২০১৪ সালে সাহিত্যকর্মের জন্য ম্যান বুকার ইন্টারন্যাশনাল পুরস্কার পান তিনি। এ পুরস্কার বিশ্বসাহিত্যে তাঁর অবস্থানকে সুদৃঢ় করে।
লাসলোর সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—স্বতন্ত্র শৈলী ও গঠন। উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু হলো—মানবতার অবক্ষয়, ধ্বংসের অনিবার্যতা ও আধুনিক জীবনের লক্ষ্যহীন চলন। তাঁর চরিত্রদের মধ্যে প্রায়ই একধরনের হতাশা ও বিচ্ছিন্নতা দেখা যায়; তারা এমন এক জগতের পথিক, যেখানে নৈতিকতা ও আশা বিলীনপ্রায়।
১৯৮৫ সালে প্রকাশিত ‘স্যাটানটাঙ্গো’ নামে প্রথম উপন্যাস লিখেই খ্যাতি পান লাসলো। এই উপন্যাসে বিচ্ছিন্ন ও পতিত এক কৃষি সমবায় গ্রামের জীবন তুলে ধরেছেন তিনি। সেখানে একধরনের বিভ্রম ও আশার জন্ম দেয় এক রহস্যময় আগন্তুকের আগমনে। এই উপন্যাস অবলম্বনে একই শিরোনামে সাত ঘণ্টার কালজয়ী চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন বিখ্যাত পরিচালক বেলা টর।
লাসলোর আরেকটি ফিকশন উপন্যাস হলো— ‘দ্য মেলানকোলি অব রেজিস্ট্যান্স’। হাঙ্গেরির এক কাল্পনিক শহরের জীবন ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে। সামুদ্রিক প্রাণী হাঙরের প্রদর্শনীকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যকার উন্মাদনা, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও একনায়কতন্ত্রের উত্থানের চিত্র আঁকা হয়েছে তাতে।
‘ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার’ লাসলোর আরেকটি বিখ্যাত উপন্যাস। লম্বা লম্বা বাক্যে লেখা এই উপন্যাস লাসলোর শৈলী নিয়ে পাঠকদের নতুন করে ভাবায়। উপন্যাসের নায়ক একটি পাণ্ডুলিপি রক্ষা করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন শহর ঘুরে বেড়ায়। বিশ্বের চূড়ান্ত ধ্বংসের একটি কাব্যিক বর্ণনা পাওয়া যায় এই উপন্যাসে।
এবার লাসলোকে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করার নেপথ্যে নোবেল কমিটির বড় কারণ ছিল তাঁর সাহিত্যে শিল্পের জয়ধ্বনি তোলার প্রচেষ্টা। যখন সারা বিশ্বের বেশ কিছু দেশ যুদ্ধবিধ্বস্ত বা যুদ্ধের জন্য উৎসুক, তখন বারবার শিল্পের মোহিনী প্রেম ও বন্ধনের কথা মনে করিয়ে দিতে চায় লাসলোর সাহিত্য।

হাঙ্গেরির সাহিত্যে অসীম জনপ্রিয়তা ও প্রভাব তাঁর; বিশ্বজোড়া আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের দাপটেও শিল্পের শক্তি চেনায় তাঁর কলম। তিনি হাঙ্গেরিয়ান ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই; সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৫ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।
আধুনিক হাঙ্গেরীয় সাহিত্যের একজন অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব লাসলো। অভিনব শৈলীর পাশাপাশি দার্শনিক গভীরতার জন্য তাঁর সাহিত্য সমাদৃত হয়েছে। তাঁকে ফ্রানৎস কাফকা ও স্যামুয়েল বেকেটের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বজোড়া আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের মধ্যেও শিল্পের লেলিহান ঔজ্জ্বল্য ফুটে ওঠে লাসলোর লেখায়। তাই যুদ্ধবিধ্বস্ত সময়ের বুকে ফুলের মতো স্থান করে নিল তাঁর সাহিত্য।
লাসলোর জন্য সাহিত্যে এটা প্রথম পুরস্কার নয়, ২০১৪ সালে সাহিত্যকর্মের জন্য ম্যান বুকার ইন্টারন্যাশনাল পুরস্কার পান তিনি। এ পুরস্কার বিশ্বসাহিত্যে তাঁর অবস্থানকে সুদৃঢ় করে।
লাসলোর সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—স্বতন্ত্র শৈলী ও গঠন। উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু হলো—মানবতার অবক্ষয়, ধ্বংসের অনিবার্যতা ও আধুনিক জীবনের লক্ষ্যহীন চলন। তাঁর চরিত্রদের মধ্যে প্রায়ই একধরনের হতাশা ও বিচ্ছিন্নতা দেখা যায়; তারা এমন এক জগতের পথিক, যেখানে নৈতিকতা ও আশা বিলীনপ্রায়।
১৯৮৫ সালে প্রকাশিত ‘স্যাটানটাঙ্গো’ নামে প্রথম উপন্যাস লিখেই খ্যাতি পান লাসলো। এই উপন্যাসে বিচ্ছিন্ন ও পতিত এক কৃষি সমবায় গ্রামের জীবন তুলে ধরেছেন তিনি। সেখানে একধরনের বিভ্রম ও আশার জন্ম দেয় এক রহস্যময় আগন্তুকের আগমনে। এই উপন্যাস অবলম্বনে একই শিরোনামে সাত ঘণ্টার কালজয়ী চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন বিখ্যাত পরিচালক বেলা টর।
লাসলোর আরেকটি ফিকশন উপন্যাস হলো— ‘দ্য মেলানকোলি অব রেজিস্ট্যান্স’। হাঙ্গেরির এক কাল্পনিক শহরের জীবন ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে। সামুদ্রিক প্রাণী হাঙরের প্রদর্শনীকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যকার উন্মাদনা, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও একনায়কতন্ত্রের উত্থানের চিত্র আঁকা হয়েছে তাতে।
‘ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার’ লাসলোর আরেকটি বিখ্যাত উপন্যাস। লম্বা লম্বা বাক্যে লেখা এই উপন্যাস লাসলোর শৈলী নিয়ে পাঠকদের নতুন করে ভাবায়। উপন্যাসের নায়ক একটি পাণ্ডুলিপি রক্ষা করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন শহর ঘুরে বেড়ায়। বিশ্বের চূড়ান্ত ধ্বংসের একটি কাব্যিক বর্ণনা পাওয়া যায় এই উপন্যাসে।
এবার লাসলোকে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করার নেপথ্যে নোবেল কমিটির বড় কারণ ছিল তাঁর সাহিত্যে শিল্পের জয়ধ্বনি তোলার প্রচেষ্টা। যখন সারা বিশ্বের বেশ কিছু দেশ যুদ্ধবিধ্বস্ত বা যুদ্ধের জন্য উৎসুক, তখন বারবার শিল্পের মোহিনী প্রেম ও বন্ধনের কথা মনে করিয়ে দিতে চায় লাসলোর সাহিত্য।

বুড়িগঙ্গার পাড় থেকে টেমসের তীরে আসার প্রায় এক বছর হয়ে এল। গত বছর অক্টোবরে সূর্যালোক উদ্ভাসিত প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর এক দেশ ছেড়ে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পাড়ে হাড়কাঁপানো ধূসর ভূমিতে পদার্পণ করি। আমার আগমনের সময়টায় বিলাতে শীত আসি-আসি করছে—জাঁকিয়ে বসেনি। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা আগেই বলেছিলেন, ইউরোপের শীত কোনো ছেলেখ
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২২
জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল।
১ দিন আগে
জনপ্রিয় কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা রকিব হাসান মারা গেছেন। আজ বুধবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস চলাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।
৬ দিন আগে
হাঙ্গেরির ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই এবার (২০২৫ সালে) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তাঁর দীর্ঘ, দার্শনিক বাক্য ও মানবজীবনের বিশৃঙ্খলার গভীর অনুসন্ধানী সাহিত্যকর্মের জন্য। সুইডিশ একাডেমি তাঁকে সম্মান জানিয়েছে ‘শিল্পের শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার’ জন্য।
১২ দিন আগে