শাইখ সিরাজ

কৃষি গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে নেদারল্যান্ডস বিশ্বজুড়ে সুপরিচিত। আগামীর কৃষিকে টিকিয়ে রাখা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দেশটি দীর্ঘদিন ধরেই বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত সহায়তায় কৃষিপ্রযুক্তির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে যে প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখছে, তাদের মধ্যে রয়্যাল আইকোলকাম্প একটি উল্লেখযোগ্য নাম। ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে প্রতিষ্ঠানটির ব্যাপক কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের সুযোগ হয়েছিল।
১১১ বছরের ঐতিহ্য বহনকারী রয়্যাল আইকোলকাম্প মূলত একটি পারিবারিক প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে ছয়-সাত হেক্টর বিস্তৃত জমিতে তারা পরিচালনা করছে প্রযুক্তিভিত্তিক নানাবিধ কার্যক্রম। কৃষিতে ব্যবহৃত আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং বিভিন্ন উপকরণের নকশা, নির্মাণ ও ম্যানুফ্যাকচারিং তাদের প্রধান ব্যবসা হলেও, পাশাপাশি মাটি, পানি, আবহাওয়া এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বহুমাত্রিক প্রভাব নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি ধারাবাহিকভাবে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।
এপ্রিলের এক সোনালি বিকেলে আমি আমার টিমসহ উপস্থিত হয়েছিলাম নেদারল্যান্ডসের গিসব্যাক এলাকায় অবস্থিত রয়্যাল আইকোলকাম্প একাডেমিতে। সেখানে আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন প্রতিষ্ঠানটির প্রধান ফোন্স আইকোলকাম্প এবং কয়েকজন গবেষক। ফোন্স আমাদের নিয়ে গেলেন একটি দ্বিতল ভবনে, যেখানে কৃষির মৌলিক ভিত্তি ‘মাটি ও পানি’ নিয়ে তাঁদের প্রায় সব গবেষণা ও প্রযুক্তি উন্নয়নকর্ম সম্পন্ন হয়। মাটির স্বাস্থ্য, পানির গুণাগুণ ও প্রকৃত চাহিদা বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহার হওয়া আধুনিক সব যন্ত্রপাতি সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো। প্রতিটি যন্ত্রের কার্যকারিতা, প্রয়োজনীয়তা ও কৃষি উৎপাদনে এর ব্যবহার নিয়ে ফোন্স বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন।
ফোন্স দেখালেন বিভিন্ন ধরনের সেন্সর। যেগুলো রিয়েল-টাইমে জানায় মাটির রাসায়নিক গুণাগুণ, পানির স্তর, আর্দ্রতা, এমনকি মাটিতে পানির লবণাক্ততা বা দূষণের মতো সূক্ষ্মতম তথ্যও। একটি বিশেষ সেন্সর দেখিয়ে ফোন্স বললেন, এই সেন্সরটা মাটির ১৫০ থেকে ২০০ মিটার গভীরে বসানো হয়। সেখান থেকে পাওয়া তথ্য সরাসরি চলে যায় কম্পিউটার বা মোবাইল ফোনে। অফিসে বসেই আপনি সেচ ব্যবস্থাপনা করতে পারবেন, মাঠে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন নেই।
ফোন্স আমাদের দেখালেন মাটিক্ষয় নির্ণায়ক একটি সেন্সরও। সেন্সরটিতে স্থাপন করা রয়েছে অত্যন্ত সংবেদনশীল মাইক্রোফোন, যা বাতাসে মাটি কতটা আলগা হচ্ছে, কত গতিতে মাটির কণা বাতাসে আঘাত করছে, এসব বিশ্লেষণের মাধ্যমে জমির ক্ষয়মাত্রা নির্ণয় করতে পারে। অথচ আমাদের দেশে এখনো অধিকাংশ কৃষকই মাটি পরীক্ষা ছাড়া চাষাবাদ করেন। ফলে অপ্রয়োজনীয় সার ব্যবহার, খরচ বৃদ্ধি ও ফলন হ্রাস—সবই একসঙ্গে ঘটে। এসব দেখে আমি ভাবছিলাম, নিয়মিত মাটি পরীক্ষা চালু করা গেলে আমাদের কৃষিকাজে কত বড় পরিবর্তন আনা সম্ভব হতো!
এরপর ফোন্স আমাদের নিয়ে গেলেন ইনোফিল্ডস নামে আরেকটি অংশে, যা মূলত উদ্ভাবনী কৃষিপ্রযুক্তির পরীক্ষাগার। কোন ভূমিতে কৃষি, কোন জায়গায় শিল্প বা বাসস্থান হবে, তা বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে নির্ধারণ করাও তাঁদের একটি বড় কাজ। যাওয়ার পথে ফোন্স জানালেন, ১৯১১ সালে তাঁর দাদা ছিলেন এলাকার দক্ষ কামার। তাঁর হাত ধরেই কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি দিয়ে প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়। ক্রমে যান্ত্রিক কৃষির বিবর্তন, আধুনিকীকরণ এবং পারিবারিক ঐতিহ্যের ধারা ধরে আজ ফোন্স নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রতিষ্ঠানের। তাঁর কাছে আধুনিক কৃষি মানেই প্রযুক্তিনির্ভর, দক্ষতাভিত্তিক কৃষিকাজ, যেখানে কায়িক শ্রমের তুলনায় কারিগরি জ্ঞান অনেক বেশি প্রয়োজন। তাই তরুণেরাও আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসছে।
ইনোফিল্ডসে গিয়ে পরিচয় হলো তরুণ বিজনেস লাইন ম্যানেজার বব ক্লাইন লাংকহর্সটের সঙ্গে। তিনি আমাদের দেখালেন ‘ফার্মবোট’ নামে এক অভিনব রোবট। এই রোবটটি বীজ বুনন থেকে সেচ দেওয়া, আগাছা পরিষ্কার করা, তদারকি—সবকিছুই স্বয়ংক্রিয়ভাবে করতে সক্ষম। বব বললেন, ‘রোবট আগাছা পরিষ্কার করায় কেমিক্যাল ব্যবহারের দরকার নেই। আমরা মাটিতে জৈব সার ব্যবহার করি, কোনো রাসায়নিক সার বা কীটনাশকের ওপর নির্ভরশীল নই। প্রকৃতি যেমন নিজের মাটি নিজেই পুনরুজ্জীবিত করে, আমরা প্রযুক্তির সাহায্যে ঠিক সেটাই করছি, তবে রাসায়নিক ছাড়া। শার্ট-প্যান্ট পরে এই কৃষি করা সম্ভব বলে তরুণেরা খুব আগ্রহী এই কাজে। আমরা একে বলছি “সেক্সি অ্যাগ্রিকালচার”।’
বব ক্লাইন আমাদের নিয়ে গেলেন তাঁদের ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদনের স্থানে। সেখানে কেঁচোসমৃদ্ধ এক প্লট দেখিয়ে বব বললেন, এগুলো দেখুন, কী সুন্দর সুস্থ কেঁচো! এদের খাবার পর্যাপ্ত আছে, আর খাওয়া শেষে এদের বর্জ্য মাটিকে ফিরিয়ে দেয় সমৃদ্ধ জৈবগুণ। মাটির আর্দ্রতাও ঠিকঠাক আছে। এতে প্রচুর কার্বন আছে, যা জলবায়ুর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ, মাটিতে কার্বনের পরিমাণ যত বেশি থাকে, মাটি তত বেশি পানি ধারণ করতে পারে।
পরবর্তী পর্যায়ে আমরা পৌঁছালাম মাটির জীববিজ্ঞান গবেষণাগারে, যার দায়িত্বে ছিলেন স্তেরা আইটারাইক। তিনি আমাদের দেখালেন সয়েল বায়োলজি অ্যানালাইসিস। মাইক্রোস্কোপে দেখা গেল নেমাটোড, ব্যাকটেরিয়া, অণুজীব, মিনারেল। কেমিক্যাল ইনপুট ছাড়াই মাটির নিজস্ব জীববৈচিত্র্য কতটা শক্তিশালী এবং ফসল উৎপাদনে কীভাবে ভূমিকা রাখে, তা খুব দক্ষতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করলেন স্তেরা।
গবেষণাগার থেকে বের হয়ে ফোন্স আমাদের নিয়ে গেলেন মাঠে। দেখালেন সোলার এনার্জিতে চলা রেইনফল ডিটেক্টর। এটি এমন এক যন্ত্র, যা বৃষ্টির পরিমাণ, বাতাসের গতি ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক তথ্য দেয়। বিজনেস ইনোভেশন স্ট্র্যাটেজি বিভাগের ড. ইয়োখেন ফ্রুবিখ জানালেন, মাঠে স্থাপিত ইভাপোরিমিটারের তথ্য অনুযায়ী, নেদারল্যান্ডসে মোট বৃষ্টির প্রায় ৬৫ শতাংশ বাষ্পীভূত হয়ে যায়। মাটিতে কত পানি আছে, কত দরকার, বৃষ্টির পানি কতটা ধরে রাখতে পারছে—এসব তথ্য কৃষিকাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফোন্স বললেন, ‘ছয় বছর আগে ইভাপোরিমিটার আবিষ্কার না হলে আমরা জানতেই পারতাম না যে দেশের এতটা বৃষ্টির পানি বাষ্পে মিলিয়ে যায়।’
সেন্সরগুলো থেকে প্রাপ্ত রিয়েল-টাইম তথ্য তাঁদের কন্ট্রোল সেন্টারে পাঠানো হয়, যেখানে সব ডেটা বিশ্লেষণ করে স্বয়ংক্রিয় সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় সেচ ব্যবস্থাপনা, পানির ভারসাম্য বজায় রাখা এবং মাটির স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়ে। এতে কৃষকের মাঠে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন কমে গেছে। অফিসে বসেই কৃষিকাজের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব।
এই প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি তরুণদের কাছে ক্রমে আকর্ষণীয় পেশায় পরিণত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রযুক্তির ব্যবহার যে কতটা কার্যকর, রয়্যাল আইকোলকাম্প তার জীবন্ত উদাহরণ। তারা পৃথিবীর সব সম্ভাব্য হাইড্রোলজিকাল এক্সপেরিমেন্টের তথ্য সংগ্রহ করছে, পরিবেশবান্ধব কৃষির ভবিষ্যৎও গড়ে তুলছে।
আগামীর কৃষি হবে নিঃসন্দেহে প্রযুক্তির কৃষি—এ উপলব্ধি থেকেই নেদারল্যান্ডস বহু পথ এগিয়ে। জলবায়ু পরিবর্তন সামনে রেখে তারা তৈরি করছে নতুন কৃষি-ধারণা, নতুন মডেল। ঐতিহ্যবাহী কৃষি আর উদীয়মান নগরকৃষির সমন্বয়ে তারা তৈরি করছে ভবিষ্যতের কৃষিব্যবস্থা। কৃষি তাদের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি—এ সত্য আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে রয়্যাল আইকোলকাম্পের কর্মদর্শনে। আমাদের কৃষি গবেষণা, অনুশীলন এবং কৃষি-বাণিজ্যের উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানটির এ পথচলা হতে পারে অনুপ্রেরণার অশেষ উৎস।
লেখক: পরিচালক ও বার্তাপ্রধান চ্যানেল আই

কৃষি গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে নেদারল্যান্ডস বিশ্বজুড়ে সুপরিচিত। আগামীর কৃষিকে টিকিয়ে রাখা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দেশটি দীর্ঘদিন ধরেই বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত সহায়তায় কৃষিপ্রযুক্তির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে যে প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখছে, তাদের মধ্যে রয়্যাল আইকোলকাম্প একটি উল্লেখযোগ্য নাম। ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে প্রতিষ্ঠানটির ব্যাপক কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের সুযোগ হয়েছিল।
১১১ বছরের ঐতিহ্য বহনকারী রয়্যাল আইকোলকাম্প মূলত একটি পারিবারিক প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে ছয়-সাত হেক্টর বিস্তৃত জমিতে তারা পরিচালনা করছে প্রযুক্তিভিত্তিক নানাবিধ কার্যক্রম। কৃষিতে ব্যবহৃত আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং বিভিন্ন উপকরণের নকশা, নির্মাণ ও ম্যানুফ্যাকচারিং তাদের প্রধান ব্যবসা হলেও, পাশাপাশি মাটি, পানি, আবহাওয়া এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বহুমাত্রিক প্রভাব নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি ধারাবাহিকভাবে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।
এপ্রিলের এক সোনালি বিকেলে আমি আমার টিমসহ উপস্থিত হয়েছিলাম নেদারল্যান্ডসের গিসব্যাক এলাকায় অবস্থিত রয়্যাল আইকোলকাম্প একাডেমিতে। সেখানে আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন প্রতিষ্ঠানটির প্রধান ফোন্স আইকোলকাম্প এবং কয়েকজন গবেষক। ফোন্স আমাদের নিয়ে গেলেন একটি দ্বিতল ভবনে, যেখানে কৃষির মৌলিক ভিত্তি ‘মাটি ও পানি’ নিয়ে তাঁদের প্রায় সব গবেষণা ও প্রযুক্তি উন্নয়নকর্ম সম্পন্ন হয়। মাটির স্বাস্থ্য, পানির গুণাগুণ ও প্রকৃত চাহিদা বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহার হওয়া আধুনিক সব যন্ত্রপাতি সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো। প্রতিটি যন্ত্রের কার্যকারিতা, প্রয়োজনীয়তা ও কৃষি উৎপাদনে এর ব্যবহার নিয়ে ফোন্স বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন।
ফোন্স দেখালেন বিভিন্ন ধরনের সেন্সর। যেগুলো রিয়েল-টাইমে জানায় মাটির রাসায়নিক গুণাগুণ, পানির স্তর, আর্দ্রতা, এমনকি মাটিতে পানির লবণাক্ততা বা দূষণের মতো সূক্ষ্মতম তথ্যও। একটি বিশেষ সেন্সর দেখিয়ে ফোন্স বললেন, এই সেন্সরটা মাটির ১৫০ থেকে ২০০ মিটার গভীরে বসানো হয়। সেখান থেকে পাওয়া তথ্য সরাসরি চলে যায় কম্পিউটার বা মোবাইল ফোনে। অফিসে বসেই আপনি সেচ ব্যবস্থাপনা করতে পারবেন, মাঠে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন নেই।
ফোন্স আমাদের দেখালেন মাটিক্ষয় নির্ণায়ক একটি সেন্সরও। সেন্সরটিতে স্থাপন করা রয়েছে অত্যন্ত সংবেদনশীল মাইক্রোফোন, যা বাতাসে মাটি কতটা আলগা হচ্ছে, কত গতিতে মাটির কণা বাতাসে আঘাত করছে, এসব বিশ্লেষণের মাধ্যমে জমির ক্ষয়মাত্রা নির্ণয় করতে পারে। অথচ আমাদের দেশে এখনো অধিকাংশ কৃষকই মাটি পরীক্ষা ছাড়া চাষাবাদ করেন। ফলে অপ্রয়োজনীয় সার ব্যবহার, খরচ বৃদ্ধি ও ফলন হ্রাস—সবই একসঙ্গে ঘটে। এসব দেখে আমি ভাবছিলাম, নিয়মিত মাটি পরীক্ষা চালু করা গেলে আমাদের কৃষিকাজে কত বড় পরিবর্তন আনা সম্ভব হতো!
এরপর ফোন্স আমাদের নিয়ে গেলেন ইনোফিল্ডস নামে আরেকটি অংশে, যা মূলত উদ্ভাবনী কৃষিপ্রযুক্তির পরীক্ষাগার। কোন ভূমিতে কৃষি, কোন জায়গায় শিল্প বা বাসস্থান হবে, তা বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে নির্ধারণ করাও তাঁদের একটি বড় কাজ। যাওয়ার পথে ফোন্স জানালেন, ১৯১১ সালে তাঁর দাদা ছিলেন এলাকার দক্ষ কামার। তাঁর হাত ধরেই কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি দিয়ে প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়। ক্রমে যান্ত্রিক কৃষির বিবর্তন, আধুনিকীকরণ এবং পারিবারিক ঐতিহ্যের ধারা ধরে আজ ফোন্স নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রতিষ্ঠানের। তাঁর কাছে আধুনিক কৃষি মানেই প্রযুক্তিনির্ভর, দক্ষতাভিত্তিক কৃষিকাজ, যেখানে কায়িক শ্রমের তুলনায় কারিগরি জ্ঞান অনেক বেশি প্রয়োজন। তাই তরুণেরাও আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসছে।
ইনোফিল্ডসে গিয়ে পরিচয় হলো তরুণ বিজনেস লাইন ম্যানেজার বব ক্লাইন লাংকহর্সটের সঙ্গে। তিনি আমাদের দেখালেন ‘ফার্মবোট’ নামে এক অভিনব রোবট। এই রোবটটি বীজ বুনন থেকে সেচ দেওয়া, আগাছা পরিষ্কার করা, তদারকি—সবকিছুই স্বয়ংক্রিয়ভাবে করতে সক্ষম। বব বললেন, ‘রোবট আগাছা পরিষ্কার করায় কেমিক্যাল ব্যবহারের দরকার নেই। আমরা মাটিতে জৈব সার ব্যবহার করি, কোনো রাসায়নিক সার বা কীটনাশকের ওপর নির্ভরশীল নই। প্রকৃতি যেমন নিজের মাটি নিজেই পুনরুজ্জীবিত করে, আমরা প্রযুক্তির সাহায্যে ঠিক সেটাই করছি, তবে রাসায়নিক ছাড়া। শার্ট-প্যান্ট পরে এই কৃষি করা সম্ভব বলে তরুণেরা খুব আগ্রহী এই কাজে। আমরা একে বলছি “সেক্সি অ্যাগ্রিকালচার”।’
বব ক্লাইন আমাদের নিয়ে গেলেন তাঁদের ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদনের স্থানে। সেখানে কেঁচোসমৃদ্ধ এক প্লট দেখিয়ে বব বললেন, এগুলো দেখুন, কী সুন্দর সুস্থ কেঁচো! এদের খাবার পর্যাপ্ত আছে, আর খাওয়া শেষে এদের বর্জ্য মাটিকে ফিরিয়ে দেয় সমৃদ্ধ জৈবগুণ। মাটির আর্দ্রতাও ঠিকঠাক আছে। এতে প্রচুর কার্বন আছে, যা জলবায়ুর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ, মাটিতে কার্বনের পরিমাণ যত বেশি থাকে, মাটি তত বেশি পানি ধারণ করতে পারে।
পরবর্তী পর্যায়ে আমরা পৌঁছালাম মাটির জীববিজ্ঞান গবেষণাগারে, যার দায়িত্বে ছিলেন স্তেরা আইটারাইক। তিনি আমাদের দেখালেন সয়েল বায়োলজি অ্যানালাইসিস। মাইক্রোস্কোপে দেখা গেল নেমাটোড, ব্যাকটেরিয়া, অণুজীব, মিনারেল। কেমিক্যাল ইনপুট ছাড়াই মাটির নিজস্ব জীববৈচিত্র্য কতটা শক্তিশালী এবং ফসল উৎপাদনে কীভাবে ভূমিকা রাখে, তা খুব দক্ষতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করলেন স্তেরা।
গবেষণাগার থেকে বের হয়ে ফোন্স আমাদের নিয়ে গেলেন মাঠে। দেখালেন সোলার এনার্জিতে চলা রেইনফল ডিটেক্টর। এটি এমন এক যন্ত্র, যা বৃষ্টির পরিমাণ, বাতাসের গতি ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক তথ্য দেয়। বিজনেস ইনোভেশন স্ট্র্যাটেজি বিভাগের ড. ইয়োখেন ফ্রুবিখ জানালেন, মাঠে স্থাপিত ইভাপোরিমিটারের তথ্য অনুযায়ী, নেদারল্যান্ডসে মোট বৃষ্টির প্রায় ৬৫ শতাংশ বাষ্পীভূত হয়ে যায়। মাটিতে কত পানি আছে, কত দরকার, বৃষ্টির পানি কতটা ধরে রাখতে পারছে—এসব তথ্য কৃষিকাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফোন্স বললেন, ‘ছয় বছর আগে ইভাপোরিমিটার আবিষ্কার না হলে আমরা জানতেই পারতাম না যে দেশের এতটা বৃষ্টির পানি বাষ্পে মিলিয়ে যায়।’
সেন্সরগুলো থেকে প্রাপ্ত রিয়েল-টাইম তথ্য তাঁদের কন্ট্রোল সেন্টারে পাঠানো হয়, যেখানে সব ডেটা বিশ্লেষণ করে স্বয়ংক্রিয় সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় সেচ ব্যবস্থাপনা, পানির ভারসাম্য বজায় রাখা এবং মাটির স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়ে। এতে কৃষকের মাঠে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন কমে গেছে। অফিসে বসেই কৃষিকাজের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব।
এই প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি তরুণদের কাছে ক্রমে আকর্ষণীয় পেশায় পরিণত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রযুক্তির ব্যবহার যে কতটা কার্যকর, রয়্যাল আইকোলকাম্প তার জীবন্ত উদাহরণ। তারা পৃথিবীর সব সম্ভাব্য হাইড্রোলজিকাল এক্সপেরিমেন্টের তথ্য সংগ্রহ করছে, পরিবেশবান্ধব কৃষির ভবিষ্যৎও গড়ে তুলছে।
আগামীর কৃষি হবে নিঃসন্দেহে প্রযুক্তির কৃষি—এ উপলব্ধি থেকেই নেদারল্যান্ডস বহু পথ এগিয়ে। জলবায়ু পরিবর্তন সামনে রেখে তারা তৈরি করছে নতুন কৃষি-ধারণা, নতুন মডেল। ঐতিহ্যবাহী কৃষি আর উদীয়মান নগরকৃষির সমন্বয়ে তারা তৈরি করছে ভবিষ্যতের কৃষিব্যবস্থা। কৃষি তাদের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি—এ সত্য আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে রয়্যাল আইকোলকাম্পের কর্মদর্শনে। আমাদের কৃষি গবেষণা, অনুশীলন এবং কৃষি-বাণিজ্যের উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানটির এ পথচলা হতে পারে অনুপ্রেরণার অশেষ উৎস।
লেখক: পরিচালক ও বার্তাপ্রধান চ্যানেল আই

দুর্নীতি আর অন্যায়ের সঙ্গে যে আমরা মিতালি পাতিয়েছি, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালের বর্তমান অবস্থা সে কথাকেই দৃঢ় ভিত্তির ওপর আবারও দাঁড় করিয়ে দেয়। খুবই সাদামাটা ছোট একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে আজকের পত্রিকায়। দুদক এ হাসপাতালে অভিযান চালিয়েছিল গত মঙ্গলবার।
৯ ঘণ্টা আগে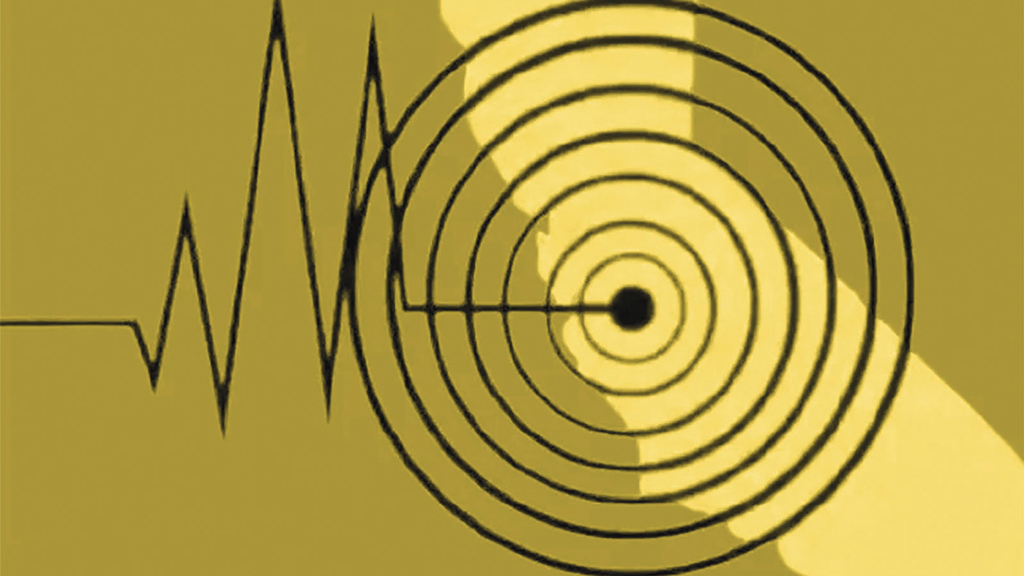
নরসিংদীতে ২১ নভেম্বর সংঘটিত ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্প দেশের ভূমিকম্পজনিত গভীর ঝুঁকির বাস্তবতাকে নতুন করে সামনে এনেছে। ২৬ সেকেন্ড স্থায়ী এই কম্পনটি ছিল দশকের মধ্যে এ অঞ্চলের অন্যতম শক্তিশালী ভূকম্পন।
৯ ঘণ্টা আগে
সম্প্রতি পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের (এফ) সভাপতি এবং দেশটির সাবেক মন্ত্রী মাওলানা ফজলুর রহমান বলেছেন, ‘পাকিস্তান সব সময় বাংলাদেশের কল্যাণ, উন্নতি, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা কামনা করে। বাংলাদেশকে তারা ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ হিসেবে মনে করে।
৯ ঘণ্টা আগে
বিশ্বায়নের যুগে একটি রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থাকে শুধু দেশের সীমানার ভেতরে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জ্ঞান ও উদ্ভাবনের কেন্দ্র হিসেবে এখন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার অংশ। তাই বিশ্বের শীর্ষ র্যাঙ্কিং তালিকায় একটি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপস্থিতি শুধু মর্যাদার বিষয় নয়, বরং তা একটি...
৯ ঘণ্টা আগেসম্পাদকীয়

দুর্নীতি আর অন্যায়ের সঙ্গে যে আমরা মিতালি পাতিয়েছি, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালের বর্তমান অবস্থা সে কথাকেই দৃঢ় ভিত্তির ওপর আবারও দাঁড় করিয়ে দেয়। খুবই সাদামাটা ছোট একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে আজকের পত্রিকায়। দুদক এ হাসপাতালে অভিযান চালিয়েছিল গত মঙ্গলবার। আর তাতেই স্পষ্ট হয়, কীভাবে রোগীদের জন্য বরাদ্দ মাংসের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে হাসপাতালের দায়িত্বশীল লোকজনই।
সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর সেবার নমুনা নিয়ে কথা বলতে গেলে কত কথাই না বলতে হয়। বেশি উদাহরণ দিতে হবে না, ভূমি অফিস, সাবরেজিস্ট্রারের অফিসে সেবা পাওয়ার জন্য যাঁরা যান, দৈবচয়ন ভিত্তিতে তাঁদের যে কারও সঙ্গে কথা বলে দেখুন, কীভাবে সেই সেবা তাঁরা পান, তা বিস্তারিতভাবে আপনার সামনে প্রকাশ পাবে। সরকারি অফিসের পিয়ন, চাপরাশি, মন্ত্রী বা উপদেষ্টার এপিএসদের দাপটের কথা শুনেছি অনেক। হবিগঞ্জ হাসপাতালের খাবারের টাকা চুরি সে তুলনায় মামুলি ব্যাপার। কিন্তু এই একটি ব্যাপার নিয়ে কথা বললেই সরকারি কাজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে উঠবে।
হাসপাতালটিতে একজন রোগীর দুবেলা খাবারের জন্য ১৭০ গ্রাম মুরগির মাংস বরাদ্দ আছে। ব্রয়লার মুরগির মাংস কেনা হয় ২৯৭ টাকা কেজি দরে। রোগীর ভাগ্যে দিনে ১৭০ গ্রাম মুরগির মাংস জুটলে তা শরীরে প্রোটিনের চাহিদা অনেকাংশে লাঘব করে। কিন্তু রোগীর কি সে ভাগ্য আছে? যাঁরা এই কেনাকাটা-রাঁধন-বাড়নের সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা কি রোগীকে গিয়ে বলবেন, ‘এই যে, আমরা আপনারই সেবায় নিয়োজিত। আপনার জন্য বরাদ্দ মাংস আপনাকেই দেওয়া হচ্ছে। খান।’ এ রকম সংলাপ সিনেমায় থাকতে পারে, রোগীরা আদৌ এ ধরনের অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হননি। বরং খাওয়ার সময় তাঁরা ট্রেতে যে মাংস দেখেন, তা তাঁদের জন্য বরাদ্দ মাংসের অর্ধেকের কম। একজন রোগীকে দুবেলা যেখানে ১৭০ গ্রাম মাংস দেওয়ার কথা, সেখানে রোগী পান বড়জোর ৭৫ গ্রাম মাংস। বাকিটা কী হয়? প্রশ্নটা সহজ এবং উত্তরও সবার জানা।
বুঝলাম, দুদকের অভিযানে বেরিয়ে এসেছে এই তথ্য। কিন্তু এই ঘটনা তো এভাবেই দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ঘটে চলেছে। রোগীর প্রাপ্য খাদ্য লোপাট করছে স্বার্থান্বেষী মহল। তারা কি কারও অচেনা? হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কি তাদের চিহ্নিত করতে পারেনি কখনো, কখনো তাদের মনে প্রশ্ন জাগেনি যে চুরি হচ্ছে কোথাও, কোনো এক বিভাগে? যাঁরা চুরি করছেন, তাঁরা হাসপাতালেরই লোক?
যাঁদের সঙ্গে যোগসাজশে হচ্ছে এই চুরি, তাঁরাও অচেনা কেউ নয়?
আসলে চোরেরা এতটাই শক্তিশালী যে তাঁদের নিয়ে কেউ কথা বলতে সাহস পায় না। তার চেয়ে চোরদের সঙ্গে ভিড়ে যাওয়া অথবা চুরি সম্পর্কে নীরব থাকাই শ্রেয় বলে মনে
করে ছা-পোষা মানুষ। এ কারণেই হয়তোবা দিনের পর দিন চোরের সংখ্যা বাড়তে থাকে। আর জাতীয় পরিসরে যখন চুরির কথা ভাবা
হয়? আমরা নিশ্চিত, তাহলে বুকের রক্ত হিম হয়ে আসবে!

দুর্নীতি আর অন্যায়ের সঙ্গে যে আমরা মিতালি পাতিয়েছি, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালের বর্তমান অবস্থা সে কথাকেই দৃঢ় ভিত্তির ওপর আবারও দাঁড় করিয়ে দেয়। খুবই সাদামাটা ছোট একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে আজকের পত্রিকায়। দুদক এ হাসপাতালে অভিযান চালিয়েছিল গত মঙ্গলবার। আর তাতেই স্পষ্ট হয়, কীভাবে রোগীদের জন্য বরাদ্দ মাংসের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে হাসপাতালের দায়িত্বশীল লোকজনই।
সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর সেবার নমুনা নিয়ে কথা বলতে গেলে কত কথাই না বলতে হয়। বেশি উদাহরণ দিতে হবে না, ভূমি অফিস, সাবরেজিস্ট্রারের অফিসে সেবা পাওয়ার জন্য যাঁরা যান, দৈবচয়ন ভিত্তিতে তাঁদের যে কারও সঙ্গে কথা বলে দেখুন, কীভাবে সেই সেবা তাঁরা পান, তা বিস্তারিতভাবে আপনার সামনে প্রকাশ পাবে। সরকারি অফিসের পিয়ন, চাপরাশি, মন্ত্রী বা উপদেষ্টার এপিএসদের দাপটের কথা শুনেছি অনেক। হবিগঞ্জ হাসপাতালের খাবারের টাকা চুরি সে তুলনায় মামুলি ব্যাপার। কিন্তু এই একটি ব্যাপার নিয়ে কথা বললেই সরকারি কাজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে উঠবে।
হাসপাতালটিতে একজন রোগীর দুবেলা খাবারের জন্য ১৭০ গ্রাম মুরগির মাংস বরাদ্দ আছে। ব্রয়লার মুরগির মাংস কেনা হয় ২৯৭ টাকা কেজি দরে। রোগীর ভাগ্যে দিনে ১৭০ গ্রাম মুরগির মাংস জুটলে তা শরীরে প্রোটিনের চাহিদা অনেকাংশে লাঘব করে। কিন্তু রোগীর কি সে ভাগ্য আছে? যাঁরা এই কেনাকাটা-রাঁধন-বাড়নের সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা কি রোগীকে গিয়ে বলবেন, ‘এই যে, আমরা আপনারই সেবায় নিয়োজিত। আপনার জন্য বরাদ্দ মাংস আপনাকেই দেওয়া হচ্ছে। খান।’ এ রকম সংলাপ সিনেমায় থাকতে পারে, রোগীরা আদৌ এ ধরনের অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হননি। বরং খাওয়ার সময় তাঁরা ট্রেতে যে মাংস দেখেন, তা তাঁদের জন্য বরাদ্দ মাংসের অর্ধেকের কম। একজন রোগীকে দুবেলা যেখানে ১৭০ গ্রাম মাংস দেওয়ার কথা, সেখানে রোগী পান বড়জোর ৭৫ গ্রাম মাংস। বাকিটা কী হয়? প্রশ্নটা সহজ এবং উত্তরও সবার জানা।
বুঝলাম, দুদকের অভিযানে বেরিয়ে এসেছে এই তথ্য। কিন্তু এই ঘটনা তো এভাবেই দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ঘটে চলেছে। রোগীর প্রাপ্য খাদ্য লোপাট করছে স্বার্থান্বেষী মহল। তারা কি কারও অচেনা? হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কি তাদের চিহ্নিত করতে পারেনি কখনো, কখনো তাদের মনে প্রশ্ন জাগেনি যে চুরি হচ্ছে কোথাও, কোনো এক বিভাগে? যাঁরা চুরি করছেন, তাঁরা হাসপাতালেরই লোক?
যাঁদের সঙ্গে যোগসাজশে হচ্ছে এই চুরি, তাঁরাও অচেনা কেউ নয়?
আসলে চোরেরা এতটাই শক্তিশালী যে তাঁদের নিয়ে কেউ কথা বলতে সাহস পায় না। তার চেয়ে চোরদের সঙ্গে ভিড়ে যাওয়া অথবা চুরি সম্পর্কে নীরব থাকাই শ্রেয় বলে মনে
করে ছা-পোষা মানুষ। এ কারণেই হয়তোবা দিনের পর দিন চোরের সংখ্যা বাড়তে থাকে। আর জাতীয় পরিসরে যখন চুরির কথা ভাবা
হয়? আমরা নিশ্চিত, তাহলে বুকের রক্ত হিম হয়ে আসবে!

কৃষি গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে নেদারল্যান্ডস বিশ্বজুড়ে সুপরিচিত। আগামীর কৃষিকে টিকিয়ে রাখা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দেশটি দীর্ঘদিন ধরেই বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত সহায়তায় কৃষিপ্রযুক্তির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে যে প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখছে...
৪ দিন আগে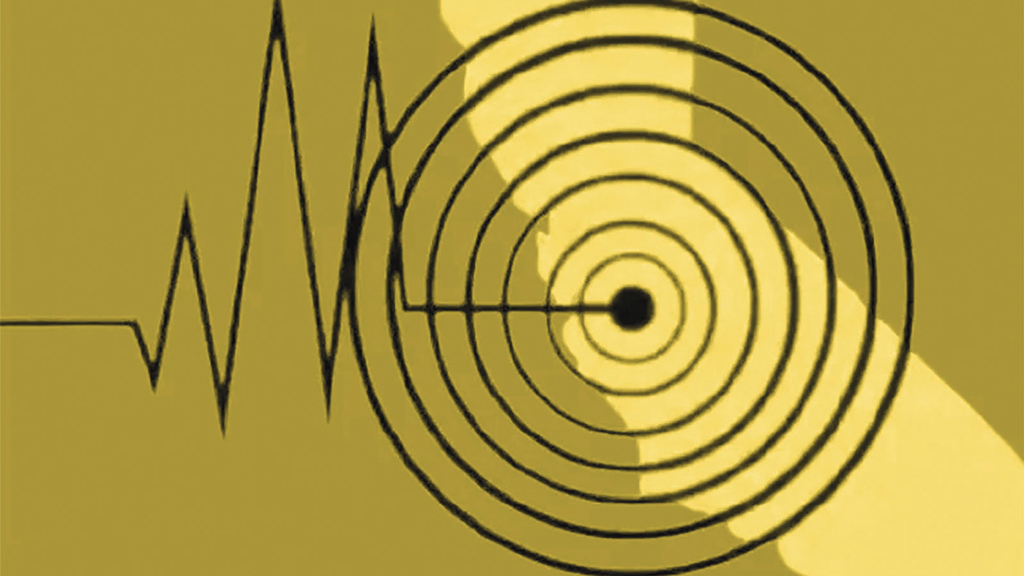
নরসিংদীতে ২১ নভেম্বর সংঘটিত ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্প দেশের ভূমিকম্পজনিত গভীর ঝুঁকির বাস্তবতাকে নতুন করে সামনে এনেছে। ২৬ সেকেন্ড স্থায়ী এই কম্পনটি ছিল দশকের মধ্যে এ অঞ্চলের অন্যতম শক্তিশালী ভূকম্পন।
৯ ঘণ্টা আগে
সম্প্রতি পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের (এফ) সভাপতি এবং দেশটির সাবেক মন্ত্রী মাওলানা ফজলুর রহমান বলেছেন, ‘পাকিস্তান সব সময় বাংলাদেশের কল্যাণ, উন্নতি, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা কামনা করে। বাংলাদেশকে তারা ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ হিসেবে মনে করে।
৯ ঘণ্টা আগে
বিশ্বায়নের যুগে একটি রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থাকে শুধু দেশের সীমানার ভেতরে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জ্ঞান ও উদ্ভাবনের কেন্দ্র হিসেবে এখন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার অংশ। তাই বিশ্বের শীর্ষ র্যাঙ্কিং তালিকায় একটি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপস্থিতি শুধু মর্যাদার বিষয় নয়, বরং তা একটি...
৯ ঘণ্টা আগেড. মুনাজ আহমেদ নূর
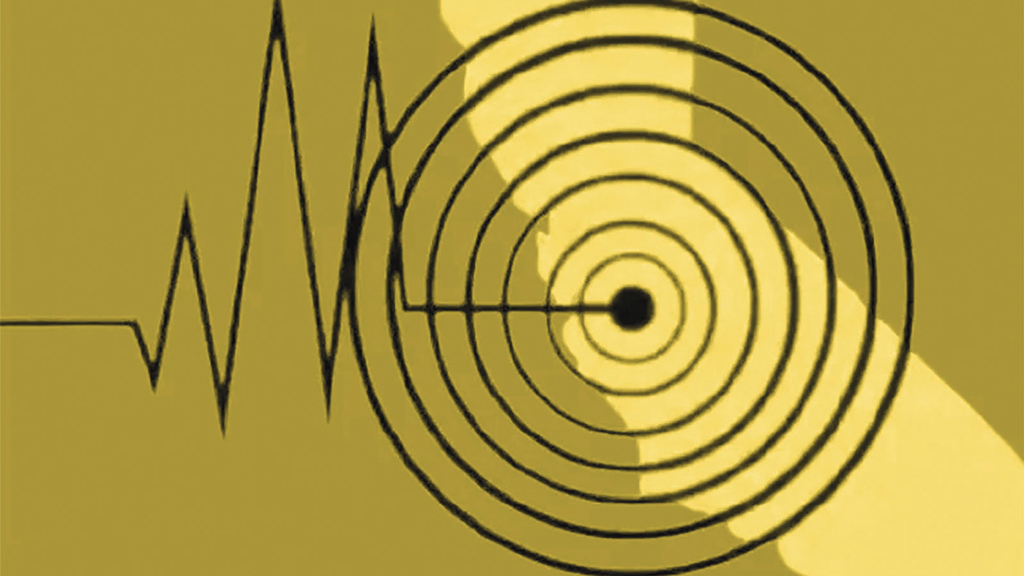
নরসিংদীতে ২১ নভেম্বর সংঘটিত ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্প দেশের ভূমিকম্পজনিত গভীর ঝুঁকির বাস্তবতাকে নতুন করে সামনে এনেছে। ২৬ সেকেন্ড স্থায়ী এই কম্পনটি ছিল দশকের মধ্যে এ অঞ্চলের অন্যতম শক্তিশালী ভূকম্পন। ভবন কেঁপে ওঠায় হাজারো মানুষ আতঙ্কে রাস্তায় বের হয়ে আসে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যুর খবর আসে, অনেকে আহত হয় মূলত দুর্বল স্থাপনার ভাঙা অংশের নিচে চাপা পড়ে। মাত্রায় মাঝারি হলেও এই ভূমিকম্প আমাদের মনে করিয়ে দিল অস্বস্তিকর সত্যটি—সক্রিয় টেকটোনিক ফল্টলাইনের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা বাংলাদেশ অনেক বড় ভূমিকম্পের মুখোমুখি হতে পারে যেকোনো সময়। বহু তরুণের জন্য এটি ছিল ভূমিকম্পের সঙ্গে প্রথম সরাসরি পরিচয়, যা সরকারকে বিষয়টিকে ‘গুরুতর সতর্কবার্তা’ হিসেবে স্বীকার করতে বাধ্য করেছে। ইতিহাস, বিজ্ঞান ও আমাদের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা এখন একই কথা বলছে—প্রস্তুতির জন্য সময় আর খুব বেশি নেই।
বিশ্বে যেসব দেশ ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে থাকে, তারা বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার উৎস। জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও তুরস্ক দেখিয়েছে, কঠোরভাবে প্রয়োগযোগ্য আধুনিক বিল্ডিং কোড প্রাণ বাঁচায়। তুরস্ক ১৯৯৮ সালে কোড শক্ত করার পর ২০২৩ সালের ভূমিকম্পে নতুন ভবনগুলো তুলনামূলকভাবে অনেক ভালোভাবে টিকে গিয়েছিল। ক্যালিফোর্নিয়ায় দুর্বল ইটের ভবন ও ‘সফট-স্টোরি’ স্থাপনার বাধ্যতামূলক রেট্রোফিটিং (পূর্বে নির্মিত বিল্ডিং বা কাঠামোয় নতুন কিছু সংযোগ করে, একে আরও শক্তিশালী করার প্রক্রিয়া) মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়েছে। এ কারণে ভবন এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে, যাতে কম্পনের সময় বাঁকতে পারে, কিন্তু ভেঙে না পড়ে। আর নিয়ম শুধু কাগজে নয়, প্রয়োগে নিশ্চিত করতে হবে।
জাপান এ ক্ষেত্রে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। ১৯৯৫ সালের কোবে ভূমিকম্পের পর দেশটি ব্যাপক আইন সংস্কার এনে রেট্রোফিটিংকে বাধ্যতামূলক ও উৎসাহপ্রদায়ক করেছে। আজ দেশটির ৮০ শতাংশের বেশি ঘরবাড়ি ভূমিকম্প-সহনশীল। সারা দেশে স্কুল, হাসপাতাল, সেতু ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় রেট্রোফিটিং হওয়ায় ২০২৪ সালের উত্তর জাপানের ভূমিকম্পে প্রাণহানি সীমিত রাখতে পারা সম্ভব হয়েছে। স্টিল ব্রেসিং, গ্রাউন্ড ফ্লোর শক্তিশালীকরণ, কলামে ফাইবার র্যাপ—এ ধরনের রেট্রোফিটিং এখন কার্যকর ও তুলনামূলক সাশ্রয়ী।
উন্নত প্রকৌশলব্যবস্থা ঝুঁকি কমানোর অতিরিক্ত স্তর তৈরি করতে পারে। জাপানে হাজারো ভবনে ব্যবহৃত বেস আইসোলেশন ও টিউনড মাস ড্যাম্পার প্রযুক্তি বড় ভূমিকম্পেও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোকে সচল রাখতে সহায়তা করেছে। অটোমেটিক গ্যাস শাট-অফ ভালভের মতো সহজ উদ্ভাবনও অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে কার্যকর। আর টোকিওতে এগুলো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। জাপান প্রতিবছর জাতীয় মহড়া চালায়, যুক্তরাষ্ট্রের শহরগুলো স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণ দেয় এবং জনসচেতনতা বাড়ায়। মোবাইল ও টিভির মাধ্যমে আগে থেকে সতর্কবার্তা দিলে ঝুঁকি কমাবে। যেটা জাপান, মেক্সিকো ও ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রচলিত। বাংলাদেশে এখনো এমন ব্যবস্থা নেই, কিন্তু এ মডেলগুলো গ্রহণ করা সম্ভব। বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা বলে—প্রতিরোধে ব্যয় দুর্যোগ-পরবর্তী ক্ষতির তুলনায় বহুগুণ কম।
বাংলাদেশে ভূমিকম্পের ঝুঁকি কমানোর সবচেয়ে বড় বাধাগুলোর একটি হলো বিপুলসংখ্যক ঝুঁকিপূর্ণ ভবনকে শক্তিশালী করার ব্যয়। নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে এ ধরনের ব্যাপক রেট্রোফিটিং করা চ্যালেঞ্জ হলেও, তা যেকোনো উপায়ে কার্যকর করার পথ খোঁজা জরুরি। কেবল ঢাকা শহরেই বড় একটি ভূমিকম্প প্রায় ৬৯ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি করতে পারে, যা প্রতিরোধমূলক ব্যয়ের বহুগুণ। তা সত্ত্বেও বাজেট-সংকট ও গৃহমালিকদের অনীহায় সেটা করা হচ্ছে না।
বহুমাত্রিক অর্থায়ন কৌশল জরুরি। সরকারের প্রথম অগ্রাধিকার হওয়া উচিত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো—হাসপাতাল, স্কুল, ফায়ার সার্ভিস স্টেশন, বিদ্যুৎ-গ্যাস নেটওয়ার্ক—যেগুলো সংকটে সচল থাকা প্রয়োজন। প্রয়োজনে বিশ্ব উন্নয়ন-সহযোগী সংস্থা ও অন্য দেশের সহযোগিতা নিয়েও উদ্যোগগুলো গ্রহণ করা। বৈশ্বিক এক তথ্য থেকে জানা যায়, রেজিলিয়েন্সে (আগের অবস্থায় ফিরে আসা) বিনিয়োগ করা প্রতি ১ ডলার ভবিষ্যৎ ক্ষতি থেকে ৪ ডলার বাঁচায়। বেসরকারি খাতকে উৎসাহ দিতে সম্পত্তি কর রিবেট, ইউটিলিটি ডিসকাউন্ট, শূন্য-সুদের রেট্রোফিটিং ঋণ ও জাতীয় ভূমিকম্প রেজিলিয়েন্স তহবিল গঠন করা যেতে পারে। ব্যাংকগুলো স্বল্পসুদের ঋণ দিতে পারে, আর তুরস্কের ‘ড্যাস্ক’ মডেল অনুসরণ করে ভূমিকম্প বিমা সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।
নতুন কিছু নির্মাণের ক্ষেত্রে অর্থায়ন সরাসরি ভূমিকম্প-নিরাপত্তা মানদণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। ব্যাংকগুলো যেন ঋণ দেওয়ার আগে সার্টিফায়েড স্ট্রাকচারাল ডিজাইন বাধ্যতামূলক করে। মানদণ্ড ছাড়িয়ে গেলে দ্রুত অনুমোদন বা অতিরিক্ত ফ্লোর এরিয়া দেওয়া যেতে পারে। নিয়ম ভঙ্গ করলে কঠোর শাস্তি, এমনকি ভবন ভেঙে ফেলা বাধ্যতামূলক করতে হবে। জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ দুর্যোগ বন্ড বা আঞ্চলিক বিমা পুলে যুক্ত হতে পারে। বড় নগর প্রকল্পে সামান্য ‘রেজিলিয়েন্স সারচার্জ’ আরোপ করে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় রেট্রোফিটিংয়ে অর্থ জোগানো সম্ভব। সরকার, উন্নয়ন-সহযোগী, বেসরকারি খাত ও জনগণের সমন্বয়েই নিরাপদ ভবিষ্যৎ গড়া সম্ভব।
তবে তাৎক্ষণিক অগ্রাধিকার হলো কাঠামোগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও দ্রুত প্রযুক্তি ব্যবহার করা। রাজউক, বুয়েট ও সামরিক প্রকৌশল দলগুলোকে ফাটল ধরা ভবন, বিশেষত পুরান ঢাকা পরিদর্শন করে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন দ্রুত খালি করতে হবে। নাগরিকদের মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতির তথ্য পাঠাতে উৎসাহিত করতে হবে, যাতে রিয়েল-টাইম ড্যাশবোর্ডে সব তথ্য জমা হয়। আফটারশক সতর্কতা, গ্যাস-বিদ্যুৎ লাইনের নিরাপত্তা পরীক্ষা ও অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধও জরুরি। ড্রোন, রিমোট সেন্সিং ও এআই ব্যবহার করে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা দ্রুত চিহ্নিত করা সম্ভব। গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে ভূমিকম্পে কীভাবে নিরাপদ থাকতে হবে, জরুরি কিটে কী থাকবে—এসব বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে।
বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোডকে কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে সব পৌরসভায়, যার জন্য প্রয়োজন বিল্ডিং সেফটি সেল, প্রশিক্ষিত পরিদর্শক ও কাঠামো প্রকৌশলী। তুরস্ক ও ভারতের মডেল দেখে রাবার বিয়ারিং, ফাইবার-রিইনফোর্সড পলিমার, ইঞ্জিনিয়ার্ড বাঁশ এবং গ্রাউন্ড ফ্লোর শক্তিশালীকরণের মতো উদ্ভাবনী প্রযুক্তির পাইলটিং করা যায়। জরুরি সেবা সংস্থাগুলোকে আধুনিক সরঞ্জাম, নিয়মিত মহড়া ও ডিজিটাল সমন্বয় ব্যবস্থা দিতে হবে। স্কুল কারিকুলাম, কমিউনিটি ভলান্টিয়ার ও প্রশিক্ষিত রাজমিস্ত্রি নেটওয়ার্ক গড়ে তুললে বস্তি ও অনানুষ্ঠানিক এলাকায় কম খরচে নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা সম্ভব। নীতি সংস্কার, স্ট্রাকচারাল ফিটনেস সার্টিফিকেট ও রেট্রোফিটিং ঋণব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে।
দীর্ঘ মেয়াদে (৫ বছরের বেশি) নগর-পরিকল্পনাকে ভূমিকম্প-সহনশীল করে গড়ে তুলতে হবে। সব নতুন ভবনকে ভূমিকম্প-নিরাপদ ডিজাইনে নির্মাণ করতে হবে এবং পুরোনো ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলোকে রেট্রোফিট বা সরিয়ে ফেলতে হবে। ডিজিটাল পারমিটিং সিস্টেম ও এআইভিত্তিক কমপ্লায়েন্স চেকের মাধ্যমে শুধুই কোডসম্মত নকশা অনুমোদন দেওয়া উচিত। শহর পরিকল্পনায় ভূমিকম্প-ঝুঁকির মানচিত্র, প্রশস্ত রাস্তা, উন্মুক্ত স্থান ও টেকসই অবকাঠামোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সফলতা নির্ভর করবে ভূকম্পন পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক বিস্তৃতি, স্থানীয় গবেষণা সহায়তা ও আঞ্চলিক সহযোগিতার ওপর। আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা ও শহরব্যাপী ডিজিটাল ঝুঁকিম্যাপ যুক্ত হলে প্রস্তুতি আরও শক্তিশালী হবে।
নরসিংদীর ভূমিকম্প মাত্রায় মাঝারি হলেও বাংলাদেশ ভূমিকম্প-ঝুঁকি থেকে নিরাপদ—এমন ভুল ধারণাকে সম্পূর্ণ দূর করেছে। প্রশ্ন এখন আর ‘কবে হবে’ নয়, বরং ‘যখন হবে তখন আমরা কতটা প্রস্তুত?’ এখন প্রয়োজন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগ—নিয়ম প্রয়োগ, প্রস্তুতি বৃদ্ধি, ত্রাণ-প্রতিক্রিয়া সক্ষমতা উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিকভাবে সফল মডেল অনুসরণ। একই সঙ্গে প্রযুক্তি, কমিউনিটি প্রশিক্ষণ ও বুদ্ধিমান নগর-পরিকল্পনার ভূমিকা অবহেলা করা যাবে না। যেভাবে বাংলাদেশ গত কয়েক দশকে ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় বিশ্বমানের সক্ষমতা অর্জন করেছে, ঠিক সেভাবেই ভূমিকম্প প্রস্তুতিতেও ঐতিহ্যগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে আধুনিক সমাধানের সমন্বয় ঘটাতে হবে। আজকের উদ্যোগ ও টেকসই বিনিয়োগই বাংলাদেশকে ঝুঁকির চক্র থেকে বের করে একটি নিরাপদ ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যেতে পারে।
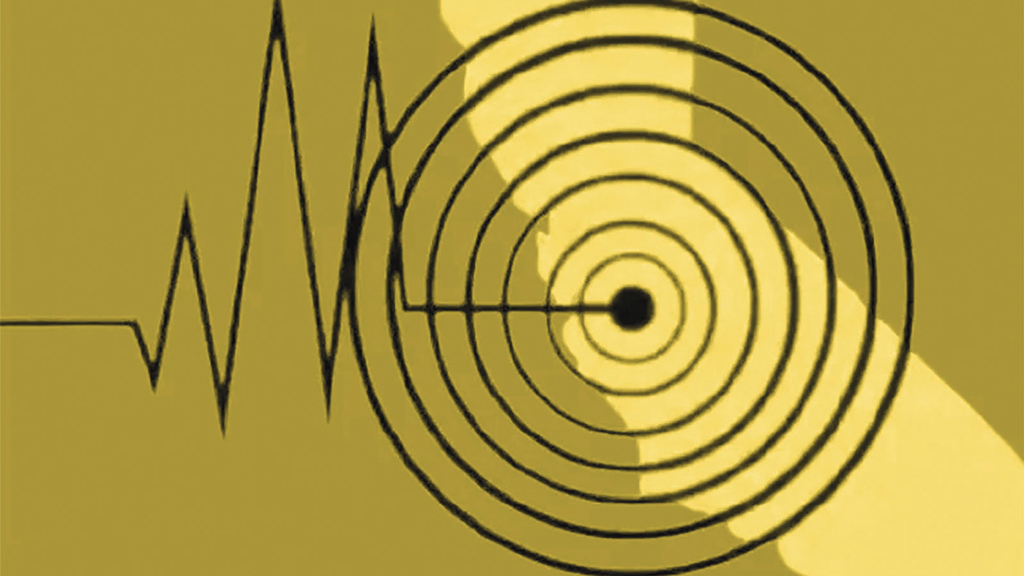
নরসিংদীতে ২১ নভেম্বর সংঘটিত ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্প দেশের ভূমিকম্পজনিত গভীর ঝুঁকির বাস্তবতাকে নতুন করে সামনে এনেছে। ২৬ সেকেন্ড স্থায়ী এই কম্পনটি ছিল দশকের মধ্যে এ অঞ্চলের অন্যতম শক্তিশালী ভূকম্পন। ভবন কেঁপে ওঠায় হাজারো মানুষ আতঙ্কে রাস্তায় বের হয়ে আসে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যুর খবর আসে, অনেকে আহত হয় মূলত দুর্বল স্থাপনার ভাঙা অংশের নিচে চাপা পড়ে। মাত্রায় মাঝারি হলেও এই ভূমিকম্প আমাদের মনে করিয়ে দিল অস্বস্তিকর সত্যটি—সক্রিয় টেকটোনিক ফল্টলাইনের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা বাংলাদেশ অনেক বড় ভূমিকম্পের মুখোমুখি হতে পারে যেকোনো সময়। বহু তরুণের জন্য এটি ছিল ভূমিকম্পের সঙ্গে প্রথম সরাসরি পরিচয়, যা সরকারকে বিষয়টিকে ‘গুরুতর সতর্কবার্তা’ হিসেবে স্বীকার করতে বাধ্য করেছে। ইতিহাস, বিজ্ঞান ও আমাদের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা এখন একই কথা বলছে—প্রস্তুতির জন্য সময় আর খুব বেশি নেই।
বিশ্বে যেসব দেশ ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে থাকে, তারা বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার উৎস। জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও তুরস্ক দেখিয়েছে, কঠোরভাবে প্রয়োগযোগ্য আধুনিক বিল্ডিং কোড প্রাণ বাঁচায়। তুরস্ক ১৯৯৮ সালে কোড শক্ত করার পর ২০২৩ সালের ভূমিকম্পে নতুন ভবনগুলো তুলনামূলকভাবে অনেক ভালোভাবে টিকে গিয়েছিল। ক্যালিফোর্নিয়ায় দুর্বল ইটের ভবন ও ‘সফট-স্টোরি’ স্থাপনার বাধ্যতামূলক রেট্রোফিটিং (পূর্বে নির্মিত বিল্ডিং বা কাঠামোয় নতুন কিছু সংযোগ করে, একে আরও শক্তিশালী করার প্রক্রিয়া) মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়েছে। এ কারণে ভবন এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে, যাতে কম্পনের সময় বাঁকতে পারে, কিন্তু ভেঙে না পড়ে। আর নিয়ম শুধু কাগজে নয়, প্রয়োগে নিশ্চিত করতে হবে।
জাপান এ ক্ষেত্রে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। ১৯৯৫ সালের কোবে ভূমিকম্পের পর দেশটি ব্যাপক আইন সংস্কার এনে রেট্রোফিটিংকে বাধ্যতামূলক ও উৎসাহপ্রদায়ক করেছে। আজ দেশটির ৮০ শতাংশের বেশি ঘরবাড়ি ভূমিকম্প-সহনশীল। সারা দেশে স্কুল, হাসপাতাল, সেতু ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় রেট্রোফিটিং হওয়ায় ২০২৪ সালের উত্তর জাপানের ভূমিকম্পে প্রাণহানি সীমিত রাখতে পারা সম্ভব হয়েছে। স্টিল ব্রেসিং, গ্রাউন্ড ফ্লোর শক্তিশালীকরণ, কলামে ফাইবার র্যাপ—এ ধরনের রেট্রোফিটিং এখন কার্যকর ও তুলনামূলক সাশ্রয়ী।
উন্নত প্রকৌশলব্যবস্থা ঝুঁকি কমানোর অতিরিক্ত স্তর তৈরি করতে পারে। জাপানে হাজারো ভবনে ব্যবহৃত বেস আইসোলেশন ও টিউনড মাস ড্যাম্পার প্রযুক্তি বড় ভূমিকম্পেও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোকে সচল রাখতে সহায়তা করেছে। অটোমেটিক গ্যাস শাট-অফ ভালভের মতো সহজ উদ্ভাবনও অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে কার্যকর। আর টোকিওতে এগুলো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। জাপান প্রতিবছর জাতীয় মহড়া চালায়, যুক্তরাষ্ট্রের শহরগুলো স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণ দেয় এবং জনসচেতনতা বাড়ায়। মোবাইল ও টিভির মাধ্যমে আগে থেকে সতর্কবার্তা দিলে ঝুঁকি কমাবে। যেটা জাপান, মেক্সিকো ও ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রচলিত। বাংলাদেশে এখনো এমন ব্যবস্থা নেই, কিন্তু এ মডেলগুলো গ্রহণ করা সম্ভব। বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা বলে—প্রতিরোধে ব্যয় দুর্যোগ-পরবর্তী ক্ষতির তুলনায় বহুগুণ কম।
বাংলাদেশে ভূমিকম্পের ঝুঁকি কমানোর সবচেয়ে বড় বাধাগুলোর একটি হলো বিপুলসংখ্যক ঝুঁকিপূর্ণ ভবনকে শক্তিশালী করার ব্যয়। নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে এ ধরনের ব্যাপক রেট্রোফিটিং করা চ্যালেঞ্জ হলেও, তা যেকোনো উপায়ে কার্যকর করার পথ খোঁজা জরুরি। কেবল ঢাকা শহরেই বড় একটি ভূমিকম্প প্রায় ৬৯ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি করতে পারে, যা প্রতিরোধমূলক ব্যয়ের বহুগুণ। তা সত্ত্বেও বাজেট-সংকট ও গৃহমালিকদের অনীহায় সেটা করা হচ্ছে না।
বহুমাত্রিক অর্থায়ন কৌশল জরুরি। সরকারের প্রথম অগ্রাধিকার হওয়া উচিত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো—হাসপাতাল, স্কুল, ফায়ার সার্ভিস স্টেশন, বিদ্যুৎ-গ্যাস নেটওয়ার্ক—যেগুলো সংকটে সচল থাকা প্রয়োজন। প্রয়োজনে বিশ্ব উন্নয়ন-সহযোগী সংস্থা ও অন্য দেশের সহযোগিতা নিয়েও উদ্যোগগুলো গ্রহণ করা। বৈশ্বিক এক তথ্য থেকে জানা যায়, রেজিলিয়েন্সে (আগের অবস্থায় ফিরে আসা) বিনিয়োগ করা প্রতি ১ ডলার ভবিষ্যৎ ক্ষতি থেকে ৪ ডলার বাঁচায়। বেসরকারি খাতকে উৎসাহ দিতে সম্পত্তি কর রিবেট, ইউটিলিটি ডিসকাউন্ট, শূন্য-সুদের রেট্রোফিটিং ঋণ ও জাতীয় ভূমিকম্প রেজিলিয়েন্স তহবিল গঠন করা যেতে পারে। ব্যাংকগুলো স্বল্পসুদের ঋণ দিতে পারে, আর তুরস্কের ‘ড্যাস্ক’ মডেল অনুসরণ করে ভূমিকম্প বিমা সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।
নতুন কিছু নির্মাণের ক্ষেত্রে অর্থায়ন সরাসরি ভূমিকম্প-নিরাপত্তা মানদণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। ব্যাংকগুলো যেন ঋণ দেওয়ার আগে সার্টিফায়েড স্ট্রাকচারাল ডিজাইন বাধ্যতামূলক করে। মানদণ্ড ছাড়িয়ে গেলে দ্রুত অনুমোদন বা অতিরিক্ত ফ্লোর এরিয়া দেওয়া যেতে পারে। নিয়ম ভঙ্গ করলে কঠোর শাস্তি, এমনকি ভবন ভেঙে ফেলা বাধ্যতামূলক করতে হবে। জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ দুর্যোগ বন্ড বা আঞ্চলিক বিমা পুলে যুক্ত হতে পারে। বড় নগর প্রকল্পে সামান্য ‘রেজিলিয়েন্স সারচার্জ’ আরোপ করে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় রেট্রোফিটিংয়ে অর্থ জোগানো সম্ভব। সরকার, উন্নয়ন-সহযোগী, বেসরকারি খাত ও জনগণের সমন্বয়েই নিরাপদ ভবিষ্যৎ গড়া সম্ভব।
তবে তাৎক্ষণিক অগ্রাধিকার হলো কাঠামোগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও দ্রুত প্রযুক্তি ব্যবহার করা। রাজউক, বুয়েট ও সামরিক প্রকৌশল দলগুলোকে ফাটল ধরা ভবন, বিশেষত পুরান ঢাকা পরিদর্শন করে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন দ্রুত খালি করতে হবে। নাগরিকদের মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতির তথ্য পাঠাতে উৎসাহিত করতে হবে, যাতে রিয়েল-টাইম ড্যাশবোর্ডে সব তথ্য জমা হয়। আফটারশক সতর্কতা, গ্যাস-বিদ্যুৎ লাইনের নিরাপত্তা পরীক্ষা ও অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধও জরুরি। ড্রোন, রিমোট সেন্সিং ও এআই ব্যবহার করে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা দ্রুত চিহ্নিত করা সম্ভব। গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে ভূমিকম্পে কীভাবে নিরাপদ থাকতে হবে, জরুরি কিটে কী থাকবে—এসব বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে।
বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোডকে কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে সব পৌরসভায়, যার জন্য প্রয়োজন বিল্ডিং সেফটি সেল, প্রশিক্ষিত পরিদর্শক ও কাঠামো প্রকৌশলী। তুরস্ক ও ভারতের মডেল দেখে রাবার বিয়ারিং, ফাইবার-রিইনফোর্সড পলিমার, ইঞ্জিনিয়ার্ড বাঁশ এবং গ্রাউন্ড ফ্লোর শক্তিশালীকরণের মতো উদ্ভাবনী প্রযুক্তির পাইলটিং করা যায়। জরুরি সেবা সংস্থাগুলোকে আধুনিক সরঞ্জাম, নিয়মিত মহড়া ও ডিজিটাল সমন্বয় ব্যবস্থা দিতে হবে। স্কুল কারিকুলাম, কমিউনিটি ভলান্টিয়ার ও প্রশিক্ষিত রাজমিস্ত্রি নেটওয়ার্ক গড়ে তুললে বস্তি ও অনানুষ্ঠানিক এলাকায় কম খরচে নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা সম্ভব। নীতি সংস্কার, স্ট্রাকচারাল ফিটনেস সার্টিফিকেট ও রেট্রোফিটিং ঋণব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে।
দীর্ঘ মেয়াদে (৫ বছরের বেশি) নগর-পরিকল্পনাকে ভূমিকম্প-সহনশীল করে গড়ে তুলতে হবে। সব নতুন ভবনকে ভূমিকম্প-নিরাপদ ডিজাইনে নির্মাণ করতে হবে এবং পুরোনো ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলোকে রেট্রোফিট বা সরিয়ে ফেলতে হবে। ডিজিটাল পারমিটিং সিস্টেম ও এআইভিত্তিক কমপ্লায়েন্স চেকের মাধ্যমে শুধুই কোডসম্মত নকশা অনুমোদন দেওয়া উচিত। শহর পরিকল্পনায় ভূমিকম্প-ঝুঁকির মানচিত্র, প্রশস্ত রাস্তা, উন্মুক্ত স্থান ও টেকসই অবকাঠামোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সফলতা নির্ভর করবে ভূকম্পন পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক বিস্তৃতি, স্থানীয় গবেষণা সহায়তা ও আঞ্চলিক সহযোগিতার ওপর। আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা ও শহরব্যাপী ডিজিটাল ঝুঁকিম্যাপ যুক্ত হলে প্রস্তুতি আরও শক্তিশালী হবে।
নরসিংদীর ভূমিকম্প মাত্রায় মাঝারি হলেও বাংলাদেশ ভূমিকম্প-ঝুঁকি থেকে নিরাপদ—এমন ভুল ধারণাকে সম্পূর্ণ দূর করেছে। প্রশ্ন এখন আর ‘কবে হবে’ নয়, বরং ‘যখন হবে তখন আমরা কতটা প্রস্তুত?’ এখন প্রয়োজন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগ—নিয়ম প্রয়োগ, প্রস্তুতি বৃদ্ধি, ত্রাণ-প্রতিক্রিয়া সক্ষমতা উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিকভাবে সফল মডেল অনুসরণ। একই সঙ্গে প্রযুক্তি, কমিউনিটি প্রশিক্ষণ ও বুদ্ধিমান নগর-পরিকল্পনার ভূমিকা অবহেলা করা যাবে না। যেভাবে বাংলাদেশ গত কয়েক দশকে ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় বিশ্বমানের সক্ষমতা অর্জন করেছে, ঠিক সেভাবেই ভূমিকম্প প্রস্তুতিতেও ঐতিহ্যগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে আধুনিক সমাধানের সমন্বয় ঘটাতে হবে। আজকের উদ্যোগ ও টেকসই বিনিয়োগই বাংলাদেশকে ঝুঁকির চক্র থেকে বের করে একটি নিরাপদ ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

কৃষি গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে নেদারল্যান্ডস বিশ্বজুড়ে সুপরিচিত। আগামীর কৃষিকে টিকিয়ে রাখা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দেশটি দীর্ঘদিন ধরেই বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত সহায়তায় কৃষিপ্রযুক্তির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে যে প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখছে...
৪ দিন আগে
দুর্নীতি আর অন্যায়ের সঙ্গে যে আমরা মিতালি পাতিয়েছি, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালের বর্তমান অবস্থা সে কথাকেই দৃঢ় ভিত্তির ওপর আবারও দাঁড় করিয়ে দেয়। খুবই সাদামাটা ছোট একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে আজকের পত্রিকায়। দুদক এ হাসপাতালে অভিযান চালিয়েছিল গত মঙ্গলবার।
৯ ঘণ্টা আগে
সম্প্রতি পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের (এফ) সভাপতি এবং দেশটির সাবেক মন্ত্রী মাওলানা ফজলুর রহমান বলেছেন, ‘পাকিস্তান সব সময় বাংলাদেশের কল্যাণ, উন্নতি, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা কামনা করে। বাংলাদেশকে তারা ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ হিসেবে মনে করে।
৯ ঘণ্টা আগে
বিশ্বায়নের যুগে একটি রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থাকে শুধু দেশের সীমানার ভেতরে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জ্ঞান ও উদ্ভাবনের কেন্দ্র হিসেবে এখন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার অংশ। তাই বিশ্বের শীর্ষ র্যাঙ্কিং তালিকায় একটি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপস্থিতি শুধু মর্যাদার বিষয় নয়, বরং তা একটি...
৯ ঘণ্টা আগেসেঁজুতি মুমু

সম্প্রতি পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের (এফ) সভাপতি এবং দেশটির সাবেক মন্ত্রী মাওলানা ফজলুর রহমান বলেছেন, ‘পাকিস্তান সব সময় বাংলাদেশের কল্যাণ, উন্নতি, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা কামনা করে। বাংলাদেশকে তারা ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ হিসেবে মনে করে। বাংলাদেশ-পাকিস্তান ভাই ভাই, অতীতের সবকিছু তারা ভুলে গেছে। অতীতের সবকিছু আমরা ভুলে গেছি!’ এই কথাটা শুনে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর বিখ্যাত ‘বাতাসে লাশের গন্ধ’ কবিতাটির কথা মনে পড়ে গেল।
‘আজো আমি বাতাসে লাশের গন্ধ পাই, আজো আমি মাটিতে মৃত্যুর নগ্ন নৃত্য দেখি, ধর্ষিতার কাতর চিৎকার শুনি আজো আমি তন্দ্রার ভেতরে—এ দেশ কি ভুলে গেছে সেই দুঃস্বপ্নের রাত, সেই রক্তাক্ত সময়?’
বাংলাদেশ ও পাকিস্তান ভাই ভাই—এই কথাটা অবধি আমার কোনো আপত্তি ছিল না। প্রশ্ন হলো, অতীতের সব ভুলে ভাই ভাই কীভাবে হওয়া সম্ভব? আমি অতীতের সব ভোলার কথাকে মোটেও সমর্থন করছি না। তবে বিশ্বযুদ্ধের পরও বিশ্বের যেসব দেশ শত্রু ছিল, তারা এখন বন্ধু। বন্ধু হতে দোষ নেই, তবে অতীত ভোলা যাবে না। ১৯৪৭-৭১ সাল অবধি দীর্ঘ ২৪ বছরের নিপীড়ন ভোলা এত সহজ? লাখ লাখ শহীদের রক্ত, লাখ লাখ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি, সেই অতীত ভুলে যাওয়া সম্ভব? তিনি কীভাবে বলতে পারলেন কথাটি।
বর্তমান পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের বিরোধ নেই। চিরকাল কোনো দেশ শত্রু থাকতে পারে না। নিজের দেশের স্বার্থে পুরোনো শত্রুর সঙ্গে বন্ধুতা করাই শ্রেয়। শত্রুতা খালি ধ্বংস বয়ে আনে। তবে তার মানে এই নয় যে অতীত ভুলে যাব। এক কোটি বাস্তুহারা শরণার্থীর কান্না ভুলে যাওয়া অসম্ভব। আমরা জেন-জি প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের রক্তের প্রতিটা কণায় মিশে আছে। কারণ, আমরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানি—মুক্তিযুদ্ধের ডকুমেন্টারি ও সিনেমা দেখে এবং মা-বাবা, দাদা-দাদির কাছে মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ দিনগুলোর গল্প শুনে। শুধু জেন-জি প্রজন্ম কেন, আগামী দিনের অনাগত প্রজন্মও ভুলবে না মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। কোনো বিকৃত ইতিহাস নয়, বরং আমাদের রক্তের ইতিহাস। তা ভুলে যাওয়া অসম্ভব। আমি নিশ্চিত, পাকিস্তানে যদি এই রকম হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটত, তবে তিনি এই কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না।
আমি বারবার একই কথা বলব, বাংলাদেশ-পাকিস্তান বন্ধু হতেই পারে, কিন্তু অতীত ভুলে নয়। বর্তমানে দুই দেশের স্বার্থে বাংলাদেশ-পাকিস্তান বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক চুক্তি করবে। একে অন্যের সাহায্য করবে, বিভিন্ন বিষয়ে একে অপরের মধ্যে সম্পদ, শিক্ষা বিনিময় করবে, একত্রে গবেষণা করবে, পরস্পর পরস্পরের দেশে সফর করবে। এই তো হবে একই মহাদেশে অবস্থিত দুই প্রতিবেশী দেশের সম্পর্ক। কিন্তু তাই বলে অতীত ভোলা অসম্ভব।
বাংলাদেশ ও পাকিস্তান মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। তবে আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতি সব আলাদা। তবে তা দুই দেশের সম্পর্কের মাঝে বাধা হবে না। বর্তমান যুগ বিশ্বায়নের যুগ। একে অপরের শিক্ষা, গবেষণা, সংস্কৃতি থেকে অনেক কিছু শিখবে। একে অপরের ভালো দিকগুলো নেবে। কিন্তু তাই বলে যে অতীত ভুলে যাব, তা সম্ভব নয়। আমাদের ভাইয়ের রক্ত, আমাদের মা-বোনের সম্ভ্রম, বাস্তুহারা পরিবারের আর্তনাদ আজ ৫৪ বছর পর কেন, হাজার বছরেও ভোলা অসম্ভব। যেভাবে আজও মানুষ ভোলেনি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, ভোলেনি হাজার বছর আগের সহিংস যুদ্ধগুলোর ইতিহাস। তেমনি বাংলাদেশিরা কোনো দিনও ভুলতে পারবে না মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস।
মাওলানা ফজলুর রহমানের উদ্দেশে বলতে চাই, নিজের প্রয়োজনে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক থাকবে। কিন্তু আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্য, আমাদের ইতিহাস আমরা কোনো দিন ভুলব না। কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক হবে বর্তমান পাকিস্তানের সঙ্গে, কিন্তু ১৯৪৭-৭১-এর পাকিস্তানের সঙ্গে সখ্য সম্ভব নয়। সেই প্রজন্ম চলে গেছে, অনেকে বেঁচে আছে হয়তো। কিন্তু আমাদের বর্তমান পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধ নেই। আসুন, আমরা একসঙ্গে গবেষণা করব, বাণিজ্যিক চুক্তি করব, কিন্তু দুঃখিত, আমাদের অতীত ভোলা সম্ভব নয়।

সম্প্রতি পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের (এফ) সভাপতি এবং দেশটির সাবেক মন্ত্রী মাওলানা ফজলুর রহমান বলেছেন, ‘পাকিস্তান সব সময় বাংলাদেশের কল্যাণ, উন্নতি, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা কামনা করে। বাংলাদেশকে তারা ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ হিসেবে মনে করে। বাংলাদেশ-পাকিস্তান ভাই ভাই, অতীতের সবকিছু তারা ভুলে গেছে। অতীতের সবকিছু আমরা ভুলে গেছি!’ এই কথাটা শুনে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর বিখ্যাত ‘বাতাসে লাশের গন্ধ’ কবিতাটির কথা মনে পড়ে গেল।
‘আজো আমি বাতাসে লাশের গন্ধ পাই, আজো আমি মাটিতে মৃত্যুর নগ্ন নৃত্য দেখি, ধর্ষিতার কাতর চিৎকার শুনি আজো আমি তন্দ্রার ভেতরে—এ দেশ কি ভুলে গেছে সেই দুঃস্বপ্নের রাত, সেই রক্তাক্ত সময়?’
বাংলাদেশ ও পাকিস্তান ভাই ভাই—এই কথাটা অবধি আমার কোনো আপত্তি ছিল না। প্রশ্ন হলো, অতীতের সব ভুলে ভাই ভাই কীভাবে হওয়া সম্ভব? আমি অতীতের সব ভোলার কথাকে মোটেও সমর্থন করছি না। তবে বিশ্বযুদ্ধের পরও বিশ্বের যেসব দেশ শত্রু ছিল, তারা এখন বন্ধু। বন্ধু হতে দোষ নেই, তবে অতীত ভোলা যাবে না। ১৯৪৭-৭১ সাল অবধি দীর্ঘ ২৪ বছরের নিপীড়ন ভোলা এত সহজ? লাখ লাখ শহীদের রক্ত, লাখ লাখ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি, সেই অতীত ভুলে যাওয়া সম্ভব? তিনি কীভাবে বলতে পারলেন কথাটি।
বর্তমান পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের বিরোধ নেই। চিরকাল কোনো দেশ শত্রু থাকতে পারে না। নিজের দেশের স্বার্থে পুরোনো শত্রুর সঙ্গে বন্ধুতা করাই শ্রেয়। শত্রুতা খালি ধ্বংস বয়ে আনে। তবে তার মানে এই নয় যে অতীত ভুলে যাব। এক কোটি বাস্তুহারা শরণার্থীর কান্না ভুলে যাওয়া অসম্ভব। আমরা জেন-জি প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের রক্তের প্রতিটা কণায় মিশে আছে। কারণ, আমরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানি—মুক্তিযুদ্ধের ডকুমেন্টারি ও সিনেমা দেখে এবং মা-বাবা, দাদা-দাদির কাছে মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ দিনগুলোর গল্প শুনে। শুধু জেন-জি প্রজন্ম কেন, আগামী দিনের অনাগত প্রজন্মও ভুলবে না মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। কোনো বিকৃত ইতিহাস নয়, বরং আমাদের রক্তের ইতিহাস। তা ভুলে যাওয়া অসম্ভব। আমি নিশ্চিত, পাকিস্তানে যদি এই রকম হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটত, তবে তিনি এই কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না।
আমি বারবার একই কথা বলব, বাংলাদেশ-পাকিস্তান বন্ধু হতেই পারে, কিন্তু অতীত ভুলে নয়। বর্তমানে দুই দেশের স্বার্থে বাংলাদেশ-পাকিস্তান বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক চুক্তি করবে। একে অন্যের সাহায্য করবে, বিভিন্ন বিষয়ে একে অপরের মধ্যে সম্পদ, শিক্ষা বিনিময় করবে, একত্রে গবেষণা করবে, পরস্পর পরস্পরের দেশে সফর করবে। এই তো হবে একই মহাদেশে অবস্থিত দুই প্রতিবেশী দেশের সম্পর্ক। কিন্তু তাই বলে অতীত ভোলা অসম্ভব।
বাংলাদেশ ও পাকিস্তান মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। তবে আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতি সব আলাদা। তবে তা দুই দেশের সম্পর্কের মাঝে বাধা হবে না। বর্তমান যুগ বিশ্বায়নের যুগ। একে অপরের শিক্ষা, গবেষণা, সংস্কৃতি থেকে অনেক কিছু শিখবে। একে অপরের ভালো দিকগুলো নেবে। কিন্তু তাই বলে যে অতীত ভুলে যাব, তা সম্ভব নয়। আমাদের ভাইয়ের রক্ত, আমাদের মা-বোনের সম্ভ্রম, বাস্তুহারা পরিবারের আর্তনাদ আজ ৫৪ বছর পর কেন, হাজার বছরেও ভোলা অসম্ভব। যেভাবে আজও মানুষ ভোলেনি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, ভোলেনি হাজার বছর আগের সহিংস যুদ্ধগুলোর ইতিহাস। তেমনি বাংলাদেশিরা কোনো দিনও ভুলতে পারবে না মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস।
মাওলানা ফজলুর রহমানের উদ্দেশে বলতে চাই, নিজের প্রয়োজনে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক থাকবে। কিন্তু আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্য, আমাদের ইতিহাস আমরা কোনো দিন ভুলব না। কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক হবে বর্তমান পাকিস্তানের সঙ্গে, কিন্তু ১৯৪৭-৭১-এর পাকিস্তানের সঙ্গে সখ্য সম্ভব নয়। সেই প্রজন্ম চলে গেছে, অনেকে বেঁচে আছে হয়তো। কিন্তু আমাদের বর্তমান পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধ নেই। আসুন, আমরা একসঙ্গে গবেষণা করব, বাণিজ্যিক চুক্তি করব, কিন্তু দুঃখিত, আমাদের অতীত ভোলা সম্ভব নয়।

কৃষি গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে নেদারল্যান্ডস বিশ্বজুড়ে সুপরিচিত। আগামীর কৃষিকে টিকিয়ে রাখা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দেশটি দীর্ঘদিন ধরেই বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত সহায়তায় কৃষিপ্রযুক্তির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে যে প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখছে...
৪ দিন আগে
দুর্নীতি আর অন্যায়ের সঙ্গে যে আমরা মিতালি পাতিয়েছি, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালের বর্তমান অবস্থা সে কথাকেই দৃঢ় ভিত্তির ওপর আবারও দাঁড় করিয়ে দেয়। খুবই সাদামাটা ছোট একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে আজকের পত্রিকায়। দুদক এ হাসপাতালে অভিযান চালিয়েছিল গত মঙ্গলবার।
৯ ঘণ্টা আগে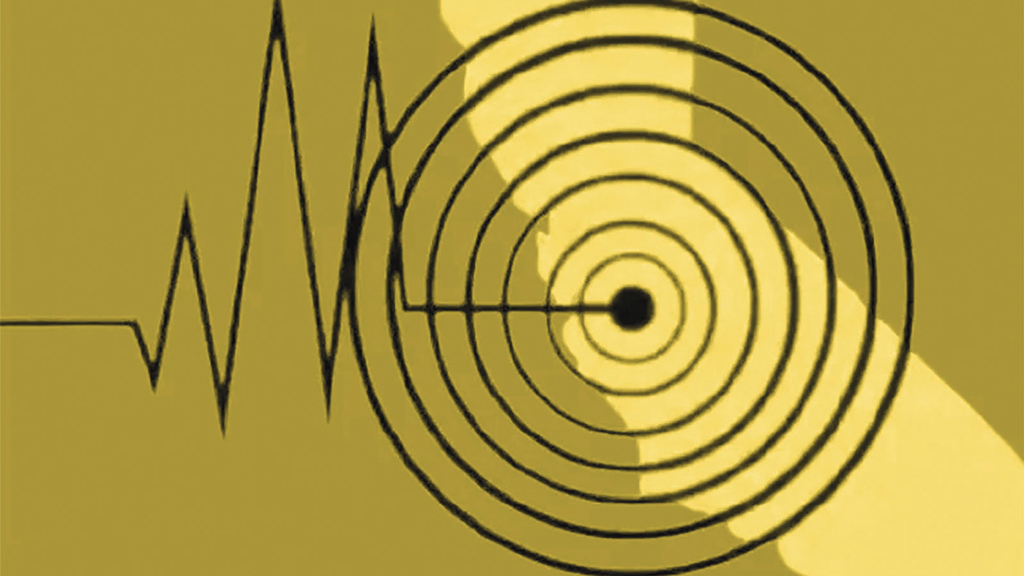
নরসিংদীতে ২১ নভেম্বর সংঘটিত ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্প দেশের ভূমিকম্পজনিত গভীর ঝুঁকির বাস্তবতাকে নতুন করে সামনে এনেছে। ২৬ সেকেন্ড স্থায়ী এই কম্পনটি ছিল দশকের মধ্যে এ অঞ্চলের অন্যতম শক্তিশালী ভূকম্পন।
৯ ঘণ্টা আগে
বিশ্বায়নের যুগে একটি রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থাকে শুধু দেশের সীমানার ভেতরে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জ্ঞান ও উদ্ভাবনের কেন্দ্র হিসেবে এখন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার অংশ। তাই বিশ্বের শীর্ষ র্যাঙ্কিং তালিকায় একটি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপস্থিতি শুধু মর্যাদার বিষয় নয়, বরং তা একটি...
৯ ঘণ্টা আগেসাদিয়া সুলতানা রিমি

বিশ্বায়নের যুগে একটি রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থাকে শুধু দেশের সীমানার ভেতরে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জ্ঞান ও উদ্ভাবনের কেন্দ্র হিসেবে এখন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার অংশ। তাই বিশ্বের শীর্ষ র্যাঙ্কিং তালিকায় একটি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপস্থিতি শুধু মর্যাদার বিষয় নয়, বরং তা একটি দেশের শিক্ষার মান, গবেষণা সক্ষমতা ও মানবসম্পদের প্রতিফলন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন ওঠে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কোথায় দাঁড়িয়ে? কেন পিছিয়ে আছে? আর এই অবস্থান থেকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার উপায়ই-বা কী?
বিশ্ববিদ্যালয়ের র্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে আলোচিত দুটি প্ল্যাটফর্ম হলো যুক্তরাজ্যভিত্তিক ‘কিউএস ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং’ এবং ‘টাইমস হায়ার এডুকেশন (টিএইচই) ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং’। এই তালিকাগুলোতে বিশ্বের হাজার হাজার বিশ্ববিদ্যালয় নানা সূচকের ভিত্তিতে মূল্যায়িত হয়—যেমন গবেষণা, একাডেমিক সুনাম, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী উপস্থিতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত, শিল্প সহযোগিতা ইত্যাদি। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ অনেক প্রতিষ্ঠান এসব তালিকায় অংশ নেয় বটে, কিন্তু শীর্ষ স্থানে পৌঁছাতে পারে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ‘টিএইচই’ র্যাঙ্কিংয়ে সাধারণত ৮০১-১০০০ অথবা তারও পরের ক্যাটাগরিতে অবস্থান করছে। ‘কিউএস’ র্যাঙ্কিংয়েও এটি প্রায় ১০০১+ স্তরে অবস্থান করে। বুয়েটও কখনো কখনো সামান্য ভালো জায়গায় উঠে এলেও, এখনো তা বিশ্বের সেরা ৫০০-এর ভেতরে স্থান করতে পারেনি। অর্থাৎ সার্বিকভাবে বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের শীর্ষ ৫০০-এর তালিকায় এখনো জায়গা করে নিতে পারেনি।
এ অবস্থানের পেছনের অন্যতম কারণ হলো, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণার পরিমাণ ও মান যথেষ্ট নয়। বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় মানেই শুধু ক্লাসরুমে জ্ঞান বিতরণ নয়; বরং নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা-সংস্কৃতি এখনো সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হয়নি। গবেষণায় অর্থায়নের অভাব, ল্যাব ও আধুনিক যন্ত্রপাতির সীমাবদ্ধতা, বিদেশি জার্নালে প্রকাশনার জটিলতা এসব কারণে আমাদের গবেষণা আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠতে পারে না। বিশ্বে হার্ভার্ড, অক্সফোর্ড বা ন্যানইয়াং টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটি গবেষণার ওপর যে গুরুত্ব দেয়, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেখানে এখনো পথচলার শুরুতে।
আরেকটি বড় ঘাটতি দেখা যায় আন্তর্জাতিকীকরণে। বিশ্ব র্যাঙ্কিং মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হলো বিশ্ববিদ্যালয়ে কতজন বিদেশি শিক্ষার্থী ও শিক্ষক রয়েছেন এবং তাঁদের সঙ্গে কতটা আন্তর্জাতিক সহযোগিতা রয়েছে। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিদেশি শিক্ষার্থী বা প্রফেসরের সংখ্যা খুবই কম। আমাদের বেশির ভাগ পাঠ্যক্রমও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে তৈরি নয়। এতে আন্তর্জাতিক একাডেমিক বিনিময় ও বহুভাষিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে না। তুলনামূলকভাবে ভারত, মালয়েশিয়া বা চীনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিদেশি শিক্ষার্থী আকর্ষণে অনেক এগিয়ে আছে।
শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত, অবকাঠামো ও একাডেমিক পরিবেশও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও সেই অনুপাতে শিক্ষক, আধুনিক ল্যাব, লাইব্রেরি, গবেষণা তহবিল বা আবাসিক পরিবেশ তৈরি হয়নি। ফলে মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে চাপ তৈরি হয়। একই সঙ্গে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক জটিলতা, রাজনীতি, সেশনজট, শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতার সংকটও শিক্ষার মানকে প্রভাবিত করছে।
তবে সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়তো মানগত উন্নয়নের পরিকল্পনায় ধারাবাহিকতার অভাব। অনেক সময় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর লক্ষ্য থাকে শুধুই ডিগ্রি প্রদান; কিন্তু বিশ্বমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তারা সমাজকে বদলে দেওয়ার জন্য উদ্ভাবন, স্টার্টআপ সংস্কৃতি, শিল্প খাতের সঙ্গে গবেষণা সহযোগিতা, প্রযুক্তিগত আবিষ্কার—এগুলোকে কেন্দ্র করে শিক্ষা ও গবেষণাকে গড়ে তোলার কাজ করে। বাংলাদেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব বিষয়ে পরিকল্পনা থাকলেও বাস্তবায়নের কার্যকর উদ্যোগ এখনো কম।
তবে এই ছবির মাঝেও রয়েছে আশার আলো। প্রথমত, বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম আজ অভূতপূর্বভাবে প্রযুক্তি, গবেষণা ও আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহী। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে Robotics Club, Research Cell, Debate Forum বা Innovation Hub গড়ে উঠছে। পাবলিক ও প্রাইভেট উভয় খাতেই কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক মানের ল্যাব, গবেষণা ফান্ড ও প্রযুক্তিগত সুবিধা তৈরি করছে। কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, যেমন ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি এখন আন্তর্জাতিক গবেষণা ও এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে বেশ সক্রিয়।
বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন নির্ভর করবে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির ওপর। শিক্ষাব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানের করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে শুধু র্যাঙ্কিংয়ের কথা মাথায় না রেখে জ্ঞান ও উদ্ভাবনের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় যদি তার নিজস্ব বিশেষায়িত ক্ষেত্র তৈরি করে কারও কৃষি গবেষণায় দক্ষতা, কেউ মেরিন সায়েন্সে, কেউ প্রযুক্তি বা জনস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে, তাহলে দেশের সামগ্রিক উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে পরিবর্তন ঘটবে।
বাংলাদেশ এখন বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ বাইরেও নয়। আমরা এখনো ৮০০ কিংবা ১০০০-এর গণ্ডিতে অবস্থান করছি। এটা হয়তো গৌরবের জায়গা নয়, কিন্তু শুরু করার জায়গা। যদি পরিকল্পনা, রাজনৈতিক সদিচ্ছা, শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও গবেষণা বিনিয়োগ একসঙ্গে বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে আগামী এক দশকেই বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের শীর্ষ ৫০০-এর তালিকায় পৌঁছাবে, এমন আশা অমূলক নয়। আমাদের প্রয়োজন লক্ষ্যভিত্তিক কাজ, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং একাডেমিক সততা। তাহলে ‘বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয়’ আর শুধু স্বপ্ন থাকবে না, হতে পারে বাস্তবতা।

বিশ্বায়নের যুগে একটি রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থাকে শুধু দেশের সীমানার ভেতরে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জ্ঞান ও উদ্ভাবনের কেন্দ্র হিসেবে এখন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার অংশ। তাই বিশ্বের শীর্ষ র্যাঙ্কিং তালিকায় একটি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপস্থিতি শুধু মর্যাদার বিষয় নয়, বরং তা একটি দেশের শিক্ষার মান, গবেষণা সক্ষমতা ও মানবসম্পদের প্রতিফলন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন ওঠে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কোথায় দাঁড়িয়ে? কেন পিছিয়ে আছে? আর এই অবস্থান থেকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার উপায়ই-বা কী?
বিশ্ববিদ্যালয়ের র্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে আলোচিত দুটি প্ল্যাটফর্ম হলো যুক্তরাজ্যভিত্তিক ‘কিউএস ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং’ এবং ‘টাইমস হায়ার এডুকেশন (টিএইচই) ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং’। এই তালিকাগুলোতে বিশ্বের হাজার হাজার বিশ্ববিদ্যালয় নানা সূচকের ভিত্তিতে মূল্যায়িত হয়—যেমন গবেষণা, একাডেমিক সুনাম, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী উপস্থিতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত, শিল্প সহযোগিতা ইত্যাদি। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ অনেক প্রতিষ্ঠান এসব তালিকায় অংশ নেয় বটে, কিন্তু শীর্ষ স্থানে পৌঁছাতে পারে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ‘টিএইচই’ র্যাঙ্কিংয়ে সাধারণত ৮০১-১০০০ অথবা তারও পরের ক্যাটাগরিতে অবস্থান করছে। ‘কিউএস’ র্যাঙ্কিংয়েও এটি প্রায় ১০০১+ স্তরে অবস্থান করে। বুয়েটও কখনো কখনো সামান্য ভালো জায়গায় উঠে এলেও, এখনো তা বিশ্বের সেরা ৫০০-এর ভেতরে স্থান করতে পারেনি। অর্থাৎ সার্বিকভাবে বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের শীর্ষ ৫০০-এর তালিকায় এখনো জায়গা করে নিতে পারেনি।
এ অবস্থানের পেছনের অন্যতম কারণ হলো, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণার পরিমাণ ও মান যথেষ্ট নয়। বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় মানেই শুধু ক্লাসরুমে জ্ঞান বিতরণ নয়; বরং নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা-সংস্কৃতি এখনো সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হয়নি। গবেষণায় অর্থায়নের অভাব, ল্যাব ও আধুনিক যন্ত্রপাতির সীমাবদ্ধতা, বিদেশি জার্নালে প্রকাশনার জটিলতা এসব কারণে আমাদের গবেষণা আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠতে পারে না। বিশ্বে হার্ভার্ড, অক্সফোর্ড বা ন্যানইয়াং টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটি গবেষণার ওপর যে গুরুত্ব দেয়, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেখানে এখনো পথচলার শুরুতে।
আরেকটি বড় ঘাটতি দেখা যায় আন্তর্জাতিকীকরণে। বিশ্ব র্যাঙ্কিং মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হলো বিশ্ববিদ্যালয়ে কতজন বিদেশি শিক্ষার্থী ও শিক্ষক রয়েছেন এবং তাঁদের সঙ্গে কতটা আন্তর্জাতিক সহযোগিতা রয়েছে। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিদেশি শিক্ষার্থী বা প্রফেসরের সংখ্যা খুবই কম। আমাদের বেশির ভাগ পাঠ্যক্রমও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে তৈরি নয়। এতে আন্তর্জাতিক একাডেমিক বিনিময় ও বহুভাষিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে না। তুলনামূলকভাবে ভারত, মালয়েশিয়া বা চীনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিদেশি শিক্ষার্থী আকর্ষণে অনেক এগিয়ে আছে।
শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত, অবকাঠামো ও একাডেমিক পরিবেশও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও সেই অনুপাতে শিক্ষক, আধুনিক ল্যাব, লাইব্রেরি, গবেষণা তহবিল বা আবাসিক পরিবেশ তৈরি হয়নি। ফলে মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে চাপ তৈরি হয়। একই সঙ্গে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক জটিলতা, রাজনীতি, সেশনজট, শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতার সংকটও শিক্ষার মানকে প্রভাবিত করছে।
তবে সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়তো মানগত উন্নয়নের পরিকল্পনায় ধারাবাহিকতার অভাব। অনেক সময় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর লক্ষ্য থাকে শুধুই ডিগ্রি প্রদান; কিন্তু বিশ্বমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তারা সমাজকে বদলে দেওয়ার জন্য উদ্ভাবন, স্টার্টআপ সংস্কৃতি, শিল্প খাতের সঙ্গে গবেষণা সহযোগিতা, প্রযুক্তিগত আবিষ্কার—এগুলোকে কেন্দ্র করে শিক্ষা ও গবেষণাকে গড়ে তোলার কাজ করে। বাংলাদেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব বিষয়ে পরিকল্পনা থাকলেও বাস্তবায়নের কার্যকর উদ্যোগ এখনো কম।
তবে এই ছবির মাঝেও রয়েছে আশার আলো। প্রথমত, বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম আজ অভূতপূর্বভাবে প্রযুক্তি, গবেষণা ও আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহী। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে Robotics Club, Research Cell, Debate Forum বা Innovation Hub গড়ে উঠছে। পাবলিক ও প্রাইভেট উভয় খাতেই কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক মানের ল্যাব, গবেষণা ফান্ড ও প্রযুক্তিগত সুবিধা তৈরি করছে। কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, যেমন ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি এখন আন্তর্জাতিক গবেষণা ও এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে বেশ সক্রিয়।
বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন নির্ভর করবে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির ওপর। শিক্ষাব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানের করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে শুধু র্যাঙ্কিংয়ের কথা মাথায় না রেখে জ্ঞান ও উদ্ভাবনের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় যদি তার নিজস্ব বিশেষায়িত ক্ষেত্র তৈরি করে কারও কৃষি গবেষণায় দক্ষতা, কেউ মেরিন সায়েন্সে, কেউ প্রযুক্তি বা জনস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে, তাহলে দেশের সামগ্রিক উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে পরিবর্তন ঘটবে।
বাংলাদেশ এখন বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ বাইরেও নয়। আমরা এখনো ৮০০ কিংবা ১০০০-এর গণ্ডিতে অবস্থান করছি। এটা হয়তো গৌরবের জায়গা নয়, কিন্তু শুরু করার জায়গা। যদি পরিকল্পনা, রাজনৈতিক সদিচ্ছা, শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও গবেষণা বিনিয়োগ একসঙ্গে বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে আগামী এক দশকেই বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের শীর্ষ ৫০০-এর তালিকায় পৌঁছাবে, এমন আশা অমূলক নয়। আমাদের প্রয়োজন লক্ষ্যভিত্তিক কাজ, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং একাডেমিক সততা। তাহলে ‘বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয়’ আর শুধু স্বপ্ন থাকবে না, হতে পারে বাস্তবতা।

কৃষি গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে নেদারল্যান্ডস বিশ্বজুড়ে সুপরিচিত। আগামীর কৃষিকে টিকিয়ে রাখা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দেশটি দীর্ঘদিন ধরেই বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত সহায়তায় কৃষিপ্রযুক্তির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে যে প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখছে...
৪ দিন আগে
দুর্নীতি আর অন্যায়ের সঙ্গে যে আমরা মিতালি পাতিয়েছি, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালের বর্তমান অবস্থা সে কথাকেই দৃঢ় ভিত্তির ওপর আবারও দাঁড় করিয়ে দেয়। খুবই সাদামাটা ছোট একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে আজকের পত্রিকায়। দুদক এ হাসপাতালে অভিযান চালিয়েছিল গত মঙ্গলবার।
৯ ঘণ্টা আগে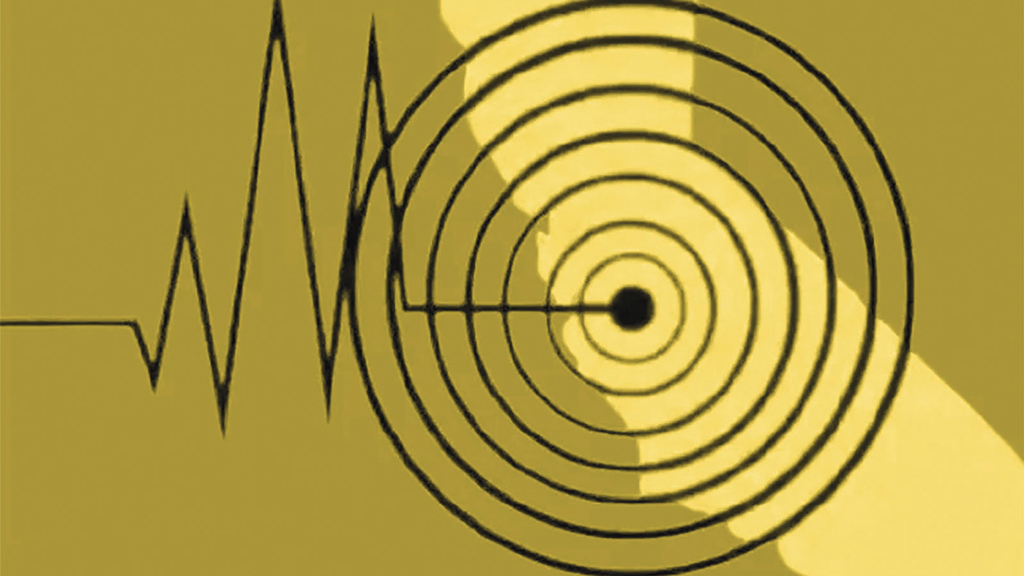
নরসিংদীতে ২১ নভেম্বর সংঘটিত ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্প দেশের ভূমিকম্পজনিত গভীর ঝুঁকির বাস্তবতাকে নতুন করে সামনে এনেছে। ২৬ সেকেন্ড স্থায়ী এই কম্পনটি ছিল দশকের মধ্যে এ অঞ্চলের অন্যতম শক্তিশালী ভূকম্পন।
৯ ঘণ্টা আগে
সম্প্রতি পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের (এফ) সভাপতি এবং দেশটির সাবেক মন্ত্রী মাওলানা ফজলুর রহমান বলেছেন, ‘পাকিস্তান সব সময় বাংলাদেশের কল্যাণ, উন্নতি, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা কামনা করে। বাংলাদেশকে তারা ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ হিসেবে মনে করে।
৯ ঘণ্টা আগে